
।। ফরহাদ মজহার ।।
লেখালিখি শেখার বিপদ হচ্ছে যারা শিখবে লেখালিখি তাদের আলাভোলা করে তুলবে, কারন তারা তাদের স্মৃতিশক্তিকে আর ব্যবহার করবে না; নিজের বাইরে লিখিত অক্ষরগুলাকেই বিশ্বাস করবে তারা, নিজেকে আর মনে রাখবে না। যে বিশেষ উপায় তোমরা আবিষ্কার করেছো সেটা স্মৃতির কোন কাজে আসবে না, মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া। আর তুমি তোমার ছাত্রদের কোন সত্যের অভিজ্ঞতা দান করছ না, সত্যের মতো কিছু একটা করছ মাত্র; তারা অনেক কিছুই শুনবে কিন্তু কিছুই শিখবে না। মনে হবে তারা অনেক কিছুই জানে, কিন্তু সাধারণত কিছুই জানবে না; তাদের সঙ্গ হবে বিরক্তিকর, জ্ঞানের ভান নিয়ে থাকবে, অথচ তাদের বাস্তবের কোন খবর নাই।
সক্রেটিস, প্লেটোর কথোপকথনে (Phaedrus)
(Plato, 1961, pp. ৪৭৫-৫৩২)

প্রবেশিকা
এটা তো আমরা জানি যে সক্রেটিস জীবনে কিছুই লেখেন নি; চিরকূট, চিঠি, পুঁথি – কিছুই না। বই তো দূরের কথা। তাঁর সম্পর্কে আমরা যা জানি তা প্লেটোর মারফত; শাগরেদদের সঙ্গে ডায়ালগ বা কথোকথনের মধ্য দিয়ে প্লেটো সক্রেটিসকে হাজির করেছেন। কাহিনী আছে সক্রেটিস নামে আদতে কেউ ছিলেন কিনা। প্লেটোই কি দর্শন বা চিন্তার পদ্ধতিকে কথোপকথনের ছক দেবার জন্য এই মহাজ্ঞানীকে বানিয়েছেন? কে এই সাধু? যিনি সব কিছুর উত্তর জানেন, আবার কিছুই জানেন না। যদি জানেন তাহলে তিনি প্রশ্ন কেন করেন? তাঁর জিজ্ঞাসা এমন যেন তিনি কিচ্ছুই জানেন না, তাই জানতে চান। আর যদি না জানেন তাহলে কীভাবে প্রশ্ন করলে জ্ঞানের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে পোঁছানো যায় সেটা তিনি আগাম জানেন, বোঝেন বা আন্দাজ করেন কী করে? আমরা তো জীবনে কোন জিজ্ঞাসা ছাড়া জাহেলিয়ার মধ্যেই খাবি খেয়ে মনুষ্যজীবন সদানন্দে পার করে দিতে পারি। তাই না? দিচ্ছি তো!
তাহলে জিজ্ঞাসা থাকার দরকার কি মানুষের? দ্বিতীয়ত মানবেতিহাসে জিজ্ঞাসা আদৌ কি কোনদিন শেষ হবে? নাকি জিজ্ঞাসা এমনই একটা বৃত্তি যা মানুষের স্বভাব এবং তা সবসময়ই জারি থাকতে বাধ্য। যে কারণে কোনো বিশেষকালে সমাজ যা সত্য বলে মানে সেটা নতুন জিজ্ঞাসার আলোকে আর আগের মতো সত্য মনে হয় না। দেশকালপাত্রভেদে বিশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালপাত্র নির্দিষ্ট উত্তর থাকতে পারে, কিন্তু তারপরও জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসাই থেকে যায়। মানুষের জিজ্ঞাসার কোনো শেষ নাই। তাহলে চূড়ান্ত উত্তর বা চূড়ান্ত সত্য বলেও কিছু নাই। যা আছে তা হোল স্তর থেকে স্তরান্তরে উন্নীত হওয়া। ইমাম গাজ্জালীর সত্তর হাজার পর্দা এক এক করে অতিক্রম করে যাওয়ার মতো (Al_Ghazzali, 1980)। তারপরও সত্য পর্দার আড়ালে থেকে যায়। নিরাকার ও নিরঞ্জন। সত্য নিরন্তর গায়েব। সহজে ধরা দেয় না। দেশকালপাত্রভেদে কেউ কেউ রূপের ছটায় মোহিত হয় বটে, কিম্বা যা গায়েব তা নিরন্তর গরহাজির থাকে। গায়েবে আত্মসমর্পন ছাড়া জীবের আর কোনো গতি নাই। ‘ঈমান’ মানে বিশ্বাস না। নিঃশর্ত আত্মসমর্পন। এর কোনো বাংলা অনুবাদ সম্ভব না।
গাজ্জালিকে সাক্ষ্য মানলে আমাদের জিজ্ঞাসার মাত্রা যতদূর পৌঁছায়, ততটুকই আমরা মানুষ । পরবর্তী পর্দা ভেদ করবার জন্য অন্যদের জন্য মানুষের ইতিহাস অপেক্ষা করতে থাকে। মানুষের সদাই নতুন ডায়ালগ বা কথোপকথনের অপেক্ষা। সক্রেটিসের ডায়ালগ বা কথোপকথন থেকে এটা আমরা বুঝি। সে কারণে সক্রেটিস নামে আদৌ কেউ ছিলেন নাকি ছিলেন না সেটা দর্শনের জগতে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না। সক্রেটিস মানে জীবন্ত মানুষের সহজ স্বাভাবিক দৈনন্দিনের জিজ্ঞাসা লালন, সতত জীবন্ত জিজ্ঞাসাকে সপ্রাণ রাখা এবং মানুষের অন্তর্গত রুহানি আকুতির তাগিদে অপরের সঙ্গে কথোপকথন জারি রেখে জাহেলিয়ার পর্দাগুলো সরিয়ে দেওয়া। জীবন্ত মানুষের মধ্যে জীবন্ত জিজ্ঞাসা জারি রাখা— এতটুকু বুঝলেও আন্দাজ করা যায় সক্রেটিস কেন বই লিখলেন না। বই সপ্রাণ কথোপকথনের পথে কাঁটা হয়ে উঠতে পারে।

হেন সক্রেটিস এবং তার শিষ্য-পরিকরদের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা ‘প্লেটোর ডায়লগ’ নামে পরিচিত। কথোপকথন লিখেছেন প্লেটো। সক্রেটিসের সঙ্গে প্লেটোর কথোপকথন যীশুর জন্মেরও প্রায় ৩৭০ বছর আগে লেখা। সেই সকল কথোপকথন বা ডায়লগের মধ্যে আমরা ফেদ্রুসের (Phaedrus) আড্ডা বা আলাপ আমাদের আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। কারণ, এখানে লিখিত অক্ষর, লেখালিখি বা বই নিয়ে কথাবার্তা আছে। এই কথোপকথনের সূত্রে কতিপয় জিজ্ঞাসাকে সপ্রাণ করে তোলাই এখানে আমাদের চেষ্টা থাকবে।
সক্রেটিস নামে আদৌ কেউ ছিলেন নাকি ছিলেন না সেটা দর্শনের জগতে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না। সক্রেটিস মানে জীবন্ত মানুষের সহজ স্বাভাবিক দৈনন্দিনের জিজ্ঞাসা লালন, সতত জীবন্ত জিজ্ঞাসাকে সপ্রাণ রাখা এবং মানুষের অন্তর্গত রুহানি আকুতির তাগিদে অপরের সঙ্গে কথোপকথন জারি রেখে জাহেলিয়ার পর্দাগুলো সরিয়ে দেওয়া। জীবন্ত মানুষের মধ্যে জীবন্ত জিজ্ঞাসা জারি রাখা— এতটুকু বুঝলেও আন্দাজ করা যায় সক্রেটিস কেন বই লিখলেন না। বই সপ্রাণ কথোপকথনের পথে কাঁটা হয়ে উঠতে পারে।
ফেদ্রুসের সঙ্গে সক্রেটিসের আলাপ বা কথোপকথন দর্শনের মহলে মোটামুটি জমজমাট। এর একটা কারণ, মনে রাখা বা স্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কথোপকথন ও লিখিত অক্ষরের ফারাক এবং দুইয়ের ব্যবধান নিয়ে তর্ক এখানে বেশ স্পষ্ট ভাবে প্লেটো হাজির করেছেন। দ্বিতীয়ত ফারাক নির্দেশ করতে গিয়ে অক্ষরগিরি বা লেখালিখিকে সক্রেটিস টেকনলজিপনা বা কৃৎকৌশলগিরি গণ্য করেছেন। আসলেই, লেখালিখি একধরনের কারিগরি। এর ফলে লেখালিখি নিয়ে কথোপকথনের তাৎপর্য টেকনলজির বিপরীতে দারুন ভারি ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে। হয়ে উঠেছে মানুষের সঙ্গে টেকনলজির সম্পর্ক বিচারের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক তর্ক। সাহিত্যের দিক থেকে তাৎপর্য হল তর্কতা শুরু হয়েছে ভাষা নিয়ে।
কারিগরি হিশাবে লিখিত অক্ষরের সুবিধা ও অসুবিধা এই কথোপকথনে মোটামুটি পরিষ্কার। ফলে নানান দিকে জিজ্ঞাসা এখন ধাবিত হতে পারে। সক্রেটিসের প্রশ্ন তোলার ধরণ এবং কথোপকথনকে তিনি যেদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন তাতে এই ধারনাই দৃঢ় হয় যে তিনি অক্ষর বিদ্বেষী বা লেখালিখির বিরোধী। তাঁর পক্ষপাত মুখস্থ ভাষা এবং কথোপকথনের প্রতি। তবে কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে সক্রেটিস লিপি, লিখন বা অক্ষরগিরির একাট্টা বিরোধিতা করেছেন কথাটা নাকি পুরাপুরি ঠিক না। তাদের দাবি সক্রেটিস টেকনলজির ভালমন্দ বিচার করার প্রতিই জোর দিয়েছেন।
কিন্তু বিষয়টা আসলে অতো সরল নয়। লিখিত ভাষার চেয়ে মুখস্থ ভাষার প্রতি পক্ষপাত সক্রেটিসের প্রধান উদ্দেশ্য কিনা সেটাও তর্ক সাপেক্ষ। লিখিত অক্ষরের বিপরীতে কন্ঠস্বরকে যতটা নয়, সক্রেটিস বরং যত্ন ও রক্ষা করতে চাইছেন সামাজিক মানুষের সারার্থ: জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের কথোপকথন। সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথোপকথনে তৈরি হয় এবং জারি থাকে। অতএব সক্রেটিস মানুষের সমাজ জীবিত রাখতে চাইছেন। কথাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সমাজ জারি থাকার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তাকে জীবিত রাখতে হলে কথোপকথন জারি রাখা চাই। জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের কথোপকথনই আসল গুরুত্বের জায়গা। কন্ঠস্বর বনাম অক্ষরের তর্ক সেই তুলনায় গৌণ। কিন্তু অনেকেই—ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা যেমন— একেই প্রধান তর্কের জায়গা হিশাবে বেছে নিয়েছেন। টেকনলজি বা কারিগরির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের তর্ক একালের অনেক দার্শনিকদের লেখালিখির মধ্যে নতুন ভাবে হাজির আছে। যথা, মার্শাল মাকলুহান, জাক দেরিদা, বারনার্ড স্টিগলার প্রমুখ। মার্টিন হেইডেগার তো আছেনই। তবে মুখস্থ বা কন্ঠের ভাষা (Voice) এবং লিপিগিরি (Writing) নিয়ে জাক দেরিদার কাজ আমাদের অনেক কিছুই নতুন ভাবে ভাবতে বাধ্য করে। সেটা আরও ভাল বোঝা যাবে যদি ফেদ্রুসের সঙ্গে প্লেটোর কথোপকথন আমরা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে পারি।
ফেদ্রুসের সঙ্গে কথোপকথন প্লেটো পেশ করছেন বিশেষ পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার পরিবেশও তর্কের তাৎপর্যকে সুনির্দিষ্ট মহিমা দান করতে সক্ষম হয়। কথোপকথন হচ্ছে সুদর্শন তরুণ ফেদ্রুসের সঙ্গে। ফলে আলোচনার মধ্যে বিষয় হিশাবে প্রেমও এসে গিয়েছে। সমকামিতাও। গ্রিক দর্শনে Philosophy বা দর্শন বলতে বোঝায় জ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রতি প্রেম বা ভালবাসা। এই প্রেম কামসম্পন্ন, এমনকি বুঝি পরকীয়াও— সেই ইঙ্গিতও আমরা পাই। তবে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

সুদর্শন তরুণ ফেদ্রুসের সাথে সক্রেটিস ঘুরছেন। ফেদ্রুসের চাদরের নীচে ‘সোফিস্ট’ লাইসিয়াসের একটি বক্তৃতার খসড়া লুকানো। সেই খসড়ায় লেখা আছে একজন প্রেমিকের কাছে নয় বরং যার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক নাই তার কাছেই আত্মসমর্পণ করা উচিত। কথোপকথনের সময় লিসিয়াসের বক্তৃতা ফেদ্রুস পাঠ করে শোনালেন। সক্রেটিস সেটা মনোযোগ দিয়েই শুনলেন। তারপরে নিজের দুটি বক্তৃতা শোনালেন। কাম, প্রেম, পরকীয়া এবং সমাকামিতার আবহে বক্তৃতা, বাগ্মিতা, অলঙ্কারশাস্ত্র, লেখা, বীজ বপন এবং খেলা নিয়ে জমজমাট কথা চলে। এরই মধ্যে সক্রেটিস লিখন বা লিপির আবিষ্কারক থিউথ সংক্রান্ত মিশরীয় পুরাণ বর্ণনা করেন। যে পরিবেশে কথোপথন এবং পুরাণের গল্প বলা হল সেই পরিপ্রেক্ষিত মনে না রাখলে মুখের ভাষা আর লিখিত ভাষার ফারাক নিয়ে প্লেটোর তোলা গুরুত্বপূর্ণ তর্কের খেই হারিয়ে যায়। কিম্বা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা ও বিপদ ঘটে।
সক্রেটিস লেখালিখি, অক্ষর বা লিপির কারিগরিকে নিন্দা করেছেন, স্তুতি করেছেন মুখস্থ ভাষার, কন্ঠস্বরের। কারণ। তাঁর পক্ষপাত জীবন্ত মানুষের পারস্পরিক কথোপকথনে। কন্ঠস্বর, অর্থাৎ জ্যান্ত মানুষের প্রতি। পাশ্চাত্য দর্শনে এতোকাল ধরে বহাল প্রধান মত হচ্ছে সেই কন্ঠস্বরই আসল। কন্ঠস্বরই ভাষা। লেখালিখি কন্ঠস্বরেরই লিখিত রূপ মাত্র। জাক দেরিদার পুরা দর্শন পাশ্চাত্যের এই অনুমানকে প্রশ্ন তুলে এলোমেলো করে দিয়ে গড়ে উঠেছে। বদ্ধমূল অনুমানটিই নড়বড়ে করে দিতে পেরেছেন। এখানে তাঁর প্রবল কৃতিত্ব।
সক্রেটিস বই লেখেন নি কারণ তিনি লেখালিখির বিরুদ্ধে ছিলেন, তিনি সরাসরি মুখস্থ ভাষা বা কথোপকথনের পক্ষে— এটাই প্রচলিত মত। সক্রেটিসের অভিমতটাই শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে পাশ্চাত্যে প্রবল ভাবে জারি রয়েছে। পাশ্চাত্য আসলে যা প্রবল ও প্রকট ভাবে জারি রেখেছে সেটা হল মুখস্থ ভাষা এবং লিখিত অক্ষরের দ্বন্দ্ব। কথোপকথন ও ছাপাখানার ভেদ। দেরিদার গুরুত্ব হল এই অনুমানগুলোকে দর্শনের জায়গা থেকে নতুন জিজ্ঞাসার বিষয়ে পরিণত করতে পারা।
সক্রেটিস বরং যত্ন ও রক্ষা করতে চাইছেন সামাজিক মানুষের সারার্থ: জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের কথোপকথন। সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথোপকথনে তৈরি হয় এবং জারি থাকে। অতএব সক্রেটিস মানুষের সমাজ জীবিত রাখতে চাইছেন। কথাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সমাজ জারি থাকার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তাকে জীবিত রাখতে হলে কথোপকথন জারি রাখা চাই। জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের কথোপকথনই আসল গুরুত্বের জায়গা। কন্ঠস্বর বনাম অক্ষরের তর্ক সেই তুলনায় গৌণ। কিন্তু অনেকেই—ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা যেমন— একেই প্রধান তর্কের জায়গা হিশাবে বেছে নিয়েছেন। টেকনলজি বা কারিগরির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের তর্ক একালের অনেক দার্শনিকদের লেখালিখির মধ্যে নতুন ভাবে হাজির আছে। যথা, মার্শাল মাকলুহান, জাক দেরিদা, বারনার্ড স্টিগলার প্রমুখ। মার্টিন হেইডেগার তো আছেনই।
‘ফেদ্রুস’ এবং ‘সিম্পসিয়াম’ শিরোনামের কথোপকথন অন্যান্য কারনেও বিখ্যাত। প্রেম সম্পর্কে প্লেটোর মোট ভাবনাচিন্তা কমবেশী এই দুই বাতচিতে মেলে। গ্রিকদের কাছে দর্শন (Philosophy) কোন অর্থে জ্ঞানের (sophia) প্রতি ভালবাসা (phio) তার মানে বোঝার জন্যও এই দুটো কথোপকথন পড়ে রাখা দরকারি। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম বা ভালবাসার সম্বন্ধ এখন আর আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যেহেতু এখন আমরা হৃদয়ের আকুতির চেয়ে বুদ্ধির দাবির প্রতি অধিক অনুগত হতে শিখেছি। বুদ্ধির সর্দারি আমরা এখন যত নির্বিচারে মানি গ্রিক দর্শনে সেই প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকে আমরা বুদ্ধির নির্মাণ বলেই স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেই। ফলে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক বোঝাতে গ্রিকরা যখন ‘ফিলসফি’ কথাটা বলে তখ্ন তাকে যারপরনাই অবোধ্য গ্রিক ভাষাই মনে হয়।
বাংলা ভাষায় ‘ফিলসফি’র অনুবাদ ‘দর্শন’। একসময় ধর্ম আর দর্শনে কোন ভেদ করার দরকার ছিল না। ধৃ থেকে ধর্ম, তাই যা আমরা ধারণ করি তাই ধর্ম। জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা, রসতত্ত্ব, আচার, সংস্কার, সমাজ ব্যবস্থাপনা, শাসন ব্যবস্থা সবই ধর্মের অন্তর্গত বিষয়। দর্শনও ধারণ করবারই বিষয়। তাই ধর্ম মানেও দর্শন। কিম্বা দর্শন মানেও ধর্ম। কিন্তু আধুনিক কালে আমরা যখন পাশ্চাত্যের ‘ফিলসফি’-কে দর্শন অনুবাদ করতে শুরু করলাম তখন তা একই সঙ্গে ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয়ের গজফিতা হয়ে উঠল। যেমন, ধর্ম মানে যা দর্শন নয়, যা আমাদের ধারণ করবার বিষয় হয়ে যেমন রইল না, তেমনি ধর্ম থেকে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, নীতিনৈতিকতা ইত্যাদি আলাদা হয়ে গেল। ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধির ছেদ ঘটে গেল। ধর্ম প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধির কিম্বা বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয়ের বিষয় হয়ে আর রইল না। ধর্ম হয়ে উঠল স্রেফ ‘বিশ্বাস’। সেখানে যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার প্রজ্ঞার কোন বালাই নাই। বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তি, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার বিপরীত জিনিস। ধর্ম স্রেফ আদেশ পালন এবং আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কারের বিষয়ে পরিণত হল। এখন তা আরও অধোগামী হয়ে স্রেফ পরিচয়বাদী সাম্প্রদায়িক পোশাক হয়ে উঠেছে।
তাছাড়া বাংলায় ‘দর্শন’ কথাটা আমরা ব্যবহার করি বটে কিন্তু তার উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত থেকে। এতে ‘দেখা’ বা ‘দৃষ্টি’র প্রতি নজর নিবিষ্ট। এমন যে মনে হয় জ্ঞান বা জ্ঞানের সত্য বুঝি শুধু চেয়ে দেখার জিনিস। প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করবার বিষয়। চোখ দিয়ে দেখানো গেলেই প্রমাণ সিদ্ধ হয়, নইলে না। বুদ্ধি এখানে আধুনিক পাশ্চাত্যের মতো প্রকট ভাবে হাজির নাই, কিন্তু আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় বা বৃত্তির চেয়েও ‘চোখ’ এখানে বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে হাজির: সত্য দ্রষ্টব্য বা দেখে নির্ণয় করবার বিষয় হয়ে ওঠার কারনে সত্যের ধারণাও তাই সৎ বা পরিচ্ছন্ন ভাবে দেখতে পারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। চিন্তাজগতে এই ঘটনাগুলো আমাদের অজান্তে ঘটে গিয়েছে। আমাদের খুব একটা হুঁশ আছে মনে হয় না।
কথোপকথন কোনো আগাম অনুমান কিম্বা ধ্রুব সত্যের দাবি নিয়ে শুরু হয় না। জীবন্ত মানুষ মাত্রই সামাজিক, তার সামাজিকতা সক্রিয় কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। দৈনন্দিনের বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে উঠে আসা জিজ্ঞাসা কেন্দ্র করেই কথোপকথনে আমরা প্রবেশ করি। কখনও তর্কের নিষ্পত্তি হয়, কখনো হয় না। কিন্তু সমাজ যদি মতপার্থক্যের কারণে বিভেদ ও বিভাজন এড়াতে চায়, তাহলে কথোপকথন সদাসর্বদা জীবন্ত রাখা বা চালু রাখা জরুরী। এর মধ্য দিয়েই সমাজ জারি থাকে। সমাজের জন্য কথোপকথনের কোনো বিকল্প নাই।
তাই এখানে আমাদের কৌতুহল মূলত লিখিত ভাষার বিরুদ্ধে সক্রেটিসের আপত্তি অনুসরণ করা। তাঁর উৎকন্ঠা ভালো ভাবে বোঝা এবং তাঁর আপত্তি আমাদের সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক করে তোলা। সক্রেটিস ও ফেদ্রুসের কথোপকথনের মধ্যে কখন কোন্ প্রসঙ্গে বিষয়টি উঠেছে এবং প্রসঙ্গক্রমে সক্রেটিস কেন লিখিত অক্ষরের বিরোধিতা করেছেন সেই দিকটা আমরা জানা ও বোঝার চেষ্টা করব। সক্রেটিস সবসময়ই কথোপকথনে আগ্রহী। জানার প্রতি ভালবাসাকেও আমরা কথোপকথনের আকুতি থেকে আলাদা করতে পারি না। কথোপকথনের আকুতি ছাড়া তাহলে দর্শনও সম্ভব না। আগেই বলেছি, প্রাচীন গ্রিক ধারণা অনুযায়ী দর্শন বলতে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রতি ভালবাসাই বোঝায়। যেখানে কথোপকথন নাই, সেখানে দর্শনও নাই। ফেদ্রুস পড়তে গিয়ে এই দিকটা আমরা মনে রাখব।
কথোপকথন কোনো আগাম অনুমান কিম্বা ধ্রুব সত্যের দাবি নিয়ে শুরু হয় না। জীবন্ত মানুষ মাত্রই সামাজিক, তার সামাজিকতা সক্রিয় কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। দৈনন্দিনের বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে উঠে আসা জিজ্ঞাসা কেন্দ্র করেই কথোপকথনে আমরা প্রবেশ করি। কখনও তর্কের নিষ্পত্তি হয়, কখনো হয় না। কিন্তু সমাজ যদি মতপার্থক্যের কারণে বিভেদ ও বিভাজন এড়াতে চায়, তাহলে কথোপকথন সদাসর্বদা জীবন্ত রাখা বা চালু রাখা জরুরী। এর মধ্য দিয়েই সমাজ জারি থাকে। সমাজের জন্য কথোপকথনের কোনো বিকল্প নাই।
মিশরীয়দের পুরাণ
তরুণ ও সুদর্শন ফেদ্রুসকে নিয়ে সক্রেটিস ধীরে সুস্থে হাঁটছেন। ওর মধ্যে কথোপকথন চলছে।
ফেদ্রুসের জামার তলায় লিসিয়াসের একটি লিখিত বক্তৃতা। লিসিয়াস বক্তা এবং বক্তৃতা লেখেন। ফেদ্রুস এপিক্রেটসের বাড়িতে লিসিয়াসের সঙ্গে সারা সকাল বসে কাটিয়েছেন। তাদের দুইজনেরই বন্ধু একিউমেন ফেদ্রুসকে বাইরে হাঁটতে পরামর্শ দিয়েছে। তাই ফেদ্রুস এখন নগরের প্রাচীরের বাইরে মুক্ত বাতাসে হাঁটতে বেরিয়েছেন। একিউমেনের দাবি শহরের বদ্ধ জায়গার চেয়ে খোলা হাওয়ায় হাঁটা অনেক বেশী শক্তি জোগায়। নগরের বাইরে হাঁটার পক্ষে যুক্তিটা আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও নাগরিকতার সঙ্গে কথোপকথন এবং গ্রিক ‘পলিস’-এর সম্বন্ধের ইঙ্গিত শুরুতেই আমরা পাই। সক্রেটিস একিউমেনের কথায় আপত্তি করেন না। কিন্তু তার আগ্রহ যতটা না নগরের প্রাচীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় বেড়ানো, তার চেয়ে অনেকে বেশী লিসিয়াসের সঙ্গে ফেদ্রুসের কী কথাবার্তা হয়েছে সেইসব শোনা। শুনতে চাইলে ফেদ্রুস তাকে অনুসরণ করতে বলল। সক্রেটিস এক কথায় রাজি। কারন সক্রেটিসের ভাষায়, সব কাজের চেয়ে বড় ‘কাজ’ হচ্ছে কথোপকথন শোনা। কথোপকথনে রাজি থাকা।
তাদের দুইজনেরই খালি পা। তারা এমন একটা জায়গা খুঁজে নিলেন যেখানে ঝর্ণার জলে পা ঝুলিয়ে দুজনে বসতে পারেন।
যেখানে তারা বসলেন সেটা বরিয়াস অরিথিয়ার কাহিনীর স্থান কিনা ফেদ্রুস সক্রেটিসের কাছে জানতে চাইলেন। সেটা আসলে আরো দূরে। বলার পর সক্রেটিস পৌরাণিক কাহিনীটি ফেদ্রুসকে আবার বর্ণনা করলেন। ফেদ্রুস সক্রেটিসের জ্ঞানের তারিফ করলেন। ফেদ্রুস বললেন কোন বিদেশী যদি কোন দেশে বেড়াতে যায় তাহলে স্থানীয় লোকজনকে দিয়ে সেই দেশ জানা বা বোঝা যাবে না। একজন গাইডের দরকার হবে। ফেদ্রুস বললেন, সক্রেটিস নিজেও ‘এক অদ্ভূত মানুষ’, সেই রকম গাইডের মতো। অদ্ভুত, ‘কারন সক্রেটিস প্রায় কখনই নগরের সীমানা’ ছাড়িয়ে বাইরে প্রকৃতিতে ফেদ্রুসের মতো খোলা হাওয়া খেতে যান না। খুব কমই দেয়ালের বাইরে পা বাড়ায়!

কথোপকথনের এই অংশটুকু আমাদের আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে সক্রেটিসের আগ্রহ জীবন্ত মানুষে। তাদের সঙ্গে কথোপকথনে। নগরের সারবত্তা বা ভিত্তি তৈরি হয় নাগরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। যারা একসঙ্গে বাস করতে চায়, একই সমাজে অন্তর্ভূক্ত থাকতে রাজি কথোপকথন তাদের সকলের সামাজিক সত্তা তৈরি করে। আমরা সামাজিক হই কথোপকথনে। পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন জাহেলিয়ার পর্দা সরিয়ে দেয়। তাই কথোপকথনের বিকল্প নাই। তাহলে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য স্রেফ শহরে বা নগরে থাকা নয়। বরং এক সঙ্গে বাস করা যেখানে কথোপকথন সম্ভব এবং জীবন্ত মানুষের সমাজ যেখানে গড়ে উঠতে পারে। কথোপকথন সমাজের ভিত্তি। তাই কথোপকথনের মধ্য দিয়েই গ্রিক অর্থে ‘পলিস’ বা ‘রাজনৈতিক পরিসর’ গড়ে ওঠে।‘পলিস’কে নগররাষ্ট্র বাংলায় অনুবাদ করবার ফলে জীবন্ত মানুষের সঙ্গে কথোপকথন বা সমাজ গড়ে উঠতে দেওয়ার গুরুতর তাৎপর্য আমরা ধরতে পারি না। আমরা মনে করি গ্রিক ‘পলিস’ বা নগর রাষ্ট্রগুলো বলতে গ্রিক দার্শনিকরা যা বুঝিয়েছেন তা বুঝি আমাদের বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রেরই আদি কোনো রূপ। যা মোটেও ঠিক না। ফেদ্রুসের তারিফের উত্তরে সক্রেটিস বলছেন:
“প্রিয় বন্ধু, আমাকে মাফ কর, আমি জ্ঞানের প্রেমিক। গাছপালা আর এই গ্রামীন দৃশ্য আমাকে কিছু শেখাতে পারে না। কিন্তু নাগরিকে পারে। ক্ষুধার্ত জন্তুর সামনে গাজর বা ঘাস ঝুলিয়ে রেখে তাকে তুমি হাঁটাতে পার। ঠিক তেমনি তুমি যদি আমাকে ভলিউমের পর ভলিউম বক্তৃতা শোনাও সারা আফ্রিকা, কিম্বা তোমার ইচ্ছা মতো জায়গায় আমাকে দিয়ে হাঁকিয়ে বেড়াতে পারবে, এ ব্যাপারে সন্দেহ করি না”।
দেখা যাচ্ছে নগরের দেয়ালের বাইরে ফেদ্রুসের সঙ্গে সক্রেটিস হাঁটতে রাজি প্রকৃতির প্রতি প্রেম বশত নয়। কিম্বা খোলা জায়গায় হাওয়া সেবনেও তাঁর আগ্রহ নাই। তাঁর আগ্রহ জীবন্ত কথোপকথনে।
জীবন্ত মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক কথোপকথনের গুরুত্ব এবং প্লেটোর দর্শনে তার তাৎপর্যটুকু পরিষ্কার না বুঝলে সক্রেটিস কেন বই লিখলেন না তার গভীরতা ও ব্যাপ্তির কিছুই আমরা ধরতে পারব না। এর সঙ্গে, আগেই বলেছি, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে গ্রিক ‘পলিস’-এর ধারণা। যাকে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাচীন সংস্করণ গণ্য করে সাধারণত বাংলায় ‘নগর রাষ্ট্র’ অনুবাদ করা হয়। সে কারণে আমরা সহজে ধরতে পারিনা যে ‘পলিস’ মূলত আধুনিক রাষ্ট্রের কোনো আদি রূপ নয়। পলিস হচ্ছে পরিবার ও গার্হস্থ্য জীবন থেকে পৃথক পরিসর। যা আর বিচ্ছিন্ন গৃহ বা আলাদা আলাদা পরিবারের গার্হস্থ্য পরিসর হয়ে থাকে না, বরং সামাজিক পরিসর হয়ে ওঠে বাংলায় একেই আমরা ‘পলিস’ না বলে ‘সমাজ’ বলে থাকি। অনেকের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে হলে যে সামাজিক রীতিনীতি পারস্পরিক কথোপকথন ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নির্ণয় এবং আমরা যা মানি সেই সকল কথোপকনের সারপদার্থের ওপর সমাজ দাঁড়ায় বা গঠিত হতে পারে। সমাজ হচ্ছে কথাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে কথাসম্পন্ন মানুষের জীবন্ত সম্বন্ধ যা পরিবার কিম্বা গার্হস্থ্য পরিসরের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন্মের সম্বন্ধ থেকে আলাদা।
কথোকথনের সম্বন্ধ যার ওপর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসর গড়ে ওঠে। এটাই সমাজ বা সামাজিকতার সারার্থ যা ‘কথামৃত’ বা ‘কথার বাজার’ নামে বড় বাংলার সাধুগুরুসন্তদের কাছে পরিচিত।
মনে রাখতে হবে সক্রেটিসের আগ্রহ জীবন্ত মানুষে। তাদের সঙ্গে কথোপকথনে। নগরের সারবত্তা বা ভিত্তি তৈরি হয় নাগরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। যারা একসঙ্গে বাস করতে চায়, একই সমাজে অন্তর্ভূক্ত থাকতে রাজি কথোপকথন তাদের সকলের সামাজিক সত্তা তৈরি করে। আমরা সামাজিক হই কথোপকথনে। পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন জাহেলিয়ার পর্দা সরিয়ে দেয়। তাই কথোপকথনের বিকল্প নাই। তাহলে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য স্রেফ শহরে বা নগরে থাকা নয়। বরং এক সঙ্গে বাস করা যেখানে কথোপকথন সম্ভব এবং জীবন্ত মানুষের সমাজ যেখানে গড়ে উঠতে পারে। কথোপকথন সমাজের ভিত্তি। তাই কথোপকথনের মধ্য দিয়েই গ্রিক অর্থে ‘পলিস’ বা ‘রাজনৈতিক পরিসর’ গড়ে ওঠে।‘পলিস’কে নগররাষ্ট্র বাংলায় অনুবাদ করবার ফলে জীবন্ত মানুষের সঙ্গে কথোপকথন বা সমাজ গড়ে উঠতে দেওয়ার গুরুতর তাৎপর্য আমরা ধরতে পারি না। আমরা মনে করি গ্রিক ‘পলিস’ বা নগর রাষ্ট্রগুলো বলতে গ্রিক দার্শনিকরা যা বুঝিয়েছেন তা বুঝি আমাদের বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রেরই আদি কোনো রূপ। যা মোটেও ঠিক না।
সক্রেটিস ফেদ্রুসের কাছে লিসিয়াসের বক্তৃতা শুনলেন, নিজেও ফেদ্রুসকে দুইটা বক্তৃতা দিলেন। তাঁরা প্রেম, ভাষার অলংকার, বক্তৃতা, বীজ বপন ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে লিখিত ভাষা বা অক্ষর নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। লেখালিখি বা অক্ষরগিরি ঠিক না বেঠিক সেই প্রশ্ন ফেদ্রুসকে সক্রেটিস বোঝাতে চাইছেন। প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ পরিস্থিতিতে লেখালিখি বা লিপি ঠিক বা বেঠিক হয় সক্রেটিস তা নির্ণয় করতে চান। তর্কে সহজে প্রবেশের জন্য তিনি মিশরের একটি গল্প বলছেন।
নীল নদের একটি শাখার তীরে গড়ে ওঠা মিশরের প্রাচীন শহর ‘নক্রাতিস’-এর গল্প। এটাই গ্রিকদের প্রথম এবং একসময়ের স্থায়ী উপনিবেশ। সক্রেটিস জানাচ্ছেন এই গল্পটা তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছেন।
যখনকার গল্প তখন নক্রাতিসের রাজা থামুস (Thamus)। এটা গ্রিকদের দেওয়া নাম, তারা তাকে মিশরীয় ‘থিবস’ও (Egyptian Thebes) বলত। মিশরের উত্তরে তাঁর রাজ্য; মিশরীয়দের কাছে তিনি রাজা ‘এমন’ (Ammon) নামেও পরিচিত। মিশরে প্রাচীন এক দেবতা হচ্ছেন ‘থিউত’ (Theuth), যার কাছে ‘ইবিস’ (Ibis) পাখি পবিত্র। দেবতা হিসাবে থিউতের খ্যাতি হচ্ছে তিনি সংখ্যা, সংখ্যার হিসাব বা নামতা, জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা আবিষ্কার করেছিলেন। এমনকি ড্রাফট ও পাশা খেলাও দেবতা থিউতের আবিষ্কার। তবে সক্রেটিস বলছেন, থিউতের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে লিখন পদ্ধতি, লিপি বা লেখা আবিষ্কার।

রাজা থামুসের কাছে দেবতা থিউত গিয়ে নিজের কারিগরি প্রদর্শন করে বললেন, এই লেখার কারিগরি মিশরীয়দের কাছে প্রচার ও প্রসার করা দরকার। রাজা যেন তা করেন। রাজা থামুস প্রশ্ন করলেন এসবের কী ব্যবহার আর সুবিধাটাই বা কী? থিউত ব্যাখ্যা করার পর রাজা প্রতিটির ভাল দিক যেমন স্বীকার করলেন, তেমনি খারাপ দিকটাও স্পষ্ট বলতে ছাড়লেন না।
গল্পটি বলার সময় সক্রেটিস ফেদ্রুসকে বলছেন রাজা বিভিন্ন কলাকৌশলের যেভাবে ভাল ও মন্দ উভয় দিক নিয়ে বিস্তর বাছবিচার করেছেন সেই সব পুরাপুরি বর্ণনা করতে বিস্তর সময় লেগে যাবে। তাই রাজা থামুস ও দেবতা থিউতের লিপি, বর্ণায়ন, লেখা বা লিখিত অক্ষর নিয়ে তর্কে সক্রেটিস এলেন। লেখার কারিগরি নিয়ে থিউত রাজাকে বলছিলেন, ‘হে রাজন! পেশ করছি এমন এক শিখন পদ্ধতি যা মিশরের জনগণকে আরও জ্ঞানী করবে এবং স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটবে; আমার আবিষ্কার স্মৃতি এবং জ্ঞানের ওষুধ (pharmakon) ”। রাজা থামুস তখন বললেন:
“হে নানান কারিগরের কারিগর, একজনের কাজ হচ্ছে নানা কাজের কারিগরি আবিষ্কার, আর আরেক জনের কাজ হচ্ছে যারা সেইসব ব্যবহার করবে তাদের ওপর কী মাত্রায় ক্ষতি আর কতোটা লাভ হবে তা খতিয়ে দেখা। লিখনের জন্মদাতা তুমি, ফলে তার প্রতি তোমার স্পর্শকাতর পক্ষপাত থাকার কারণে তুমি লিখিত অক্ষরের আসল পরিণতি কী ঘটবে তার উল্টাটাই বললে। যদি মানুষ লেখালিখি শেখে তাহলে তাদের স্মৃতি শুকিয়ে যাবে, লিখিত অক্ষরে বিশ্বাস অন্যের এঁকে রাখা চিহ্নের ওপর নির্ভর হবার অভ্যাস তৈরি করবে, যে চিহ্নগুলো বাইরের, তাদের নিজেদের অন্তরের গহিনে নয়। তাহলে তারা যা কিছু শেখে তাদের মন থেকে লেখালিখি সেইসব মুছে ফেলার পরিণতি ডেকে আনবে। তোমার আবিষ্কার স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ওষুধ না, শুধু বাইরের টোকা মাত্র। তোমার ছাত্রদের এর দ্বারা কোন জ্ঞানবুদ্ধির চর্চা শেখাচ্ছ না, বরং বাইরে থেকে দিচ্ছ জ্ঞান-জ্ঞান মার্কা একটা জিনিস। তারা বিস্তর পড়বে, কিন্তু কোন শিক্ষাগুরুর সংস্পর্শ ছাড়া তাদের কিছু না শিখিয়ে তাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়ায় মনে হবে তারা বুঝি অনেক কিছু জানে, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা কিচ্ছুটি জানে না, তারা ফেঁপে উঠবে জ্ঞানে নয়, বরং জ্ঞানের অহংকারে। তাদের সঙ্গ তখন দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠবে”।
(Plato, 1961, p. ৫২০), (Waterfield, 2002)
এরপর সক্রেটিস লেখালিখিকে ছবি আঁকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলছেন,
এটা অদ্ভুত যে লেখালেখি আসলে ছবি আঁকার সঙ্গেই মেলে। শিল্পীর কাজ আমাদের সামনে এমন ভাবে দাঁড়ায় যে মনে হয় তারা জীবন্ত। কিন্তু যদি তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় তারা একপ্রকার রাজকীয় নীরবতা অবলম্বন করে। লিখিত অক্ষরেরও একই দশা। মনে হয় তারা বুঝি বুদ্ধিমান, কথা বলছে তোমার সঙ্গে। কিন্তু যদি তারা কি চায় নির্দেশের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা কর, তারা একই কথা চিরকাল বারবার বলতে থাকবে।
সক্রেটিসের দাবি হচ্ছে লেখালিখি, অক্ষর বা বই কথোপকথন কিম্বা চিন্তার আদান প্রদানের ভাল মাধ্যম না। কারন জীবন্ত মানুষের সহজ দৈহিক বৃত্তির বাইরে চিহ্ন হিশাবে স্মৃতিকে শরীরের বাইরে এঁকে রাখলে সেটা স্মৃতিকে রক্ষা কিম্বা সবল করে না। সক্রেটিস তাই অক্ষর, লেখালিখি, বই বা গ্রন্থের বিরোধী। আরও আলোচনায় প্রবেশের আগে এই কথোপকথনের মর্ম আমরা নিজেরা যেভাবে বুঝেছি সেভাবে আগে সাজিয়ে নেব।
১. টেকনলজি আবিষ্কার আর সমাজে টেকনলজি ব্যবহারের লাভ ও ক্ষতির মাত্রা বিচার সম্পূর্ণ দুটো আলাদা বিষয়। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিচার বা মূল্যায়ন সবসময়ই অতীব জরুরী। টেকনলজি স্রেফ ব্যক্তির ব্যবহারের মামলা না, সমাজ ও সমাজের বিকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
২. লেখালিখি ছবি টাঙিয়ে রাখার মতো, যা লিখে রাখা হয় তার বাইরে কোন জিজ্ঞাসা করতে জানে না, কোনো নতুন জিজ্ঞাসা তৈরি করতেও পারে না, নতুন কোন জিজ্ঞাসার উত্তরও দিতে পারে না।
৩. স্মৃতি জীবন্ত সমাজে জীবন্ত মানুষের জীবন্ত চর্চার বিষয়। জীবন্ত মানুষের জীবন্ত সম্পর্ক চর্চার বাইরে চিহ্ন, অক্ষর, লেখালিখি, বই, গ্রন্থ, মানুষের স্মৃতি শুকিয়ে ফেলবে। হৃদয় মরে যাবে। দুর্বল ও ক্ষয়ে যাওয়া স্মৃতি দিয়ে কোন শক্তিশালী প্রাজ্ঞ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা যাবে না। কথোপকথনের বাইরে লেখালিখি হচ্ছে স্মৃতির বিষ; জীবন্ত মানুষ নিজেদের আত্মা বা হৃদয়ের অন্তর্গত স্মৃতি চর্চা বাদ দিয়ে যদি বাইরের চিহ্ন বা লিখিত অক্ষরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, তাহলে স্মৃতির ক্ষয় হয়। স্মৃতির ক্ষয় মানে আত্মার ক্ষয়। হৃদয় হারিয়ে ফেলা। আত্মা বা হৃদয়ের চর্চা একই সঙ্গে নিজেকে জানা। যাকে আমরা ‘নিজ’ বা ‘আমি’ বলি সে সমাজ কিম্বা ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ না। কথোপকথন ও স্মৃতির চর্চা একই সঙ্গে নিজেদের জানা এবং সামাজিকতার বিকাশ ঘটানো। ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজ এবং সমাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির বিকাশ ঘটে।
৪. মানুষ ও মানুষের সমাজ গ্রন্থের, শাস্ত্রের, বইওয়ালাদের অধীনস্থ হয়ে পড়বে, মানুষের বৃত্তির বিকাশ ঘটবে না। গ্রন্থ হয়ে উঠবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসক। ধর্মগ্রন্থ, লিখিত শাস্ত্র, আইন, রাষ্ট্র মানুষের ওপর খোদ শাসক হয়ে উঠবে। অর্থাৎ যুগপৎ মানুষ ও সমাজ গ্রন্থ বা অক্ষরের দাসে পরিণত হবে। মানুষ টেকনলজির নাটবল্টুতে পরিণত হবে। টেকনলজি নির্ভর সমাজ মানুষকে মেশিনের দাসে পরিণত করে। খেয়াল করতে হবে, এটা টেকনলজি বিরোধী অবস্থান নয়, টেকনলজিকে সামাজিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অধীনস্থ রাখবার তর্ক।
৫. অক্ষর বা লেখালিখি অন্যের লিখে রাখা বাইরের অক্ষর বা চিহ্নে বিশ্বাস স্থাপন করা, অপরের লিখে রাখা চিহ্নের ওপর নির্ভর হবার অভ্যাস তৈরি করবে। মানুষ নিজের উপলব্ধি, বুদ্ধি, বিচার বা প্রজ্ঞার স্বাধীন বা মুক্ত অন্বেষণকে আর বিশ্বাস করবে না। নিজের অজ্ঞানতা বা জাহেলিয়াত কাটিয়ে ওঠার কঠিন প্রচেষ্টা চালাবে না। লোকপরম্পরায় গড়ে ওঠা সামাজিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চর্চা ক্ষুণ্ণ ও রুদ্ধ হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের জীবন্ত কথোপকথনের অভাব সমাজকে দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে নিয়ে যাবে, সমাজের জীবন্ত সারার্থের ক্ষয় ঘটলে সমাজ টিকবে না।
৬. যে চিহ্ন শুধু বাইরের, কিন্তু অন্তরের গভীর চিহ্ন বা আয়াত না সেই প্রজ্ঞার হদিস মানুষ আর পাবে না। নিজেদের বিচার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। নির্ভরশীল হয়ে উঠবে পণ্ডিত, এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞদের ওপর। এটা শুধু সেকুলার জীবন সম্পর্কে সত্য না। একইভাবে মানুষ এখন ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ বা পরকালের বিষয়ে এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পুরোহিত, পাদ্রি বা আলেম সমাজ আমাদের পরকালীন প্রভু হয়ে বসেছেন। এর বিপরীতে নিজেকে জানা, নিজেকে বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সরাসরি ও জীবন্ত সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য বাইরের চিহ্নের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে ‘দিল-কোরআন’ আবিষ্কারের কথা ওঠে। বাইরের চিহ্ন পরিহার করে মানুষের আপন হৃদয়ের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনার কথা ওঠে। জাত-পাতের বিরুদ্ধে প্রেমের, ভক্তির আন্দোলন গড়ে ওঠে, যেন জাতপাত চুরমার করে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেমের সম্বন্ধ রচনা করা যায়, ইত্যাদি।
৭. লেখালিখি বা বই জ্ঞানবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার চর্চা শেখায় না বরং বাইরে থেকে জ্ঞান-জ্ঞান মার্কা ভাব দেখায়। বইয়ে বন্দী হয় যারা তারা বিস্তর পড়বে, কিন্তু কোন জীবন্ত শিক্ষাগুরুর সংস্পর্শ ছাড়া তাদের বস্তা বস্তা পড়াশুনা বইয়ের বোঝা বয়ে বেড়াবার মুটেগিরি হবে। মনে হবে তারা বুঝি অনেক কিছু জানে, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা হবে ফাঁপা। তারা ফেঁপে উঠবে জ্ঞানে নয়, বরং জ্ঞানের অহংকারে। তাদের সঙ্গ তখন দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠবে।
ফেদ্রুসের সঙ্গে কথোপকথনের যে কয়েকটি স্থান চিন্তার উর্বর ক্ষেত্র স্পর্শ করেছে তার একটি হচ্ছে এরকম যে, “তোমার আবিষ্কার স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিরওষুধ না, শুধু বাইরের টোকা মারা মাত্র”। সরল ভাবে বলা যায় টেকনলজি সমাধান না, বরং ‘ওষুধ’। এখন এই ওষুধকে গ্রিক ভাষা অনুযায়ী আমরা কি শুধু বিষ জ্ঞান করব, নাকি তার কিছু নিরাময়ের গুণও আছে দর্শনে সেটা এখন এক বিশাল তর্কের বিষয়। প্লেটো লেখালিখিকে স্মৃতির বিকল্প জ্ঞান করছেন না – এই দিকটা গোড়াতেই বোঝা জরুরি। স্মৃতি আর স্মৃতিক্ষয়ের ‘ওষুধ’ সমার্থক না। আমরা ভুলে যাব না যে প্লেটো কথোপকথন – অর্থাৎ জ্যান্ত মানুষের আন্তরিক সম্পর্ক চর্চার আলোকে এই কথাগুলো বলছেন। ওষুধ আমরা খাই যখন শরীর তার সপ্রাণ স্বভাব অনুযায়ী চলতে অক্ষম। গ্রিক ভাষা অনুযায়ী ‘ওষুধ’ হচ্ছে phármakon, (φάρμακον) কিন্তু এই শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আছে। তাই তার সঠিক অনুবাদও কঠিন। ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রেও নানা রকম দেখা যায়। কোথাও আছে, What you have discovered is a recipe not for memory but for reminder (Plato, 1961, পৃষ্ঠা ৫২০)। আবার কোথাও Your invention is a potion for jogging the memory, not for remembering (Waterfield, 2002, পৃষ্ঠা ৬৯)। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়েও তর্ক আছে। গ্রিক ‘ফার্মাকন’ শব্দটির একসঙ্গে কিম্বা ক্ষেত্র বিশেষ নানান মানে হতে পারে। যেমন ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও সংস্কার, ওষুধ, বিষ, তাবিজ, রঙ, প্রসাধনী, আতর, মদ। ইত্যাদি। তাহলে ‘ফার্মাকন’ বলতে আমরা কি বুঝব? ‘ফার্মাকন’ ধারনার কোন নিশ্চিত সারার্থ নাই। অনুপস্থিত। The essence of the pharmakon is its very lack of a stable essence. (Rinella, 2010)। সাম্প্রতিক দার্শনিক তর্কাতর্কির বেশ বড় একটা ধারা জাক দেরিদার বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘প্লেটোর ফার্মেসি’ কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। দেরিদার দাবি হচ্ছে অক্ষর বা লেখালিখিও ফার্মাকন। অর্থাৎ বিষ, ওষুধ নাকি অমৃত কিছুই সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তাঁর অবিনির্মাণ পদ্ধতি অনুযায়ী (Deconstruction) অনির্ণেয় (Undecidable)। প্লেটো কিন্তু ভিন্ন কথা বলেছেন। অক্ষর বা লেখালিখিকে প্লেটো একদম ‘বিষ’-ই গণ্য করেছেন। কারন লিখিত কাগজপত্র অন্যদের সঙ্গে কথোপকথনে কোন সামর্থ্য জোগায় না। বরং স্মৃতির ক্ষয় ঘটিয়ে কথোপকথনেরও ক্ষয় ঘটায়। স্মৃতি বা নিজের হৃদয় বা চিত্তবৃত্তির শক্তি চর্চা না করে বাইরের চিহ্নের ওপর অতি নির্ভরশীলতার কারণে আমাদের স্মরণশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়, চেষ্টা করেও আমরা অনেক কিছু আর মনে করতে পারি না।
যেহেতু বিষয়টি গুরুতর, তাই থামুসের বরাতে সক্রেটিস যা বললেন তা আমরা যথাযথ বুঝেছি কিনা সেটা আরও বিস্তৃত ভেবে দেখা দরকার।
মানুষ এখন ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ বা পরকালের বিষয়ে এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পুরোহিত, পাদ্রি বা আলেম সমাজ আমাদের পরকালীন প্রভু হয়ে বসেছেন। এর বিপরীতে নিজেকে জানা, নিজেকে বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সরাসরি ও জীবন্ত সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য বাইরের চিহ্নের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে ‘দিল-কোরআন’ আবিষ্কারের কথা ওঠে। বাইরের চিহ্ন পরিহার করে মানুষের আপন হৃদয়ের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনার কথা ওঠে। জাত-পাতের বিরুদ্ধে প্রেমের, ভক্তির আন্দোলন গড়ে ওঠে, যেন জাতপাত চুরমার করে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেমের সম্বন্ধ রচনা করা যায়…
টেকনলজি বনাম প্রজাপালন বা শাসন
থামুস রাজা, তাঁর কাজ প্রজাদের সার্বিক মঙ্গলের দিকে খেয়াল রাখা। তাই কোন কিছু তিনি যাচাই ও পর্যালোচনা ছাড়া গ্রহণ করতে রাজী নন। টেকনলজি মানেই ভাল এটা তিনি মানছেন না।
সক্রেটিসের বলা এই গল্প থেকে আমরা বুঝি, রাজা আর বিজ্ঞানী এক না। তেমনই রাজা আবিষ্কারক কিম্বা টেকনলজি বিশারদ নন। আবার টেকনলজি বিশারদ রাজা নন। রাজা থামুসকে আমরা আমাদের সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক করতে চাইলে ‘রাজা’ কথাটা রাজতন্ত্রের রূপ বা মর্ম দিয়ে নয়, বুঝতে হবে শাসনের দায়ের দিক থেকে। রাজা থামুসের কথা থেকেই বোঝা যায়, ‘রাজা’ কথাটার অর্থ যার কাজ প্রজাদের সার্বিক মঙ্গল। তাই তিনি বিজ্ঞানের আবিষ্কার কিম্বা টেকনলজির চোখ ধাঁধানো উপকার প্রচারে মুগ্ধ হয়ে পড়ছেন না। বিজ্ঞান ও টেকনলজির ক্ষতিকর দিক নিয়েও তিনি ভাবছেন। তাদের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে প্রজাদের রক্ষা করার কর্তব্যও তাঁর, তাই সেই ক্ষতিকর দিক নিয়েও তিনি ভাববেন। এটাই শাসন, এটাই শাসকের কাজ। ‘শাসন’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বর্গ। শাসন আর ক্ষমতা সমার্থক নয়। আধুনিক রাষ্ট্র একই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতার একচেটিয়া রাষ্ট্রের। কিন্তু ক্ষমতাচর্চা মানেই শাসন নয়।
গণতন্ত্রে শাসক মানে নির্বাচিত শাসক, রাজা না। অন্তত কাগজে কলমে ক্ষমতা জনগণের। রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষমতাকে ন্যায্য করবার জন্য নির্বাচন আধুনিক রাষ্ট্রের আচার। যদি শাসনকে ক্ষমতার বর্গ থেকে আলাদা করি তাহলে গণতন্ত্রে শাসকের অর্থ দাঁড়ায় রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা। সেই দিক থেকে শাসন অবশ্যই এমন হতে হবে যেন নির্বিচারে টেকনলজিকে বাহাবা দেওয়া না হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও টেকনলজিরও শাসন দরকার। বিজ্ঞান ও টেকনলজির উপকারের কথা বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়াররা বলবেন, অসুবিধা নাই। নিজেদের পক্ষে প্রপাগাণ্ডা তারা করবেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও টেকনলজির উপকার পেতে হলে বিজ্ঞান ও টেকনলজির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগনকে রক্ষা করা প্রাথমিক দায়। বিজ্ঞানী বা টেকনলজির আবিষ্কারক বিজ্ঞান বা টেকনলজি নিয়ে গর্ব করতেই পারে, হাজার অহংকারী প্রপাগান্ডা হতেই পারে, কিন্তু জনগণের সামষ্টিক স্বার্থ দেখা যদি শাসনের কর্তব্য হয় তাহলে বিজ্ঞান ও টেকনলজি মানেই ভাল এই প্রকার নির্বিচার গোঁয়ার্তুমি বা কুসংস্কার থেকে অবশ্যই মুক্ত হওয়া জরুরী। এ কালে টেকনলজির রমরমা চলছে। সকলের কল্যাণ যার কর্তব্য তাঁকে টেকনো-প্রাপাগাণ্ডায় বিশ্বাসী হলে চলে না। রাজা বলি, রাষ্ট্র বলি, সমাজের পরিচালক বা শাসক বলি, সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা যাঁর কর্তব্য তাঁর কাজ বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃৎকলা বা টেকনলজির সার্বিক বিচার করা, যেন শুধু ভাল দিক নয়, তাদের খারাপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও হুঁশিয়ার থাকা যায়। জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করবার এটাই পথ। বিজ্ঞান ও টেকনলজি অবশ্যই কঠোর পর্যালোচনার বিষয়।

এখন রাজতন্ত্রের কাল আর নাই। আমরা রাজার দ্বারা শাসিত নই। শাসিত হই রাজনীতিবিদদের দ্বারা। তাহলে রাজনীতির ধারনাকেও বদলানো জরুরী। রাজনীতিরও খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায় হচ্ছে বিজ্ঞান ও টেকনলজির পর্যালোচনা। নানান প্রকার কারিগরির ভালমন্দ বিচার। বলাবাহুল্য রাজনীতি বলতে নির্বাচন কিম্বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার কার্যকলাপ বোঝায়। আধুনিক রাজনীতিতে দেশ শাসন বা রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণার মধ্যে বিজ্ঞান বা টেকনলজি পর্যালোচনা একদমই নাই।
টেকনলজির পর্যালোচনাকে থামুস কেন রাজনীতি বা শাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত মনে করেন? যুক্তি হিশাবে থামুস বলছেন নানান কারিগরির আবিষ্কারক আর সেই কারিগরি যারা ব্যবহার করবে তারা আলাদা। এই গোড়ার পার্থক্য বুঝে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ফারাক কখনই ভুলে গেলে চলবে না। তাই যারা ব্যবহারকারী তাদের ওপর টেকনলজির খারাপ প্রভাব কি পড়বে সেটা অবশ্যই পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। বিজ্ঞানী বা কারিগরের কাজ গবেষণা ও আবিষ্কার, কিন্তু বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী সামগ্রিক প্রভাব সমাজের ওপর কিভাবে পড়ে, পড়তে পারে বা পড়বে সেটা বিচার করার ভার বিজ্ঞানী বা কারিগরদের নয়। সেই কাজ সমাজের বিকাশ ও কল্যাণের জন্য যারা কাজ করেন তাদের। সমাজ পরিচলনার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত এই কর্তব্য তাঁদের ওপরই বর্তায়। সারকথা হচ্ছে বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও টেকনলজি মানেই ভাল এই অনুমান থেকে মুক্ত হওয়া দরকার; বিজ্ঞান ও টেকনলজির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা খুবই জরুরী।
বিজ্ঞান ও টেকনলজির উপকার পেতে হলে বিজ্ঞান ও টেকনলজির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগনকে রক্ষা করা প্রাথমিক দায়। বিজ্ঞানী বা টেকনলজির আবিষ্কারক বিজ্ঞান বা টেকনলজি নিয়ে গর্ব করতেই পারে, হাজার অহংকারী প্রপাগান্ডা হতেই পারে, কিন্তু জনগণের সামষ্টিক স্বার্থ দেখা যদি শাসনের কর্তব্য হয় তাহলে বিজ্ঞান ও টেকনলজি মানেই ভাল এই প্রকার নির্বিচার গোঁয়ার্তুমি বা কুসংস্কার থেকে অবশ্যই মুক্ত হওয়া জরুরী। এ কালে টেকনলজির রমরমা চলছে। সকলের কল্যাণ যার কর্তব্য তাঁকে টেকনো-প্রাপাগাণ্ডায় বিশ্বাসী হলে চলে না। রাজা বলি, রাষ্ট্র বলি, সমাজের পরিচালক বা শাসক বলি, সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা যাঁর কর্তব্য তাঁর কাজ বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃৎকলা বা টেকনলজির সার্বিক বিচার করা, যেন শুধু ভাল দিক নয়, তাদের খারাপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও হুঁশিয়ার থাকা যায়। জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করবার এটাই পথ। বিজ্ঞান ও টেকনলজি অবশ্যই কঠোর পর্যালোচনার বিষয়।
টেকনলজি বনাম বৃত্তি বা হৃদয়ের ব্যাকরণ
ফেদ্রুসের সঙ্গে সক্রেটিসের কথোপকথন বিশেষ ভাবে যে দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য করে সেটা হচ্ছে মানুষের শরীর ও সহজাত বৃত্তির ওপর টেকনলজি বা কৃৎকৌশলের আমূল প্রভাব। এই প্রসঙ্গেই সক্রেটিস স্মৃতির প্রশ্ন তুলেছিলেন।
সক্রেটিসের বিশাল আপত্তি হচ্ছে স্মৃতির ক্ষতি বা অবক্ষয় নিয়ে। লেখালিখি স্মৃতি শুকিয়ে ফেলার বিপদ তৈরি করে, এটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি। মানুষ যদি অক্ষর লিখতে শেখে তাহলে মনের গুরুতর রূপান্তর কতোটা ঘটতে পারে সে সম্পর্কে আমরা পুরাপুরি অনুমান করতে পারি না। মনের গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি হচ্ছে স্মৃতি ধারণ ও স্মৃতি চর্চা। এই স্মৃতি কোথায় আমরা ধারণ করি? সেটা করি সক্রেটিসের ভাষায় মনে বা হৃদয়ে। একে এক কিন্তু মানুষ যদি কোনো কিছু মনে রাখার চেষ্টা না করে লিখে রাখবার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাদের স্বভাব আভোলা-অমনোযোগী হয়ে পড়বে, তাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি না পেয়ে লোপ পাবে। তারা স্মৃতির কাছে ধর্ণা দিতে ভুলে যাবে। নিজের গহিন বৃত্তির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। নির্ভরশীলতা বাড়বে বাইরের চিহ্নের ওপর। অক্ষরের আঁকিবুকির ওপর মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, বাইরের চিহ্নব্যবস্থা তার হৃদয়ের ব্যাকরণ বিন্যস্ত করবে, হৃদয় বাহিরকে নয়। করবে। হয়তো অক্ষর, লিখিত ভাষা কিম্বা ছাপাখানা আমাদের স্মৃতির কাঠামো বা সহজাত স্বভাবকেও আমূল বদলে দিতে পারে। আমরা আর আগের মানুষ থাকব না।
কিন্তু স্মৃতি কী? অন্তর বা হৃদয়ের স্বাভাবিক ও সহজ বৃত্তি, যা আমরা জন্মসূত্রে পেয়ে থাকি। স্মৃতিচর্চা মানে কী? অন্তর বা হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক ও সহজ বৃত্তির বিকাশ ঘটানোর চর্চা।। মন বা হৃদয়কে শক্তিশালী করা যাতে মানুষ ‘মানুষ’ হিশাবে যা দেখেছে ও আত্মস্থ করেছে তা যেন আর ভুলে না যায়। কি ভুলে না যাওয়া? মানুষের নিজের উৎপত্তি। সক্রেটিস স্মৃতিকে শুধ্য ব্যক্তির স্মৃতি অর্থাৎ দেশকালে সীমাবদ্ধ আত্মার স্মৃতির কথা বলছেন কিনা সেই তর্ক থেকে যায়।
সক্রেটিস স্মৃতির সংজ্ঞা দিচ্ছেন ভুলে যাবার বিপরীতে। একে নিছকই আধুনিক কালের সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির স্মৃতি না ভেবে মনুষ্য প্রজাতির ভুলে যাওয়া অর্থেও ব্যাখ্যা করা যায়। স্মৃতি মানে ভুলে না যাওয়া। স্মৃতি তাহলে স্রেফ গল্প, ইতিহাস বা জাদুঘর না। আমরা তাই হয়ে উঠি যা আমরা স্মৃতিতে ধারণ করি, স্মৃতিতে ধরে রাখি। স্মৃতি হয়ে উঠতে আমাদের গোপনে বা প্রকাশ্যে প্রণোদিত করে। স্মৃতির মধ্য দিয়ে বা স্মৃতি ধারণ করেই মানুষ ‘বর্তমান’ থাকে। তাই থামুসের দাবি, স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ তাদের অন্তরের গভীর বা গহিন থেকে কোন কিছু আর স্মরণ করবে না, নির্ভর করবে বাইরের আঁকাবুকির ওপর।
তাই যদি হয় তাহলে আমাদের স্মৃতি সম্পর্কে আধুনিক কালের পাঠের হদিসও নিতে হবে। যেমন, ফ্রয়েড। আর ফ্রয়েড ধরলে জাক লাকঁও আসবেন। থামুসের সূত্র ধরে সক্রেটিস বোঝালেন অক্ষর স্মৃতি নষ্ট করে। কিন্তু একালে ফ্রয়েড বোঝালেন, অক্ষর না, বা মুদ্রিত বইয়ের কোনো দোষ নাই। আমরা নিজেরাই নিজেদের অবচেতনে স্মৃতিকে দমন করি। দোষ অক্ষরের না। দোষ আমাদের। ফ্রয়েড আমাদের স্মৃতি আর অক্ষরের দ্বন্দ্ব বা বিরোধের আদি তর্ক ভুলিয়ে দিলেন। টেকনলজিকে আসামি না করে ফ্রয়েড মানুষকে আসামি করলেন। তিনি মানুষের মধ্যে অবচেতনা আবিষ্কার করলেন। আমাদের জন্য নতুন জিজ্ঞাসা তৈরি হয়ে রইল যে অক্ষর আর অবচেতনার মধ্যে সম্পর্ক কী আসলে? কী তাদের সম্বন্ধ। কী রিশতা ছাপাখানা আর অবচেতনার মধ্যে?
কথোকথন বা আড্ডাবাজি জীবন্ত। জীবন্ত মানুষের জীবন্ত চর্চা। সেটা বন্ধুদের মধ্যে হোক কিম্বা হোক, শিক্ষক/ছাত্র, গুরু/শিষ্য ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে। সক্রেটিসের কাছে দর্শনের বিষয়ও তাহলে জীবন্ত মানুষ, মৃত অক্ষর নয়। তাই তিনি কথোপকথন ভালবাসতেন, পড়া না। কথা আমাদের ভেতর থেকে ঘটে, নইলে কথোপকথন হয় না, কিন্তু অক্ষর বা বই আমাদের ভেতরে প্রবেশের জন্য আমাদের বাইরে অপেক্ষায় থাকে। যদি ‘নিজেকে জানা’ দর্শনের উদ্দেশ্য হয়, তো বই সেই ক্ষেত্রে সহায়ক না একদমই। বরং উলটা বই নিজেকে জানান দিতে চায়। বই পড়লে বইকে জানা যায়, কিন্তু নিজেকে জানা যায় কিনা সন্দেহ। নিজেকে জানার পথ হচ্ছে অন্যের কাছে বা অপরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করা, কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে জানা। অপর হচ্ছে আয়নার মতো, অন্যের মধ্যে নিজেকে দেখা। চেনা ও জানার উত্তম পথ হচ্ছে কথা– কথোপকথন। ডায়ালগ। আড্ডা।
জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের সম্পর্ক আর মৃত বইয়ের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের সম্পর্ক এক নয়। একদমই আলাদা। কৃৎকৌশল হিসাবে ছাপাখানার বই দর্শন বা ভাবচর্চার মধ্যস্থতাকারী হিসাবে হাজির হওয়ায় আমাদের চিন্তার স্বভাব ও ধরণে আমূল বদল ঘটেছে। শ্রুতি ও কন্ঠস্বরের জগত ক্রমে গৌণ হয়ে গিয়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেছে ছাপাখানার জগত। এই পরিবর্তন কি প্রচলিত দর্শন বা ভাবচর্চার পদ্ধতি দিয়ে বোঝা সম্ভব? নাকি দর্শন বা ভাবচর্চাকে অবশ্যই নৃতত্ত্ব বা টেকনলজির সমাজতত্ত্বে মনোনিবেশ করা ছাড়া এখন আর উপায় নাই? উপায় থাকে না। তাহলে কৃৎকৌশলের বিচার ছাড়া টেকনলজি-নিরপেক্ষ দর্শন বা ভাবচর্চার বিচার কি নিছকই আহাম্মকি? দর্শন বা ভাবচর্চার দিক থেকে সম্পর্কের এই আমূল বদলের তাৎপর্য এবং সম্ভাব্য পরিণতি কী?
আমরা এখন ছাপাখানার জগতে নাই, বাস করি ডিজিটাল জগতে। নতুন ডিজিটাল টেকনোলজি আমাদের দেহ, মন ও চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে যে রূপান্তর ঘটাচ্ছে তাকে আমলে না নেওয়া ছাড়া উপায় নাই। ‘দেহ’,’মন’, ‘চিন্তা’ ইত্যাদি ধারণারও নতুন মানে তৈরি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন বা ভাবচর্চার দিক থেকে নতুন টেকনলজিকে ‘আমলে নেওয়া’ কথাটার কী মানে হতে পারে? ‘সত্য’ প্রকাশ এবং ‘সত্য’ চর্চা সংক্রান্ত আমাদের প্রথাগত অনুমানও পর্যালোচনা দরকার, কিন্তু তার পদ্ধতি কী হবে?
বৈষ্ণব রসতত্ত্বের শক্তিশালি দার্শনিক বয়ান থাকা সত্ত্বেও ফকির লালন শাহ দাবি করেছিলেন দাস্য ভাবই সর্বোচ্চ ভাব।

কথোকথন বা আড্ডাবাজি জীবন্ত। জীবন্ত মানুষের জীবন্ত চর্চা। সেটা বন্ধুদের মধ্যে হোক কিম্বা হোক, শিক্ষক/ছাত্র, গুরু/শিষ্য ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে। সক্রেটিসের কাছে দর্শনের বিষয়ও তাহলে জীবন্ত মানুষ, মৃত অক্ষর নয়। তাই তিনি কথোপকথন ভালবাসতেন, পড়া না। কথা আমাদের ভেতর থেকে ঘটে, নইলে কথোপকথন হয় না, কিন্তু অক্ষর বা বই আমাদের ভেতরে প্রবেশের জন্য আমাদের বাইরে অপেক্ষায় থাকে। যদি ‘নিজেকে জানা’ দর্শনের উদ্দেশ্য হয়, তো বই সেই ক্ষেত্রে সহায়ক না একদমই। বরং উলটা বই নিজেকে জানান দিতে চায়। বই পড়লে বইকে জানা যায়, কিন্তু নিজেকে জানা যায় কিনা সন্দেহ। নিজেকে জানার পথ হচ্ছে অন্যের কাছে বা অপরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করা, কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে জানা।
সহায়ক বনাম উপায় বা মাধ্যম
জ্ঞানচর্চা কিম্বা জ্ঞান প্রকাশের মাধ্যম হিশাবে লেখালিখি ভাল উপায় বা মাধ্যম না। সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে জীবন্ত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথন। প্লেটো ‘ডায়ালগ’ বা কথোপকথনকে সেই জন্য সর্বোচ্চ মান্যতা দিয়ে গিয়েছেন। ধর্মগ্রন্থ, বেদ, শাস্ত্র, ছাপাখানা এবং অজস্র কেতাবাদির কাল পার হয়ে এসে ডিজিটাল যুগে সক্রেটিসের এই দাবি আমাদের বেশ স্তম্ভিত করে। সন্দেহ নাই। তর্ক হতে পারে, কিতাব ছাড়া জ্ঞানের চর্চা কীভাবে সম্ভব? এর একটা উত্তর হচ্ছে যদি বই পড়েই কাজ হত তাহলে স্কুল, কলেজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে জীবন্ত মাস্টারের কোন দরকার পড়ত না। বই পড়েই মানুষ জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী হয়ে যেত। এযাবতকাল মানবেতিহাস বই জ্ঞানচর্চার উপায় কিম্বা মাধ্যম হিশাবে ব্যবহৃত হয় নি। হয়েছে হাতিয়ার হিশাবে, ইংরেজিতে যা ‘এইড’ বা সহায়ক বলে গণ্য।
সক্রেটিস বই বা টেকনলজির কোন ইতিবাচক ভূমিকা থাকতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন তোলেন নি, বা তোলার দরকার মনে করেন নি। বই কিম্বা কেতাবোত্তর টেকনলজি নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যাথা ছিল মনে হয় না। তার জিজ্ঞাসার গোড়ায় ছিল আমাদের স্মৃতি, কিম্বা মানুষের হৃদয়। যেখানে আমাদের যার যার ‘আমি’ বাস করেন। ফকির লালন শাহের ভাষায় ‘বারামখানা’। যেখানে ‘সাঁই’ স্বয়ং বাস করেন। শুধু জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কেবল সেই গহিন হৃদয়ের খবর আমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিতে পারি। লিখালিখির প্রতি সক্রেটিসের আপত্তির বড় জায়গাটা এখানে। লিখিত চিহ্ন আর স্মৃতির দ্বন্দ্ব মোকাবিলার তাগিদ তাঁর মধ্যে তীব্র এবং স্পষ্ট। কিছুটা আমরা ধরতে পারি।
লেখালিখি কেন জ্ঞান প্রকাশের কিম্বা জ্ঞানচর্চার ভাল উপায় বা মাধ্যম না? কেন কথোপকথন সর্বোত্তম? তার কারণ অক্ষর হচ্ছে জ্ঞানের ছবি বা চিত্রকলা — খোদ জ্ঞান বা জ্ঞানচর্চা না। তাই অক্ষরকে জ্ঞান না, স্রেফ চিহ্ন জ্ঞান করে আমাদের জ্ঞানের গহিনে প্রবেশের চেষ্টা করতে হয়। যেমন কারো ফটোগ্রাফের ছবি সেই মানুষটি না। সেই মানুষটি সম্পর্কে কিছু জানবার ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফ কাজ দেয় না। আমি কলকাতা শহর ও লোকজনের লক্ষ ছবি দেখলেও ঢাকায় বসে কলকাতাকে কখনই জানতে পারব না। একটা অস্পষ্ট বা আবছা ধারণা হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা কলকাতা শহরকে জানি বলা যায় না। কলকাতার লক্ষ ছবি দেখলেও কলকাতাকে জানা যাবে না। কলকাতায় বাস করতে হবে এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে হৃদয় খুলে কথাবার্তা তর্কাতর্কি করতে হবে। হাজার বই কিম্বা কলকাতা নিয়ে লক্ষ লক্ষ কেতাব পড়েও আমরা কলকাতাকে জানব না। কিম্বা জেনেছি দাবি করা যাবে না। ব্যাপারটা সক্রেটিসের কাছে প্রায় এরকমই। ছবি দেখে ছবির বিষয়ে জ্ঞান হয় না।
কিন্তু কেউ যদি একবার কলকাতা গিয়ে থাকে এবং কলকাতার মানুষজনের সঙ্গে জীবন্ত সঙ্গ যাপন করবার অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে কলকাতার ছবি তার মনে পুরানা স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। লেখালিখির এই ভূমিকা সক্রেটিস অস্বীকার করছেন না। কিন্তু যদি স্মৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে ছবি কোন কাজে আসে না। টেকনলজি হিশাবে লেখালিখি বা বই সেই ক্ষতিটাই করে। স্মৃতি নষ্ট করে। তার কুফল জ্ঞানচর্চার ওপরও বর্তায়।

তাই লেখালিখি বা ছাপা বই কিম্বা রক্ত মাংসের মানুষের সঙ্গে কথোপকথন ছাড়া লিখিত অক্ষর শাস্ত্র কেতাব ইত্যাদি জ্ঞানপ্রকাশ কিম্বা জ্ঞান চর্চার ভাল মাধ্যম না। সক্রেটিস নিজেও তাই কোন কেতাব লেখেন নি। জ্ঞানচর্চার খাঁটি মাধ্যম হছে কথোপকথন। জ্ঞানের প্রতি ভালবাসার বলে পরস্পরের তর্কাতর্কি আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে পরস্পরের হৃদয়ের গহিন থেকে যা আমরা সকলের জন্য জড়ো করি। বই কিম্বা জ্ঞানচর্চার যে কোন উপায় বা টেকনলজি সেই ক্ষেত্রে কী ধরণের ভূমিকা পালন করে সেটা টেকনলজির চরিত্র দ্বারা বিচার্য।
ধরা যাক একটি বাচ্চা একা একা বইপড়ার ডিজিটাল হাতিয়ার কিন্ডল নিয়ে বড় হচ্ছে। এই ডিজিটাল পাঠ-কৌশল যন্ত্রে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস সহ দুনিয়ার সকল গ্রন্থ ঠাসা। সামাজিক সম্পর্ক, মানুষের পারস্পরিক কথোপকথন এবং তর্কাতর্কির মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান তৈরি ও জড়ো হয়, একা একা কিন্ডল হাতে কোন নিঃসঙ্গ বালকের পক্ষে কি সেই জানাজানি সম্ভব? সে কিছুই জানবে না তা নয়। তর্কটা সেখানে নয়। তর্ক হচ্ছে সক্রেটিস ‘জ্ঞান’ বলতে আমাদের কি বোঝাতে চাইছেন। জ্ঞানের সঙ্গে স্মৃতি ও কথোপকথনের সম্বন্ধ কোথায় সেই দিকটা বুঝতে পারাই আসল কথা। যদি বুঝি তাহলে ‘জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা’ কি বুঝতাম? তাহলে গ্রিকরা ‘ফিলসফি’ বলতে কি বুঝত সেটা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম? এটা তো ঠিক হাজার শতাব্দী ধরে আমরা লিখিত পুঁথি ও ছাপাখানার বইপত্রকে জ্ঞানের হাতিয়ার হিশাবে ব্যবহার করেছি। জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানচর্চার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হিশাবে মাথা উঁচু করে আছে হাতিয়ার। তাহলে জ্ঞানের প্রতি আশেকানি ঘটবে কিভাবে? মাঝখানে হাতিয়ার সমাসীন।
অক্ষর হচ্ছে জ্ঞানের ছবি বা চিত্রকলা — খোদ জ্ঞান বা জ্ঞানচর্চা না। তাই অক্ষরকে জ্ঞান না, স্রেফ চিহ্ন জ্ঞান করে আমাদের জ্ঞানের গহিনে প্রবেশের চেষ্টা করতে হয়। যেমন কারো ফটোগ্রাফের ছবি সেই মানুষটি না। সেই মানুষটি সম্পর্কে কিছু জানবার ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফ কাজ দেয় না। আমি কলকাতা শহর ও লোকজনের লক্ষ ছবি দেখলেও ঢাকায় বসে কলকাতাকে কখনই জানতে পারব না। একটা অস্পষ্ট বা আবছা ধারণা হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা কলকাতা শহরকে জানি বলা যায় না। কলকাতার লক্ষ ছবি দেখলেও কলকাতাকে জানা যাবে না। কলকাতায় বাস করতে হবে এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে হৃদয় খুলে কথাবার্তা তর্কাতর্কি করতে হবে। হাজার বই কিম্বা কলকাতা নিয়ে লক্ষ লক্ষ কেতাব পড়েও আমরা কলকাতাকে জানব না। কিম্বা জেনেছি দাবি করা যাবে না। ব্যাপারটা সক্রেটিসের কাছে প্রায় এরকমই। ছবি দেখে ছবির বিষয়ে জ্ঞান হয় না।
জীবন্ত মানুষ ভজনা বনাম বই পূজা
ডায়লগ বা কথোপকথন চিন্তা চর্চার খুবই আদি একটা রূপ, আর সেটা সাক্ষর বা অক্ষরকেন্দ্রিক জগতের কারবার না। সে জগত ‘নিরক্ষর’। অক্ষরহীন ভাবচর্চার অন্তর্গত। সক্রেটিসের মৌখিক বা মুখস্থচর্চাকে লিপিবদ্ধ করে প্লেটো ‘ডায়ালগ’কে সাহিত্যের বিশেষ প্রকার বানিয়েছেন। যা আমরা পড়ি: যথা, ‘প্লেটোর ডায়লগ। লিখিত কিম্বা মুদ্রিত। আর এখন পড়ি এলসিডি স্ক্রিনে। কিন্তু সক্রেটিসকে নিয়ে প্লেটোর যে দার্শনিক ডায়ালগ সেটা আমরা পড়ি বইয়ে ছাপা ‘সংলাপ’ হিসাবে। একটা স্ববিরোধী অবস্থা আমাদের মোকাবিলা করতে হয়। কিন্তু এটা যে স্ববিরোধী সেটা বোঝাটাও গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো সক্রেটিস প্লেটোর তৈয়ারি একটি দার্শনিক চরিত্র। আমাদের আলোচনার জন্য সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সক্রেটিসের বরাতে আমরা যা পড়ছি সেটাই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। ছাপা অক্ষর পড়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি ছাপা অক্ষর জ্ঞানচর্চার জন্য উত্তম মাধ্যম না।
কথোপকথন আদতে জীবন্ত মানুষদের কথাবার্তা, বইয়ের ছাপা অক্ষরে পাঠ না। বলা যায় আড্ডাবাজি। সময়যাপনের বিশেষ ধরণ যেখানে দুই বা ততোধিক মানুষের মধ্যে কথাবার্তা তর্কাতর্কি সত্য উপলব্ধি জ্ঞানের সম্ভাবনা বা জ্ঞান জড়ো করার সম্ভাবনা তৈয়ার করা যায়। লিখিত বা ছাপা বই জীবন্ত কথোপকথন নয়, মৃত অক্ষর থেকে পাঠক নিজের প্রস্তুতি, যোগ্যতা ও অভ্যাস অনুযায়ী অর্থ তৈয়ার করেছেন। যিনি লিখেছেন সেটাই তাঁর মনের কথা বা সঠিক অর্থ কিনা সেটা সবসময়ই বিতর্কিত থেকে যায়। দুইয়ের আকাশপাতাল পার্থক্য। আড্ডার কথোপকথন থেকেই ডায়ালেকটিকস বা দ্বান্দ্বিক চিন্তা পদ্ধতির জন্ম হয়েছে বলে দাবি আছে। তবে এটা আমরা সহজে বুঝতে পারি যে জীবন্ত কথোপকথনকে সরলরৈখিক মৃতবাক্যের মধ্যে সঞ্চারণ অসম্ভবই বটে। দুই বা ততোধিক মানুষের সঙ্গে জীবন্ত চিন্তা চর্চা, তার মধ্য দিয়ে সত্য উপলব্ধি আর বিপরীত ছাপা বইয়ে লিখিত বাক্য থেকে লেখকের প্রস্তাব পড়া এবং পর পর নাকচ ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জ্ঞান, সত্য বা পরম প্রজ্ঞায় পৌঁছাতে পারার দাবির মধ্যে ফারাক আছে। মার্কস তাই ক্রিটিক বা ‘পর্যালোচনা’র কথা বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে প্রতিভাবান পর্যালোচনাও জীবন্ত মানুষের কথোপকথনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই ক্ষেত্রে নদীয়ার ফকিরদের ‘মানুষ ভজনা’র গুরুত্ব আমাদের সামনে চলে আসে।
সক্রেটিস জীবিত থেকে শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা লিপিবদ্ধ হয়েছে দেখলে নির্ঘাত গোস্বা করতেন। অনুমোদন করতেন না। আপত্তি করতেন। সজ্ঞান, সজীব ও জীবন্ত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক চর্চাকে জীবন্ত স্মৃতিতে ধারণ না করে মৃত কাগজে এঁকে রাখাটা তাঁর কাছে ছিল একদমই অগ্রহণযোগ্য একটা কাজ। কাগজের লেখালিখির মধ্যে কথোকথন হয় না, ডায়লগ চলে না, আড্ডাবাজি জমে না। ছাপার অক্ষর শব্দ করে না, কথা বলে না, প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয় না বা দিতে পারে না। এমনকি লেখার অর্থও বাতলাতে পারে না। যিনি লিখিত আঁকিবুকির অর্থ উদ্ধার করেন – অর্থাৎ পাঠক – অথচ সেই পাঠকের ধারণা তিনি যাকে পাঠ করছেন তিনিই বুঝি লেখার অর্থও তাঁকে বলে দিচ্ছেন। আসলে কিন্তু মৃত অক্ষর থেকে অর্থ করছেন জীবিত পাঠক স্বয়ং। বই না।
বইয়ের প্রতি সন্দেহ তো আজকের নয়। এই সন্দেহ নিয়ে দর্শনে মেলা তর্কবিতর্ক আছে। দার্শনিক তর্ক বলে ভাববার কোনো কারণ নাই যে এর কোন ব্যবহারিক দায় নাই। যাঁরা শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন তাঁরা জানেন অল্প বয়সে বই পাঠের ওপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বাচ্চাদের চিন্তা-প্রতিবন্ধী করে তোলে। বাচ্চাদের স্বাধীণভাবে জগত আবিষ্কার না শিখিয়ে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে ক্রিমিনাল কাজ আর কিছুই হতে পারে না। বইয়ে লিখিত ফুল গাছের বর্ণনা পাঠের চেয়ে বাচ্চাদের দরকার ফুল গাছ দেখা, ফুলগাছের পাতা স্পর্শ করা, ফুলের গন্ধ নেওয়া, ফুল আর মৌমাছির সম্বন্ধ সরাসরি নিজ চোখে দেখা, ইত্যাদি। চোখে দেখার মধ্য দিয়েই শিশু ফুলগাছকে আবিষ্কার করে। বই পড়ে না। ফুলগাছ দেখা আর ফুলগাছ সম্পর্কে পড়া এক কথা নয়। তাই ভেবে দেখা দরকার যে বয়সে বাচ্চাদের জগত আবিষ্কার করার কথা বই সেই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে।
কিন্তু এটা বই পড়া না পড়ার তর্ক নয়। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানুষের বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা জড়ো করবার প্রক্রিয়ার বিষয়; সক্রেটিসের কথা মতো মানুষের স্মৃতি, গহিন বৃত্তি কিম্বা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের ব্যাকরণ মেলানো। অর্থাৎ জীবন্ত মানুষের স্মৃতির ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধ রচনার কর্তব্য ভুলে গিয়ে জ্ঞানচর্চাকে বই পড়ায় পর্যবসিত করলে বিপদ। তাই বাচ্চাদের বই পড়তে চাপ সৃষ্টি করা, বইয়ের মধ্যে বন্দী রাখা, পিঠে বইয়ের বস্তা বহন করে প্রতিদিন বাচ্চাদের ইস্কুলে যেতে বাধ্য করা ইত্যাদি শিশুর স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফুর্ত বিকাশকে নষ্ট করে। এই কাজ গর্হিত অপরাধ। বাচ্চাদের আদর স্নেহের কথা আমরা বলি বটে, কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশের ক্ষেত্রে আমরাই সবচেয়ে বড়ো ঘাতক হয়ে উঠি। কিন্তু নিত্য শিশুদের কীভাবে খুন করা হয় সেটা আমরা কমই বুঝি। আধুনিক শিক্ষার চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে দর্শনের যদি কিছু বলার থাকে তো সক্রেটিসের মতো বই বিরোধীদের তরফে অনেক কিছুই বলার আছে।
মানব শিশু ভারী বিস্ময়কর জিনিস। শিশুকাল এমন এক বয়েস – যখন স্নায়ুযন্ত্র পাকা হয় নি। অন্য জন্তুদের বাচ্চা যখন পয়দা হয় তখন তারা পরিণত প্রাণী হিসাবে ধরাধামে আসে। কিন্তু মানুষের ছা এতোই হীনবল ও অপরিণত যে তাকে কম পক্ষে তিন বছর মায়ের সঙ্গে গা ঘেঁষে না থাকলে তার স্নায়ুযন্ত্র পুরাপুরি পাকা হয় না। গর্ভের বাইরে লম্বা সময় ধরে স্নায়ু, বৃত্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। নানান ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে যদি জগতকে নিজের মতো করে আবিষ্কার করতে মানুষের বাচ্চা শিশু বয়স থেকে শিখতে ব্যর্থ হয়, তবে তার পরিণতি ভাল হয় না। স্মৃতি এমন এক প্রতিভা যার বিস্তার সারা শরীরে। ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে তার সুনির্দিষ্ট যোগ বিস্তর তর্কের বিষয়। এর বসত ঠিক কোথায় সেটা চিহ্নিত করাও অসম্ভব। তাহলে সক্রেটিস যখন স্মৃতি নিয়ে উৎকন্ঠা ব্যক্ত করেন তিনি আসলে মানুষের ছানাপোনাদের শারিরীক বিকাশ নিয়েই আসলে কথা বলেন। একালে এই প্রশ্নটাই আরও বিস্তৃত অর্থে শরীরের সঙ্গে টেকনলজির সম্পর্ক বিচারের তর্কে রূপ নিয়েছে।

আধুনিকতার ওজন বইতে গিয়ে আমরা গ্রিকদের বোঝা টানি। বেগার খাটি অনেক। গ্রিকদের ছাড়া কি স্মৃতি, টেকনলজি ইত্যাদি আলোচনা করা যায় না? হয়তো যায়। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতায় গ্রিক প্রভাব বলতে সক্রেটিসই সম্ভবত সবচেয়ে গৌণ, এবং প্রান্তিক। এই অর্থে লিই, লিখন, অক্ষর বা বই ক্ষতিকর এভাবে কেউ আর বলেন নি। তাই সক্রেটিসের কোন বই নাই কথাতার তাৎপর্য গভীর।
গ্রিকদের ‘জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা’ কিভাবে গ্রিকো-খ্রিস্টিয় জগতে শুধু ‘নিশ্চয় জ্ঞান’ বা জ্ঞানের নিশ্চয়তায় রূপ নিল সেটা দীর্ঘ ইতিহাস। এই ছেদবিন্দু না বুঝলে প্রজ্ঞা নয় বরং তথাকথিত ‘নিশ্চয় জ্ঞান’ কিম্বা বিজ্ঞানই কেন পাশ্চাত্য সভ্যতার আরাধ্য হয়ে উঠল আমরা বুঝব না। এখান থেকে প্রজ্ঞা নয় – তথাকথিত নিশ্চিত সত্য সম্পর্কে আধুনিক গোঁড়ামির সূত্রপাত ঘটেছে। কী করে সেটা ঘটল সেই ইতিহাস আমরা ভাল করে বুঝবো না। সেটা না বুঝলে নিশ্চয় জ্ঞান সম্পর্কে গোঁড়ামি আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে। এখানে তা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই।
জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা মানুষের স্বভাব কিনা সেটা তর্ক সাপেক্ষ, কিন্তু জ্ঞানের নিশ্চয়তার জন্য জিদ একটা যুগের লক্ষণ যার কারনে বিজ্ঞান ও টেকনলজির দাসত্ব মানুষ আধুনিক কালে স্বেচ্ছায় মানে। এই এক জাহেলি যুগ যেখানে শুধু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জগত ও যুক্তিসর্বস্বতার মধ্যে মানুষ নিজেকে নিজে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়। অথচ যে জগতে মানুষ সহজ, স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত সেই কল্পনা, সংকল্প ও ভাবুকতার দুনিয়া বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের তুলনায় আধুনিক মানুষের কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছে।
মানব শিশু ভারী বিস্ময়কর জিনিস। শিশুকাল এমন এক বয়েস – যখন স্নায়ুযন্ত্র পাকা হয় নি। অন্য জন্তুদের বাচ্চা যখন পয়দা হয় তখন তারা পরিণত প্রাণী হিসাবে ধরাধামে আসে। কিন্তু মানুষের ছা এতোই হীনবল ও অপরিণত যে তাকে কম পক্ষে তিন বছর মায়ের সঙ্গে গা ঘেঁষে না থাকলে তার স্নায়ুযন্ত্র পুরাপুরি পাকা হয় না। গর্ভের বাইরে লম্বা সময় ধরে স্নায়ু, বৃত্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। নানান ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে যদি জগতকে নিজের মতো করে আবিষ্কার করতে মানুষের বাচ্চা শিশু বয়স থেকে শিখতে ব্যর্থ হয়, তবে তার পরিণতি ভাল হয় না। স্মৃতি এমন এক প্রতিভা যার বিস্তার সারা শরীরে। ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে তার সুনির্দিষ্ট যোগ বিস্তর তর্কের বিষয়। এর বসত ঠিক কোথায় সেটা চিহ্নিত করাও অসম্ভব। তাহলে সক্রেটিস যখন স্মৃতি নিয়ে উৎকন্ঠা ব্যক্ত করেন তিনি আসলে মানুষের ছানাপোনাদের শারিরীক বিকাশ নিয়েই আসলে কথা বলেন। একালে এই প্রশ্নটাই আরও বিস্তৃত অর্থে শরীরের সঙ্গে টেকনলজির সম্পর্ক বিচারের তর্কে রূপ নিয়েছে।
অক্ষর ও নদীয়ার ভাবান্দোলন
সেকি অন্য তত্ত্ব মানে
মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
– ফকির লালন শাহ
সক্রেটিসের সূত্রে নদীয়ার ভাবচর্চা সম্পর্কে কিছু নোক্তা দিয়ে রাখতে চাইছি, যাতে এ বিষয়ে তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র আমরা করতে পারি।
ঐতিহাসিক দিক থেকে নদীয়ার ভাবচর্চার সঙ্গে সক্রেটিসের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু দুটো কাজ দুইদিক থেকে হওয়া দরকার যেন সহজে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য যুগপৎ আমরা ধরতে পারি। একটি কাজ হচ্ছে নদীয়ার ভাবচর্চার জায়গা থেকে সক্রেটিসের পর্যালোচনা। তাকে কতটা প্রাসঙ্গিক ও আন্তরিক করে তোলা যায় তার সীমা ও সম্ভাবনা বিচার করে দেখা। অপরদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা ও পর্যালোচনার নজর দিয়ে নদীয়াকে আরও গভীরভাবে বোঝার জায়গাগুলো শনাক্ত করতে পারা, যেন উভয়দিক থেকে কথোপকথনের রাস্তা প্রশস্ত হয়। সেই কর্তব্যের দিক থেকে সক্রেটিসের লিখিত অক্ষর কিম্বা বইয়ের বিরোধিতা গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র ধরা গেলে মানুষের নতুন সম্ভাবনার বীজগুলো শনাক্ত করা সহজ হয়।
নদীয়ার ভাবচর্চায় কোনো বই নাই। অক্ষরের কোন সর্বগ্রাসী ভূমিকা নাই। কিন্তু ভূমিকা আছে ভাবের। ভাব দেওয়ার এবং নেওয়ার। ‘ভাব দিয়ে ভাব নিলে পরে তবেই রাঙা চরণ পায়’। রক্তমাংসের মানুষের মধ্যেই ভাবের দেওয়া নেওয়া ভাবের বাজার বসা ঘটে।
বই, গ্রন্থ বা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে নদীয়ার অবস্থান গ্রহণের কারণ হচ্ছে সত্যকে কোন নির্দিষ্ট চিহ্নব্যবস্থায় চিহ্নিত করার বিপদ থেকে রক্তমাংসের মানুষকে মুক্ত রাখা। যেন মানুষ তার নিজের বাইরে কোন নৈর্ব্যক্তিক, চিরায়ত ও শ্বাশ্বত সত্যের ফাঁদে ধরা দিয়ে নিজেকে বন্দী করে না ফেলে, দেশকালপাত্রে আবদ্ধ না করে। পরমার্থিক সত্য সবসময়ই চিহ্নের অতীত এবং রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় নিজেকে নিজে প্রকাশ করে চলেছে। তাই ভাব দিয়ে ভাব দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে রক্ত-মাংসের মানুষের ‘সংক্ষেপে স্বরূপে রূপ দেখা’ বা নিজের মধ্যে সত্যের আস্বাদন নদীয়ার সাধনার কেন্দ্রীয় দিক। রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় জ্ঞান বা প্রজ্ঞা হয়ে যে সত্য বিকশিত হয়ে চলে।

নিমাই ছিলেন পণ্ডিত। তাঁর আমলে ন্যায় শাস্ত্রের শীর্ষে তাঁর অবস্থান। কিন্তু তিনি কোনো গ্রন্থে নিজেকে ধরা দিলেন না। উলটা গ্রন্থাদি পুঁথিপথ বিসর্জন দিয়ে তিন খোল কাঁধে ‘নাম সংকীর্তনে বেরিয়ে গেলেন। যা বাহ্য – বা বাইরের তার বিপরীতে যা অন্তরের সেই ব্যাকরণের দিকে মুখ ফেরালেন। রামানন্দের সঙ্গে ‘কথোপকথনে’ তার হৃদয় বৃত্তি বা হৃদয়ের ব্যাকরণ আমরা মোটামুটি ধরতে পারি। তিনি কথোপকথনের সময় দফায় দফায় বললেন, ‘এহ বাহ্য, আগে কহ আর’। বললেন, ভগবানকে আচার-অনুষ্ঠান, পূজা, প্রকরণের মধ্য দিয়ে পাবার ধৈর্য তাঁর নাই। সেই সাধ্যের কথা জানতে চাইলেন যার দ্বারা ঈশ্বরকে তিনি তৎক্ষণাত আস্বাদন করতে পারেন।
তাই নিমাই ফকির লালন শাহের কাছে নদীয়ার প্রথম ‘ফকির’। তিনি ব্রাহ্মণের আসন থেকে সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে এসেছিলেন। কিন্তু নদীয়া ছেড়ে যাবার পর আবার তাঁকে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ হিশাবেই পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা করা হোল। নদীয়ার ফকিররা নিমাইকে উচ্চকোটির অবতারে পরিণত করা এবং ব্রাহ্মণদের কেতাব-গ্রন্থাদির দ্বারা শাস্ত্র সম্মত ‘অবতার’ রূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস মেনে নেয় নি। চৈতন্য নদীয়ায় আর ফিরলেন না। যিনি তাঁর ভাবের বিকাশে নেতৃত্ব দিলেন তিনি নিত্যানন্দ। তাই ‘দয়াল নিতাই কারো ছেড়ে যাবে না’ – এই আর্তি নদীয়ার ফকিরদের কণ্ঠে আমরা শুনি। যে আর্তির মধ্যে চৈতন্যের বিরুদ্ধে অভিমানও রয়েছে।
বই, গ্রন্থ বা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে নদীয়ার অবস্থান গ্রহণের কারণ হচ্ছে সত্যকে কোন নির্দিষ্ট চিহ্নব্যবস্থায় চিহ্নিত করার বিপদ থেকে রক্তমাংসের মানুষকে মুক্ত রাখা। যেন মানুষ তার নিজের বাইরে কোন নৈর্ব্যক্তিক, চিরায়ত ও শ্বাশ্বত সত্যের ফাঁদে ধরা দিয়ে নিজেকে বন্দী করে না ফেলে, দেশকালপাত্রে আবদ্ধ না করে। পরমার্থিক সত্য সবসময়ই চিহ্নের অতীত এবং রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় নিজেকে নিজে প্রকাশ করে চলেছে। তাই ভাব দিয়ে ভাব দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে রক্ত-মাংসের মানুষের ‘সংক্ষেপে স্বরূপে রূপ দেখা’ বা নিজের মধ্যে সত্যের আস্বাদন নদীয়ার সাধনার কেন্দ্রীয় দিক। রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় জ্ঞান বা প্রজ্ঞা হয়ে যে সত্য বিকশিত হয়ে চলে।
ভাবের দিক থেকে বলি। চৈতন্যের পর ব্রাহ্মণকুল আবার শাস্ত্র, টীকাভাষ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু নদীয়া অক্ষর বিরোধী গ্রন্থ বিরোধী শাস্ত্র বিরোধী রয়ে গেল। নদীয়ার ফকিররা এই অবস্থানই বহাল রাখল। সেই লড়াই আজ অবধি চলছে। গ্রন্থ বা শাস্ত্র নৈর্ব্যক্তিক ও চিরায়ত সত্য দাবি করে। ছাপাখানার বই বারবার ছাপা যায়। বারবার ছাপা যায় বলে মনে হয় গ্রন্থ বুঝি চিরায়ত সত্য ধারণ করে। তখন মানুষ নয় – বই, গ্রন্থ ও শাস্ত্রই প্রভু হয়ে বসে। মানুষ তার দেশকাল্পাত্র নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার স্তর পার হয়ে আর সামনে আর অগ্রসর হতে পারে না। একেকেটা শাস্ত্র বা গ্রন্থের মধ্যে মানুষের ইতিহাস আটকে পড়ে যায়। মানুষকে জ্জ্যান্ত রাখতে হলে বই বিরোধী বা শাস্ত্র বিরোধী হওয়া খুবই আবশ্যক।
শাস্ত্র যে পরমার্থিক সত্যের কথা বলে তিনি সর্বত্রই আছেন। সব জায়গাতেই তিনি বিরাজ করেন। খাল, বিল, পুকুর সমুদ্র সর্বত্রই ‘জল’ আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে জল এসে মেশে তা বেদ শাস্ত্র, গ্রন্থ কিম্বা সকল প্রকার চিহ্নব্যবস্থা অতিক্রম করে যায়। তাকে কোন চিহ্নব্যবস্থা দিয়ে আর গ্রেফতার করা যায় না।
নদীয়া তাই জীবন্ত মানুষের ভজনা করে। কোনো মৃত মানুষকে নয়। সে কারণে ‘লালনপন্থা’ বলে কোনো পন্থা আছে, নদীয়া তা স্বীকার করে না। নদীয়ায জ্যান্ত গুরু আছেন। যিনি বর্তমান। গুরু থুয়ে নদীয়া গৌর ভজনা করতেও রাজি না। নদীয়ায় গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ খুবই শক্তিশালী চিন্তার ওপর দাঁড়ানো। যাকে প্রথাগত গুরু-শিষ্যের ধারণা দিয়ে বোঝা যায় না। মানুষ সত্য নয়, সত্য হচ্ছে গ্রন্থ বা শাস্ত্র– নদীয়া তা মানতে রাজি না। সত্য সবসময়ই রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং রপায়িত হয়ে চলেছে। বই বা শাস্ত্রের অর্থও একমাত্র জীবন্ত মানুষই করতে পারে। কিন্তু মানুষ দোহাই দেয় শাস্ত্রের। শাস্ত্রের বিপরীতে জীবন্ত মানুষকে সদাসর্বদাই তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।
নদীয়া অক্ষর বিরোধী কেন? ‘অক্ষর’ এই ধারণা দেয় যে সত্য বুঝি জীবন্ত মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং ভাব-পরম্পরার বাইরে স্বাধীন ও নৈর্ব্যক্তিক সত্য হয়ে উঠতে পারে। নদীয়া তাই শুধু জীবন্ত ও বর্তমান মানুষ মান্য করে, মানুষের বাইরে কোন চিহ্ন বা বস্তুর পূজা করে না।
কিন্তু মানুষ অনিত্য। তাহলে নিত্য বা পরম কেবল তিনি যিনি গুরুশিষ্য পরম্পরায় স্মৃতি ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে আসছেন। নদীয়া জ্ঞান বা ভাবচর্চা বলতে ‘সহজ মানুষ’ ভজনা বোঝে। মানুষের সঙ্গে মানুষের জীবন্ত সম্পর্ক চর্চা বোঝে। যার সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। মানুষই বর্তমান ও জীবন্ত, তাই মানুষ ভজনাই নদীয়ার আরাধ্য। নদীয়ার সাধনার ক্ষেত্র স্বর ও স্মৃতি। সাধনার উপায় বা মাধ্যম হচ্ছে জীবন্ত মানুষের গান ও গুরুশিষ্য পরম্পরায় স্মৃতি চর্চা।
নদীয়ায় তাই দর্শন সংক্রান্ত লিখিত পুঁথি বা ‘বই’ নাই বললেই চলে। কিন্তু গানে গানে শক্তিশালী মুখস্থ বা জীবন্ত ভাবচর্চা বা জ্ঞান চর্চার ধারা আছে। ‘সাধুসঙ্গ’ আছে। ‘ভাবান্দোলন’ বইতে যার কিছু ইঙ্গিত ও প্রমাণ আমি পেশ করবার চেষ্টা করেছি। নদীয়া বই লেখায় আগ্রহী না। কিন্তু তাই বলে সত্যের অন্বেষণ ও উপলব্ধির চর্চা অর্থাৎ জ্যান্ত থেকে পরমার্থিকতার স্বাদ অন্বেষণের ধারা শক্তিশালী।
লেখালিখি জীবিতরাই করে, মৃতরা না
আসলে লেখালিখি জীবিতরাই করে, মৃতরা না। কিন্তু ছাপাখানার বই মূলত অজীব বা মৃত। এর সঙ্গে লেখক জীবিত আছে কি নাই তার কোন সম্পর্ক নাই। লেখক জীবিত হোক বা মৃত, বইয়ের লেখক বইয়ের মধ্য দিয়ে জীবিতদের মধ্যে ‘ভূত’ হয়ে আছর করে, বাসও করে। জীবন্ত পাঠকের মধ্যে লেখক ভূত হয়ে যখন আছর করে। তখন পাঠকই আসলে ভূত হয়। ‘ভূত’ – পাঠক নিজেই। জীবিত পাঠক যেভাবে মৃত কিম্বা অনুপস্থিত লেখকের লেখা পাঠ করে সেই পঠনপাঠনের মধ্য দিয়েই মৃত লেখকই ভূত হয়ে জীবিতের ওপর আশ্রয় বা আছর করে।
আসলে সারকথা হচ্ছে আমরা যখন বই পড়ি আমরা ভুলে যাই যে বইয়ের অর্থ বই নিজে করে না। কারন অর্থোৎপাদনের ক্ষমতা বইয়ের নাই। মৃত ও মুদ্রিত অক্ষর, কালাম বা চিহ্নিত ব্যবস্থাকে যেভাবে জীবিতরা পাঠ করে সেইভাবাই জীবিতরা তার অর্থ করে। তাই বইয়ের অর্থ দেশ কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন হয়। বই নিয়ে তর্কবিতর্ক, হানাহানি ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। ‘মতাদর্শ’ নামে আমরা সত্যের যে চিরায়ত ও শ্বাশ্বত রূপ খাড়া করি তার জন্য আমরা জীবন দিয়ে দিতে বা শহিদ হয়ে যেতে কুন্ঠিত হই না। অক্ষর বা বই তাহলে ভয়ংকর বিষয়।
আমরা কার্ল মার্কস পড়ে বলি মার্কস অমুক বলেছেন, কিম্বা তমুক বলেছেন। আসলে জীবিত মানুষ হিশাবে আমরা মার্কসকে যেভাবে বুঝি সেটাই বলি। মৃত মার্কস জীবিত হয়ে আমাদের তাঁর তত্ত্ব বোঝাতে আসেন না। সব মৃত গ্রন্থ সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য।
ঠিক তেমনই সব ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও একই সত্য। আল্লার কোন ছাপাখানা নাই যেখান থেকে কোরানুল করিম ছাপা হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। আখেরি নবির কাছে কোরানুল করিম এসেছে ‘ওহি’ হিশাবে, কোন ছাপা গ্রন্থ জিব্রাইল তাঁকে দেন নি। বোঝা যাচ্ছে ‘ওহি’ কোন মৃত লেখকের বই হিশাবে নাজিল হয় নি। যিনি ‘ওহি’র মধ্য দিয়ে ধরা দিয়েছেলেন তিনি সততই অধরা, গায়েব বা অনুপস্থিত। তাঁর বাস জীবন্ত মানুষের মধ্যে। মানুষের বাইরে না। ইসলামে সেই জন্য ‘নিরক্ষর নবী’র ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অক্ষরের দোষমুক্ত ক্বলব, হৃদয় বা চিত্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এখান থেকে সুফিদের ‘দিল-কোরান’ ধারনার উদ্ভব, নদিয়ার ভাবচর্চাতেও যা স্থান করে নিতে পেরেছে। ‘দিল-কোরান’ কোন লিখিত বা মুদ্রিত বই নয়। বরং সেই কোরান যা আল্লার কাছ থেকে ‘ওহি’ হিশাবে নাজিল হয়েছে। অতএব অক্ষরের দোষমুক্ত বিশুদ্ধ হৃদয় ও অন্তর ছাড়া আল্লার ‘ওহি’র মর্মোদ্ধার জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা নবীর নিঃশর্ত আশেকান এবং যাদের কাছে রাসুলে করিম (সা.) মূর্তিমান আদর্শ হয়ে বিরাজ করেন।
নদীয়া জীবন্ত মানুষের ভজনা করে। কোনো মৃত মানুষকে নয়। সে কারণে ‘লালনপন্থা’ বলে কোনো পন্থা আছে, নদীয়া তা স্বীকার করে না। নদীয়ায জ্যান্ত গুরু আছেন। যিনি বর্তমান। গুরু থুয়ে নদীয়া গৌর ভজনা করতেও রাজি না। নদীয়ায় গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ খুবই শক্তিশালী চিন্তার ওপর দাঁড়ানো। যাকে প্রথাগত গুরু-শিষ্যের ধারণা দিয়ে বোঝা যায় না। মানুষ সত্য নয়, সত্য হচ্ছে গ্রন্থ বা শাস্ত্র– নদীয়া তা মানতে রাজি না। সত্য সবসময়ই রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং রপায়িত হয়ে চলেছে। বই বা শাস্ত্রের অর্থও একমাত্র জীবন্ত মানুষই করতে পারে। কিন্তু মানুষ দোহাই দেয় শাস্ত্রের। শাস্ত্রের বিপরীতে জীবন্ত মানুষকে সদাসর্বদাই তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।
আমরা জীবিতরা যেভাবে দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়ি, তার অর্থ আমরা নিজেরাই– জীবন্ত মানুষেরাই করে থাকি। বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি ‘ওহি’ হিশাবে কোনো নবী বা রসুলের কাছে নাজিল হয় নি। তাই কেতাবি ধর্ম যে অর্থে ‘ধর্মগ্রন্থ’ সেই অর্থে বেদ, উপনিষদ, গীতাকে ধর্মগ্রন্থ বলা যায় কিনা সেটা বিতর্কিত হতে পারে। হয়তো খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের কেতাবের বিপরীতে এদেরকেও ধর্মের কীতাবে হিশাবে দাবি করা হয়েছে। অথচ অক্ষর বা ছাপা বই সংক্রান্ত তর্ক সম্পর্কে যদি আমরা হুঁশিয়ার থাকি তাহলে ‘শ্রুতি’, ‘স্মৃতি’ ইত্যাদি ধারণা এবং তাদের গুরুত্ব আরও গভীর ভাবে বরং ধরা পড়ে। আরও গভীরতর বিষয়ে নতুন ভাবে প্রবেশের সূত্র তখন আমরা একই সঙ্গে নদীয়ার ভাবচর্চা কোনো অর্থে ‘বেদ’ ও ‘শাস্ত্র বিরোধী’ সেই প্রশ্নটিকেও আমরা নতুন ভাবে বিবেচনা করতে বাধ্য হই। জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা অর্থাৎ জীবন্ত মানুষ হিশাবে পাঠ করতে গিয়ে আমরা গ্রন্থের যে অর্থ বুঝি তাকেই গ্রন্থের অর্থ গণ্য করি। তাফসির বা টিকাভাষ্যও তাই। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা ধর্মগ্রন্থ বা বই পড়ে যা বুঝেছেন সেটাই লিখেছেন। তাঁদের ছাপা টিকাভাষ্য বা তাফসির পড়ে আমরা তাদেরকেও আমামদের মতো বুঝি, আমাদের মতো অর্থ করি। আমরা আবার একই ফাঁদে পড়ে চক্রাবর্তে ঘুরতে থাকি।
ছাপা বই কথা বলতে পারে না, বইয়ের সঙ্গে নীরবে কথোপকথন করি আমরা পাঠক, স্বয়ং। আমরা জীবিতরাই বিভিন ধর্মগ্রন্থ পড়ি, তাফসির বা টিকাভাষ্য লিখি। লেখক জীবন্ত পাঠকের ওপর ‘ভূত’ ভর করে বললে ভূতের অন্তর্নিহিত দ্যোতনা বোঝা যায় না। আসলে ‘ভূত’ মানে ভূ–ভবতি– সত্তা, বিদ্যমানতা– এই অর্থে। যিনি আছেন অথচ নাই। সক্রেটিস আছেন, তাঁকে নিয়ে আমরা জীবিতরা কথা বলছি, অথচ তিনি নাই। ভূতকে এভাবে বুঝলে আর ভয় লাগে না। আর, আমার কথা বুঝতেও আরাম হবে।
কিন্তু সক্রেটিস অক্ষরের মধ্যে ‘ভূত’ হয়ে বাঁচতে চান নি, তিনিও জীবন্ত দেহের উপাসক। রক্তমাংস সম্পন্ন দেহের বিভিন্ন প্রতিভার মধ্যে ‘স্মৃতি’ নামক প্রতিভা অসামান্য। যার স্মৃতি নাই, সে জীব মাত্র – তার ইতিহাসও নাই। লিখালিখির অর্থ হচ্ছে স্মৃতিকে শক্তিশালী করবার কাজ থুয়ে তাকে দুর্বল কবার প্রস্তাব। লিখে রাখা মানে যা আমরা ভুলে যেতে চাই, তাকে ভুলে যাবার ব্যবস্থা করা। আমাদের ধারণা আমরা আবার যা টুকে রেখেছি তা আবার পড়ে নিলে ভুলে যাওয়া বিষয় আবার মনে পড়বে। আসলে কি তাই? বোধ হয় না। কারন স্মৃতি মানে নিছক মনে করিয়ে দেওয়া নয়। ‘স্মৃতি’ গুরুতর বিষয়। একই সঙ্গে স্মৃতির সঙ্গে জীবন্ত দেহের – অর্থাৎ স্মৃতি নিয়ে বর্তমান বা জাগতিক থাকার গভীর অর্থটাও বুঝতে হবে।
ছাপা বই কথা বলতে পারে না, বইয়ের সঙ্গে নীরবে কথোপকথন করি আমরা পাঠক, স্বয়ং। আমরা জীবিতরাই বিভিন ধর্মগ্রন্থ পড়ি, তাফসির বা টিকাভাষ্য লিখি। লেখক জীবন্ত পাঠকের ওপর ‘ভূত’ ভর করে বললে ভূতের অন্তর্নিহিত দ্যোতনা বোঝা যায় না। আসলে ‘ভূত’ মানে ভূ–ভবতি– সত্তা, বিদ্যমানতা– এই অর্থে। যিনি আছেন অথচ নাই। সক্রেটিস আছেন, তাঁকে নিয়ে আমরা জীবিতরা কথা বলছি, অথচ তিনি নাই। ভূতকে এভাবে বুঝলে আর ভয় লাগে না। আর, আমার কথা বুঝতেও আরাম হবে।
দেরিদা কিম্বা প্লেটোর ফার্মেসি
জাক দেরিদা প্লেটোর কন্ঠস্বর বা মুখের ভাষা বনাম অক্ষর বা লিখিত ভাষার বাইনারি মানেন না। কোনো চিহ্ন বা ধারণার বিপরীতে আরেকটিকে বসিয়ে একটির প্রতি পক্ষপাতের বিরোধিতা করেন তিনি। প্লেটোর মুখের ভাষার প্রতি পক্ষপাতের ক্ষেত্রেও তিনি একই ব্যবহার করেছেন। আমরা সাধারণত অনুমান করি মুখের ভাষা বা কন্ঠস্বরই হচ্ছে আসল ভাষা। অক্ষর বা লিখিত ভাষা কন্ঠস্বরেরই বর্ণায়ন মাত্র। সেটা শুধু আমরা করি বললে ভুল হবে এরিস্টটল দাবি করেছেন মানসিক অভিজ্ঞতার চিহ্ন। অন্যদিকে লিখিত অক্ষর হচ্ছে মুখের ভাষারই চিহ্নায়ন। কারন লেখালিখি মুখের ভাষাকে চিহ্নে রূপ দেবার জন্যই আবিষ্কৃত হয়েছে, অতএব তাৎক্ষণিক মানসিক অভিজ্ঞতা থেকে চিহ্ন দূরবর্তী। প্লেটোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় মুখের কথাকে তিনি লিখিত ভাষার উপরে স্থান দিচ্ছেন। মুখের ভাষার সঙ্গেই তিনি ‘লোজস’ (Logos), জ্ঞান বা যুক্তির (Reason) ঘনিষ্ঠতা বা আন্তরিক সম্পর্ক খুঁজে পান। চিন্তার যে কোন বিষয়বস্তু মুখের ভাষার মতো আমাদের চিন্তার সাক্ষাতে সরাসরি হাজির থেকেই নিজের সত্য প্রদর্শন করে— মুখের ভাষার এই প্রাধান্য পাশ্চাত্য চিন্তার ইতিহাসে অতি আদি অনুমান। বিষয়কে বুদ্ধির দরবারে সামানাসামনি হাজির করে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা এবং সত্যতা নিশ্চিত হবার বাসনা ‘হাজিরাগিরির পরাবিদ্যা’ (Metaphysics of the Presence) নামে পরিচিত। দেরিদার চিন্তা বা দর্শন এই হাজিরাগিরির পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।
দেরিদার দাবি, কন্ঠস্বরকে অক্ষরের ওপর কায়েম করতে গিয়ে প্লেটো লিখিত ভাষার চরিত্রটাই বরং কণ্ঠের ভাষার ওপর আরোপ করেন। দেরিদা প্লেটোর লেখার স্টাইলকে নাম দিয়েছেন ‘ফার্মাকন’। প্লেটোর লেখার মধ্যেই ধারণাটা আছে। অর্থাৎ লেখালিখি বা যেকোনো টেকনলজি একই সঙ্গে ভাল এবং মন্দ, বিষ এবং অমৃত। প্লেটো থেকে ‘ফার্মাকন’-এর ধারণা ধার নিয়ে প্লেটোর সঙ্গে বাহাস করেছেন দেরিদা। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর ওপর লেখা দেরিদার বিখ্যাত নিবন্ধের নাম ‘প্লেটোর ফার্মেসি’ (Derrida, 1981)।

দেরিদার দ্বারা প্লেটোর ‘ফেদ্রুসের সঙ্গে কথোপকথন’ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমরা বুঝি কীভাবে ‘ফার্মাকন’-এর অনুবাদ বা ব্যাখ্যা আমরা করি তার ওপর। গ্রিক ভাষায় এর নানান ব্যবহার আছে, কোন অর্থ গ্রহণ করব আমরা? ওপরে আলোচনায় আমরা সবচেয়ে সরল এবং সিধা অর্থই বুঝেছি: লেখালিখি স্মৃতির বিষ। জীবন্ত মানুষের নিজের স্মৃতির বাইরে কোনো চিহ্নের ওপর নির্ভরশীলতা সহজ স্বাভাবিক কথোপকথনে বাধা, অতএব সামাজিকতা বিকাশের প্রতিবন্ধক। দেরিদার কাছে প্লেটোর লেখার ধরণটাই ফার্মাকন। ফেদ্রুসের সঙ্গে কথোপকথনে একটি মিশরীয় পুরাণ প্রসঙ্গে প্লেটো ‘ফার্মাকন’ ধারনাটি ব্যবহার করেছেন। প্লেটোর এই অংশটি যতোটা জটিল নয়, দেরিদা তাকে আরও প্রশ্নাত্মক বা সমস্যাসংকুল করে তুলেছেন। তাঁর অবিনির্মাণ কলার (Deconstruction) এটা একই সঙ্গে গুণ এবং দোষ, কিম্বা প্রতিভা রবং অপচয়। মিশরীয় পুরাণ সক্রেটিস উল্লেখ করছেন কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে। উদ্দেশ্য কথোপকথনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা কথোপকথন সমৃদ্ধ করা। মিশরীয় পুরাণটি এই ক্ষেত্রে কথোপকথনের অধীন, কথোপকথনের মর্মের বাইরে তাকে আলাদা করে ব্যাখ্যা মূল বিষয় থেকে আমাদের সরিয়ে নেওয়া। দেরিদা কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতের নয় বরং ‘ফার্মাকন’কে কথোপকথনের বাইরে সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের আলোকে প্রতিস্থাপন করেন।
দেরিদা দেখাতে চেয়েছেন পাশ্চাত্য দর্শন লেখা বা অক্ষরকে নয়, অর্থের নিশ্চয়তার জন্য প্রাধান্য দিয়েছে কন্ঠস্বর বা মুখের ভাষাকে। লেখালিখির বিরোধিতা করে প্লেটো ঠিক করেন নি। কারণ তাঁর ব্যবহৃত ‘ফার্মাকন’ ধারণাটি তিনিও নানান অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ‘নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র, ‘বিষ’ এবং ‘অনির্ণেয়’। একই চিহ্নের মধ্যে নানান অর্থ খেলা করে। যারা প্লেটোর অনুবাদ করেন তারা কোন একটি অর্থ ধরে নিয়েই অনুবাদ করেন। দেরিদার কাছে এটা ‘প্লেটোনিজম’ বা প্লেটোর বিশ্বাস যে কোনো একটি লেখার একটি মাত্রই অর্থ বা ব্যাখ্যা থাকে।
দেরিদার দাবি কন্ঠস্বরের ভাষা আর লিখিত ভাষার মধ্যে কে আগে বা কে পরে এই তর্ক আমাদের কোত্থাও নেয় না। কন্ঠস্বর ও অক্ষরের বাইনারি অনুমান করে কন্ঠস্বরকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পাশ্চাত্যে চিন্তার যে ধারা গড়ে উঠেছে তার পেছনে রয়েছে ভাষা বা যে কোন চিহ্নব্যবস্থার মধ্যে সুনির্দিষ্ট বা আগাম তৈরি রাখা অর্থের উপস্থিতি আছে এই প্রকার নিশ্চয়তাবোধ। কোনো কিছু প্রত্যক্ষ হাজির থাকলেই আমরা নিশ্চয় বোধ করি। কন্ঠস্বরে ভাষার জীবন্ত উপস্থিতি— অর্থাৎ যিনি কথা বলছেন তিনি সামনে হাজির এবং বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে দূরত্ব না থাকা, ইত্যাদি—আমাদের মধ্যে অর্থের নিশ্চয়তাবোধ তৈরি করে। এই নিশ্চয়তাবোধ কণ্ঠস্বরের প্রতি আমাদের পক্ষপাত তৈরি করে। যেহেতু অক্ষর বা লিখিত ভাষাকে আমরা মুখের ভাষার বর্ণায়ন গণ্য করি, তাই আমরা যা পড়ি তাতে অনুমান করি লেখক যা বলতে চেয়েছেন সেটা তাঁর লেখার মধ্যেই থাকে বা আছে। লেখক স্বয়ং লেখার মধ্যে হাজির। আসলে অর্থ তৈরি হয় পাঠকের পাঠের গুণে। তবু আমরা মনে করি কোন লেখা পড়া মানে লেখক যে অর্থ আমাদের কাছে পৌঁছাবার জন্য অক্ষরের আশ্রয় নিয়েছেন অক্ষর ভেদ করে সেই অর্থ আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে। দেরিদার দাবি পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস এই অনুমানের ওপর গড়ে উঠেছে— দর্শন দার্শনিকের মনে আগেই তৈরি হয়ে থাকা ভাব বা অর্থ লিখিত ভাষায় প্রকাশ করছে মাত্র। অর্থাৎ ভাষার আগেই অর্থ তৈয়ার হয়ে আছে। সেটা ভাষায় শধু পেশ করা হয়। ভাষা বাইরের খোলস, বিপরীতে অর্থ শাঁসের মতো ভেতরে থাকে। বাহিরটা অশুদ্ধ। ভেতরটাই আসল বা শুদ্ধ।
এই যে ভাষার বিশুদ্ধ অভ্যন্তর একে উদ্ধার করার উপায় কী? উপায় হচ্ছে যদি যা ‘বাহির’ তার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায়। দেরিদা বলছেন, অক্ষর বা লিখিত ভাষার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে প্লেটো সেই কাজটাই করছেন। প্লেটোর কাছে লিখিত ভাষা হচ্ছে কোন কিছু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বাইরে দাগ বা চিহ্ন দিয়ে রাখা। প্লেটো বাহিরকে বাহির গণ্য করে, ভাষা থেকে ভাষার রূপ বা চিহ্নব্যবস্থাকে সংযোজন, সম্পূরক, মাধ্যম, বাহক, পরিশিষ্ট ইত্যাদিতে পর্যবসিত করে ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষা ও উদ্ধার করতে চান। চিহ্নব্যবস্থা ভাষার জন্য দরকারি না, বরং ক্ষতিকর। ভাষার বাহ্যিক আঁকিবুকি ভাষার অন্তরবস্তু নষ্ট করে দিতে পারে। অন্তরবস্তুর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিষ, ওষুধ বা ফার্মাকন ব্যবহার করা যাবে না। অক্ষর হচ্ছে পরজীবীর মতো ভহাষার জীবন যা ক্ষয় করে ফেলতে পারে। তাহলে বাহিরকে বাইরেই যদি রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই লেখালিখি ঠিক যা সেভাবেই রাখতে হবে। অর্থাৎ সহায়ক, আনুষঙ্গিক বাড়তি বা অতিরিক্ত বোঝা হিশাবে। বাইরে। দাঁড়াতে হবে মুখের ভাষার পক্ষে (Derrida, 1981, পৃষ্ঠা ১২৮)। প্লেটোর বক্তব্যকে এভাবেই দেরিদা সারার্থ করেছেন।

মুখের ভাষায় বক্তা যে ‘মনের ভাব’ প্রকাশ করে সেটা বক্তার মুখোমুখি কিম্বা বক্তার সামনে হাজির থাকবার কারণে আমরা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় বা নিশ্চিত হই। অর্থ বুঝি ভাবি। উপস্থিতিমূলক এই প্রকার নিশ্চয়বোধ আমরা লিখিত ভাষার কাছ থেকেও প্রত্যাশা করি। বই যখন আমরা পড়ি তখন বইয়ের লেখক আমাদের সামনে হাজির থাকে না, কিন্তু আমরা মনে করি অক্ষর বা লিখিত ভাষার মধ্যেও লেখক যেমন চেয়েছেন তেমন সঠিক বা শুদ্ধ অর্থ হাজির রয়েছে। তাই ধরতে পারি না যে ভাষা বা যেকোন চিহ্নই পাঠকের পাঠ গুণে নানান অর্থ তৈরি করতে সক্ষম এবং করেও বটে।। এটা ভাষা বা চিহ্ন ব্যবস্থার স্বভাব বা গুণ।
এই অনুমান থেকে আমরা দাবি করি ভাষা স্রেফ ভাব বা অর্থ প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। আমরা যখন বলি ভাষা মনের ভাব প্রকাশের উপায় – তখন আমরা একই সঙ্গে অনুমান করি গ্রন্থের মধ্যেই তার ছহি অর্থ নিহিত রয়েছে। কাজ হচ্ছে তাকে হাজির বা দৃশ্যমান করে তোলা। কিন্তু ভাষা বা যে কোন চিহ্নব্যবস্থাই অবস্থা, পাত্র ও সম্পর্ক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরি করতে পারে।
কন্ঠস্বর কেন আমাদের অর্থের নিশ্চয়তা বোধ দেয়? আমাদের মনে হয় আমরা বুঝি অর্থ তখন তৎক্ষণাৎ বুঝি। এমনকি কোন কিছু আমরা মনে মনে বললেও– এই বোধ ঘটে যে মনে মনে যা বলছি তার অর্থও আমাদের কাছে ‘হাজির’, ‘আছে’ বা উপস্থিত। কারন আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা তখন ভাষাকে জীবন্ত হাজির উপলব্ধি করতে পারি। যখ আমরা পরস্পর কথা বলি, তখন আমরা পস্পরের কাছে বর্তমান থাকি। এর বিপরীতে দেরিদার দাবা লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে লেখক ও পাঠকের মধ্যে দেশ ও কালের দূরত্ব বা ফারাক ঘটে। ফলে লিখিত ভাষার অর্থের ক্ষেত্রে সব সময়ই অনিশ্চয়তা ভর করে।
এই যে ভাষার বিশুদ্ধ অভ্যন্তর একে উদ্ধার করার উপায় কী? উপায় হচ্ছে যদি যা ‘বাহির’ তার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায়। দেরিদা বলছেন, অক্ষর বা লিখিত ভাষার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে প্লেটো সেই কাজটাই করছেন। প্লেটোর কাছে লিখিত ভাষা হচ্ছে কোন কিছু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বাইরে দাগ বা চিহ্ন দিয়ে রাখা। প্লেটো বাহিরকে বাহির গণ্য করে, ভাষা থেকে ভাষার রূপ বা চিহ্নব্যবস্থাকে সংযোজন, সম্পূরক, মাধ্যম, বাহক, পরিশিষ্ট ইত্যাদিতে পর্যবসিত করে ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষা ও উদ্ধার করতে চান। চিহ্নব্যবস্থা ভাষার জন্য দরকারি না, বরং ক্ষতিকর। ভাষার বাহ্যিক আঁকিবুকি ভাষার অন্তরবস্তু নষ্ট করে দিতে পারে। অন্তরবস্তুর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিষ, ওষুধ বা ফার্মাকন ব্যবহার করা যাবে না। অক্ষর হচ্ছে পরজীবীর মতো ভহাষার জীবন যা ক্ষয় করে ফেলতে পারে। তাহলে বাহিরকে বাইরেই যদি রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই লেখালিখি ঠিক যা সেভাবেই রাখতে হবে। অর্থাৎ সহায়ক, আনুষঙ্গিক বাড়তি বা অতিরিক্ত বোঝা হিশাবে। বাইরে। দাঁড়াতে হবে মুখের ভাষার পক্ষে (Derrida, 1981, পৃষ্ঠা ১২৮)। প্লেটোর বক্তব্যকে এভাবেই দেরিদা সারার্থ করেছেন।
ফকিরি নোক্তা
ফকিরি নোক্তা বলছি কারন নদীয়ার ফকিরদের তরফে কিছু কথা বলে রাখতে চাছি।
পাত্র বা পাঠক ভেদে চিহ্ন, অক্ষর বা লেখালিখি সবসময়ই নানান অর্থ তৈরি করে। ভাষা সম্পর্কে এই শিক্ষাটা আমাদের পাশ্চাত্য থেকে নিতে হবে এমন কোন কথা নাই। এই তর্ক আমাদের ভাবচর্চার মধ্যেও প্রবল ভাবেই আছে। এমনকি সবকিছুর মধ্যেও বিষ এবং অমৃত মাখামাখি থাকে এটাও আমাদের জন্য নতুন কোনো তত্ত্ব না। ‘বিষামৃতে আছেরে মাখাজোখা’ – এটা আমরা জানি। প্রেমে কাম এবং কামের মধ্যেও প্রেম থাকেন।
কিন্তু জাক দেরিদার দারুন তাৎপর্য হচ্ছে পাশ্চাত্য দর্শন বা চিন্তার ইতিহাসে ভাষা সম্পর্কে এই অনুমান – হাজিরাগিরির পরাবিদ্যা — কিভাবে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে, সেটা দেখিয়ে দেওয়া। ফকির লালন শাহ বেশ সাহসের সঙ্গে বলেন বই পড়ে আমরা যা বুঝি সেটা আমাদের যার যার মনেরই বুঝ। গ্রন্থের মধ্যে সেই বুঝ হাজির আছে এটা স্রেফ অনুমান। তাই প্রত্যকে যার যার বুঝ মতোই পড়ে। যদি তা না হোত তাহলে একই কোরআন পড়ে কেউ মৌলবি আর কেউ মওলানা হয় কেন? এতো ভিন্ন ভিন্ন হাজার হাজার তাফসির বা ব্যাখ্যারই বা কারণ কি? শুদ্ধ পাঠ বলে কো পাঠ নাই। ছহি অর্থ বলে কোন অর্থ নাই। এমনকি কোরান, বাইবেল গীতা, বেদ, উপনিষদও গ্রন্থ হিশাবে ছাপাখানায় ছাপা মৃত বই। যে যার মতো বোঝে। সমাজে নানান মত ও পথ তৈরি হয়।
কে বোঝে সাঁইয়ের আলেকবাজি
হচ্ছে রে কোরানের মানে
যা আসে যার মনের বুঝ-ই।।
একই কোরান পড়াশুনা
কেউ মৌলভি কেউ মওলানা
দাহেরা হয় কত জানা
সে কী মানে শরার কাজী।।
কোরআন, বাইবেল, গীতা, উপনিষদ আর যেকোনো গ্রন্থ বলি সেইসব গ্রন্থ যে যেভাবে পড়ে তার বুঝও সেই রকমই হয়। তাহলে ভাষার সঙ্গে অর্থের সম্পর্কের বিষয় শুধু দর্শন নয়, ধর্মতত্ত্বেরও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কোরান পাঠের মধ্য দিয়ে যে বিভিন্ন প্রকার অর্থোৎপত্তি ঘটে সেটা শরিয়ার আইন দ্বারা শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যার যার বুঝ মোতাবেক আইন দিয়ে যদি ধর্ম, ভাব বা পরমার্থিক জগৎ কায়েম করতে হয় তাহলে ধর্ম আর শরিয়া কিম্বা ধর্ম আর আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। মনুশাস্ত্র কিম্বা বাইবেল সম্পর্কেও একই। এই কারণে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের নানান তাফসির, নানান ব্যাখ্যা নানান মজহাব, নানান মত ও পথ তৈরি হওয়া অনিবার্য। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে নিজ নিজ নিজ বুঝ দিয়েই যদি জগৎ কায়েম করতে হয়, সেটা তাহলে সকলের ধর্ম বা আরাধ্য থাকে কিনা সেটা তর্কের বিষয় হয়ে ওঠে।
সমাধানের জন্য ইসলামে এর একটা চর্চা আছে। সেটা হচ্ছে তেলাওয়াতকে গুরুত্ব দেওয়া। তেলাওয়াতের ধ্বনিমাধুর্যের মধ্য দিয়ে ‘ওহির’ দিব্য রূপ ও মর্ম কন্ঠস্বর এবং শ্রুতি দিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা। অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থকে অক্ষর ও বুদ্ধির বিমূর্ত ও একচ্ছত্র কারবার থেকে নামিয়ে তাকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও হৃদয়ের বিষয় হিশাবে সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও এই চেষ্টা ঘটেছে বা আছে। অন্যান্য ধর্মকেও ভাষার বহু অর্থ জ্ঞাপকতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। জীবন্ত মানুষ মৃত অক্ষরের নতুন ব্যাখ্যা বা অর্থ দাঁড় করাবেই।

এই কারণে বড় বাংলার ভক্তি আন্দোলন শাস্ত্র বিরোধী। কারন লিখিত অক্ষর বা শাস্ত্রের নামে চিরায়ত সত্যের দাবি করা সহজ। বই মরে না। বারবার ছাপা যায়। ফলে ছাপাখানার কল্যাণে গ্রন্থের বারবার প্রত্যাবর্তন করা অর্থাৎ চিরায়ত দাবি করার সুযোগ থাকে। এমনই যে মনে হয় বই যা বলে তাই সত্য, বিশেষত যদি তা ধর্মগ্রন্থ হয়। গ্রন্থের তুলনায় মানুষ নশ্বর। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ বাদ দিলে শাস্ত্র বিরোধী প্রেমের ধর্ম প্রচার হৃদয় ও অক্ষরের বিভাজন মোচনের জন্য। বিশেষত অক্ষর যখন দাবি করে সে ঐশ্বরিক, তখন সেটা মানুষের বিশাল সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেয়।
শুরুর দিকে কোরআন হেফজ বা মুখস্থ রাখার ওপরই তাই জোর দেওয়া হয়েছিল। কোরানকে স্মৃতিতে জীবন্ত ধরে রাখা, স্মৃতির চর্চাকে প্রাধান্য দেওয়া। লিখিত কোরানকে নয়। প্লেটো যার ওপর জোর দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা টেঁকে নি। এখন কোরান শরিফকে আল্লার ওহি হিশাবে নয়, বরং এমনভাবে বাকবিতণ্ডা চলে মনে হয় আল্লার একটা ছাপাখানা আছে সেখান থেকে নিত্যদিন কোরান ছাপা হয়ে দুনিয়ায় নাজিল হচ্ছে। অথচ কোরান নিজেকে কোন ধর্মগ্রন্থ, কিম্বা আল্লার তরফ থেকে ‘আইনের বই’ বা ‘আইনের গ্রন্থ’ বলে দাবি করে নি। কোরানুল করিমের বিনীত দাবি: মানুষের হেদায়েত বা মানুষকে উপদেশ দেবার জন্যই আল্লার তরফ থেকে ওহি হিশাবে রাসুলে করিমের প্রতি কোরান নাজিল হয়েছে। এই জন্যই এই ‘কেতাবে’ কোন সন্দেহ নাই।
ফলে দেরিদা পাশ্চাত্যের ‘হাজিরাগিরির পরাবিদ্যা’র যে পর্যালোচনা করেছেন তা আমাদের কাজে লাগে। কিন্তু দেরিদার যেখানে প্রবল ঘাটতি সেটা হোল তাঁর পুরা আলোচনা পাশ্চাত্য দর্শনকে কাবু করতে গিয়ে মানুষের সমাজ ও জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের সম্পর্ক ভুলে যাওয়া। তিনি একজন ব্যক্তি কিভাবে প্লেটো পড়তে পারে, তার দোষগুণ বিচার করেছেন। সেটা ভালো। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন প্লেটো যে মুখের ভাষার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন সেটা কথোপকথনকে জীবন্ত ও সমৃদ্ধ করবার দরকারে। একমাত্র কথার মধ্য দিয়েই জীব তার পরমার্থিক সত্তাকে সকলের মধ্যে আবিষ্কার এবং সঞ্চারিত করতে সক্ষম। সেই ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থ, বই বা টেকনলজি নয় – জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের কথোপকথন ও সম্পর্কই নদীয়া যাঞ্চা ও বাঞ্ছা করে। সাধুসঙ্গই সাধুর পরমার্থিক জীবন।
তবে ‘মানুষ ভজনা’ কথাটা গভীরতর সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থে বোঝার ক্ষেত্রে নদীয়ার ফকিরদের বিপুল ঘাটতি আছে। সেটাও স্বীকার করে নেওয়া ভাল।
বড় বাংলার ভক্তি আন্দোলন শাস্ত্র বিরোধী। কারন লিখিত অক্ষর বা শাস্ত্রের নামে চিরায়ত সত্যের দাবি করা সহজ। বই মরে না। বারবার ছাপা যায়। ফলে ছাপাখানার কল্যাণে গ্রন্থের বারবার প্রত্যাবর্তন করা অর্থাৎ চিরায়ত দাবি করার সুযোগ থাকে। এমনই যে মনে হয় বই যা বলে তাই সত্য, বিশেষত যদি তা ধর্মগ্রন্থ হয়। গ্রন্থের তুলনায় মানুষ নশ্বর। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ বাদ দিলে শাস্ত্র বিরোধী প্রেমের ধর্ম প্রচার হৃদয় ও অক্ষরের বিভাজন মোচনের জন্য। বিশেষত অক্ষর যখন দাবি করে সে ঐশ্বরিক, তখন সেটা মানুষের বিশাল সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেয়
বইপত্রের হদিস
Al_Ghazzali. (1980). The Niche for Lights (Meshkatul Anwar ), tr. W.H.T.Gairdner. দেখুন, Four Sufi Classic (পৃষ্ঠা ৫৭-১৬১). London: The Sufi Trust।
Derrida, J. (1981). Plato’s Pharmacy. London: The University of Chicago Press.
Plato. (1961). The Collected Dialogues of Plato. সম্পাদনা করেছেন Edith Hamilton and Huntington Cairn. New York: Princeton University Press.
Rinella, M. A. (2010). Pharmakon: Plato, Drug Culture, and Identity in Ancient Athens. New York: Lexington Books.
Waterfield, R. (2002). Phaedrus, PLATO’s. New York: Oxford University Press.
ফরহাদ মজহার

কবি, চিন্তক, বুদ্ধিজীবী ও কৃষক। জন্ম: ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায়। পড়াশুনা করেছে ওষুধ শাস্ত্র ও অর্থনীতি বিষয়ে যথাক্রমে ঢাকা ও নিউইর্কে। পেশা সূত্রে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের ‘নয়াকৃষি আন্দোলন’-এর প্রধান সহযোদ্ধা। লালন ধারা-সহ বৃহৎ বঙ্গের ভাবান্দোলন পরম্পরার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সমাজ ও রাজনীতি চিন্তা এবং দার্শনিক বিষয়ে বহু গদ্য রচনা করেছেন। এছাড়াও লিখেছেন নাটক। অনুবাদও করেছেন।
তাঁর বইগুলি-
কাব্যগ্রন্থ:
খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ (১৯৭২) ।। ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি (১৯৭৭) ।। আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে (১৯৮৩) ।। সুভাকুসুম দুই ফর্মা (১৯৮৫) ।। বৃক্ষ: মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ক কবিতা (১৯৮৫) ।। অকস্মাৎ রপ্তানিমুখী নারীমেশিন (১৯৮৫) ।। খসড়া গদ্য (১৯৮৭) ।। মেঘমেশিনের সঙ্গীত (১৯৮৮) ।। অসময়ের নোটবই (১৯৯৪) ।। দরদী বকুল (১৯৯৪) ।। গুবরে পোকার শ্বশুর (২০০০) ।। কবিতার বোনের সঙ্গে আবার (২০০৩) ।। ক্যামেরাগিরি (২০১০) ।। এবাদতনামা (২০১১) ।। অসময়ের কবিতা (২০১১) ।। কবিতাসংগ্রহ (২০১১) ।। তুমি ছাড়া আর কোন্ শালারে আমি কেয়ার করি? (২০১৬) ।। সদরুদ্দীন (২০১৮)
গদ্যগ্রন্থ:
প্রস্তাব (১৯৭৬) ।। সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান প্রসঙ্গে (১৯৮৫) ।। রাজকুমারী হাসিনা (১৯৯৫) ।। সাঁইজীর দৈন্য গান (২০০০) ।। জগদীশ (২০০২) ।। সামনা সামনি: ফরহাদ মজহারের সঙ্গে কথাবার্তা (২০০৪) ।। বাণিজ্য ও বাংলাদেশের জনগণ (২০০৪) ।। মোকাবিলা (২০০৬) গণপ্রতিরক্ষা (২০০৬) ।। ক্ষমতার বিকার ও গণশক্তির উদ্বোধন (২০০৭) ।। ভাবান্দোলন (২০০৮) পুরুষতন্ত্র ও নারী (২০০৮) ।। সাম্রাজ্যবাদ (২০০৮) ।। রক্তের দাগ মুছে রবীন্দ্রপাঠ (২০০৮) ।। সংবিধান ও গণতন্ত্র (২০০৮) ।। নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০৮) ।। তিমির জন্য লজিকবিদ্যা (উপন্যাস, ২০১১)
প্রাণ ও প্রকৃতি (২০১১) ।। মার্কস পাঠের ভূমিকা (২০১১) ।। ডিজিটাল ফ্যাসিবাদ (২০১২)
যুদ্ধ আরো কঠিন আরো গভীর (২০১৪) ।। ব্যক্তি বন্ধুত্ব ও সাহিত্য (২০১৬) ।। মার্কস, ফুকো ও রুহানিয়াত (২০১৮)
নাটক:
প্রজাপতির লীলালাস্য (১৯৭২)
অনুবাদ:
অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার একটি ভূমিকা (মূল: কার্ল মার্ক্স) (২০১০)
খুন হবার দুই রকম পদ্ধতি (মূল: রোকে ডাল্টন) (২০১১)

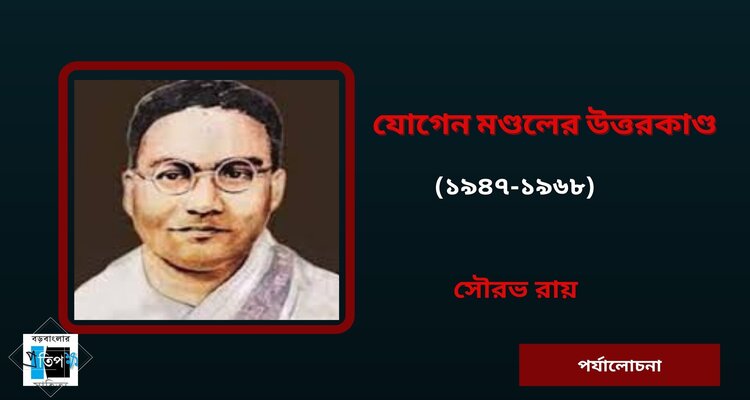

পড়লাম।অনেক ভালো লেগেছে…