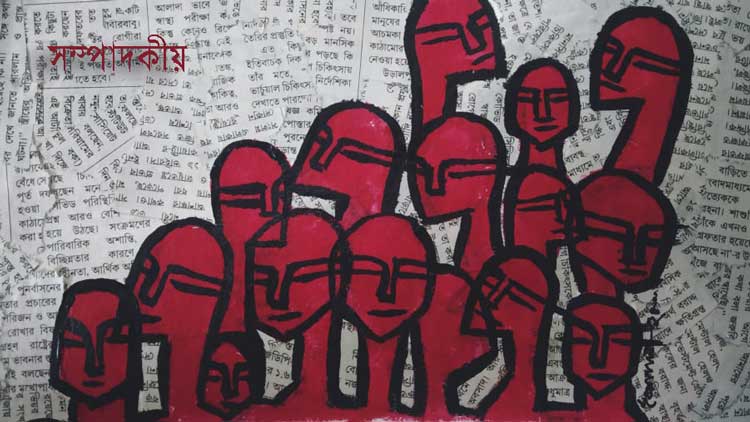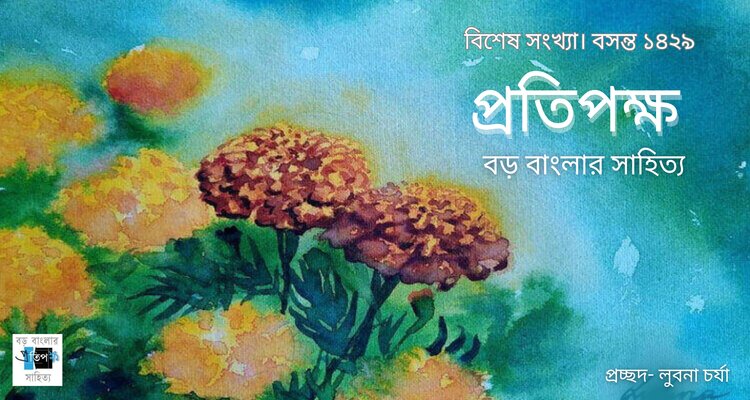।। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ।।
এবারে আমাদের পত্রিকার মুদ্রিত সংখ্যার মূল ফোকাস ‘গণঅভ্যুত্থান’। ৫২-র ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ’৬৯ ও ’৭১-এর পরম্পরাকে ধরে রেখে চব্বিশের আবির্ভূত হওয়া সংক্রান্ত প্রবন্ধের পাশাপাশি এই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নানা দিক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। তার সঙ্গে রয়েছে ইতিহাস, বিউপনিবেশায়ন, ধর্ম, সমাজ, সিনেমা, প্রাণ-প্রকৃতি ও সাহিত্য পর্যালোচনামূলক গদ্য এবং একঝাঁক লেখক-কবির গুচ্ছ কবিতা ও গল্প। রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাক্ষাৎকার। মুদ্রিত পত্রিকা একুশের বইমেলার শেষ কয়েকটি দিন মেলাপ্রাঙ্গনে পাওয়া যাবে। মেলার পরে প্রতিপক্ষর ঢাকা ও কলকাতার দপ্তরে মিলবে আমাদের মুদ্রিত পত্রিকা। আশা করব, হে পাঠক, আপনি আমাদের সঙ্গে এহেন গদ্য-পদ্য-বাহাস-যুক্তি-তক্কো ও গপ্পোর ভিতর দিয়ে সম্পর্ক দৃঢ় করবেন। শুভেচ্ছা।
আমরা একটি সপ্রাণ ও সুনির্দিষ্ট ভূগোলে বড় হয়েছি এবং নানান বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য-সহ শিথিল অর্থে ‘বড় বাংলা’-য় বাস করি। ‘বড় বাংলা’ বহু ও বিচিত্র অনেকের আবাস, যারা কমবেশি পরস্পরের ভাষা বোঝে এবং নানান প্রকার সামাজিক আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে সবার বোধগম্য একটা ভাষা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। সেই ক্ষেত্রে ভাষা ও আর্থ-সামাজিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক আমাদের নিজেদের একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত কল্পনা করতে অনুপ্রাণিত করে। সেই ক্ষেত্রে পুঁজিতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থা, গুটেনবার্গ টেকনোলজি ইত্যাদির ভূমিকা আছে। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন তাঁর ‘Imagined Communities’ গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একালে ডিজিটাল টেকনোলজি ও কমিউনিকেশন বিপ্লব আরও বৃহৎ ও বিস্তৃত পরিসরে ঔপনিবেশিক শক্তির আঁকা মানচিত্রের বাইরে স্মৃতি, ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির মিলের কারণে বাংলাকেও আরও বড় বা বৃহৎ কল্পনা করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। আমরা দেশকাল-নির্দিষ্ট মানচিত্র এবং রাষ্ট্রের বাইরে পরস্পরের সঙ্গে আরও বৃহৎ সম্পর্ক কল্পনা করতে এবং নিজেদের নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে ও পর্যালোচনা করতে পারি।
‘প্রতিপক্ষ’ বাংলা ভাষায় সকলের সহিত সম্বন্ধ পর্যালোচনা এবং নতুন সম্বন্ধ রচনার সম্ভাবনা বিচারের পত্রিকা। এই ‘বাস’ বা ‘আবাস’ তথাকথিত রাজনৈতিক মানচিত্র কিংবা নিষ্প্রাণ ভূগোলের ধারণা থেকে আলাদা। প্রথাগত রাজনীতির ধারণা থেকেও আলাদা। ‘বড় বাংলা’ এমন এক আবাসে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যেখানে ভূগোল, প্রাকৃতিকতা, জীবনযাপন, ভাব এবং ভাষার স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। তৈরি করে ভাষা, সংস্কৃতি, ভূগোল ও আবাসের সম্বন্ধ বিচারের নতুন সম্ভাবনা। নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ দৃঢ় করা এবং নতুন করে নিজেদের কল্পনা করতে পারা সম্ভব কি না, সেটা পর্যালোচনা করার মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ জাতিবাদের সীমা অতিক্রম করবার বাসনাও সৃষ্টি হয়। মানুষ শুধু ভূগোলে নয়, ভাষার মধ্যেও বাস করে। বড় বাংলা আবাস ও ভাষা এই দুয়ের সম্বন্ধ পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের বৈষয়িক ও আত্মিক বিকাশের নতুন কিন্তু শক্ত ভিত্তি সন্ধানে আগ্রহী।
পুঁজি এবং আধুনিক জীবন ব্যবস্থা আমাদের প্রথাগত সম্বন্ধ নিত্যদিন ভাঙছে, সমাজকে বিভিন্নভাবে চুরমার করে দিচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভক্তি ও শত্রুতাও বাড়াচ্ছে। বড় বাংলার ধারণা এবং নতুনভাবে সম্বন্ধ তৈরির আকুতি এই ক্রমবিভাজিত প্রক্রিয়া, বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিরোধ বলতে পারেন। আমরা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার বিপরীতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের ক্ষত অতিক্রম করে সকলের সঙ্গে সহজ-সরল, স্বাভাবিক ও সপ্রাণ সম্পর্ক বিকাশের বীজ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি।
নতুন সম্বন্ধ আবিষ্কার ও বসবাসের উপাদান বড় বাংলার ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে আমরা বিশেষভাবে খুঁজি। জাতপাত, বর্ণ পরিচয় ও সামাজিক বিভাজনের বিরুদ্ধে বাংলার ভাবান্দোলন শক্তিশালী একটি ধারা। সাধকদের জীবনযাপন ও ভাবচর্চার মধ্যে আমরা নতুন করে সামাজিক ও পারমার্থিক আকুতিসম্পন্ন মানুষকে চিনি এবং নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারি। নিজেদের নতুন করে বুঝি। এই আবাসের লোকেশন বা দেশকালপাত্র রয়েছে, ‘বড় বাংলা’ কথাটা আমরা কোথায় আছি সেই দিকচিহ্নের অবস্থান আবিষ্কারের চেষ্টা বলা যায়। ‘বড় বাংলা’ কথাটা নিজেদের লোকেশন চিহ্নিত করবার চিহ্ন হিসাবে আমরা ব্যবহার করি। এই ‘বড় বাংলা’ ধারণার মধ্যে নেই কোনো আত্ম-অহমিকা বোধ বা অস্মিতাচিহ্ন। কিংবা নেই, ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দুইটি জাতিরাষ্ট্র কাঠামোর অন্দরে অপরিহার্যভাবে বিভক্ত হয়ে যাওয়া অখণ্ড বঙ্গকে ফের ভূরাজনৈতিকভাবে একত্ব করবার কোনো জাতিবাদী চেতনা ও বাসনা। ‘বড় বাংলা’র কোনো জাতিবোধ, জাতিবাদ, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ কিংবা সাম্প্রদায়িক পরিচয় নেই। কোনো চিরায়ত পরিচয় বা জাতিবাদ নেই। কিন্তু ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস, ভাষা, ভক্তি ও ভাব ইত্যাদি রয়েছে। ভেদবিচার আছে, কিন্তু ভেদ নাই।
সে কারণে ‘সাহিত্য’ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চর্চার বিষয় হয়ে হাজির হয়েছে। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সম্বন্ধ তৈরি, সম্বন্ধ পাতানো— বিভেদ তৈরি বা শত্রুমিত্র ভাগ করা নয়। শত্রুমিত্র ভেদের রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ মৌলিক। শত্রুমিত্র ভেদের বিপরীতে মানুষের সর্বজনীন আকুতি আবিষ্কার ও মূর্ত করে তোলাই সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য শত্রুমিত্রের ভেদরেখা মুছে দিতে সক্ষম। সাহিত্য এমনই একটা ধারণা যেখানে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন এবং সকলের সঙ্গে বাস করবার আকুতি তৈরি হয়।
এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের কথা উল্লেখযোগ্য। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নিয়ে নানা সম্ভাবনাময় আলাপ উঠে আসছে। সমস্ত জাতিবাদী, পরিচয়বাদী এবং গোত্রবাদী ধারণাকে ভেঙে বাংলাদেশের জনতাকে একটা নতুন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সে সম্ভাবনা সাকার হলে নয়া সেই রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয়ভাবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ে বৈচিত্র্য, স্বাধীনতা ঐক্যের মাধ্যমে সদা বিরাজমান হবে। শুধু ধর্মীয় সম্প্রদায়গত জায়গা থেকেই এটা নয়, বরং ভাষাভিত্তিক ‘জাতীয়তা’র ক্ষেত্রেও বাঙালি ও বাংলাদেশের সকল অবাঙালি ভূমিসন্তানদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এই একই আলাপ প্রযোজ্য। শুধু তা-ই নয়, উপমহাদেশে জাতিরাষ্ট্রগতভাবে আলাদা হয়ে থাকা বাঙালি, বাঙলাভাষী-সহ সকল বঙ্গীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে পূনর্মূল্যায়িত করতে পারাটা বাংলাদেশের গণমনুষের রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যাতে আমাদের বৈচিত্র্যময় ঐক্যের সেতু আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারি, সেই কাজটা করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ ‘প্রতিপক্ষ’।
আগেই বলেছি সাহিত্য এমনই একটা ধারণা যেখানে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন এবং সকলের সঙ্গে বাস করবার আকুতি তৈরি হয়। কার্ল মার্কস এই আকুতির উৎপত্তি মানুষের প্রজাতিগত সত্তার (Species Being) মধ্যে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। অ্যারিস্টটলের ‘পলিস’ (Polis) ধারণার মধ্যেও এই মর্ম নিহিত রয়েছে। এই ধারণাগুলোর গভীরে আমরা প্রবেশ করবার চেষ্টা করি। এর সঙ্গে বড় বাংলার জীব-পরমে সম্বন্ধ নির্ণয়ের দীর্ঘ বাহাস বা তর্কাতর্কির ঐতিহ্যও আমরা মনে রাখি। এই জন্য ‘সাহিত্য, ‘বড় বাংলা’ ইত্যাদি বর্গ বাংলার ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তার মধ্যে যে বাংলার রূপ আমরা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি সেটা কোনো জাতিবাদী বাংলা না, সহজ মানুষের বাংলা। বড় বাংলার বীজ এই প্রকার শক্তিশালী ভাবচর্চার ক্ষেত্রগুলোতে আমরা সন্ধান করি। বীজ আছে, জমি আছে— যা আছে তাকে চাষ করবার কথা আমরা বলি। যেমন সাধকেরা তাঁদের যাঁর যাঁর অঞ্চলের সাহিত্যে, কাব্যে, গানে, নানান জীবনযাপন চর্চায় বাস করেন, নিজ নিজ অবস্থান থেকেই তাঁরা সকলের সঙ্গে নিজ নিজ সম্পর্ক মজবুত করেন, সর্বজনীন বা সকলের হয়ে ওঠেন। বড় বাংলাও সেই প্রকারে সকলের বাংলা হয়ে ওঠার সাধনা।
‘সহিত’ থেকে এসেছে ‘সাহিত্য’। তাই সাহিত্যের আসল কথা সম্বন্ধ রচনা করা। তাই ‘সাহিত্য’ কথাটা বড় বাংলায় ‘লিটারেচার’ হিসাবে আমরা অনুবাদ করি না। পাশ্চাত্যের লিটারেচারের ধারণা আমরা গ্রহণ করি না। ‘লিটারেচার’ থেকে ‘সাহিত্য’ অনুবাদ করি না। ‘সাহিত্য’ মানে সকলের সহিত বাস করতে শেখা, বাস করতে পারা, সম্বন্ধ পাতানো। আমরা পাশ্চাত্য অনুকরণ করি না। ঔপনিবেশিক আমলে ছাপাখানা ও বইকেন্দ্রিক যে সাহিত্যের ধারণা গড়ে উঠেছে, সেই লিটারেচারে আমরা সায় দিই না। আমরা সাহিত্যের পাশ্চাত্য ধারণার বিরোধী, লিটারেচারের ধারণা বাইরে থেকে নকল করা। আমরা পাশ্চাত্য নকল করি না।
আমরা যে পরস্পর কথা বলি, আলাপ করি, এটাই সাহিত্য। এখন কথোপকথন ছাড়াও সেটা লেখালেখি হতে পারে, নাচ হতে পারে, গান হতে পারে, শিল্পকলা হতে পারে, অন্য আরও অনেক কিছুই হতে পারে। কথোপকথন যেমন আরেকটি সচেতন জীবের সাথে সম্বন্ধ তৈরিতে সহায়ক, তেমনি অন্য যে কোনো চিহ্নব্যবস্থা ও মাধ্যমও একই কাজ করতে পারে। কথোপকথন যে পরিসর ও ভাব আদানপ্রদানের ক্ষেত্র তৈরি করে, তার প্রেরণায় আমরা পরস্পরের কথোপকথনের মধ্যে বাস করা শুরু করি— আপনি আমার কথা শুনছেন, আমি আপনার কথা শুনছি, ঘাড় নাড়ছেন, ঘাড় নাড়ছি— এই যে পারস্পরিকতা— এটাকেই বলে ‘সাহিত্য’। এখানে দু’জনের ‘সহিত’ বা সাহিত্য হল।
সাহিত্যের এই ধারণা আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে হারিয়ে গিয়েছে, ফলে ভক্তির ধারণাও চলে গেছে। এখন সাহিত্য বলতে ছাপাখানার বই বোঝায়। সকলে বই পূজা করে। কিন্তু গ্রন্থ সম্বন্ধ তৈরির একটা উপায়। মুখের কথা বা কথোপকথনের স্বতন্ত্র মূল্য আছে, বিশেষত আমাদের সাধকদের ধারার মধ্যে, শ্রুতি ও কন্ঠের স্বতন্ত্র একটা পরিমণ্ডলও আছে, একটা লম্বা ইতিহাস আছে এ সকলের— তবে তার খুব একটা খবর এখন আর আমাদের কাছে নাই; না থাকার জন্য আমাদের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। ভাবুন, লালনকে যেভাবে হাজির করে এখানকার শিক্ষিতরা— লালন যেন একটা থিয়েট্রিক্যাল ব্যাপার— সাদা কাপড় পরিয়ে ছেলেমেয়েদের নাচানো, ইত্যাদি। লালন একাডেমি ও ছেঁউড়িয়ার অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে সরকার, এটা প্রচণ্ড ক্ষতি করছে আমাদের। লালন সম্পর্কে, বাংলার ভক্তিধারার ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এইসব উপদ্রব মারাত্মক ক্ষতি করেছে। শুধু তা-ই নয়, এ সকল কারণে বাংলার যে দুটো প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়— সনাতন হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম— এই দুই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত যারা— তাদের নিজেদের মধ্যেকার বোঝাবুঝির জায়গায় মারাত্মক ফাঁক তৈরি হচ্ছে, ক্রমশ পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে, গহ্বর বড় হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে শাক্তদের যে ভক্তির ধারা গড়ে উঠেছিল সেটা খুবই শক্তিশালী। রামপ্রসাদ ফারসি জানতেন, আরবি জানতেন। যেমন কমলাকান্তও জানতেন। বিদ্যাসাগরের হাত ধরে সংস্কৃতায়ন শুরু হয়, তারপর সাহেব-পণ্ডিতের বাংলা। রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত কী অপূর্ব সব গান লিখেছেন, দর্শনের গোড়া ধরে টান দিয়েছেন, ধর্মতত্ত্বের থামগুলো ভেঙেছেন। এখন তো শাক্তদের সেই ধারা আপনাদের ওখান থেকে হারিয়ে গেছে বলেই মনে হয়। গান হয় খুব সুন্দর। পারফেক্ট। কিন্তু ভক্তি নাই। সেটা পর্যবসিত হয়েছে হিন্দুত্ববাদী পরিচয় নির্মাণে। এখন দেখা যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে যে ইস্কন গড়ে উঠেছে, সে ব্যাপারে কলকাতায় যাঁরা শিক্ষিত— যাঁদের এই ভক্তির ধারা— অর্থাৎ চিন্তা, দর্শন বা ভাব পর্যালোচনার ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার কথা ছিল, তাঁরা সজ্ঞান থাকেননি। যাঁদের প্রশ্ন করার কথা ছিল বা জানবার কথা ছিল, তাঁরা সেই বিষয়ে অবগত নন। ফলে একটা ক্ষতি হচ্ছে। তাঁদের তো প্রশ্ন করার কথা ছিল বা জানার কথা ছিল যে, ইস্কন যেটা করছে সেটা কি আদৌ চৈতন্যদেবের ধারা, না অন্য কিছু? তাঁরা কিন্তু সেই কাজ করছেন না। ভক্তিধারা মাত্রই মানুষকে আকৃষ্ট করে, ভক্তির ধারা মানুষকে পরস্পর থেকে আলাদা করে না। এর প্রথম পর্যায়ে আসে মৈত্রী, তারপর আসে সঙ্গ। আমি আপনার সঙ্গে একই অনুমান ও একই চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যখন কথা বলি, তাকেই বলে সঙ্গ। পরস্পরকে জানার এই প্রয়াসকে আরও গভীরে নেবার নাম, ‘সাধুসঙ্গ’। যেখানে আমাদের বাইরের আবরণ খসে পড়ে, আমাদের সর্বজনীন সহজ মানুষের রূপটা প্রকাশিত হয়। ‘সাধুসঙ্গ’ তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারি। যখন আমরা একই ভাষা ও চিন্তার বর্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠি।
নবপর্যায়ে ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকার চলমানতার মাঝেই নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে বাংলাদেশ। নতুন করে দেশগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শূদ্র ও মজলুমের বঙ্গদেশের পূর্বপ্রান্ত, যা আজকের বাংলাদেশ, এই ভূমি বারবার ইতিহাস তৈরি করেছে। ইতিহাসের অগ্রসরতা এ মাটিতে কখনোই স্থবির হয়ে যায় নাই। লাখো লাখো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে একাত্তরে যে স্বাধীনতা বাংলাদেশের মানুষ অর্জন করেছিল, অচিরেই তা বেহাত হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেই বেহাত হয়ে যাওয়া স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনতে, একাত্তরের অমীমাংসিত গণসার্বভৌমত্ব, সাম্য, ইনসাফ ও সহাবস্থানের বুনিয়াদি ধারণাগুলিকে কার্যকরী রূপ দিতে আবারও হাজারো ছাত্র-জনতা তাঁদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী রাজনীতির যাত্রামুখে পূর্ণচ্ছেদ বসিয়ে বঙ্গের পূর্বপ্রান্তের গণমানুষের অনন্ত অভিযাত্রামুখের হদিশ দিয়েছেন। হাজারো তরুণ-অরুণরা অস্তাচলে গিয়ে ফের বাংলাদেশের পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্যোদয় ঘটিয়েছে। বিশ্বকে চমকে দিয়েছে কালো-বাদামি চামড়ার মজলুম ও শূদ্র জনতা আর ছাত্র সমাজ। ছাত্রদের নেতৃত্বে নয়া ইতিহাস লিখনের প্রস্তাবনা রচিত হয়ে গিয়েছে। এহেন ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে বড় বাংলার সাহিত্য পত্রিকা ‘প্রতিপক্ষ’ ফের প্রকাশিত হয়েছে। রক্তাক্ত জুলাইয়ের স্মৃতি, জুলাই অভ্যুত্থানের পর্যবেক্ষণ ও জুলাই বিপ্লবের নিরিখে পুনর্বার গঠনের অভিপ্রায়কে সঙ্গে করেই ভাষা আন্দোলনের মাস তথা রক্তপলাশের দ্রোহচেতনার দিনকালে আবারও পাঠকের দরবারে হাজির হতে চলেছে ‘প্রতিপক্ষ’-র মুদ্রিত সংখ্যা। কিন্তু বাংলাদেশের জনজাগণের এই নয়া কালপর্বে প্রকাশিত এবারের এই পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখার শুরু থেকে সেইসব খুন হওয়া শহিদ শিশু-কিশোর আর তরুণদের মুখ স্মৃতিতে ভাসছে। পরম সম্মান ও রক্তিম সালামে তাঁদের স্মরণ করছি। কিন্তু এই সকল শহিদদের প্রাণের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদী জমানার অবসানের পরেও বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কার ও রাষ্ট্রের কাঠামো মেরামতের যে কাজ চলছে, তা যেন গণমুখী, প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রতি দরদি হয়। এক হাতে সংঘর্ষ ও আরেক হাতে নির্মাণের প্রক্রিয়া যেন জারি থাকে। এমনটাই আমরা চাইব। আমরা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করব, স্বপ্ন দেখব আবহমান কালের পূর্ববঙ্গ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভক্ত বড় বাংলায় যাতে বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, আশা রাখব যেন বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার নয়া রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের অবকাঠামোয় সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ইনসাফ ও সাংস্কৃতিক বহুত্ব বিকশিত হয়।
বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তি দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের জাতিবাদী, গোত্রবাদী, পরিচয়বাদী রাজনীতির খাঁচায় বন্দি করে রেখেছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতিবাদের বাইনারির ভয়ঙ্কর খেলায় বড় বাংলার মানুষকে আবদ্ধ রেখেছিল বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট শক্তি। বড় বাংলার সাহিত্য পত্রিকা ‘প্রতিপক্ষ’ দীর্ঘদিন ধরেই এই পরিচয়বাদী রাজনীতির খাঁচাকে ভাঙতে তৎপর। ’২৪-এর গণঅভ্যুত্থান এক ফ্যাসিস্ট শক্তিকে উৎখাত করেছে। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী আওয়ামী লীগ আজ বাংলাদেশে প্রায় নেই হয়ে গেছে। যে ‘জয় বাংলা’ মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান ছিল, তাকে কার্যত ফ্যাসিস্ট স্লোগানে পরিণত করেছিল আওয়ামী লীগ। এখন বাংলাদেশের মাটিতে শোনা যাচ্ছে বিপ্লবের স্লোগান ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’। কিন্তু নতুন করে মুসলিম জাতিবাদী শক্তির উত্থান শুরু হয়েছে। এদিকে ভারতের মাটিতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারে বাংলাদেশ-বিদ্বেষ ক্রমশ বাড়ছে। এই বিদ্বেষ পরিণত হচ্ছে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, অসম আর ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্কের সেতু হিসাবে কাজ করতে তৎপর ‘প্রতিপক্ষ’। এই সম্পর্ক ভাবগত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক প্রতিনিয়ত যোগাযোগের সম্পর্ক। বড় বাংলার সাহিত্য পত্রিকা ‘প্রতিপক্ষ’-ই সেই সম্পর্কের সেতু হিসাবে কাজ করবে। এই সম্পর্ক আদানপ্রদানই হয়ে উঠবে সমস্ত বিদ্বেষ ও পরিচয়বাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে হাতিয়ার।
বড় বাংলার সাহিত্যের স্লোগানকে সামনে রেখে পথচলা শুরু করেছিল ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকা। আন্তর্জালিক মাধ্যমে কোভিড পরবর্তী শ্লথ ও স্থবির সময়কালে নবপর্যায়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরবর্তীতে সীমিত পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে একটি মুদ্রণ সংখ্যা প্রকাশের চেষ্টা করেও তা সার্বিক হয়নি সাংগঠনিক সামর্থ্যের অভাবে। অবশেষে এই ২০২৫ সালে ভাষা সংগ্রামের মাস ফেব্রুয়ারিতে ও বাংলা দিনলিপির ফাল্গুনে ‘প্রতিপক্ষ’ মুদ্রিত হতে পারছে। এ জন্য বৃহৎ বঙ্গের পাঠক ও লেখকদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। যাঁরা না থাকলে টানা পাঁচ বছর পত্রিকা টিকে থাকতে পারত না।
এবারের আমাদের পত্রিকার মুদ্রিত সংখ্যার মূল ফোকাস ‘ ‘গণঅভ্যুত্থান’। ৫২-র ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ’৬৯ ও ’৭১-এর পরম্পরাকে ধরে রেখে চব্বিশের আবির্ভূত হওয়া সংক্রান্ত প্রবন্ধের পাশাপাশি এই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নানা দিক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। তার সঙ্গে রয়েছে ইতিহাস, বিউপনিবেশায়ন, ধর্ম, সমাজ, সিনেমা, প্রাণ-প্রকৃতি ও সাহিত্য পর্যালোচনামূলক গদ্য এবং একঝাঁক লেখক-কবির গুচ্ছ কবিতা ও গল্প। রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাক্ষাৎকার। মুদ্রিত পত্রিকা একুশের বইমেলার শেষ কয়েকটি দিন মেলাপ্রাঙ্গনে পাওয়া যাবে। মেলার পরে প্রতিপক্ষর ঢাকা ও কলকাতার দপ্তরে মিলবে আমাদের মুদ্রিত পত্রিকা। আশা করব, হে পাঠক, আপনি আমাদের সঙ্গে এহেন গদ্য-পদ্য-বাহাস-যুক্তি-তক্কো ও গপ্পোর ভিতর দিয়ে সম্পর্ক দৃঢ় করবেন। শুভেচ্ছা।