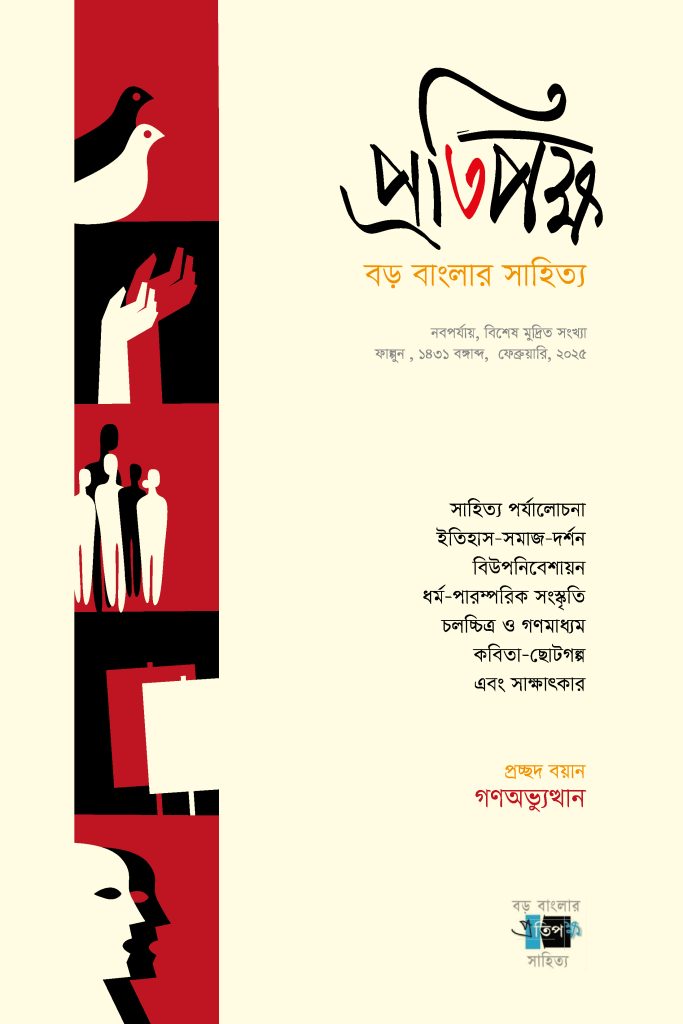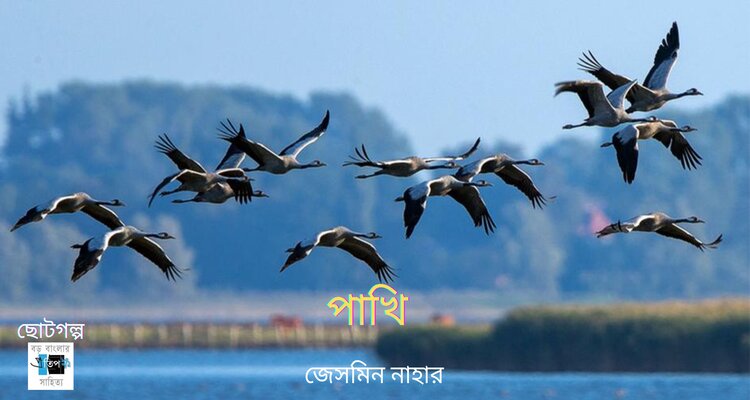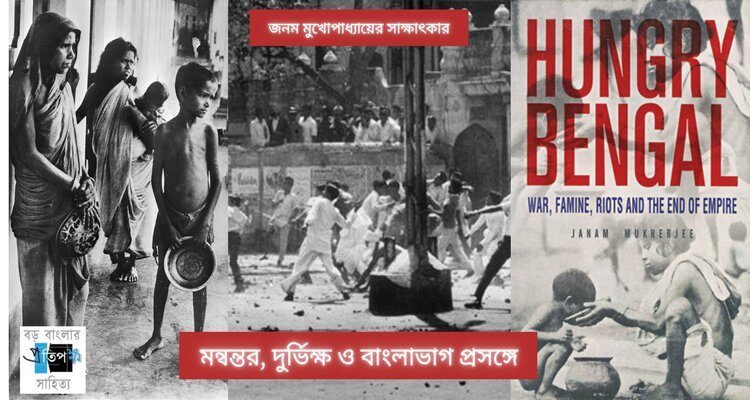।। মাহফুজ আলমের সাক্ষাৎকার ।।
মাহফুজ আলম। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামক বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের রাজনৈতিক মঞ্চের বিশিষ্ট মুখ। কোটা সংস্কার আন্দোলন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সামনের সারির নেতৃত্ব। এছাড়াও তিনি একজন চিন্তক ও সমাজকর্মী। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রতিপক্ষ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক অতনু সিংহ।

প্রতিপক্ষ: জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই বৈষম্যের উপাদন রয়েছে। আপনারা যখন বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন, কোথাও কি জাতিরাষ্ট্র কাঠামো বিনির্মাণের ভাবনা ছিল?
মাহফুজ আলম: জাতিরাষ্ট্র বিষয়ে আপনার প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটা বলতে হয়, সেটা এরকম যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভাবনার ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা হল বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও তার ক্রাইসিস। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের দরজা ধরেই এই দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তো এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে আমাদের একরকম ক্রিটিক ছিল। কারণ এই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করেই আওয়ামী লীগের ফ্যাসিজমের উদ্ভব হয়েছে। ফলত আমরা এই বিষয়টা নিয়ে একটু ক্রিটিক্যাল ছিলাম। যা-ই হোক, কাঠামোগত জায়গা থেকে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমরা হয়তো আন্দোলনের আগে অনেক আলোচনা করেছি, যেমন, বিউপনিবেশায়ন, প্রতিষ্ঠানিক বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনবান্ধব করে তোলা ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষয়গুলি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওইভাবে ফুটে ওঠেনি। তবে আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, যেটা বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট, ওইটার ব্যাপারে আমরা ক্রিটিক্যাল ছিলাম।
প্রতিপক্ষ: একাত্তরের উত্তরসূরী হিসাবেই চব্বিশ বাংলাদেশের ইতিহাসে হাজির হয়েছে, এ কথা বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সাতচল্লিশের প্রসঙ্গও উঠছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের অমীমাংসিত থাকা এবং মুক্তিযুদ্ধের অর্জন বেহাত হয়ে যাওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, সাতচল্লিশ ও একাত্তরে কোন কোন বিষয় অমীংসিত রয়ে গিয়েছে। তার ঐতিহাসিক মীমাংসা কীভাবে সম্ভব বলে মনে করছেন?
মাহফুজ: সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরের গল্পটা হচ্ছে, সাতচল্লিশের যে বাউন্ডারি সেটাই একাত্তর হয়ে উঠেছে, এবং সাতচল্লিশের বাঙালি মুসলমান আর নিম্নবর্গের হিন্দুদের লড়াইয়ের বদলেই কিন্তু এই দক্ষিণ এশিয়ার এই প্রান্তে এই ভূখণ্ড আমরা পাইছি। এই ভূখণ্ডে আমাদের যে মানুষের হিতকার্যের স্বপ্ন ছিল, তা পাকিস্তানের শাসকদের কারণে বাস্তবায়িত হয় নাই। লিঙ্গুইস্টিক পলিসি আর মিলিটারি পলিসির কারণে আমরা স্বাধীনভাবে মুক্তভাবে বাঁচতে পারিনি, ফলত আমাদের জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সকল জনগণ অংশ নিয়েছেন এবং অংশ নিয়ে সকল পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে একটা রিপাবলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করেছেন। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধ হওয়ার পরে মুক্তিযুদ্ধের যে সাম্য এবং সামাজিক সুবিচারের ধারণা ও বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করানোর স্বপ্ন, এই দুইটা বিষয়ই আসলে কম্প্রোমাইজড হয়ে গেছে। আমরা আওয়ামী লীগের দলীয় মূল নীতিকে রাষ্ট্রের মূল নীতি হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখি আর মুজিববাদের জয়জয়কার দেখি। যার ফলে এক ধরনের অন্তহীন ক্রাইসিস শুরু হয় বাংলাদেশের সোসাইটিতে এবং এক ধরনের ছদ্ম ইসলাম-বিরোধী, ইসলামোফোবিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাওয়ালপিন্ডির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আমরা দিল্লির হাতে গিয়ে পড়েছি। ফলে মুক্তিযুদ্ধ বেহাত হওয়ায় আমরা স্বাধীন হতে পারিনি। ইডিয়োলজিক্যালি আমাদের পুরা জনগোষ্ঠীকে গঠন করার যে সুযোগ ছিল, সেই সুযোগটা একটা দলকেন্দ্রিক হয়ে উঠল। ফলে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একটা ন্যাশনাল কনশাসনেসের ভিত্তিতে একত্রিত করতে পারিনি। আর অন্যদিকে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র না থাকায় আমাদের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হয়নি। এই দু’টি জায়গাতেই আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল জনগণের, সেটা ফেইল হয়েছে। আর মীমাংসার ব্যাপারে বলতে হয় যে এ জন্য আমাদের ইডি য়োলজিক্যাল জায়গাটা আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে, যাতে ইডিয়োলজিক্যালি এখানে যে ইসলামফোবিয়া আছে বা বাঙালি জাতীয়তাবাদের কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর যে এক ধরনের এলিয়েনেশন আছে, সেটাকে কাটিয়ে ওঠা আমাদের কাছে একটা বড় সংগ্রাম। একই সাথে ইসলামোফোবিয়াকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে, সকল জনগোষ্ঠীকে অ্যাকোমোডেট করা। অসাম্প্রদায়িকক চেতনাকে রক্ষা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই অ্যাট দ্য সেম টাইম অসাম্প্রদায়িকক চেতনার নামে ইসলামঘৃণার যে প্রকল্প, তাকে নস্যাৎ করা। ফলত এই দুইটা লড়াই আমাদের করতে হবে। আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের যে দৈনন্দিন ক্রাইসিস আছে, অর্থনৈতিক দিক অর্থাৎ চাকরিবাকরি, তার যে আরও দশটা সংগ্রাম আছে, ভূমি ইস্যু আছে, সরকারি অফিসগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করার চ্যালেঞ্জ আছে, এগুলিকে ডিল করা… রাষ্ট্রের অনেকগুলি অর্গ্যানকে ঠিক করতে হবে। এটা আমাদের জন্য মনে করি রাষ্ট্র গঠনের একটি প্রকল্প। তাছাড়া রাষ্ট্রগঠনের আরেকটা দিক হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল স্বাধীন স্বয়ম্ভূ হয়ে ওঠা এবং ইন্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের আরও প্র্যাগম্যাটিক হওয়ার পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব হিসসা বুঝে নেওয়া।
প্রতিপক্ষ: যোগেন মণ্ডলের ছবি দেখা গেল বাংলাদেশের বিজয় দিবসের মিছিলে। এমনকী সম্প্রতি বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তরফে যোগেন মণ্ডলের বিষয়ে একটি আলোচনাসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আপনার ফেসবুক প্রোফাইলের কভার ফটোতেও তিনি বিদ্যমান। আবুল হাশিম, ফজলুল হক ও হোসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পাশেই যোগেন মণ্ডল। তাঁকে আপনারা জাতীয় নেতাও বলছেন। অথচ পাকিস্তানের মন্ত্রী হওয়ার পরেও এক সময়ে তাঁকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন? আপনারা কি এক্ষেত্রে ইতিহাসের পর্যালোচনা ক্রিটিক্যালি করছেন?
মাহফুজ: যোগেন মণ্ডলের পাকিস্তান থেকে ভারতে ফিরে যাওয়া, এটা আসলে পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিষয়টিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। বিশেষ করে নিম্নবর্গের হিন্দু মুসলমানের যে সলিডারিটি কোয়েশ্চেন, তাকে পরাজিত করেছে। আমরা যোগেন মণ্ডলকে আমরা জাতীয় নেতা হিসাবে মানি কারণ যোগেন মণ্ডলকে আমাদের দরকার। তাঁকে আমাদের দরকার। আসলে আমাদের মৈত্রী কার সাথে হবে, এই বোধটা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি করার জন্যই যোগেন মণ্ডলকে আমাদের দরকার। যেখানে পুরা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ধরে নেন এক্সট্রিমিজম আছে বিভিন্ন রিলিজিয়নের, এছাড়াও সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস দক্ষিণ এশিয়ার জন্য হচ্ছে হিন্দুত্ববাদ। হিন্দুত্ববাদের যে এক ধরনের উত্থান, এই উত্থানটা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য ক্রাইসিস নয়, এটা দলিতদের জন্যও ক্রাইসিস তৈরি করবে। ভারতের যেসব জনজাতি আছে তাদের জন্যও ক্রাইসিস তৈরি করবে। গোটা দক্ষিণ এশিয়ার ক্রাইসিস হল হিন্দুত্ববাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদকে যদি ডিল করতে হয়, মনুবাদকে যদি ডিল করতে হয়, তবে বাংলাদেশে এক ধরনের সহানুভূতিশীল ইসলাম লাগবে। তাকে নিম্নবর্গের হিন্দুদের সাথে মৈত্রীর যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনার পাশাপাশি অতীতকে রিভিজিট করতে হবে। আমরা মনে করি এই কারণে আমাদের যোগেন মণ্ডলকে লাগবে। মৈত্রী ভাবনার জন্য এবং মৈত্রী অনুশীলন করার জন্য।
প্রতিপক্ষ: আপনাদের রাজনীতিকে কোন ক্যাটাগরিতে ফেলবেন আপনারা, নিম্নবর্গের ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশের গণসার্বভৌমত্বের রাজনীতি, নাকি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের নবনির্মাণ?
মাহফুজ: আসলে কোনও ক্যাটাগরিতে আমরা নিজেদের ফেলছি না। এটা বিশেষ করে বিগত ১০-১৫ বছরে আমাদের চিন্তা, মানে আমাদের প্রজন্মের। আমাদের পূর্বজ যারা আছেন, তাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে ক্রিটিক্যাল ছিলেন, তাঁরা নিম্নবর্গের পলিটিক্স করেছেন, সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন, অনেকে ইসলামি সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন, পালনবাদের কথা বলেছেন মওলানা ভাসানী। কিন্তু আমরা এই শাহবাগ, ওয়ার অন টেরর এবং আরও যে প্রকল্পগুলো গত ১৫ বছরে দেখেছি শেখ হাসিনার আমলে, তাতে আমাদের ভাবনাগুলো কোনো ক্যাটাগরিতে খোপবদ্ধ হয়নি। বলা ভালো আমরা খোপবদ্ধ করিনি। আমরা একটা ডিসকাশনে আছি, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে। অনেকের সঙ্গে আমাদের চিন্তার মিল আছে, অনেকের সাথে নেই। কোথাও আমরা হয়তো একটু বাম ঘেঁষা, কোথাও আবার আমাদের চিন্তাগুলো সাবেকি। কিন্তু এগুলোকে স্পেসিফিক্যালি কোনো ক্যাটাগরিতে আবদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, এবং কোনো নামকরণ করা হয়নি। এটা হচ্ছে গত ১০-১৫ বছরে আমাদের যা যাপিত জীবন, আমাদের প্রজন্মের এবং আমাদের পূর্ব প্রজন্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও উপলব্ধিকে সংশ্লেষ করে আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছাতে চাইছি, সেটা যাতে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে, রাষ্ট্রের ইডিয়োলজিক্যাল অ্যাপারেটাসকে অনেক বেশি জনমুখী করে তোলে। আর এইমাত্র যেটা বললাম যে একইসঙ্গে ইসলামোফোবিয়া আর সব ধরনের কমিউনাল ভায়োলেন্স, এই দুটোকেই আমরা প্রতিহত করে আগাতে চাই। আবার ধরেন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানকে আপনি কীভাবে একটি ইডিয়োলজিক্যাল প্লেনে ইনস্টিটিউশন বিলডিংয়ের জায়গায় নিয়ে আসবেন, তা নিয়ে চর্চা দরকার। এছাড়া পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রের মানুষের স্বার্থটাই প্রধান বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। আমাদেরও সেটাই ভাবনা। এছাড়া দেশের অর্থনীতিকে আরও বেশি করে গণমুখী করে তোলার ভাবনার ক্ষেত্রে কখনো কেউ কেউ বলছে আমরা একটু ডান দিকে, আবার অনেকে বলছে আমরা বামপন্থী, কেউ কেউ আবার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটও বলছে। ফলত আমরা কিন্তু আমাদের ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে শিখছি, আমাদের ভিন্ন তাত্ত্বিক বা দার্শনিক প্রস্তাবনাগুলোকে সামনে আনার চেষ্টা করছি। এগুলো সবই আমাদের পরীক্ষা। আশা রাখছি যে আমাদের চিন্তাগুলো অ্যাট সাম পয়েন্ট এক জায়গায় দাঁড়াবে। কিন্তু এটা কোনো গোষ্ঠী বা কোনো ক্যাটাগরিক্যাল জায়গা থেকে নয়।
প্রতিপক্ষ: রাষ্ট্র সংস্কার নাকি রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল বদল, কোনটি চাইছেন?
মাহফুজ: শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা দুনিয়াতেই রাষ্ট্র একটা গিভেন ক্যাটাগরি হিসাবে ধরে নেওয়া আছে যে এটাই আমাদের ভবিতব্য। নেশন স্টেট ইজ আ প্রাইমারি স্টেজ অফ হিসট্রি। তবে এটার বাইরে আমরা হয়তো কেউ কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ভাবি। কিন্তু আমরা যদি সামগ্রিকভাবে চিন্তা করি তাহলে বলা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ধরে আমরা এগোতে চাইছি। ফলে আমরা রাষ্ট্র সংস্কারের কথাই বলব এবং এই সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আসলে বিশাল রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীকে গঠনের কথাই বলব। যদি কখনো রাষ্ট্র কাঠামোর আমূল বদলের সুযোগ বা সম্ভাবনা হয়, সেটা যাতে আমরা এক্সপ্লোর করতে পারি, সেটার জন্যই দরকার আগে রাষ্ট্রটাকে গুছিয়ে নেওয়া।
প্রতিপক্ষ: একাত্তরের কথা আপনারাও বলছেন, বিএনপিও বলছে। ইন ফ্যাক্ট একাত্তরের কথা ঘুরে ফিরে সবাই নিজের মতো করে উত্থাপন করে। কিন্তু একাত্তরকে লালন করার পারিভাষিক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিগুলির মধ্যেই অনেক ফারাক আছে। মতাদর্শিক ক্ষেত্রেও তা বিদ্যমান। পারিভাষিক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগে ‘চেতনা’ শব্দটিকে যেভাবে ব্যবহার করত, আর আজ নতুনভাবে বিএনপি একাত্তরের যে আলাপ তুলছে, তার মধ্যে কি কোনো সাযুজ্য রয়েছে?
মাহফুজ: একাত্তর প্রশ্নে বিএনপির পোজিশন এবং আওয়ামী লীগের পোজিশনে অনেক ফারাক আছে। কিন্তু শত্রু নির্মাণের ক্ষেত্রে যেভাবে জামায়াত প্রশ্ন আওয়ামী লীগ নিয়ে এসেছিল, বিএনপি হয়তো রাজনৈতিক কৌশলের প্রশ্নে এটা নিয়ে এসেছে। শত্রু নির্মাণের বাইরে আমি মনে করি যেহেতু জামায়াতের একটি ভূমিকা আছে, প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা আছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে, ফলত এটাকে তো সবাই সমালোচনা করবেই এবং এটা খুবই ন্যায্য। কিন্তু এর বাইরেও বিএনপির একাত্তরের বিষয়ে আলাদা বক্তব্য, পোজিশন থাকা খুবই জরুরি। এখন আওয়ামী লীগের যে বয়ান, এই বয়ানের যে অনেকগুলো শাখাপ্রশাখা আছে, সেগুলো কোনোটাই বিএনপি এক্সপ্লোর করতে পারবে না। বিএনপি এগুলোকে যদি মেনে চলে বা এগুলো করতে যায়, তাহলে দেখা যাবে জিয়াউর রহমান যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করেছেন, নিজে যেভাবে সংবিধানে সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার সঙ্গে কিন্তু বিএনপির রাজনীতি সাযুজ্যপূর্ণ হবে না। ফলত বিএনপির আওয়ামী লীগ হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু জামায়াত প্রশ্নে ক্রিটিক্যাল হওয়া উচিত এবং প্রশ্ন তোলা উচিত। এবং শুধু জামায়াত নয়, বরং যারাই একাত্তরের গণহত্যাকে সাপোর্ট দিয়েছে, তাদের সবার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা উচিত, কিন্তু এই প্রশ্ন যেন বিএনপিকে না আওয়ামী লীগ বানিয়ে দেয়, সেটা মনে রাখতে হবে। আর সেটা মাথায় রেখেই বিএনপির উচিত বিএনপির রাজনীতিটাই করা।
প্রতিপক্ষ: সিপিবিকে অনেকেই আওয়ামী রেজিমের সাংস্কৃতিক এক্সেটেনশন হিসাবেই দেখেছে, বিষেশত শাহবাগ আন্দোলনের পর থেকে। বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সিপিবির ভূমিকাকে আপনারা কীভাবে দেখেছেন?
মাহফুজ: কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশের ভূমিকা আওয়ামী লীগের বৃহত্তর যে মুজিববাদী রাজনীতি, তারই একটা এক্সটেনশন বলে আমরা মনে করি। কিন্তু যেহেতু আমি একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে এখন আছি, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এভাবে বলতে পারি না। তো ওনাদের ভূমিকা কী ছিল এটা জনগণ জানে। কিন্তু আদর্শগত পোজিশন থেকে ওনারা বাহাত্তরপন্থী এবং মুজিববাদী রাজনীতিরই তল্পিবাহক। এবং অনেকাংশেই বাংলাদেশের ইতিহাসে তারা আওয়ামী লীগকে সাসটেইন করেছে। জামায়াতকে ঠেকানোর নামে, সাম্প্রদায়িকতা ঠেকানোর নামে তারা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিজমকে দীর্ঘায়িত করেছে।
প্রতিপক্ষ: শেখ মুজিবুর রহমানের জমানা থেকেই বিপ্লবী কমিউনিস্ট ধারা, যারা নিজেদের মূলধারার বামেদের সমান্তরালে নকশালপন্থী হিসাবে প্রচার করেছে, তাদের উপরে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বিভিন্ন সরকারের আমলেই চরম আকার নিয়েছে। সংগঠিতভাবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নকশালপন্থীরা আছেন কিনাও জানা নেই। আপনারা এদের ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন? সিরাজ সিকদারদের ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী?
মাহফুজ: বিপ্লবী কমিউনিস্ট ধারা প্রসঙ্গে বলতে বলতে হয়, বাংলাদেশের প্রশ্নে তাদের অনেকগুলো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছিল, সিরাজ সিকদারের সোভিয়েতের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উপর অনেকগুলো আলোচনা ছিল। কিন্তু আমরা মনে করি, একাত্তরের পরে যে বিপ্লবী কমিউনিস্ট ধারা বাংলাদেশে ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থী রাজনীতি ছিল, সেই রাজনীতিটা ভারতে যেহেতু তাৎপর্যপূর্ণভাবে আর নেই, তাই বাংলাদেশেও এর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না। বরং এই রাজনীতি অনেকাংশে বাংলাদেশে নৈরাজ্য তৈরি করেছে। এবং সিরাজ শিকদারের রাজনীতির যে খণ্ড খণ্ড অংশগুলি বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় আছে, তারা কিন্তু জনগণের রাজনীতি করে উঠতে পারছে না। এবং যেটাকে গণলাইন বলে, তাকে অবলম্বন করে তারা যে রাজনীতি করবে, তার কোনো উদাহরণও আমরা গত কয়েক দশকে পাইনি। বরং ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে নকশালপন্থীদের স্ট্রাগলকে পাঠ করাই ভালো, কিন্তু এখন এই রাজনীতির সম্ভাবনা আছে বলে আমরা মনে করি না। তাদের রাজনীতির অনেকগুলো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে যেগুলো বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের যে রাজনৈতিক ধরন বা সশস্ত্র সংগ্রামের যে প্রক্রিয়া, সেটা জনগণের সাথে সংযুক্ত বলে আমরা মনে করি না। মাওবাদী ধারা যে অর্থে সক্রিয় ছিল ষাট-সত্তর দশকে, সেটা তো আসলে দুনিয়ায়ও সেভাবে নেই, আর বাংলাদেশে তো সেভাবে নেই বটেই। আমি মনে করি এই রাজনৈতিক ধারা তিরোহিত হয়েছে সেই আশির দশকে। এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ-বিরোধী ইতিহাস হিসেবে সিরাজ সিকদার আলোচনায় উপস্থিত আছেন এবং থাকবেন।
প্রতিপক্ষ: বামপন্থীদের একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারা বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে থেকেছে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তাদের প্রতিনিধি নেই, কেন?
মাহফুজ: শুধু বামপন্থীদের নয়, ডানপন্থীদেরও বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারা ছিল। বিভিন্ন অংশের অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় বামপন্থীরা ছিলেন, শ্রমিক আন্দোলন করেছেন এমন মানুষ ছিলেন, মধ্যপন্থী্রা ছিলেন, দক্ষিণপন্থীরা ছিলেন। সাবেক ছাত্র শিবির করেছেন এমন ব্যক্তিরা ছিলেন, আলেম-ওলেমাদের সঙ্গে থাকা অনেকেই এই আন্দোলনে ছিলেন, সাবেক ডানপন্থী ও ইসলামপন্থীরা ছিলেন, তবে আলাদা করে একমাত্র বামপন্থীদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন এখানে নেই। এই পর্যায়ে যাঁরা আন্দোলনে ছিলেন এবং জনগণের আস্থাভাজন হয়েছেন, তাঁরা এসেছেন এবং তাঁরা হয়তো একটা সময়ে এখানে সরকারে প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তাঁরা মোটামুটি সর্বজস্বীকৃত এখনও পর্যন্ত।
প্রতিপক্ষ: বিপ্লবের ঘোষণাপত্র যারা বিপ্লব বা অভ্যুত্থান ঘটাল, তাদের বদলে বাংলাদেশ সরকার দেবে বলছে, এটাকে আপনি সরকারের বাইরে থেকে রাজনৈতিক কর্মী ও চিন্তক হিসাবে কীভাবে দেখছেন?
মাহফুজ: বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের যে ঘোষণাপত্র, সেই ঘোষণাপত্রের যে সময় সেটা পেরিয়ে এসেছে। ফলত এখন হয়তো এটা এক ধরনের রাজনৈতিক ঐকমত্যের দলিল হিসেবে যাচ্ছে এবং ঘোষণাপত্র নামে যাচ্ছে, কিন্তু সেই মোমেন্টামটা আসলে আমাদের সামনে নেই। ফলত এটি সরকার দিচ্ছে না, বরং সরকার ফেসিলিটেট করছে এবং জনগণের মধ্যে দিয়ে আসলে এটি প্রকাশিত হবে।
প্রতিপক্ষ: এতদিনকার মূলধারার রাজনৈতিক দল ও নানা পক্ষ কি ছাত্রদের স্বাধীন অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে?
মাহফুজ: এটি দৃশ্যমান যে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এই প্রজন্মের মধ্যে একটি ধন্দও তৈরি হয়েছে। আমাদের যে পূর্ব প্রজন্ম, যাদের অনেক লড়াইয়ের ইতিহাস আছে, ওনাদের একটা বোঝাপড়া আছে। আর আমাদের গত ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী আমলে লড়াইয়ে কারও আট বছর, কারও দশ বছর, কারো বারো বছরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমাদের একটা বুঝ-জ্ঞান তৈরি হয়েছে। এই বুঝজ্ঞানের সাথে হয়তো ওনাদের বুঝজ্ঞান-বোধ সম্পৃক্ত নয়, সাযুজ্যপূর্ণ নয়। এক ধরনের কনফ্লিক্ট বা দ্বন্দ্ব আছে। যেহেতু পূর্ব প্রজন্মের লোকেরা সবক’টি প্রতিষ্ঠানে আছেন, ফলত ওনাদের প্রজন্মের এক ধরনের চাপ তো আমাদের প্রজন্মের উপরেও রয়েছে। আমরা মনে করি যে এই দুই প্রজন্মের এক ধরনের মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে নতুন বাংলাদেশের পথ পরিক্রমা তৈরি হবে।
প্রতিপক্ষ: আপনারা ইতিপূর্বে রাত জেগে মন্দির পাহারা দিয়েছেন, সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। হিন্দুদের স্বার্থের বিষয়টিতে আপনাদের কনসার্ন দেখা গিয়েছে, এক্ষেত্রে সনাতন জোটের আট দফা দাবিকে কীভাবে দেখছেন? আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার বিষয়টিতে আপনারা কী ভাবছেন?
মাহফুজ: হিন্দুদের ব্যাপারে যেটা হচ্ছে যে, আমি আমার জায়গা থেকে দুর্গাপুজোয় ছুটির ব্যাপারে নিজে অবস্থান নিয়েছি এবং সেটা আমার তরফ থেকে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয় থেকেই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। দূর্গাপূজার অনুদানও এবার দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছি। গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরের পর থেকে হিন্দুদের উপর দুর্ভাগ্যজনক হলেও কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তা এমনভাবে ঘটেনি যে আগস্ট মাসে যেরকম একসাথে অনেকগুলো জায়গা আক্রমণ হয়েছিল, বরং অল্প কিছু জায়গায় হামলা হয়েছে এবং আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি এবং দেখা গেছে যে দুটি সপ্তাহের মধ্যে আর কোনো হামলা হচ্ছে না। সুতরাং আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, ফলত হামলার পরিমাণ অনেক কমে এসেছে। আমাদের ব্যবস্থার ফলে মামলা হচ্ছে এবং যারা হিন্দুদের উপর হামলা করেছেন তাদের গ্রেফতারি, বিচারকার্য চলছে। এবং এখানে যেহেতু আদিবাসী নৃগ্রোষ্ঠীর বিষয়ে একটি তর্ক আছে, আমাদের রাষ্ট্রের সাংবিধানিক এবং আইনগতভাবে একটি তর্ক হয়ে গেছে। অধিকারের প্রশ্নে যদি বলেন তাহলে আমাদের বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনের তরফ থেকে আমরা বলব যে, সকল নাগরিকের অধিকারই সমান থাকবে। এবং নাগরিক অধিকারের জায়গাতেই কারও জাতপাত-ধর্ম-লিঙ্গ ইত্যাদি কোনোভাবে ভূমিকা রাখবে না। আর আট দফা দাবি অধিকাংশই আমরা মনে করি যে সরকার সদিচ্ছা রেখেছিল। আমি নিজে যখন বৈঠক করেছি আমি বলেছিলাম যে, ধারাবাহিকভাবে এই আট দফা দাবি পূরণের ক্ষেত্রে সরকার ভূমিকা রাখবে। কিন্তু দেখা গেছে যে আট দফা দাবির বাইরেও এখানে একটি বৃহত্তর রাজনীতি আছে। এবং রাজনীতিটা আসলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য অনুকূল না। আমরা দেখেছি যে এখানে অনেকগুলো সংঘাত, সহিংসতার ঘটনাও ঘটছে। কিন্তু আট দফার ব্যাপারে আমরা আন্তরিক ছিলাম। কিন্তু আমি নিজে যখন কয়েকবার দেখা করেছি, কথা বলেছি তাদের সাথে, যারা আট দফা দাবি পেশ করছেন, আমি বলেছি যে ধীরে ধীরে যতদিন এই সরকার আছে, আমি এই দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা চালাব।
প্রতিপক্ষ: বিত্তবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য ও সম্প্রদায়িক বৈষম্য তথা জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে স্ট্রাগেলের ক্ষেত্রে বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কতটা কনসার্নড?
মাহফুজ: লিঙ্গ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, বিত্ত বৈষম্য, এইগুলো আসলে এত সহজে আমরা নির্মূল করতে পারব না। আমাদের হাতে অনেক কম সময়, আমাদের অনেকগুলো প্রস্তাবনা আছে। গত ১৫ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক যে বিশৃঙ্খলা আছে বা যেভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা রিঅ্যাক্টিভেট করা, এরকম অনেকগুলো চ্যালেঞ্জেস আছে। এর ভিতর দিয়ে আসলে এত বড় বড় যে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যগুলো আছে, সেগুলোকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে বিত্ত অথবা লিঙ্গ অথবা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যতগুলো জায়গায় বৈষম্যের প্রভিশনগুলো আছে, সেগুলোকে কীভাবে রেকটিফাই করা যায় তা নিশ্চিত করতে। যাতে এর ভিত্তিমূলটা তৈরি করে দিতে পারি যে যারাই সামনে ক্ষমতায় আসবে, তারা যেন এই বিষয়গুলোতে একটি জনগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং বৈষম্যগুলো দূরীভূত করতে পারেন।
প্রতিপক্ষ: ব্যক্তিগতভাবে আপনার চিন্তা ও সক্রিয়তায় বাংলার পারম্পরিক ঐতিহ্যের প্রভাব, ফকিরি-মুর্শিদি-বয়াতি ধারা, ইসলাম ও ’৪৭-পূর্বর্বর্তী সময় থেকে বঙ্গের নীপীড়িত-মজলুমের রাজনৈতিক অধিকারের স্ট্রাগলের ধারার ছাপ লক্ষ করা যায়। ইউরোপীয় তথা বৈশ্বিক বিপ্লবী ধারাকে কি আপনি এগুলির সঙ্গে মেলাতে চান? মানে রাজনীতির মধ্যে ঘরানা ও বাহিরানার মেলবন্ধন বা ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ক স্থাপন করতে চান? আপনার আইকন কারা?
মাহফুজ: আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়ায় যেটা মনে হয়েছে, আমি মনে করি যে বাংলা মানে শুধুমাত্র পূর্ব বাংলা নয়। পুরো বাংলাতেই এক ধরনের চিন্তা-দর্শন-ভাব-বুলি এসবগুলির মধ্যে এক ধরনের বিশিষ্টতা আছে। উপমহাদেশের, দক্ষিণ এশিয়ার চিন্তাপ্রক্রিয়া ও দর্শনগুলো থেকে এই অঞ্চলের মানুষের চিন্তা এবং মানুষের সক্রিয়তাগুলি খুবই আলাদা ধরনের। তো বৈশ্বিক যে বিপ্লবী ধারাগুলি আছে, যে পরিবর্তনকামী ধারাগুলি আছে, সেগুলির কাছ থেকে শিখতে চাই এবং তারা কীভাবে তাদের সমাজে পরিবর্তনে এনেছেন, তাদের নেশন বিল্ড করেছেন বা কীভাবে তাদের জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করেছেন, এইরকম অনেকগুলো ক্ষেত্রে তাদের থেকে আমরা শিখতে পারি। কিন্তু আমরা মনে করি বেঙ্গল বা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার, যা এখন বাংলাদেশ, এখানকার মানুষের এক্সপেরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতাগুলো খুবই ভিন্ন। কীভাবে আমরা জাতিগোষ্ঠী আলাদা করে গড়ে তুলব, নেশন আকারে গড়ে তুলব, তারপর আমরা কীভাবে তাদের ভেতরকার যে সভ্যতার কাছে চিন্তা বা ভাবনা আছে, সেগুলোকে কীভাবে ফুটিয়ে তুলব এবং আদর্শিক লড়াই আছে, সেই লড়াইগুলোকে আমরা এখানে কীভাবে, যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করব, সেগুলো বৈশ্বিক বিপ্লবী ধারাগুলোর থেকে শেখার আছে। আমাদের এখানে একটি নদীময় সহনশীল ইসলাম আছে। এখানে গাজিদের ধারা আছে, যারা জাতপাত-বিরোধী লড়াইয়ে হাজির ছিলেন। আবার এখানে সুফি ধারা আছে। মানে ইসলামের যুদ্ধংদেহি ধারা ও সহনশীল ধারা, এ দুই-ই হাজির আছে। ফলত এগুলোর থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আবার এখানে অনেকগুলো জাতপাত-বিরোধী লড়াই হয়েছে। লালন শাহের ভূমিকা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া মওলানা ভাসানী আছেন। এখানে অনেকেই বেড়ে উঠেছেন, বৈশ্বি ক ধারাকে সংশ্লেষণ করেছেন নিজের ভিতরে। উপমহাদেশের সুফি ধারা বা ভাবান্দোলনের যে ধারণা, সেগুলোও বাংলা অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। ফলত এখানে এরকম অনেক কিছু বিশ্লেষিত ও ব্যাখায়িত হয়েছে, তাই আমরা চাই বৈশ্বিক চিন্তাসমূহকে স্থানিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এখানে ব্যাখ্যাত করতে এবং বিশ্লেষণগুলোকে স্থানিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেশকে, নেশনকে নতুনভাবে দাঁড় করাতে।
প্রতিপক্ষ: মওলানা ভাসানির পর রাজনৈতিকভাবে রবুবিয়াত বা পালনবাদের কথা একমাত্র ফরহাদ মজহারকে বলতে শোনা গিয়েছিল। এখন আপনাকেও রবুবিয়াতের কথা বলতে শুনি। ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্র কাঠামোয় প্রাণ-প্রকৃতি-পরমের মেলবন্ধন ও পালনবাদী রাজনীতির অভিমুখ তৈরি করা কি আদৌ সম্ভব?
মাহফুজ: সাম্প্রতিক সময়ে ফরহাদ মজহার বেশ জোরের সঙ্গেই রবুবিয়াত বা পালনবাদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আরও অনেকেই করেছেন, কিন্তু ফরহাদ ভাই-ই সবচেয়ে উচ্চকিত ছিলেন। এর আগে মওলানা ভাসানী এখানে মানে বাংলাদেশে এই আলাপ করেছেন। উপমহাদেশে মওলনা আজাদ সুবহানী এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এটার তো একটা বৈশ্বিক মাত্রা আছে। বৈশ্বিক জলবায়ু এবং প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের ওপরে যেভাবে হামলা, আগ্রাসন চলে, তার বিরুদ্ধে স্ট্রাগল কিংবা বিগ কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যে একটা লড়াই রয়েছে, রবুবিয়াত সেই স্ট্রাগলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মেলবন্ধন, মানুষ আসলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখবে, সেক্ষেত্রে রবুবিয়াত মুখ্য হয়ে ওঠে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও এই রবুবিয়াত ও পালনবাদের বিষয়টি ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আমি আসলে কীভাবে ভাবছি… আমি যেটাকে ব্যবহার করেছি ‘দায় ও দরদ’ দিয়ে। আমি একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছি। আমার ভিতরে দরদের অনুভব কীভাবে আছে আর দায়িত্বশীল আচরণ করছি কি না… এই বিষয়টাকে পালনবাদের এক্সটেইনশন হিসাবে আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছি, পালনবাদের রাজনৈতিক সংশ্লেষণের ভিত্তিতে। তবে আমি আগে যে বললাম যে জাতিরাষ্ট্র কাঠামো একটা গিভেন হিসট্রি, কিন্তু আমার এটাকে এন্ড অব হিসট্রি বলেও মনে হয় না। এর বিয়ন্ডে ইতিহাস আছে, সেটা হয়তো ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাব। তবে এখন যা পরিস্থিতি তাতে আমি মনে করি একটা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার প্রকল্প, শিক্ষার প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ; এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য যে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে মানুষ কীভাবে সম্পর্ক তৈরি করবে সে ব্যাপারে তাদের সচেতন করা।
প্রতিপক্ষ: অনেকে ’৪৭-’৭১-’২৪ পরম্পরার মাঝে ’৭৫-কেও ঢোকাতেই চাইছেন। মেজর ডালিমের ইন্টারভিউ নেওয়া হল, সেখানে আবার ডালিমের আগের বয়ানেরও ভিন্নতা দেখা গেল অনেক ক্ষেত্রে। আপনাকে প্রশ্ন, সেনা অভ্যুত্থানের সঙ্গে কি গণঅভ্যুত্থান মেলানো যায়? ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার গণউন্মেষের সঙ্গে কি শেখ মুজিবুর রহামান-সহ তাঁর পরিবারকে হত্যা করার ঘটনা মেলানো যায়? শেখ মুজিব গণনেতা থেকে স্বৈরাচারে বদলে যান একথা ঠিক, কিন্তু তাঁকে রাজনৈতিকভাবে, মাস কনসেন্ট নিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করার বদলে সপরিবারে ব্যক্তিহত্যার ঘটনার সঙ্গে চব্বিশকে ইক্যুয়েট করা কি নাজায়েজ নয়?
মাহফুজ: বাকশাল ও দুর্ভিক্ষের কারণে গণঅভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি পঁচাত্তরে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু যেটা হয়েছিল তা হল সেনা অভ্যুত্থান। এক্ষেত্রে আমরা বলব, শেখ মুজিব-সহ তাঁর পরিবার, নারী ও শিশু হত্যা… আমরা স্পষ্টই বলতে চাই, নারী ও শিশুদের হত্যাকে কোনোভাবেই ন্যায্যতা দেওয়া যায় না। ফলত ওটি একটি ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড। এক্ষেত্রে আরও যেটা বলার তা হল, এ ধরনের অভ্যুত্থানগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্রতিহিংসার রাজনীতি হয়। সেটাই হয়েছে। আবার এই প্রতিহিংসার রাজনীতি শেখ হাসিনার ওপরেও ভর করেছিল। শেখ হাসিনা মূলত বাংলাদেশের জনগণের ওপর তাঁর বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছেন। যে কোনো প্রতিহিংসার রাজনীতিই একটা জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসে। শেখ মুজিবকে তাই গণঅভ্যুত্থান অথবা সেনা অভ্যুত্থান ফেস করতে হত, ওনাকে সরে যেতেই হত। কিন্তু যখন ওনার বাচ্চা অথবা নারীদের হত্যা করা হচ্ছে, সেটা একেবারেই মানবতা-বিরোধী অপরাধ, এটা কোনো যুদ্ধের নিয়মেও পড়ে না। আপনি কারও স্ত্রী, শিশুসন্তানকে হত্যা করতে পারেন না। তাই এক্ষেত্রে আমাদের জনগণের সাবালকের মতো চিন্তা করা উচিত যে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করার পরে শেখ হাসিনার মতো একজন ফ্যাসিস্টের উদ্ভব হয়েছে, উনি প্রতিহিংসা ও খুনকে ওনার রাজনীতির অভিষ্ট লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেছিলেন। আমি মনে করি, ফ্যাসিস্ট স্বৈরশাসককে ক্ষমতাচ্যুত করাটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়, কিন্তু তাঁর পরিবারের নারী ও শিশু সদস্যকে হত্যা করাটা মানবতা-বিরোধী কাজ। এটা নিয়ে উল্লাস করাটাও উচিত নয়। এই ধরনের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি একটি জাতিগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্তই করে। আমরা একাত্তরের আগে শেখ মুজিবের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে, আবার একইসঙ্গে বাহাত্তর থেকে তিনি যেভাবে স্বৈরাচার কায়েম করে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে নির্মূল করতে চেয়েছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে গুম-খুন করিয়েছেন, তার আমরা নিন্দা জানাব। দ্বিতীয়ত পঁচাত্তরে সঙ্গে চব্বিশকে কোনোভাবেই এক করে দেখা উচিত নয়। চব্বিশ সেনা অভ্যুত্থান তো নয়-ই। সেনা সদস্যরা শেষ পর্যায়ে আমাদের সমর্থন দিয়েছেন, ৪ আগস্ট। কিন্তু শেখ হাসিনার ব্যাপারে জনগণের ক্ষোভ তার আগেই তৈরি হিয়েছিল, তাঁকে দুই দিন বাদে হলেও ক্ষমতা থেকে সরতে হতই। আর চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের সহযোগিতায় হয়েছিল, সেটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এবারেই প্রথম যে কোনো অন্য রাষ্ট্র, কোনো গ্রুপ, কোনো ভেস্টেড ইন্টারেস্টধারী অংশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটা পুরোপুরি জনগণের অভুত্থান। গ্রাম থেকে শহর, ধার্মিক থেকে নাস্তিক , ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা-সিপাহি, সবার অভ্যুত্থান ছিল এইটা। এই ঘটনার সঙ্গে ’৭৫-কে কোনোভাবেই মেলানো যায় না। আর ৭ নভেম্বর যে সিপাহি-জনতার বিপ্লব ঘটেছিল, সেটা হচ্ছে মুজিববাদী প্রতিবিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য জনগণের এগিয়ে আসা। কিন্তু চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশে প্রথম। এই গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে পঁচাত্তরকে ইক্যুয়েট করা যায় না।
প্রতিপক্ষ: জামায়াতের নেতা বললেন শাহবাগীদের বিচারের আওতায় আনা দরকার। কিন্তু এই যে ট্যাগিয়ে দেওয়ার রাজনীতি, যা আওয়ামী জমানায় যে কোনো বিরোধী কণ্ঠস্বরকে জামায়াত বলে ট্যাগিয়ে দেওয়ার মতো, কীভাবে দেখেন বিষয়টিকে? ইডিয়োলজিক্যাল বহুত্ব নাকি বাংলাদেশের দরজা কোনো কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে আপনারা? কোনটা?
মাহফুজ: আমাদের যেটা দরকার, তা হল আমাদের মতাদর্শ-উত্তর রাজনীতি। আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশ একটি মতাদর্শ-উত্তর রাজনীতিতে বা পোস্ট-ইডিয়োলজিক্যাল পর্বে ঢুকে পড়েছে। আসলে পোস্ট-ইডিয়োলজি তো এক ধরনের দীর্ঘ লড়াইয়ের বিষয় বা পোস্ট-ইডিয়োলজি বলতে যেটা বুঝায় সেটা আসলে নতুন ইডিয়োলজির দিকে আগাবে। মূলত পুরোনো যে ইডিয়োলজি, যেগুলো বিবদমান ছিল, যেগুলো দ্বান্দ্বিক সেগুলোকে আমরা মনে করি যে কীভাবে কাটছাঁট করা যায় বা কীভাবে কমিয়ে আনা যায়। যেমন: বাকশালে এক ধরনের ইসলামফোবিক, একধরনের ভারতপন্থী রাজনীতি আছে। এ কারণে সে এখানে পাকিস্তান-বিরোধী বা জামায়াত-বিরোধী রাজনীতি এভাবে করে। এবং জামায়াতকে পাকিস্তানের সাথে ইক্যুয়েট করে, আবার জামায়াত ভারতের সাথে ইক্যুয়েট করে। এরকমভাবে অনেকগুলো রাজনীতি আছে যেগুলো আদর্শিকভাবে দন্দ্ব তৈরি করে, এটা নির্মূলের রাজনীতি, যেমন শাহরিয়ার কবিরের নাটক দ্বারা… এটা নির্মূলীকরণের রাজনীতি। নির্মূলীকরণ রাজনীতি কোনো সভ্য সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর, তা প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি এবং এক ধরনের গৃহযুদ্ধ তৈরির প্রকল্প। আমরা বাংলাদেশে কোনোরকম গৃহযুদ্ধ তৈরির পরিস্থিতি দেখতে চাই না। এবং গৃহযুদ্ধ তৈরির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে মুজিববাদ। আমরা সেটার বিরোধিতা করেছি, এবং আরও করব বিরোধিতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে মুজিব বাহিনী থেকে যারা এসেছেন, সবাই মিলেই সংকটটা তৈরি করেছেন। আর জামায়াত প্রশ্নে যেটা বলার— জামায়াতের যে ভূমিকা তা স্পষ্ট করা উচিত। স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া উচিত। তাদের গণতান্ত্রিকভাবে আরও উপস্থিতি নিশ্চিত করা উচিত। কিন্তু এই ট্যাগের রাজনীতি কোনোভাবেই থাকা উচিত না। বরং মুজিববাদ, বা যে ধরনের রাজনীতি এক ধরনের বিভাজন তৈরি করেছে, তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। এবং এমন এক জায়গায় আসা উচিত যেখানে গৃহযুদ্ধের রাজনীতি না থাকে। আমরা মূলত নির্মূলীকরণ রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছি। এই রাজনীতি বিভিন্ন ফাংশন, বিভিন্ন ধরনের ডান, বাম, মধ্য রাজনীতি থাকবে, সেটা থাকতেই পারে। কিন্তু কোনোভাবেই সেটা যেন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভাগাভাগি না হয়, নির্মূলীকরণ রাজনীতি না হয়, এক ধরনের হত্যাযজ্ঞের রাজনীতি না হয়। এটাই আমাদের আদর্শিক লড়াই, এটা থাকবে। এটি একটা রক্তপাত পর্যায় দিয়ে পার হয়েছে। এটা তাত্ত্বিক এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি দিয়ে পোক্ত হবে। কিন্তু এটা এখনই পোক্ত হবে না। এটা ঘটা শুরু হয়েছে মাত্র। এটা এমন এক জায়গায় পৌঁছাবে যেখানে আগের রাজনীতি আর কাজ করবে না। নতুন কিছু, নতুন আদর্শিক লড়াই তৈরি হবে।
প্রতিপক্ষ: গোদিমিডিয়া বা মোদিফায়েড মিডিয়া গণঅভ্যুত্থানকে যেভাবে বিকৃত করে আওয়ামী ন্যারেটিভে প্রচার চালাচ্ছে ভারত জুড়ে, চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতের বাংলা প্রদেশগুলির পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের গণমানুষের সম্পর্কের সেতুকে ধ্বংস করতে, সেই চেষ্টায় বা হাসিনাকে পুর্নবহাল করার চেষ্টাগুলিকে সফল করে দিতে বাংলাদেশের ভিতর থেকেও কি কেউ কেউ তৎপর?
মাহফুজ: বাংলাদেশে যারা মূলত বাংলাদেশে থেকেও ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্য অবশ্যই সক্রিয় আছেন। এবং বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে দেশ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ অপপ্রচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন। এটা আমরা খেয়াল রাখছি আর বাংলাদেশের সাথে যে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো আছে, সেখানে জনগোষ্ঠীর সাথে জনগোষ্ঠীর সুসম্পর্ক খুবই দরকার এবং তাদের সাথে আমাদের বোঝাপড়া আছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া আছে। এছাড়া ধর্মীয় পরিচয় ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিচয়ের বিভিন্ন সম্পর্ক আছে। আমরা এই সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে চাই। এবং যেভাবে হিন্দুত্ববাদীরা চায় না যে আমরা বাংলাদেশের চারপাশের জনগোষ্ঠীর সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং তাদের সাথে আমাদের লেনাদেনা হোক। তারা চায় এগুলো নস্যাৎ করতে এবং বাংলাদেশের চারপাশে যে বাঙালি জনগোষ্ঠী আছে— পশ্চিম বাংলায়, আসামে, ত্রিপুরায়, এবং আরও যেসব জায়গায় আমাদের বাঙালিরা বসবাস করেন, যাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ঝালাই করা উচিত। এবং আমাদের এই অভ্যুত্থানে, বিশেষ করে কলকাতার যারা তরুণ ছাত্ররা আমাদের সাহায্য করেছেন, সমর্থন করেছেন, তাদের সাথে আমাদের আরও সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করা উচিত। আর বাংলাদেশে থেকেও যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জণগণ অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে। এবং কখনো সরকারও পদক্ষেপ নিচ্ছে, নেবে।
প্রতিপক্ষ: পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বাংলা প্রদেশগুলির রাজনীতিকে কীভাবে দেখেন?
মাহফুজ: আমরা মনে করি ওখানে যারা জনগোষ্ঠী আছে, তারা ভারতের অংশ এখন এবং তাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে নাগরিক অধিকারগুলো আছে, সেগুলো ন্যায্যভাবে পাওয়ার জন্য যে গণতান্ত্রিক লড়াই আমরা বাংলাদেশে করেছি এবং আমাদের চেষ্টা আছে বাংলাদেশের জনগণের চেষ্টায় বাংলাদেশ বিনির্মাণের। ওনারাও করুন, ওনাদের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রতি সলিডারিটি থাকবে এবং ভারত রাষ্ট্রের ভেতরে যাতে জান, মালের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক এক ধরনের যে অধিকার আছে, সেটা নিয়ে যেন থাকতে পারেন— এই শুভকামনা থাকবে। এবং তারা তাদের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে আমাদের পাশে পাবেন, যেভাবে আমাদের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে তাদের পাশে পেয়েছি।
প্রতিপক্ষ: ভারতের গণমানুষের প্রতি কী বার্তা আপনাদের?
মাহফুজ: একই কথা যে, গণতান্ত্রিক লড়াই এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই অঞ্চলের মানুষের এক ধরনের গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারগুলো আছে, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো আছে; সেই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ ভারতের জনগণের সাথে দীর্ঘমেয়াদি মৈত্রী চায় এবং তাদের মৈত্রী আমরা কামনা করি। তাদের সাথে সুসম্পর্ক এবং সব ধরনের সম্পর্ক আমরা কামনা করি। এবং এই সম্পর্ক নস্যাৎ করতে যে প্রকল্প আছে—ভারতের ভেতরকার বিভিন্ন যে প্রকল্প আছে, ভারতের জনগণ যারা আছেন, তারা নস্যাৎ করে দিয়ে আমাদের কথাগুলো আমাদের কাছ থেকে শুনুন এবং আমরা তাদের কথাগুলো তাদের কাছ থেকে শুনি। তাদের সাথে আমাদের পরিষ্কার সম্পর্ক থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রতিপক্ষ: সামাজিক ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও পড়াশুনার পাশাপাশি আর কী করেন?
মাহফুজ: পড়াশুনা ও রাজনীতির বাইরে আর তো কিছু করি না। এখন একটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আছি, আগামীতে হয়তো আবার পড়াশুনা ও রাজনীতিতে ফিরে যাব।
প্রতিপক্ষ: আপনাদের আন্দোলন ও তার সাফল্যের পরে নানা জায়গায় রাজনৈতিক সংগঠনের গঠনগত জায়গায় উল্লম্ব বা ভার্টিকাল স্ট্রাকচার না হয়ে আনুভূমিক গঠন বা হরাজেন্টাল স্ট্রাকচারের কথা উঠে আসছে যা এতদিনকার কমিউনিস্ট, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিস্ট রাজনীতির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিকল্প, আপনারা কখনো পার্টি তৈরি করলেও কি ডেমোক্রেটিক সেনট্রালিজমের বদলে হরাইজন্টাল ডেমোক্রেসির ভিত্তিতেই দলের কাঠামো বানাবেন?
মাহফুজ: আমাদের লিডারশিপের এক ধরনের ডাইভার্সিটি থাকবে। আমাদের রাজনীতি যদি আমরা করি, রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আমরা মূল লিডারশিপ তৈরির দিকে মনোযোগ দেব। একটা সেনট্রাল লিডারশিপকে ঘিরে রাজনীতি, রাজনৈতিক আর্ট উৎপাদনের যে সংস্কৃতি আছে, সেটার বাইরে বেরিয়ে আমরা মোর ডিফারেন্ট নেতৃত্ব, সাংস্কৃতিক, সামাজিক নেতৃত্ব তৈরির জন্য চেষ্টা করব। জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করব— সর্বসাধারণের, সর্ব স্তরের জনগণের। এটা কোনো ব্যক্তিবিশেষের যেন না হয়ে যায়। বিভিন্ন লেয়ারে বিভিন্ন নেতৃত্ব আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব। বাংলাদেশে যে কয়েক দশক ধরে সংস্কৃতি পাড়ায় দক্ষ এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাব রয়েছে, সেটা আমরা কীভাবে পূরণ করব, সেখানেও আমাদের রাজনৈতিকভাবে একটা অগ্রাধিকার আছে।

সংগ্রহ করুন ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকার বিশেষ মূদ্রিত সংখ্যা। বাংলাদেশে অর্ডার করুন +8801627317743 নম্বরে। পশ্চিমবঙ্গে +9163571268 নম্বরে