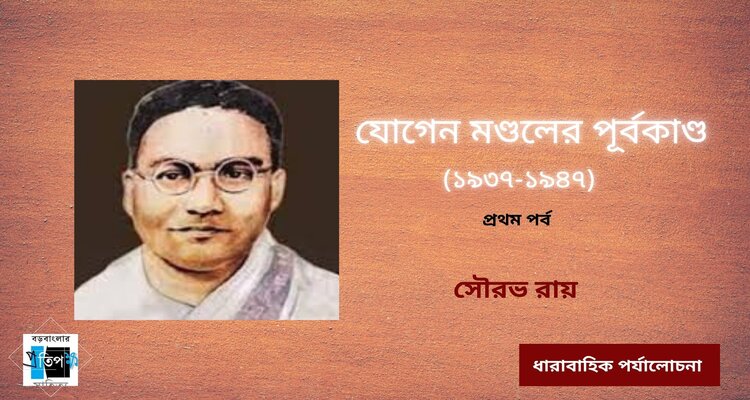।। ফরহাদ মজহার ।।
চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলাদেশের গ্রামে এখনও শিবপার্বতী আসেন। বাংলার শিব উত্তর ভারতের শিব নন। ইনি আগাগোড়া স্ত্রৈণ, পার্বতীর দাস। সাজুগুজু শিব-পার্বতী যুগলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো আর নৃত্য এখনও চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে দেখি। বিস্মিত হই। যখন বাবুরা আর সাহেবরা একদিকে জাতিবাদি হিন্দু আর অন্যদিকে জাতিবাদী মুসলমান হয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, গ্রামের সাধারণ মানুষ সেই বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে সেই বিভাজন ঠেকাতে চাইছে। বিষাক্ত বিভেদের দাগগুলো আড়াল করে কিভাবে এখনও বাংলাদেশের মানুষ চৈত্রে শিব-পার্বতীর জন্য আকুল হয়, অবাকই লাগে! কতদিন টিকবে জানি না। বাংলাদেশের কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করতে করতে বুঝতে পারি সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে প্রতিরোধের নানান সাংস্কৃতিক চর্চা আবিষ্কার করে । বিশুদ্ধ বা ছহি ঐতিহ্য বলে কিছু নাই। গ্রাম বদলে যাচ্ছে দ্রুত। কিন্তু তারপরও চৈত্রে শিবপার্বতীর দল বাড়ি বাড়ি নেচে যায়, আবার সারারাত বয়াতি গানের আসরে নবী-রসুলদের জারি গান শোনে। ফজর নামাজের পর মসজিদ হয়ে বাড়ি ফেরে।
চৈত্র সংক্রান্তি, শিব ও দয়াল চাঁদ
বাংলা নববর্ষ পালন করার পক্ষে যে যুক্তি সাধারণত দেওয়া হয় সেটা হয় সাহেবদের অথবা মুঘল আমলের জমিদার-মহাজনদের যুক্তি। সাহেবরা ‘নিউ ইয়ার’ পালন করেন। ইংরেজি নববর্ষে তারা সকালে পরস্পরকে বলেন, ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’। এর একটা স্মার্ট ধ্বনিগত চমক আছে। চৌকস। অতএব আমাদের চামড়া বাদামি হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরও ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ বলবার একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। সাহেব হবার বাসনায় আমরাও ‘নববর্ষের শুভেচ্ছা’ চালু করলাম। বাংলা নববর্ষের চল হোল।
বাংলা নববর্ষ’ নামক আদৌ কি কিছু ছিল? সেটা কেমন ছিল? কারা করত? কোথায় ছিল? আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। সেটা ছিল না যে এমন নয়। ছিল, কিন্তু সেটা বাঙালির বা এই দেশের জনগোষ্ঠির নববর্ষ নয়। সেটা ছিল সুদখোর মহাজন ও ব্যবসায়ীদের দিবস। কার কাছে কি দেনা পাওনা তার হিসাব মিলিয়ে পুরানা খাতা বন্ধ আর নতুন লাল খেরো খাতা খুলবার দিন। জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের সংস্কৃতিও সংস্কৃতি। কিন্তু একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা শ্রেণির সংস্কৃতি। একালে তাকে সকলের সংস্কৃতি বলে চাপিয়ে দেওয়া একটা বিশেষ শ্রেণির আধিপত্য প্রমাণ করে। একালে জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের সংস্কৃতিকে সার্বজনীন দাবি করাটা রাজনীতি, সংস্কৃতি নয়। সেই জমিদার নাই, সেই সুদখোর মহাজনও নাই। কিন্তু বাংলাদেশে উপনিবেশের ঔরসে পয়দা হওয়া ‘বাঙালি’ বাবু ও বাঙালি ‘সাহেব’ আছে। তারাই এখন নববর্ষ করে, মঙ্গল শোভাযাত্রা করে। করুক। কিন্তু তারা দাবি করে এটাই ‘আবহমান বাংলার সংস্কৃতি’। এরপর তারা সংস্কৃতি, ইতিহাস বা ঐতিহ্য নিয়ে গুরুগম্ভীর তর্ক করে। যেমন, বাংলা সন প্রচলন করেছিল কে? শশাঙ্ক নাকি আকবর ? সাদা কথায় হিন্দু নাকি মুসলমান? চেনা জিনিস। কিন্তু বারবার ভেংচি কেটে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা কতো বিষ আমাদের ফণায় ধারণ করি।
গত ২০ -২৫ বছর ধরে আমি গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিয়ে কাজ করছি। দেখেছি বাংলা নববর্ষকে তারা জমিদার-মহাজনদের খাজনা আদায়ের দিন কিংবা সারা বছরের সুদের হিসাব মেলাবার জন্য যতোটা বোঝে তথাকথিত ‘বাঙালি সংস্কৃতি’ হিসাবে বোঝে না বললেই চলে। সংক্রান্তির পরের দিন ঘর ধোয়ামোছা, গরুকে গোসল করানো ইত্যাদি অনেক কিছু তারা করে বটে, কিন্তু তাকে ‘নববর্ষ’ নামক কোনো ধর্মীয়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উৎসব বলা যায় না। বরং চৈত্রের শুরু থেকে সংক্রান্তি অবধি নানান চৈতালি অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তির পর ঘর ধোয়ামোছা স্বাভাবিক কাজ বলেই গণ্য করে।
বাংলা নববর্ষ বানানো জিনিস। উপনিবেশের ঔরসে পয়দা হওয়া ‘বাঙালি’ এটা বানিয়েছে। তাতে অসুবিধা নাই। কিন্তু ইতিহাস ভুলে গিয়ে একে ‘সার্বজনীন বাঙালি’র দাবি করলেই মুশকিল বাঁধে। এই ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু এরাই আবার ‘বাঙালি’র সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বয়ান রচনার জন্য নিজেদের যোগ্য মনে করে। নিজ শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখবার জন্যই সেটা তাদের অবশ্য দরকার হয়ে পড়ে। ‘বাঙালির নববর্ষ’ নামক একটা বয়ান নিজ শ্রেণীর স্বার্থেই এদের বানাতে হয়েছে। তারপর সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা এখন দাবি করে, আমাদেরও ‘নিউ ইয়ার’ আছে। এই দেখ আমাদের বাংলা নিউ ইয়ার, বাংলা নববর্ষ।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষকদের শোষণ লুন্ঠন করে যে-অভিজাত জমিদার ও সুদখোর মহাজন শ্রেণি গড়ে উঠেছিল তাদের সংস্কৃতিও সংস্কৃতি, কিন্তুই এটা একটি বিশেষ বর্ণ ও শ্রেণীর সংস্কৃতি। বাংলাদেশের সকল বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ বা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি নয়। ‘সার্বজনীন বাঙালি’ নামক কোন ডুমুরের ফুল আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এই ভূগোলে ছিল না। জাত বর্ণ শ্রেণি লিঙ্গে বিভক্ত বদ্বীপে ‘বাঙালি’ নামক কোন বর্গ ছিল না। এটা গড়ে উঠেছে অনেক পরে। অতএব সাহেবদের অনুকরণে জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের নববর্ষও সকল বাঙালির ছিল না। বাঙালির ধারণা গড়ে উঠেছে অনেক পরে। এই জাতিবাদী ধারণা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে বর্ণ, জাত, লিঙ্গ ও শ্রেণীর পার্থক্য বেমালুম গায়েব করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। জাতিবাদ গভীরতর বিভেদ্গুলোকে আড়াল করে দেয়। তাই ঔপনিবেশিক কলকাতা শহর গড়ে ওঠা বাঙালিত্ব এবং তাকে কেন্দ্র করে অভিজাতদের যে বাঙালি সংস্কৃতি তার জাতিভেদ আছে, বর্ণভেদ আছে, সাহেবি বৈশিষ্ট্য আছে, শ্রেণি ও পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাস আছে। ইত্যাদি। সেই ইতিহাস মুছে ফেলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বাদ রেখে উচ্চ বর্ণের অভিজাতদের সংস্কৃতিকেই আমরা ‘বাঙালি সংস্কৃতি’ বলে দাবি করি। পাশ্চাত্য ‘রেঁনেসা’র নকল করে অভিজাতদের সংস্কৃতিকে ‘বাঙালির পুনর্জাগরণ’ বলা হয়। এর বিরুদ্ধে কাঁইকুঁই সমালোচনা হয়েছে বটে। কিন্তু কুকুরের লেজ সহজে সোজা হয় না। আজ অবধি এটাই চলছে।
নববর্ষের আবাহন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়ে। আবহমান বাংলার কেচ্ছা গাওয়া আমরা ঠাকুরের কাছ থেকে নতুন ভাবে শিখেছি। ।
‘দাঁড়াও আমার আঁখিরও আগে’
নতুন বছর। অতএব, ‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো… ইত্যাদি। যা কিছু ‘পুরাতন’, ‘জীর্ণ’, ‘আবর্জনা’ সব ‘যাক যাক’ – সব ‘নতুন’ করে শুরু হোক। ‘নতুন’-কে বরণ করা আর যা কিছু ‘পুরাতন’ তাকে আবর্জনা ও পরিত্যজ্য জ্ঞান করে ফেলেই যদি দিতে হয় তো বেচারা রবীন্দ্রনাথকেও ফেলে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকে না। তিনিও এখন ‘পুরাতন’। ফলে এখন ঠাকুরকে মহা আয়োজন করেই টিকিয়ে রাখবার দশা হয়েছে।
এখন নববর্ষে ব্যান্ড সঙ্গীতও ঢুকেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন গান লিখছিলেন তখন ব্যান্ড সঙ্গীতের হুল্লোড় ছিল না। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা ব্যান্ড সঙ্গীত দুটোর একটিরও বিপক্ষে নই। আমি গান পাগল মানুষ অতএব দুটোর প্রতি আমার সমান ভালোবাসা। এখানে আমি গানের বিচার করতে বসিনি। যে কথা শুরু করেছি তার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবার জন্য খানিক কোশেশ করছি মাত্র। যেমন ব্যান্ড সঙ্গীত ‘নতুন’ বলেই যদি ‘এসো এসো’ বলে বরণ করতে হয় আর ঠাকুর ‘পুরাতন’ বলে তাকে ‘যাক যাক’ বলে ফেলে দেবার নির্দেশ আসে তাহলে তো আমার খুবই অসুবিধা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার গড়ে ওঠার ইতিহাসের অংশ। তাকে আমি পুরাতন আর জীর্ণ বলে ফেলে দিতে আগ্রহী নই। কিন্তু তাঁকে বাঙালির সার্বজনীন ভাবাদর্শ ভাববারও কোন কারন নাই। জীবিত থাকলে তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সমর্থন করতেন কিনা সে ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তিনি হিন্দুত্ববাদী ভারতই চাইতেন। অতএব পুরাতনকে কোন পর্যালোচনা ছাড়া ‘জীর্ণ’ বলে পরিত্যাগ করা আর নতুনকে নির্বিচারে ‘এসো এসো’ বলা খুবই মন্দ একটি আদর্শ। এই বালখিল্যতা ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিরোধী। কিন্তু এই আদর্শই আমরা ঠাকুরের বরাতে নববর্ষে বারবার প্রচার করি।
তবু ঠাকুর আমার প্রিয়। হয়তো তার পেছনে শ্রেণীগত কারণ আছে। আমি দীনহীন দরিদ্র শ্রেণী থেকে আসি নি। হোক আমার বাড়ি নোয়াখালি। আমার বয়স যখন খুবই কম তখন মাঝে মধ্যে সকালে জামে মসজিদে ফজর নামাজের পরে যে গানটি গাইতে গাইতে নোয়াখালীর মতো একটি নিমশহরে অস্ফুট প্রভাতে ঘরে ফিরতাম সেটা ছিল, ‘দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে’। সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যা আমার প্রাণে সাড়া তুলেছে তাকে ‘আমার’ বলতে আমার অসুবিধা হয় নি। কিন্তু ‘আমার’ সংস্কৃতি সকলের সংস্কৃতি নয়, সার্বজনীনও নয়, এই হুঁশটুকু হারিয়ে ফেলা ঠিক না। ‘আমি’ কে? আমার জাতপাত শ্রেণি লিঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাকে সদাসর্বদা হুঁশিয়ার থাকা চাই।
আহ্ সেই সুবেহসাদেক। আকাশ খানিক অন্ধকার, অতঃপর লালাভ হয়ে উঠছে চতুর্দিক। ভাবতাম আমার ‘আঁখির আগে’ দাঁড়াবার জন্য আমি কাকে আবাহন করছি? কে দাঁড়াচ্ছে? সুবেহসাদেক থেকে শুরু করে যা ক্রমশ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে — অনির্বচনীয় মুহূর্তের সেই এক অস্ফূট এবাদত –যার স্মৃতির সঙ্গে গোটা মাইজদী কোর্ট আমার বুকের মধ্যে আজও খচিত হয়ে আছে। অতএব ঠাকুরকে আর যাই হোক ‘যাক্ যাক্’ বলে ফেলে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নতুন আর পুরাতনের ভেদরেখা টেনে একটিকে অন্যটির চেয়ে অধিক মূল্যায়নের যে ব্যাকরণ, রীতি, অভ্যাস বা দর্শন আমাদের চিন্তা অধিকার করে রাখে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার শিক্ষা আমি সুবেহসাদেক থেকেই নিয়েছি। সেই ভাবের মধ্যে সন্ধিক্ষণ বা সংক্রান্তির আলোছায়া; সেই না আলো না ছায়া এমন এক আনন্দ নিয়ে হাজির হয় যে নিজের অজান্তেই আমাদের ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। ডাকি, ডাকতে থাকি: ‘দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে’।
বহুদিন আগে কমল মজুমদারের ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ পড়বার সময় প্রথম বাক্যেই পড়েছিলাম যে, ‘আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বার আমরা প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। আলো ক্রমে আসিতেছে।…’। একটা শিহরণ হয়েছিল আমার। ভুলবার নয়।
মোঘলাই যুক্তি
বাঙালি সংস্কৃতির বয়ান তৈয়ার করবার তাগিদে বাংলা নববর্ষ পালন করবার পক্ষে মোঘলাই যুক্তির মূল কথা হচ্ছে সম্রাট আকবর বাংলা বছর চালু করেন সৌর বছর আশ্রয় করে। ঠিক। কিন্তু তিনি কাজটা করেছিলেন খাজনা আদায় করবার জন্য। জমির মালিকানা ও দখলদারির ওপর মোঘলাই শাসন কায়েম করবার দরকারে। ওখানে মোঘলাই খাজনাদারি কিভাবে বাঙালির আবহমান সংস্কৃতি হয়ে উঠল সেটার ব্যাখ্যা খুব একটা পাওয়া যায় না। আমি সাহেবও নই, মোঘলও নই। কিন্তু সাহেবি বা মোঘলাই যুক্তি দেখিয়ে বাংলা নববর্ষ নামক একটি ব্যাপার চালু হয়ে যাবে আর তাকে আমাদের ‘আবহমান বাঙালির সংস্কৃতি’ বলে মেনে নিতে হবে অতোটা উদার আমি হতে পারি না।
সবাই যখন বাংলা নববর্ষ বা বাঙালির (সাহেবি বা মুঘলিয়ানা) সংস্কৃতি নিয়ে মশগুল তখন চৈত্রসংক্রান্তি পালন করবার পক্ষে ওকালতি করে আমি ২০০৬ সালে একটা লেখা লিখেছিলাম ইংরেজি দৈনিক ‘নিউ এইজ’ পত্রিকায়। (Let Us Celebrate Chaitra Sangkranti) সেই লেখা বাংলায় বিশদ করে এখানে হাজির করবার ধৈর্য আমার হবে না। উৎসাহী পাঠক একটু ঘাঁটলে খুশি হব।লেখাটি তাদের আর্কাইভে এখন আছে কিনা জানি না। এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই লিখছি, তা এখানে একটু জানান দিলাম।
লেখাটিতে বাংলার ভাবান্দোলনের জায়গায় দাঁড়িয়ে সকলকে সংক্রান্তি পালনের আহবান জানিয়েছিলাম। যে দিকটার তাৎপর্য তুলে ধরে ওকালতি করেছি তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বাংলার ভাবে ‘সময়’ সংক্রান্ত ধারণা। এর কিছুটা ইশারা ‘সন্ধিক্ষণ’, ‘সংক্রান্তি’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মধ্যে পাঠক খানিকটা টের পেতে পারেন। একই ভাব ধরবার জন্য আমি যখন আরবিতে ‘সুবেহসাদেক’ বলি তখন অনেকের উশখুশ লাগতে পারে। এটাও ‘সন্ধিক্ষণ, ‘সংক্রান্তি’ ইত্যাকার সময়মূলক ধারণার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এটা মুসলমানদের শব্দ, অতএব পরিত্যজ্য — এই প্রকার নিকৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার চর্চাই ‘বাঙালি’ হবার সুবাদে আমরা করি।
অথচ আমাদের কাজ নিজেদের সাম্প্রদায়িক বিষ থেকে দ্রুত মুক্ত করা। দরকার বহু, বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাবে বাংলাকে নানান দিক থেকে যারা সমৃদ্ধ করেছে তাদের একই বন্ধনে বা সূত্রে গেঁথে নেবার চেষ্টা। বাংলাভাষী সকলকে নিয়ে একসঙ্গে ভাববার সম্ভাবনা তৈরি করা। কিছু কর্তব্য ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে; পুঁজিতান্ত্রিক গোলকায়নের যুগে নানান বাংলাভাষীদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের সামষ্টিক ভাষিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য অসম বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়বার জায়গাগুলো দ্রুত গড়ে তোলা দরকার। নিদেন পক্ষে একত্রে লড়বার জায়গাগুলো চিনে নেওয়া খুবই জরুরি। যদি সেটা বুঝতে পারি, তাহলে সংক্রান্তি আর ঔপনিবেশিক আমলের নববর্ষ নামক উৎসবের পার্থক্য বোঝা দরকার। ঋতুর পরিবর্তে সময়কে সরল রেখা হিশাবে ভাববার মধ্য দিয়ে আমরা কি হারাই সেই ক্ষতির খতিয়ান টানা খুবই দরকার। এটা নিছইকই সাংস্কৃতিক ঝড়াবিবাদ নয়, পুঁজিতান্ত্রিক গোলকায়নের যুগে টিকে থাকার প্রশ্ন।
চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলাদেশের গ্রামে এখনও শিবপার্বতী আসেন। বাংলার শিব উত্তর ভারতের শিব নন। ইনি আগাগোড়া স্ত্রৈণ, পার্বতীর দাস। সাজুগুজু শিব-পার্বতী যুগলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো আর নৃত্য এখনও চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে দেখি। বিস্মিত হই। যখন বাবুরা আর সাহেবরা একদিকে জাতিবাদি হিন্দু আর অন্যদিকে জাতিবাদী মুসলমান হয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, গ্রামের সাধারণ মানুষ তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে সেই বিভাজন ঠেকাতে চাইছে। বিষাক্ত বিভেদের দাগগুলো আড়াল করে কিভাবে এখনও বাংলাদেশের মানুষ চৈত্রে শিব-পার্বতীর জন্য আকুল হয়, অবাকই লাগে! কতদিন টিকবে জানি না। বাংলাদেশের কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করতে করতে বুঝতে পারি সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে প্রতিরোধের নানান সাংস্কৃতিক চর্চা আবিষ্কার করে । বিশুদ্ধ বা ছহি ঐতিহ্য বলে কিছু নাই। গ্রাম বদলে যাচ্ছে দ্রুত। কিন্তু তারপরও চৈত্রে শিবপার্বতীর দল বাড়ি বাড়ি নেচে যায়, আবার সারারাত বয়াতি গানের আসরে নবী-রসুলদের জারি গান শোনে। ফজর নামাজের পর মসজিদ হয়ে বাড়ি ফেরে।
শিবের সঙ্গে প্রকৃতি ও কৃষিব্যবস্থার যে সম্পর্ক — সেটা নদীবিধৌত বাংলার একান্তই নিজের জিনিষ — উত্তর কিম্বা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ — এর মর্ম আমরা কখনই পুরাপুরি বুঝি নি, এখনও বুঝি কিনা সন্দেহ। শিবের জটা আঁচড়ে দিচ্ছেন পার্বতী, মেঘের আওয়াজ হয়ে গুরুগম্ভীর কাঁপছে নভোমণ্ডল, আর বৃষ্টির ধারা হিমালয় থেকে বাংলায় ধেয়ে আসছে পলিমাটি বুকে নিয়ে — এছাড়া কিভাবে বাংলার কৃষির বিকাশ সম্ভব! এরপর রয়েছে বঙ্গোপসাগরের তীরে মহেশখালির আদিনাথ পাহাড়ে গোরক্ষনাথ ও নাথপন্থীদের গল্প। সে এক বিশাল আখ্যান। শৈশব থেকেই তাদের স্মৃতি আমি বয়ে বেড়াই। সেই স্মৃতির দাগ অনুসরণ করে আমি নদিয়ায় যাই, ফকির লালন শাহকে দেখি। চিনি। মনে হয়, তিনি আমার সাত পুরুষের চেনা। আরও গভীরে খুঁজতে থাকি। অন্বেষণের আরম্ভে রয়েছে সেই এক দেবের দেব ভোলানাথের চিহ্ন। (লিঙ্গ বললে আজকাল আমরা দণ্ড বুঝি, অথচ এর মানে যে ‘চিহ্ন’ সেই বাংলা আমরা ভুলে গিয়েছি)। চিরকাল চিহ্নের তদন্তে আমার ইতিহাস থেকে পুরাণে স্তর থেকে স্তরে নেমে যাওয়া। অতলে। আরম্ভে। তাকে সন্ধান করা যিনি বিষ পান করে ‘নীলকন্ঠ’ হয়েছেন। সাগর মন্থনে উঠে আসা বিষ গিললে মৃত্যু, আর উগরে দিলে সৃষ্টির ধ্বংস: প্রাণের বিনাশ। কন্ঠে বিষ ধারণ করে শিব সমগ্র সৃষ্টি ও সকল প্রাণের হেফাজত করছেন। বিষে তাঁর কণ্ঠ নীল, আর সেই কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে আছে ঠাণ্ডা সরিসৃপ। এই সেই শিব যিনি প্রকৃতি ও প্রাণের গ্রন্থি। মহেশ্বর। এই সেই চিহ্ন যা জন্ম ও মৃত্যুর ভেদ রেখা।বাংলার এই শিব কোন সম্প্রদায়ের নন, কারণ সকল প্রাণের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন বলেই তিনি দেবের দেব মহাদেব।

আমি ইংরেজ বা আরব নই। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা আমার মাতৃভাষা নয়। আমার ভাষা বাংলা। ইংরেজি, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ ইত্যাদি যে কোন ভাষা থেকে ধার করতে আমার কোন লজ্জা নাই। কিন্তু ভাষাটা বাংলা। ধর্মসূত্রে এবং মুঘল শাসনের কারণে আরব ও পারস্য সভ্যতার সঙ্গে আমাদের যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ঘটেছে তাকে আমরা রাবার দিয়ে মুছে ফেলতে পারি না। যেমন, ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসকেও নয়। কিন্তু বাংলাভাষাকে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু, জর্মন, ইংরেজি হলে চলবে না। ঠিক। কিন্তু খাসিলত অনেকের এখনও বদলায় নি। সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ আহরণকে আমরা স্বাভাবিক গণ্য করি, এমনকি হরদম ইংরেজি ব্যবহারেও আপত্তি করি না। কিন্তু আরবি, ফারসি বা উর্দু থেকে শব্দ আহরণকে কানা চোখে দেখি। এটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। অন্য ভাষা ও ভাব আমার ভাষা ও ভাবের মধ্যে আত্মস্থ করবার শক্তি অর্জনের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও ভাবের বিকাশের সমূহ সম্ভাবনা। বিশেষত যে সকল ভাষা ও ভাবের সঙ্গে ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় আমাদের যোগ ঘটেছে। জনগোষ্ঠি হিসাবে বিশ্বসভায় আমাদের দাঁড়াবার সম্ভাবনাও নির্ভর করবে আত্মস্থকরণ বা আত্মীকরণের মহিমা ও হিম্মতটুকু দেখাবার মধ্য দিয়ে।
বাংলা ভাষা ও ভাবের হজমি শক্তি প্রবল। পণ্ডিত আর সাহেবে মিলে যে বাংলা গদ্য দাঁড় করিয়েছে তাকে ‘প্রমিত’ বা একমাত্র ‘বাংলা’জ্ঞান করবারও কোনো যুক্তি নাই। রবীন্দ্রনাথও সেটা মানেননি। আমিও মানি না।
‘সময়’ সংক্রান্ত ধারণার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক আমি বাংলার ভাবের জায়গায় দাঁড়াবার জন্য হারাতে চাই না। সেটা হচ্ছে সময় একান্তই সরলরৈখিক ব্যাপার এই ধারণার আধিপত্য সম্পর্কে সবসময় হুঁশিয়ার থাকা। বাংলার ভাবে বছর আর ঋতুর পার্থক্য প্রবল। এই ভাব মোতাবেক বছর ‘নতুন’ হয় না, বরং ফিরে ফিরে আসে। প্রত্যাবর্তন করে। একই ঋতুরই বারবার আবির্ভাব ঘটে। অতএব বছর শেষ আর শুরুর মুহূর্তকে একই কালের আবর্ত বলে বিচার করবার যে শিক্ষা আমরা আমাদের ঐতিহ্যে পাই আমি তাকে ভুলে যেতে নারাজ। একালে তার উপযোগিতা কোথায়, কিম্বা কিভাবে সময়ের ধারণা নতুন করে বিচার করবার ইঙ্গিত বৃত্ত বা ঋতুর ধারণা থেকে পেতে পারি, তার প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ।
আধুনিক কালে ‘নববর্ষ’ বা বছর নতুন ভাবে আসে এই ধারণার আধিপত্যের মধ্যে আছি আমরা এখন। তাই নববর্ষ পালন অপরাধ নয়, কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তি ভুলে যাওয়া মহা অপরাধ। এর মুশকিল হোল যা চলে গিয়েছে বা যা ‘পুরাতন’ হয়ে গিয়েছে তাকে আবর্জনা বা বর্জনীয় গণ্য করা প্রবল হয়েছে। নতুনকে আবাহনের নামে পুরাতন বর্জনের যে-রাজনীতি আমি সে সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক থাকতে চাই। নববর্ষ বা নতুন বছর ঘটা করে পালনের কারনে চৈত্র সংক্রান্তি আমাদের স্মৃতি ও ইতিহাস থেকে মুছে যাবার উপক্রম হয়েছে। বাংলা নববর্ষের বিরুদ্ধে আমার নালিশের জায়গা এখানে।
নতুন বছর পালন পুরনা বছর পেছনে থুয়ে নতুন বছর উদযাপন। কিন্তু সংক্রান্তির উদ্দেশ্য জগত বা ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে গ্রহ নক্ষত্র ও প্রকৃতির মধ্যস্থতায় আমরা যে সম্বন্ধে নিত্যদিন যুক্ত থাকি সেই সম্বন্ধকে স্মরণ করা। সূর্যের রাশি পরিভ্রমণের বৃত্ত অনুসরণ করতে গিয়ে আকাশে সূর্যের গতিপথকেও জানা। চিত্রা আর বিশাখাসহ নানান নক্ষত্রের পরিচয় জানা। যদি আমরা সংক্রান্তি ভুলে গিয়ে শুধু নববর্ষ পালন করি তাহলে গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে যে সম্বন্ধে আমরা যুক্ত হতে শিখেছি সেটা আস্তে আস্তে আমরা ভুলে যেতে শুরু করি। ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা বড়সড় ছেদ ঘটে।
তাই অন্যে করলে ‘নববর্ষ’ করুক, সেখানে বাধা দেবার কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু বাংলা নববর্ষের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। বাধা দেওয়ার ফল কুফলই বয়ে আনবে। আগেই বলেছি, যা ‘নতুন’ তার বিপরীতে ‘পুরাতন’-কে প্রতিষ্ঠা করাও আমার রাজনীতি নয়। আমি বরং বছর বা ঋতুর এই ফিরে ফিরে আসার ভাবটা রক্ষা করতে বিশেষ ভাবে আগ্রহী। আবর্তের বা প্রত্যাবর্তনের এই ধারণা আমাদের ভাবে, জ্ঞানে ও সংস্কৃতিতে এমন একটা স্থান দখল করে আছে যার মূল্য অপরিসীম। একে আমি হারাতে নারাজ। সংক্রান্তি, বিশেষত চৈত্র সংংক্রান্তি তাই আমা্র কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যারা সাহেব হতে গিয়ে নববর্ষ পালন করতে চায় করুক, আমি চৈত্রের সংক্রান্তি পালন করতে চাই। সংক্রান্তির সংস্কৃতি ও ভাব হারিয়ে ফেললে আমি দরিদ্র হয়ে পড়ি। স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠি হিশাবে আমামদের নিজেদের কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। হারিয়ে ফেলি। জগতে বৈচিত্র্যের নিরাকরণ ঘটে। এটা ক্ষতি।
চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলাদেশের গ্রামে এখনও শিবপার্বতী আসেন। বাংলার শিব উত্তর ভারতের শিব নন। ইনি আগাগোড়া স্ত্রৈণ, পার্বতীর দাস। সাজুগুজু শিব-পার্বতী যুগলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো আর নৃত্য এখনও চৈত্র সংক্রান্তির সময় দেখি। বিস্মিত হই। যখন বাবুরা আর সাহেবরা এক দিকে জাতিবাদি হিন্দু আর অন্যদিকে জাতিবাদী মুসলমান হয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, গ্রামের সাধারণ মানুষ সেই বিভাজনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ সেই বিভাজন ঠেকাতে চাইছে। বিষাক্ত বিভেদের দাগগুলো আড়াল করে কিভাবে এখনও বাংলাদেশের মানুষ চৈত্রে শিব-পার্বতীর জন্য আকুল হয়, অবাকই লাগে! কতদিন টিকবে জানি না। বাংলাদেশের কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করতে করতে বুঝতে পারি সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে প্রতিরোধের নানান সাংস্কৃতিক চর্চা আবিষ্কার করে । বিশুদ্ধ বা ছহি ঐতিহ্য বলে কিছু নাই। গ্রাম বদলে যাচ্ছে দ্রুত। কিন্তু তারপরও চৈত্রে শিবপার্বতীর দল বাড়ি বাড়ি নেচে যায়, আবার সারা রাত বয়াতি গানের আসরে নবী-রসুলদের জারি গান শোনে। ফজর নামাজের পর মসজিদ হয়ে বাড়ি ফেরে।
তাহলে একটিকে অন্যটির বিপরীতে বসিয়ে অন্যটির তুলনায় অধিক মূল্যায়নের যে নীতি, মানদণ্ড, দর্শন বা ভাব তাকে পরিহার করবার কথাই বলছি। ঠিক। কিন্তু ভাব আর রাজনীতি তো এক কথা নয়। চৈত্রসংক্রান্তি পালন করার মধ্য দিয়ে মুঘল, ইংরেজ এবং একালের ‘সাম্রাজ্যবাদ’ আমাদের ভাবগত অবস্থান থেকে টলিয়ে দেবার যে প্রবল ধারা বজায় রেখেছে তার বিরুদ্ধেও তো দাঁড়ানো দরকার।
কেন দরকার? কারন চৈত্রসংক্রান্তি পালন করা না করা নিছকই ভাবের ব্যাপার মাত্র নয়, নিছকই সংস্কৃতি নয়। এটা রাজনীতি। আর যখনই আমরা রাজনীতির জায়গায় দাঁড়াই তখনই ভেদবিচার ছাড়া চলে না। যদি মোঘলাই, সাহেবি বা নব্য মধ্যবিত্তের সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাবগত বিকাশের পরিপন্থি এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিগঠনের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে তাহলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া পথ কই? দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক কারণেও আমাদের চৈত্র সংক্রান্তি পালন করা দরকার।
তবে, আরেকটি দিকও আছে।

নারীর জ্ঞানচর্চা ও ক্ষমতা
বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন সংক্রান্তি; সূর্য এক রাশি থেকে আরেক রাশিতে যখন গমন করছে তখন প্রতি মাসেই তার সংক্রান্তি ঘটে। সংক্রান্তি পালনের অর্থ তাহলে গ্রহ-নক্ষত্র ও বিশ্বনিখিলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একটা ব্যাপারও বটে। যে গ্রহ বা নক্ষত্রের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগ নাই, যাদের অধিকাংশকেই আমি কখনোই দেখিনি বা দেখব না, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার যে ভাব তার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই দিক থেকেও আবার চৈত্র মাসের সংক্রান্তির ভাব আলাদা। বসন্তের শেষে সূর্যের শেষ দাবদাহ জ্বালিয়ে দিচ্ছে সব। কিন্তু বিদায় নিচ্ছে চৈত্র। আসছে বৈশাখ আর ওর হাত ধরে মেঘ আর জল। জমিতে জো আসবে এখন, কৃষক নতুন আমন ধান লাগাবার জন্য তৈরি হবে। আর মেয়েদের কাজ? বিস্তর…।
সব কাজের সেরা কাজ হচ্ছে চৈত্রসংক্রান্তিতে প্রকৃতির খোঁজখবর নেওয়া। কৃষকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যে দিকটা আমাকে দারুণ আকৃষ্ট করেছে সেটা হচ্ছে প্রকৃতির খোঁজখবর নেবার ধরন; এই কাজটা বিশেষ ভাবে কৃষক মেয়েরা করে। কি করে খোঁজখবরের কাজটি করে তারা?
শহরে এই বয়েসী শিশু যখন বইয়ের বোঝা বহন করে ক্লান্ত, গ্রমের এই মেয়েটি তখন হাজার লতাপাতার ভিড় ঠেলে যে শাকটি তার দরকার সেটি ঠিকই চিনে নিয়ে তুলে আনতে সক্ষম। ধান গাছ সম্পর্কে পড়ে ধান গাছের বিদ্যা অর্জন করা যায় না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া। তেমনি চৌদ্দ রকমের অনাবাদী আবাদি/অনাবাদী একশ রকম শাকের নাম জানা লাগে, চেনার প্রয়োজন হয়, সর্বোপরি কিভাবে তূলতে হবে সেটাও শিখতে হয়। গোড়া সহ তুলে নিয়ে এলে আগামি বছর এই শাক আর পাওয়া যাবে না। এই ছোট মেয়েটি রীতমতো শাক বিশেষজ্ঞ। চৈত্র সংক্রান্তিতে তার কেন বিশেষ ভাবে তেলাকুচা দরকার, সেটাও সে জানে। খুম কম উদ্ভিদবিদ পাওয়া যাবে যারা চৈত্রে অনাবাদি শাকের নাম এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।
সংস্কৃতি একই সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চাও বটে, স্রেফ উৎসব নয়
বাংলার মেয়ে চৈত্রসংক্রান্তিতে শাক কুড়াতে বেরুবে। তাকে চৌদ্দ রকম শাক কুড়াতে হবে। ‘চৌদ্দ’ কথাটা আক্ষরিক অর্থে নিলে চলবে না। এর অর্থ যতো সংখ্যক পাওয়া সম্ভব। নানান ধরনের বিচিত্র সব শাক। আবাদি শাক নয় কিন্তু, অনাবাদী অর্থাৎ বনেজঙ্গলে আপনজালা শাক। ঘরের পাশে আলান পালান মাঠের আনাচে কানাচে কোনাকানচি থেকে তোলা শাক। বাংলার মেয়েকে সংক্রান্তি মুহূর্তে খবর নিতে হবে প্রকৃতির যে অংশ অনাবাদী – যে অংশ কৃষি সংস্কৃতির সংরক্ষণ করে রাখার কথা, নইলে প্রাণের সংরক্ষণ ও বিকাশ অসম্ভব – সেই অনাবাদী প্রকৃতি ঠিক আছে কিনা। যে সব গাছপালা, প্রাণ ও প্রাণী আবাদ করতে গিয়ে আবাদী জায়গায় কৃষক তাদের উঠতে দেয়নি, থাকতে দেয়নি, তারা সব কি ঠিকঠাক আছে?
এখানে ‘কৃষি’ বললে কথাটি পরিষ্কার করা যায় না। বলতে হয় ‘চাষাবাদ’। ‘চাষ করা’ এবং ‘আবাদ করা’। কৃষক ‘চাষ’ যখন করে তখন প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বা প্রাকৃতিকভাবে যে সকল শাক গাছপালা লতাগুল্ম বেড়ে ওঠে তাকে তার পরিষ্কার করতে হয়। তাদের বাদ দিয়ে সেখানে যে-জাত বা প্রজাতি কৃষক চাষ করতে চায় তারই বীজ বোনা হয় বা , তারই চাষ হয়। মানুষ নিজের ভোগের জন্য যে জাতি ও প্রজাতিগুলো দরকার তার চাষ করল কিন্তু যেসব জাত বা প্রজাতি সে মাঠে বাড়তে দিল না, তাদের কী হবে? ‘আবাদ’ করার অর্থ হচ্ছে যেসব জাত বা প্রজাতি চাষ করা হোল না তাদের প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত ভাবে রক্ষা করবার ব্যবস্থা রাখা, যাতে তারা নষ্ট না হয়, হারিয়ে না যায়। কৃষকের এখন যা দরকার তা চাষ করবার জন্য প্রকৃতির একটা অংশ ব্যবহার করতে হচ্ছে, অন্যদিকে প্রকৃতির অনাবাদী অংশে তাকে রক্ষা করতে হচ্ছে সেই সব জাত এবং প্রজাতি যারা আজ নয়, কিন্তু আগামী দিনে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণিকুলের প্রয়োজন। প্রাণের বেঁচে থাকার শর্ত। প্রকৃতির ব্যবহার এই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটাবে। কার প্রয়োজন? মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতি তো শুধু মানুষের জন্য নয়। মানুষের এখনকার প্রয়োজন মেটাবার জন্য ‘চাষ’ করলেও আগামির জন্য ‘আবাদ’ বা প্রাণের বিস্তৃত পরিমণ্ডলের ব্যবস্থাপনা কৃষককে করতে হয়। প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হয় যাতে প্রাণ ও প্রাণবৈচিত্রের ক্ষয় না ঘটে। প্রকৃতির আবাদি ও অনাবাদি দুটো দিককেই সমানভাবে চর্চা ও উভয়েরই ফলন ও প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে কৃষি সভ্যতা দাঁড়ায়। টিকে থাকে।
তাহলে চৈত্রসংক্রান্তিতে মেয়েদের চৌদ্দ রকম শাক খাওয়া তো আসলে সব রকম গাছপালা প্রাণ ও প্রাণীর হালহকিকতের খোঁজ নেওয়া। বাংলার মেয়ের ব্রত – পুরুষতান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে যার বিরোধ চিরকালের – সেই ব্রতের উপলক্ষ সপ্রাণ প্রকৃতি। সৃষ্টি থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন ভাবে ‘স্রষ্টা’ নামক কোনো কর্তাসত্তা নয়। স্রষ্টা আছেন, কিন্তু কল্পনা বা বুদ্ধির নির্মাণ হিসাবে নন, আছেন সৃষ্টির নিরন্তর প্রক্রিয়ায় – সপ্রাণ প্রকৃতির সপ্রাণতার অন্তর্গত হয়ে। তিনি কর্তা হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি তাঁর ‘অঙ্গ’ হয়ে সতত বিরাজমান।
‘পুরুষ পরওয়ারদিগার
অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তার
প্রকৃতি প্রকৃত সংসার সৃষ্টি সবজনা”
-ফকির লালন শাহ
নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রকৃতিতে মানুষের কৃষিমূলক হস্তক্ষেপ ও অনাবাদি জগতকে সাময়িক অপসারণের পরও সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার কর্তব্য থেকে যায় আমাদের। চৈত্রসংক্রান্তিতে অনাবাদি শাক কুড়ানো ও তার কদর প্রতিষ্ঠা সে কারণে জরুরী হয়ে পড়ে। তার মানে পুরুষ কৃষক কৃষি কাজ করতে গিয়ে প্রকৃতির এমন কোনো ক্ষতি করল কিনা, অনাবাদি জাত ও প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিনা সেই খবর নেবার জন্য ‘অনাবাদি’ শাকের খোঁজ পড়ে চৈত্রসংক্রান্তিতে। চৈত্রসংক্রান্তি সেই দিক থেকে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। চৈত সংক্রান্তি নারীর ক্ষমতা নিশ্চিত করবার দিন।
গণমানুষের সংস্কৃতি প্রকৃতি ও লোকায়তিক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলার নারীও পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছে নারীর আকিদা ও আমলের জায়গা থেকেই: দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া নানান ব্রত, মানত ও বিবিধ লুপ্তপ্রায় এবাদতের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতি, প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে বাংলার জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি এখানে অঙ্গাঙ্গি হয়ে বিরাজ করে। জীবন যাপন থেকে এই সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যদি আমরা প্রাণে বেঁচে থাকতে চাই তাহলে এই সংস্কৃতির এবাদতই আমাদের কাজ। কারণ শেষাবধি সকল প্রশংসা তাঁর যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে মানুষকে তার হেফাজতের দায়িত্ব দিয়ে মানুষকেই খলিফা হিশাবে ইহলোকে পাঠিয়েছেন। আগুনের তৈরি ফেরেশতা নয়, মাটির তৈরি মানুষ।
‘তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া
ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
তাই নূরের ফেরেশতা করে আদমকে সেজদা
সবার চেয়ে দিলে মাটির মানুষকে সম্মান
আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালু
শেষ করাতো যায়না গেয়ে তোমার গুণগান’।।
যে সত্য গ্রামের সাধারণ মানুষ সহজে বোঝে, তাদের গানে তাদের সুরে ও নিত্যদিনের চাষাবাদে যা মূর্ত করে তোলে সেই সত্যের ধারে কছেও শহরে নববর্ষ পালন করা শিক্ষিত শ্রেণি নাই। নিজেদের জ্ঞাঞ্চর্চার ধারা থেকে বিযুক্ত বলে হয়তো তাদের পক্ষে বোঝাও কঠিন। অথচ এই সত্যের উপলব্ধি এই কালে – পরিবেশ বিধ্বংসী সভ্যতার এই কলিকালে – আমাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছে। ‘বাঙালি’ বা ‘বাংলাদেশী’ হবার জন্য নয়, প্রকৃতির মধ্যে টিকে থাকার যে লড়াই – জীবের সে-লড়াইয়ের রাজনীতিকে সামনে নিয়ে আনার জন্যই দরকার চৈত্রসংক্রান্তি। এই বিষয়ে আমি ‘ভাবান্দোলন’ বইতে ‘কৃষি, ভাব ও কাব্য’ নিবন্ধে আমি আরও আলোচনা করেছি। এখানে আর কথা বাড়াব না। নতুন একটি প্রসঙ্গে যাবো।
এখানে ‘কৃষি’ বললে কথাটি পরিষ্কার করা যায় না। বলতে হয় ‘চাষাবাদ’। ‘চাষ করা’ এবং ‘আবাদ করা’। কৃষক ‘চাষ’ যখন করে তখন প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বা প্রাকৃতিকভাবে যে সকল শাক গাছপালা লতাগুল্ম বেড়ে ওঠে তাকে তার পরিষ্কার করতে হয়। তাদের বাদ দিয়ে সেখানে যে-জাত বা প্রজাতি কৃষক চাষ করতে চায় তারই বীজ বোনা হয় বা , তারই চাষ হয়। মানুষ নিজের ভোগের জন্য যে জাতি ও প্রজাতিগুলো দরকার তার চাষ করল কিন্তু যেসব জাত বা প্রজাতি সে মাঠে বাড়তে দিল না, তাদের কী হবে? ‘আবাদ’ করার অর্থ হচ্ছে যেসব জাত বা প্রজাতি চাষ করা হোল না তাদের প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত ভাবে রক্ষা করবার ব্যবস্থা রাখা, যাতে তারা নষ্ট না হয়, হারিয়ে না যায়। কৃষকের এখন যা দরকার তা চাষ করবার জন্য প্রকৃতির একটা অংশ ব্যবহার করতে হচ্ছে, অন্যদিকে প্রকৃতির অনাবাদী অংশে তাকে রক্ষা করতে হচ্ছে সেই সব জাত এবং প্রজাতি যারা আজ নয়, কিন্তু আগামী দিনে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণিকুলের প্রয়োজন। প্রাণের বেঁচে থাকার শর্ত। প্রকৃতির ব্যবহার এই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটাবে। কার প্রয়োজন? মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতি তো শুধু মানুষের জন্য নয়। মানুষের এখনকার প্রয়োজন মেটাবার জন্য ‘চাষ’ করলেও আগামির জন্য ‘আবাদ’ বা প্রাণের বিস্তৃত পরিমণ্ডলের ব্যবস্থাপনা কৃষককে করতে হয়। প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হয় যাতে প্রাণ ও প্রাণবৈচিত্রের ক্ষয় না ঘটে। প্রকৃতির আবাদি ও অনাবাদি দুটো দিককেই সমানভাবে চর্চা ও উভয়েরই ফলন ও প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে কৃষি সভ্যতা দাঁড়ায়। টিকে থাকে।
শিব ও দয়াল চাঁদ
দেবের দেব মহাদেব কেন বাংলায় কৃষির দেবতা – এই প্রশ্ন আমার বহুদিনের। চৈত্রের শুরু থেকেই হরগৌরি সেজে গ্রামে গ্রামে গান, অভিনয়, ঢোল বাদ্যি ইত্যাদি এখনও রয়েছে। কেন শিবের এই ডাঁট আর তার পাশে পার্বতীর এই প্রতাপ এটা ভেবে ভেবে আমার অনেক দিন গিয়েছে। কিন্তু শিক্ষাটা শেষাবধি গ্রামের কৃষক মেয়েদের কাছেই পেয়েছি। মহাদেবের পিন্দনে এখন যে বাঘছাল, আর হাতে ত্রিশূল – শিব বা মহাদেব আদিতে বাঘছালি আর ত্রিশূল্ধারী ছিলেন কিনা সেটা ঘোর সন্দেহের। একবার দেখি গলায় নীল রঙ মেখে নীলকণ্ঠ সেজে মহাদেব পার্বতিকে পাশে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন প্রচণ্ড চৈত্রে। আর হঠাৎ ধূপ ধূপ করে হিন্দু মেয়েরা প্রণাম আর মুসলমান নীলকণ্ঠ মহাদেব আর তাঁর বৌকে সেলাম করছে। মেয়েদের শুধালাম শিব এতো প্রিয় কেন মেয়েদের? তাদের প্রথম উত্তর হচ্ছে শিব যেহেতু তার স্ত্রীর ‘দাসত্ব’ করে অতএব আমরা মেয়েরা পার্বতীর হয়ে শিবের ভক্তি করি। এই উত্তরে খুশি না হওয়ায় প্রায় সব কৃষক মেয়ে উত্তর দিল, এই যে গলায় বিষ ধারণ করে আছেন মহাদেব তাকে দেখেন, নাগিনী বিষের জ্বালা শীতল করবার জন্য তার গলা পেঁচিয়ে আছে। শিব মহাদেব বটে, কিন্তু দেবতাও নন, অসুরও নন। তিনি আসলে মানুষ, তাই তিনি মহাদেব। তিনি মানুষ বলেই তাকে আমাদের ভক্তি। প্রশ্ন করলাম, এতো মানুষ থাকতে শিব কেন? উত্তর এলো অসুর আর দেবতা উভয়েই অমৃত চায়। তাদের সাধনা যে তারা ‘অমর’ হবে। কিন্তু শিব তো ‘অমর’ হবার সাধনা করে না, ‘মানুষ’ হবার সাধনা করে। তাই শিব পাগল, মাস্তান, উন্মাদ।

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পী রাম বসাক আর আমি। বিষ্ণুপুর গ্রামে নয়াকৃষির রিদয়পুর বিদ্যাঘরে চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবে। রাম আর আমাদের সঙ্গে নাই। হায় সেই নাচও নাই, দুজনেই গ্রামের মানুষকে আনন্দ দিয়ে মজা পেতাম। যে বন্ধন অন্যেরা ছিঁড়ে ফেলতে চায়, চৈত্র সংক্রান্তি ছিল সেই বন্ধনে নতুন করে গিঁট লাগাবার উৎসব।
সাগর মন্থন করে যখন বিষ উঠে এলো সেই বিষ দেবতা আর অসুররা কোথায় রাখবে ঠিক করতে পারছিল না। তখন তারা সেই বিষ খাইয়ে দিল শিবকে। এখন শিব দেখলেন তিনি যদি বিষ খেয়ে ফেলেন তো তিনি মরেন, আর যদি উগরে ফেলে দেন তাহলে সমস্ত জগৎ সংসার ধ্বংস হয়। সমস্ত প্রাণ ও পরিবেশের সর্বনাশ ঘটে। শিব তখন করলেন কী, তিনি বিষ রাখলেন তাঁর কণ্ঠে। বিষে তার গলা নীল হয়ে গেল। বিষের জ্বালা নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সাপ এসে কণ্ঠ ঠাণ্ডা রাখবার জন্য গ্রিবা জড়িয়ে ধরল। বিষ কন্ঠে যেন প্রকৃতি বাঁচে, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, জীব অনুজীব প্রাণে রক্ষা পায়। এই যে নীলকণ্ঠ, দেবের দেব মহাদেব, তিনি ছাড়া ভক্তির পাত্র তো অন্য আর কন দেবতা হতে পারেন না। অসুর নয়, দেবতা নয় শিবরূপের ভজনাই বাংলায় প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষার ধারনার সঙ্গে যুক্ত। শিবকে স্ত্রৈণ বলা যায়, কারণ তিনি পার্বতীর দাসত্ব করেন, এই দাস তো আসলে প্রকৃতির দাস, প্রাণের হেফাজতকারী। যে প্রাণ ব্রহ্মাণ্ডকে সচল ও সজীব রাখে তাকেই রক্ষা করেন শিব। সে কারনেই তিনি দেবের দেব মহাদেব।
সাগর মন্থন করে যখন বিষ উঠে এলো সেই বিষ দেবতা আর অসুররা কোথায় রাখবে ঠিক করতে পারছিল না। তখন তারা সেই বিষ খাইয়ে দিল শিবকে। এখন শিব দেখলেন তিনি যদি বিষ খেয়ে ফেলেন তো তিনি মরেন, আর যদি উগরে ফেলে দেন তাহলে সমস্ত জগৎ সংসার ধ্বংস হয়। সমস্ত প্রাণ ও পরিবেশের সর্বনাশ ঘটে। শিব তখন করলেন কী, তিনি বিষ রাখলেন তাঁর কণ্ঠে। বিষে তার গলা নীল হয়ে গেল। বিষের জ্বালা নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সাপ এসে কণ্ঠ ঠাণ্ডা রাখবার জন্য গ্রিবা জড়িয়ে ধরল। বিষ কন্ঠে যেন প্রকৃতি বাঁচে, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, জীব অনুজীব প্রাণে রক্ষা পায়। এই যে নীলকণ্ঠ, দেবের দেব মহাদেব, তিনি ছাড়া ভক্তির পাত্র তো অন্য আর কন দেবতা হতে পারেন না। অসুর নয়, দেবতা নয় শিবরূপের ভজনাই বাংলায় প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষার ধারনার সঙ্গে যুক্ত। শিবকে স্ত্রৈণ বলা যায়, কারণ তিনি পার্বতীর দাসত্ব করেন, এই দাস তো আসলে প্রকৃতির দাস, প্রাণের হেফাজতকারী। যে প্রাণ ব্রহ্মাণ্ডকে সচল ও সজীব রাখে তাকেই রক্ষা করেন শিব। সে কারনেই তিনি দেবের দেব মহাদেব।

নিজে বিষ ধারণ করে জীবের প্রাণ রক্ষা করার আবেদন ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই আবেদন সৃষ্টি করে। হর-গৌরি প্রতিবছর দর্শন দিয়ে প্রাণ সুরক্ষার ভাবই প্রচার করেন। একে নিছকই একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব গণ্য করার ফলে এর তাৎপর্য সকল সম্প্রদায়ের কাছ থকেই হারিয়ে গিয়েছে। চৈত্রের সংক্রান্তিতে কৃষকের যে-উৎসব, সেখানে বাংলাদেশে শিব পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যান। প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষার পাঠ মনে করিয়ে দেন; এর মধ্যে মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে হুশিয়ারি জারি করে যান। তিনি, অবিনশ্বর মানুষ, বাস করেন জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে ‘জগত’ নামের একটি জায়গায়, যা আসলে শ্মশান মাত্র। নশ্বর মানুষে দাহ ক্রিয়ার ক্ষেত্র।হরগৌরিকে এভাবে উপমহাদেশে অন্যত্র দেখা যায় না।
কে জানে হয়তো এই জন্যই ফকির লালন শাহ তার আগের প্রচলিত সমস্ত ‘গুরু’ সংক্রান্ত ধারণাকে নাকচ দিয়ে বললেন, ‘গুরু’ যিনি তাকে ধ্যানী শিবের মতোই জীবের প্রতিপালক হতে হবে :
‘কিঞ্চিত ধ্যানে মহাদেব
সে তুলনা কী আর দেব
লালন বলে গুরু ভেব
যাবে রে মনের ধোঁকা
পাবে সামান্যে কি তার দেখা ।
যিনি নিরঞ্জন ও নিরাকার সেই ‘সামান্য’কে বোঝাই কী করে? এই হচ্ছে লালনের জিজ্ঞাসা। যদি বোঝাতে চাই তাহলে কোন একটা বিশেষ প্রতীকী রূপকেই উদাহরণ হিশাবে ধরে ‘সামান্য’কে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অন্তত মনের ধোঁকা কাটাবার আর কোন সহজ পথ নাই। আর কি উদাহরণ হতে পারে কন্ঠে বিষ ধারণ করে রাখা দেবের দেব মহাদেব ছাড়া।
এজন্যই বলা হয় যদি চৈত্রসংক্রান্তি ভুলে যাই তো শিবকেও ভুলি। যদি শিবকে ভুলি, তাহলে ধ্যান ও প্রজ্ঞার অর্থও ভুলি। ভক্তি কথাটিরও কোনো অর্থ আর থাকে না। জগতে যদি ভক্তি না থাকে তাহলে বিষ রাখব কোথায়? জীবের বাঁচার উপায় কি হবে? জগৎ কি ছারে খারে যাবে?
এই কালের রাজনীতি সেই পরওয়ারদিগারের রাজনীতি যিনি জগতের ‘প্রভু’ হবার বাসনা করেন না, কিন্তু হতে চান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ‘রব’ বা প্রতিপালক। রাব্বুল আলামীন। জগত বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নামে আমরা যাকে একটি বৃত্তের মতো ভাবি যার বাইরে কিছুই আর নাই, তিনি সেই সমস্ত কিছুর — অর্থাৎ যার বাইরে আর কোন কিছু নাই — সেই সমগ্রের প্রতিপালক। তাকেই আমরা ‘দয়ার দয়া’ নামে ডাকি।
ইকলজি (ecology) বা প্রাণ ও প্রকৃতির রাজনীতি একালের ভাষা। ইসলামের ভাষা ‘রবুবিয়াত’। বড় বাংলার মওলানা ভাসানী এর মর্ম বুঝতেন। ভাবগত দিক থেকে ইসলামের গৌরবের দিক হচ্ছে একদিকে আল্লাহকে ‘প্রভু’ হিসাবে গণ্য করবার ঐতিহাসিক ইব্রাহিমি ধারাকে এই ধর্ম অস্বীকার করে নি এবং করে না কিন্তু তাঁর যে ‘ইসম’ বা নাম নেবার বিধান মোমিনদের জন্য ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে, ‘বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহিম’। সেই ইসম বা নামই আমাদের আরাধ্য যাঁর দয়ার কোন সীমা পরিসীমা নাই। তাঁর যে গুণের এবাদত বা ভজনার নির্দেশনা সেটা তাঁর দয়ার দিক, প্রভুত্বের বা আধিপত্যের রূপ নয়। বাংলায় রাহমানুর রাহিম কথাটির ভারি সুন্দর অনুবাদ হচ্ছে : ‘দয়াল’।
সব কাজই সেই কারণে দয়ালের নামে শুরু করাই বাংলার সংস্কৃতি। হয়তো বাংলার বিধানও তাই। এমনকি ওপারে যাবার সময় যখন আসে তখন সে দয়ালের দয়ার জন্যই কাতর অপেক্ষা করে।
‘দয়াল চাঁদ আসিয়ে আমায় পার করিবে
এমন সুভাগ্য আমার কবে হবে’…

(লেখাটি সাপ্তাহিক বুধবারে ছাপা হয়েছিল ২০১০ সালে এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখে।)
ফরহাদ মজহার

কবি, চিন্তক, বুদ্ধিজীবী ও কৃষক। জন্ম: ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায়। পড়াশুনা করেছে ওষুধ শাস্ত্র ও অর্থনীতি বিষয়ে যথাক্রমে ঢাকা ও নিউইয়র্কে। পেশা সূত্রে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের ‘নয়াকৃষি আন্দোলন’-এর প্রধান সহযোদ্ধা। লালন ধারা-সহ বৃহৎ বঙ্গের ভাবান্দোলন পরম্পরার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সমাজ ও রাজনীতি চিন্তা এবং দার্শনিক বিষয়ে বহু গদ্য রচনা করেছেন। এছাড়াও লিখেছেন নাটক। অনুবাদও করেছেন।
তাঁর বইগুলি-
কাব্যগ্রন্থ:
খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ (১৯৭২) ।। ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি (১৯৭৭) ।। আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে (১৯৮৩) ।। সুভাকুসুম দুই ফর্মা (১৯৮৫) ।। বৃক্ষ: মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ক কবিতা (১৯৮৫) ।। অকস্মাৎ রপ্তানিমুখী নারীমেশিন (১৯৮৫) ।। খসড়া গদ্য (১৯৮৭) ।। মেঘমেশিনের সঙ্গীত (১৯৮৮) ।। অসময়ের নোটবই (১৯৯৪) ।। দরদী বকুল (১৯৯৪) ।। গুবরে পোকার শ্বশুর (২০০০) ।। কবিতার বোনের সঙ্গে আবার (২০০৩) ।। ক্যামেরাগিরি (২০১০) ।। এবাদতনামা (২০১১) ।। অসময়ের কবিতা (২০১১) ।। কবিতাসংগ্রহ (২০১১) ।। তুমি ছাড়া আর কোন্ শালারে আমি কেয়ার করি? (২০১৬) ।। সদরুদ্দীন (২০১৮)
গদ্যগ্রন্থ:
প্রস্তাব (১৯৭৬) ।। সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান প্রসঙ্গে (১৯৮৫) ।। রাজকুমারী হাসিনা (১৯৯৫) ।। সাঁইজীর দৈন্য গান (২০০০) ।। জগদীশ (২০০২) ।। সামনা সামনি: ফরহাদ মজহারের সঙ্গে কথাবার্তা (২০০৪) ।। বাণিজ্য ও বাংলাদেশের জনগণ (২০০৪) ।। মোকাবিলা (২০০৬) গণপ্রতিরক্ষা (২০০৬) ।। ক্ষমতার বিকার ও গণশক্তির উদ্বোধন (২০০৭) ।। ভাবান্দোলন (২০০৮) পুরুষতন্ত্র ও নারী (২০০৮) ।। সাম্রাজ্যবাদ (২০০৮) ।। রক্তের দাগ মুছে রবীন্দ্রপাঠ (২০০৮) ।। সংবিধান ও গণতন্ত্র (২০০৮) ।। নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০৮) ।। তিমির জন্য লজিকবিদ্যা (উপন্যাস, ২০১১)
প্রাণ ও প্রকৃতি (২০১১) ।। মার্কস পাঠের ভূমিকা (২০১১) ।। ডিজিটাল ফ্যাসিবাদ (২০১২)
যুদ্ধ আরো কঠিন আরো গভীর (২০১৪) ।। ব্যক্তি বন্ধুত্ব ও সাহিত্য (২০১৬) ।। মার্কস, ফুকো ও রুহানিয়াত (২০১৮)
নাটক:
প্রজাপতির লীলালাস্য (১৯৭২)
অনুবাদ:
অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার একটি ভূমিকা (মূল: কার্ল মার্ক্স) (২০১০)
খুন হবার দুই রকম পদ্ধতি (মূল: রোকে ডাল্টন) (২০১১)