
সজলকান্তি সরকার
ভাটি অঞ্চল-সহ বঙ্গের নানা জায়গায় এক সময়ে ‘বাঁদি’ বা ‘বান্দি’ কেনাবেচার রেওয়াজ ছিল, বিশেষত উচ্চবর্ণের অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে। বিধবা কিংবা কোনও কারণে নির্দিষ্ট বয়স হয়ে যাওয়ার পরেও যাদের বিয়ে হয়নি কিংবা যেসব পিতা তাঁর কন্যাসন্তানের বিয়ে দিতে পারতেন না আর্থিক সামর্থ্যের কারণে, মুলত তাঁদের বিক্রি করে দেওয়া হত। আর এইসব মেয়েদের ঠাঁই হত বাবুদের বান্দিখানায়। যৌনদাসী হয়ে বেঁচে থাকার পাশাপাশি বিনা পারিশ্রমিকে গৃহশ্রমের কাজ করেই জীবননির্বাহ করতে হত এইসকল মেয়েদের। তাঁদের কন্যাসন্তান হলে তার জীবনও গিয়ে থামত অলঙ্ঘনীয় পরিণতির মধ্যে । বাবু পরিবারগুলি তাঁদের কন্যাসন্তানের বিয়েতে পাত্রপক্ষকে যৌতুক হিসেবে ‘বাঁদি’র কন্যাকে তুলে দিত। আর বাবুর ঔরসে ‘বাঁদি’ পুত্রসন্তান প্রসব করলে সেই সন্তানের সামাজিক পিতৃপরিচয় তৈরি করতে বাঁদিদের ‘পান্নুয়া’ বিয়ে দেওয়া হত। যে বিবাহের পাত্রের কাজই কেবল বিয়ে করে তিন-চারদিন সহবাস করা। বিনিময়ে অসহায় মেয়েটির পুত্রকে পিতৃপরিচয়টুকু দেওয়া। আজকের বড় বাংলার বর্ণহিন্দু পরিবারগুলির পূর্বসূরীদের মধ্যে যারা উচ্চবিত্তের ছিল, তাদের অনেকের মধ্যে খোঁজ করলেই হয়ত এই নির্মম দাসপ্রথার ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ পাওয়া যাবে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের বাংলার এমনই এক ‘বান্দি’র জীবনকে স্মরণে রেখে লেখক-গবেষক সজলকান্তি সরকার পদ্য-সহযোগে লিখছেন’প্রতিপক্ষ’র বিশেষ গদ্যসাহিত্য ‘বান্দিপুরাণ’। প্রচ্ছদের ছবিটিও লেখকের সৃজন।
বান্দিপুরাণ
গিরস্তের পুত্-
বরষায় কুত্ কুত্, হেমন্তে জুত
বাকি সব যেন নাই কামের ছুঁৎ।
পুত আর জুতই গৃহস্তের সম্পদ। মূলত উঠোন থেকে জোত-জমি পর্যন্তই ভাটির গৃহস্থকূলের স্বপ্নের সিঁড়ি। পুত আর জুত- যেন অমূল্য হীরা-মানিক। নেহাত জীবন-মরণ সংক্রান্ত কারণ ছাড়া উঠোন-জমিনের বাইরে গিয়ে ভাটি ময়ালে কারও স্বর্গবাসী হওয়ারও খায়েশ এককালে ছিল না। আর পাঠশালা কিংবা পুঁথিবিদ্যা অর্জন? তা কেবলই কর্মহীন সন্ধ্যায় খুপি বাতির কেরোসিনের সামর্থ্য অনুযায়ী আলোতে ঘরের মেঝেতে বিছানো ছালার চটে বসে বাল্যশিক্ষা পড়েই খান্ত হয়। তাই নাম-দস্তখত লেখা, চিঠিপত্র পড়া, জোত-জমির মাপজোপ আর খাজনার হিসাব-নিকাশ জানলেওয়ালারাই ছিল একসময় ভাটি-ময়ালের বিদ্যাসাগর।
১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ। বাল্যশিক্ষা শেষ করে আমি অবুঝ মায়ের কান্নায় মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য ভাটির ‘গিরস্তময়াল’ ছেড়ে কিছুটা উজানে লজিং-বাড়িতে যাই। লজিং-বাড়িটি এলাকায় ‘দারোগাবাড়ি’ নামে পরিচিত। বেশ নামডাক আছে তার। যদিও দারোগাবাবু তখন থেকে অনেক আগেই বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে গেছেন। তবুও বাড়িতে দাসীবান্দি নিয়ে লতাগোষ্ঠি এখনও পড়ে আছে ভিটার মাটি কামড়ে। লম্বা-লম্বা টিনের ঘর আর স্বাদু মাছের পুকুরপাড়ে জোনাকজ্বলা লেবুবাগান ও ভিতর বাড়ির ঐতিহ্যের পর্দা এখন অনেকটা মলিন হয়ে গেছে। এই দারোগা বাড়িতেই আমার পিতামহ তঁার একমাত্র কন্যা সবেধন নীলমণি অর্থাৎ আমার পিসিমণিকে বিয়ে দিয়েছেন। আর এই আত্মীয়তার সুবাদেই আমাকে পুঁথিবিদ্যা শেখাতে যেমন মায়ের কান্নাকাটি, তেমনই পিসির ইচ্ছাতেও দারোগা বাড়ি থেকে আমার হাইস্কুলে পাঠগ্রহনের সুযোগ হয়। অর্থাৎ আমার পিসির বাড়িই লজিং-বাড়ি। জং-ধরা মরচে পড়া দারোগাবাড়ির টিনের ঘরে শালকাঠের চৌকাঠে বেঁধে রাখা আয়েশে শিকার করা বুনো হরিণের শিঙওয়ালা মাথা আর হাট থেকে এক টাকায় কেনা দাসী-বান্দির জৌলুস এখনও এ বাড়ির অতীত বিলাসিতার স্বাক্ষী হয়ে আছে। আমি তখন অল্প বয়সের ‘গিরস্তের পুত’। দাসী-বান্দি বোঝার মতো আক্কেল আমার হয়নি তখন। যতটুকু বুঝেছি দারোগা বাড়ি এসে পিসিমণির কাছ থেকে শুনে শুনে। পিসিমণি শুধু একটি কথাই বলতেন, ‘বড় হও বাবা তখন বুঝবে।’ পিসিমণি তখন ছিলেন জৌলুসভাটা দারোগাবাড়ির বড়বউ। যখন দাসী-বান্দিদের সেই জৌলুসময় জোয়ার-জামানা নেই। কিন্তু এ বাড়িতে বান্দি ছিল ঠিকই। তবে বান্দিরা তখন দারোগাবাড়ির বারামখানা বা অন্দরমহল ছেড়ে লোকাসমাজে স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া অহেতুক বান্দি খাটানোর মনোবৃত্তি পিসিমণির কখনও ছিল না। ফলে দারোগাবাড়ির বান্দিত্বে মনুষ্য জীবনযাত্রা চলছে। যাইহোক, যখন আমি জানতে পারি বান্দি এ বাড়ির লতাগোষ্ঠির কেউ নয়, আগন্তুক মাত্র, তখন নিজের কথাও ভাবতাম। তফাৎ খুঁজতাম! মনে হত, কেউ কুটুম, কেউ কামলি। কষ্ট পেতাম। আমি বান্দিকে তো পিসি বলেই ডাকতাম, নিজের পিসিই মনে করতাম। মাঝে মাঝে রাগ হলে বড়দের শিখানো বুলি আউড়ে ‘বান্দিপিসি’ বলেও ডাকতাম অবশ্য। তখন তো বান্দিদের অন্তর্নিহিত তথ্য বোঝার বয়স আমার হয়নি, তবুও মনের স্বাভাবিক খেয়ালে প্রশ্ন জাগতো-তাদের পরিচয় কী? তারাও কি আমার মতো কোনও কিছুর দায় নিয়ে এ বাড়িতে পরবাসী? তারাও কি আমার মতো লজিংয়ে থাকে? আমার সাথে তাদের তফাৎ কোথায়? আর এ কথা ভাবার কারণ এই যে, আমাদের বাড়িতেও আমি গৃহস্থালী কাজের নিমিত্তে অনেককে জাগির থাকতে দেখেছি। যারা তাঁদের প্রয়োজনে আশ্রয় নিয়েছে, আবার প্রয়োজন ফুরালে চলেও গেছে। একসময় বয়স বাড়তে বান্দি বিষয়ে ভুল ভাঙলো। আমি লজিংবাড়ি ছাড়লাম কিন্তু বান্দিরা দারোগাবাড়ি ছাড়লো না। তাই শুধু কৌতুহল নয়! মাঝে মাঝেই ফিরে যেতাম দারোগাবাড়ি- ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের ওই রাজার রাজত্বে’ শুধু এই মন্ত্রটা বান্দিপিসিকে শোনাব বলে। এক সময় বলতে বলতে ওঁরা স্বাধীন হয়ে যায়। শুরু হয় সম্পত্তির অধিকার নিয়ে তঁাদের আলাদা ঘর-সংসার। আর তখন থেকেই আমার বান্দিপ্রথা বিষয়ে জানাবোঝা শুরু। বেরিয়ে আসে তৎকালীন সমাজে বান্দির নিমিত্তে মানুষ কেনাবেচার নানা তথ্য। বান্দিকূল নিয়ে কোমর বেঁধে ঘঁাটাঘঁাটি করে পাওয়া কিছু খণ্ড তথ্য ও তত্ত্বের লেখ্যচিত্র যা প্রায় দুইকুড়ি বছর পর আজ তুলে ধরছি। শুধু তাই নয় ভাটির ময়ালে গিরস্তবাড়িতে অনেক বান্দি প্রথার বাস্তবচিত্রের শেষদৃশ্যও আমি দেখেছি এবং গল্প শুনেছি। তাই আজকের মূল বিষয় এসব বান্দি জীবনবোধের গল্প ও বাস্তবতার আংশিক সমাচার।
ভাটির ময়ালে (বর্তমান সামাজিক মর্যাদার বিষয় চিন্তা করে সাকিন ও নাম নেপথ্যে রইল) মায়ারানি নামে এক বান্দি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে। তিন আনা যৌতুকের অভাবে সময় মতো বিয়ে হয় নাই বলে সামাজিক বিবাহ বিধানে অপয়া দুষে মায়ারাণী ব্রাহ্মণ সভ্যকুল বা পিত্রালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভাটির অচিনগাঁয়ের বান্দিকূল হয় তার বেঁচে থাকার খোঁয়ার। এ খোঁয়ারের বান্দিজীবনাচার নিয়ে লিখতে গিয়ে আমার হৃদয় নড়ে ওঠে। হৃদয়ের বিবেকতীরে কষ্টের ঢেউ আছড়ে পড়ে। তাই কাতর হয়ে মাঝে মাঝে কিছুটা বিলাপ সুরেই লিখে যাই বান্দিপুরাণ।
আমি কি লিখিব গো বান্দিপুরাণ কলমের কালিতে
রাজা-বাদশার অন্দরমহল হায় পারি নাই দেখিতে।
রাজমহলে ফোঁটে গো কমল কোন বা বান্দির হাতে
রাজার কেন বান্দিবিলাস হায় রাজরাণী থাকিতে।
স্বামী ছাড়া বান্দির পেটে সন্তান হয় কাহারও বরেতে
বান্দিপুত্র রাজত্ব পায় রাজ’ন্ন খায় কোন বিধি মতে।
বান্দির পেটে জন্মায় পণ্ডিত কোন শক্তির বলেতে
রানি কেন মূর্খ বিয়ায়, বল গো রাজ-ঔরস থাকিতে।
কেবা বান্দি কেবা রানি কেহই গো না পারে বুঝিতে
রাজমহলে সবাই রাজলোক, এ গো থাকে যে সুখেতে।
কোথায় হতে আসে বান্দি জন্ম তার কোন কুলেতে
রাজমহলের বান্দি যারা ভিন্ন তারা- গিরস্তবান্দি হতে।
এসব রাজবান্দির কথা গো আমি চাই না যে লিখিতে
তারা কেহই নয়তো দুখী থাকে রাজলোকের সারিতে।
আমি লিখিব সেই বান্দিপুরাণ রয় যা গিরস্ত গৃহেতে
ব্রাহ্মণ কন্যা বান্দি কেন মানব ধর্মের এই দুনিয়াতে।
দুনিয়াতে সভ্যতা বিকাশের ফলেই দাস-দাসী বা বান্দি-গোলাম প্রথার উদ্ভব হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, ক্রয়সূত্রে, সামাজিক বিধানে ও গৃহস্থালীর প্রয়োজন-সহ নানা কারণে নানাভাবে এ প্রথা শুরু হয়। যার রয়েছে নানা ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনই দাসী-বান্দি কথাটি সূত্রে চলে আসে রাজমহল। চলে আসে রাজা-রানির অন্দরমহল। তবে ধর্মমহলের চরণদাস কিংবা চরণদাসীর বিষয়টি একটু ভিন্ন। তার চেয়ে ভিন্ন ভাটিময়ালের গেরস্তগৃহে বান্দিদের কথা। আজকের বিষয় আমার শৈশবের স্মৃতিময় অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া দক্ষিন ভাটিগাঁয়ের বেতাল পরগণার ব্রাহ্মণের মেয়ে মায়ারাণীর বান্দিজীবন-সহ এ যাবৎকালে জানা ভাটি ময়ালের ‘গিরস্ত বান্দিসমাচার’ । ব্রাহ্মণের মেয়ে মায়ারানি। তিনি তঁার পিতার নয়জন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। ব্রাহ্মণের কোনও পুত্র সন্তান নেই। তবে স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মণের এখনও আছে। এ নিয়ে সমাজে ব্রাহ্মণীর নিন্দার শেষ নেই। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক বছর আগে অতিবয়স্ক ‘দ্বিত্তাব্বর’ পাত্রের সঙ্গে। এ বিয়ের ঋণ পরিশোধে এখনও সুদে-আসলে খাতায় হিসাব করে ব্রাহ্মণের বসতভিটে বুঝে নেওয়ার ফাঁদ তৈরি করে আছে মহাজন। এবার দ্বিতীয় মেয়ে মায়ারানির বিয়ের পালা। সামাজে প্রচলিত ‘রোহিনী বিবাহ প্রথা’ অনুযায়ী আর তিন মাস পরেই দশ বছরে পা দিয়ে ‘অপয়া’ হবে মায়ারানি। ব্রাহ্মণ চিন্তিত। কিন্তু প্রতি বছর স্ববর্ণে ও স্ববংশে কন্যাদান এখন ব্রাহ্মণের কাছে উঠানসমুদ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ক্ষুধার পেট এখন আর জজমানিতে ভরে না। ঈশ্বরের কৃপায় মন্দিরের প্রসাদ খেয়েও বেঁচে থাকার কোনও পথ নেই। ভাটির ময়ালে অভাবের কারণে ব্রাহ্মণ সেবার মাহাত্ম্য এখন লোকালয় ছেড়েছে। ব্রহ্মত্ব বুঝানোর জন্য পৈতা কানে ঝুলিয়েও কাজের কাজ হয় না। তাই কন্যাদান যেনও আপদ বিদায়।
১৩৫০ বাংলা সন। দারুণ অভাব-অনটনে দিন যায় ব্রাহ্মণের। বিয়ে-থা নিয়ে সকল মেয়ের বাপেরাই এখন বিপাকে আছেন। আর জোত-জমিহীন ব্রাহ্মণের এখন অন্নযুদ্ধই যেন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ময়ালে এখন আর ঠোঙা ভরে ভোগ-নৈবদ্য বা দক্ষিণা দিয়ে কেউ পুজা করে না। এখন পুজা হয় কেবল ধান-দূর্বা আর তিল-তুলসী দিয়ে। ব্রাহ্মণসমাজ নিরুপায়। মন্ত্রগুণের জামানা ফুরিয়ে আসছে। পৈতার জলে এখন আর কারও চিত্তশুদ্ধ হয় না। আর এসব কথা চিত্ত উজার করে লিখতে গিয়ে গদ্যাকারে লিখে সুখ পাচ্ছি না। তাই লিখে যাই সুরের মহিমায়, গানের কথায়।
দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ ছিল বসতি হয় দক্ষিণ ভাটিগাঁয়
কী লিখিব গো তার গৃহের কথা প্রাণে সহনও না যায়।
ব্রাহ্মণী তার চরণদাসী তৃণগৃহে শাক-অন্নে দিন যায়
অভাবে হয় একাদশী ব্রাহ্মণেরে তিনবেলা খাওয়ায়।
জজমানি করে অন্ন যোগায়, বস্ত্র পায় দান দক্ষিণায়ন
‘জন গো তার শ্রীকন্যা হয় একজন পুত্র নাহি পায়।
অন্নদাতা হয় বিধাতা, বাঁচে তারা গোবিন্দের কৃপায়
ভিক্ষা করে যোগায় অন্ন নিত্যি যা ব্রাহ্মণে গো পায়।
কেমনে হবে কন্যাদান হায় তারা পড়ল ভীষণ দায়
দেখা দিল দারুণ অভাব তেরো’শ পঞ্চাশ বাংলায়।
নয় বছরে হয় কন্যাদান ধর্মের বিধান খণ্ডন নাহি যায়
তার অধিক হইলে কেহ মোড়লবাড়ি বান্দিতে বিকায়।
মায়ারাণীর বিয়ের বয়স লিখা আছে সমাজের খাতায়
পান্নুয়া বিয়া হইবে গো তার বয়স যদি নয় গইয়া যায়।
রূপ-যৌবনে ভরা দেহ তার ছিন্নবস্ত্রে নাহি যে কুলায়।
বহু বিয়ের স্বামী পাইবে বান্দিগোত্র লিখিয়ে তার গায়।
বিবাহের মেয়াদ উত্তির্ণ মেয়েরা পিত্রালয় ছেড়ে ‘পান্নুয়া’ বা ‘পডক্যিয়া’ (পরকীয়া) বিয়ের সুবাদে বান্দিগোত্রে নাম লিখে বাঁচার অধিকার পায়। নয়-এ নববধু না হলে মেয়েরা পিতৃকুল হারায়। মেয়েরা পিত্রালয়ে ঋতুবতী হলে মহাপাপ। ব্রাহ্মণ সমাজেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বরং ব্রাহ্মণ সমাজে অপয়াদের মুখ দর্শনে অশুভ ফলের ভীতি ছিল বেশি। তাই মেয়েরা পিত্রালয়ে ঋতুবতী হলে কুলহারা হইত কলঙ্কিনী রূপে। তার তাই হয়তো বাউল আব্দুল করিমও বিলাপ সুরে গেয়ে উঠেছেন- ‘আমি কুলহারা কলঙ্কিনী আমারে কেউ ছইও না গো সজনী।’ ব্রাহ্মণ সমাজেও বিবাহের কঠোরতা ছিল। এ সমাজে পাত্র পাওয়াই ছিল বড় দূরহ ব্যাপার। আর পেলেও যৌতুকের ‘জায়’ বা ‘ফর্দ’ বেশ দীর্ঘ হত। তাই কন্যাদান সহজ ছিল না। মায়ারানির বাবা পুজাপার্বণ করে যা পায় তাতে বাঁচাই বড় দায়। এদিকে তৃতীয় কন্যাও নয় বছরে পা দিল-দিল। তাই বছর বছর কন্যাদানের ভাবনা ব্রাহ্মণকে নির্দয় করে তুলছে। পিতৃত্ব এখন আর সন্তানের স্নেহ বুঝে না। অভাবের কারণে সংসারে দেখা দেয় নিষ্ঠুর স্বভাব। এ ভাবে বিয়ের দিন চলে যায়- মায়ারানি দশ বছরে পা দিয়ে অপয়া হয়। তার স্বাভাবিক বিয়ের আর সুযোগ নেই। সমাজ এখন দিন গুণছে তাকে নিলামে নিতে। সমাজপতি দুই একবার তাগিদ দিয়ে গেছেন পান্নুয়া বিয়ে দিয়ে মেয়েকে বান্দিকুলে পাঠাতে। ব্রাহ্মণী তখন অনুনয়-বিনুনয় করে মায়ারানির জন্ম তারিখ কমিয়ে কিছুদিন সময় নিলেও এখন আর এ সুযোগও নেই।
একদিন তাই সমাজপতি ক্রোধে অতি ব্রাহ্মণে কইল
উদয়-অস্ত সময় দিলাম অপয়া কন্যা গৃহহারা হইল।
পতিবচন শুনিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা লইয়া পন্থে মেলা দিল
মায়ে কান্দে বইনে গো কান্দে এ বিধান খণ্ডন না গেল।
আগে-আগে হাটে ব্রাহ্মণ পিছে কন্যা নীরবে চলিল
মায়ারানির কান্দিতে মানা মনের দুঃখ মনেতে রহিল।
অপয়া দেখে পথের লোকে কতই না গাল-মন্দ দিল
মায়ারাণী হায় মাথা নুইয়ে বান্দি হাটে চলিতে লাগিল।
মোহনগঞ্জ নামেতে এক হাট ভাটির ময়ালেতে ছিল
ব্রাহ্মণে তার কন্যা লয়ে দুঃখ সয়ে হাটেতে আসিল।
বান্দি-নেবে, বান্দি-নেবে এই বলে ব্রাহ্মণে ডাকিল
সিঁদুর ছাড়া অপয়া নারী ক্রেতাগণ বুঝিতে যে পাইল।
গঠন-ঘাটন দেখিয়া তার কত ক্রেতা দর-দাম করিল
এমনও পণ্য কেউ চিনলো না শুধু মুনিবগণেই চিনিল।
বিধির লিখা যায় না তো দেখা কার কপালে কি গো ছিল
এক টাকা তার মূল্য দিয়া দারোগা বাবু কিনিয়া যে নিল।
দাসী-বান্দি বিক্রয়ের প্রচলন প্রাচীন যুগ থেকেই ছিল। তবে মায়ারানির বিষয়টি ভিন্ন। দারিদ্র্য কিংবা সহায়-সম্পত্তির লোভে নয় নিতান্তই সমাজের বিধানে নিরুপায় হয়ে কন্যা বিক্রয় করতে বাধ্য হয় ব্রাহ্মণ। তিন-আনা যৌতুকের দায়ে ষোলআনা মেয়েটি অপয়া হয়। হাটের পণ্য হয়। তৎকালে মায়ার বাঁধনের চেয়ে সমাজের শাসন মেনে নেওয়া ধর্ম ছিল। তাই বান্দিহাটে মায়ারানিকে কতওজন যে কতওভাবে দরদাম করল তা ভদ্র ভাষায় বলা মুশকিল। কেউ দেখল কামের শরীর কেউ দেখল রূপের, কেউ দেখলো মূল্য কতও কেউ দেখল জাতের। সুশ্রী মায়ারানির দরদামের ফাঁকে কতজন যে গাঁ ঘষে দাঁড়ালো তার ইয়ত্তা নেই। ব্লাউজ ছাড়া টগবগে বুকের কাপড় সামলাতে গিয়ে যখন তার পিঠ উদোম হয়ে যেত তখন নিতম্বের ভাঁজে ক্রেতাগণ হাবুডুবু খেত। ভাগ্যিস ক্রেতাদের কেউ মায়ারানির চাঁদমুখের হাসি দেখে নাই। তাহলে হয়তো হাটে মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে বান্দি জয়ের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে পারতো। সেদিন ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য সন্তান বিক্রয়ের নানা পৈশাচিকতা মেনে নিয়েও ক্রেতার সংগে দর কষাকষি করতে পারলো না। তাই লাখ টাকার ‘মাল’ বিক্রয় হলো মাত্র এক টাকায়। দাসখতের বিক্রয় দলিলে ব্রাহ্মণ ভুল ঠিকানা দিল ইজ্জতের ভয়ে। মায়ারানি এরপর থেকেই ভুল ঠিকানা ব্যক্ত করে তার বাবার ইজ্জৎ আড়াল করে বান্দি হয়। এখন মায়ারাণী দারোগা বাবুর উপাধি সূত্রে আচার্য থেকে তালুকদার। আমি অনেক চেষ্টা করেও মায়ারানির জন্ম-ঠিকানা জানতে পারিনি (তবে আন্দাজ করতে পেরেছি)। তাই তার পিতৃনিবাস এখানে অজানা। তবে দক্ষিণ ভাটির বেতাল পরগণাই তার দাস হয়ে ওঠা দলিলিক জন্মভূমি । আর দরিদ্র ব্রাহ্মণই তার পিতা ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই যদিও বিষয়টি প্রকাশিত নয়। মায়ারানির ভাষ্যমতে, দলিলে শুধু এতটুকুই উল্লেখ ছিল যে দাসীর নাম মায়ারানি, দাসীর বয়স-১০ বছর ২ মাস। বিক্রয়ের কারণ,অপয়া। বিক্রয়ের ধরণ, নিদাবী। বিক্রেতা: পিতৃকুলের (ব্রাহ্মণের) ভুল নাম। টিপসই: বিক্রেতা। ক্রেতা: বান্দিকুলের (দারোগা বাবুর) নাম ঠিকানা। টিপসই: ক্রেতা। দলিলাদি শেষে দান-দক্ষিণা আর ঠোঙ্গার ভোজ্জিতে বেঁচে থাকা ব্রাহ্মণ মেয়ে বিক্রয়ের এক টাকা পেয়ে বিত্তশালী হলেও চিত্ত তার অনলে জ্বলছে। ব্রাহ্মণ দারোগা বাবুকে হাতে ধরে শুধু একটি কথাই বলেছে- ‘বাবু মেয়েটা আমার ব্রতচারী, অধর্ম কুকর্ম সইতে পারে না।’ দারোগাবাবুর কানে এসব কথা বাজারের হট্টগোলের মতোই শোনালো। দারোগাবাবু ব্রাহ্মণের হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে মায়ারানিকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলেন। এদিকে পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে লোকলজ্জার ভয়ে মায়ারানি বিদায় বেলা চোখের জল ফেলে কাঁদতেও পারলো না। কিন্তু ব্রাহ্মণ টাকা পাইয়া হাউমাউ করে কাঁদিয়া উঠিল।
টাকা পাইয়া কান্দে ব্রাহ্মণ সন্তানের মায়া ভুলা যায় না
মায়ারানির ভাঙলো বিয়া বরের দাবি ছিল তিন-আনা।
ভবের হাটে লেনা-দেনা মনের দাবী কেউ জানে না
মায়ারানি তাই ওজন ছাড়া টাবগা হইল বেচা-কিনা।
জোৎস্নামাখা রূপ-যৌবন ভবের হাটে কেউ চিনল না
বান্দির হাটে নিলামেতে বিকাইল মাল লাভ হইল না।
মনকারবারি নাই গো হাটে মায়ারানির দাম উঠল না
কাজের বান্দি বানাইয়া রাঙের দরেই বিকল সোনা।
বিকাইয়া পেটের সোনা ব্রাহ্মণের আর প্রাণে সয় না
আদর কইরা কইল মাগো দেখা হয়ত আর হবে না।
মায়ারানি হায় কান্দিয়া কয় বাবা তোমায় করি মানা
মায়ের কাছে বান্দিপুরাণ মনের ভুলেও শুনাইও না।
বইনানরে কইও ভালো আছি হইব বিয়া বারামখানা
সময় হইলে নাইয়র যাইব কিনে রাখত শাড়ি-গয়না।
এই বলেই সে দাসক্ষত দিল মুনিব সনে ষোলআনা
ভাটি গাঁয়ের দারোগাবাড়ি হইল যে তার বান্দিখানা।
বান্দি নিয়ে হাট থেকে বাড়ি ফিরছেন দারোগা বাবু। পথে পথে কতও টিপ্পনি। দারোগাবাবুর বান্দি ঐতিহ্যের অহংকার প্রচার হচ্ছে পথ চলতে চলতে লোকের কানে কানে। সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছানো মাত্রই লোকজনের ভিড়। বাড়ির বউ-ঝি পরিবার পরিজন কত রঙে কথকতা বলে গেল। পাড়ার লোকজনও আসলো এ রঙ দেখতে। কেউ কেউ লোলুপ দৃষ্টিতে বান্দি দেহে কাম বিলাসে মত্ত হল। মায়ারানির অসহায় চোখ, বাকরূদ্ধ অধর, হৃৎপিণ্ডে বেদনার দম আর লজ্জাবতী মুখ কারও মনেতে দাগ কাটলো না। রাতেই সংসারের নানা কাজ বুঝিয়ে তাকে আলাদা বান্দিঘরে থাকতে দওয়া হল। নিঃসঙ্গ রাতে মা-বাবা ভাই-বোনের কথা ভাবতে ভাবতে ডুকরে উঠলো মায়ারাণীর বুক। রাত পোহালে শুরু হয় তার নতুন পরিচয়ের সকাল। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার মোহনগঞ্জ থানার অধীনে কোনও এক দারোগাবাড়ি হল মায়ারাণীর বেঁচে থাকার ঠিকানা অর্থাৎ বান্দিখানা। দিনগুলি কেটে যায় তার নানা কাজে কিন্তু রাত্রি এলেই যত বিপর্যয়। বাবুদের গতরের ব্যাথা সারাতে তেল মালিশ, ঘুম পাড়ানোর শীতল বাতাস আর তামাক সাজিয়ে পানের বাটায় খিলি বানানো তার নিত্যদিনের কাজ। তারপর, ঘুমের ঘরে প্রহরে প্রহরে, নাগর আসে বান্দিবাসরে। বিধাতার শরীর কী আর বান্দির ইজ্জত কিংবা সমাজ-নমাজ বুঝে! জরায়ু তো আর স্বামী চিনে সন্তান জন্ম দেয় না, তাই বেইমানিও করে না! ফলে রাতারাতি বান্দির ‘পেট’ জেগে ওঠে অদৃশ্য শিবের বরে। সমাজে বান্দির পেট নিয়ে শুরু হয় বদনাম তালা-তালি। মহারানির পেট যতো বড় হয়, তার কামলিপনার দায় তত বাড়ে। যেখানে বাড়ির বড়বাবুর স্ত্রী পাঁচ বছরেও মা হতে পারে না সেখানে রাত পোহালেই বান্দির পেটে বাচ্চা! এ কেমন কথা! কার এত বড় সাহস? বনাজি ঔষধ আর কবিরাজি লতাপাতা খেয়েও যখন পেট অপসারনে কাজের কাজ হয় না বাবুদের ইজ্জত বাঁচাতে, বান্দিপেটের বৈধতা দিতে মায়ারানির ‘পান্নুয়া’ বিয়ের আয়োজন হয়। ভোগ পরগণার পঁয়ষট্টি বছরের বয়স্ক বরের সাথে ১০০ টাকার যৌতুক চুক্তিতে স্বামীর একান্নতম বধু হয় মায়ারানি। সেদিন বাসর রাতে মায়ারানি স্বামীর চরণে সকল কলঙ্ক অঞ্জলি দিয়ে সিঁদুর কপালি হয়ে কেবল বাচ্চা বিয়ানোর সনদই পেয়েছিল, বাহু-বন্ধনে হৃদয় দেওয়া নেওয়া নয়। তেরাত্র বাস করে বর চলে যায় ঠিকানাহীন গন্তব্যে অন্য বিয়ের সন্ধানে। স্বামী সুখ নয়, মাতৃত্বের দলিল নিয়েই সুখে থাকতে হয় মায়ারানিকে। আর বাবুরা পান নিরাপদ বিনোদনের বান্দিশরির। এধরণের বিয়ের বরদেরকে বলা হয় পান্নুয়াবর, পাণ্ডাবর, টল্লুয়াবর বা পডক্যিয়াবর। সমাজের ইজ্জত রক্ষায় নিত্য দায়হীন বিয়ে করাই ছিল এদের কাজ। বাবু-মোড়লদের ইজ্জত রক্ষার জন্য তারা অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করত। ভাটির ময়ালে এমনও শোনা যায় নীলমণি দাস নামে এক লোক ছয়কুড়ি বিয়ে করেছিলেন। একদিন একশ একুশতম বিয়ে করতে যখন কলার তলে বসেন তখন কন্যাদানে মন্ত্রপাঠে কন্যার বাবার নাম নীলমণি দাস জানতে পারেন। পরে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেন মেয়েটি তারই সন্তান। তারপর নীলমণি দাস আর বিয়ে করেননি। অনুতপ্ত হয়ে দেশান্তরি হন। এটাই ভাটির ময়ালে পান্নুয়া বিয়ের সর্বোচ্চ সংখ্যা বলে মনে করা হয়। তবে মায়ারানির স্বামীও ছয়কুড়ি বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায়। এদিকে দারোগা বাড়ির বড় বউ(দরোগার বউ) আছেন মুশকিলে। স্বামীসনে রতিকর্মে সারারাত কাউচালি করেও মা হতে পারছেন না তিনি। কিন্তু বান্দির পেটে বছর বছর বাচ্চা বিয়ায়! কোন শক্তির বলে? যেখানে ঠাকুর ঘর, তুলসীতলা আর পুজামণ্ডপে জোরপাটা মানত করেও কাজ হচ্ছে না তার। কেউ কেউ বলছে ‘বড় বউয়ের বাচ্চা’ বান্দির পেটে চালান হয়ে যাচ্ছে’, তাই বান্দি বিদায় না করলে কাজের কাজ হবে না। মায়ারানির পেট নিয়ে শুরু হয় সমাজে নানা কথা। বড়বউয়ের পক্ষ থেকে মায়ারানিকে নিষেধ করা হয় বাচ্চা বিয়াতে। বান্দি ঘরে পাহারা বসানো হয়। তবুও যখন কাজ হয় না, একের পর এক চাঁদমুখের জন্ম হয়। তাই সিদ্ধান্ত হয় বান্দি বিদায়ের। কিন্তু চাইলেই কি আর বান্দি বিদায় সম্ভব? পুত্র ত্যাগ করার বিধান আছে সমাজে কিন্তু বান্দি বিদায়ের বিধান নেই। তাই শত জ্বালা সয়ে সয়ে মায়ারানি বড় বউয়ের চক্ষুশূল হয়ে এ বাড়িতেই আছে।
মুনিবগৃহে মায়ারানি থাকে গো কত জ্বালা লইয়া বুকে
খানাপিনা যেমন-তেমন সেবাছলে পানান দিতে ডাকে।
পানান বান্দির হয় পান্নুয়া বিয়া জানে গো সর্বলোকে
মায়ারানির হইল যে বিয়া ভবঘুরে এক পাণ্ডাবর দেখে।
যোগেন্দ্র নাগ নাম যে তার ঘর-বাড়ি নাই গো ভূলোকে
ভাবে-সাবে নয়াযৌবন, বয়স বুঝি দাঁতপড়া মুখ দেখে।
নিত্যি নিত্যি করে বিয়া টাকা লইয়া নব বধুর শখে
মায়ারানির হয় বিয়া একান্নতম বিয়ের দলিল লিখে।
মাতৃত্বের অধিকার হইল মায়ারানি বান্দিখানা থেকে।
বছর গিয়া হইল পুত্র চাঁদমুখ হায় পিতায় নাহি দেখে।
একের পরে দুই হইল মায়ারানি কান্দে স্বামীর শোকে
বাপের আদর পায় না সন্তান গাল-মন্দ কয় লোকে।
এক পুত্ররে ‘ইন্দুর’ ডাকে সবাই জন্মের কিতাব দেখে
যেন পশুকুলে জন্ম তাহার ভাবে গাঁয়ের সর্বলোকে।
একদা সে হয় বিধবা, পতির মরণ না দেখিয়া চোখে
রূপ-যৌবনে ভাটা দেহ বিধবা তাই মানিল মুল্লুকে।
দাসী-বান্দিদের সঙ্গে গৃহস্বামীর যৌনসম্পর্কের বিষয়টি তৎকালীন সমাজে অন্দরমহলের বিলাসিতা বলেই মনে করা হত। মায়ারানি সেই বিলাসিতার নিরাপদ পণ্য ছিল। কেননা সে ছিল বিবাহিত। সন্তান জন্মদানের অধিকার সমাজ তাকে দিয়েছে। মায়ারানির রূপ-যৌবন যখন ভঁাটা পড়ে যায় ঠিক তখনই তার স্বামী বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে!
সতীর আগে পতি মরে না।
বান্দি সতী হতে পারে না।
তাই সধবা হিসেবে বেঁচে থাকার বা সতীত্বের অহংকার তার কেড়ে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন স্বামীর অনুপস্থিতিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় বিধানমতে। মায়ারানি হয় বিধবা। যদিও সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা থাকাকালে বিধবা বা স্বামীর প্রশ্নে টঁু শব্দটিও হয়নি। ভাগ্যিস বিধবা মায়ারানি শুধু দুই ছেলের মা। মেয়ে সন্তান হলে হয়তো বাড়িতে আরও পাণ্ডাবর আসতো। বিশেষ করে বান্দিদের গর্ভে মেয়ে সন্তান হলে তাদেরকে পরবর্তীতে মুনিবদের কন্যাদানের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে গৃহদাসী হিসাবে দান করা হত। যা ছিল ভাটিময়ালের পারিবারিক ঐতিহ্যের বিষয়। এভাবেই বান্দিকুল ছড়িয়ে পরে পরিবার থেকে পরিবারে। অনেক সময় ছেলেদেরকেও গৃহস্থালীর প্রয়োজনে আত্মীয় বাড়িতে প্রেরণ করা হত। কখনও কখনও বান্দি পুত্রের সঙ্গে মুনিবের মেয়ের অবৈধ সম্পর্কের সুবাদে তারা সমাজচুত্য হয়ে সংসার করত। এক সময় ভাটির ময়ালে বিবাহিত মুনিবগণ পান্ডাবরের অভাবে বান্দির গর্ভাবস্থা সামাল দিতে না পেরে বিয়ে করতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে মুনিবদের সঙ্গে বান্দিদের ‘আট্টুয়া’ বা ‘ হাট্টুয়া’ বিয়ার প্রচলন হয়। অর্থাৎ বরের হঁাটুতে মুকুট দিয়ে তাতে মাল্য প্রদান করে বিবাহসম্পন্ন হওয়া। কেননা বান্দিকুল হিসেবে মুনিবকুলের মস্তকে মাল্যদান হলে তা মুনিবের অমর্যাদা হয়। তাই এ প্রথা। বান্দিস্ত্রী সম্পত্তির অধিকার পেলেও সমাজ তা ভিন্ন নজরে দেখে। সন্তাদের বান্দিতরফের সন্তান বলে অবিহিত করা হয়। বর্তমানে ভাটি ময়ালে চৌধুরী বা তালুকদার জাতক বান্দি তরফের অনেক সন্তান জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারী চাকুরীতে উচ্চপদে কর্মরত আছেন। যা সমাজ সভ্যতার বহি:প্রকাশ। তাই দারোগাবাড়ির মায়ারানিও এখন আলাদা বাড়িতে থাকেন সন্তান লয়ে। তাকে কিছু সম্পত্তিসহ বাড়ির ভিটার অধিকার দিয়ে দারোগাবাবু বাড়ি ছেড়েছেন। বাড়ির লতাগোষ্ঠি-সহ গাঁয়ের সকলেই তাদের সাথে সমাজ-নমাজ করে দিন কাটাচ্ছেন। মায়ারানি দুই পুত্রবধু ও নাতি-নাতনি রেখে স্বর্গবাসী হয়েছেন। মহা ধূমধামে দান-দক্ষিণা করে মায়ারানির শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তার ছেলেরা এখন সমাজপতি। দারোগাবাড়ির মানুষ।
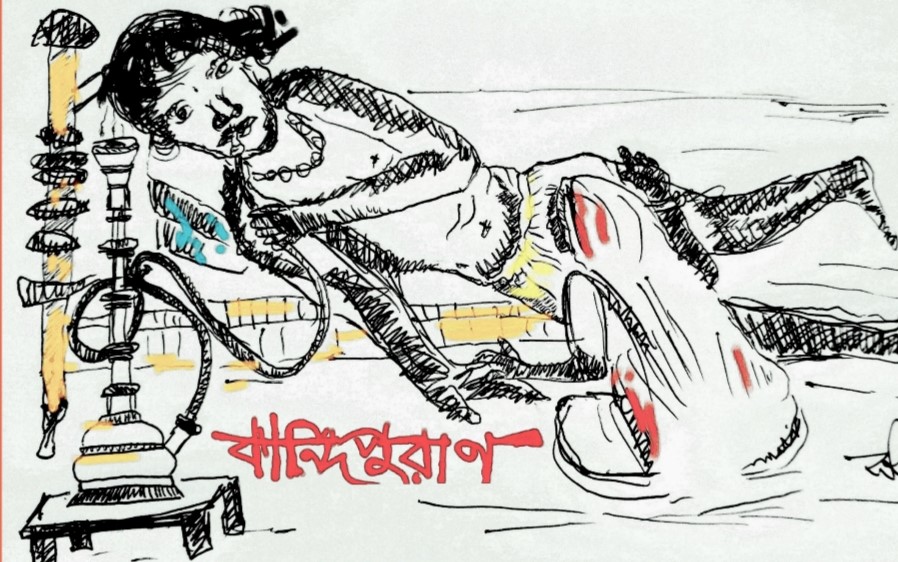
সজলকান্তি সরকার

হাওর গবেষক ও ‘হাওরপারের ধামাইল (হাপাধা) বাংলাদেশ। মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।.
