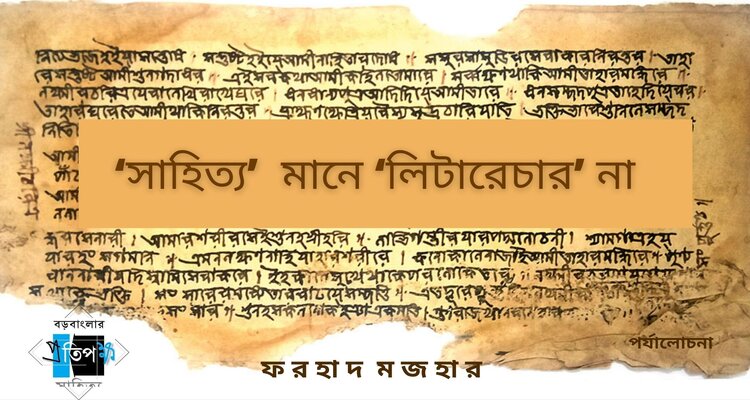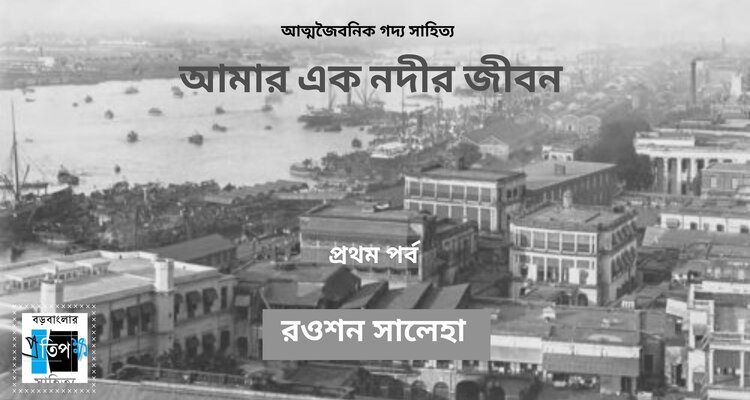
।। রওশন সালেহা ।।
রওশন সালেহার ‘আমার এক নদীর জীবন’ বাংলা আত্মজৈবনিক সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অধীন অবিভক্ত বাংলা এবং পাকিস্তান আমলের পূর্ব বাংলার নানা খণ্ডচিত্র উঠে এসেছিল এই গদ্য সাহিত্যে। বিশেষত অবিভক্ত বাংলায় নোয়াখালী, ঢাকা ও কলকাতার সমাজ জীবন, রাজনীতি, শিক্ষাপ্রসার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ, ইতিহাসের নানা বাঁক ‘আলোকপ্রাপ্ত’ বাঙালি মুসলিম পরিবারের ভিতর থেকে আত্মজৈবনিক কথনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছিলেন রওশন সালেহা। এই রচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে রওশন সালেহা শক্ত স্থান দখল করে নেন। এছাড়াও ‘ফিরে এসো খামার কন্যা’ উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে পরিচিত। আমরা ‘আমার এক নদীর জীবন’ নামক আত্মজৈবনিক এই গদ্য সাহিত্যকে কয়েকটি পর্বে ধারাবাহিকভাবে ‘প্রতিপক্ষ’-এ পুণরায় প্রকাশ করছি।
আমার এক নদীর জীবন (প্রথম পর্ব)

জন্মেই কেঁদেছিলাম
আমি নিশ্চয়ই জন্মে কেঁদেছিলাম। অধিকার ঘোষণার কারণে নয়, নেহাৎ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান একটি শিশু যা করে সে রকম। আমার মাও বেশ জোরে কেঁদেছিলেন। অতঃপর সংজ্ঞা হারিয়ে যায় তাঁর। সবাই বলতো মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।
আমার মায়ের বয়স যখন তের আমি তখন জন্মাই। আমার জন্মের সময়, দিনক্ষণ বলতে গেলে তার চোখে-মুখে কষ্ট এবং বিভীষিকা জেগে উঠতো। আমার স্মরণে আসে, আমি তা লক্ষ্য করতাম। নিজের উপরও রাগ হত, কেন এমন কষ্ট দিয়েছিলাম! মা নিজের কষ্টের কথা বলতেন না, আমি নিজেই তখন বুঝতে শিখেছিলাম।
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের গরম। দেশের বাড়ি। আম-কাঁঠাল পেকে যাচ্ছে গাছে। মা তখন সাত মাসের পোয়াতি। বাড়ির মধ্যে মায়ের ঘরের খাটের তলাকে নিরাপদ জায়গা বলে বেছে নিয়েছিলেন আমার ফুফু, চাচি এরা। ঐ গরম আর কাঁঠালের গন্ধে মা যখন তখন হড়হড় করে বমি করতেন, কাহিল হয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন অতি উঁচু মনের। কাউকে কিছু বলতেন না, এমনকি আমার বাবাকেও না। তার কেবল অবাক লাগতো এরা কাঁঠাল খায়, অথচ তার বাপের বাড়িতে এ হচ্ছে চাকর-চাকরানি এবং গরুর খাদ্য। তারপর তার মন খারাপ হয়ে যেত। অভিমান হত, এত লোক তার তত্ত্ব-তালাশ নিচ্ছে, কিন্তু কাঁঠালের গন্ধ যে সহ্য হয় না— এটি বোঝে না কেন তারা!
দেশাচার অনুযায়ী ‘সাধ’ দেয়া এবং প্রথম পোয়াতিকে পিত্রালয়ে রাখার নিয়মে আমার মামা পাল্কি নিয়ে এসেছিলেন। মাও তৈরি হয়েছিলেন। কিন্তু জেঠাজি আপত্তি তুললেন, অনেক আরজু করে ছোট বৌকে এবাড়িতে এনেছি। আল্লাহর রহমতে ভাইয়ের সন্তানের মুখ দেখব, কিন্তু পথের কষ্ট বৌয়ের শরীরে সইবে না। বিপদ ঘটবে। নৌকার দিন হলে আমি নিষেধ করতাম না। এখন খাল-বিল শুকনা, ঐ পাল্কির ঝাঁকুনিতে কি হয় আল্লাহ মাবুদ জানে। মামা ফেরত চলে গেলেন।
আমার দাদিমা ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। মাকে বুকে টেনে নিয়ে নিজের আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে দিয়ে অনেক আদর করলেন। বললেন, মোহাম্মদ মিঞার উপর এ বাড়ির কেউ আমরা কথা বলি না। ওর দিলে কালি নেই। দেখবে তোমাকে কি রকম আদর-যত্ন দিয়ে রাখে। শ্বশুর পাও নাই, ভাসুর পাইলা। এ বাড়ির সবচেয়ে ভাগ্য ভাল তোমার। তুমি বড় ঘরের মেয়ে। তোমার সমাদর মোহাম্মদ সেভাবেই করবে; পরে আমার কথা বুঝবা। দাদিমার কথাগুলা মা ঠিকমত শোনেন নি, মনের অবস্থা তেমন ছিল না। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন, তাকে এ বাড়িতেই থাকতে হবে, চাচাতো বোনদের মতো তেমন কোনো উদার পরিবারে তার বিয়ে হয়নি। এখানে আসার পর তার যে ভোগান্তি শুরু হয়েছে তার জের সহজে কাটবে না।
দাদিমা বিশেষ বাড়িয়ে কিছুই বলেননি। বড় ছেলেকে তিনি যথার্থই চিনতেন। বাড়ির বৌঝি সকলকে কড়া নির্দেশ দিলেন জেঠাজি, ছোট বৌয়ের যেন কোন প্রকার অযত্ন না হয়। গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে এমন দাই হাজির করলেন, যার হাত যশ আছে। মৌলবী রাখলেন, সর্বক্ষণ মসজিদ থেকে দোয়া-দরুদ পড়তে থাকবে। ‘সাধ’ অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকে করালেন। নানাবাড়ির লোকজনদের নিজে গিয়ে দাওয়াত দিয়ে আসেন। একমাত্র দশ বার বছর বয়সী আমার মামা কয়েকজন চাকরসহ তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল, শুনেছি।
বাবা ছিলেন যেমনি সাদাসিধা তেমনি ভদ্র। বড় ভাই পরিবারের কর্তা, তার উপর তিনি কথা বলতেন না। মায়ের মনের কষ্ট তিনি বুঝতেন কিন্তু এই নিয়ে কথা তুলতেন না। তিনি স্বভাবে স্বল্পভাষী ছিলেন কিংবা ভাবতেন, মেয়েদের এ কষ্ট দূর করার সাধ্য তার নেই। সেই সময় তিনি রাজনীতিতে বেশ নাম করেছিলেন। কলকাতা থেকে আইন পাসকরে সরকারি চাকরিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নোয়াখালী সদরে জজ কোর্টে আইন ব্যবসা করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তাঁদের জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণে আমার জন্ম।
উনিশ’শ উনত্রিশ সালের পহেলা জুলাই। বাবা দিনক্ষণ ডায়েরি করেননি। কিন্তু তাঁর জীবনের উল্লেখ্য সময় ছিল তখন, স্মরণে ছিল তার দিনটি। আহম্মদ মিঞাবাড়ির পূর্ব-উত্তর দিকের টিনের ঘরটিতে শুক্রবার সুবেহ সাদেকের সময় পর্যন্ত তিনি উৎকণ্ঠা নিয়ে বাইরের দিকে সারারাত বসেছিলেন। নবজাতকের কান্না শুনে তিনি দাঁড়িয়ে দু’হাত কানে দিয়ে আযান দিতে যাচ্ছিলেন, খবর পেলেন কন্যাসন্তান। আযান দিতে হবে না। তিনি হাত নামিয়ে নিলেন না, কিন্তু মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ার আযান শুরু হয়ে গেল। বাবা মনের কথা কখনও খোলাখুলি প্রকাশ করতেন না, তখন সেই অবকাশে করলেন, আল্লাহ আমার ইচ্ছা পূরণ করেছেন। শোকর। আলহামদুলিল্লাহ। এদিকে অন্য সকলের মনে হয়েছিল ছেলে হবে। না হলে মা প্রসবকালে এত কষ্ট পায় না। ছেলে বড় হয়ে মাকে রোজগার করে খাওয়াবে, সেটা জন্মকালে উসুল করে নেয়। মেয়ে তো জন্মে পরের ঘরে যাওয়ার জন্যে। তাই সহজে জন্ম নেয়।
প্রসূতির কষ্ট লাঘবে সেযুগে অন্য একটা জিনিসেও বিশ্বাস ছিল মানুষের। মক্কা শরীফে হজ্বব্রত পালন করতে গেলে হাজীরা ‘বিবি মরিয়মের ফুল’ নামে এক ধরনের শুকনো ফুল নিয়ে আসতো, আমার দাদিমা খোঁজ লাগিয়ে ঐ ফুল সংগ্রহ করেন। তিনবার ‘কুল’ পড়ে ফুঁ দিয়ে ফুলটি পানিতে ডুবিয়ে রাখার নিয়ম। তিনি তাই করেছিলেন এবং বৌমাকে দমে দমে এক চামচ করে মুখে দিয়েছিলেন। শিশুর জন্মের পর ‘মেয়ে হয়েছে শুনতে পেলেন মা, ডুকরে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে থাকেন। আমার ছোট ফুফুও বেশি আশা করেছিলেন- বৌয়ের কষ্টের ফল হবে একটি পুত্র সন্তান। তিনি একটি ক্ষোভের ছড়াও কাটলেন। ‘মাইয়া অইলো ভূতের ছালা, ঠেলি ঠেলি হুইত হালা। এগা হুত ঘরের হালা, আল্লাহ দিলে হোনার দলা। ( মেয়ে হচ্ছে ভূতের ছালা, ঠেলে ঠেলে পুকুরে ফেলা, একটি ছেলে ঘরের পালা (খুঁটি), আল্লাহ দিলে সোনার টুকরা)।
শরীর ভাল হচ্ছিল না মায়ের। আমাকে লালন-পালন করতেন মেজ জেঠিমা। কোলে নিতেন বড় জেঠাতো বোন ফাতেমাতুজ জোহরা। সে যুগে ঝিনুক কেটে দুধ খাওয়াতো শিশুকে কোলে নিয়ে। আমাকে সেভাবে দুধ খাওয়াতেন জেঠিমা। পেট ভরতো না বলে সর্বক্ষণ নাকি ট্যাস ট্যাস করতাম। মায়ের কষ্ট তাতে আরো বাড়তো। নিরুপায় হয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে আমাকে কোলে তুলেন, বুকের দুধও দেন, আমি স্বাস্থ্যবান হতে থাকি। খাওয়া আর ঘুম হলে নিশ্চিন্তি স্বভাব হয়ে গেল সে সময়। মা সংসার দেখার সময় করতে লাগলেন। মায়ের কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে জেঠাজি ‘সদ্গা’ মানত করেছিলেন, একটা বড় গরু জবাই করে গরিব-মিসকিন খাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ছোট বৌকে তিনি যেমন জোর করে এ বাড়িতে রেখেছিলেন, এভাবে সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সকলে বলতো এ নাহলে বড় মিঞা! বাটৈয়া ইউনিয়নের মাথা (প্রেসিডেন্ট)।
জেঠাজি কারবারি দরবারি মানুষ। সহসা আকিকা দেয়ার ব্যবস্থা নিলেন এবং সশরীরে হাজির থেকে আমার নানা সিরাজুল হক ভুইঞাকে আকিকায় আসার দাওয়াত কবুল করিয়ে আসলেন।
উনিশ’শ উনত্রিশ সালের পহেলা জুলাই। বাবা দিনক্ষণ ডায়েরি করেননি। কিন্তু তাঁর জীবনের উল্লেখ্য সময় ছিল তখন, স্মরণে ছিল তার দিনটি। আহম্মদ মিঞাবাড়ির পূর্ব-উত্তর দিকের টিনের ঘরটিতে শুক্রবার সুবেহ সাদেকের সময় পর্যন্ত তিনি উৎকণ্ঠা নিয়ে বাইরের দিকে সারারাত বসেছিলেন। নবজাতকের কান্না শুনে তিনি দাঁড়িয়ে দু’হাত কানে দিয়ে আযান দিতে যাচ্ছিলেন, খবর পেলেন কন্যাসন্তান। আযান দিতে হবে না। তিনি হাত নামিয়ে নিলেন না, কিন্তু মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ার আযান শুরু হয়ে গেল। বাবা মনের কথা কখনও খোলাখুলি প্রকাশ করতেন না, তখন সেই অবকাশে করলেন, আল্লাহ আমার ইচ্ছা পূরণ করেছেন। শোকর। আলহামদুলিল্লাহ।
নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে ফেনী) দাগনভুঞাতে বর্ধিষ্ণু গ্রাম উদরাজপুর এবং হাসান আলী ভুইঞাবাড়ি ধনে এবং মানে নামকরা। পরোপকারী এবং নিরহংকারী বলেও সুনাম ছিল। আমার নানাকে আমিও দেখেছি নিজের লুঙ্গি ও টুপি নিজ হাতে সেলাই করতেন। শিক্ষার প্রতিও তিনি অনুরাগী ছিলেন। আমার মাকে বাড়ির বাইর মহলের প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়েছিলেন এবং জামাতা হিসেবে আমার বাবাকে বেছে নিয়েছেন। দাওয়াতে আসার আগে তিনি একটি গরু, একটি খাসি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে নৌকায় রওয়ানা দেন। সাথে নিলেন একমন পোলাওয়ের চাল, ঘি, মিষ্টি, দই ইত্যাদি। দাগনভুঞা অঞ্চলে পোলাওয়ের চাল খুব সুগন্ধী এবং স্বাদের হয়। এখন এই চালের নাম কালিজিরা শুনতে পাই। নোয়াখালীর ভাষাতে ‘সাককর খোরা’ বলতে শুনতাম। আমার নানীমা কিন্তু আসেননি। তিনি সুন্দরীতো ছিলেনই, আবার দাম্ভিকও ছিলেন। কন্যা এবং ভুইঞাবাড়ির বৌ। দালান-কোঠায় থাকার অভ্যাস। মেয়ের টিনের চালার ঘরে থাকতে পারবেন না। গরমে সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। মাকে এবার সাথে করে নিয়ে যাওয়ার কথা বার বার স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিতে অবশ্য তিনি ভুলেননি। নাতনীর নামও তিনি লেখেন ‘বেগম রোকেয়া’। নাম নিয়ে নানারও শখ ছিল। তিনি বলেছিলেন, একটি ভাল মেয়ে চাই, না হলে একটি ভাল সংসার গড়ে তুলবে কে? আমি রাখবো সালেহা খানম। এদিকে আমার বাবা রওশন জাহান ঠিক করে রেখেছিলেন। জেঠাজি ছোট ভাইয়ের বিয়ে নিয়ে অনেক কষ্ট, মনোমালিন্য এবং মনোকষ্ট পুষে এ পর্যন্ত এসেছেন। তিনি আর গণ্ডগোলে গেলেন না। মালার মত সব কয়টি নাম সাজিয়ে আকিকার কাজ সুসম্পন্ন করেন।
একটি চলনসই মধ্যবিত্ত চেহারার বাড়ি, তাতে কোন ঠাঁটবাট নেই। নেই কোন পাকাঘর। এমনকি নামাজের মাচাটিও বাঁশের তৈরি। নারকেল আর সুপারি, আম-কাঁঠাল গাছে ভর্তি জঙ্গলবাড়ির মতো। এমন বাড়ি দেখে নানার মনে কষ্ট হয়েছে, মা তেমন আশংকা করে লজ্জায় পড়লেন। কিন্তু নানার তাতে কোনো দুঃখ হয়নি। কারণ তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন আমাদের আদি বসতবাটি মেঘনার ভাঙনে ভেসে গিয়েছে। এটি আমার দাদিমার পাওয়া পৈতৃক সম্পত্তি। আমার দাদা আহম্মদ মিঞা আদি বাস হারালেও এখানে আসার পর কিছু তালুক ক্রয় করেন ও অন্যান্য খাস ধানি জমি পত্তনি নেন। সস্নেহে মেয়েকে সে সব জানিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন, “মা, তুমি ভাগ্যবতী, তোমার এ ঘর পাকা ইমারত হবে, আমি জীবিত অবস্থায় দেখে যাব এই আশাও করতে পারি।’
মা অন্তরের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিলেন। নানা জিতিয়ে দিলেন তাকে। এদিকে দাদিমা ছিলেন সংসারের একটি খোলা বই, যার ইচ্ছা চোখ বুলিয়ে পড়, বারবার পড় সে ধরনের। নোয়াখালীর দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ আজ ধনী কাল ভিটেমাটিহীন নিঃস্ব। সর্বগ্রাসী মেঘনা তাদের আশপাশে বয়ে যায়। আগুনের সর্বনাশ মানুষের ভিটেমাটি। ধ্বংস করতে পারে না। কিন্তু এই নদী ভিটেও নিশ্চিহ্ন করতে মায়া করে না। মানুষকে স্ত্রী-কন্যার গায়ের গহনা বেচে অন্য ভিটে কিনতে হয়। না পারলে ভূমিহীনের সারিতে শামিল হয়ে যায়। তবুও সে আশায় বুক বাঁধে। এ দিকের মানুষ সহজে হার মানে না। আমার মা এই বই পড়া শুরু করলেন, একবার নয় বহুবার। শেষে নিজেও এক সময় বই হয়ে গেলেন।
শৈশবের অবুঝ মন
সেকালে পুতুল কিনে দিতেন না কেউ। আমরা পুরনো কাপড় পাটশোলাতে জড়িয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় পুতুল বানিয়েছি। কাপড় না জুটেছে বুনো মানুষের মত পাতা পরিয়েছি, পাটের শন দিয়ে চুল বানিয়েছি, পুতুলের বিয়ে দিতাম, মাটির পিঠাপুলি বানিয়ে অনুষ্ঠান করতাম। সময় কোন ফাঁকে চলে যেত, মায়ের খোঁজ পড়তে গোসলের সময়ে; খাওয়া। আর গোসল এ দুটো নিয়ে তিনি বেশি ভাবতেন। ভাইটির শরীর ইতিমধ্যে কিছুটা ভাল থাকছিল।
আমাকে নিয়ে মায়ের সব সময় বুকে ধুকধুকানি, কখন কী করে বসি! জুমাবারে ছেলে জন্ম নিলে বড় ভাল কথা। মসজিদে যাবে, নামাজ পড়বে, ময়মুরুব্বিদের কবর জিয়ারত করবে, কিন্তু মেয়ে হলে তার জন্যে অন্য ঝামেলা। আমাকে নিয়ে মা পেরে উঠছিলেন না। পাটি পেতে মাটিতে শুইয়েছেন কি বসিয়েছেন, আমি হামাগুড়ি দিতে শিখেছি— ব্যস, আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটে খেতে চলে গেলাম পাটির বাইরে। পিঁপড়া, কেঁচো কখনও মুখে পুরে দিয়েছি। মা ঘেন্নায় তক্ষুণি গোসল করিয়ে দিতেন। জ্বর-সর্দি লেগেই থাকতো আমার। শেষে চৌকিতে তুললেন, একদিন গড়িয়ে পড়ে থুতনি কেটে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে, তাই দেখে তিনি অজ্ঞান। অতঃপর হাঁটা শিখতেই, দৌড়াতে পারতাম। পরিষ্কার জামা-জুতো পরিয়ে দিলে কি হবে। ধুলো-মাটি-কাদায় একাকার করতে সময় নিতাম না। অসহ্য মেজাজ করতেও তিনি পারতেন না। কারণ, আমার চেহারা অতি নিরীহ এবং শান্তশিষ্ট ছিল। অন্যরা বলতেন, এ আর নতুন কি, সব বাচ্চারাই এমন করে।
কিন্তু দেড় বছর বয়সে ডান পায়ের গোড়ালির উপর ও হাঁটুর নিচে একধরনের ঘা ও চুলকানি হল এবং চিকিৎসা চালিয়ে যখন ভাল হয় না, ঘা থেকে মাংস পচা গন্ধ বের হচ্ছিল, মা তখন পাগলের মত হয়ে গেলেন। কিছুতেই এ বাড়িতে থাকবেন না, চারদিক নোংরা। বাবা নোয়াখালী সদরে তখন মাত্র ওকালতি শুরু করেছিলেন। যাওয়া-আসার মধ্যে থাকতেন। তিনি মাকে উদরাজপুর রেখে চলে আসেন। সেকালে জামাই শ্বশুরবাড়িতে একদিনের বেশি থাকতো না। শাশুড়িজামাইয়ের সঙ্গে পর্দা করতেন। তাছাড়া আমার বাবার সময়ও ছিল না। আশ্চর্যের কথা হল, আমার ঘা শীঘ্রই ভাল হয়ে গেল। নানাজি বনজ চিকিৎসা জানতেন। তার চিকিৎসাতেই কাজ হয়ে গেল। মায়ের বদ্ধ ধারণা হল কাঁচা বাড়িঘর এবং বাড়ির নোংরা ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে থাকায় আমার ঘা শুকাতো না। যাহোক, আমার ঘায়ের দাগ পড়ে গেল শাদা রঙের এবং নানাজির ওষুধ আরো লাগাতে হতো। কিন্তু বাবা ইতোমধ্যে এসে আমাদের নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। ধুলোবালি মাখা নিয়ে আমি খেলায় মেতে থাকতাম এবং ক্রমান্বয়ে মা শুচিবাইগ্রস্ত হতে থাকেন। আমি তখন তার কাছে যেতে পারতাম না। আমার পরে একটি বোন হল। দেখতে সুন্দর এবং মায়ের মতই পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির। রোববারে জন্ম, সময়ও এমন ছিল না যে মসজিদ থেকে অযাচিত আযান শোনা যাবে। বাবা ওর নাম দিলেন নূরজাহান এবং ওর আদর-যত্ন মা নিজেই করতেন। নিজের বিছানায় শুইয়েছেন। আমি ধুলোবালি ঘাটা মেয়ে, ওর কাছে ঘেঁষতে দিতেন না মা আমাকে। গোসল আর খাওয়া নিয়েও আমি নির্বিকার। জেঠাতো বোন ফাতেমাতুজ জোহরা শিশু থাকতে আমাকে দেখতেন। এ সময়ও তিনি আমার দেখাশোনা করেছেন, মা এ নিয়ে ভাবতেন না। ছোটটিকে মনের মত গড়তে হবে, এটাই ছিল মনে। সুন্দর বোনটাকে আদর করতে গিয়েছি হয়তো, ও নিজেই আমাকে ‘নোংরা’ বলে দূরে সরে গিয়েছে। দেখতে না দেখতে ওর তিন বছর হয়ে গেল এবং আমাদের মায়ের কোলে একটি ছেলে এলো। ভীষণ খুশি হই। বোনের আদর এবার যাবে। ও একলাটি হয়ে আমার সঙ্গে খেলবে। এক সঙ্গে আমরা দু’জন এক বিছানায় শোব।
এর জন্যে আমার উপর প্রচণ্ড ঘষামাজা করা হত। সারাদিন বনবাদাড়ে ঘোরার অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারতাম না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা একজন ঝি সাবান আর ঝিঙের খোসা ঘষে ইচ্ছেমতো পানি ঢেলে গোসল করিয়ে দিত, সেটা মেনে নিয়েছিলাম। এদিকে আমার বাইরে ছুটাছুটি মাঝে মধ্যে মা আটকিয়ে রেখে বন্ধ করতে চাইতেন। ছোট ভাইকে পাহারা দেয়া, ও বিছানা থেকে যদি পড়ে যায়, পেশাব বদলে দেয়া, কাঁদলে নিপল মুখে দেয়া আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হল। কোন কারণে ভাই কাঁদলে মা ছুটে এসে আমাকে বকে রাখতেন না, চড় মারতেন। আমি বাইরে খেলবার জন্যে যাব। ওকে চিমটি কেটে কাঁদিয়েছি। মায়ের মনে বিশ্বাস, আমি কোন কাজের নই, বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের মতো ধাঙ্গড় হয়ে উঠছি। তখন ‘ধাঙ্গড়’ শব্দটির অর্থ বুঝতাম না, নোংরা ও অবাধ্য হয়ে চললে বুঝি এই গালি খেতে হয়— এই মনে হত। আসলে ধাঙ্গড় একটি জাতি, এরা শহরের মানুষের ময়লা, পায়খানা, নোংরা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে। এটা তাদের চাকরি, এর জন্যে বেতন পায়। পরে বুঝেছি।
একটি পুত্র সন্তান মায়ের মধ্যে বেশ পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আগের। মতো আমাকে নিয়ে মেজাজ করেন না। সংসারে তার প্রচুর কাজ বেড়েছে। দাপটও হয়েছে, তিনি তখন ছেলের মা। নানাজির দেয়া নাম সালেহউদ্দিন পাকা করেন। ওর আকিকাও হয়ে গেল আঁকজমক করে। মা আদর করে বাট্টু ডাকতেন। আমরাও সে সঙ্গে। কিন্তু একটা বিষয় মায়ের চোখের ঘুম কেড়ে নিল। ভাইটি প্রায় অসুস্থ থাকে। বাবাকেও এই নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। ডাক্তার, কবিরাজ, ঝাড়-ফুক ইত্যাকার সব রকমের চিকিৎসা ওর জন্যে করা হত। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মাকে দেখতাম মসজিদে বাতাসা (তখন মিলাদে জিলাপির প্রচলন কম ছিল) পাঠাতেন।
ঘরের ভেতর খেলা আমাদের জন্যে অসম্ভব ব্যাপার। হাত-পা ধুয়ে চৌকিতে বসে ছোটখাট কোনো খেলা পর্যন্ত করতে গেলে মা শাসন করেছেন। সারাদিন তো খেলা, এখন ঘুমাও, নয় চুপচাপ শুয়ে থাক। আমাদের তো মন খারাপ। বাইরে অফুরন্ত খেলার জায়গা আর রয়েছে উপকরণ। এত বড় খোলামেলা বাড়ি, পুকুর পাড়, আম গাছ। বিছানায় বসে বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি করতেও দিতেন না।
সেকালে পুতুল কিনে দিতেন না কেউ। আমরা পুরনো কাপড় পাটশোলাতে জড়িয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় পুতুল বানিয়েছি। কাপড় না জুটেছে বুনো মানুষের মত পাতা পরিয়েছি, পাটের শন দিয়ে চুল বানিয়েছি, পুতুলের বিয়ে দিতাম, মাটির পিঠাপুলি বানিয়ে অনুষ্ঠান করতাম। সময় কোন ফাঁকে চলে যেত, মায়ের খোঁজ পড়তে গোসলের সময়ে; খাওয়া। আর গোসল এ দুটো নিয়ে তিনি বেশি ভাবতেন। ভাইটির শরীর ইতিমধ্যে কিছুটা ভাল থাকছিল।
একদিন টুপ করে পুকুরে পড়ে যাওয়ায় আমাদের একটা গোপন খেলার জায়গা প্রকাশ হয়ে যায়। পুকুরের পাড়ে একটি আম গাছ হেলে পড়ে চারটি ডালপালা ছড়িয়েছিল, মাঝে সুন্দর বসার জায়গা পাওয়া গেল। সেখানে ঝিরঝিরে পাতার শব্দ, নিচে পানির হিমশীতল ভাব আমরা মনের সুখে পুতুল খেলতাম, ঝগড়া করতে গিয়েই পড়েছি। তখন হৈচৈ কান্নাকাটি পড়ে গেল। আমি সামান্য সাঁতার জানতাম, গাছের গুঁড়ি ধরে ভেসে থাকি। অন্যরা টেনে তোলে। আমাদের কারো ভয় লাগেনি, বরং মজা পেয়েছিলাম, কিন্তু গভীর উদ্বেগ দেখালেন মা। তার নিয়ম ও সংস্কার মানে না তার মেয়ে। যার বয়স মাত্র পাঁচ শেষ হল, সে? তাঁদের বাড়ির নিয়ম আচার-আচরণ ভাল, ভাল কথা কেন এ বাড়িতে ‘ভাল’ কেউ বলে না! তবে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন না। আমার— লেখাপড়ার সময় ঠিক রাখার জন্যে মাস্টার রেখে দিলেন। আমিও এদিকে পড়াতে মন বসাতে পারি না। বাড়ির অন্যরা হাঁস পালে, পুঁতির মালা পরিয়ে হাঁসকে সাজায়। আমিও করবো। কিন্তু টাকা-পয়সা কোথায় পাব! খেলার সাথীরা বুদ্ধি যুগিয়ে দিল। কেন সকালবেলা উঠে নারকেল, সুপারি কুড়িয়ে জমিয়ে একদিন বিক্রি করবি। ব্যাপারটিতে অন্য ধরনের আকর্ষণ বোধ করি এবং কাজে লেগে যাই। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে আমি পেরে উঠি না, একজন বুদ্ধি দিল সুপারি গাছে উঠতে শেখ। পায়ে দড়ি লাগিয়ে চেষ্টা করতে থাকি, কী করে গাছ বাওয়া যায়। বানরের তৈলাক্ত বাঁশের মাথায় ওঠার মত সাধনা চালিয়ে অন্য বিপদে পড়ে গেলাম। বুকে আঁচড় পড়ে গেল। ছোট বোনকে আমাদের পুতুল খেলায় নিতাম না বলে ওর রাগ ছিল আমার ওপর। মায়ের কাছে নালিশ করে এবং আমি ধরা পড়ে গেলাম যে গাছে উঠছি। প্রচণ্ড রাগে মা ফেটে পড়লেন। নারকেল শলা গোছা করে এমনিতে বেঁধে রাখতেন। দুষ্টামি করলে দু এক ঘা দিতেন। সেদিন অনেক জেদ উড়িয়ে নিলেন এবং আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছি। সেটা ছিল ইচ্ছাকৃত। সকলকে ডেকে হাজির করা। ঘটনাক্রমে তা-ই হল। মেজ জেঠিমা যিনি আমাকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাইয়ে জন্মের পর পালন করলেন, তিনি ছুটে এসে আমাকে আড়াল করলেন। তারপর কেঁদে কেঁদে গান ধরলেন, মিষ্টি গলায়, ‘বাঁশের বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় যে ঘরখানি সেথায় বধূ থাকে লো, সেথায় বধূ থাকে . . .’। আমিও এক অস্বাভাবিক কাণ্ড করে ফেললাম। মা এবং জেঠিমা উভয়েই আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি চিৎকার দিয়ে মাকে বলেছিলাম তোমাকে আমি মা ডাকবো না। এই আমার মা–তুমি চলে যাও এখান থেকে।
আমার মা একটুও রাগ করেননি। শান্ত গলায় বললেন, খুব হয়েছে আর নয়। আমরা দুজনেই তোর মা… দুজনেই আদর করবো। তুই পাগলামি করিস না আর।
বয়সের ব্যবধানে আমি আজ অনেক দূরে। সেই বয়সের আমি সেদিন মাকে যেভাবে দেখেছি এবং পেয়েছি, আজো তা আমার প্রাণ স্পর্শ করে গেল। কিছুক্ষণ কলম তুলে রেখে ভাবনা তাড়িয়ে অনুভব করলাম, জরা বার্ধক্য মানুষের দেহকে আক্রান্ত করে, প্রাণকে স্পর্শ করতে পারে না।
আমার মা সংসারে পুটুলি-সর্বস্ব ছিলেন না। গ্রামের ক্ষেত-খামারের চাষবাস, শহরে বাবার রাজনীতি, রুজি-রোজগার সবটাতে নিজে বুদ্ধি ও মেধা লাগিয়ে পরিচালনা করতেন। আমি যখন মাকে বললাম, কেন গাছে উঠলে কি হয়? আমার কুপরামর্শ দেয়ার সাথীরা দূরে মায়ের হাতে পিটুনি খাওয়া দেখে হাসছিল। ওরা তখন হো হো করে হাসে; বলে, মেয়েদের ভূতে ধরে, বিয়ে হয় না।
বাজে কথা বলছো কেন তোমরা! ও যদি গাছ থেকে পড়ে যেত হাতপা ভাঙতো না? সাবধান করে দিতে পারতে। দুপুর বেলায় বাইরে টো টো করে না। যে যার ঘরে যাও। অমন ভূত তাড়ানো মার খেয়েও আমার কোন ব্যথা ছিল না। মা পিঠে তেল মালিশ করে দিলেন, কি নরম সে হাত, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
একটি কিংবদন্তীর বিয়ে
বাবা রাজনৈতিক কাজকর্মে অধিক মনোযোগ দিলেন এবং সেই সঙ্গে রিপন কলেজে আইন পড়া শুরু করেন। সেকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক দল কংগ্রেসে তিনি কাজ করতেন। সুনাম এবং যোগ্যতার বলে তিনি ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন। (Member of legislative council সংক্ষেপে M. L. C.)। ব্রিটিশ সরকার ভারতের উপর আইন প্রণয়ন করার পূর্বে এখানে বিশদ আলোচনা হতো, বাবার প্রশ্ন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছিল, সংবিধানে উঠেছিল। এক সময় কথা প্রসঙ্গে বাবা আমাকে বইটি দেখিয়েছিলেন, আমাদের বৈঠকখানার আলমারিতে বইটি ছিল, পরবর্তীতে বাবার মৃত্যুর পর খুঁজে পাইনি। সম্ভবত আইন বইসহ নোয়াখালী বার লাইব্রেরিতে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন
ভুইঞাবাড়ির এবং উঁচু প্রাচীরের মধ্যে বেশ কয়েকটি মেয়ে শাড়ি পরা ধরেছে, তখন ছয়-সাত বছরে পড়লেই মেয়েরা শাড়ি পরতো। আমার মা মোসাম্মৎ মাহবুবের নেসা আট বছরে পড়েছিলেন, রূপের খ্যাতি তার ছিল না। গায়ে গতরে চোখে পড়ার মত স্বাস্থ্যও ছিল না। স্কুলে যেতেন, মনযোগ দিয়ে পড়তেন, চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তিও পেয়েছিলেন। এমন মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া আশ্চর্য ঘটনা। এরা তো বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ। মেয়ে লেখাপড়া করে কি জজ-ব্যারিস্টার হবে? সংসার করবে তবে কে? এই ভয়ে মেয়েদের কেউ লেখাপড়া করতে উৎসাহ দিত না, মায়ের ডাকনাম ছিল রূপধন। বোধ করি নানাজি আদর করে এ নামে ডাকতেন। তার বড় মেয়ে চেহারায় আর গায়ের রঙে তারই মতো ছিলো তো!
সময়টা ছিল উনিশ শতকের বিশ থেকে তিরিশ দশকের মধ্যে। দেশে লবণ আন্দোলন চলছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের গরিব জনমানুষেরা সমুদ্রের লোনা পানি থেকে দেশীয়পন্থায় লবণ তুলে জীবন ধারণ করতো। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুরা তাতে হস্তক্ষেপ করে। বিলাতি লবণ আমদানি করতে থাকে। লবণ আন্দোলনের মূলে ছিল দেশের লবণ তৈরি। বিলাতি লবণ কেউ ব্যবহার করবে না। যারা ব্রিটিশঘেঁষা বড়লোকি দেখাত, তারা এর বিরোধিতা করে। সে সময় ভুইঞাবাড়িতে বিলাতি লবণ ব্যবহার করতো। চট্টগ্রামে স্বদেশী আন্দোলনও তখন শক্তিশালী হচ্ছিল। স্বদেশীদের একটা শ্লোগান ছিল, ‘ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইদুরে করলো সারা’, এদের তাড়াতে হবে।
ঐ সময় কলকাতা থেকে বাংলার গভর্ণর, তখন ছোট লাট বলা হত, তার ফেনী আসার প্রোগ্রাম। ফেনীতে রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর ইত্যাদি খেতাব বিতরণ অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু প্রকারান্তরে স্বদেশী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় করাও হয়তো ছিল। দাগনভুঞার গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে মোটরযোগে যাওয়ার পথে স্বদেশীরা বাধা দেয়, তারা এমন শক্ত পিকেটিং করে, ব্যারিকেড দেয় যে, লাট সাহেব ফেরত চলে যান। আসলে রক্তপাত না ঘটিয়ে তারা অন্যভাবে বিদ্রোহ দমনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। বিদ্রোহের নায়ককে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ পদ যেমন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দেবেন খবর করা হলো। ঐ দাগনভুঞা অঞ্চলের বড় বাড়ির ব্রিটিশঘেঁষা কোন পরিবারের মেয়ে আছে কিনা, খোঁজ-খবর শুরু হয়ে গেল। আমার বাবা ঐ গ্রুপের একজন নেতা, ডিশটিংশান নিয়ে প্রথম হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, আমার জেঠাজি বাবার এতদসকল কাজকর্ম পছন্দ করতেন না এবং বাবার সঙ্গে পেরেও উঠতেন না। সুযোগটি তিনি কিভাবে গ্রহণ করবেন. ভাবনা-চিন্তায় পড়লেন। তারপর ভুইঞাবাড়ির বড় হিস্যার বড় মেয়েকে না দেখেই মিঞাবাড়িতে বৌ করে আনার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যান। অপরপক্ষ এ বিয়ে সম্ভব নয় বলে জেঠাজির প্রত্যেকটি পয়গাম ঘৃণাভরে ঠেলে দিতে থাকে। নানাজির আপত্তি চরম, এমন ঘরে তার প্রথম কন্যা তিনি বিয়ে দেবেন না। আমার বাবাও তার বিয়ের পাত্রীকে জানতেন না। তাকে তো ব্রিটিশ সরকারের রক্তচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে-পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। বড় ভাই সংসারের কর্তা, মা জীবিত রয়েছেন। সেকালে নিজের বিয়ের ব্যাপারে মতামত দেয়াকে ভীষণ লজ্জার ব্যাপার বলে ধরা হত। বাবা অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। বয়স তার ত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছিল।
বাবা ছিলেন কম কথার মানুষ, কিন্তু মনের দিক থেকে চিন্তাশীল। বাপ নেই, বড় ভাই অভিভাবক, তার ইচ্ছায় মাদ্রাসায় পড়লেন, ভালভাবে কৃতিত্ব নিয়ে টাইটেল পাসও করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজি শিখবার আগ্রহ তিনি দমিয়ে রাখতে পারলেন না। গোপনে সদরে গিয়ে নোয়াখালী আর.কে. জিলা স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়ে গেলেন। আশ্রয় নিয়েছিলেন এক গরিব বুড়ির কুঁড়েঘরে। এখানে তাকে কেউ খুঁজে পাবে না বলে শহর প্রান্তে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন। কিন্তু ঝাঁটা নিয়ে ঐ বুড়ি একদিন তেড়ে আসে, শিগগির তোর মায়ের কাছে যা, না খেয়ে চোখের সামনে মরবি নাকি? মা থাকতে কাকে ভয়? দাদিমার মুখে এসব শুনতাম, তিনি চোখ মুছে বলতেন, আমার ধন কাক-পক্ষীতে খায়, আমার সন্তান উপোস যায়! আমি মা কাঁদি। বড় ছেলের যেমন জিদ, ছোটটারও তেমন। কেউ আমার কথা শোনে না। শেষে গোপনে সাদু মিঞাকে ধান-চাল এবং সুপারি-নারকেল বিক্রি করে দাদিমা অর্থের যোগান দিয়েছিলেন। বড় ছেলে যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে সে রকম ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। সস্তার দিনের চাল, ক্ষেত খামারে হতোও প্রচুর। আমার বাবার চাহিদাও ছিল সামান্য। দাদিমা বড় ছেলের হাতে ধরাও পড়েননি। নির্বিঘ্নে অথচ গোপনে চারটি বছর বাবাকে খরচ যুগিয়েছিলেন তিনি। তার মনের জোর ছিল সাংঘাতিক। ছোট ছেলের বিদ্যাবুদ্ধিতে তার গভীর বিশ্বাসও ছিল। আমি তাকে যখন দেখি, সে সময় তিনি লাঠিভর দিয়ে হাঁটেন, মুখে বলিরেখা স্পষ্ট, চোয়ালে কোন দাঁত নেই। তবুও তার মুখের হাসি আমার চোখে অদ্ভুত সুন্দর মনে হতো। চেয়ে থাকতাম। ছেলে যে তার একদিন বড় হবে, দেশের একজন নামকরা লোক হবে, ছোটকালে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এই সুন্দর হাসি তার সাফল্য। সংসারে তার খুঁটিও শক্ত করেছিলেন এমনি করে। জেঠাজি ম্যাট্রিক পাসের পর বাবার উপর আর রাগেননি, পড়ার জন্যে খরচ দিতেন। কলকাতা হোস্টেলে থেকে আই. এ. বি. এ এবং এম. এ. পড়ছিলেন। এম. এ (ইংরেজি সাহিত্য) পড়ার সময় রাজনীতিতে নেমে যান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ঘনিষ্ঠ সহকারী হয়ে পড়েন খুব শিগগির। নোয়াখালী জেলার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। বিয়ের ঘটনাও তখনকার বিষয়।
বিয়ের পর নতুন বৌ সাথে করে জেঠাজি কোন বিশ্বযুদ্ধ জয় করারমত আনন্দ নিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। গ্রামের মেয়ে এবং বৌ-ঝিরা বৌ দেখতে ঝাপিয়ে পড়ে। মোহাম্মদ মিঞা লাখ টাকা দিয়ে কাকে আনলেন, বাটৈয়া আর উদরাজপুরে যাতায়াত কয়’শ কয় বার তিনি করেছেন। রাস্তার ঘাস মরে গিয়েছিল। বৌখানি নিশ্চয়ই সোনার বরণ হবে। আমার ছোট ফুফু তড়িঘড়ি পাল্কির দরজা খুলে কাপড়ের পুটুলি বের করে। মায়ের মুখ উদোম হতেই, তিনি হায় হায় করে ওঠেন। তারপর চেঁচিয়ে বলেন, “বাইছাব, ইয়া কি আইনছেন, এগগা কাউ-আ এ না … আডি আডি হঁতের দুব্বা মারি, বোইরের ক্ষুরা ক্ষয় করি হালাইছে ইয়ান আইনতো! বাইছাবের চোখে ছানি ছিল নি?( কী এনেছে, একটা কাক, হেঁটে হেঁটে পথের দূর্বা মাড়িয়ে পায়ের গোড়ালি ক্ষয় করে ভাই সাহেব কি এনেছেন? তার চোখে ছানি পড়েছিল কি?)
জেঠাজি শুনতে পেয়েছিলেন কথাগুলো। বোনের উপর রাগ করলেন, চড় থাপ্পড় দিতে গিয়ে সামাল দিলেন, বললেন, সেবাযত্ন কর, বড় ঘরের মেয়ে পা দিয়েছে এ বাড়িতে, রূপ ধুয়ে পানি খাবি নাকি? রূপ তোরও আছে, কথা বলতে শিখলি না। আর যদি এ রকম কথা শুনি বাড়ি থেকে বের করে দেব।
মা ছিলেন শ্যামলা রঙের মিষ্টি চেহারার, দেখতেও ছোটখাট। ফুফু তার বিদ্বান ভাইয়ের জন্যে রূপসী বধূ আসবে আশা করেছিলেন, কিন্তু বড় ভাই বকুনি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলেন, এই বৌ তার অতি আদরের ধন, বাড়ির মান-সম্মান একধাপ উপরে তুলতে পেরেছেন তিনি একে বাড়িতে আনতে পেরে, এ তার বড় বিজয়। এদিকে মা নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে বুঝতে পারলেন, তিনি পুতুল খেলার বয়স নিয়ে এ বাড়ি এলেও তাকে কেউ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারবে না, তার শক্ত খুঁটি আছে। তিনি ভুইঞাবাড়ির মেয়ে।
বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলেই অনুষ্ঠানাদি শেষ হয় না। বাংলাদেশে ‘ফিরানি’ নামের বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে। মেয়ের বাবার বাড়ির লোকেরা অর্থাৎ মেয়ের বাবা, চাচা-এ জাতীয় মুরুব্বিরা এসে মেয়েজামাই ফেরত নিয়ে যান। জাঁকজমক করে ‘বৌভাত’ করে তাদের খাওয়ানো হয়। আমার মায়ের বিয়ের ঘটকালি, বাজার-সদাই এবং বিয়ের অনুষ্ঠান জেঠাজি করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীর উপর অধিকার বর্তায় স্বামীর। আমার বাবা তখন যে আন্দোলনে ছিলেন। সেটি ছিল দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার। গ্রামের ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটা এবং তাতে কাপড় বুনন করাতেন তারা এবং সকলকে মোটা শাড়ি পরার জন্যে বলতেন। বিলাতি দ্রব্য বর্জন এবং তাদের স্থাপিত কলকারখানার জিনিস ব্যবহার না করার আন্দোলনে ছিলেন বাবা। কিন্তু মায়ের পরনে লেসের কাজ করা সেমিজ আর মিহিন বেনারসি শাড়ি। সহসাই বাবা হাতে বোনা তাঁতের মোটা শাড়ি মাকে পরিয়ে দিতে বললেন জেঠীমাকে। বিয়ে করে তিনি নীতি বিসর্জন দিতে পারেন না। মা নির্বিকার। তার পরনের সুন্দর ফিনফিনে শাড়ি খুলে মোটা এবং খসখসে নীলের উপর উলের সুতায় ফুল তোলা এক ভারি শাড়ি পরিয়ে দেয়া হল। কাঁন্নাও নাকি চোখে ছিল না। এ বাড়ির সবকিছু অন্যরকম, এখানে থাকতে হলে সে রকম চলতে হবে, খটখটা চোখে বুঝে নিলেন। তাছাড়া স্বামীর আন্দোলন করার কথা তিনি জানতেনও। ব্রিটিশ প্রভুদের বিরুদ্ধে তিনি লড়ছেন। এইতো ভাল কথা। কিন্তু মনে প্রবোধ পেলেও শরীরতো অভ্যাসের দাস। গরমের মধ্যে জড়িয়ে পেঁচিয়ে সেমিজ ছাড়া শাড়ি তার শরীরকে নানাস্থানে ছিঁড়ে দিল, ঘামাচি ফুটে সারা গা গুইলের চামড়া হয়ে গেল। মায়ের অস্থিরতা নিবারণের জন্যে কয়েকজন বড় ছোট মেয়ে হাতপাখা দিয়ে অবিরাম বাতাস দিয়ে যাচ্ছিল। পিঠাপুলি দই-মিষ্টি চোখ দিয়েও মা দেখতেন না, শুধু পানি, লেবুর শরবত খেয়েছিলেন।
যথারীতি ফিরতি যাওয়ার আগে বৌ ভাতের আয়োজন করা হল। কিন্তু অন্য এক গুরুতর পরিস্থিতিতে পড়ে মা ঐ বালিকা বয়সেই বুদ্ধি করে সামলিয়ে ছিলেন। স্বামীর রাজনৈতিক সম্মান হাসিমুখে মাকে উন্নত রাখতে হয়েছিল। জেঠাজি বিয়ের জিনিসপত্র কিনেছিলেন, বাবা জানেনও না। ওদিকে পিত্রালয়ের শাড়ি-গহনা, সব জিনিসই ছিল বাবার আদর্শের বিপক্ষে। বাবার পার্টির লোকেরা শাড়িগুলো পুড়িয়ে। দেয়ার কথা তোলে। এদের মধ্যে আমার মেজ ফুফাও ছিলেন; তিনিও খদ্দর পোশাক পরতেন, মৃত্যুর পর খদ্দরের কাপড়ের কাফন পরার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। ঘরের লোক, তিনি মায়ের চাবি নিয়ে সব নিয়ে গেলেন, মা খুশি মনে দিয়েও দিলেন। বাড়ির উঠানে শাড়িগুলো পুড়িয়ে দেয়া হল। গহনাগুলো জমা দিয়ে আসেন চৌমুহনীর খাদি প্রতিষ্ঠানে। আরো তাঁত বসাতে টাকার প্রয়োজন। কিন্তু একজন বালিকা নববধূর কাছে এসব কি কোন অর্থ বয়ে এনেছিল? এই অসম্ভব কাজ তিনি কি করে সহজে মেনে নিয়েছিলেন? জানার কোন পথ ছিল না। জেঠাজি মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। ছোট ভাইয়ের কার্যকলাপে নতুন আত্মীয়তা কী রূপ নেবে অতঃপর তিনি চিন্তিত হন এবং ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিলেন। ভাইয়ের হিস্যা ভাগ করে দিয়ে তিনি পৃথক হয়ে যান। জেঠিমায়েরা এসব নিয়ে কোন প্রকার আলাপ করার সাহস পর্যন্ত করতেন না। তবে মায়ের ধরন-ধারণ এবং সাদাসিদা বেশভূষা দেখে তারা মনে করতেন ‘ছোট বিবি’ বয়সে ছোট কিন্তু একবার যা খুলে নেয়া হয়েছিল, তা আবার গায়ে তুলবেন না। সে রকম জিদ তার অঙ্গে রয়েছে। কিন্তু তার কথাবার্তায় কখনও রাগ অথবা হা-হুতাশ অথবা আক্ষেপ ছিল, সেটি কেউ বলেনি। এমনই গভীর জলের মাছ ছোট বিবি।
ফিরানি করার জন্যে মা গিয়েছেন। নানীমা মেয়ের হাল দেখে সহ্য করতে পারলেন না, মূর্ছা গেলেন। তার মত ছিল না, কিন্তু বন্ধও করতে পারেননি মেয়ের বিয়ে। আদরের মেয়ে ফকিরনীর মতো ফিরে এলে কোন্ মা সে দৃশ্য চোখে দেখতে পারে! মেয়ে আটক করে রেখে দিলেন। নানাজি এবার কোন উচ্চাবাচ্য করেননি। মেয়ের নাস্তানাবুদ অবস্থা দেখে তিনিও কষ্টে মূহ্যমান ছিলেন।
রাতের অন্ধকারে শাড়ি পোড়ান হয়েছিলো। কিন্তু তা রইল না গোপনে। লোকের মুখে মুখে রটে গেল সবখানে। ব্রিটিশপন্থীরা স্বদেশীদের ‘ডাকাত’ বলতে শেখাত সাধারণ মানুষদের। তবে তাদের কাছে এ ছিল সম্মানের, দুঃসাহসের এবং তাই আদরের। ঐ অঞ্চলে এ কাহিনী কিংবদন্তী হয়ে গেল। এসব ঘটনা ইতিহাসে স্থান পায়নি, কেউ এতদাঞ্চলের মেয়েদের ত্যাগ ও সেবার কথা লিখে যায়নি, তবুও ঐ সময়ের কেউ যদি বেঁচে থাকেন, আজও সম্ভ্রমের সাথে সেসব কাহিনী বলবে, বলবে আগুনে কিকি পুড়ে ছাই করা হয়েছিল, গহনাগুলো সেরদরে বিক্রি করা হয়েছিল এবং সেই সাথে কোনো এক বালিকা বধূর নিরাভরণ সৌন্দর্যের কথা। যতটা ভয় করা হয়েছিল, ঘটনার রেশ ততদূর গড়াল না। মা যে অসাধারণ এ বিষয়ে বাবা নিশ্চিন্ত। কলকাতায় তার বিস্তর কাজ, কালবিলম্ব না করে পাড়ি জমালেন। রাজনৈতিক কাজকর্মে অধিক মনোযোগ দিলেন এবং সেই সঙ্গে রিপন কলেজে আইন পড়া শুরু করেন। সেকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক দল কংগ্রেসে তিনি কাজ করতেন। সুনাম এবং যোগ্যতার বলে তিনি ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন। (Member of legislative council সংক্ষেপে M. L. C.)। ব্রিটিশ সরকার ভারতের উপর আইন প্রণয়ন করার পূর্বে এখানে বিশদ আলোচনা হতো, বাবার প্রশ্ন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছিল, সংবিধানে উঠেছিল। এক সময় কথা প্রসঙ্গে বাবা আমাকে বইটি দেখিয়েছিলেন, আমাদের বৈঠকখানার আলমারিতে বইটি ছিল, পরবর্তীতে বাবার মৃত্যুর পর খুঁজে পাইনি। সম্ভবত আইন বইসহ নোয়াখালী বার লাইব্রেরিতে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন।
দিল্লির পাঠ উঠে গেলে বাবা কলকাতায় ফিরে আসেন, আইন পড়ায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। তখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজও করেন। উর্দু ভাষায় প্রাইমারি স্কুলের জন্যে অংক বইও লিখেছিলেন। বইটিতে ছবির সাহায্যে সংখ্যা, যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ শেখানোর পদ্ধতি ব্যবহার করেন তিনি। প্রাইমারির গরিব শিশুদের মুখে বাংলা ছিলো না। ভুল উর্দুতেই কথা বলতো। ওদের শিক্ষার কথা ভেবেই উর্দুতে লিখেছিলেন।
তখন বাসা ভাড়া করে মাকে কলকাতায় নিয়ে যান। আমার ফুফাতো ভাই আব্দুর রউফ চৌধুরীও তখন আইন পড়ছিলেন। মামা এবং ভাগনে একসাথে পরীক্ষা দিয়ে ভাগ্নে মুন্সেফের চাকরি নিলেন। কিন্তু বাবা স্বাধীন আইন ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে নোয়াখালী চলে আসেন। বাড়ির পূর্বের ঘরটিতে মাকে নিয়ে উঠলেন। তিনি অন্তঃসত্ত্বা। প্রথম সন্তান ধারণ করছিলেন দেহে। কিংবদন্তীর নায়ক এবং নায়িকা যারা, আমার গর্ব-তারা, তাদের নিয়ে এত কথার গৌরচন্দ্রিকা দিয়েছি এই লক্ষ্যে যে, আমার জন্ম হয়েছিল মিঞাবাড়ির মাটির গন্ধ নিয়ে। জেঠাজি পরম ধৈর্য এবং সহনশীলতা দেখিয়ে এ দিনের অপেক্ষা করেছিলেন। ভুইঞাবাড়ির মেয়ে এনে যে বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন, তা এভাবে তিনি পাকাপোক্ত করেন। তবে নানাজির উদারতা এবং নিরহংকার চরিত্র গুণে এতটা সম্ভবপর হয়েছিল, তা সকলেই শ্রদ্ধাভরে আজো বলে থাকে। নানা সিরাজুল হক ভুইঞা দাগনভুঞা কামাল আতাতুর্ক হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।
গ্রাম থেকে বিদায়
খেলতে যদিও দিত না নানীমা, কাছে কাছে রাখতেন আমাদের। কিন্তু কেটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন, দালান ঘরের জানালার তাক। এত চওড়া ছিল সেটা-আমরা দু বোন হাড়ি পাতিল, পুতুল-বিয়ে এসব স্বচ্ছন্দে খেলতাম। ঐ বয়সে সুঁই-সুতো হাতে ধরিয়েও দিয়েছিলেন তিনি। একদিন পুতুলের সেমিজ সেলাই করছিলাম। নিজের ফ্রকটাও সেটার সাথে জুড়ে সেলাই হয়ে গেল, দেখিনি। আমি ভীত হয়ে গেলাম। নতুন ফ্রক, নানীমা নিশ্চয়ই মারবেন। সুতো ছিড়ে খুলে নেয়া যায়, মাথায় এ বুদ্ধি এল না, দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ফ্রক ছিড়ে দিলাম। নানাজিকে সেলাই করতে দেখতাম। লুকিয়ে তাঁকে দেখাই, তিনি সুতা খুলে নিলেন এবং ঐ ছেঁড়া ফ্রক রিপু করে দিলেন। নানীমাব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু চুপ থাকলেন। আমরা আরো ভয় পেয়ে গেলাম। খেলা যদি বন্ধ করে দেন? তাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি ঐ জানালার তাকে বসে খেলতাম। পুতুলের জামা সেলাই করতাম। সেলাই যে শিখছি, নানীমা বকবেন কেন! সেলাই-এর হতেখড়ি সেই থেকে হয়েছিল আমার।
গ্রামে জন্মেছি, বড় হয়েছি। ভাল লাগতো মেঠো পথ ধরে মন ছুটিয়ে দিতে। কেউ যদি বাইরে যেত, বাড়ির কেউ হোক, চাকর-মিন্তি যে কেউ হোক, বড়দের চক্ষুর আড়াল পেলেই ঐ মেঠো পথে বেরিয়ে পড়তাম। ডোবায় পাট ভিজিয়েছে, সেগুলো পঁচে গেলে তুলে ছাল ছাড়িয়ে পানিতে আছাড় দিয়ে যা বের করতো, দেখতাম ময়লা কাদা নেই, ঝকঝক করছে পাটের আঁশ। ওখানকার পচা গন্ধ নাকেও লাগতো না। কেউ মাছ ধরার জন্যে জাল ছড়িয়েছে। মাছ যা উঠলো, তার থেকে দেখতাম কাঁকড়া উঠলেই চিৎকার দিতাম খুশিতে। আমার ধোপানী বান্ধবী সবিতাকে খবর দেব। আমরা খেতাম না। ভীষণ ইচ্ছে হত টেস্ট করবো-কিন্তু সবিতাই দিত না। ঠাকুরাণ তোকে মারবে। আমার মাকে ওরা ‘ঠাকুরান’ বলতো— যদিও মা পছন্দ করতেন না। উনি শিখিয়ে দিতেন ‘ছোট বিবিসাব’ ডাকার জন্যে। সবিতার কাঁকড়া পুড়িয়ে খাওয়া দেখতেও আমি চাইতাম। শুকনো পাতা জড়ো করে কারো থেকে ম্যাচের কাঠি চেয়ে নিয়ে (বিশেষ করে চাকরদের বিড়ি খাওয়ার জন্যে ওটা সাথে থাকতো) আগুন ধরিয়ে পুড়ে, খোসা ছাড়িয়ে গরম গরম খেয়ে ফেলতো। ওদের মজার খাওয়া আমাদের জন্যে কেন নিষেধ? সবিতা বলতো, হিন্দুদের খাওয়া। আবার তোরা গরু খাস, আমরা গরুকে দেবতা ডাকি, খাই না। ভয়ে মাকে কখনও এসব বলতাম না। সবিতাদের ঘরের পিঠা, সন্দেশ খেতেই আমার লোভ ছিল।
বাবা শহরে থাকেন। শনিবার সন্ধ্যায় আসেন, সোমবার ভোরে উঠে চলে যান। শুকনোর দিনে হেঁটে আসেন যান, বর্ষায় নৌকায়। একটাঘরে তার মুহুরিদের নিয়ে দিনে অফিস, রাতে শোয়া, হোটেল থেকে খাওয়া। মা যাওয়ার কথা বলেন, বাবা চিন্তা করেন আর কিছুদিন পর যাওয়া হতে পারে। দশগণ্ডা জমি কিনেছি। বৈঠকখানা ঘর হয়েছে, ভেতরের ঘরগুলো তুলতে হবে। পানির কষ্ট হবে। একটা পুকুর, চারপাশে কত লোকের বাস। ‘তোলা পানিতে আপনি চলতে পারবেন না।’
আমার বয়স তখন ছয় হবে। এসব কথা শুনতাম, আর আল্লাহকে ডাকতাম। যেন শহরে যেতে আরো দেরি হয়। পুকুর নেই বাড়িতে। দশগন্ডা কতখানি জমি? ওতে কি থাকা যাবে! শহর খুব কষ্টের জায়গা বলে মনে হত। বেশি করে আল্লাহকে ডাকতাম। সেই বয়সে নানার বাড়িকেই আমার কাছে শহর মনে হতো। রাস্তাঘাট, দালানবাড়ি, স্কুল, মসজিদ সবই দেখার মত ছিল। যেই মাত্র আমরা নানারবাড়িতে পৌঁছেছি এবং বাড়িতে ঢুকেছি, মা-খালা-নানী জড়াজড়ি করে একদফা কেঁদে নিতেন। বহুদিন ভেবে কূল করতে পারতাম না, বেড়াতে এসে এত কান্না কেন? অতঃপর খালারা দুজন আমাদের দু বোনকে নিয়ে পড়তেন, দেহের ঘষামাজা কাকে বলে! চোখ দিয়ে পানি এসে যেত, তবুও কাঁদতাম না। একখানা গোটা সাবান, ঝামা; ধুনদুলের খোসা ঘষতে ঘষতে খালারা কাহিল হয়ে যেতেন। কিন্তু নানীমা ছাড়ার পাত্রী ছিলেন না। অবজ্ঞাভরে বলতেন, নাক সিঁটকাতেন, ওরে গেরস্ত বাড়ির ময়লা এক গোসলে কি যায়! আরো পানি ঢালতে থাক। কিছু হবে না। মেছোনি দুটোর চেহারা দেখ। পানিতে সারাদিন ভিজলেও জ্বর আসবে না। ওসব হল ভদ্রলোকের জন্যে। আমার ছোট বোনটির এতটা অত্যাচার সহ্য হতো না। হাঁচিকাশি দিত এবং মা এসে বলতেন, নূরজাহান আমার কথা শুনে চলে, অবাধ্য হয় না। ওকে ছেড়ে দিন আম্মা।
শুদ্ধি অভিযানের আর এক পর্বের কথা এখন বলছি। পিতলের কলস সোনার মত ঝকঝক করে মেজেঘষে আনা হল। তাতে পানির বর্ণও সোনালি দেখায়। ওর মধ্যে সোনার আংটি এবং কোমরের রূপার বিছা নানীমা ডুবিয়ে রেখে তারপর ঐ পানি মাথার উপর ঝরঝর বৃষ্টির মতো করে আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে ঢালতেন নিজে। আগের জামা আগেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হত। নতুন জামা পরিয়ে দিয়ে নানী মা ক্ষান্ত দিতেন। হাসিমুখ— আহা কী সুন্দর রঙ! মাটি কাদায় চাপা পড়ে ছিল। রূপধন তোর মেয়েদের দিকে তাকা একবার। মিষ্টি হাসির উত্তর ছাড়া মাকে তখন কথা বলতে শুনিনি। মাথা এবং পা এ দুটো নিয়েও নানীমার তুলকালাম কাণ্ড দেখতাম। চুল ছাড়া রাখে পেত্নীরা, পায়ে জুতা খড়ম রাখে না ছোট জাতেরা। তোদের বাড়ির জাত অভ্যাস এখানে দেখাবি তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব।
মাথায় তেল দিয়ে, দুই বিনুনি বেঁধে দিতেন নিজ হাতে। পায়ের জুতো নানাকে ফেনী পাঠিয়ে কিনে এনে দিয়েছিলেন। পা ধোওয়ার সময় কাঠের খড়ম রেখে দিতেন আমাদের জন্যে। আমার মধ্যে এত ভাল থাকার বিরুদ্ধে রোষ জেগে উঠতো। এত কড়াকড়িতে হাঁপিয়ে উঠতাম, সেজন্যে কখনও অবাধ্য হয়েছি। আমার জন্যে মা বকুনি খেতেন। তোর জন্যে ইজ্জত যাচ্ছে আমার, তাদের মেয়ের চলাফেরা দেখলে বাড়ির বৌ-ঝিরা কি বলবে, গৃহস্থ বাড়ির মেয়ে, বাপ উকিল হয়েছে তো কী! ছোটলোকের স্বভাবতো যায়নি। রূপধন, তোকে কি আমি এমনি করে বড় করলাম। মেয়েদের চলন-ফেরন ভদ্রলেঅকের মত হচ্ছে না কেন? বুঝেছি ঐ বাড়ির অন্য মেয়েরা যেমন চলে, তোর দুটোও তেমন হচ্ছে। জামাইকে এসব বলবি। সে এখন শহরে থাকে। ছোটখাট বাসা করে তোদের যেন নিয়ে যায়। ছেলেটা এখন কোলে, ওটা বড় হলে সর্বনাশের কথা হবে। মানুষ না হয়ে হবে গরু-ছাগল।
ভুইঞাবাড়িতে নানীমা চলাফেরা, রান্নাবান্না, সেলাই ইত্যাদিতে অতি উঁচুমানের ছিলেন। তার নাতনীদের এহেন বড় হওয়া তাকে দুঃখ দিত, সহ্য করতেও পারতেন না। আমাদের খাওয়ার অভ্যাসও তার অপছন্দ ছিল। রান্নাঘরের পাশে খাওয়ার জায়গা ছিল, চুলার পাশে পিড়ি পেতে খাওয়া তিনি একদম পছন্দ করতেন না। অথচ আমি তাড়াহুড়ো করে ওরকম খেতে চাইতাম, কি জানি ভালও লাগতো। নিয়মমতো খাওয়া, যেমন ভোরে পিঠা ও দুধ, দশটার দিকে পোলাওয়ের চালের ভাত ওডিম, দুপুরে গোসল করে নানান তরকারি, মাছ-গোস্ত সহকারে সরু চালের ভাত, বিকেল বেলায় পরিচ্ছন্ন হয়ে খই, মুড়ি, নারকেলের নাড়ু ইত্যাদি। বেলের শরবত, সন্ধ্যার পর রাতের খাওয়া। রাতে শুধু গোস্ত-ভাত। এমন খাওয়া পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি। আম-জামের দিনে, কি আখের মৌসুমে ঘরভর্তি করে রাখতেন নানা এবং নানী উভয়েই। নানীমা এ ব্যাপারে উদার ছিলেন।
বিকেলে সেজেগুজে নানাজির হাত ধরে আমরা দু’বোন ভেতর বাড়ির আংগিনা ও দেয়াল পেরিয়ে যখন বাইরে বের হতাম, তখনকার আনন্দ অবিনশ্বর। আমি তখন পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পা দিয়েছি, আমার বোনও তিনে … নানাজি তাদের বিরাট বাড়ি বিভিন্ন শরিকদের বৈঠকখানা, মসজিদ, মুসাফিরখানা ঘুরিয়ে মাগরিবের আজান দিলে এরপর আমাদের অন্দরমহলে রেখে নিজে নামাজের জন্যে চলে যেতেন।
খেলতে যদিও দিত না নানীমা, কাছে কাছে রাখতেন আমাদের। কিন্তু কেটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন, দালান ঘরের জানালার তাক। এত চওড়া ছিল সেটা-আমরা দু বোন হাড়ি পাতিল, পুতুল-বিয়ে এসব স্বচ্ছন্দে খেলতাম। ঐ বয়সে সুঁই-সুতো হাতে ধরিয়েও দিয়েছিলেন তিনি। একদিন পুতুলের সেমিজ সেলাই করছিলাম। নিজের ফ্রকটাও সেটার সাথে জুড়ে সেলাই হয়ে গেল, দেখিনি। আমি ভীত হয়ে গেলাম। নতুন ফ্রক, নানীমা নিশ্চয়ই মারবেন। সুতো ছিড়ে খুলে নেয়া যায়, মাথায় এ বুদ্ধি এল না, দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ফ্রক ছিড়ে দিলাম। নানাজিকে সেলাই করতে দেখতাম। লুকিয়ে তাঁকে দেখাই, তিনি সুতা খুলে নিলেন এবং ঐ ছেঁড়া ফ্রক রিপু করে দিলেন। নানীমাব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু চুপ থাকলেন। আমরা আরো ভয় পেয়ে গেলাম। খেলা যদি বন্ধ করে দেন? তাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি ঐ জানালার তাকে বসে খেলতাম। পুতুলের জামা সেলাই করতাম। সেলাই যে শিখছি, নানীমা বকবেন কেন! সেলাই-এর হতেখড়ি সেই থেকে হয়েছিল আমার।
মামা থাকতেন ফেনীতে, হাই স্কুলের ছাত্র। বাড়িতে আসার পর মা তাকে ধরলেন আমাদের রেখে আয়। বাড়িঘর খালি, ধান-চাল চুরি হয়ে যাবে। গোলাঘর নেই বাড়িতে। খোলামেলা পড়ে রয়েছে। আসলে বাবা সপ্তাহের রোববার বাড়িতে আসেন। মা সেই অসুবিধের কথা ভাবতেন, কিন্তু বলতেন না। এদিকে নানীমা আমাকে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, মা কোনো কথা বলেন না। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়েছেন। নানীমা গোস্বা করলেন, এভাবে যদি যাস, আর কখনো আসবি না। চোখ ভিজে গেলে তিনি আর কি করবেন, আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তুই থাকবি আমার কাছে। কিন্তু কে থাকবে! আমরা চলে আসি। ফেরার পথে আবারও জড়াজড়ি করে মায়েরা সবাই কাঁদলেন।
গরুর গাড়িতে আমরা যাত্রা করলাম। রাস্তা এত ভাংতি গর্ত যে গরুকে মেরে মেরে তাড়া করছিল গাড়োয়ান। মামা বসেছিলেন বাইরে গাড়োয়ানের সাথে, আমরা পর্দায় ঘেরা ঢাকনির ভেতরে। ঝাকুনিতে একেবারে কাহিল। মা একবারও কোল থেকে নামিয়ে রাখেননি শিশু পুত্রকে। আমরা ‘ওডার হাটে’ (একটি স্থানীয় বাজারের নাম) পৌঁছলে গাড়োয়ানকে একটি বটগাছ তলায় গাড়ি রাখতে বলেন মামা। গরু দুটোকে পিঠে ছড়ি পেটা করে লাভ হচ্ছিল না। ও দুটো একটু গিয়ে, হাঁটু ভেঙে বসে যাচ্ছিল। বটগাছটি বেশ পুরান, ছায়া শীতল স্থান। আমাদের সেখানে রেখে মামা হাট থেকে বিস্কুট আর টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে যান। গাড়োয়ান গরুকে খড় আর ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেল। দূরে পুকুর দেখে পানি খাওয়াতে নিল পরে।
গাড়ির পর্দা সরিয়ে বাইরে বসি। মা তাকিয়েই বললেন, জায়গাটা ভাল না, ঐ দেখ, কালীপূজার মণ্ডপ, জবা ফুল দিয়ে কত লোক সকাল বেলায় পূজা দিয়েছে, কুলহু আল্লাহ পড়, ভূত-প্রেত কাছে-কিনারে থাকতে পারে। গাড়ির পর্দা টেনে দিয়ে মা ভেতরে বসেন, আমাদেরও টেনে নিলেন। হঠাৎ ছোট ভাই তারস্বরে কাঁন্না জুড়ে দিলে মা দরূদ পড়া শুরু করলেন। একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল তখন, বট গাছের একটি ডাল গাড়ির ছাউনিতে ঝাকুনি দিল একবার। মা এত ভয় পেলেন, মুখে দুরূদ পড়াও নেই। ভাইকে জাপটে ধরে আছেন, ভীষণ কাঁপুনি গায়ে। মামাও ফিরে এসে দেখেন আমরা ভয়ে কেমন যেন হয়ে আছি। মা কোনোমতে বললেন, ভর দুপুরে কালীর মণ্ডপ বড় খারাপ জায়গা, হিন্দুরাও এ সময় আসে না এমন জায়গায়, তোরা গাড়ি থামিয়ে ভাল করলি না। আমার কী জানি ভয় লাগছে। যেটা আমায় ভয় দেখিয়েছে, সেটা যদি আমাদের সাথে লয়। কী জানি!
মামার ভয়ডর নেই, বুক চিতিয়ে বলে দিল, আসুক না। মেরে ঠ্যাং ভেঙে ঐ কালীমন্দিরে ঢুকিয়ে দেব। ভয় করিস কেন বুবু? আমি তো আছি বলে মামা গরুর লেজ ধরে হেঁই হেঁই করে তাড়া দিল। গাড়ি চলা শুরু করে। মায়ের মুখের ভয় রয়েই গেল। তিনি বললেন, তোর ভাগ্নেটার জন্যে ভয় করছি, ওর কিছু হলে আমি বাঁচবো না রে, সন্ধ্যার আগে বাড়ি পৌঁছাতে পারবি তো!
মাত্র দু’মাইল পথ বাকি ছিল। সন্ধ্যার বেশ আগে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। সেদিন শনিবার। বাবা শহর থেকে রাতে আসেন। আমাদের দেখে অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু খুশিও হয়েছিলেন। মা কিন্তু একবারও তার ভয়ের কথা বলেননি। রাতে ঘুমের মধ্যে অস্বাভাবিক গোঁ গোঁ শব্দ করেন। ঘুম ভাঙার পর মা তার ভয়ের কথা বললেন, শাদা কাপড় পরা কেউ এক অচেনা লোক, সারা মুখে দাঁড়ি গোঁফ, তার কোলের সন্তান কেড়ে নিতে এসেছিল। উনি তারস্বরে চিৎকার দিয়েছেন, এদিকে কেউ শোনেনি। ঘটনাটি ‘বোবায় পাওয়া’ হিসাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিল, এরকম হতে পারে। কিন্তু প্রায় রাতে মায়ের এমন অবস্থা হতে থাকায় বাবা চিন্তিত হন। একজন খোন্দকার আছে তাকে এনে ঝাড়ফুঁক দেওয়া হল মাকে। মশারির উপর কয়েক ফর্দ শাড়ি চাদর চাপিয়ে তার ভিতরে মা বসেছিলেন, বাইরে থেকে ঐ লোক পানিপড়া ছিটালেন। তারপর তাবিজ দিলেন। চারটি মাটির সরার মধ্যে সূরা-জ্বীন লিখে ঘরের চারকোণে লাগিয়ে দিলেন। গ্রামে এবং মফঃস্বল শহরে এই চিকিৎসায় তখন লোকের বিশ্বাস ছিল। আল্লাহর নাম-কালামের উপর মায়েরও অগাধ বিশ্বাস, তিনি খুবই ধর্মপরায়ণা।
নানার বাড়ি থেকে কিছুটা পরিচ্ছন্ন এবং ভদ্র স্বভাবের মেয়ে হয়ে এসেছিলাম। মায়ের এক অদ্ভুত অসুখ। খুব মনমরা হয়ে ঘরেই থাকতাম বেশি। এ সময় আমার শালিক ধরার শখ হয়েছিল। আমার এক জেঠাতো ভাই মাছ ধরার ‘পলো’ এনে তাতে লম্বা দড়ি বেঁধে দিয়ে আমাকে বললো, শালিক লাল মরিচ খুঁটে খেতে ভালবাসে। পলোর তলায় আমি কতগুলো শুকনো মরিচ ছিটিয়ে দিলাম। তুই দড়ি ধরে পলোর একটি দিক তুলে ধরে রাখ আড়ালে। শালিক ঢুকলেই দড়ি ছেড়ে দিস। ওর কথা শুনে কাজটি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় লাগলো। ঘরে বসে উঠানে উড়ে আসলো যে শালিক, সেটি ধরবো। মনের আনন্দে নেচে উঠি। এদিকে আনন্দ কোথায়, হাতের দড়ি ছাড়তে না ছাড়তে শালিক উড়ে যায়। ওরা আমার ফন্দি টের পেয়ে গেল। আমি কেঁদে ফেলি। একটা ধরতে পারলেই আমি খুশি হতাম। আদর করে চাল ভেজা, বুট ভেজা খেতে দিতাম। ওর নাম দিতাম। কথা বলতে শিখাতাম। সবিতার ঠাকুরদার ময়নাটা কী সুন্দর! দেখলেই বলে, ‘দাদা, অতিথ আইচে, হিড়ি দ, হরে রাম হরে কৃষ্ণ। আমি ওসব ধর্ম কথা শেখাব না। আমার পাখি বলবে, ‘আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই।’
বেশী শখে পড়লে যা হয়; আবার শালিক ধরার কাজে লেগে গেলাম। এক দু’দিন গেল। তৃতীয় দিনে একটা শালিক ফাঁদে পড়ে গেল। প্রচন্ড খুশিতে দৌড় ঝাপ দিতে থাকি।ফলে মা দেখে ফেলেন। এমন চড় মারলেন, কে তোকে এই বুদ্ধি দিল? ঐ ধাপার মেয়ে সবি? ঐ মেয়ের সঙ্গে আর যদি তোকে দেখি ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব। যত বাজে বুদ্ধি দেবে। পাখি উড়ে বেড়ায়, ওটা বন্দি করলে আল্লাহ গুনাহ দেয়। আর কখনো একাজ করবি না। ঐ মেয়ে তোকে কাঁকড়া খাইয়েছে আমি শুনেছি। কাঁকড়া আমরা খাই না। তোর কি কোনদিন বুদ্ধি হবে না?
আসলে সবিতার সাথে মিশি আমি। কিন্তু ওর কথায় পাখি ধরিনি। এই সত্য সেদিন বলতে পারিনি বলে মনে আরো দুঃখ হল। পাখিও গেল, বান্ধবীও গেল, এ দুঃখ আমার ছোট্ট মনকে বহুদিন ঘিরে রেখেছিল। অবশেষে দুটো হাঁস পুষে মনের দুঃখ ভুলেছি। আমার কুড়ানো সুপারি বিক্রির পয়সা কয়গন্ডা হয়েছিল, সেটা দিয়ে বাড়ির পিছনে নাপিতবাড়ি থেকে কিনেছিলাম। দুটো হাঁসই ছিল শাদা আর খয়েরি মেশানো। ওদের কানে, গলায়, পায়ে পুঁতির গহনা পরিয়ে দিতাম। ঠোঁটে ফাঁক করে ঝিনুক ভেঙ্গে ভিতরকার মাংসটা খাওয়াতাম। ডিম দিত, কিন্তু জমিয়ে রাখতাম, বাচ্চা ফুটাতে দেব মেজ জেঠিমাকে। তিনি এসব কাজে তেমন বাধা তো দিতেনই না, বরং খুশি হতেন। কিন্তু সবার উপর মা, তিনি বাচ্চা ফোটাতে দিলেন না। স্পষ্ট বলেছিলেন, উকিল সাহেবের মেয়ে, হাঁস-মুরগি পালবি?
তারপর যা হবার তা হতে লাগলো। মা অসহ্য হয়ে পড়ছেন আমাকে নিয়ে। নষ্ট হয়েও যাচ্ছি। আজগুবি সব কাজ করি, জ্ঞানবুদ্ধি একেবারেই নেই। শহরে কবে নিয়ে যাবেন বাবা। তাগিদ দিচ্ছেন বাবাকে। আমার জ্ঞানবুদ্ধি নেই, এটা মা বুঝলেন কি করে, বাবা জানতে চাইলেন। আমি কাছে ছিলাম। দূরে তাড়িয়ে বললেন, বাড়ির ছেলেমেয়েরা যা করে, রৌশনী সেটা করে। ওরা গায়ের কাপড় ছেড়ে উপরে রেখে পানিতে নামে, খেলে না সঁতার কাটে কি জানি। আপনার মেয়েও একদিন ধরা পড়লো আমার হাতে। সেমিজ খুলে, জাঙ্গিয়াটা খুলে পানিতে ঐ যে আমগাছের একটা ঝুড়ি নেমেছে তা ধরে সাঁতার দেয়। কি লজ্জার কথা। আমাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েরা একেসাথে তো পুকুরে নামে না। ভিতরে ছেলেদের আসা মানা। এখানে কি করে ওকে তারপর রাখা যায়? মেয়ের ছয় বছর বয়স, আপনি তো আমার কথা কানে তোলেন না।
বাবা তখনই বোধ হয় আমাদের শহরে নেয়ার প্রস্তুতি নেবেন ঠিক করলেন।
বাবার বৈঠকখানা
বাবার বৈঠকখানা আমাকে যখন তখন হাতছানি দিত, মা সেলাই নিয়ে বসেছেন, চুপিসারে সেখানে হাজির হতাম, প্রথমেই তাকাতাম মাথার উপর কি ওটা ঝুলছে। লাল সালুর কুচি দেয়া কাপড় কাঠের দন্ডে সেলাই করে লাগানো, একজন লোক দড়ি টেনে বাতাস করে আমাকে বুঝিয়ে দিল, এই টানাপাখা হাকিম আর উকিল বাবুদের গরমের সময় মাথায় বাতাস দিতে লাগে। ন্যায়-অন্যায় বেছে বিচার করার জন্যে মাথা ঠাণ্ডা রাখা লাগে। আরেকটা জিনিস টেবিলে দেখেছি, আধা চাঁদের আকারে কাঠের তৈরি হ্যান্ডেল বানানো রয়েছে। মাঝে ফুটো রেখে, তলায় চুষনি কাগজ সেঁটে দেয়া। দোয়াত কালি কলম টেবিলে কাঠের কলমদানিতে সাজানো দেখেছিলাম জেঠাজির অফিস ঘরে, কিন্তু এই চুষনি কাগজ দেখিনি। নিজের মনমতো আঁকাবুঁকি করে ওটা দিয়ে চুষে নিতাম।
শহরে যাওয়ার দিনটি আনন্দের মধ্যে হলে কি জানি এত মনে পড়তো না হয়তো। মায়ের কাণ্ড দেখে আমরা দু’বোন কেবলই অবাক হচ্ছিলাম। তিনি এত কাঁদছেন কেন? যাওয়ার জন্যে বাবাকে এমন জালাতন করে শেষে কিনা বাড়ি ছেড়ে যেতে মনের কষ্ট লুকোতে পারছেন না। বড় জেঠি, মেজ জেঠি আমাদের জন্যে কত রকম রান্না করে এনেছিলেন, এখন খাব, পথে নেব এবং শহরে গিয়ে খাব। হাত রুটি পিঠা, মুরগির মাংস ভাজা, নারকেলের সন্দেশ জাতীয় খাবারে বোঝাই করে দিচ্ছেন তারা। চাল-ডাল-নারকেল বোঝাই। এক নৌকায় যাবেন ছোট ফুফা, অন্যটায় আমরা। নৌকাঘাট বেশি দূরে ছিল না। আমাদের ঘর বরাবর বাড়ির সীমানার শেষ প্রান্তে হেঁটে যাওয়ার মত দূর। মা বড়দের সালাম করলেন। বললেন, মাফ করে দেবেন। মেজ বিবি, বড় বিবি, আপনাদের অনেক ছোট আমি, অনেক বেয়াদবি করেছি, মাফ করে দেবেন। কেঁদে ভাসালেন তিনি। অতঃপর আমরা সকলে কাপড়ে ঢাকা একটি বড় মশারির মধ্যে ঢুকলাম। চারজন লোক মশারির চারকোণা ধরে ঘাটের দিকে হেঁটে চললো। নারীরা ছোট বড় সকলেই ভিতরে মশারীর ঘাট পর্যন্ত এল। পুরুষরা সরে গেলে আমরা নৌকায় উঠলাম। এ মশারির ভিতর ঢুকে জেঠিমা ও আমার বোনরা বাড়ি ফিরে গেলেন একইভাবে।
দাদিমা পর্দা কি আর করবেন! লাঠি ভর করে তিনি ঘাট পর্যন্ত এলেন। বাবাকে বললেন, এই পথ ধরে তোকেও বহুবার বিদায় দিলাম, আজ দিলাম বৌ-নাতি-নাতনীদের। বাড়ির পুব দিকটা খালি হয়ে গেল। খালি করে দিয়ে যাচ্ছো আমার বুকের ভিতর দিকটা। আবার কবে আসবা ছোট মিঞা? মাকে এই কি শেষ দেখে যাও?
– প্রত্যেক শনিবার এসে সোমবার সকালে যাব, এখন যেমন আসা যাওয়া করি তেমন। মা, দোয়া করবেন আপনি।
– তোর ঘরদোর কে দেখবে? আক্কাস আলী? ওকে ঠিকমত কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যা … আমার কি বয়স আছে তোর বিছানাটা রোদে দেব যে!
দাদিমাকে বাবা নিজে ধরে বাড়িতে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। এবং ফিরে আসার পর আমাদের নৌকা ছাড়লো। আমার খেলার সাথীরাও ঘাটে এসেছিল, আমরা কেন যেন কেউ কাঁদিনি। বাবা আমাদের আবার নিয়ে আসবেন। হেসে হেসে তাই আমরা চলে এলাম। তাছাড়া দেখছিলাম বাবাকেও। লম্বা শরীরে শাদা পাঞ্জাবি, শাদা লুঙ্গি, মাথার মাঝখানে সিঁথি করে দু’পাশে ঢেউ খেলানো কালো চুল সকালের রোদে অন্যরকম লাগছিল। এমন করে তাকে কখনোদেখিনি। দাদিমার বয়সের ভারে ন্যূজ দেহ, চওড়া কপালে বলিরেখা, নেতিয়ে পড়া নাক এ যাবত আমি বুঝি দেখিনি। তিনি কি বলে যাচ্ছেন তার ছোট মিঞাকে, মেয়েদের পেয়ে বুড়ো মাকে ফেলে চলে গেলি? গাঁয়ের মাকে ভুলে যাবি না তো… গায়ের মানুষকে তুই যে বড়ই ভালবাসিস।
আমার এতক্ষণে কাঁন্না পেল। গায়ের খালের আঁকাবাঁকা পথে মাঝি লগি ঠেলে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। কত সুন্দর ছবি চোখের সামনে। কিন্তু ঝাপসা চোখে কি আর দেখা যাবে, দাদিমাকেই বার বার দেখছিলাম। তিনি একদিন গল্প করেছিলেন সাম্পানের বোটে চড়ে তার নীলপানিয়া (বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে কলকাতা যাওয়ার কথা। ঘরবাড়ির মতো বোট। কেবল ঢেউ লাগলে তার বুক কাঁপতো, এই বুঝি ডুবে যাবেন। দাদাজির ভাই কলকাতার খিদিরপুরে থাকতেন। কলকাতার মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। তিনি খিদিরপুরে নোয়াখালী থেকে মেহনতি মানুষ সাপ্লাই করার ব্যবসা করতেন। তার কোনো সন্তান ছিল না। ভাইয়ের বৌয়ের সন্তান হবে শুনে কলকাতায় নিয়ে গেলেন, ছেলে হোক কি মেয়ে হোক এটি তিনি পালক নেবেন। বাড়িতে নার্স রেখে সব সময় সেবা-যত্ন করিয়েছেন। এক কন্যা হল, নাড়ি কাটিয়ে দিলেন সোনার পাত বানিয়ে। সোনায় ময়লা থাকে না, ঘা হয় না। দাদিমা তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্যে কত দামী জিনিস? ভেবে অবাক হয়েছিলাম। উনি ভালও হলেন, কিন্তু শিশুটি মরে গেল। দাদিমা মুখ শুকনো করে আমাকে বলেছিলেন, হিংসা করে মেরে দিয়েছিল ঐ কলকাতার বাঁজা মেয়েলোকটা, শেষকালে তাবিজটোনা করে সে নিজের স্বামীকেও মেরেছিল। হিংসুকের কপাল ছারে খারে যায়। তাই হয়েছিল। ওর কপালে কিছু থাকলো না, নিজের ভাই আর ভাবী বাড়ি দখল করে ওকে দয়া করে একটা ঘরে থাকতে দিয়েছিল। মনের দুঃখে বেচারি বেশি দিন বাঁচলো না, মরে কবরে ঠাঁই পেল। আল্লাহ তার বেহেস্ত নসীব করবেন। দাদিমা মোনাজাতের মতো করে কথা শেষ করেছিলেন।
নৌকার ছইয়ের বাইরে বসেছিলাম। অন্যমনস্ক। বাবার গলা শুনতে পেলাম। বলছেন, খাল শেষ হয়েছে এবার আমরা বড় নদীতে পড়বো, ভিতরে যাও। নদীর এখানটার নাম জালছেঁড়া, আসলে মেঘনা নদী। বড়ই ভয়ঙ্কর এর রূপ। জোয়ার আসছে, দেখতে পাবে বড় বড় ঢেউ। ভয় করবে না।
নীলপানিয়ার ঢেউ আরো বড়। দাদিমা বলেছেন, সাগরের ঢেউ অনেক উচু হয়, তাই না আব্বা। হ্যাঁ বলে তিনি চুপ করে গেলেন। আমি এদিকে প্রশ্ন করে যাচ্ছি, দাদিকে আমাদের সাথে নিয়ে এলেন না কেন? আমাদের মন খারাপ করছে, উনিও কাঁদছিলেন।
বাবা আমাকে আবারো ভিতরে যেতে বললেন। সকলকে সবখানে আনা যায় না, মা সেখানেই ভাল থাকবেন। কথাগুলো এতে সহজে বললেন বাবা, আমি কষ্ট পেলাম। মনে মনে ভেবেছি, বাবা গ্রামে যখন যাবেন, আমি সাথে যাওয়ার জন্যে এমন কান্না জুড়ে দেব, উনি সাথে
নেবেনই, মা দিতে চাইবেন না। কিন্তু শেষে দিতে হবেই। দাদিমার একটা আলাদা ভাগ করা ঘর আছে, বড় বিছানা পাতা, সিথানের কাছে লম্বা লম্বা শিক্কা ঝুলিয়ে রাখেন, কত মজার খাবার, তেঁতুল, গুড়, চিড়ার লাডডু, নারকেলের সন্দেশ আরো কত কি! মাটির হাঁড়িতে ভরে ভরে রাখেন, সেখানে দাদির সঙ্গে একরাত কাটিয়ে দেব। উনি গল্প শোনাবেন, রাত জেগে শুনতে শুনতে ভোরের আযান হয়ে যাবে। আমি মন খারাপ করে ছইয়ের মধ্যে শুয়েছিলাম। নৌকা দোল খাচ্ছিল। মাথা ঘুরে উঠে সে সময়। মা বমিও করলেন, সাথে ‘চিলমচি’ ছিল সেটার মধ্যে মুখ নিয়ে সে কি বমি! যা খাওয়া হয়েছিল, পেটে কিছু থাকলো না এমন ওয়াক ওয়াক। নুরজাহান এবং বাট্টু দুজনেই কান্না জুড়ে দিল। আসলে সেই দোলানিটা ছিল শেষ, ঘাটে পৌছানোর সময়, ওখানটায় নদী ভাঙনের ঢেউ উচু আর বার বার আসছিল। নদীটার নামই যে জালছেঁড়া, পাড়ও ভাঙে, জেলে নৌকার জালও ছেঁড়ে।
মন্তিয়ারখোনা ঘাটে আমাদের নৌকা ভিড়লো। আমাদের জন্যে ঘাটে নোয়াখালী বাসার লোকজন অপেক্ষায় ছিল। কোলে চড়ে আমরা পাড়ে নামলাম। মাকে কাপড় মুড়িয়ে ঢেকেঢুকে বাবা কোলে তুলে সোজা ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়ে দিলেন। আমরা দুবোন জড়াজড়ি করে বসি, মা বাট্টুকে কোলে নিয়ে। পাল্কিগাড়ি, জানালা বন্ধ। জানালায় খিড়কি আছে, একটু ফাক করে বাইরে দেখে অবাক হচ্ছিলাম, এত বাড়িঘর, এত লোক! ভাত-ডালের হোটেল, তরকারি রান্নার গন্ধ বাতাসে। রাস্তাপাকা ছিল, বাসাও আমাদের দূরে ছিল না। পৌঁছে গেলাম। বাবা তার দলবল নিয়ে হেঁটে এসেছিলেন।
নানার বাড়িকেই আমি শহর ভাবতাম। আমার বাবা যে শহরে ওকালতি করেন সেখানটা আরো দালানকোঠা নিয়ে বাহারি হবে, মনে সেরকম একটা ছবি ছিল, কিন্তু এসে দেখি আমার ছবির ধারে কাছেও নেই, গ্রামের কাছারি হাটের ঘরবাড়ি, দোকানপাট এর থেকে সুন্দর। বড়মুখ ছোট হয়ে গেল আমার। মা রাগ করেন এবং বলেন,বাড়িতে মানুষ থাকে? আমি এক্ষুণি ফিরে যাব। বাবাকেও দেখলাম মুখ চুন করে কথা বলছেন, আপনি সময় দিলেন না, ঝটপট ছনের ছাউনি দিয়ে আপনাদের নিয়ে এলাম, এখানে গরম বেশি, ছনের ঘর ঠান্ডা। আপনার কষ্ট কম হবে।
এসবে কান দিলেন না মা, আলনায় কাপড় গোছাতে লাগলেন, আমাকেও সাথে নিলেন। একবার বললেন, বাসার মধ্যে এতবড় চাকর রেখেছেন, চলাফেরা করি কি করে। ওকে বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করে দেবেন।
মায়ের তরফ থেকে এই সামান্য অভিযোগ বাবা কল্পনাও করেননি। তিনি নিশ্চিন্ত মনে বৈঠকখানায় মক্কেল নিয়ে বসে গিয়েছিলেন। তার বৈঠক ঘরে কয়েকটি কাঠের চেয়ার, টেবিলটি বেশ বড়, উপরে গাঢ় সবুজ রঙের শক্ত রাবারের মত কাপড় ছোট ছোট পেরেক ঠুকে সরু বেত দিয়ে আটকান। বাবার চেয়ারটি উঁচু, পিঠ, হাতলে সামান্য নকশা, কিন্তু আমার কাছে সেটি যেন সিংহাসন আর তিনি সেখানে বসলে অচেনা হয়ে যেতেন। মোটা বই খুলছেন, পড়ছেন, লিখছেন, আর মুখে কথা বলছেন। কত কষ্ট করেন। মাকে যে পকেট থেকে টাকা বের করে দিতেন সেগুলো রূপার গোল চাকতির মতো, একদিকে ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবি। ষোল আনায় একটাকা, চার পয়সায় এক আনা, তখন পয়সা ছিল তামার গোল চাকতি, আধা পয়সা, পাই পয়সা ছোট ছিল। কাগজের নোট দেখিনি। সে সময়ে ছিল না।
বাসার মধ্যে পানি ও গোসলের জন্যে কেরোসিনের চৌকো টিন উপরের অংশ কেটে তাতে পানি তুলে রাখা হতো। দুটো ছেলে চাকর সারাদিন ধরে পানি টানতো, সামনের পুকুরটা বেশ বড় ছিল এবং চার পাশের অগুনতি লোকজন ওখান থেকে পানি নিত, ব্যবহার করতো। রান্নার পানি মাটির কলসি, মুটকিতে ভরে রাখতো। খাওয়ার পানি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ট্যাঙ্কি ছিল, সেখান থেকে আনতে দেখতাম। বড় চাকরের কাজ ছিল হাটবাজার, ধোপার এবং বাইরেরসকল কাজ। রান্নার জন্যে মেয়ে রাধুনি ছিল। কিন্তু মা রাঁধতেন নিজের হাতে। কোন পুরুষ বাড়ির ভিতরে আসতে হলে গলায় খাকারি দিয়ে জানান দিতে হতো। মেয়েরা সরে গেলে তার আসার অনুমতি মিলতো।
শহরে আসার পর আমাদের জামা-কাপড় কিনে দিলেন বাবা। মা একদিন জানালেন একজন মহিলা এসেছিল। সেলাইয়ের কল কিনলে সেলাই শিখিয়ে দেবে সে। মায়ের ইচ্ছা তিনি কিনবেন। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, ওদের জন্যে বেশি কাপড় সেলাই লাগবে। মেশিনের নাম ছিল সিঙ্গার, হাতল ঘুরিয়ে সেলাই করতেন মা। সেই মহিলা যা শিখিয়ে ছিল, মা তার চেয়েও বেশি ভাল পারতেন, তবে সে প্রায় আসতো, খেয়ে যেত, মাকে দিদি ডাকতো। মাকে তার খুব পছন্দ ছিল। দুঃখ করে বলে যেত অনেক কথা, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মেশিন বেচার কাজ করি, কয়জনায় বা কিনতে চায়, বিনা খরচায় সেলাই শেখাতে চাই, তাও না, যে দু চারজনই মেশিন কিনলো, তারা দেখি ঠিক করে কেচি ধরতেই মাস চলে যায়। আপনাকে তো আমার শেখাতেই হয় নাই দিদি।
এ সব কথায় মা মিষ্টি করে উত্তর দিতেন, আমার মায়ের কথা কত আর বলি, আমাকে যতদূর, পেরেছেন শিখিয়েছে, আর ঐ আমার একরত্তি মেয়েকেও হাতে সুতো ধরিয়ে দিয়েছেন। উনি বলেন, সেলাই আর রান্নার গুণেই মেয়েদের বংশ পরিচয়।
সিঙ্গার মেশিন নিয়ে মা দুপুরবেলায় বসতেন, শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে নিজের বিছানার উপর চাঁদোয়া বানিয়ে টাঙ্গিয়ে দিলেন। ছনের চালা থেকে খড়কুটা কি পোকা-মাকড় পড়বে সেই ভয় ছিল তার। সে কালে শাড়ির পাড়ে গাছ পাতা, নৌকা-নদী, হাতি- ঘোড়া, ময়ূর তিনচার রঙের সুতা মিলিয়ে ভালা থাকতো, ঐ শাড়ির দাম এক টাকা থেকে দেড় টাকার বেশি ছিল না। নোয়াখালী আসার পর মা খদ্দরের মোটা শাড়ি পরতেন না। শুনেছি আমার জন্মের পর দেশের তাঁতের শাড়ি পরা ধরেছিলেন। ছয় ছাটের পেটিকোট সেলাই শেখেন এ সময়।ব্লাউজও কাটতে শেখেন। আমাদের জন্যে ফ্রক কাটা এবং সেলাই করতেন তিনি, এবং দর্জির মতো ভাল হতো। অন্যদের থেকে প্রশংসা শুনেছি।
মেশিনের দাম কিস্তিতে পাঁচ টাকা ছিল, ছয় মাসে পাঁচ টাকা সুদসহ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন বাবা, মেশিনের দাম পঁচিশ টাকা ছিল। তাতে কাঁচি, কুচি দেয়ার ও হেমিং করার ছোট পার্টসও ছিল। দুটো ববিন, তেল ভরা সুদৃশ্যপট, সুতার রিল এবং আরো কত কি!
বাবার বৈঠকখানা আমাকে যখন তখন হাতছানি দিত, মা সেলাই নিয়ে বসেছেন, চুপিসারে সেখানে হাজির হতাম, প্রথমেই তাকাতাম মাথার উপর কি ওটা ঝুলছে। লাল সালুর কুচি দেয়া কাপড় কাঠের দন্ডে সেলাই করে লাগানো, একজন লোক দড়ি টেনে বাতাস করে আমাকে বুঝিয়ে দিল, এই টানাপাখা হাকিম আর উকিল বাবুদের গরমের সময় মাথায় বাতাস দিতে লাগে। ন্যায়-অন্যায় বেছে বিচার করার জন্যে মাথা ঠাণ্ডা রাখা লাগে। আরেকটা জিনিস টেবিলে দেখেছি, আধা চাঁদের আকারে কাঠের তৈরি হ্যান্ডেল বানানো রয়েছে। মাঝে ফুটো রেখে, তলায় চুষনি কাগজ সেঁটে দেয়া। দোয়াত কালি কলম টেবিলে কাঠের কলমদানিতে সাজানো দেখেছিলাম জেঠাজির অফিস ঘরে, কিন্তু এই চুষনি কাগজ দেখিনি। নিজের মনমতো আঁকাবুঁকি করে ওটা দিয়ে চুষে নিতাম।
আমি বাবার চেয়ারে কখনো বসিনি। ও ছিল আমার স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে এক মনোরম সুখ। দেখতে ভাল লাগতো। তবুও একদিন মা টের পেলেন। দুজন মুহুরি এ ঘরেই চৌকি পেতে থাকতো। চৌকির লাগোয়া তাদের বাক্স, তাতে যাবতীয় জিনিস ভিতরে রেখে উপরে তারা টেবিলের মত কাজ করতো। নালিশ ওদের থেকেই এসে থাকবে। কিন্তু আমি জিদ করে আরো বেশি যেতাম ঐ ঘরে। আমার বাবার বৈঠকখানা। তারা নিষেধ করার কে? আমার মনের ভাব এমন হয়েছিল, কিন্তু পরের ঘটনা অন্য। একজন খেলার সাথী পেয়ে গেলে আর ও মুখো হইনি। সে আমাকে একদিন স্কুলের কথা বলেছিল।
আমার প্রথম স্কুল
বাবা বললেন, ওকে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করিয়ে নিন, মনে হয় ভালই পারবে। স্পেলিং করে স্কুলের নাম নোয়াখালী সদর গার্লস এম. ই স্কুল পড়লো, আপনার নামটিও পড়লো, মিস শিশির যামিনী বসু। হেড মিস্ট্রেস।
মেয়ে হয়েছে শুনেও বাবা কেন যে আযান দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে কানে হাত দিয়েছিলেন, উনি তো টাইটেল পাস মৌলভী, জানতেন না? আযান দিতে হয় না, শুধু কলেমা পড়ে নবজাতকের কানে ফুঁ দিলেই হতো। সময়ের লুকোচুরি খেলা বেশ জমেছিল। মসজিদ থেকে তখনই আযান হয়ে গেল, বাবা খুশি হলেন, কিন্তু অন্যদের মন্তব্য ছিল, এ ভাল না, মেয়েটার জীবনে কী জানি আল্লাহ কী রেখেছে। সেই লুকোচুরি খেলা যে প্রথম স্কুল যাওয়া নিয়ে আবারো সবার অলক্ষ্যে আমাকে নিয়ে বিধাতা কেন ঘটিয়ে দিলেন, সেটাও আশ্চর্য।
বাড়ির প্রথম সন্তান। ঘটা করে হাতেখড়ি অনুষ্ঠান কপালে আমার জুটলো না। সামনে ডালাকুলা ভর্তি মন্ডামিঠাই একপাশে। তার পাশে বই খাতা কালি কলম। মাঝে ঘিয়ের প্রদীপ সাজিয়ে আমাকে কে আর বসাবে। মাকে যে আমি প্রচন্ড রাগিয়ে দিয়েছিলাম। তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার দুঃসাহস করে ফেলেছি তিনি টের পেলেন না। একা মানুষ সংসারে, বাবা তো থাকেন মক্কেল এবং আইন-আদালত নিয়ে। তিনি একহাতে কতদিক সামলাবেন। সংসারে আমরা গুটিকয় প্রাণী হলেও খাওয়ার লোক বাইরের অনেক। মুহুরি সাহেবরা, গ্রামের বাড়ির মক্কেলরা হরহামেশা মেহমান থাকেন। আমি এসব সুযোগে তাকে ফাঁকি দিয়েছিলাম। তদুপরি কড়া রকমের পর্দানশীন থাকতেন তিনি। তাতে কাজের ঝামেলা বাড়তি সামলাতে হতো তাকে।
বৈঠকখানায় পাংখাপুলার ছেলেটা খুব জোরে বাতাস দিচ্ছিল আমাকে। আমি বাবার চেয়ারের হাতল ধরে সামনের খোলা দরজায় দেখতে পেলাম, বই খাতা বগলে একটি ছেলে আমারই বয়সি লাগছিল, ওকে
ডেকে পাঠালাম। পরিষ্কার গলায় পাংখাপুলার ছেলেটা ওকে ডাকছে, বাচ্চুবাই এই দিকে আয়েন, উইল সাবের বৈঠকখানায় হেতেনের মাইয়ায় বোলায়। ছেলেটা কিন্তু শুনেও শুনলো না, হন হন করে চলে যাচ্ছে, আমি দৌড়ে ওকে ধরলাম, কোথায় যাও? আমার সঙ্গে খেলবে?’এখন স্কুলে যাই, পারবো না, বিকালে খেলি আমি।
– স্কুলে না গেলে মা বকবে?
– মা এখানে থাকে না, বাড়িতে। আব্বার সাথে থাকি, ঐ তো আমাদের ঘর।
– কাল আমাকে স্কুলে নেবে?
ছেলেটির দৌড় দেখে আমি বুঝলাম, ইচ্ছা করে সে আমাকে নেবে না, জোর করে ওর পিছু নিতে হবে। ছেলেটা দুষ্ট।
শুরু করলাম এভাবে ওর সাথে স্কুল যাওয়া, কত ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ছে, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে খেলছে। গ্রামে খেলার সাথী ফেলে আসার জন্যে দুঃখ করতাম, এখন আনন্দে মেতে উঠলাম। তবে পেটে পেটে বুদ্ধি রেখেছিলাম। স্কুলে একটা ঘন্টা পড়লে আর আমি সেখানে নেই। ভাল মানুষটি সেজে ঘরে হাজির। গোসল করার নিয়ম ছিল বাবার, কোর্টে যাওয়ার আগে, সাড়ে নয়টায় শেষ। পরিষ্কার জামা পরে বাবার সাথে আমরা দু বোন খেয়ে নিতাম, এটা নাস্তার মতো। দুপুরে পেটপুরে খাইয়ে মা আমাদের বিছানায় শুইয়ে দিতেন। ঐ স্কুল দূরে ছিল না। রাস্তা বাদ দিয়ে এ বাড়ির পেছন, ও বাড়ির উঠান ধরে দেবালয়ের চত্বর কোনাকুনি হেঁটে স্কুলে চলে যেতাম আর আসতাম।
এভাবে বেশ লুকোচুরি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সেটা কতদিনের এক মাসও হতে পারে, কমও হতে পারে, কিন্তু আমার আজ মনে পড়লে বুঝতে পারি, এর চেয়ে অনেক কম দিন। আনন্দের মধ্যে স্কুল যাওয়া নয়, লুকিয়ে। ধরা পড়ার ভয়তো ছিলই। কিন্তু যেভাবে ক্লাসে ধরা খেলাম, বড় লজ্জার কথাতো বটেই। নিজের পিতাকেও যে এর মধ্যে টেনে এনেছিলেন হেডমাস্টার তাতে দুঃখ পেয়েছিলাম বেশি। কয়েকদিন থেকে একটি অপরিচিত মেয়ে দেখে তার মনে সন্দেহের উদয় হয়। ক্লাসের মধ্যেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোর বাবার নাম কী? ভয়ে বুক কেঁপে গেল, গলা থেকে কথাও বের হচ্ছিল না। তিনি ধমক দিতেই কেঁদে দিলাম। আমার সাথী বাচ্চু বলে দিল, বাড়ির কেউ জানে না, আমার সাথে স্কুলে এসেছে। উকিল সায়েদুল হক সাহেবের মেয়ে।
– কী সর্বনাশ! তুই আমার চাকরি খাবি নাকি? উকিল সাহেবের মেয়ে ফ্রি মডেল প্রাইমারিতে পড়ছে! উনি যে আমার স্কুলের মেম্বর, সব জানিয়ে দিতে হবে তাকে। গরিবদের সঙ্গে পড়তে এলে কেন মামনি। চলো তোমাকে ঘরে দিয়ে আসি।
আমি বুঝি কথাগুলো শুনে শিউরে উঠলাম। পিঠ খালি করে কেউ কি শলার পিটুনি দিতে শুরু করলো? ছোটবোন ভয়ে কেঁদে দিচ্ছে, আপাকে আর মারবে না আম্মা, এবার থেকে ও তোমার কথা শুনে চলবে। বল না আপা ভাল মেয়ে হবি তুই। এত মার খেলে তুই মরে যাবি, বল না আপু।।
কী আশ্চর্য ঘটনা, মা মোটেও রাগ করলেন না। হেডমাস্টার সাহেবকে খুব খাতির-যত্ন করে বিদায় দিলেন। আড়াল থেকে বলেছিলেন, নতুন এসেছি, ওর খেলার মত কেউ এ পর্যন্ত পায়নি কিনা, আপনার স্কুলে গিয়ে পেয়েছে। কেবল খেলা, লেখাপড়ায় মন নেই। ওকে ভাল স্কুলে শিগগির দিয়ে দেব। আপনি আমার অনেক উপকার করলেন, মাস্টার সাহেব।
অফিস থেকে ফেরার পর বাবা শুনলেন সব। নাস্তা-চা খেয়ে মা পান. বানিয়ে দিলেন, বলছেন আর হাসছেন, মা পান খেতেন খুব বেশি। মশলা, জর্দা আরো কত খুশবু। বাবাকেও খেতে দেন। আমি বাঁশেরবেড়ার আড়ালে আমাদের কোঠায়, বেশিতো দূর নয়, ফুটো দিয়ে দেখা যায়, শোনাও যায়, পানের রসে, গল্পে আর হাসিতে মায়েরখাটের উপর রুম রুম ঝুম ঝুম বাজনা বেজে যাচ্ছে।শুনতে পেলাম, আমার কানে এতোই মধুর লেগেছিল, আজও স্মৃতিতে শুনতে পাই।
এক সপ্তাহের মধ্যে সময় মতো বাবা আমাকে স্কুলে নিয়ে গেলেন। বড়দিমনি বাবার সাথে আমাকে দেখেই কোলে টেনে তোলেন, আপনার মেয়ে? দেশ থেকে কবে আনলেন?ওমা কি নরম ওর চুল। কি তুলতুলে শরীর, হাত পা কি সুন্দর, একটুও ময়লা নেই নখে, কি লক্ষ্মী মেয়ে, কি নাম তোমার?স্কুলে পড়বে?
বাবা বললেন, ওকে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করিয়ে নিন, মনে হয় ভালই পারবে। স্পেলিং করে স্কুলের নাম নোয়াখালী সদর গার্লস এম. ই স্কুল পড়লো, আপনার নামটিও পড়লো, মিস শিশির যামিনী বসু। হেড মিস্ট্রেস।
– কিন্তু অঙ্ক পারবে না। বছরের শেষে ভর্তি করাই কি উপায়ে। না পারলে ওর জন্যেই ক্ষতি, সারা বছরের বেতনও আপনাকে মিছে মিছি দিতে হবে। আপনি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে আছেন। নিয়মত জানেন। নেক্সট জানুয়ারিতে নিয়ে আসবেন।
ওদের কর্থাবার্তা শুনে আমি আর বড়দির কোল থেকে নামি না, প্রাইমারি স্কুলের সুরকরা গলায় নামতা পড়তে লেগে গেলাম। বড়দি আশ্চর্য বোধ করলেন। কে শিখিয়েছে? তারপর তিনি বলেছিলেন, কাল থেকে স্কুলে আসবে, কিন্তু তখন কোলে নেব না।
মেঘনা নদীর ভাঙনের মুখে স্কুলটি, চর পড়ে নদীর খাত বেশ দূরে সরে গিয়েছে। ওদিকে জজ কোর্ট ছিল, তার দীঘিটি নদীগর্ভে বিলীন। কালেক্টরি ঠিকঠাক রয়েছে। ফুটবল খেলার মাঠটি নদী থেকে রক্ষা পেয়েছে। চারদিকে ঘেরা বিরাট গেট লাগানো স্কুলটি ভারি সুন্দর। সামনে ফুলের বাগান। পিছনে ছোটদের খেলাধুলার জন্যে তিন জোড়া দোলনা। দুটা ঢেঁকি (সি-স), জিকজ্যাক ইত্যাদি ছিল। স্কার্ট পরা এক দেশী মেম আমাদের খেলার ক্লাস নিতেন। তার হুইসেল বাজলেই যার রুটিনে তখন শারীরিক শিক্ষা থাকতো, তারা মাঠে নেমে লাইনে দাড়িয়ে যেতাম।
এই সুন্দর স্কুলটা পরের বর্ষাকালে নদীতে ভেঙে গেল। আমাদের স্কুল উঠে গেল কয়েদিদের জেলখানায়। একদিকের দেয়াল নদীতে ভেঙে নিয়ে গেলে কয়েদিদের নতুন তৈরি জেলখানা মাইজদীকোর্টে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। বিরাট এলাকা, খেলার মধ্যে কোথায়ও লুকিয়ে থেকে, ক্লাসে না এলেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু সেটি হওয়ার উপায় ছিল। দিদিমনিরা কড়া নজরে রাখতেন, ধরা পড়লে শাস্তিও ছিল কড়া, মারধর ছিল না কিন্তু লেখাতেন একটা খাতা ভর্তি করে, আর এ কাজ করবো না জাতীয় লাইন এবং সারা স্কুল চক্কর দিয়ে দেখিয়ে দিতেন এরা অবাধ্য, ফাঁকিবাজ ইত্যাদি। তবে এই প্রকাণ্ড উন্মুক্ত জেলখানায় বেশিদিন স্কুল বসেনি, অন্যরকম ভয় ছিল, ভীষণ শোঁ শোঁ শব্দে জোয়ারের ঢেউ আসার সময় হওয়ামাত্র স্কুল ছুটি দিতে হত। স্কুলের আয়ারা আমাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতেন। কারো কোন ক্ষতিকর কিছু হলে অভিভাবকরা স্কুলকে জবাবদিহি করতেন। আয়ারা বাড়িতে যেয়ে ডেকে বলতো, “মা, দিদিকে দিয়ে গেলাম’, প্রতি উত্তর পেলে তবে সে চলে যেত। মাথায় ছাতা, হাতে লাঠি, শাদা শাড়ি পরতে দেখতাম তাদের। আমাকে যে আনা-নেয়া করতো, তার নাম মালিনা। কথার মধ্যে কয়েকবার ‘বাবা যিশু’ উচ্চারণ করতে শুনতাম। স্কুলের ভাঙ্গনে আমাদের পড়ালেখার বিশেষ ক্ষতি করতে দেননি বড়দিমনি। অরুণ চন্দ্র হাইস্কুলে সকাল বেলায় তিনি স্কুল চালাতেন। অন্যান্য দিদিরা তাকে অমান্য করতেন না। তারা থাকতেন একত্রে। বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছিলেন, তবে অধিকাংশই কলকাতার। অবিবাহিত, সরকারের চাকরি নিয়ে নদী ভাঙ্গন নোয়াখালী শহরে সাহস করে এসেছিলেন। একটি সুন্দর দোতালা বাড়িতে তাদের থাকার জন্যে সরকার থেকে ভাড়া নেয়া হয়েছিল। সামনে বড় মাঠ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি চুনু মিঞা স্কুলের জন্যে সবটুকু ছেড়ে দিলেন। তাই রক্ষা পেল সেকালের স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত মাত্র একটি স্কুল। বাঁশের তর্জায় তৈরি নতুন বাড়ি উঠে গেল ঐ মাঠে। অফিস, লাইব্রেরি ছিল দালানের নীচতলার দুটো রুমে। স্কুল থেকে টিফিন দেয়া হতো না। কিন্তু দারোয়ান সুরেন্দ্র এবং দপ্তরি রেনু মিঞাঠোঙ্গা বানিয়ে চীনে বাদাম বিক্রি করতো। বড়ই ছিল ঠোঙ্গা-দাম মাত্র এক পয়সা। টিনে ভর্তি বিস্কিটও ছিল। ওরাই বিক্রি করতো। মালি আবার ফুলের বাগান গড়ে তুললো, দোলনা বসালো মাঠের এককোণে। বড়দিমনির বয়স কত ছিল কি জানি, কিন্তু প্রায়ই তিনি আমাদের নিয়ে মাঠে নেমে যেতেন। স্কিপিং রেইস দেয়াতেন মেয়েদের দিয়ে, খেলার দিদিও সাথে থাকতেন। ককফাইটও খুব মজা লাগতো, যার নাম মুরগির লড়াই। নাচার মধ্য দিয়ে অন্যদের কুপোকাৎ করতে গিয়ে নিজেই বেশির ভাগ দিন হেরে গিয়েছি, কিন্তু ভাল লাগতো, কি হবে হারলে, খেলার মধ্যে উত্তেজনা বোধ করতাম।
স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রকৃতি পাঠ এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এ দুটো নিয়ে দিদিমনিদের বেশি নজর থাকতো, খাতা বানিয়ে তাতে নানান রঙের ফুল পাতা সেঁটে দিয়েছি, নিচে নাম। প্রজাপতি, পিঁপড়ে কিছু বাদ দিতাম না। স্বাস্থ্যরক্ষা নিয়মে তারা সাংঘাতিক কড়া ছিলেন। পঞ্চাশ নম্বর ছিল এর জন্যে। দাঁত, নখ, চুল, শরীরের ধুলোবালি, ময়লা জামাকাপড় প্রত্যেক দিন স্কুলের শুরুতে চেক করতেন। প্রভাদি ছিলেন ক্লাস টু-এর টিচার, একটা স্কেল নিয়ে পায়ে ঠুকঠুক শব্দ তুলে আসার সময় আমাদের বুক কাঁপতো, কি জানি যদি মারে, তাহলে এক নম্বর কাটা যাবে।
দিনিমনিদের স্কুলের মেয়েগুলো ছাড়া অন্য কিছু কি দেখার নেই! সারাক্ষণ আমাদের নিয়ে লেগেছিলেন, পরীক্ষা নেয়া, খাতা দেখা, সেলাই শেখানো, বাগান করা, এমনকি চিনে বাদাম ভাজা শেখানো বাদ দেননি তারা। ক্লাসে গল্প পড়ে শোনাতেন। ঐ সময় নীহাররঞ্জন গুপ্তের ‘কালো ভ্রমর’ বের হতো মাসিক শিশুসাথীতে। আশাদি কি সুন্দর গলায় রহস্য করে পড়ে শোনাতেন। পরের সংখ্যা কবে পড়বেন, আমরা সেই আশায় দিন গুণতাম।
স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষা ছিল তিন শ্রেণীতে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক নিতেন ক্লাস টু ও ফোরের শেষে। বৃত্তির হার ছিল ‘টু’ এর জন্যে তিন টাকা এবং ফোরের জন্যে পাঁচ টাকা। ক্লাস সিক্সে হতো মেধারী
ছাত্রীদের জন্যে বিভাগীয় মিডল ইংলিশ স্কলারশীপ পরীক্ষা। এর মূল্য ছিল দশ টাকা, চার বছর মেয়াদী, অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত। স্কুলের বেতন দিতে হতো না।
১৯৩৯ সন। বড়দিমনি আমাকে বিভাগীয় বৃত্তি পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি করছেন। এ তৈরি করার ব্যাপার অবিশ্বাসের মনে হলেও সত্যি। বাবার থেকে আমাকে চেয়ে নিলেন, নিজের ঘরে এনে, কখনো কোলে তুলে, কখনো বিছানায় শুইয়ে আদরে-সোহাগে পড়িয়েছেন। ইংরেজি গ্রামার, রচনা, ভাবসম্প্রসারণ, ইওর স্কুল গার্ডেন, পোস্টম্যান, ভিলেজ ফেয়ার, এ জার্নি বাই বোট—এ ধরনের কত রচনা তিনি সহজ করে আমাকে দিয়ে বার বার লিখিয়ে নিতেন। ঘোড়ার গাড়ি করে কখনো বাসায় ঘুরিয়ে নিতেন। তাঁর বিনা বেতনের এই শ্রম সাধনার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, তার স্কুলের নাম এক নম্বরে রাখা চাই, এজন্যে তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তার আশাকে আমি চার নম্বরে ডুবিয়ে দিলাম, তাও আবার রান্না পরীক্ষায় খারাপ করে। পায়েস রাধতে গিয়ে দুধ উথলে পড়ে গেল, তখন উনুনে জ্বাল বেশি বাড়িয়ে দেয়া ভুল হয়েছিল, তারপর পায়েসের চাল শক্ত খেয়ে বিভাগীয় ইন্সপেক্টর মিস সুরমা ঠোঁট উল্টালেন, তিনি আরো কয়েকজন পরীক্ষক নিয়ে হলের মাঝখানে বসে, কটমট করে এদিক ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছেন। আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, অথচ আমার মা আমাকে সবচেয়ে সুন্দর করে মাটির তোলা উনুন বানিয়ে দিয়েছিলেন, সরু করে শুকনো খড়ি জ্বালানি দিয়েছিলেন, তার মেয়েকে রান্নায় ভালো করতেই হবে। তখন সবেমাত্র শাড়ি পরা শিখেছি। বেণী শক্ত করে চুল এঁটে রেখে, কোমরে আঁচল গুজে আমিও তৈরি ছিলাম। এক রান্নার নম্বর যে আমাদের এমন তলিয়ে দেবে কেউ ভাবতে পারেনি! কেবল পাস নম্বর দিয়ে বোধধকরি সুরমাদি বড়দিমনির শ্রমকে ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়েছিলেন।
ছুটির আনন্দ
যেবার আমি ক্লাস ফাইভে পড়ছিলাম, এই আশ্বিনে পূজার ছুটিতে বাড়ি আসলে নতুন এক অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম। কাল বৈশাখীর মতো সাংঘাতিক ক্ষতি করে দিয়েছিল সেবারের আশ্বিনের ঝড়। বাবার টিনের ঘরটি বাতাসে দুলে নড়বড়ে হয়ে গেল, টিনের চালা উড়ে গেলে আমরা ছুটে এসে পাশের তাহের ভাইদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ঝড়ে এ ঘরটিও বুঝি উড়িয়ে নেবে এমন বাতাস তখনও বইছিল। বাড়ির সকল ঘরে ছেলেরা আযান দিচ্ছিল, সামনের ঘরে মেজ জেঠা আযান দিচ্ছেন। অন্যদিকে আমাদের নিয়ে বাবাও ক্রমাগত আল্লাহু আকবর, আশাদু-আল্লা … হাঁক দিয়ে যাচ্ছেন, আল্লাহ আমাদের বাঁচান।
মন্তিয়ারখোনায় আমরা থাকতাম যে অংশে, সেটি ছিল মুসলমান উকিল, মোক্তার, পেশকার, কেরানি, মুহুরিদের পাড়া। বড় পুকুরটির উত্তর পাড়ে মসজিদ এবং পরে নদী। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে রাস্তা ইট বসানো, উপরে সুরকি-চুন ইত্যাদির প্রলেপ। এ রাস্তা পূর্বে সিমেন্টের পাকা রাস্তা ধরে কোর্ট-কাছারির দিকে যায়। পশ্চিমে চলে গিয়েছে নাগপাড়ায়, সেটি হিন্দুদের, সেখানে দেবালয়ে পূজা হতো, কংগ্রেসের সভা-সমিতির জন্যে বিরাট চত্বর ছিল। এদিকটায় পাকাবাড়ি যেমন ছিল, রাস্তাও ভালো ছিল। পরে এদিকে টাউন হল তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের দিকে তেমন কিছু উন্নতি চোখে পড়েনি। খাদেমুল ইসলাম নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, টিনের ঘর। লাইব্রেরি ও পাঠাগার হিসাবে এটি ব্যবহার করা হতো।
গ্রাম ছেড়ে এসে এই ঘিঞ্জি এলাকায় থাকতে কিছুতেই মন বসতো না। আমাদের পাশের বাড়িতেও যেতে মন উঠতো না। ওদের ঘর পাকা ছিল কিন্তু তারা থাকতো নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, গ্রামের আত্মীয়রা থাকতো, মেসের মত খাওয়ার ব্যবস্থা। বাড়ির মেয়ে ছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এগিয়ে আসতো না। ফলে স্কুল ছুটি হলে গ্রামে যাওয়ার জন্যে আমরা রীতিমত কান্না জুড়ে দিতাম। বড় জেঠাজি এসে খবরও দিতেন দাদিমার শরীর ভাল নয়, তাকে কেন দেখতে যাই না। অতঃপর আমাদের ছুটি কাটানোর নিয়ম এমন হলো যে, বাবার গ্রীষ্মের ছুটি নেই, অতএব মামার বাড়ি উদরাজপুরে যেতে হবে, আশ্বিনের পূজার ছুটি দেড় মাসের বেশি এবং বাবাও ছুটি পান। জজকোর্ট বন্ধ। অতএব যাবো বাটৈয়ায় দেশে বাড়িতে।
বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে পথের কষ্ট ঢেকে যেত। যানবাহন বলতে এক নৌকা, দুই গরুর গাড়ি, অতঃপর রেলগাড়ি। নোয়াখালী থেকে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে আসতাম সোনাপুর রেল স্টেশনে। তারপর চৌমুহনী। একটি বড় স্টেশন, নদীবন্দর এবং বাজার। আমরা সোনাপুর থেকে দুটো স্টেশন পর চৌমুহনী পৌঁছতাম। অতঃপর নৌকার দিন হলে তাতে, নয়তো গরুর গাড়িতে। রাস্তা ছিল কাঁচা। বৃষ্টি হলে কাদামাটিতে গরু হাঁটতে পারতো না। এক ঘন্টার পথ দু ঘন্টা লেগে – যেতো। আমরা তাতেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছি, পায়ে হাঁটতে হয়নি। খারাপ হোক রাস্তাতো আছে। ছাতি মাথায় দিয়ে কাপড়ের পুটলি সেজে আগাগোড়া ঢাকনি দিয়ে পথে নামতে হয়নি। তখনকার মানুষ অল্প নিয়ে সুখে থাকতো, আমাদের স্বভাবও সেরকম ছিল।
বাড়িতে এসে ক্লান্তি নেই, খুশিতে টগবগ অবস্থা। বাড়ির দায়িত্বে আক্কাস আলী, লেপেমুছে বাড়ির ভিটেমাটি তক তক করে রেখেছে। নতুন গোসলখানা এবং পায়খানা বানিয়েছে। রান্নাঘর নিয়ে মায়ের শুচিবাই আছে, সে কথাটি পর্যন্ত মনে রেখে নতুন উনুন, শুকনো কাঠ, পাটখড়ি মজুত করেছিল সে। গ্রামে আক্কাস আলীর একটাই বদনাম, সে খায় বেশি, দিনে তিনবার খায় এবং প্রতিবার দু’সের চালের ভাত। ভাল, তরকারির জন্যে কোন চাহিদা তার ছিল না। লবণ, পেঁয়াজ, লঙ্কা পেলেই তার ভাত খাওয়া শেষ। গতরে বেশ বিরাট, কাজও করতে পারতো অসুরের মত। কিন্তু গ্রামে তার এই খোরাকি জুগিয়ে দিতে পারে, তেমন সচ্ছল লোকের সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। আমাদের কাজকে সে জানপ্রাণ দিয়ে করতো, বাড়িঘর দেখে মা ওর উপর খুশি। বাবাকে বলে ওর মাসিক বেতন দু টাকার স্থলে চার টাকা করে দিয়েছিলেন। বাড়ির ভাইবোন খেলার সাথী আমাদের দু বোনকে দেখে কাছে আসলো না ভেবেছিলাম এক বছরের মধ্যে ওদের দেখিনি, কত খেলবো, মজা করবো। কিন্তু ওরা আমাদের মেহমান মনে করে।
সেরকম ভাব দেখাচ্ছিল। কথা বলে উত্তরও পাচ্ছিলাম না, কেবল চোখ বড় করে দেখছে, মুখে কাপড় গুঁজে, আধা ঢেকে। মনে করলাম আমাদের কথা ওরা বুঝতে পারছিল না। শহরের ভাষা বলে যাচ্ছি। বাড়িতে যেভাবে আগে কথা বলতাম, চেষ্টা করলাম। আমাদের মুখের কথা অন্য রকম, তাদেরও শাড়িপরা জড়োসড়ো ভাব। তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, দাদিমা যে তার ঘর ছেড়ে আমাদের দেখতে আসেননি? ঐদিকে দৌড়ে গিয়ে তাকে পেলাম, নিজের বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখে উঠতে গিয়ে পারলেন না। শরীর খারাপ ভেবেছিলাম, আসলে যা ভেবেছি তার চেয়ে বেশি খারাপ, ক্ষয়ে যাচ্ছেন, ওঠার শক্তি হারিয়ে চলেছেন, তার কুঞ্চিত চোখ দেখছিলাম, পানি পড়ে বালিশ ভিজে যাচ্ছিল, আমি আর ঠিক থাকতে পারিনি, বুকে মুখ লুকিয়ে জোরে কেঁদে দিয়েছি। তেঁতুল, গুড়, মোয়া, চাল ভাজা আঙ্গুলের ইশারায় দেখিয়ে খেতে বলেছিলেন। আমি কান্নাভেজা গলায় বলেছিলাম, এবার আপনাকে নিয়ে যাব, শহরে ডাক্তার আছে, অসুখ সারিয়ে দেবে।
আর নিতে পারলি না, সময় শেষ। এই দেখ শুয়ে নামাজ পড়ি, সূরা মনে থাকে না। আল্লাহকে বলি, তোমার ওয়াস্তে নিয়ত বাধলাম এই আছরের নামাজের। আল্লাহ তুমি এক, তুমি দয়ালু, আমার নামাজ কবুল কর … আমি কান পেতে শুনেছিলাম এবং কাছে বসে থাকলাম। অনেক পরে আমার খোঁজ পড়ে, বনে-বাদাড়ে ঢুকে কোথায় লতা-পাতায় পা জড়িয়ে পড়ে আছি। কেউ জানতো না আমি এতক্ষণ দাদির কাছে, খেলাধুলা ছেড়ে ঐ বয়সে কে আর বাকশক্তিহীন বৃদ্ধার কাছে বসে থাকবে। মা কাজকর্ম গুছিয়ে দাদিকে দেখতে গিয়ে দেখলেন আমি সেখানে। ঘরে যেয়ে কাপড় জামা ছেড়ে বিছানায় বসে থাকার হুকুম দিলেন। মশারির নিচে বসেছিলাম, আর কেঁদেছিলাম। জিদ আসলে আমার দাঁত দিয়ে কিছু কাটতে ইচ্ছা হতো, দাঁত বসিয়ে সেলাইয়ের সময় সূতা কাটতাম, তখন মশারির খানিকটা কেটে দিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম সেদিন।
শৈশবকাল মানবজীবনের একটা চঞ্চল মুহূর্ত, কি করবে ভেবে পায় না।থিতু হওয়া নেই। আমরা বাড়ি গিয়ে কয়েকদিন না যেতেই এক ফাঁকে আগের সেই যেমন ছিলাম তেমনটি হয়ে গেলাম। খেলাধূলার মধ্যে সুপারি গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে পিড়ি বসিয়ে দোল খাওয়া ওদের শিখিয়ে দিলাম, বেশ জমে উঠলো। মেয়েরা এটার দিকে বেশি ঝুঁকে গেলাম। সাঁতার কাটার জন্যে আগের মত যখন তখন পানিতে ঝাপিয়ে পড়তে পারতাম না, তোলা পানির গোসলে প্রায় অভ্যাস হয়ে গেল, সাঁতারে নামতে ভয়ও করছিলাম। তখন সাঁতারের সাথীরা শহুরে মেম বলে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিত। ওদিকে মা ভাবতেন আমি পানিতে নেমেছি। এক এক সময় দুই দিকের কোনটা ছাড়বো, কোনটা করবো, এই ভেবে দিশে পেতাম না। আমার ছোটবোন এরকম চলতোনা, উল্টো আমাকে বকুনি দিতে আসতো, ওরা যে অসভ্য, ন্যাংটা হয়ে পানিতে নামে, তুই ওদের সঙ্গে খেলবি না, পানিতে নামবি না। আমি ওর কথা নিয়ে রাগ করতাম না, আমার ভেতর দোটানা ভাব যে আছে, ওর নেই, আমার চেয়ে ও যে ভাল স্বীকার করে নিতাম।
আমাদের ঘরের সামনের দিকে একটা বড় কদম গাছ ছিল, ফুল গাছে নেই, হঠাৎ একদিন উপরে মগডালে এক থোকা কদমফুল দেখি। মেজ জেঠাতো ভাই তাহের, আমার থেকে সামান্য বড়, সেও বাবার সাথে পূজার ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। যশোর জেলা পেরিয়ে বনগাঁ হাই স্কুলে পড়ে। বনগাঁয়ের কাচা গোল্লা (ছানার তৈরি মিষ্টি), খুব নামকরা, জেঠাজি প্রতিবছর ছুটিতে বাড়ি আসার সময় আনেন। তাহের ভাই লুকিয়ে আমাকে খাওয়াতেন। বলতাম, জেঠীমা আমাদের অনেক দিয়েছেন, তুই আবার দিচ্ছিস কেন? ওকে গাছে উঠতে বললাম, ঐ কদম ফুল পেড়ে দিলে তবে তোর মিষ্টি খাব। বেচারা কিছুদূর উঠে আর পারলো না, ভয়ে নেমে দৌড়ে পালিয়ে গেল। উনিও শহরে বাস করেন, কলকাতার ভাষায় সুন্দর কথা বলেন, স্কুলের ভাল ছাত্র, জেঠাজি ঐ স্কুলের হেড মৌলভী। গাঁয়ের ঐসব দস্যিপনা স্বভাব তার থেকেও বিদায় নিয়েছে।
সেবার মায়ের অত্যাগী জ্বর হয়েছিল। সিন্দুকের উপর পিতলের কলসির মুখে শাপলার নল লাগিয়ে রাতদিন. মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি। মেজ ও বড় জেঠীমাদের সারারাত জেগে থাকতে দেখতাম। কপাল, হাত, পা বার বার মুছে দিতেন। মেজ জেঠী নিজে হোমিওপ্যাথিক বাক্স খুলে ওষুধ দিয়েছেন, বার্লি, সাগু শুধু পানিতে জ্বাল দিয়ে খেতে দিতেন, দুধ মেশাতেন না। এমন সেবা-যত্ন পেয়ে মায়ের জ্বর চলে গেল। কৈ মাছের ঝোল, কাঁচা কলা সিদ্ধ, বাচ্চা মুরগির সুরা খেয়ে মা সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমরা আর কেউ জ্বরে পড়িনি। সেবার ছুটি শেষে শহরে চলে আসি।
যেবার আমি ক্লাস ফাইভে পড়ছিলাম, এই আশ্বিনে পূজার ছুটিতে বাড়ি আসলে নতুন এক অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম। কাল বৈশাখীর মতো সাংঘাতিক ক্ষতি করে দিয়েছিল সেবারের আশ্বিনের ঝড়। বাবার টিনের ঘরটি বাতাসে দুলে নড়বড়ে হয়ে গেল, টিনের চালা উড়ে গেলে আমরা ছুটে এসে পাশের তাহের ভাইদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ঝড়ে এ ঘরটিও বুঝি উড়িয়ে নেবে এমন বাতাস তখনও বইছিল। বাড়ির সকল ঘরে ছেলেরা আযান দিচ্ছিল, সামনের ঘরে মেজ জেঠা আযান দিচ্ছেন। অন্যদিকে আমাদের নিয়ে বাবাও ক্রমাগত আল্লাহু আকবর, আশাদু-আল্লা … হাঁক দিয়ে যাচ্ছেন, আল্লাহ আমাদের বাঁচান… আমরা দু’বোন কি করেছিলাম, আজো যেমন হাসি পায়, তেমনি মজাও লাগে। কেবল পেশাব পাচ্ছিল, চিলমচিতে করতাম আর বদনায় পানি খরচ করতাম, মুখে বলে যাচ্ছিলাম, আল্লাহ ঝড় থামিয়ে দাও, আর কখনো মাথার বাম দিকে সিথি কাটবো না, স্কুলে পেশাব করে পানি নেব, এমনি উঠে আসবো না, খেলতে গিয়েও মিথ্যা কথা বলবো না। ঝড় থেমেছিল ভোরে সূর্য ওঠার পর। ঝকঝকে রোদে চারদিক ঝলমল করছিল, নিজের ঘরে গিয়ে বিছানা জিনিসপত্র দেখে, মাকে শক্ত মুখে বলতে শুনলাম, এবার এখানে পাকা বাড়ি না তুলে শহরে যাব না, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি? বাবা বুঝতে পেরেছিলেন মায়ের আত্মসম্মানে ভীষণ আঘাত লেগেছে, বাড়ির অন্যান্য ঘর ঠিক দাড়িয়ে। তারটাই একমাত্র গরিবের বাড়ির মতো ঝড়ের কবলে পড়ে গেল। মাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন বাবা করতে দিলেন না। বলেছিলেন, খুব ভাল কথা, আক্কাস আলীতো আছেই, আপনি দেখাশোনা করবেন।
আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যস্বরূপ আমাদের আক্কাস আলী অক্লেশে দালান বানানোর লোকজন, মালমশলা জমা করে চললো, আমরা পাশে টিনের ছাউনিঘেরা দেয়া নতুন ঘরে থাকছি। বাবা শহরে যান-আসেন। দালান উঠতে থাকে। রাজমিস্ত্রীরা চাঁদনিরাত পেলে সারারাত কবির লড়াই, দল বেঁধে গায়, এন্না বেন্না বলে কি সব গায় . . . লাঠির আগায় পাট জড়িয়ে মশাল বানিয়ে রাতেও কাজ করে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস এসব দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। কিন্তু নভেম্বরের মাঝামাঝি আমি অস্থির, শহরে যেতেই হবে। বার্ষিক পরীক্ষা। বই-খাতা সাথে এনেছিলাম, নিজেরা পড়া চালিয়ে গেলে কি লাভ, পরীক্ষা না দিলে বড়দিমনি রেগে যাবেন, উপরের ক্লাসে উঠতে দেবেন না। বাবাকে একদিন বললাম, আমাদের শহরে নিয়ে চলেন, আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা সামনে। বাবা বেশ সচ্ছন্দে বলেছিলেন, তোমাদের দিদির সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে। তোমাদের সারা বছরের রেজাল্ট ভালো, কোন অসুবিধা হবে না। উনি বলেছেন। আমি একটুও দমে গেলাম না। আবার বলে দিলাম, পরীক্ষা না দিলে প্লেস থাকবে না। পরের বছর বৃত্তি দেব কি করে? প্রথম চারজনকে বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে নাম দেয়া হয়। আমি কি বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারবো না?
– সে ব্যবস্থা স্কুল নেবে, তুমি এমন জালাতন করছো কেন? থাম। বাড়িটা শেষ করতে দাও।
বাবা আদর করে কথা বলার মানুষ, এত জোরে ধমক দিয়ে কখনো কথা বলেন না, আমি কেঁদে দিলাম। বললাম, গ্রামে দালান বানিয়ে কি হবে?শহরে গিয়ে তো থাকবো ছনের ছোট ঘরে, আমার বান্ধবী সীতা, ছবি আমাদের বাসায় আসতেই চায় না, বলে তোরা কি গরিব নাকি, কুড়েঘরে থাকিস কেন?
আমি বাবাকে রাগতে দেখলাম না, কেবল আমার কথার জন্যে উত্তর দিলেন, ‘ওরা ভাল কথা বলেনি।’ এদিকে তাকে আমি নিজের মনের অবস্থা বোঝাতে চাই, তিনি তার কথাই বলে যাচ্ছেন। শহরে যাওয়ার সময় আবারো বায়না ধরলাম, আমাকে নিয়ে চলেন। তিনি এবার রাগলেন, পড়ালেখার নাম নেই, পরীক্ষা দিতে লাফানি-ঝপানি। তোর মা একলা, তুই ঘরের বড় মেয়ে, সে কথা আগে চিন্তা কর।
বাবা আমাদের কখনো তুই করে বলতেন না, সময় সময় আপনিও বলতে শুনতাম। সেটা আদরের ছিল। ঐ দিন আমার ভীষণ কষ্ট লাগছিল। উনি চলে যাওয়ার পর একটা চিন্তা মাথায় এলো, মুখে এতো কথা বলা যায় না। চিঠি লিখতে হবে। প্রথম চিঠি, কি রকম করে লিখব। ব্যাকরণ বই আমার ছিল দুটো, তাতে খুঁজে পেলাম, ‘পরম পূজনীয় পিতা ঠাকুর, সম্বোধন করে হিন্দুরা, মুসলমান করে ‘শতকোটি সালাম বাদ আরজ এই আব্বাজান। আমার বাবাকে মনের কথা লিখতে যাচ্ছি-এরকম লিখলে কেমন হবে, উনি তো আমাকে সব সময় নিজের থেকে মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখান। অনেকক্ষণ চুপ থেকে লিখতে থাকি ‘আব্বা, আপনি সামনে থাকলে আসল কথা বলতে পারি না, অন্যসব কথা বলে ফেলি, সেজন্যে এ চিঠি লিখলাম, দাদিমা বলেছেন, আপনি মাদ্রাসা লাইনে আর পড়বেন না, পালিয়ে গিয়ে ইংরাজি স্কুলে পড়েছিলেন। আরো শুনেছি আপনি আমার জন্মের পর ছেলে কি মেয়ে আলাদা না করে আযান দিতে ছিলেন। আমি আপনারই সন্তান, বার্ষিক পরীক্ষা দেবই, যদি না নিয়ে যান আমি পালিয়ে গিয়ে শহরে উঠবো।
হ্যারিকেনের আলোয় রাত জেগে পড়ছি দেখে মা আর দেখলেন না আমি আসলে কি লিখছি। ভোরে আক্কাস ভাই শহরে যাওয়ার সময় চিঠিটা দিয়ে খুব গোপনে তাকে বলে দিলাম, আব্বার হাতে দেবেন।
ঐ চিঠি কেলেঙ্কারি করে ছাড়লো। বাবাদের ‘বার লাইব্রেরিতে যারা তার ঘনিষ্ঠ ছিলেন, বাবাকে বকে আর রাখলেন না কিছু। সতর্কও করলেন, তুমি কেন, এই মেয়েকে দুনিয়ার কেউ আটকে রাখতে পারবে না। ভাল চাওতো শিগগির নিয়ে আস। ডিসেম্বর মাস শুরু হয়ে গেছে।
ঐ চিঠির জের বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলেন বাবা। শনিবার অফিস শেষ করে বাড়ি এসেছেন। চিঠিটা মাকে দেখালেন, বলে দিলেন বন্ধুদের কথাগুলো। বললেন, নিজ নিজ জিনিসপত্র ঠিকমত গুছিয়ে নাও। সেবার আমরা নৌকায় গিয়েছিলাম, জোয়ারের হিসাব মিলিয়ে নৌকা ছাড়া হয়েছিল তবুও এক জায়গায় নৌকা এসে আটকে গেল। ভাটার কারণে কচুরিপানা জমে গিয়েছিল। রাত তখন। ভাগ্য ভালো ছিল, কাছেই বাবার এক মক্কেল বাড়ি ছিল। ভোরে জোয়ার। আমরা সে বাড়িতে মেহমান ছিলাম সেই রাতে। আমার জন্যে সব্বাই এত কষ্ট পেল, ভাবতে আমারই কষ্ট লাগছিল। মা কিংবা বাবা যদি একবারও মুখ খিস্তি করে বলতেন, হারামজাদা মেয়ের এতো বাড়াবাড়ি, তাহলে হয়তো ভালো ছিল। কিন্তু আমার মা-বাবাকে আমি কোনদিন এবং কখনো মন্দ গালি মুখে আনতে শুনিনি, আমাদের জন্যে তো নয়-ই, চাকর-বাকরদের উদ্দেশেও নয়।
বাড়ি থেকে আসার সময় দাদিমাকে লাঠি ভর করে নৌকাঘাটে রেখে এলাম; পরীক্ষা দিয়েই চলে আসবো বলে এসেছিলাম। আসার দু দিন আগের ঘটনা। তিনি ধাপাবাড়ি গিয়েছিলেন, সবিতার ঠাকুরদাকে তুলসি তলায় নিয়ে রেখেছে, প্রাণটা যখন তখন বেরিয়ে যাবে। আমি সাথে, দাদি মা বার বার চোখ মুছে চলেছেন, সবিতার বাবা মনিব ঠাকুরণকে ঐ বিপদের মধ্যেও বার ঘর খুঁজে একখানা চেয়ার এনে বসতে দিল। ঠাকুরদার পাখিটির মুখে এখন কেন ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম নেই, ওকি বুঝতে পেরেছে তার প্রিয়জনটি আর তাকে দানাপানি দিতে উঠে আসবে না? দাদিমার সঙ্গে আমিও চোখ মুচ্ছিলাম। ফেরার পরে দাদিমার দুঃখ দুঃখ গলা, তোর দাদার পাঞ্জাবি লুঙ্গি ছিল শাদা, ফকফকা করে ধুয়ে দিত নন্দ ধোপা, এতদিনে ওর স্বর্গলাভ হবে। ধোপাবাড়ি যাওয়ার পথে, আমাদের বাড়ির পেছনে একটা নালা ছিল, তার উপর একখানা তক্তা, দাদিমা অবলীলায় পার হয়ে এলেন, আমাকে ধরতে হয়নি তাকে। শহরে আসার পথে এসব কথা মনে আসছিল। পরীক্ষার কথা একবারও মনে পড়েনি।
দেশের পাকা বাড়িটি শেষ করার তাগিদ ছিল। আক্কাস আলী খবরাখবর দিত। আমরা ট্রেন ও গরুর গাড়ি ধরে বাড়ি ফিরে আসি। বাবাও দালানের ছাদ পেটানোর কাজ বাদ দিয়ে কাঠের পাটাতন লাগিয়ে উপরে টিন বসালেন। সামনে লাল ইট, সিংহ দরজা দিলেন সামনে, চওড়া পাকা সিড়ি। চমৎকার এক বাংলোবাড়ি। নাম লেখালেন লাল-শাদা রঙের নকশা কেটে, আহম্মদ মঞ্জিল, আহকার সায়েদুল হক। পিতার নামের মিঞা লেখালেন না বাবা। নিজের নামের মিঞা আগেই জেলা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় ছেঁটে দিয়েছিলেন।
একটি স্কুলের জন্ম
তখন ব্রাবোর্ন কলেজ পার্ক সার্কাস থেকে বালিগঞ্জে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। আমাদের বাসা পার্ক সার্কাসে। কলেজের গাড়িতে যাওয়া-আসা। সেজন্যে চট করে মঞ্জুদেকে বলতে পারিনি যাব। জীবনে এমন নাটকীয় মুহূর্ত এল, অথচ গ্রহণ করতে পারলাম না। সময়টা আমার জন্যে ভাল ছিল না। বাড়িতে ঝগড়া হত আমাকে নিয়ে। কলকাতায় আমরা যে বাসায় থাকতাম, সেটি ছিল স্বামীর বড় বোনের। তিনি আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। আমি একটি পুত্র সন্তানের জননী। শিশু ফেলে কলেজে যাওয়া তার কাছে মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। কলেজ থেকে অন্য কোথায় বেড়াতে গিয়েছি, বাসায় দেরিতে ফিরলে তিনি কৈফিয়ৎ চাইবেন। আমি সেই সংকটকে বেশি ভয়াবহ ধরে নিয়েছিলাম। হয়তো এ কারণে কলেজে আসা-যাওয়া-পড়া বন্ধ হয়ে যাবে আমার। সে জন্যে সাহস করিনি।
নদীর করাল গ্রাসে নোয়াখালীর সদর শহরটির অনেক গিয়েছে। তারপরেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকলো, তা কিন্তু কম নয়। আনন্দ করার জন্যে, গর্ব করার জন্যে আমাদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু স্থান ও বিষয় অবশ্যই ছিল। বরুণ (হয়তো ব্রাউন) সাহেবের দিঘি ঘিরে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য এলাকা, আলোক উজ্জ্বল দোকানপাট, বাংলার রাজধানী কলকাতার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শহরের সুনাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। দীঘির উত্তর পাড়ে (সম্ভবত) জোড়া বটগাছ, তার তলায় ঝুলন যাত্রা, রাধাকৃষ্ণের লীলা দেখার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে ভিড় করতো। আমরাতো শহরেই থাকি, প্রতিদিন যেতাম, প্রতিদিনই মিষ্টি পেত যারা সেখানে উৎসব দেখতে গিয়েছিল। কে এত ভারে ভারে মিষ্টি যোগান দিত? সে এক আশ্চর্য কাজ, হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি ছিল এবং অর্থবানও ছিল, হতে পারে তারা সংগঠন করে এসব পরিচালনা করেছিলেন।
ঐ দীঘির পাড়ে বকুল, রাধাচূড়া গাছের সারি দেখলে অবাক হতে হতো। তাছাড়া রাস্তার ধারে যেমন দুদিকে মেঘনার উপশাখাগুলো প্রবহমাণ ছিল, তেমনই সারি সারি পবন গাছ (এখন ঝাউগাছ বলে) ঠান্ডা বাতাস দিত। গ্রাম থেকে আসা লোকজনদের শুয়ে থাকতে দেখতাম। মামলার দিন পড়েছে, দিনের কাজ শেষ হলে ফিরে যান তারা গায়ে।
নোয়াখালীর জজকোর্টটি ব্রিটিশ শাসকরা কেন যে এত দর্শনীয় করে বানিয়েছিল, কে জানে। সাম্পান বোঝাই ছোট বড় সুদৃশ্য পাথর, রঙিন বালুকণা তারা আনতো কোথা থেকে জানতে পারিনি। কেবল
অনুপম সৌন্দর্যময়ী প্রাসাদতুল্য কোর্টটি স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আশ্বিনে পূজার ছুটির দিনে ফুলের মালা হাতে নিয়ে বাবার সাথে কোর্টে যেতাম। আমার আকর্ষণ ছিল জজ সাহেবের নদীমুখো ছোট বারান্দাটি। একখানা লাল ভেলভেটে মোড়া চেয়ার, সিংহাসন যেমন, নকশা তেমন, সামনে কোন কোলাহল ছিল না, ধূ ধূ মাঠ, চরাঞ্চল, অবশেষে নীল জলরাশির ঢেউ কোন আকাশ তলায় গিয়ে মিশে যেত। কিছু জানার নয় শুধু ভাবনাকে ছেড়ে দেয়া। আমি জজ সাহেবদের জন্যে এত উদার উন্মুক্ত স্থান দেখে হিংসায় মরে যেতাম। কোন কোন সময় ঐ চেয়ারে বসেও যেতাম। দুর্গাপূজার ঐ ছুটির দিনটায় উকিল, নাজির, পেশকার সকলেই মজা করতেন। নানান অনুষ্ঠানও করতেন … হাসির গল্প বেশি শুনতাম।
শহরটি ছোট হয়েছে নদী ভাঙ্গার কারণে। জেলার আয়তন বড় ছিল। চর দখল, মারামারি, লাঠালাঠি, খুন-জখম নিয়ে মামলা করার লোকও কমতি ছিল না। হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ফেনী, লক্ষ্মীপুর থেকে সদরে মামলা দায়ের করার জন্যে প্রতিদিন প্রচুর মানুষের আনাগোনা হতো।
একবার এলেন এক পাগলা জজ সাহেব। আসলে তিনি সৎ, মেধাবী এবং করিৎকর্মা পুরুষ ছিলেন বলে স্থানীয় লোকদের তাকে নিয়ে ভালবাসার প্রকাশ ছিল ঐ ‘পাগলা’ শব্দটি। সহজ সরল গায়ের মানুষ। প্রশংসা করেছিল তেমনি সহজ কথায়। তিনি ছিলেন আই. সি.এস. জ্ঞানাংকুর দে। দেখতেও ছিলেন রাজপুত্র, ঘরেও তার ছিল অসামান্য রূপসী বিদূষী স্ত্রী উমা। উমা দেখলেন এ এক আজব শহর। পুরুষরা কি জাহাবাজ উচ্চ শিক্ষিত অথচ মেয়েদের লেখাপড়া করবার সুযোগসুবিধা নেই এখানে। ঐ টিম টিমে একটি প্রদীপ, সরকারী এম. ই স্কুল! তিনি স্বামীর মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিলেন নিজের ভাবনা। এই শহরে মেয়েদের জন্যে হাই স্কুল একটা চাই। সুন্দর আঁখিপল্লব স্থির রেখে স্বামীকে বলেছিলেন, তোমার উকিলদের লজ্জাও নেই, মেয়েদের মূর্খ রেখে তারা তোমার সঙ্গে আইনের প্যাচ কষে। ওদের বলে দিও এই শহরের মেয়েরা পড়ার জন্যে কলকাতা, ঢাকা যাবে না, আমি এখানে থেকে ওদের পড়ার ব্যবস্থা করা দেখতে চাই। জজ সাহেব দেরিকরলেন না, কয়েকজন বিশিষ্ট উকিল এবং মোক্তারকে নিজ বাঙলোয় নিমন্ত্রণ করে আনেন। যা বলার মেম সাহেব বললেন। ঘটনাটি চমকপ্রদ। মেয়েদের স্কুল একটা তুলতে এমন আর কি? ইনসপিরেশন এসেছে এমন এক নারীর থেকে, তাকে তুষ্ট করতে পারলে আইনজীবীরা ধন্য হবেন। সময় ছিল ডিসেম্বর মাস। শুকনোর মৌসুম। চরের খোলা জায়গায় বিদেশী সার্কাস পার্টি, বোবা টকিজ, খেলাধূলার ক্যাম্প প্রভৃতি বসানো যাবে। প্রতিবছর এরা আসে ব্যবসা করতে। এবার এদের নিয়ে চ্যারিটি শো করা হবে কয়েকটি। টিকিটের বই ছাপানো এবং বিক্রি এ ধরনের দায়িত্ব বাবা নিয়েছিলেন। আমাদের বৈঠকখানায় মিটিং এবং খাওয়া-দাওয়া হতে দেখেছি। আমি নিতান্ত ছোট নই, চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা শেষ, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী।
উমা যে সাক্ষাৎ উমা দেবী ছিলেন! তিনি ঐ বিশিষ্ট আইনজীবীর স্ত্রীদের নিয়ে তার সোনাপুর ডাকবাংলোয় মিটিং ডেকেছিলেন। বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি তবুও মাকে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে যেতে দেখলাম। দিনেও নয়, সন্ধ্যার পর। আমি একটু মাথা তোলা ছিলাম সেজন্যে সাথে যেতে পেরেছিলাম। অনেকের উপস্থিতির মধ্যে মুসলিম ছিলেন আমার মা, রেজাকুল হায়দার চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী, মৌলভী আবদুল গোফরান সাহেবের স্ত্রী (অন্য কেউ হয়তো ছিলেন এক কি দুই)। এদের মধ্যে মা বেশি পর্দা করছিলেন, গায়ের চাদর খোলেননি। অপর দিকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উমা দে জ্বলজ্বল করছিলেন মিটিং রুমে। জজ সাহেবের পেশকার, নাজিরদের স্ত্রীও একজন ছিলেন। তাদের স্বামীরা মিটিংয়ের আয়োজনে ছিলেন, হয়তো স্বামীর চাকরির কারণে আসতে হয়েছে, সেদিনের একটি কথা ধ্রুবতারা হয়ে আমার। জীবনে উদিত করেছিলেন মহিয়সী উমা। মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার মেয়েটাকে দেখে আমি একটা কথা জানতে চাই। এই সুন্দর হাসিখুশি মেয়েটার ভবিষ্যত কি ঐ ক্লাস সিক্স পর্যন্ত? তারপর ওকে কোথায় পড়াবেন? অন্যদের মতো কলকাতা, ঢাকা, কুমিল্লা যে পড়াবেন না সেটি আপনাকে দেখেই আমি অনুমান করছি। আপনি সাংঘাতিক কনজারভেটিভ। আমি দেখছি এই নোয়াখালী শহরে আপনাদের মতো মুসলিম মহিলার সংখ্যাই বেশি। একটা কিছু করুন আপনারা। এসব মেয়েদের পড়ার জন্যে শহরের মধ্যে হাই স্কুল করতেই হবে। আমি আপনাদের সাথে আছি। ঐদিন রায়বাহাদুর জগদীশ চন্দ্র রায় চৌধুরীর স্ত্রীকে সভাপতি করে একটি অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছিলেন শ্রীমতি উমা। চাঁদা আদায়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করা এ কমিটির কাজ ছিল। এতে মাকে সদস্য করা হয়, মায়ের সঙ্গে সেজেগুজে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কয়েকবার চৌধুরীদের চকমেলান দালান বাড়ির সাজানো অন্দরমহলে। আমি গিয়েছিলাম সে কথা বেশ মনে পড়ে। তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা কলকাতায় থেকে পড়ালেখা করতো। উকিল রায় চৌধুরীর মা তখন সদ্য প্রয়াত। তিনি মায়ের নামে এক ভরি ওজনের স্বর্ণপদক ‘যোগমায়া স্মৃতিপদক’ দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। নতুন স্কুলে যে সবচেয়ে ভাল করবে ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে, তাকেই এই পুরস্কার দেয়া হবে।
এ স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে মা সাহসী হলেন, আত্মবিশ্বাসীও সে সঙ্গে। নিজের সোনার গহনাতো আগেই দেয়া হয়ে গিয়েছে, সেই শিক্ষা তিনি এখন অন্যদের উপর দিতে থাকেন। সাড়াও পেয়েছিলেন। সংসারের অনেক খরচও তিনি কমিয়ে স্কুল কমিটিতে চাদা দিয়েছিলেন। ভাল কাজের জন্যে পথে নামলে একদিন তার সুফল পাওয়া যায়, মা একথা প্রায় শোনাতেন। বিদ্যা শিক্ষা করা মুসলমানদের জন্যে ফরজ’ একথা মা এবং বাবা দুজনের মুখ থেকে শুনতাম। কিন্তু মনে প্রায়শ প্রশ্ন হয়েছে পরে, একজন কলকাতার মেয়ে। এসে মেয়ে স্কুল স্থাপনের কথা এমন করে ভেবেছিল, শহরের মধ্যে কত বিদ্বান সমাজসেবী এবং রাজনীতিবিদ ভারত উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারা কেন ভাবেননি? শ্রীমতি উমা তাই আমাদের কাছে বেহেস্ত থেকে এসে হাজির হয়েছেন। এক পবিত্র ব্যক্তিত্ব, তার নামে স্কুলটি দাড়িয়ে গেল। হোক না মাটির ভিটে, কিন্তু টিনের ছাউনি আর দেয়াল সেগুন কাঠের ফ্রেমের উপর মজবুত তার গাঁথুনি। দরজা-জানালাও বেশ বড় এবং দেখার মত। নোয়াখালী টাউন হলের ওদিকে লোকসবতি ঘন, সম্ভবত কোন মহানুভব ব্যক্তিসামান্য দামে বেশ বড় কোন জমি স্কুলের জন্যে দিয়েছিলেন। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী, এ চারটি ক্লাস নিয়ে স্কুল।
স্কুলের শিক্ষকতা করতে এগিয়ে এলেন নিবেদিত প্রাণ কয়েকজন উকিল বাবু। পার্টটাইম পড়িয়ে যেতেন, অংক, ইংরাজি, বাংলা। এরা কোন অর্থ নিতেন না। কিন্তু এভাবে তার স্কুল চলবে? শ্রীমতি উমা তাতে দুঃখ পেলেন, তার গড়া স্কুল টিকিয়ে রাখার চিন্তায় তিনি অন্য ব্যবস্থা নিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান করে শিক্ষা ফান্ড গঠন করালেন। বিচক্ষণতার আড়ালে তার স্বপ্নসাধ ছিল অতি উঁচুমানের। ফান্ড যখনবেশ আশাপ্রদ হয়ে গেল, তিনি কলকাতা থেকে প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিয়ে এলেন। তিনি মিসেস সৌদামিনী চৌধুরী। তার স্বামীও একজন সমাজসেবক এবং পেশায় আইনজীবী। তারা উভয়ে উমা দেবীর মহান ডাকে সাড়া দিলেন। তারা অনেক বছর পর্যন্ত স্কুলে থাকলেন, মজবুত বুনিয়াদ দিয়ে গেলেন। স্কুলের ভিতর হোস্টেল করা হল তাদের জন্যে। নোয়াখালী শহরের লোকজন হয়তো তাদের উপযুক্ত সম্মানী দিতে পারেনি, কিন্তু প্রচুর সমাদরে রেখেছিল একথা যথার্থ। তা নইলে নিজেদের পুত্র-কন্যা ছেড়ে সুদূর নদীভাঙ্গা এক অনুন্নত শহরে তারা থাকতে পারতেন না। তবে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে এতদাঞ্চলে হিন্দুরাতো বটেই, মুসলমানদের কয়েকজন উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত ছিলেন। এরা শিক্ষিত পরিবেশ পেয়েছিলেন। এ কথা তারা বলতেনও।
আমার আজো এ বয়সে ভাবতে ভাল লাগে, উমা দে কে আমি দেখলেই আকাশ থেকে পরী নেমে এসেছে, এমন খুশি হতাম। ঐ স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তিনি কলকাতায় ফিরে যান, আর দেখিনি তাকে। দেখার আকাংক্ষা ছিল। লোকে বলে আশা করলে ফলে না, মনের দুঃখ ঘুচে না, কিন্তু ‘উমা দে’কে দেখার আকাংক্ষা আমার পূরণ হতে গিয়ে নিজের ভাগ্য দোষে সম্ভব হল না, সে দুঃখ আমি রাখবো কোথায়। শৈশবের চাওয়া বেশি পাওয়ার মত, সেজন্যে ঐ ঘটনাটি আমি আজো হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছি। কলকাতা লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রীরা নবীনবরণ অনুষ্ঠান
করছে, নাটক করছিল চন্দ্রগুপ্ত। বীর আলেকজান্ডারের স্ত্রী হেলেন সেজেছিল মঞ্জু দে (নামটি ঠিক মনে নেই। ভুলও হতে পারে) সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী ছায়া দেবী হয়েছিল নমিতা সিংহ। বিদেশিনীর সাজে একেবারে অচেনা লাগলেও পরে মঞ্জুদের মুখখানা চেনা মনে হচ্ছিল। এমন সুন্দর একখানা মুখ কোথায় দেখলাম কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। এক সময় আমার পরিচয় দেয়ার পালা এলো। কোন মতে নামটা বলতে পেরেছি। এতো বড় নাম হাসাহাসি শুনছিলাম। তার মধ্যে একটু রসিকতার সুরে কে যেন জিজ্ঞেস করছে, কোন ডিস্ট্রিক্ট? এ কথায় কাজ হল। মনে রাগ এসে যাওয়ায় গলার জড়তা চলে গেল। গর্ব ঢেলে বলেছিলাম, নোয়াখালী উমা গালর্স হাই স্কুল থেকে ফার্স্ট গ্রেড স্কলার। যোগমায়া গোল্ড মেডেল নোয়াখালীর মেয়ে বলেই পেয়েছি, কলকাতার হলে দিত না।
আমি মনে করলাম, এই মঞ্জু দে নিশ্চয় উমা দে’র কন্যা। ওর মুখে মায়ের মুখের আদল। আমার সেই বিপন্ন অবস্থার মধ্যে মঞ্জু এগিয়ে এসে আমার দু হাত টেনে ধরে আবেগী গলায় বলে, তুমি আমার মায়ের স্কুল থেকে এসেছ? কি আশ্চর্য! মা শুনলে খুশিতে না হার্টফেল করেন, তুমি কি যাবে আমাদের বাড়ি? কাছেই ঐ তো বালিগঞ্জ লেক প্লেসে।
তারপর মঞ্জু আমার এক হাত ওর এক হাতের উপরে উঠিয়ে সকলকে উদ্দেশ করে ঘোষণা দিল, কোন জেলা শুনেছ? ওটা আমার মায়ের স্কুল, সেখানে লেখাপড়া হয় শুনলেতো।
তখন ব্রাবোর্ন কলেজ পার্ক সার্কাস থেকে বালিগঞ্জে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। আমাদের বাসা পার্ক সার্কাসে। কলেজের গাড়িতে যাওয়া-আসা। সেজন্যে চট করে মঞ্জুদেকে বলতে পারিনি যাব। জীবনে এমন নাটকীয় মুহূর্ত এল, অথচ গ্রহণ করতে পারলাম না। সময়টা আমার জন্যে ভাল ছিল না। বাড়িতে ঝগড়া হত আমাকে নিয়ে। কলকাতায় আমরা যে বাসায় থাকতাম, সেটি ছিল স্বামীর বড় বোনের। তিনি আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। আমি একটি পুত্র সন্তানের জননী। শিশু ফেলে কলেজে যাওয়া তার কাছে মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। কলেজ থেকে অন্য কোথায় বেড়াতে গিয়েছি, বাসায় দেরিতে ফিরলে তিনি কৈফিয়ৎ চাইবেন। আমি সেই সংকটকে বেশি ভয়াবহ ধরে নিয়েছিলাম। হয়তো এ কারণে কলেজে আসা-যাওয়া-পড়া বন্ধ হয়ে যাবে আমার। সে জন্যে সাহস করিনি।
আমার ভাগ্যের পরিহাস তখন শুনিনি। আমার বালিকা চোখের পরীর মতো সুন্দর অসাধারণ মানবীকে ভয়ে দেখতে গেলাম না অথচ কলেজ যাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল। মঞ্জু দে কে আর দেখিনি, সেও পাস করে চলে গিয়েছিল। এমনই হয়, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মানুষকে দেখার ভাগ্য সাধারণত মিস হয়ে যায়, সে যে কারণেই হোক।
যে স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রীকে নিয়ে এত স্মৃতি অথচ ঐ স্কুলের জন্যে নোয়াখালী শহরের হয়তো আরো অনেকে নিবেদিত প্রাণে সেবা দিয়েছিল, আমার অপরিণত বয়সের জ্ঞান ও সীমাবদ্ধতার কারণে আমি তাদের চিনিনি, জানিনি। তাই তাদের নাম উল্লেখ করতে পারিনি বলে লজ্জিত এবং দুঃখিত। তারা আমার শিক্ষালাভের পথ নিষ্কন্টক করেছেন, আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার মানুষ।
উমা স্কুল থেকে প্রথম বর্ষে ম্যাট্রিক দেয়া হয়নি, কিন্তু তার পর থেকে ঐ মঞ্জু দে এবং অন্যরা ম্যাট্রিক দিয়েছিল। সেই ১৯৪০ সনের কথা। সম্ভবত মিসেস মেহেরুন নেসা লালু আপা (ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট), রাজিয়া মতিন চৌধুরী (প্রিন্সিপাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ), শহীদুন নাহার এবং ১৯৪৪ সালে দেই আমি এবং সুফিয়া (কেবল মুসলমান মেয়েদের নাম দিয়েছি)।
রক্ষণশীলতা এবং পর্দাপ্রথার জন্যে মুসলমান মেয়েরা শহরে অবস্থিত অন্যান্য ছেলেদের স্কুলে পড়তে যেত না। হিন্দুদের জন্যে এ সমস্যা ছিল না। তারা অবাধে অরুণ স্কুল, কল্যাণ স্কুলে পড়তে যেত। এমনকি অনেকে উমা স্কুল হওয়ার পরও ঐসব স্কুলেই পড়তো। সম্ভবত এজন্যে শহরে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রভাবশালী হিন্দুরাঅনুভব করেননি। মুসলমান মেয়েদের পড়তে হলে মক্তবেই যেতে হয়েছে। আরবি ভালো শেখার সাথে সামান্য বাংলা এবং অংক পড়তো তারা। আমার ক্লাসমেট সুফিয়া মহব্বতপুর মক্তব থেকে এসে উমা স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছিল। এখানে সপ্তম শ্রেণী দিয়েই ক্লাস শুরু। যারা রক্ষণশীল মুসলমান অথচ স্ত্রী শিক্ষা দিতে আগ্রহী, তারা মেয়েদের ঢাকা ইডেন হোস্টেলে, কুমিল্লা নওয়াব ফয়জুন্নেছা স্কুল হোস্টেলে রেখে ম্যাট্রিক পড়িয়েছেন কিংবা কোন আত্মীয়ের কাছে কলকাতায় রেখে দিতেন। কলকাতা ব্রাবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা করার, প্রয়োজনবোধ করেছিলেন স্মরণীয় নেতা এ. কে. এম. ফজলুল হক। তাতে মুসলমান মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধা হয়েছিল, নোয়াখালী থেকে আমরাও সে সুযোগ গ্রহণ করি।
নোয়াখালীতে এমন অনেকেও ছিলেন, মেয়েদের শিক্ষা দিতে আগ্রহী, অথচ সুযোগ পাননি। বারে বারে নদী ভেঙ্গে নিয়েছিল তাদের সহায়সম্পদ, মেয়েকে বাইরে পড়াবার খরচ করবেন এমন সামর্থ হয়তো ছিল না। অল্প বয়সে সৎ ও বিদ্বান পাত্র খুঁজে বের করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাদের সাধ মিটিয়ে নিতে হয়েছে। সুধারাম ও হাতিয়ার অধিবাসীরা বেশি নদী ভাঙার সাথে বরাবর যুদ্ধ করে এসেছে। সন্দ্বীপও এ গ্রুপে ছিল। অতঃপর চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হয়ে যায়। এ অঞ্চলের মডেল প্রাইমারি স্কুলগুলোর অবস্থা শোচনীয় ছিল। শিক্ষক মূলত একজন, ছাত্ররা ছিল নানা বয়সী, বয়স বেশি থাক, কিন্তু পড়ুক, ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। মুসলমান মেয়েরা আসতোই না। প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুলও ছিল তখন। এগুলোতে মাস্টারদের বেতন শুনেছি ছাত্রদের মাসিক একআনা চাঁদা আদায় থেকে হয়ে যেত। পার্বতী বাবুর প্রাইমারি স্কুলটায় লেখাপড়া হতো। শহরে নাম ছিল।
(ক্রমশ)
রওশন সালেহা

রওশন সালেহার জন্ম নোয়াখালী, ১৯২৯ সালী ১ জুলাই। বাবা ছিলেন আইনজীবী। কলকাতায় ম্যাট্রিক ও আইএ পড়েছেন। সাতচল্লিশে দেশভাগের পরে বিএ পড়বার সময় দেশে ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করেন। বৈরুতে আমেরিকান ইউনির্ভাসিটি থেকে শিক্ষা প্রশাসন (UNESCO), দিল্লী এবং ব্যাংকক থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে প্রশিক্ষন নিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের জনশিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা থেকে ডিডিপিআই পদমর্যাদায় অবসর নেন। তাঁর প্রবল সাহিত্য অনুরাগের জন্য তিনি তাঁর সমকালীন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অনেক কবি সাহিত্যিকদের প্রায় সকলের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর ‘আমার এক নদীর জীবন’ প্রকাশিত হবার পর আত্মজৈবনিক সাহিত্য তিনি শক্ত স্থান দখল করে নেন। ‘ফিরে এসো খামার কন্যা’ উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে পরিচিত।