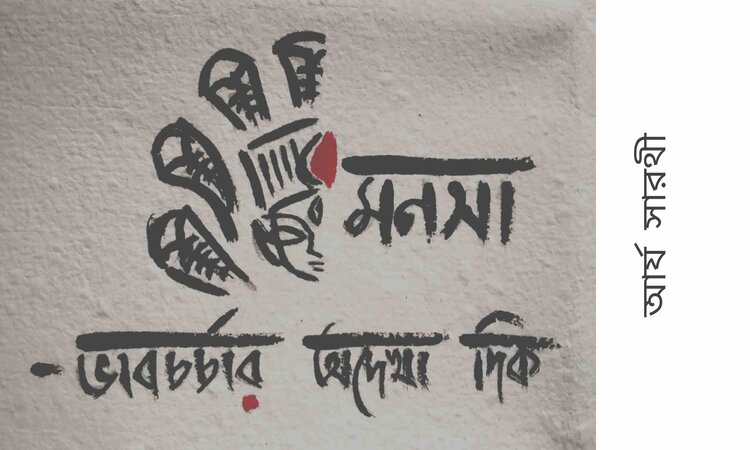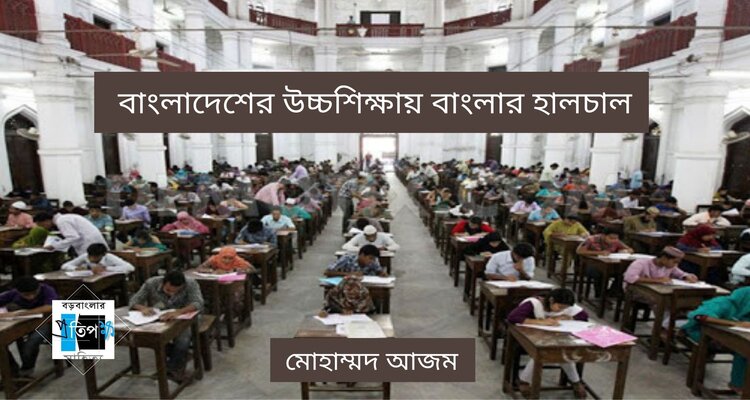।। সারোয়ার তুষার ।।
জায়নবাদের ইতিহাস ও মতাদর্শের আলোচনা করতে গেলে উল্লিখিত মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের আলোচনা না করে উপায় থাকে না। কারণ, আমরা পরে দেখব, জায়নবাদের ইতিহাস মূলত আধুনিক উপনিবেশ ও জাতিবাদেরই ইতিহাস। ওয়েস্টফালিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টরা নিজেদের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে ইহুদিরা নতুনভাবে অপরায়নের শিকার হতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি এ পর্যায়ে আধুনিক জাতিবাদী যুক্তির কোপানলে পড়ে তারা। “রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম”— এহেন সাম্প্রদায়িক নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টান সমাজের দোর্দণ্ডপ্রতাপে ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রান্তিক ইহুদি সম্প্রদায়কে পুনরায় কোণঠাসা করে। আঠারো-উনিশ শতকের নতুন ইউরোপীয় বাস্তবতায় ইহুদি সম্প্রদায়কে নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রশ্নে নতুন করে বিচলিত হতে হয়।
জায়নবাদ১: ইতিহাস ও মতাদর্শ

Like all nationalism, Zionism is founded on a binary of self and other for its identitarian project. What is noteworthy in this regard is how it is the anti-Semite, not the Jew, who constitutes the self for Zionism, with the Jew being the other against whom the new self must be based. In internalizing anti- Semitic subjectivity, Zionism adopts its epistemology lock, stock and barrel, thus seeing the Jew as everything the new Zionist identity is not.
— Joseph Massad২
ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট
ইহুদি আখেরিতত্ত্ব মোতাবেক মানব ইতিহাস শুভ ও অশুভর কুরুক্ষেত্র। মসিহার আগমনের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ঘটবে। মসিহার আগমন ইতিহাসেরও পরিসমাপ্তি ঘটাবে। একজন সাচ্চা ইমানদার ইহুদির কর্তব্য হচ্ছে মসিহার আগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করা। এই আখেরিতত্ত্ব মোতাবেক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ ইহুদিদের নাই। যে ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অধীনেই তারা থাকুক না কেন, নির্বিকার থাকাই সংখ্যালঘু ও ধর্মপ্রাণ ইহুদিদের জন্য বেহতর। ইহজাগতিক প্রশ্নে চূড়ান্ত নির্লিপ্তি ইহুদি ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টান সমাজের জুলুম নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় মসিহা আগমনের নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষা ও প্রার্থনাই ছিল রেওয়াজ।৩
সকল কালের সকল সমাজেই ভিনদেশি অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ কমবেশি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ইউরোপের ‘ইহুদি সমস্যা’ তথা ইহুদি ঘৃণার গোড়া খুঁজতে গেলে বেশ তাজ্জব হতে হয়। কারণ ইউরোপে ইহুদিরা সেই অর্থে ভিনদেশি কিংবা অচেনা সম্প্রদায় ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই ইহুদিরা ইউরোপীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মধ্যযুগের মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ইহুদিদের বিচরণ ছিল। তথাপি, পশ্চিমা সমাজে ইহুদিরা ছিল অপরের প্রতিরূপ (figure of the other)। সকল ধরনের অপরের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ইহুদি প্রতিরূপের মাধ্যমে ঘটত।৪
ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের সম্পর্ক বেশ অম্লমধুর। খ্রিস্টান ধর্ম নিজেকে একইসাথে ইহুদি ধর্মের ধারাবাহিকতা এবং শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করে এসেছে। খ্রিস্ট ধর্মতত্ত্ব মোতাবেক খ্রিস্টানরা খোদার সাথে সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরানা চুক্তি পেরিয়ে এসেছে। চার্চের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের সাথে খোদার নতুন ধরনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।৫ যিশুখ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ইহুদিরা তাদের জন্মগত বিশেষাধিকার খুইয়েছে, কাজেই খ্রিস্টানরাই খোদায়ী মনোনয়নের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।৬ গসপেলের বাণীকে অবজ্ঞা করে এবং যিশুখ্রিস্টকে শূলে চড়ানোর মাধ্যমে ইহুদিরা গর্হিত পাপাচারে লিপ্ত।৭ তাদেরকে পৃথিবীতে টিকে থাকতে দেয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে তাদের প্রাপ্য শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত যিশুর বাণী প্রত্যাখ্যানকারীদের অনন্ত ঘৃণা, অবজ্ঞা ও শাস্তির মধ্যেই দিনাতিপাত করতে হবে।৮
পশ্চিমা চৈতন্যে ‘ইহুদি প্রশ্নের’ অস্তিত্ব খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক দীক্ষার সমসাময়িক। এমনকী বাস্তব জীবনে ইহুদি হাজিরার পূর্বেই চৈতন্যগত ‘ইহুদি’ পশ্চিমা মানসে বরাবর জাগরূক থেকেছে। নিউ টেস্টামেন্টে ইহুদিদের সত্য ও নাজাতের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে বাস্তবের ইহুদিদের মন্দের প্রতিরূপ সাব্যস্ত করাটা খ্রিস্টান সমাজে আহামরি কোনো ব্যাপার ছিল না। নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত যিশুর জন্ম ও মৃত্যুর উপাখ্যান মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতার ঊষালগ্নে ইউরোপ ও আমেরিকার নাটক, গান, গল্পে বারবার পুনরুৎপাদিত হয়েছে। ইহুদিরা খ্রিস্টধর্মের বাণীকে প্রত্যাখান করার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যে দুর্ভোগ লিখিয়ে নিয়েছে। ইহুদিদের প্রতি খ্রিস্টান সমাজের এই মনোভাব এতটাই স্বাভাবিক ও ন্যায্য ধরে নেয়া হয়েছে যে এমনকী জেমস জয়েসের উপন্যাসের চরিত্রকেও বলতে শোনা যায়: “They sinned against the light… and you can see the darkness in their eyes. And that is why they are wanderers on the earth to this day.”৯
নিজ কর্মদোষেই যেন ইহুদিদের করুণ পরিণতি। এই ধারণা থেকে এমনকি খ্রিস্টান সমাজের উদার অংশও পুরোপুরি মুক্ত ছিল না। জার্মান পুরোহিত মার্টিন নিম্যোলারের হিটলার-বিরোধিতা পৃথিবীব্যাপী সুবিদিত। তিনি পর্যন্ত মনে করতেন যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পাপের বোঝা ইহুদিরা তাদের রক্তে বংশ পরম্পরায় বহন করে চলেছে: “… as a fearsome burden the unforgiven blood-guilt of their fathers.”১০
আদি–আধুনিক পর্বের ইহুদি বিদ্বেষ ও নিধন
১৩৪৮ সালের ব্ল্যাক ডেথ মহামারির পরে ইহুদিরা রাইন উপত্যকা থেকে পূর্ব ইউরোপে (বিশেষত পোল্যান্ড ও ইউক্রেন) হিজরত করে। এই মহামারিতে ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী নিহত হয়।১১ মহামারি ও ব্যাপক প্রাণহানির জন্য ইহুদিদের দায়ী করা হয়। ইউরোপের আধুনিক জমানায় রূপান্তর নতুন করে ইহুদি-ঘৃণার জন্ম দেয়। ১৪৯২ সাল একদিকে ছিল ইউরোপের নতুন যুগের যাত্রাবিন্দু; অন্যদিকে, ইহুদিদের সামষ্টিক জীবনে, এই সাল নতুন বিপর্যয় ডেকে আনে। সে বছরের ৩১ মার্চ স্পেন থেকে আড়াই লক্ষ ইহুদি বিতাড়িত হয়।১২ বিতাড়নের পূর্বে স্পেনে ইহুদিদের অন্তত এক হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছিল। হয় খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হবে, অথবা স্পেন ছাড়তে হবে— এমন পরিস্থিতিতে ইহুদিরা স্পেন ত্যাগই বেছে নেয়। ১৫১৬ থেকে ১৫৭১ সালের মধ্যে ভেনিস, রোম ও ফ্লোরেন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে ইহুদি ঘেটো নির্মিত হয়।১৩
মধ্য ও আধুনিক যুগের শুরুতে ইউরোপে ইহুদিদের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এ সময়ে তারা কায়মনোবাক্যে রুহানি মুক্তির উপায় সন্ধান করেছেন। প্রাত্যহিক প্রার্থনায় জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেছেন। পরের বছর যেন একে অপরের সাথে জেরুজালেমে কাটাতে পারেন, সেই প্রার্থনা করেছেন।১৪ কিন্তু এই প্রার্থনা কখনোই কোনো বাস্তব কর্মসূচিতে পরিণত হয়নি। রুহানি প্রার্থনা হিসেবেই বিরাজমান থেকেছে। ১৫২৪ সালে ডেভিড হ্যারিউভেনি (David Hareuveni) নামক একজন রহস্যময় ব্যক্তি সপ্তম ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপ ক্লিমেন্টের দ্বারস্থ হন এবং অটোমানদের উৎখাতপূর্বক পবিত্র ভূমি দখল করার প্রস্তাব পেশ করেন। পোপের কাছে এই উদ্ভট প্রস্তাবের তেমন একটা আবেদন ছিল না। হ্যারিউভেনি, সলোমন মলখো (Solomon Molcho) নামক আরেক পর্তুগিজ রহস্যবাদীর যোগসাজশে রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের কাছে একই প্রস্তাব পেশ করেন। সম্রাট দু’জনকেই গ্রেফতার করেন। মলখোকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয় এবং এক পর্যায়ে হ্যারিউভেনির আর কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।১৫
ইহুদিদের মধ্যে কে বা কোন গোষ্ঠী সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনে স্বতন্ত্র ইহুদি আবাসভূমির কথা তুলেছিল, এ নিয়ে বেশ কিছু মতামত চালু আছে। তবে ধারণা করা হয় প্রাগের অর্থোডক্স রাব্বি লিভা (১৫২৫-১৬০৯) প্রথম ফিলিস্তিনে ইহুদি পুনর্বাসনের দাবি তোলেন। তখনও ‘ইহুদি রাষ্ট্র’ ধারণার জন্ম হয়নি। তবে এ কথা ঠিক যে, স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে পূর্ণতা লাভের অংশ হিসেবেই রাব্বি লিভা ফিলিস্তিনের কথা ভেবেছিলেন।১৬ ১৬৪৮ সালে ইহুদি ইতিহাসের সবচাইতে বড় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইউক্রেনে হলোকাস্টের শিকার ইহুদিরা বোহদান জাইনোভি মাইখাইলোভিচ খমেলনিৎস্কির নেতৃত্বে পোলিশ জমিদারদের বিরুদ্ধে (ইউক্রেন তখন পোল্যান্ডের অন্তর্গত) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে প্রায় এক লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়।১৭ সমগ্র পূর্ব ইউরোপের ইহুদি জনগোষ্ঠী ৩০ শতাংশে নেমে আসে।১৮
এমন সময়ে সাব্বাতাই জেভি নামে একজন রহস্যবাদী ইহুদি নিজেকে মসিহা ঘোষণা করে ইহুদি সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ১৬৬৬ সাল নাগাদ ইহুদিদের পরিপূর্ণ নাজাতপ্রাপ্তি ঘটবে। এই ঘোষণার ফলে ইহুদিরা স্পেন ও ইউক্রেনে সংঘটিত দুই ভয়াবহ গণহত্যাকে নাজাতপ্রাপ্তির আবশ্যিক আগমনী ধাপ সাব্যস্ত করেন। মসিহার আগমনের মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুর দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে বিশ্বাস করে ইহুদিরা তাদের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে শুরু করেন। কিন্তু দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। উপরন্তু ইহুদিদের মধ্যে মসিহা আগমনের স্বপ্ন বুনে দেয়া সাব্বাতাই জেভি নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।১৯ এই ঘটনা ইহুদিদের স্তব্ধ ও বিমূঢ় করে দেয়। খোদা তাঁদের সাথে কোনো নিষ্ঠুর তামাশায় লিপ্ত কি না, নাকি তাঁদের কপালেরই দোষ— তাঁরা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিলেন না। প্রকৃত মসিহাই কেবল এই নিষ্ঠুর তামাশা বন্ধ করতে পারেন বলে তাঁরা পুনরায় বিশ্বাসে বুক বাঁধেন।
জাতিরাষ্ট্রের যুগে ইউরোপ
খ্রিস্টানদের ইহুদি-ঘৃণার ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট তো ছিলই। তা ছাড়াও নতুন যুগে পদার্পণের ফলে ইউরোপে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে পরিবর্তন ঘটছিল, সেটাও ইহুদি-ঘৃণার নতুন বাতাবারণ সৃষ্টি করেছিল। খ্রিস্টানদের অন্তঃধর্মীয় (intrafaith) বিবাদে সে সময়ের ইউরোপ টালমাটাল ছিল। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের প্রারস্পরিক বিদ্বেষ ও হানাহানি রীতিমতো যুদ্ধের রূপ লাভ করে। ত্রিশ বছরের এই ধর্মযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাব্যস্ত হয় যে, রাজার ধর্মই হবে প্রজার ধর্ম। অবশ্য চতুর্দশ শতকের স্পেনকে মুসলমানদের হাত থেকে ক্যাথলিকরা পুনরুদ্ধারের পর থেকে এটাই ছিল রেওয়াজ।২০ হয় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা ভিটামাটি ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যেতে হবে। অবশেষে ত্রিশ বছরব্যাপী ধর্মযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই দফারফা হল যে ক্যাথলিক রাজত্বে সকল প্রজার ধর্ম হবে ক্যাথলিক; আর প্রোটেস্টান্টদের রাজত্বে সকল প্রজার ধর্মমত হবে প্রোটেস্টান্ট। এ সাম্প্রদায়িক নীতিকেই “রাজার ধর্মই হবে প্রজার ধর্ম” আপ্তবাক্যে হাজির করা হল।২১ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের এই দফারফা ইতিহাসে “ওয়েস্টফালিয়ার সন্ধি” হিসেবে পরিচিত।২২ এর ফলে ধর্মের দিক থেকে রাজত্বগুলো একবাদী হয়ে উঠেছিল। ধর্মযুদ্ধে বিধর্মীনাশের মাধ্যমে ইউরোপে এক অদ্ভুত সাম্প্রদায়িক ‘শুদ্ধতা’ অর্জিত হয়েছিল। আশ্চর্য নয় যে, পরবর্তী কালের ইউরোপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে স্বাধিকার চেতনা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ইউরোপের এই একবাদী জাতীয়তাবাদের সাথে বহুত্ববাদী ধ্যানধারণার তীব্র সংঘাত লেগেই থেকেছে। এক অর্থে, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস “এক জাতি এক ধর্ম এক ভাষা এক রক্ত” কিসিমের বর্ণবাদী ধারণার সাথে বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক চেতনার সংগ্রামেরই ইতিহাস। ইতিহাসবিদ সুদীপ্ত কবিরাজ মন্তব্য করেছেন:
আমরা ইয়োরোপের যে ইতিহাস পড়ি এবং মুখস্থ করে পরীক্ষা পার হই তাতে দেখানো হয় যে ইয়োরোপীয় মানব ক্রমশই একটা থেকে আরেকটা মুক্তির দিকে লম্ফ দিয়ে বাকি পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যায় সেই ইতিহাস যে কেবল শ্রেণিবিদ্বেষের এবং শোষণের ওপরে প্রতিষ্ঠিত তাই নয়, নিজের অস্মিতা (identity) ছাড়া সে অন্য সব অস্মিতাকেই অবমাননা এবং হিংসা করে এসেছে। এবং তাই পাশ্চাত্যের আধুনিক ইতিহাস মানবিক ভ্রাতৃত্বের ইতিবৃত্ত নয়, প্রত্যেক জাতির অন্য জাতির বিরুদ্ধে হিংসার ও যুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস।২৩
সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান মোতাবেক ‘জাতি’ ধারণা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইউরোপ তার ধর্ম প্রশ্নের মীমাংসা করেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সত্য হচ্ছে, ইউরোপের ‘জাতি ধারণা’-র সাথে (খ্রিস্ট)ধর্মের যোগাযোগ ও আঁতাত গভীর।২৪ কারা এক ও অভিন্ন ‘জাতি’?— এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে আধুনিক ইউরোপ সাব্যস্ত করেছে যে, যারা ভাষা, ধর্ম ও রক্তের দিক থেকে ‘এক ও অভিন্ন’, তারাই একীভূত জাতি। অর্থাৎ, ইউরোপের জাতি ধারণা ‘মধ্যযুগীয়’ ধর্মের প্রতিবিধান তো নয়ই; বরং, ধর্ম, ভাষা ও তথাকথিত অমিশ্রিত রক্তই ইউরোপের আধুনিক জাতিবাদী ধ্যানধারণার গাঠনিক উপাদান হিসেবে রয়ে গেছে। একই রক্তের অধিকারী অভিন্ন ভাষিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী নির্দিষ্ট ভূমিতে ‘জাতিরাষ্ট্র’ কায়েম করবে— এমন ধ্যানধারণা ইউরোপ তো বটেই, উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর কাছে অমোঘ ও স্বাভাবিক মডেল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এই কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী রাষ্ট্র মানেই জাতিরাষ্ট্র।২৫ বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের মোড়কে হাজির করা হলেও, সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী এই (জাতি)রাষ্ট্রতত্ত্ব আধুনিক জমানার সকল সংকটের মূলে। আধুনিক জাতিবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্কও অত্যন্ত গভীর।২৬
‘জাতি’ ধারণার বলেই ইউরোপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। অভিন্ন ধর্ম-ভাষা-রক্তের বলে বলীয়ান কোনো ‘জাতি’ তথা সংগঠিত ইউরোপীয় লোকশক্তি পরদেশ আক্রমণ ও দখল করেছে। উপনিবেশিত অঞ্চল আকারে এবং জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তুলনায় বড়ো হলেও, তারা শুরুর দিকে উপনিবেশের যৌক্তিক বিরোধিতা করতে পারে নাই জাতি/জনগণ ধারণার অভাবে। উপনিবেশের শুরুর জমানায় উপনিবেশিত অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীরা ঠিক এ কারণেই উপনিবেশের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। এমন নয় যে তারা স্বাধীনতা-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কেন স্বাধীনতা? কার জন্য স্বাধীনতা? আমরা কি স্বাধীনতার লায়েক হয়ে উঠেছি তথা আমরা কি ‘জাতি/জনগণ’ হয়ে উঠতে পেরেছি?— এটাই ছিল প্রধান তর্ক।২৭ তার মানে দাঁড়াচ্ছে, কেবল স্বাধীনতা চাইলেই হবে না, তা চাওয়ার আগে ‘জাতি/জনগণ’ হয়ে উঠতে হবে। এই অর্থে ঔপনিবেশিক শাসন কেবল সামরিক শক্তির জোরে নয়, জাতি ধারণার বয়ানের জোরে তামাম দুনিয়া শাসন করেছে।২৮ আবার, ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে ‘সাংঘর্ষিক মোলাকাতের’২৯ মধ্য দিয়েই উপনিবেশিত অঞ্চলে স্বশাসনের বাসনা বিকশিত হয়েছে। ইউরোপীয় জাতিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত এ সকল অঞ্চলে ক্রমশ জাতীয় মুক্তির চেতনা তৈরি হওয়াতে তারা উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আবারও সুদীপ্ত কবিরাজকে দোহাই মানতে হয়:
… আধুনিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক পৃথিবীটা তৈরি হয়ে উঠেছে, সেটা স্ববিরোধী— তার মধ্যে দুটো বিরোধী স্রোত। একটা হলো প্রত্যেক জাতি-জনের স্বাধীনতার স্পৃহা এবং নিজের assertion— স্বশক্তির আস্বাদনের অনুভব— এবং স্বশক্তির আস্বাদনের সব থেকে বড় উপায় অন্যকে নিজের শক্তির অধীন করে রাখতে পারা। ইয়োরোপের নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের ইতিহাসে এর দুটো দিকই স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ফ্রান্স নিজের স্বাতন্ত্র্যের বিস্তারে অন্য সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে অধীন করেছে একদিক দিয়ে, আবার তারই জন্যে অন্যদিক দিয়ে পরাজিত জনগণেরা স্বাধীনতার সংগ্রামে নেমে পড়েছে।৩০
উপনিবেশিত অঞ্চলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যে যুক্তিতে তারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলকে (আমরা ইতিহাসের অগ্রসর স্তর তথা সংগঠিত লোকশক্তি জাতিবাদের স্তরে আছি) নিজেদের দখলে নিয়েছে, সেই একই যুক্তিতে উপনিবেশিত অঞ্চলের মানুষজন বিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তথা নিজেদেরকে জাতি/জনগণ ঘোষণা করেছে।৩১
আধুনিক কালের ইহুদি ইতিহাস
জায়নবাদের ইতিহাস ও মতাদর্শের আলোচনা করতে গেলে উল্লিখিত মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের আলোচনা না করে উপায় থাকে না। কারণ, আমরা পরে দেখব, জায়নবাদের ইতিহাস মূলত আধুনিক উপনিবেশ ও জাতিবাদেরই ইতিহাস। ওয়েস্টফালিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টরা নিজেদের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে ইহুদিরা নতুনভাবে অপরায়নের শিকার হতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি এ পর্যায়ে আধুনিক জাতিবাদী যুক্তির কোপানলে পড়ে তারা। “রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম”— এহেন সাম্প্রদায়িক নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টান সমাজের দোর্দণ্ডপ্রতাপে ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রান্তিক ইহুদি সম্প্রদায়কে পুনরায় কোণঠাসা করে। আঠারো-উনিশ শতকের নতুন ইউরোপীয় বাস্তবতায় ইহুদি সম্প্রদায়কে নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রশ্নে নতুন করে বিচলিত হতে হয়। নতুন এই যুগে ‘ইহুদি প্রশ্ন’ ইউরোপের নামজাদা বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকদের বেচইন রাখে: “Emancipation brought the Jews into the world, but at the same time it created the Jewish question.”৩২
ঠিক এমন পরিস্থিতিতেই জায়নবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। জাতিবাদ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে ‘ইহুদি প্রশ্ন’৩৩ নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। আঠারো শতকের ইহুদিদের মধ্যে ঐতিহাসিক ধৈর্যচ্যুতি লক্ষ করা যায়। মসিহা আগমনের নিষ্ক্রিয় নিষ্ফলা গালগল্পে তাদের আর আস্থা ছিল না। ইতিমধ্যেই গত দুইশো বছরে ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আধুনিকায়নের সংস্পর্শে অন্যান্য যে কোনো সম্প্রদায়ের মতো তাঁরাও মানব ইতিহাসের প্রায় সকল যজ্ঞের সমান অংশীদার ছিলেন। বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পী-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সকল শ্রেণি-পেশায় তাঁদের সরব উপস্থিতি ছিল। তবু, জাতিধর্মবাদী ইউরোপে দৈনন্দিন বর্ণবাদের শিকার হওয়া থেকে তাঁদের রেহাই মেলেনি।
আলোকায়নের স্বপ্ন
জায়নবাদের আগে নব প্রজন্মের ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোকায়ন এবং ইউরোপীয় সমাজে আত্মীকৃত হবার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। আধুনিক ইউরোপের নানান গালভরা প্রতিশ্রুতি নতুন প্রজন্মের ইহুদিদের মধ্যে আরও একবার স্বপ্ন বুনে দিয়েছিল। আঠারো শতকের অন্তিম পর্যায়ে ইহুদি বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকরা ‘ইহুদি আলোকায়ন’ প্রকল্পের প্রতি মনোযোগী হন। আধুনিক মূল্যবোধের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ইহুদি সত্তার প্রস্তাব রাখেন মোসেস মেন্ডেলসোহন (Moses Mendelssohn, 1729-86)। জার্মান এই ইহুদি দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রথম ইহুদি আলোকায়নের রূপকল্প পেশ করেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন আত্মীকৃত ইহুদি। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে সংঘটিত গভীর পরিবর্তনের তিনি কেবল পর্যবেক্ষকই ছিলেন না, সক্রিয় অংশীদারও ছিলেন। পরবর্তীকালে গুরুত্ব হারালেও, আঠারো শতকের ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে তিনি ছিলেন একজন পরিচিত মুখ।৩৪
তবে পশ্চিম ইউরোপ নয়; পূর্ব ইউরোপ হয়ে ওঠে নতুন ইহুদি আলোকায়নের তীর্থভূমি। হাসকালাহ (Haskalah) তথা ইহুদি আলোকায়নের ফলে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে— বিশেষত পোল্যান্ড, ইউক্রেন, রোমানিয়া, লিথুয়ানিয়া ও রাশিয়া— ইহুদি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণ লক্ষ করা যায়। ইহুদি আলোকায়নের দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।
● অভ্যন্তরীণ: তথা নিজ সম্প্রদায়ের পুরানা সেকেলে ধ্যানধারণার জিঞ্জির ভেঙ্গে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ।
● বাহ্যিক: ইউরোপীয় মূলধারার সমাজে আত্মীকৃত হওয়ার ন্যায্য বাসনা।৩৫
হাসকালাহ আন্দোলনের সদস্যদের বলা হত মাসকিলিম (maskilim)। মাসকিলিমদের হাতে সর্বপ্রথম ইহুদি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদই সমসাময়িক জায়নবাদী সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ এবং ইজরায়েলি সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে দেয়। এর ফলে নতুন ‘ইহুদি সত্তা’-র সাথে ধর্মীয় জুডাইজমের যোগাযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। ‘ইহুদি’ বর্গটি স্রেফ ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক বর্গে পরিণত হয়। ইহুদি ধর্ম ও সংস্কৃতি পুনর্গঠনের সমস্ত তোড়জোড়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইহুদিদেরকে ইউরোপীয় সমাজে ‘গ্রহণযোগ্য’ করে তোলা। ইহুদি ধর্মের এমন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যেন খোদ ইউরোপীয় (পড়ুন খ্রিস্টান) সমাজ তাদের খুশিমনে গ্রহণ করে:
…they wanted to reinterpret Judaism in their own image: to make it modern, acceptable or even attractive to Europeans. This necessitated rejecting most of it in practice, and presenting to the world a sanitized, Europeanized version of ‘rational’, ‘humanistic’ Judaism.৩৬
মধ্য উনিশ শতকের জায়নবাদ অন্তিম-আঠারো শতকি হাসকালাহ আন্দোলনের দ্বারা নানাভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে। মূলত জায়নবাদী সংস্কৃতি হাসকালাহ সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদেরই পরিমার্জিত রূপ।৩৭ হাসকালাহ আন্দোলনের মাধ্যমেই জায়নবাদের ভাষ্য ও বয়ান সৃষ্টি হয়েছে। তবে একদিক থেকে জায়নবাদ ইহুদি আলোকায়ন ও আত্মীকরণ রূপকল্পকে ছাপিয়ে গেছে। ইহুদি আলোকায়ন ও আত্মীকরণ প্রকল্প ছিল ইউরোপীয় সমাজেই ‘ইহুদি প্রশ্ন’ সমাধানের চেষ্টা। অন্যদিকে, ‘ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি’ তথা ইহুদি-রাষ্ট্রের ধারণা উনিশ ও বিশ শতকি জায়নবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল। ইউরোপে থেকে ইহুদি সমস্যার কোনো সমাধান হবে— জায়নবাদীরা তা মনে করেননি। তাই বলে তাঁরা তাঁদের ইউরোপীয়তা বিসর্জন দিতে চাননি। ‘ইউরোপের এশীয়’ (Asians in Europe) ইহুদিদেরকে জায়নবাদ ‘এশিয়ার ইউরোপীয়’ (Europeans in Asia) সত্তায় রূপান্তরের প্রকল্প গ্রহণ করে।৩৮
রূপকল্পগত পার্থক্য সত্ত্বেও হাসকালাহ ও জায়নবাদের মধ্যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক ঐক্য লক্ষ করা যায়। বিশেষত ঐতিহ্যিক ইহুদি সত্তার প্রতি দুর্নিবার ঘৃণা উল্লিখিত দুই আন্দোলনেরই সাধারণ প্রবণতা হিসেবে থেকে গেছে। সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখিতে হাজার বছরের ইউরোপীয় ইহুদি অধিবাসীরা ‘অভিবাসী’ ও ‘ভিনদেশি’ হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করে।৩৯ প্রবলভাবে ধর্মকর্ম আঁকড়ে থাকা নিজস্ব ভূখণ্ডহীন ইউরোপীয় ইহুদিদের ‘পরাশ্রিত’, ‘পরজীবী’, ‘পশ্চাৎপদ’ অভিহিত করা হয়।
আত্মীকরণের প্রচেষ্টা
আলোকায়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবেই আত্মীকরণের (assimilation) উদ্যোগ নেয়া হয়। আত্মীকরণ প্রকল্প ইহুদিদের স্ব স্ব দেশের মূলধারায় মিশে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। ঘেটো জীবন থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মূলধারার সমাজের লায়েক হয়ে উঠতে হবে তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের বিরক্তি উদ্রেক করে এমন আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে হবে— এমন প্রচারণা চলতে থাকে।৪০ এমনকী, প্রয়োজনে, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে জাতীয় সংস্কৃতিতে জায়গা করে নেয়ার ফরমায়েশও করা হয়। এ সময়ে অনেক ইহুদি আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা ইহুদি সংস্কৃতি পুরোপুরি পরিত্যাগ করেননি। যেমন কার্ল মার্কসের পুরো পরিবার খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।৪১ মার্কসের জন্য অবশ্য এই ধর্মান্তরণ আনুষ্ঠানিকতার বেশি কিছু ছিল না। উনিশ শতকে সমগ্র বিশ্বের মোট ইহুদি জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫ ভাগ (সাড়ে সাত লক্ষ) খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।৪২ ধর্মান্তরিত অনেকেই অ-ইহুদি নাম গ্রহণ করলেও, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবেচনায় তাদের ইহুদিত্ব সম্পূর্ণ রূপে বিলীন হয়নি।
আলোকায়ন ও আত্মীকরণের পর্ব পেরিয়ে জায়নবাদী ইতিহাস
আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসকে এড়িয়ে জায়নবাদের ইতিহাস যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। জায়নবাদ আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসেরই অংশ।৪৩ জাতিবাদের পরস্পরবিরোধী প্রবণতা জায়নবাদকে পুষ্টি জুগিয়েছে। “রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম”— ধর্মযুদ্ধ পরবর্তী এই সাম্প্রদায়িক নীতি ইউরোপীয় ইহুদিদের আরেক প্রস্থ ‘অপর’ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্রমশ বিকশিত জায়নবাদে এক অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ঔপনিবেশিক-জাতিবাদী শ্রেষ্ঠত্ববাদের মুখোমুখি হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ একদিকে ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করেছে; অন্যদিকে, ইউরোপীয় জাতিবাদের মুক্তিদায়ী প্রতিশ্রুতি থেকে অনুপ্রেরণা ও যুক্তি সঞ্চয় করেছে। অর্থাৎ ইউরোপীয় যুক্তিতেই ইউরোপীয় উপনিবেশকে ধরাশায়ী করেছে। কিন্তু ইউরোপীয় জাতিবাদী বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার শিকার জায়নবাদ অপরাপর উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের মতো করে ইউরোপীয় জাতিবাদের বিরোধিতা করেনি; বরং, নিজেরা এক ঔপনিবেশিক শক্তি হয়ে উঠেছে।৪৪ ইহুদিঘৃণা-সহ (খ্রিস্টান সমাজের ‘অপর’ ঘৃণা জায়নবাদে এসে পরিণত হয়েছে আত্মস্থ ঘৃণায়) ইউরোপীয় বর্ণবাদী মতাদর্শের সকল যুক্তির রস নিংড়ে নিয়ে জায়নবাদ আবির্ভূত হয়েছে এক সেটলার ঔপনিবেশিক-জাতিবাদী শক্তিরূপে।৪৫ জায়নবাদের এই ইতিহাস স্মরণে রাখলে ইজরায়েলকে ইন্ডিয়া, আলজেরিয়া-সহ অপরাপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে গুলিয়ে ফেলার মতো বিভ্রান্তি আমাদের পেয়ে বসবে না।৪৬
রাজনৈতিক-সেকিউলার জায়নবাদ উনিশ শতকি মতবাদ হলেও আঠারো শতকি হাসিদিক (Hasidic) আন্দোলনের মধ্যে এর ভাবাদর্শিক ভ্রূণ জন্ম নিয়েছিল।৪৭ ইজরায়েল বেন এলিজার (১৭০০-১৭৬০) ওরফে বাল শেম টভ (Baal Shem Tov) হাসিদিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। হাসিদিক আন্দোলন সনাতনী জুডাইজমের নানা আচার-রীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করে। তালমুদিক ঐতিহ্যের কঠোর ও অলঙ্ঘনীয় বিধিবিধানকে হাসিদিকরা প্রত্যাখ্যান করেন। আধুনিক জাতীয়তাবাদের সাথে তাল মিলিয়ে ঐতিহ্যিক ইহুদিতন্ত্রের হালনাগাদ করার দিকে এই আন্দোলন মনোনিবেশ করে। ইহুদিদের তরফে সংঘবদ্ধভাবে ‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তন’-এর ধারণা সর্বপ্রথম হাসিদিকরাই পেশ করে।৪৮ ফরাসি বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে হাসিদিকদের হাতেই আদি-জায়নবাদের ভিত রচিত হয়েছিল। তবে আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইহুদি আলোকায়ন, আত্মীকরণ ও সেকিউলারায়ন প্রকল্পের প্রবল প্রতাপে হাসিদিক মতবাদ খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি।
রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাস্তববাদী জায়নবাদ
উনিশ শতকি রাজনৈতিক জায়নবাদের ইতিহাসে মোসেস হেস (Moses Hess, 1812-75) গুরুত্বপূর্ণ এক নাম। স্পিনোজার অনুরাগী এই জার্মান চিন্তক এক সময়ে ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে কার্ল মার্কসের আন্তর্জাতিকতাবাদী সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করে তিনি ইহুদি-দরদি আদর্শবাদে নিজের নাম লেখান। ১৮৬২ সালে তিনি রোম ও জেরুজালেম শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেন, যেখানে তাঁর জায়নবাদী চিন্তার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়।৪৯ হেগেলিয়ান ডায়ালেকটিকের প্রভাবে মোসেস মনে করতেন ইতিহাস অবিরাম সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে পৌঁছায়। তবে হেগেল যেখানে জার্মানদের ভেবেছিলেন ইতিহাসের কর্তা, মোসেস হেস জার্মানদের স্থলে ইহুদিদের ইতিহাসের কর্তারূপে বসিয়েছিলেন।৫০
কারণ, মোসেসের মতে, একমাত্র ইহুদিদের জাতীয় জীবনেই রুহানিয়াত ও বস্তুবাদের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এদিক থেকে ইহুদিরা গ্রিক ও খ্রিস্টানদের চেয়ে এগিয়ে। কাজেই ‘ইতিহাসের পরিসমাপ্তি’ ঘটানোর উপযুক্ত কর্তাশক্তি ইহুদিদের মধ্যেই বিদ্যমান। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে ইহুদিদের নিজেদেরকে ‘জাতি’ হিসেবে পুনরাবিষ্কার এবং ফিলিস্তিনে জাতীয় জীবন উদ্বোধনের প্রয়োজন। মোসেস কেবলমাত্র ইহুদিদের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্যই ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমির জরুরত অনুভব করতেন।৫১ ইউরোপের সর্বজনীন চিন্তার মানচিত্রে খুব একটা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম না হলেও, মোসেসের অধিবিদ্যক নৃগোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা জায়নবাদের মতাদর্শিক গঠনের ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা রেখেছিল। হার্জেল-সহ বিশ শতকি জায়নবাদী সংগঠকদের চিন্তা গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।
উনিশ শতকের রুশ ইহুদিদের মধ্যে দুই ধরনের আন্দোলন ক্রমশ জায়গা করে নেয়। উভয় ঘরানার বিকাশের ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী হাসকালাহ ও সেকিউলারায়ন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। তবে উভয় আন্দোলনই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরও রেখেছিল। একদিকে রুশ সমাজতান্ত্রিকদের শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় ইহুদিদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বান্ড (Bund)৫২ আন্দোলন; অন্যদিকে, ছিল জাতিবাদী জায়নবাদ। বান্ড আন্দোলন ও জায়নবাদ উনিশ শতকি ইহুদি নবজাগরণের পরস্পর প্রতিযোগী দুই আন্দোলন। বান্ডিস্টরাও ইহুদি স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছিল, তবে তারা পোল্যান্ড, ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া-সহ পূর্ব ইউরোপের মধ্যেই ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির পক্ষে ছিল।৫৩ কিন্তু সে সময়ে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমির প্রচারণা এমনই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, জায়নবাদীরা বান্ডিস্টদের জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যায়। রুশ বংশোদ্ভূত ইহুদি লেখক ও সংগঠক পেরেটজ স্মোলেনস্কিন (Peretz Smolenskin, 1842-85) এবং মোশে লিলিয়েনব্লুম-সহ (Moshe Lilienblum, 1843-1910) অন্যান্য রুশ জায়নবাদীরা ফিলিস্তিনে ইহুদি উপনিবেশ নির্মাণকে ইহুদিদের আধুনিকায়নের চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে বিবেচনা করতেন।৫৪
রুশ ইহুদিরাই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে জায়নদরদি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। লিও পিন্সকারের (১৮২১-৯১) নেতৃত্বে ১৮৮০ সালের দিকে জায়নপ্রেমী আন্দোলন (Choveve Zion ওরফে Lovers of Zion) শুরু হয়।৫৫ এই আন্দোলন বিশ্বাস করত যে, ফিলিস্তিনে কৃষি উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারলে ইহুদিদের স্বয়ংক্রিয় মুক্তি ঘটবে।৫৬ এই আন্দোলনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন অ্যারন ডেভিড গর্ডন (১৮৫৬-১৯২২)। ইহুদি পুনর্জাগরণের জন্য তিনি ফিলিস্তিনে ইহুদি শ্রমের ধারণাকে সামনে আনেন এবং পরবর্তীকালের লেবার জায়নবাদের প্রধান তাত্ত্বিক ব্যক্তিতে পরিণত হন।৫৭
রাজনৈতিক জায়নবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইহুদি সার্বভৌমত্ব। খ্রিস্টানদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে ইহুদিদের অবশ্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। এছাড়া ইউরোপের ইহুদিভীতি থেকে কোনো মুক্তি নেই। এজন্যই রাজনৈতিক জায়নবাদের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব থিওডের হার্জেল বলেছিলেন, ইহুদিদের সমস্যা ধর্মীয় কিংবা সমাজতান্ত্রিক নয়; এটা জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন (national problem)।৫৮
হার্জেল প্রসঙ্গে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত [দেখুন: দ্বিতীয় অধ্যায়, ফিলিস্তিন: একুশ শতকের উপনিবেশের ইতিহাস, সারোয়ার তুষার, প্রকাশিতব্য] আলোচনা করেছি। জায়নবাদে দীক্ষা নেয়ার আগে তিনি গণহারে ইহুদিদের ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে ‘ইহুদি সমস্যা’ সমাধানের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির ধারণা তাঁর কাছে অধিক বাস্তবসম্মত প্রতীয়মান হয়। তবে ফিলিস্তিন হার্জেলের বিবেচনাতে থাকলেও তিনি ফিলিস্তিনের প্রশ্নে অনড় ছিলেন না। আর্জেন্টিনা, সাইপ্রাস, সিনাই, উগান্ডা ইত্যাদি অঞ্চলের কথাও তিনি ভেবেছিলেন।৫৯ হার্জেল এমনকী বিশুদ্ধ রক্তের ভিত্তিতে জাতির ধারণাও খুব একটা পছন্দ করেননি। তাঁর সমসাময়িক প্রভাবশালী ইহুদি চিন্তক ইজরায়েল জ্যাংউইলের সাথে সাক্ষাতের পরে হার্জেল বিশুদ্ধ রক্তের ধারণা পরিত্যাগ করেন। জ্যাংউইলের গাত্রবর্ণ নিয়ে হার্জেল তাঁর ডায়েরিতে অত্যন্ত বর্ণবাদী মন্তব্য করেন এবং লেখেন যে, ইহুদিদের ঐতিহাসিক সত্তা অর্থে ‘জাতি’ বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত।৬০
তার মানে দেখা যাচ্ছে যে, হার্জেলকে জায়নবাদের ‘জনক’ অভিধায় ভূষিত করা হলেও, তাঁর অজানতেই জায়নবাদী আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছিল। এমনকী হার্জেল যখন ভিয়েনায় বসে ইহুদিদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা ছক কষছিলেন, তখন ফিলিস্তিনে ১৮টি ইহুদি সেটেলমেন্ট প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।৬১ হার্জেল এসব ইহুদি বসতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলেন। তবে জায়নবাদের ইতিহাসে হার্জেলের গুরুত্ব খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তিনি তাঁর সমকালের বিভিন্ন ধরনের জায়নবাদকে একত্রিত করে জায়নবাদী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৯৭ সালে ব্যাসেলে অনুষ্ঠিত প্রথম জায়নবাদী কংগ্রেসেই ‘ইহুদি রাষ্ট্র’ ধারণা অনুমোদন করিয়ে নেন। বিভিন্ন ধরনের জায়নবাদী সংগঠনকে একই ছাতায় এনে তিনি গণতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদের মিশেলে এক অদ্ভুত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। হার্জেলের নেতৃত্বাধীন জায়নবাদী কংগ্রেসে সকল ঘরানাই মতামত পেশ করার সুযোগ পেত, তবে নীতি নির্ধারণ প্রশ্নে হার্জেল তাঁর ঘনিষ্ঠদের সমন্বয়ে গঠিত ইনার অ্যাকশন কমিটির ওপরেই ভরসা করতেন। হার্জেল কল্পিত এরেৎজ ইজরায়েল (Land of Israel) বর্তমান ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের চাইতেও বিস্তৃত। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন ইহুদি আবাসভূমি মিশর নদী থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত।৬২
রক্ত, ভূমি ও জাতির ধারণা
হার্জেলের মৃত্যুর পর (১৯০৪) জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক স্নাতকদের হাতে জায়নবাদের নেতৃত্ব চলে যায়। তাদের ওপর আধুনিক জাতিবাদের বর্ণবাদী মতাদর্শের বিপুল প্রভাব ছিল। বিশ শতকি এই তরুণ জায়নবাদীরা বিশুদ্ধ রক্তের ধারণায় আচ্ছন্ন জার্মান জাতিবাদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের প্রভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, জার্মানির ইহুদিরা তথাকথিত জার্মান রক্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তারা জার্মান জাতির অংশও নয় এবং জার্মান মাটিতে তারা ভিনদেশি।৬৩ তরুণ এই জায়নবাদী সংগঠকরা ইহুদিবিদ্বেষীদের সাথে অন্তত তিনটি প্রশ্নে একমত পোষণ করতেন:
● ইহুদিরা জার্মান জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়।
● ইহুদি ও জার্মানদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। না, কোনো ধর্মীয় কারণে নয়; জাতিগত রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার স্বার্থে।
● অভিন্ন রক্তের অধিকারী না হওয়ায় ইহুদিদের ‘নিজস্ব’ ভূখণ্ড তথা ফিলিস্তিনে চলে যাওয়া উচিত।৬৪
অর্থাৎ, বর্ণবাদী অপবিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় রক্ত ও ভূমিকেন্দ্রিক উদ্ভট এক সরল সমীকরণ দাঁড়ায়: জাতি=বিশুদ্ধ রক্তের জনগোষ্ঠী+ভূমি। একই ভূমিতে একই রক্তের অধিকারী জনগোষ্ঠী একই ‘জাতি’ গঠন করে। বিশ শতকের জার্মান জায়নবাদ ছিল জার্মান জাতিবাদী মতাদর্শেরই কার্বন কপি। জার্মানি এবং ইউরোপে ইহুদিদের হাজার বছরের ইতিহাস থাকলেও বিশ শতকের জাতিবাদী চিন্তায় তারা আর জার্মান নয়।৬৫ সে সময় প্রবল প্রতাপশালী এই রক্তবাদী-জাতিবাদী ধারণা থেকে মুক্ত ইহুদি বুদ্ধিজীবী পাওয়া বেশ দুষ্কর ছিল। যেমন দার্শনিক মার্টিন বুবেরের কথা ধরা যাক। তিনি লিখেছেন: “.. that the deepest layers of our being are determined by blood; that our innermost thinking and our will are coloured by it…. was driven out of his land and dispersed throughout the lands of the occident… despite all this, he (Jew) has remained on Oriental.”৬৬
তবে বুবের এককভাবে বিশুদ্ধ রক্তের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। একই সময়ের অপরাপর জায়নবাদী ও জায়নদরদি বুদ্ধিজীবী, দার্শনিকদের মধ্যেও বিশুদ্ধ রক্তের ধারণা জেঁকে বসেছিল। এমনকি খোদ আলবার্ট আইনস্টাইনও এর থেকে মুক্ত ছিলেন না।৬৭
কেবলমাত্র বিশুদ্ধ রক্তের ধারণা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমির পক্ষে যৌক্তিকতা তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল না। যতদিন পর্যন্ত আটলান্টিকের অপর পার আমেরিকার জমিন ইহুদিদের জন্য উন্মুক্ত ছিল, ইউরোপের ইহুদিরা জায়নবাদীদের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন যে, ইউরোপে যদি ইহুদি সমস্যার সমাধান না-ই হবে, তাহলে আমেরিকায় পাড়ি জমাতে সমস্যা কোথায়? কেন ফিলিস্তিন? এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে জায়নবাদীরা উদ্ভট যুক্তি হাজির করেছিলেন। তাঁরা জবাব দিয়েছেন, আমেরিকায় পাড়ি জমালেই ইহুদি সমস্যার সমাধান হবে না। ইহুদিরা যেখানে যায়, সাথে করে ইহুদি-ঘৃণা নিয়ে যায়। ইহুদি-ঘৃণার জন্য ইহুদিরাই দায়ী।৬৮ তাদের অভিবাসী অস্তিত্ব তাদের প্রতি অন্যের ঘৃণার উদ্রেক করে। ইহুদিরা যতদিন পর্যন্ত ‘পরজীবী’ হয়ে থাকবে তথা ‘নিজেদের ভূখণ্ড’ ফিলিস্তিনে স্বতন্ত্র আবাসভূমি গড়ে না তুলবে, ইহুদি-ঘৃণা থেকে তাদের নিস্তার নাই। অর্থাৎ, এ পর্যায়ে এসে জায়নবাদ কেবল মাত্র বিশুদ্ধ রক্তকেন্দ্রিক নয়, ভূমিকেন্দ্রিক জাতিবাদের রূপ নেয়।৬৯ ইউরোপের দেশে দেশে ইহুদিদের অবস্থান বিশ শতকে জাতিবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন জায়নবাদী বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান নিশানা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা ইউরোপীয় ইহুদিদের মনস্তত্ত্বকে তুমুলভাবে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ইহুদিদের মধ্যে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তাঁদেরকে অন্যের বিপ্লবের ফুটফরমাশ খাটনেওয়ালা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ‘নিজেদের’ ভূখণ্ডের জন্য যারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নয়, তাদেরকে দেশদ্রোহী, ডরপুক ও বিকারগস্ত উপাধি দেয়া হয়।৭০ তবে উগ্র ডানপন্থী কোনো কোনো জায়নবাদী গোটা ইহুদি সম্প্রদায়কেই ‘অস্বাস্থ্যকর ও বিকারগ্রস্ত’ তকমা দেন।৭১ যেমন বেন ফ্রমার (Ben Frommer) নামে একজন সংশোধনবাদী জায়নবাদী ১৯৩৫ সালে লেখেন: “The fact is undeniable that the Jews collectively are unhealthy and neurotic.”৭২ কোনো কোনো ইহুদি লেখক ইহুদি সম্প্রদায়কে ‘নোংরা কুকুর’ পর্যন্ত বলেছেন।৭৩
জায়নবাদীদের প্রভাবশালী ধারা লেবার জায়নবাদের মধ্যেও আত্ম-ঘৃণার প্রবল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শ্রমিকদরদি ভেক ধরলেও লেবার জায়নবাদ শ্রমিকদের খুব একটা আকৃষ্ট করেনি; বরং মধ্যবিত্ত ইহুদি বুদ্ধিজীবীরাই এই ঘরানায় নাম লিখিয়েছিলেন।৭৪ কাজেই লেবার জায়নবাদ ইউরোপের দেশে দেশে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের আওতায় থাকা শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত আন্তর্জাতিকতাবাদী মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের দিকে মৌখিক ও লিখিত আক্রমণের নিশানা তাক করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইহুদি শ্রমিকদের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরির উদ্দেশ্যে তাঁরা বলতে শুরু করেন যে, ইউরোপের কারখানাগুলোতে সব চাইতে বাজে ও তাৎপর্যহীন কাজ ইহুদিদের দিয়ে করানো হয় (এ বক্তব্যের আংশিক সত্যতা রয়েছে)। কাজেই ‘স্বাস্থ্যকর ও প্রকৃত’ শ্রেণিসংগ্রাম করতে চাইলে ‘নিজস্ব’ ভূখণ্ডে ফিরতে হবে। তথাপি, ইহুদি শ্রমিকদের মধ্যে লেবার জায়নবাদ সামান্যই আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।৭৫ কারণ শ্রমিকদের দৈনন্দিন সংগ্রামের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করার পাশাপাশি সুদূর অচেনা ফিলিস্তিনে এক বেহেশতি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো জায়নবাদের সাথে শ্রমিকরা নিজেদের সম্পর্কিত করতে পারেনি। জায়নবাদীরা প্রচার করতে শুরু করেন যে, একজন সাচ্চা জায়নবাদী ইহুদি-বিদ্বেষী না হয়ে পারে না।৭৬ যারা ফিলিস্তিনে পাড়ি দিয়ে ‘স্বদেশ নির্মাণের’ মহাযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করবে না, তারা ইজরায়েল জাতি ও গোটা মানবজাতিরই শত্রু।৭৭
তার মানে দেখা যাচ্ছে যে, উনিশ ও বিশ শতকের জায়নবাদী জাতিবাদী মতাদর্শ রক্ত ও মাটির (blut und boden) ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল। জার্মান বিশুদ্ধ রক্তবাদী জাতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক পর্যায়ে জায়নবাদীরা নিজেদেরকে জার্মানদের তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী দাবি করে বসেন।৭৮ জার্মানদের রক্তে স্লাভিক রক্তের মিশ্রণ আছে, অন্যদিকে, তাদের রক্ত এতটাই ‘বিশুদ্ধ’ যে এতে কোনো ‘দূষণ’ (পড়ুন মিশ্রণ) নাই। তবে বিশুদ্ধ রক্তের ধারণায় আত্মতুষ্ট জায়নবাদীরা পুরোপুরি স্বস্তিতে ছিলেন না। একদিক থেকে তাঁরা জার্মানদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন। জার্মানদের অন্তত নিজেদের মাটি আছে, জায়নবাদীদের তা নাই।৭৯ ‘নিজস্ব’ ভূখণ্ড ছাড়া রক্তগর্বী জায়নবাদীরা নিজেদের অন্যের ভূখণ্ডের ওপর নির্ভরশীল জোঁকের সাথে তুলনা করতেন।৮০
এর ফলে রক্ত ও ভূমিবাদী জায়নবাদীরা ইহুদিঘৃণার জন্য নিজেদের সম্প্রদায়কেই দুষতেন।৮১ তাদের আধুনিকতাবাদী প্রকল্পে ইউরোপে থেকে ইহুদিঘৃণা মোকাবেলার কোনো কর্মসূচি ছিল না। এ সময় তারা নিজেদেরকে প্রাচীন হিব্রু জনগোষ্ঠীর সরাসরি বংশধর হিসেবে দাবি করেছিলেন।৮২ তারা আরও দাবি করেন ফিলিস্তিন থেকে তারা ‘বিতাড়িত’। একমাত্র ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনই ইহুদি প্রশ্নের মীমাংসা করতে সক্ষম।
জায়নবাদের মতাদর্শিক বিচার
জায়নবাদী মতাদর্শ স্রেফ ইহুদিদের মনস্তত্ত্বকে নিশানা করেনি, খোদ ইহুদি শরীর ছিল তাদের কেন্দ্রীয় নিশানা। তারা হীন, দুর্বল ও তথাকথিত মেয়েলি ইহুদি সত্তার অপবাদ ঘোচাতে মরিয়া ছিলেন। হার্জেলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইহুদি দার্শনিক ম্যাক্স নর্ডু ছিলেন (Max Nordau) পেশীশক্তিবহুল ইহুদি সত্তার মূল প্রবক্তা।৮৩ চওড়া বুক এবং পেশীশক্তির অধিকারী প্রাচীন ইহুদি ঐতিহ্য তিনি ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বভাবতই রোমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি বিদ্রোহের নায়কোচিত চরিত্র বার কোচবা (Bar Kochba) ম্যাক্স নর্ডু প্রণীত নতুন ইহুদি সত্তার মডেলে পরিণত হন।৮৪ ম্যাক্স নর্ডু ১৮৯৮ সালে বার্লিনে বার কোচবা জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন।৮৫ এর উদ্দেশ্য ছিল পেশীশক্তির ছাঁচে ইহুদি তরুণদের দৈহিক পুনর্গঠন। বার কোচবা জিমনেশিয়ামের অনুপ্রেরণায় ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি ইহুদি জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮৬
অ্যান্টি-সেমেটিক ডিসকোর্সে ইহুদিরা ছিল ‘মেয়েলি’। এই ভাষ্য মোতাবেক মেয়েলিপনা দুর্বলতারই নামান্তর।৮৭ কাজেই শৌর্যবীর্যে বলীয়ান নতুন পুরুষালি ইহুদিরা এমন সব ‘কঠিন কাজ’ করবে যা তাদের খ্রিস্টান সমাজে করতে দেয়া হয়নি। কৃষি, যুদ্ধ ও শরীরচর্চার সম্মিলনে ‘কঠোর ইহুদি’ শরীর বানানোর তোড়জোড় শুরু হয়।৮৮ ৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাসাদায় সংঘটিত রোমান-বিরোধী ইহুদি বিদ্রোহের আদলে মোসাদ এজেন্ট এবং ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর সৈন্যের শারীরিক গড়ন তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। ৮৯
অস্ত্র, শিশ্ন, ভূমি ও নারী

জায়নবাদের নতুন ‘ইহুদি শরীর’ নির্মাণ প্রকল্পকে কেবল পুরুষতান্ত্রিক বললে কম বলা হবে। এটা ছিল শিশ্নবাদী।৯০ শিশুকালে ইহুদি বালকদের খৎনা করানো হয়। ইউরোপের খ্রিস্টান বালকরা এ কারণে ইহুদি পুরুষদের ব্যাপারে ভীত ছিল। তারা খৎনা করানোকে খোজাকরণ ও অঙ্গহানি ভেবে আতঙ্কিত থাকত। ফ্রয়েড মনে করেন ইহুদিবিদ্বেষের অচেতন গোড়ায় রয়েছে এই খোজাকরণ ভীতি:
The castration complex is the deepest unconscious root of anti-Semitism; for even in the nursery little [gentile] boys hear that a Jew has something cut off his penis— a piece of his penis they think— and this gives them a right to despise Jews. And there is no stronger unconscious root for the sense of superiority over women… and from that standpoint what is common to Jews and women is their relation to the castration complex.৯১
ইহুদিবিদ্বেষী ভাষ্যে খৎনাকৃত ইহুদি পুরুষ আর নারীতে পার্থক্য নাই। শিশ্নহীন নারী যেমন ‘দুর্বলতা’ ও ‘অস্বাস্থ্যের’ প্রতীক, ইহুদি পুরুষও তাই।৯২ কাজেই ইহুদি ব্যাটাগিরির পুনর্সংজ্ঞায়নে ইহুদি-শিশ্নের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। ইহুদিদের শিশ্নকেন্দ্রিক হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে শিশ্নগর্বী৯৩ ইহুদি ব্যাটাগিরির উদ্ভব ঘটে। নতুন এই আত্মবীক্ষায় যে ইহুদি প্রতিচ্ছবি নির্মিত হয়, তা আবশ্যিকভাবে পুরুষালি। এমনকী জায়নবাদের সাথে সম্পর্কিত হিব্রু শব্দ জায়িন (Zayin)-এর অর্থ অস্ত্র ও শিশ্ন।৯৪ ইহুদি সামরিকায়নে অস্ত্র ও শিশ্নের যুগপৎ পুনর্ব্যাখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অস্ত্র যেন এক ধরনের শিশ্ন; অন্যদিকে, শিশ্ন যেন এক ‘অস্ত্র’। জায়নবাদী কল্পনায় অস্ত্ররূপী শিশ্নের ভূমিকা কেবল মুক্তিদায়ীই নয়, জুলুমকারীও বটে। উপনিবেশিত ফিলিস্তিনি নারীদের ধর্ষণের ক্ষেত্রে জায়নবাদী বাহিনী শিশ্নকে অস্ত্ররূপে কল্পনা করেছে।৯৫
ইউরোপীয় সমাজে কৃষিকাজ থেকে বঞ্চিত ইহুদিরা ফিলিস্তিনে নতুন উদ্যম এবং প্রবল উৎসাহে কৃষিকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ‘কুমারী’ ও অনুর্বর মাটিকে তারা উর্বর এবং ফুলে-ফসলে ভরিয়ে দেবেন।৯৬ ফিলিস্তিন অনুর্বর কিংবা অনাবাদি কোনোটাই ছিল না। কিন্তু জায়নবাদী মিথে ফিলিস্তিন ছিল ভূমিহীন ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য জনশূন্য বিরান ভূমি। তাঁরা এই ‘পাথুরে’ ভূমিকে পুষ্পময় করে তোলার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কৃষিকাজে অনভিজ্ঞতার দরুন প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের সহায়তা নেয়ার কোনো বিকল্প ছিল না। পরবর্তীতে অবশ্য বিপুল সংখ্যক অভিবাসিত আরব-ইহুদিদের দ্বারা স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের প্রতিস্থাপন করা হয়।
অস্ত্র ও শিশ্নের পারস্পরিকতার মতোই জায়নবাদী কল্পনায় ভূমি ও নারী ছিল মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ভূমি যেন ‘নারী’, জায়নবাদী বীজের পুরুষালি ছোঁয়ায় যা উর্বর হয়ে উঠবে।৯৭ অন্যদিকে, ইহুদি নারীরা যেন ভূমি। তাঁরা বীর বার কোচবার উত্তরাধিকারীদের গর্ভধারণপূর্বক ইজরায়েল রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ যোদ্ধা প্রসব করবেন।৯৮ অর্থাৎ, ইহুদি-পুরুষ শরীর পুনর্গঠনের সমান্তরালে যুদ্ধ, কৃষি, শিশ্ন, অস্ত্র, নারী ও ভূমি ডিসকোর্সের যৌনবাদী নির্মাণের মধ্য দিয়ে জায়নবাদ এক নজিরবিহীন মারাত্মক সামরিকায়িত, পুরুষালি ও যুদ্ধংদেহী ঔপনিবেশিক মতবাদে পরিণত হয়।৯৯ ইজরায়েল রাষ্ট্র জায়নবাদী মতবাদেরই ‘যৌক্তিক’ পরিণতি।
প্রচলিত ধারণা হচ্ছে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইউরোপের ‘ইহুদি প্রশ্নের’ মীমাংসা ঘটেছে। জায়নপন্থীরা এতে উৎফুল্ল, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বনকারীরা এতে সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ। আদতে জায়নবাদ ইহুদি প্রশ্নের মীমাংসা করেনি; বরং, আরও জটিল করে তুলেছে। জায়নবাদী যুক্তি মোতাবেক ইজরায়েল রাষ্ট্রের সমালোচনা মাত্রই ইহুদিবিদ্বেষ।১০০ জায়নবাদের ভাষ্য ও বয়ান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জায়নবাদ নিজেই নতুন ধরনের ইহুদিবিদ্বেষ।১০১ ‘ইহুদি প্রশ্ন’ জাগরূক রাখাই তার উদ্দেশ্য। ইহুদি-বিদ্বেষী রাষ্ট্রগুলোর সাথেই জায়নবাদের ঐতিহাসিক আঁতাতের সম্বন্ধ।১০২ জায়নবাদ, ইউরোপীয় ইহুদি-বিদ্বেষীদের মতোই মনে করে, ইউরোপের ইহুদিরা ইউরোপীয় নয়। প্রাচ্যে তথা ফিলিস্তিনে স্বতন্ত্র ‘ইহুদি রাষ্ট্র’ নির্মাণ করা ব্যতীত ইহুদি প্রশ্নের কোনো মীমাংসা নাই। ‘ইহুদি প্রশ্ন’ জাগরূক রাখার পাশাপাশি জায়নবাদ ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’ জন্ম দিয়েছে।১০৩ ইহুদি-বিদ্বেষীদের হাতে ইহুদিদের করুণ পরিণতির সাথে জায়নবাদীদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের অবর্ণনীয় জুলুমের চমকপ্রদ মিল লক্ষ করা যায়।১০৪ ইহুদি প্রশ্ন মীমাংসার নামে জায়নবাদ একদিকে তৈরি করেছে নব্য ইহুদি-বিদ্বেষ; অন্যদিকে, জন্ম দিয়েছে ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’। ১০৫

ফিলিস্তিনি শিশু
শেষ কথা
ভুবনবিখ্যাত তাত্ত্বিক একবাল আহমেদ নিজেকে অনুভূতির দিক থেকে ‘আরব’ ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ, আরবের মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে তিনি নিজের সংগ্রাম ভেবেছিলেন। কথাটার আরেক তাৎপর্য এই, সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক বিশ্বব্যবস্থার অধীন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুক্তিকামী জনগণের সাথে আত্মিক ও কৌশলগত মৈত্রী গড়ে তুলতে না পারলে সংকীর্ণ জাতিবাদের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। স্থানিক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হয়ে পড়ে জাতিবাদী ও রাষ্ট্রবাদী। এর ফলে যদি নিজেদের সংগ্রামে সফল হওয়া যেত, তাহলে হয়তো আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও মুক্তিকামী সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে আসলে স্থানীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামেও সফল হওয়া যায় না।
আমাদের তরফে ফিলিস্তিনের ইতিহাসচর্চার অর্থ হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, জাতিবাদ, আধিপত্যবাদ-সহ সকল ধরনের অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ এবং অধিকতর ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক বিউপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। সারা দুনিয়াতেই বিউপনিবেশিক তত্ত্ব ও দর্শন প্রতাপশালী হয়ে উঠছে এবং গত শতাব্দীর ডিকলোনাইজেশন প্রকল্পকে তা বহুদূর পর্যন্ত ছাপিয়ে গেছে। অবশ্য বিউপনিবেশায়ন সম্পর্কে বেশ কিছু অতি-তরল পাঠ ও চর্চা লক্ষ করা যায়। উগ্র আবেগি পশ্চিম-বিরোধিতা, সংকীর্ণ স্বদেশিয়ানা এবং গোষ্ঠী-জাতীয়তাবাদকে অনেক সময় বিউপনিবেশায়নের মোড়কে হাজির করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তবে নিশ্চিতভাবেই বিউপনিবেশায়ন সংকীর্ণ জাতিবাদ ও আপেক্ষিকতার চেয়ে বেশি কিছু। বিশ শতকের ডিকলোনাইনেশন প্রকল্প জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলাকেই তার অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ক্ষমতা-সম্পর্কের ঔপনিবেশিকতাকে বহাল রেখে স্রেফ জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলা যে উপনিবেশবাদের আত্মস্থকরণ মাত্র— যুগ সীমাবদ্ধতার কারণে তা অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। অধুনা বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব ও দর্শন জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলাকে তার লক্ষ্য হিসেবে না নিলেও, আধুনিক রাষ্ট্রের বিচার-বিবেচনাশূন্য বিরোধিতাও করে না; বরং, আত্মশক্তির ওপর ভর করে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী রূপে বিশ্বের মানচিত্রে মর্যাদার সাথে টিকে থাকার নিমিত্তে প্রভাবশালী ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণার নতুন ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করাই হালের বিউপনিবেশিক তত্ত্বের কাজ। অস্তিত্ব ও যাপনের ঔপনিবেশিকতাকে চিহ্নিত করে জ্ঞানতাত্ত্বিক পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেয় বিউপনিবেশায়ন। ফলে কেবলমাত্র মানুষকে কেন্দ্রে রেখে অধুনা বিউপনিবেশায়ন কোনো ‘সামাজিক সম্পর্ক’ ভাবে না। মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কর্তাসত্তা ভাবার আবশ্যিক পরিণতি হিসেবে পৃথিবী নামক গ্রহের নাভিশ্বাস উঠেছে। সুতরাং, গ্রহীয় (Planetary) পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিউপনিবেশায়নের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রস্তাব গড়ে তোলার আশু কর্তব্যও থেকে যায়।
ফিলিস্তিন একুশ শতকের উপনিবেশ। প্রাথমিকভাবে এ চিহ্নায়নের যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন দানা বাঁধতে পারে। প্রচলিত কাণ্ডজ্ঞান মোতাবেক আমরা এক সমরূপ উত্তর-ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় বসবাস করছি; যেখানে সাক্ষাৎ উপনিবেশ উঠে গেছে। তাহলে ফিলিস্তিন কি আজও উপনিবেশিত থাকতে পারে? আমাদের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, পারে এবং তা-ই আছে। গত শতাব্দীর চল্লিশ, পঞ্চাশের দশকে যখন এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে, ফিলিস্তিন তখন উপনিবেশে পরিণত হচ্ছিল। ফিলিস্তিন, সেই অর্থে, উত্তর-ঔপনিবেশিক (post-colonial) যুগের উপনিবেশ। এই পরিস্থিতিকে একবাল আহমেদ ‘প্যারাডক্স’ হিসেবে মানতে নারাজ; তিনি একেই ‘উত্তর-ঔপনিবেশিক দশা’ অভিহিত করেছেন। ফিলিস্তিনের সিংহভাগ অঞ্চল জায়নবাদীদের ঔপনিবেশিক জিম্মায় রেখেই, তুরস্ক, মিশর, ইরান, ইরাক, জর্ডান-সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ততদিনে ‘স্বাধীন’ হয়েছে। আরবের অভিজাত নেতৃত্ব অনাগত ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ অনুধাবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইনসাফ কায়েমে প্রত্যেক আরব দেশই পশ্চিমের মুখাপেক্ষী ছিল। বলা বাহুল্য, কেবল ফিলিস্তিনের জন্য নয়, সমগ্র আরব অঞ্চলের জন্যই এই পিছুটান, অপরিণামদর্শিতা এবং আঞ্চলিক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সংকীর্ণ জাতিবাদী স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টার পরিণতি ভালো হয়নি।
স্থান-কাল সম্পর্কে সচেতনতা উত্তরৌপনিবেশিক (postcolonial) চিন্তার প্রধান এক দিক। একই ভূখণ্ডে (ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন) তিন ধরনের জনগোষ্ঠীর জন্য তিন ধরনের বাস্তবতা তৈরি হওয়া বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার জন্য কী তাৎপর্য বহন করে— তার সঠিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হাজির করা হালের উত্তরৌপনিবেশিক চিন্তকদের অন্যতম প্রধান এক কর্তব্য। একদিকে আছে আশকেনাজি তথা ইউরোপীয় ইহুদি সম্প্রদায়। তারা উপনিবেশিত ভূখণ্ডে ‘উত্তর-ঔপনিবেশিক’ মর্যাদায় অভিষিক্ত জনগোষ্ঠী। অন্যদিকে আছে ফিলিস্তিনি আরব সম্প্রদায়। তারা ‘উত্তর-ঔপনিবেশিক’ ভূখণ্ডের উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী। আরও রয়েছে আরব-ইহুদি সম্প্রদায়। তারা ফিলিস্তিনিদের সাপেক্ষে ঔপনিবেশিক, আবার আশকেনাজি ইহুদিদের সাপেক্ষে উপনিবেশিত। অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী দশায় উপনীত। একই স্থানে অবস্থান করলেও উল্লিখিত তিন জনগোষ্ঠীর কালিক বাস্তবতা ভিন্ন ভিন্ন। ‘উত্তর-ঔপনিবেশিক’ কালে ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনে কি একইসাথে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তবতা বিরাজ করছে? যদি করেই থাকে, এর অর্থ কী দাঁড়ায়? পারস্পরিক স্বার্থ ও ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত আঞ্চলিক নেটওয়ার্কসমূহের শিথিল ফেডারেশন অর্থে অনাগত ‘গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার’ সাপেক্ষে এটাই কেন্দ্রীয় প্রশ্ন।
ইজরায়েলের গাজা আক্রমণ ও নির্মূল অভিযান স্রেফ গাজায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইরানকে এই যুদ্ধে জড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। সেরকম কিছু হলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যেই যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে তা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই দু’টি বড় ঘটনা ঘটে গেছে। একদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিদের ওপর বিমান হামলা শুরু করেছে। কারণ গাজায় গণহত্যা বন্ধ এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণার দাবিতে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতি লোহিত সাগরে ইজরায়েলগামী জাহাজকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এর জবাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য হুতিদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান শুরু করেছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা গণহত্যার অভিযোগে মামলা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ শক্তিশালী পরাশক্তিসমূহের রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে কী রায় আসবে তা বলা কঠিন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো দাখিল করেছে, ঐতিহাসিক নথি হিসেবে তার বিপুল গুরুত্ব রয়েছে।
যে ইতিহাস ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’ জন্ম দিয়েছে, সেই ইতিহাস থেকে মুক্তি পেতে হলে ইতিহাসচর্চার কোনো বিকল্প নাই। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই উদ্দেশ্যের প্রতি বিনীত নিবেদন।

টীকা ও তথ্যসূত্র:
১. হিব্রু বাইবেলে এরেৎজ ইজরায়েল (Land of Israel) এবং জেরুজালেম— দুই অর্থেই ‘জায়ন’ শব্দের ব্যবহার আছে। ঐতিহাসিক অর্থে ‘জায়ন’ শব্দের দ্বারা জেরুজালেমের একটি পাহাড় এবং খোদ জেরুজালেম শহরকে নির্দেশ করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মের বিভিন্ন ফেরকা এর অর্থ ‘ইউটোপিয়া’ বুঝে থাকে। ‘জায়ন’ শব্দের আরেক অর্থ ‘পবিত্র স্থান’। আধুনিক কালে ‘জায়নবাদ’ দ্বারা একটি বসতি স্থাপনকারী ঔপনিবেশিক-জাতিবাদী মতাদর্শ ও রাজনীতিকে নির্দেশ করে যা পুরানা বাইবেলের একটি বিশেষ ব্যাখ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর সার কথা হচ্ছে, আল্লাহ ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন যে, জেরুজালেম তথা অখণ্ড ফিলিস্তিন ভূখণ্ড একমাত্র ইহুদিদের। এই চুক্তি যাবতীয় ঐতিহাসিকতা ও নৈতিকতার ঊর্ধ্বে। জায়নভূমির সঙ্গে ইহুদিদের এই সম্বন্ধ চিরন্তন, অলঙ্ঘনীয়, প্রাগৈতিহাসিক ও পরম। দেখুন: Avi Shlaim, The Iron Wall এবং ফরহাদ মজহার, সাম্রাজ্যবাদ, পৃ. ১০৩।
২. Joseph Massad, The Persistence of the Palestinian Question, p. 177.
৩. Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins: Reflections on the History of Zionism and Israel, London: Pluto Press, 1992.
৪. Ivan Marcus, “Jews and Christians Imagining the Other in Medieval Europe.” Prooftexts 15, no. 3 (1995): 209–26.
http://www.jstor.org/stable/20689425.
৫. Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins.
৬. তদেব।
৭. ইহুদিরাই যিশুখ্রিস্টের হত্যাকারী— এর স্বপক্ষে কোনো শক্ত প্রমাণ নাই; বরং হালের গবেষণা এই দাবি নাকচ করে দেয়। দেখুন: Samuel Griswold, “No Pope? What if Rome had become Jewish?”, The Times of Israel Blog, Sep 25, 2015.
https://blogs.timesofisrael.com/no-pope-what-if-rome-had-become-jewish/.
তাছাড়া নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কাহিনি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা ভিন্ন। এ বর্ণনা অনুযায়ী ঈসা (আঃ) কে হত্যা করার পূর্বেই মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে আশমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ঈসা (আঃ)-এর একজন অনুসারীকে তাঁর আকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। ঈসা (আঃ)-এর বাহ্যিক রূপ ধারণকারী সেই অনুসারীকেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। দেখুন: সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৫৭-১৫৮, পবিত্র আল কোরআন।
৮. Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins.
৯. James Joyce, Ulysses, New York, Random House, 2002.
১০. উদ্ধৃত, J.S. Conway, “Protestant Missions to the Jews 1810-1980: Ecclesiastical imperialism or theological aberration?”, Holocaust and Genocide Studies 1(1): 127–146. doi:10.1093/hgs/1.1.127.
১১. Black Death Pandemic, Encyclopedia Britannica.
https://www.britannica.com/event/Black-Death.
১২. ক্রিস্টোফার কলম্বাস তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন: “In the same month in which their Majesties [Ferdinand and Isabella] issued the edict that all Jews should be driven out of the kingdom and its territories, in the same month they gave me the order to undertake with sufficient men my expedition of discovery to the Indies.” দেখুন: “Modern Jewish History: The Spanish Expulsion (1492)” Jewish Virtual Library.
https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-spanish-expulsion-1492
১৩. Joel J. Levy/Center For Jewish History, “What Life Was Like in the World’s First Ghetto”, Time Magazine, November 2, 2016.
https://time.com/4551523/venice-ghetto-history/.
১৪. সে সময় ইহুদিরা প্রার্থনা করার সময় একে অপরের প্রতি বলতেন, “Next year in Jerusalem!” তবে এটা কেবল রুহানি প্রার্থনার অংশই ছিল, কোনো বাস্তব কর্মসূচির অংশ ছিল না। প্রার্থনার এই ‘জেরুসালেম’ সকল সময়ে ভৌত স্থানকে নির্দেশ করত না। ‘জেরুসালেম’ ছিল আদর্শ, বাসনা ও সম্ভাবনার প্রতীক। দেখুন: Dasee Berkowitz, “What Does ‘Next Year in Jerusalem’ Really Mean?”, Reform Judaism, APRIL 6, 2020.
https://reformjudaism.org/blog/what-does-next-year-jerusalem-really-mean.
১৫. Moti Benmelech, “History, Politics, and Messianism: David Ha-Reuveni’s Origin and Mission”, AJS Review 35, no. 1 (2011): 35–60.
http://www.jstor.org/stable/41310648.
১৬. Alan R. Taylor, “Vision and Intent in Zionist Thought”, in Transformation of Palestine, edited by Ibrahim Abu-Lughod, pp. 9-26.
১৭. Zenon Kohut, “The Khmelnytsky Uprising, the Image of Jews, and the Shaping of Ukrainian Historical Memory”, Jewish History 17, no. 2 (2003): 141–63. http://www.jstor.org/stable/20101495.
১৮. Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins.
১৯. তদেব।
২০. সুদীপ্ত কবিরাজ, “জাতীয়তা/অজাতীয়তা”, রাষ্ট্রচিন্তা: একটি রাষ্ট্রনৈতিক জার্নাল, ত্রয়োদশ সংখ্যা (বর্ষ ৮, সংখ্যা ২), জানুয়ারি, ২০২৪, সম্পাদক: আর রাজী।
২১. ইতিহাসবিদ সুদীপ্ত কবিরাজ মন্তব্য করেছেন, “পরশুরামের কায়দায় পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রীয় করতে না পারলেও এই রাজারা নিজেদের দেশ নিষ্প্রটেস্টান্ট এবং নিষ্ক্যাথলিক করতে পেরেছিলেন। ইয়োরোপের লোকেরা করলেও একে একটা শুভবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা বলা যায় না। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার একেবারে চরমপন্থার উপরে তাঁরা সামাজিক শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।” দেখুন: তদেব।
২২. Derek Croxton, “The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty”, The International History Review 21, no. 3 (1999).
http://www.jstor.org/stable/40109077.
২৩. সুদীপ্ত কবিরাজ, “জাতীয়তা/অজাতীয়তা”।
২৪. Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Modernity, Chicago: The University of Chicago Press, 2008.
২৫. তদেব।
২৬. Uday Singh Mehta, Liberalism and Empire: A Study in Nineteenth-Century British Liberal Thought.
২৭. নাজমুল সুলতান, “স্বাধীনতা কারে কয়? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঔপনিবেশিক আমলের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস পাঠের সমস্যা”, সময়ের কুয়াশায়: দীপেশ চক্রবর্তীর সম্মানে প্রবন্ধগুচ্ছ, সম্পাদনা: আহমেদ কামাল ও অন্যান্য, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০২৩।
২৮. সুদীপ্ত কবিরাজ, “জাতীয়তা/অজাতীয়তা”।
২৯. নাজমুল সুলতান, “স্বাধীনতা কারে কয়? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঔপনিবেশিক আমলের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস পাঠের সমস্যা”।
৩০. সুদীপ্ত কবিরাজ, “জাতীয়তা/অজাতীয়তা”।
৩১. Nazmul Sultan, Waiting for the People: The Idea of Democracy in Indian Anticolonial Thought, Cambridge: Harvard University Press, 2023.
৩২. Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins.
৩৩. কোনো একটা বিষয় কখন ‘প্রশ্ন’ হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে এডওয়ার্ড সাইদ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। কোনো একটা বিষয় যখন অন্য সকল বিষয় থেকে আলাদা রূপ ধারণ করে এবং আলাদা মনোযোগ দাবি করে, তখন তা ‘প্রশ্ন’। এজন্যই ‘ইহুদি প্রশ্ন’, ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’। এছাড়াও কোনো বিষয় যদি দীর্ঘকাল অমীমাংসিত অবস্থায় থাকে, তাহলেও সেটা ‘প্রশ্ন’ হিসেবে হাজির হয়। এমন ‘প্রশ্ন’ যা বারবার ফিরে ফিরে আসছে অথচ যার সঠিক চিহ্নায়ন হচ্ছে না। উপরন্তু কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তা যদি অবজ্ঞার শিকার হয় তথা অনেকের চৈতন্যে হাজির না থাকে, তখনও সেটা ‘প্রশ্ন’। ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে ‘ইহুদি প্রশ্ন’ জারি আছে। জায়নবাদ এই ‘প্রশ্ন’ সমাধানের নামে নতুন করে ‘ফিলিস্তিন প্রশ্ন’ সৃষ্টি করেছে। দেখুন: ফরহাদ মজহার, সাম্রাজ্যবাদ, পৃ. ১১০-১১২; আরও দেখুন: Edward Said, The Question of Palestine.
৩৪. Ben Halpern, The Idea of the Jewish State.
৩৫. Yakov M. Rabkin, A Threat From Within: A Century of Jewish Opposition to Zionism, translated by Fred A. Reed, London: Zed Books, 2006.
৩৬. Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins, p. 22.
৩৭. Alan R. Taylor, “Vision and Intent in Zionist Thought”.
৩৮. Joseph Massad, The Persistence of the Palestinian Question, p. 178.
৩৯. ফিলিস্তিনি কবি, বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিক ঘাসসান কানাফানির মতে, জায়নবাদী সাহিত্য রাজনৈতিক জায়নবাদের জন্ম দিয়েছে। বিপুল সংখ্যক জায়নবাদী সাহিত্য বিশ্লেষণ করে কানাফানি দেখিয়েছেন জায়নবাদী আন্দোলন সাহিত্যকে রাজনৈতিক ও সামরিক অভিযানের মতাদর্শিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছে। রাজনৈতিক জায়নবাদের শ্রেষ্ঠত্ববাদ ও বর্ণবাদ মূলত সাহিত্যিক জায়নবাদেরই ধারাবাহিকতা। দেখুন: Ghassan Kanafani, On Zionist Literature, translated by Mahmoud Najib, Oxford: Ebb Books, 2022 [1967].
৪০. Walter Laqueur, A History of Zionism: From the French Revolution to the Establishment of the State of Israel, New York: MJF Books, 1972.
৪১. David McLellan, Karl Marx: A Biography, Palgrave Macmillan; (4th edition), 2006.
৪২. Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins.
৪৩. Walter Laqueur, A History of Zionism.
৪৪. Richard P. Stevens, “Zionism as a phase of Western Imperialism”, in Transformation of Palestine.
৪৫. Jeff Halper, Decolonizing Israel, Liberating Palestine: Zionism, Settler Colonialism, and the Case for One Democratic State, London: Pluto Press, 2021.
৪৬. পোলিশ মার্কসবাদী সাংবাদিক ও চিন্তক আইজ্যাক ডয়েচার (Isaac Deutscher) এই ফাঁদে পা দিয়েছেন। তিনি ইজরায়েলের অন্ধভক্ত নন, ইজরায়েলের ব্যাপারে বেশ কিছু সমালোচনাও তাঁর আছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিনি ইজরায়েলকে শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রোদেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মতো সেটলার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে তুলনা না করে তুলনা করেছেন ইন্ডিয়া, বার্মা, ঘানা, আলজেরিয়া-সহ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করা রাষ্ট্রগুলোর সাথে। তিনি ইজরায়েলের সমালোচনা করছেন ঠিকই, কিন্তু অপরাপর জাতিরাষ্ট্রের সাধারণ প্রগতিশীল চরিত্রের অবক্ষয়ের অংশ হিসেবেই ইজরায়েলের অবক্ষয়কে দেখছেন: “Even those young nation-states that have come into being as the result of a necessary and progressive struggle waged by colonial and semi-colonial peoples for emancipation— India, Burma, Ghana, Algeria, and others— cannot preserve their progressive character for long….. In our epoch any nation-state, soon after its constitution, begins to be affected by the general decline of this form of political organization; and this is already showing itself in the short experience of India, Ghana, and Israel.” দেখুন: “The Non-Jewish Jew”, in The Non-Jewish Jew, p. 40-41.
উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উঠে আসা রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইজরায়েলকে একই পাল্লায় মাপার এই প্রবণতা বিভ্রান্তিকর। আমরা এ প্রবন্ধে দেখিয়েছি, ইন্ডিয়া-সহ একদা উপনিবেশিত অঞ্চলগুলো আধুনিক জাতিবাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছে ঠিকই, তবে তা আধুনিক জাতিবাদের মুক্তিদায়ী প্রতিশ্রুতি থেকে নিংড়ানো অনুপ্রেরণা, যা দিয়ে এসব অঞ্চল খোদ জাতিবাদের ঔপনিবেশিক প্রবণতার তীব্র বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে এবং কালক্রমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্যদিকে, জায়নবাদ, আধুনিক ইউরোপীয় জাতিবাদের ঔপনিবেশিক চরিত্র অনুকরণ ও আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি রূপে হাজির হয়েছে। এই পার্থক্য চিহ্নিত না করলে ইজরায়েলকে এক প্রকার দায়মুক্তি দেয়া হয়।
১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর আইজ্যাক ডয়েচার অবশ্য তাঁর অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। এ পর্বে এসে তিনি লিখছেন: “The nationalism of the people in semi-colonial or colonial countries, fighting for their independence, must not be put on at the same moral-political level as the nationalism of conquerors and oppressors. The former has its historic justification and progressive aspect which the latter has not. Clearly Arab nationalism, unlike the Israeli, still belongs to the former category.” দেখুন: Isaac Deutscher, “The Israel-Arab War, June 1967”, in The Non-Jewish Jew, p. 138.
ডয়েচারের এই বিশ্লেষণ আগের বিশ্লেষণের তুলনায় অধিকতর সঠিক হলেও পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। এর মধ্য দিয়ে তিনি বলার চেষ্টা করছেন যে, ইজরায়েল এক সময় উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও কালক্রমে (সাতষট্টির যুদ্ধের মাধ্যমে) তা হারাচ্ছে। ইজরায়েল যে ঔপনিবেশিক জায়নবাদের আবশ্যিক পরিণতি— যা এক সময় খোদ এই আন্দোলনের রূপকাররা অস্বীকার করেননি— ডয়েচারের বিশ্লেষণে সেই সত্য আড়াল হয়।
তবে ডয়েচারের বইটির গুরুত্ব অন্যখানে। তিনি আধুনিক ইহুদি ঐতিহ্যে সর্বজনীন চিন্তায় সক্ষম দার্শনিকদের (স্পিনোজা, মার্কস, ফ্রয়েড, হাইনরিশ হাইনে, রোজা লুক্সেমবার্গ, ট্রটস্কি প্রমুখ) তাৎপর্য তুলে ধরেছেন, যাঁরা ইহুদি হয়েও ইহুদিত্বের বৃত্তে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। দেখুন: Issac Deutscher, The Non-Jewish Jew and other Essays, New York: Hill and Wang, 1968.
রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে ‘পাকিস্তান’-কে ‘মুসলিম জায়ন’ অভিহিত করে আরেক দিক থেকে ইতিহাসবিদ ফায়সাল দেভজিও (Faisal Devji) একই ভুল করেছেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের উপনিবেশ-বিরোধী চরিত্র এবং ইজরায়েলের ঔপনিবেশিক চরিত্রকে আমলে নেননি। পাকিস্তান আন্দোলন যদি মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে মক্কা কিংবা আরবের কোনো অঞ্চলকে বেছে নিত, তাহলে দেভজির এই অদ্ভুত তুলনার কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা থাকত। দেখুন: Faisal Devji, Muslim Zion: Pakistan as a Political Idea, Cambridge: Harvard University Press, 2013.
৪৭. Alan R. Taylor, “Vision and Intent in Zionist Thought”, in Transformation of Palestine.
৪৮. তদেব।
৪৯. Moses Hess, Rome and Jerusalem, A Study in Jewish Nationalism, translated by Meyer Waxman, New York: Bloch Publishing House, 1918.
৫০. Alan R. Taylor, “Vision and Intent in Zionist Thought”, in Transformation of Palestine.
৫১. ফরাসি দার্শনিক ইমানুয়েল লেভিনাসও মনে করতেন ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জায়নবাদ ইতিহাসে পদার্পণ করেছে এবং একটা ‘ন্যায্য দুনিয়া’ কায়েমের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে: “The state of Israel is the first opportunity to move into history by bringing about a just world.” দেখুন: Emmanuel Levinas, “Jewish Thought Today”, in Difficult Freedom: Essays on Judaism, trans. Sean Hand, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990, p. 164.
৫২. John Rose, The Myths of Zionism, London: Pluto Press, 2004, p. 102.
৫৩. তদেব।
৫৪. Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel, trans. David Maisel, Princeton: Princeton University Press, 1998.
৫৫. “The Lovers Of Zion”, Jewish History.
https://www.jewishhistory.org/the-lovers-of-zion/.
৫৬. তারা উনিশ শতকের শেষের দিকে ফিলিস্তিনে সেটেলমেন্ট স্থাপন করেছিল। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিt আলোচনার জন্য দেখুন: ফিলিস্তিন: একুশ শতকের উপনিবেশের ইতিহাস (প্রথম অধ্যায়), সারোয়ার তুষার (প্রকাশিতব্য)।
৫৭. Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel, pp. 47-68.
৫৮. ‘ইহুদি প্রশ্ন’ সম্পর্কে হার্জেলের অভিমত: “I do not consider the Jewish question as a social one or a religious one… It is a national question, and to solve it we have to make it into a global question.” উদ্ধৃত, Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins, p. 37.
৫৯. তদেব।
৬০. এক সন্ধ্যায় লন্ডনের কোনো এক রেস্তরাঁয় হার্জেল অ্যাংলো-ইহুদি লেখক ইজরায়েল জ্যাংউইলের সাথে ডিনার করছিলেন। সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। হার্জেল তখন হন্যে হয়ে দল ভারী করার চেষ্টায় লিপ্ত। জ্যাংউইল পরে জায়নবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। জ্যাংউইল সম্ভবত ‘অভিন্ন ইহুদি বংশ’ ধারণায় বিশ্বাস করতেন। সেদিনের সাক্ষাৎ শেষে হার্জেল ডায়েরিতে লিখেছেন: “He obsesses about the racial aspect, which I cannot accept. It’s enough for me to look at myself and at him. I say only this: We are a historical entity, a nation made up of different anthropological elements. That will suffice for the Jewish state. No nation has racial uniformity.” দেখুন: Shlomo Sand, The Invention of the Jewish People, p. 258.
৬১. Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins.
৬২. ইহুদি রাষ্ট্রের সীমানা প্রসঙ্গে হার্জেল ডায়েরিতে লিখেছেন: “From the brook of Egypt to the Euphrates.” ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের স্পেশাল তদন্ত কমিটির কাছে ইহুদি এজেন্সির সদস্য রাব্বি ফিশমান ইহুদি রাষ্ট্রের সীমানা প্রসঙ্গে একই কথা বলেন: “The promised land extends from the river of Egypt to the Euphrates. It includes parts of Syria and Lebanon.” দেখুন: Ralph Schoenman, The Hidden History of Zionism.
৬৩. Lenni Brenner, “Blut UND Boden (Blood and Soil): The Roots of Zionist Racism”, Zionism in the Age of the Dictators, pp. 24-30.
৬৪. তদেব।
৬৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত জার্মানিতে ইহুদিদের নিরবচ্ছিন্ন বসবাসের ইতিহাস অন্তত ১,৭০০ বছরের। দেখুন: Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins, p. 14.
৬৬. ইহুদিদের ইউরোপে বসবাসের ইতিহাস হাঙ্গেরির ম্যাগয়ার্সদের চেয়েও পুরানা। কিন্তু ম্যাগয়ার্সদের কেউ কখনো ‘এশীয়’ না বললেও বুবের মনে করেন রক্তের ধারায় গড়ে ওঠা সম্প্রদায়— তাঁর ভাষায় ‘community of blood’— ইহুদিরা কখনোই ইউরোপীয় হতে পারবে না। দেখুন: Martin Buber, On Judaism, trans. Eva Jospe. Knopf Doubleday Publishing Group, 1996.
https://theanarchistlibrary.org/library/martin-buber-on-judaism.
৬৭. আইনস্টাইন লিখেছেন: “Nations with racial difference appear to have instincts which work against their fusion. The assimilation of the Jews to the European nations… could not eradicate the feeling of lack of kinship between them and those among whom they lived. In the last resort, the instinctive feeling of lack of kinship is referable to the law of conservation of energy. For this reason it cannot be eradicated by any amount of well meant pressure.” দেখুন: Solomon Goldman, Crisis and Decision, New York, London: Harper & Brothers, 1938, p. 116.
৬৮. এ প্রসঙ্গে হার্জেলের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: “Where [anti-semitism] does not exist, it is carried by Jews in the course of their migrations… The unfortunate Jews are now carrying the seeds of Anti-Semitism into England, they have already introduced it into America.” দেখুন: Theodor Herzl, 1988 [1896]. The Jewish State, Dover Publications: New York.
৬৯. Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators.
৭০. তদেব।
৭১. Ben Frommer, “The significance of a Jewish State”, Jewish Call, Sanghai, 1935, p. 10.
৭২. তদেব।
৭৩. ইজরায়েলি দার্শনিক এবং বাইবেল বিশেষজ্ঞ ইয়েহেজকেল কাউফম্যান ইহুদিদের সম্পর্কে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ জায়নবাদী নেতার উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। ইহুদিরা অন্য কিছু হওয়ার যোগ্য কি অযোগ্য পরের বিষয়, মিচা জোসেফ বার্ডিকজেউস্কির বিবেচনায় তারা মানুষই নয় (“not a nation, not a people, not human”)। ইয়োসেফ হাইম ব্রেন্নারের কাছে ইহুদিরা যাযাবর ও নোংরা কুকুর (“Gypsies, filthy dogs, inhuman, wounded, dogs”)। লেবার জায়নবাদের প্রধান তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব এডি গর্ডনের কাছে ইহুদিরা রীতিমতো পরজীবী ও ফেলনা (“parasites, people fundamentally useless”)। দেখুন: Yehezkel Kaufman, “Hurban Hanefesh: A Discussion of Zionism and Anti-Semitism”, Issues, (Winter 1967), p. 106.
৭৪. Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel.
৭৫. তদেব।
৭৬. নিউইয়র্কস্থ জ্যুয়িশ ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার সম্পাদক হাইম গ্রিনবার্গ ১৯৪২ সালে আত্মসমালোচনা ও আক্ষেপের সুরে লিখেছেন: “[there had been] a time when it used to be fashionable for Zionist speakers (including the writer) to declare from the platform that ‘to be a good Zionist one must be somewhat of an anti-Semite’. To this day Labour Zionist Circles are under the influence of the idea that the Return to Zion involved a process of purification from our economic uncleanliness. Whosoever doesn’t engage in so-called ‘productive’ manual labour is believed to be sinner against Israel and against mankind.” দেখুন: Chaim Greenberg, “The Myth of Jewish Parasitism”, Jewish Frontiers, (March 1942), p. 20.
৭৭. তদেব।
৭৮. Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators.
৭৯. তদেব।
৮০. তদেব।
৮১. জায়নবাদীরা কীভাবে ইউরোপীয় খ্রিস্টান সমাজে বিরাজমান ইহুদি-ঘৃণাকে আত্মস্থ করেছে, তার নিখুঁত বর্ণনার জন্য দেখুন: Nathan Weinstock, Zionism: False Messiah, trans. and ed. by Alan Adler, London: Ink Links, 1979; Michael Selzer, Aryanization of the Jewish State, New York: Blackstar, 1967.
৮২. কিন্তু ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও পৌরাণিক নজির জায়নবাদীদের এই দাবিকে সমর্থন করে না। দেখুন: Keith W. Whitelam, The Invention Of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History; Nur Masalha, The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archaeology And Post-Colonialism in Palestine-Israel; Shlomo Sand, The Invention of the Jewish People; Shlomo Sand, The Invention of the Land of Israel: From Holy Land to a Homeland.
৮৩. Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel; George Mosse, Confronting the Nation, Jewish and Western Nationalism, Hanover, NH: Brandeis University Press, published by the University Press of New England, 1993, pp. 161-175.
৮৪. Joseph Massad, “The post-colonial” colony: time, space, and bodies in Palestine/Israel”, The Persistence of the Palestinian Question, pp. 13-40.
৮৫. তদেব।
৮৬. তদেব।
৮৭. Sander Gilman, The Jew’s body, New York: Routledge, 1991.
৮৮. Paul Breines, Tough Jews, Political Fantasies and the Moral Dilemma of American Jewry, New York: Basic Books, 1991.
৮৯. পল ব্রেইনেসের বইয়ের দ্বিতীয়ভাগের উপশিরোনাম: “From Masada to Mossad: a historical sketch of tough Jewish imagery”, Tough Jews, Political Fantasies and the Moral Dilemma of American Jewry, pp. 75-167.
৯০. জোসেফ মাসাদ বহুল প্রশংসিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমা ইউরোপা ইউরোপা (Europa Europa) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন নাৎসি নিয়ন্ত্রিত জার্মানির বয়ঃসন্ধিকালীন এক ইহুদি কিশোরের শিশ্নকেন্দ্রিক হীনমন্যতাকে ঘিরে পুরো সিনেমার কাহিনি গড়ে উঠেছে। সিনেমাটির প্রধান চরিত্র ইহুদি কিশোর সলোমন পেরেল নাৎসিদের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে তটস্থ থাকে। নাৎসি বাহিনী কর্তৃক ইহুদি শনাক্তকরণের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায় শিশ্ন। যেন শিশ্নই ইহুদি পরিচয়ের একমাত্র ধারক ও বাহক! অবশ্য এই পদ্ধতিতে ইহুদি নারীদের কীভাবে শনাক্ত করা যাবে তার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। সিনেমাটিতে নাৎসিদের হাতে ধরা পড়া একজন আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান নিজের অ-ইহুদিত্বের প্রমাণস্বরূপ খৎনাহীন শিশ্ন দেখিয়ে ছাড়া পান। একজন আলবেনিয়ান কিংবা বসনিয়ান মুসলমান যদি ইহুদি সন্দেহে নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ত, এই পদ্ধতি অনুসারে তাদের অ-ইহুদিত্ব প্রমাণের কোনো সুযোগ আর থাকে না।
খৎনাকৃত শিশ্নের কারণে ইউরোপীয় খ্রিস্টান সমাজের ঘৃণা ও মশকরার শিকার ইহুদি পুরুষদের শিশ্নকেন্দ্রিক হীনমন্যতা দূর করা ছিল জায়নবাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রকল্পে “ইহুদি শরীরের পরিচর্যা ও পুনর্গঠন”-এর অর্থ দাঁড়ায় ইহুদি পুরুষের শিশ্ন হীনমন্যতা কাটিয়ে তোলা। দেখুন: Joseph Massad, The Persistence of the Palestinian Question, pp. 13-40.
৯১. Sigmund Freud, “Analysis of a phobia in a Five-year-old boy”, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, London: Hogarth Press, 1953-1974, Vol. X, 36f.
৯২. জোসেফ মাসাদের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ: “Hence the Jewish penis becomes the site of reinterpretation of Jewish masculinity by Zionism. The only way Jewish men can rejoin the world of (gentile) men after Nazi annihilation, the film suggests, is through a spectacular exposure of their circumcised penises as a visual assertion of phallicity against a discursive and materially castrating order.” The Persistence of the Palestinian Question, p. 32.
৯৩. প্রখ্যাত মনোবিশ্লেষক মেলানি ক্লেইন অবলম্বনে জায়নবাদী এই প্রকল্পকে ‘penis-pride’ তথা শিশ্নগর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন জোসেফ মাসাদ।
http://www.psychoanalysis-and-therapy.com/human_nature/nash/Nashchap3.html.
৯৪. Simona Sharoni, “To be a man in the Jewish State, the sociopolitical context of violence and oppression,” Challenge, 2:5 (September/October 1991), 26-28.
৯৫. David Hirst, The gun and the olive branch, pp. 124-129.
৯৬. Ella Shohat, “Imaging terra incognita: the disciplinary gaze of Empire”, Public Culture (1991) 3 (2): 41–70.
৯৭. Joseph Massad, The Persistence of the Palestinian Question.
৯৮. Nira Yuval-Davis, “National reproduction and ‘the demographic race’ in Israel”, in Woman–Nation–State, edited by Nira Yuval-Davis & Floya Anthias, London: Macmillan, 1989, pp. 92-109.
৯৯. Joseph Massad, The Persistence of the Palestinian Question.
১০০. অতি সম্প্রতি মার্কিন হাউজ অব রেপ্রেজেন্টেটেটিভে ৩১১ বনাম ১৪ ভোটে জায়নবাদ-বিরোধিতাকে ‘ইহুদিবিদ্বেষ’ সাব্যস্ত করার প্রস্তাব পাশ হয়েছে।
https://www.aljazeera.com/amp/news/2023/12/6/anti-zionism-is-antisemitism-us-house-asserts-in-dangerous-resolution; Robert S. Wistrich, “Zionism and Anti-Semitism in the 21st Century”, Jewish Virtual Library, August 2012.
https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-studies-an-anthology-anti-zionism-and-anti-semitism.
১০১. Nathan Weinstock, Zionism: False Messiah.
১০২. হার্জেল তাঁর জীবদ্দশাতে বলে গিয়েছিলেন যে, ইহুদি-বিদ্বেষী ব্যক্তি ও রাষ্ট্রগুলোই জায়নবাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র হবে: “The anti-Semites will become our most dependable friends, the anti-Semitic countries our allies.” Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl, Vol. 1, edited by Raphael Patai, translated by Harry Zohn, New York: Herzl Press and Thomas Yoseloff, 1960, p. 94.
তিনি আরও বলেছিলেন, “the Governments of all countries scourged by Anti-Semitism will be keenly interested in assisting us to obtain [the] sovereignty we want.” দেখুন: Herzl, Jewish State, p. 93.
হার্জেলের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের (বিশেষত পাশ্চাত্যের) প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো জায়নবাদের ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়েছে। এমনকী হলোকাস্টের মূল কারিগর, ইহুদিদের ভাইরাসের সাথে তুলনাকারী হিটলার পর্যন্ত জায়নবাদীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: “And whatever doubts I may still have nourished were finally dispelled by the attitude of a portion of the Jews themselves. Among them there was a great movement, quite extensive in Vienna, which came out sharply in confirmation of the national character of the Jews: this was the Zionists.”
দেখুন: Adlof Hitler, Mein Kampf, p. 56.
https://www.sjsu.edu/people/mary.pickering/courses/His146/s1/MeinKampfpartone000.pdf.
নাজিবাদ ও জায়নবাদের মধ্যে গভীর আঁতাতের চুলচেরা তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন লেন্নি ব্রেন্নার। দেখুন: Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators; নানা ছলচাতুরি করে ইরাকি ও মিশরীয় ইহুদিদের ইজরায়েলে আনার জন্য ইরাকি ও মিশরীয় সরকারের সাথেও জায়নবাদীদের গোপন আঁতাত হয়েছিল। দেখুন: David Hirst, The gun and the olive branch, pp. 281-297; আজের্ন্টাইন ইহুদিদের বিরুদ্ধে ইহুদি-বিদ্বেষী নীতি গ্রহণে জায়নবাদীরা আর্জেন্টাইন জেনারেলদের ফুসলিয়েছিল। দেখুন: Noam Chomsky, The Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians, Boston, MA: South End Press, 1983, p. 110.
১০৩. Joseph Massad, “The Persistence of the Palestinian Question”, in The Persistence of the Palestinian Question, pp. 166-178.
১০৪. David Hirst, The gun and the olive branch, pp. 312-314.
১০৫. নোংরা, অসুস্থ, দুর্বল, মধ্যযুগীয় ইত্যাদি নানা তকমা সেঁটে দিয়ে জার্মান ইহুদি-বিদ্বেষীরা প্রতিবেশী ইহুদিদের দৈনন্দিন জীবন বিষিয়ে তুলেছিল। অনেক ক্ষেত্রে জার্মান ইহুদিরা পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের অনুরূপ বর্ণবাদী তকমায় জর্জরিত করেছে এমন নজির পাওয়া যায়। আবার ইজরায়েল পর্বে পূর্ব ইউরোপের ইহুদিরা আরব-ইহুদিদের বর্ণবাদী ভাষায় আক্রমণ করেছে। ইতিহাসের করুণ পরিহাস হচ্ছে এই, ইজরায়েলি সেটলার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মতাদর্শিক ভিতটাই এমন যে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নির্বিশেষে ইজরায়েলি ইহুদি জনগোষ্ঠী একই ধরনের (কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও নির্মম) বর্ণবাদী ভাষা আত্মস্থ করে স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের হামেশাই ঘায়েল করেছে। দেখুন: Michael Selzer, Aryanization of the Jewish State; Ilan Pappe, “The Alien who became a Terrorist: The Palestinian in Zionist Thought”, The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge, pp. 30-50; Nurit Peled-Elhanan, Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education, I.B. Tauris, 2012.
সারোয়ার তুষার

প্রাবন্ধিক ও রাজনৈতিক কর্মী, বাংলাদেশ।