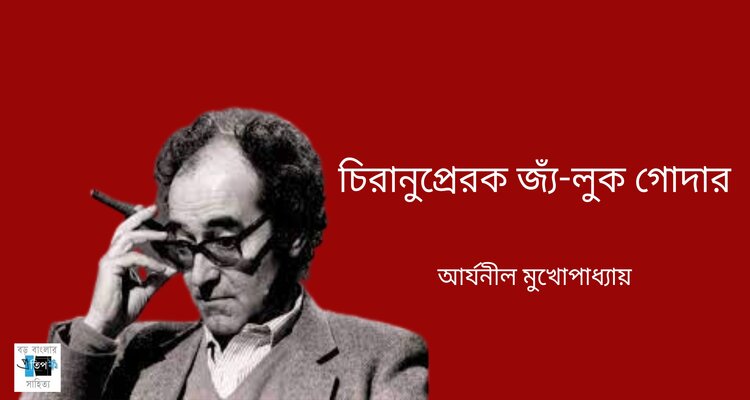(বঙ্গবিচ্ছিন্নতার বিপরীতে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র-অভিসন্দর্ভ নির্মাণের প্রয়াস)

।। অতনু সিংহ ।।
ঋত্বিককুমার ঘটক বড় বাংলার চলচ্চিত্রী। শুধু তাঁকে চলচ্চিত্রী বলা যাবে না বরং তিনি বাংলার বহুত্ববাদী জাতীয় সংস্কৃতির ভিতর থেকে চলচ্চিত্রের বঙ্গীয় লোকায়ত ভাষ্যের জন্ম দিয়ে গেছেন, যা বৈদিক দর্শনের বিপ্রতীপ, মনুবাদের বিরোধী, শঙ্করাচার্যের মায়াদর্শনের বিরোধী। একই সঙ্গে তিনি ঔপনিবেশিকতা সূত্রে আমদানিকৃত পশ্চিমা চিন্তাপদ্ধতির বিনির্মাণের প্রয়াসকে হাজির করেছেন বাংলার ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক’ সংস্কৃতির অন্দরে…
কৃষিনিবিড় বঙ্গের চারু-তরিকায় ঋত্বিকীয় সিনে-পরিকাঠামো
(বঙ্গবিচ্ছিন্নতার বিপরীতে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র-অভিসন্দর্ভ নির্মাণের প্রয়াস)

শুরুতেই দুইটি গু্রুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি
ক।
১৯৪৭-এর আগে পূর্ববঙ্গে বাবুরা যে নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপর কী পরিমাণে অত্যাচার করেছে, সে ভাবা যায় না। এবং সে কারণেই নিম্নবর্ণের মানুষ, অল ভোটেড ফর মুসলিম লীগ। এবং আফটার পার্টিশন তারাই রয়ে গেছে। যতগুলো জমিদার, সবগুলো চোর, অলমোস্ট অল, ভেরি ফিউ হয়তো ভালো। ওইভাবে কতো লোককে, কতো সম্প্রদায়কে উৎখাত করেছে, তার ঠিকঠিকানা নাই। আমি নিজে জমিদার বাড়ির ছেলে— আমার পরিবারে নিজের বাড়িতে আমি দেখেছি। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান কোনো ব্যাপার নয়, ওই বাবুরা মুসলিম চাষিদের ওপর অত্যাচার করেছে, হিন্দু চাষিদের ওপরেও করেছে, মানে ওই নিম্নবর্গের মানুষদের…
— ঋত্বিককুমার ঘটক, সাক্ষাৎকার, সিনে সেন্ট্রাল, সাক্ষাৎকার সংকলন- ‘নিজের পায়ে নিজের পথে’।
খ।
দুইডা বাংলারে আমি মিলাইতে চাইছি। দুইডারে আমি ভালোবাসি, হেইডা আমি কমু গিয়া মিঞা, এবং আজীবন কইয়া যামু, মৃত্যু পর্যন্ত আমি কইয়া যামু। আমি পরোয়াই করি না, আমার পয়সার পরোয়া নাই। I can fight that out. ঋত্বিক ঘটক can do that out here and in Dhaka. আমারে কে মারব লাথি, মারুক গা যাক। বইয়া গ্যাছে গিয়া… আমাদের তো অর্থনীতিটাও চুরমার করে দিয়েছে ওই বাংলাভাগ। আমি এইডা মানতে পারি নাই। আমি ফের আপনাদের নিয়া আমার বাংলাটারে জোড়া লাগাইতে চাই।
— ঋত্বিককুমার ঘটক, সাক্ষাৎকার সংকলন- ‘নিজের পায়ে নিজের পথে’।
বঙ্গের শিল্প-সাহিত্যে ১৯৪৭ বা বাংলাভাগের প্রতিফলন বিষয়ে আলাপ হলেই ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার প্রসঙ্গ ওঠে। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সাতচল্লিশ কী প্রভাব ফেলেছিল তা নিয়েও আর্টের দোহাই দিয়ে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় পরচর্চাপ্রবণ বাঙালিদের মধ্যে! আবার সাতচল্লিশে বাংলা ভাগের কথা বলতে গিয়ে বেশিরভাগই, ৪৭ পূর্ব ব্রিটিশ ভারতকে বিভক্ত দেশ বলে বর্ণনা করেন। বলতে থাকেন যে ভারত ভাগ হয়েছিল! আজকের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকেও পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রবিত্তরা ‘দেশ’ বলে কল্পনা করতে ভালোবাসেন। কিন্তু ৪৭ পূর্ব ঔপনিবেশিক ভারত ছিল সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শাসিত অনেকগুলি দেশের একটি সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক সমাহার। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তাকে এই ‘দেশ’ হিসাবে কল্পনা। অন্যদিকে ভারত রাষ্ট্র যে ‘দেশ’ নয় কোনোমতেই বরং তা একটি যুক্তরাষ্ট্র সেটা ভারতের সংবিধানের পার্ট-ওয়ান পাঠ করলেই স্পষ্টতই জানা যায়। যাইহোক, সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হয়েছিল এই অর্থে নয় যে ভারত ভাগ হয়েছিল বরং দেশ ভাগ হয়েছিল এই অর্থে যে বাংলা ভাগ হয়েছিল। পঞ্জাবও। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে থাকা দুটি সাংস্কৃতিক দেশ পঞ্জাব আর বাংলা ভাগ হয়েছিল। এই কথাগুলো শুরুতেই আলাপ করতে হলো, তার কারণ, ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় ৪৭-এর প্রভাব নিয়ে কথা বলতে হলে নিশ্চিতভাবেই যেই ব্যাপারে আলাপ করতে হবে তা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণের কথা। যে সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণ ঋত্বিক করতে চেয়েছিলেন। অনেকে ঐ সাংস্কৃতিক পুনর্মিলনকে দুই বাংলার রাজনৈতিক পুনর্মিলন হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। তা ঋত্বিক কখনোই চাননি। পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক কার্যকারণকেও তিনি অস্বীকার করেননি। হিন্দুমহাসভার বর্ণবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতি এবং তার প্রতি কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারত থেকে ইতিহাসসূত্রে আমদানি হওয়া অবিভক্ত বাংলার পূর্বপ্রান্তে ভদ্রবিত্ত বাবু বর্ণহিন্দুদের অস্পৃশ্যতা, নিম্নবর্গ-নিম্নবর্ণ ও মুসলিমঘৃণার রাজনৈতিক প্রতিফলনেই যে প্রজা কৃষক পার্টির বদলে মুসলীম লীগের জনভিত্তি বেড়ে গিয়েছিল বাংলায় এবং পাকিস্তান আন্দোলন সাফল্য পেয়েছিল তা ঋত্বিকও অস্বীকার করেন না। উপরের ‘ক’ অংশে উদ্ধৃত ঘটকের উক্তিটি দেখলেই এটা টের পাওয়া যায়।
আবারও বলছি বাংলা বা বঙ্গদেশ এই বর্ণবাদে আচ্ছন্ন ছিল না। বঙ্গদেশের হাজার-হাজার বছরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় পাল যুগের শেষ থেকে দশুরু করে সেন যুগে মাত্র বৈদিক সংস্কৃতির লোকেদের, ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটেছে বাংলায়। যদিও সুলতান আমলে বৈদিকতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও দার্শনিকভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যরা। বৃহত্তর নদীয়ার ভাবান্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা রুখে দিতে পেরেছিলেন শঙ্করাচার্যের গোত্রবাদী মায়াবাদ, বর্ণবাদ, বিত্তবাদ বা ধনবৈষম্য ও নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক বৈষম্যকে। কিন্তু এসবের পুনরুত্থান ঘটে ঔপনিবেশিক আমলে। এমনকি ব্রাহ্মণ্যবাদ ও তার বর্ণবাদী সংস্কৃতির পালটা ওয়াহাবিজমের বঙ্গীয় উত্থানও সেই সময়। যদিও ঔপনিবেশিক আমলে ওয়াহাবি আন্দোলন ইতিবাচকভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করেছে। যাইহোক, মোট কথা, ঔপনিবেশিক আমলেই জাতপাত বিভাজন, অস্পৃশ্যতা ও জমিদারি শোষণের মাত্রা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে বাংলার নিম্নবর্ণের ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃষক, কৃষি-মজুর ও কারিগরী সমাজ এর থেকে মুক্তি চেয়েছে এবং সেই সময় বাংলার বঙ্গীয় চেতনাও ওই বর্ণবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের রাজনৈতিক নির্মাণে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক নির্মাণের মধ্যে মিশে গেছে। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তান আন্দোলনকে কাউন্টার এফেক্ট বলা যেতে পারে। এখন ঋত্বিক ঘটক যে ‘দুইডা বাংলারে মিলাইতে’ চেয়েছেন (উপরে ‘খ’ অংশে উদ্ধৃতি), এই মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস আসলে বৈদিকতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমান্তরালে বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থান প্রকল্প নির্মাণ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কালচারালি ‘দুইডা বাংলারে’ ‘এক’ করতে চেয়েছেন ঋত্বিক, তাঁর সিনেমায়।
অনার্য বঙ্গভূমের চলচ্চিত্রী ঋত্বিক ঘটককের সিনেমা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাঁকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বা শুধুমাত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রী বলা যায় না। বরং ঋত্বিককুমার ঘটক বড় বাংলার চলচ্চিত্রী। শুধু তাঁকে চলচ্চিত্রী বলা যাবে না বরং তিনি বাংলার বহুত্ববাদী জাতীয় সংস্কৃতির ভিতর থেকে চলচ্চিত্রের বঙ্গীয় লোকায়ত ভাষ্যের জন্ম দিয়ে গেছেন, যা বৈদিক দর্শনের বিপ্রতীপ, মনুবাদের বিরোধী, শঙ্করাচার্যের মায়াদর্শনের বিরোধী। একই সঙ্গে তিনি ঔপনিবেশিকতা সূত্রে আমদানিকৃত পশ্চিমা চিন্তাপদ্ধতির বিনির্মাণের প্রয়াসকে হাজির করেছেন বাংলার ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক’ সংস্কৃতির অন্দরে। বৃহৎ বঙ্গ যে আদতে অবৈদিক, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রীকরণের বিপরীতে বহুত্ববাদী অনার্য সাংস্কৃতিক ধারা, তা ঋত্বিক তুলে ধরতে চেয়েছেন এই বঙ্গীয় ধারার মধ্যে তাঁর সিনে-ভাষ্যে ও চলচ্চিত্র-অভিসন্দর্ভ (সিনে-ডিসকোর্স) হাজির করার মাধ্যমে। ‘অযান্ত্রিক’-এ জড় ও প্রকৃতি জগতের সম্পর্ক এবং তার অনার্য প্রেক্ষিত, ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় একদিকে বৈদিকবাদ, উপনিবেশবাদ ও পিতৃতন্ত্রের দ্বারা বঙ্গ-কোতল চক্রান্তের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাংলার প্রকৃতিমগ্নতা (যা আদি তন্ত্রের আখ্যান) গ্রেইট মাদার আর্কিটাইপের মধ্যে তুলে ধরা (নীতা চরিত্রটি), ‘কোমলগান্ধার’-এ সংস্কৃত ভাষায় রচিত কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানম শকুন্তলম’-এর বঙ্গীয় বিনির্মাণে কৃষিবিপ্লব প্রস্তাব পেশ করা; বঙ্গীয় পুরুষ-প্রকৃতির দার্শনিক চিন্তার ভিতর দিয়ে আবার ‘দুইডা বাংলারে মিলাইতে’ চাওয়ার সাংস্কৃতিক প্রস্তাবনাও রচিত হয়েছে। ‘সুবর্ণরেখা’ ছবিটিতে বৈদিক মহাকাব্য রামায়ণের আর্যীয় প্রকরণকে বিচ্ছিন্ন ও বিনির্মাণ করে তাকে বঙ্গীয় করা হয়েছে। তার সঙ্গে বৈদিকবাদের পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতি ও তার দরুণ বঙ্গবিভাজনের রাজনৈতিক ইতিহাসের পোস্টমর্টেমও লক্ষ্যণীয়। আর ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ নামক ছবিতে অনার্য বঙ্গীয় ভূমিমানুষের কৃষিনিবিড় সম্পর্ক ও দ্রোহচিত্র চিত্রায়িত করেছেন, সেখানেও রয়েছে বাংলা ভাগের ইতিহাসের পোস্টমর্টেম এবং এক দ্রোহ আয়োজন। ঋত্বিক নিজে মার্ক্সবাদী। কিন্তু মার্ক্সবাদী রাজনীতির ইউরোপীয়ান প্র্যাক্টিসের কপি-পেস্টকে চুড়ান্ত ক্রিটিকও করেছেন যুক্তি তক্কোতে। যা তাঁর পূর্বকার ছবিগুলোর সারমর্ম, অনেকটা অটোবায়োগ্রাফিক এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে।
ইউরোপীয় আলোকায়ন, যুক্তিবাদ ও বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে মার্ক্স তাঁর সকল লেখায় এবং চিন্তায় হাজির করেছিলেন হেগেলের ভাববাদের বিনির্মাণ, ইউরোপীয় বস্তুবাদ ও ফায়ারবাখীয় দ্বান্দিকতার নিরিখে। এঙ্গেলস যেটাকে ইউরোপীয় ইতিহাস চেতনার নিরিখে অর্থনৈতিক কালানুক্রমবিভাজনের সরলরৈখিক ইতিহাস পর্যালোচনায় পর্যবসিত করেছিলেন, যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রাচ্যে মাও সে তুং চিনের ইতিহাস ও সমাজচেতনার নিরীখে মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের প্রয়োগ করলেও বাংলায় তথা উপমহাদেশে তা হয় নাই। বরং এঙ্গেলসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইউরোপীয় প্রেক্ষিতে ভর করে বঙ্গ তথা উপমহাদেশে বিপ্লবের প্রস্তাবনা রচিত হয়েছিল। ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’র অরণ্যদৃশ্যে নকশালপন্থী গেরিলা বিপ্লবীর সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়ে নীলকন্ঠ বাগচী চরিত্রটি এই ক্রিটিকটা খানিকটা প্রবন্ধের ঢঙে উত্থাপন করেছেন। আমরা সকলেই জানি নীলকন্ঠ বাগচী চরিত্রে ঋত্বিক শুধুই অভিনয়ই করেননি বরং ওই চরিত্রটি আসলে ঋত্বিক নিজেই।
বৃহৎ বঙ্গের জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তির ভিতর দিয়েই দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং বঙ্গের ভূমিহীন কৃষক, কৃষিমজুর ও কারিগরী সমাজের যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি মিলতে পারে এটা ঋত্বিক হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। তাই মার্ক্সের চিন্তার সঙ্গে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর গ্রেইট মাদার আর্কিটাইপ ও ফার্টিলিটি কাল্টের তত্ত্ব মিশিয়ে কৃষিপ্রধান ও জল-জমি-জঙ্গলের আধারে বঙ্গযাপনের দৃশ্যশ্রাব্যমালা বুনে গেছেন ঋত্বিক। শুধু তাই নয়, ইউরোপীয় বুর্জোয়া শিল্প-নান্দনিকতায় তৈরি হওয়া ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজের বিনির্মাণ করে তিনি বঙ্গীয় চিত্রশব্দভাষা নির্মাণ করতেও চেয়েছেন। তাঁর সিনেমার মেলোড্রামাটিক অ্যাক্টিং, থ্রিয়েট্রিক্যাল মিজ-অঁ-সিন (Mise-en-scène), লো-অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা পোজিশনে চরিত্রকে মিথিক্যাল বা আর্কিটাইপাল বানানো, লিরিক্যাল ইমেজ ও দৃশ্যনির্মাণ— এসবই তাঁর ইউরোসেন্ট্রিকতা-বিপ্রতীপ চলচ্চিত্রভাষার উপাদান।
ঋত্বিককে বড় বাংলার এই জন্যেবলা হচ্ছে না যে তিনি দেশভাগকে মেনে নিতে না পেরে রোম্যান্টিক ভাবনা থেকে দুই বাংলাকে এক করে যেতে চেয়েছেন, বরং তিনি বঙ্গীয় চিত্রভাষায় বড় বাংলার ভাবচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁর চলচ্চিত্রে। যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, এই দার্শনিকতাকেই প্রতিপাদ্য করে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক হতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে আগেই বলেছি যে পশ্চিমা যুক্তিবাদ আর আলোকবাদের সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিকতার ইতিহাসচেতনার কপি-পেস্ট করে তিনি ইউরোপীয় নান্দনিক চিত্রভাষা গড়ে তোলেননি বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের শ্রুতিনির্ভর বিদ্যাচর্চায় কাব্য, পুঁথি, আখ্যান ও গীতির যে অপার বঙ্গীয় তথা উপমহাদেশীয় ভূমিজ নান্দনিক প্রস্তাব, তা দিয়েই তিনি শিল্পবিপ্লবের ফসল চলচ্চিত্র মাধ্যমের বুর্জোয়া পরিকাঠামোর বিনির্মাণ করতে চেয়েছেন। আত্মভুবন ও আত্মপাঠের মধ্যে দিয়েই অপরের সঙ্গে ভাববিনিময়ের যে বঙ্গীয় চারুতরিকা, সেই অর্থে ভাণ্ডে যাহা আছে তাহা দিয়েই নিজ সমাজের আখ্যান ও বয়ানকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আর এসব কিছুকে উপজীব্য করেই তিনি আন্তর্জাতিকতা ও বহুজাতিকতায় বঙ্গভাষ্যের জায়গাকে পোক্ত করতে চেয়েছেন সিনে-পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, লোকায়ত বড় বাংলার ‘জাতীয়’ পরিকাঠামো তাঁর সিনেবীক্ষণে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তা কোনোভাবেই জাতীয় সমাজবাদের বয়ান নয়। অথচ ঋত্বিক কুমার ঘটককে জাতীয় সমাজবাদ তথা নাৎসিবাদ তথা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে মিলিয়ে বিকৃত করার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখন। এই আলাপটুকু্র অবতারণা অত্যন্ত জরুরী ঋত্বিকের সিনেবীক্ষণের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে। আগেই বলেছি এবং বিষয়টি অনেকেই জানেন যে ঋত্বিকের অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় এবং উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে এবং তার রাজনৈতিকতায় অবশ্যই মার্ক্সের সমাজতত্ত্ব ও সেই সূত্রে নির্মিত দর্শন গুরুত্বপ্ররণ। একইভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদও।
ঘটকের সিনেমা আমাদের মাথার ভিতরে এক ঐতিহাসিক চেতনাকে জারিত করে, যা ইউরোপীয় ইতিহাসচর্চা নয়। বরং পশ্চিমা দীপায়ন প্রকল্পের সমান্তরালে অনাদিকাল থেকে ভাব ও বস্তু মিলেমিশে প্রকৃতিনিবিড় বঙ্গে যে দার্শনিক ধারা গড়ে উঠেছিল আদিতন্ত্র, সাংখ্য, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্যে দিয়ে তা গুটেনবার্গীয় প্রিন্টিং টেকনলজি ভিত্তিক এপিস্টোমলজির বিপ্রতীপ। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীগুলির টোটেম সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে যে স্মরণাতীত বঙ্গীয় যৌথ নির্জ্ঞান প্রতিভাত হয় ঋত্বিকের চলচ্চিত্রায়িত অভিসন্দর্ভে। যা নির্মাণে ঋত্বিক কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর দ্বারস্থ হয়েছেন। উপমহাদেশীয় মিথকে তিনি বঙ্গীয় প্রেক্ষিতে বিনির্মাণ ও পরিবর্ধন করে মিথিওথোপিক চলচ্চিত্রভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রগুলিকে সামনে রেখে এই বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা দরকার। আর তাঁর মাধ্যমেই বঙ্গীয় চেতনায় ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের রাজনৈতিক অবস্থান, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলাপের মাধ্যমে এই গদ্যটির প্রাণবস্তুটিকে মূর্ত করা যেতে পারে!
আলোকবাদের সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিকতার ইতিহাসচেতনার কপি-পেস্ট করে তিনি ইউরোপীয় নান্দনিক চিত্রভাষা গড়ে তোলেননি বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের শ্রুতিনির্ভর বিদ্যাচর্চায় কাব্য, পুঁথি, আখ্যান ও গীতির যে অপার বঙ্গীয় তথা উপমহাদেশীয় ভূমিজ নান্দনিক প্রস্তাব, তা দিয়েই তিনি শিল্পবিপ্লবের ফসল চলচ্চিত্র মাধ্যমের বুর্জোয়া পরিকাঠামোর বিনির্মাণ করতে চেয়েছেন। আত্মভুবন ও আত্মপাঠের মধ্যে দিয়েই অপরের সঙ্গে ভাববিনিময়ের যে বঙ্গীয় চারুতরিকা, সেই অর্থে ভাণ্ডে যাহা আছে তাহা দিয়েই নিজ সমাজের আখ্যান ও বয়ানকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আর এসব কিছুকে উপজীব্য করেই তিনি আন্তর্জাতিকতা ও বহুজাতিকতায় বঙ্গভাষ্যের জায়গাকে পোক্ত করতে চেয়েছেন সিনে-পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে।
অযান্ত্রিক

জগদ্দল নামক একটি ভাঙাচোরা জিপ গাড়ি ও তার চালক জগদ্দলের সম্পর্ক এবং তার পারিপার্শ্বিক ভূমিমানুষের জগত ইত্যাদিকে ঘিরে ‘অযান্ত্রিক’ ছবিটির কাব্যিক আখ্যান নির্মাণ করেছেন ঋত্বিক। ঋত্বিকের সিনেমার চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রভাষার ব্যবহার এই ছবিটির লেখ্য আখ্যানকে ছাপিয়ে অনেক দূর অবধি নিয়ে গেছে। উল্লেখ্য, এই ছবিটি সুবোধ ঘোষের গল্প ‘অযান্ত্রিক’ অবলম্বনে নির্মিত হয়। আগেই বলেছি মার্ক্স ও ইয়ুং-এর মেলবন্ধন ঋত্বিকের চলচ্চিত্র-অভিসন্দর্ভের গুরুত্বপূর্ণ দিক। আর তাই আর্কিটাইপ ব্যাপারটা ঋত্বিকের ছবির ক্ষেত্রে প্রাণভোমরা হয়ে ওঠে। বিশেষত ‘অযান্ত্রিক’-এর মতো সিনেমার ক্ষেত্রে। ইয়ুং সাহেব জানাচ্ছেন, “Archetype is the word which applied to ideas or forms of natural objects held to have been present in the divine mind to prior to creation and still to exist as cognizable intellect independently of the reality of the ectypal forms/object…’’ The shorter OED, (trans. Onions, T., Oxford University Press)
বঙ্গে যেভাবে বস্তু ও ভাব একীভূত হয়ে আছে, ‘অযান্ত্রিক’ সেই দার্শনিকতাকেও প্রকাশ করে। তাই বিমলকে দেঝা যায় তার গাড়ি জগদ্দলের সঙ্গে সে কথা বলে চলে। জগদ্দল যেহেতু তার পেটে ভাত জোগাড় করে দেয়, তাই সে হয়ে ওঠে অন্নদাত্রী টোটেম। কিন্তু শেষমেশ যন্ত্রের বা বস্তুর অবসান যে নিয়তি এবং এই এক বস্তুর অবসানের মধ্যেই রয়েছে আগামী জীবনের সম্ভাবনা যা ছবির শেষে নিষ্পাপ বাচ্চার সরল হাসির মধ্যে প্রতিভাত হয়।
‘অযান্ত্রিক’-এ বিমল চরিত্রটি প্রকৃত অর্থেই আর্কিটাইপাল। বিমলের মধ্যে দিয়ে আদিম চেতনার প্রকাশ এবং ‘ওঁরাও’দের বৈরাখীনৃত্যে তার প্রতিভাস ও যন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা ইত্যাদি রূপকের মধ্যে দিয়ে আর্কিটাইপাল আইডেন্টিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে জিপ গাড়িটিতে বিমল জ্বালানি তেল ঢালছেন তখন অদ্ভুত এক শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে গাড়ি থেকে, খাবার খাওয়ার পর তৃপ্তির ঢেকুরের মতো। আর ঠিক তার পাশেই গাভীর স্তন থেকে দুগ্ধ পান করছে বাছুর। গাড়ি ও বিমল এবং গাভী ও বাছুর- এই দুটি শটের মধ্যে দিয়ে মা ও সন্তানের সম্পর্ক ও নির্ভরতার এই প্রকাশ ঘটিয়েছেন ঋত্বিক। যা থেকে বিমলের সঙ্গে জগদ্দলের মাতৃভাব (‘মাদার কমপ্লেক্স’) চিহ্নিত হয়। কেন না জগদ্দল যন্ত্র হলেও ‘তিনি’-ই বিমলের অন্নদাত্রী, যেন অন্নপূর্ণা।
একদিকে যন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অন্যদিকে ছবির শেষে যখন যন্ত্রের ক্ষয় নিশ্চিত হয় তখন বিমলের মাধ্যমে দর্শকের মধ্যে যন্ত্রের প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতার বিষয়টাও অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু কালোয়াররা যখন মৃত জগদ্দলকে যখন ঠেলাগাড়িতে করে এগিয়ে নিয়ে চলে ঋত্বিক তখনও জগদ্দলের হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রাখেন।
ছবিতে শেষমেশ যন্ত্রের অবসান হয় কিন্তু একটা শিশুর হাতে বেজে ওঠে হর্ন। নতুন প্রাণস্পন্দনের। আশাব্যঞ্জনার সঞ্চার ঘটে। বিমল চরিত্রটিকে আর্কিটাইপাল ভঙ্গিমায় প্রকাশিত করে এই ছবিতে যন্ত্রসভ্যতার বিপরীতে মানবিক আশাবাদের আলোর জায়গা চিহ্নিত করেছেন ঋত্বিক। কেননা, যন্ত্র ও জীবিতের সম্পর্ক উপমহাদেশে অনেকাংশে বস্তু ও ভাব একীভূত হয়ে থাকার মতো। ‘অযান্ত্রিক’ সেই দার্শনিকতাকেও প্রকাশ করে। তাই বিমলকে দেঝা যায় তার গাড়ি জগদ্দলের সঙ্গে সে কথা বলে চলে। শেষমেশ যন্ত্রের বা বস্তুর অবসান যে নিয়তি এবং এই এক বস্তুর অবসানের মধ্যেই রয়েছে আগামী জীবনের সম্ভাবনা, তাও ছবির শেষে নিষ্পাপ বাচ্চার সরল হাসির মধ্যে প্রতিভাত হয়। ‘ওঁরাও’দের বৈরাখী নৃত্য এই ছবিতে প্রাণপ্রবাহের জীবনচক্রের জৈবিক মেটাফর হয়ে উঠে আসে দর্শকের চোখের সামনে।
মেঘে ঢাকা তারা
নীতার মৃত্যু একদিকে খণ্ডিত বাংলার প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এই সিনেমায়, তেমনই হরগৌরীর মিলনের আখ্যানকে ছবির কাহিনীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করে রাখার মধ্যে দিয়ে বৃহৎ বঙ্গের আত্মভুবন পাঠের মাধ্যমে খণ্ডিত বাংলার সাংস্কৃতিক মিলন ও গণঐক্যের আশাও প্রতিফলিত হয়েছে। ‘দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম’ আকুতি সারা বাংলার গণমানুষের আর্তনাদ, আবার তেমনই নীতার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে হরগৌরীর মিলন আখ্যানের যে মিথ ও তার বিনির্মাণ- পুননির্মাণের মিথিওপিয়া (Mythopoeia) খণ্ডিত বঙ্গের সাংস্কৃতিক পুনর্মিলনের সম্ভাবনার আশাও বপন করে রাখলেন ঋত্বিক।
১৯৪৭ পরবর্তী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খণ্ডিত বাংলায় উদ্বাস্তুজনিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন ঋত্বিক। যদিও এই সিনেমার চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রভাষা মূল কাহিনীকে ছাপিয়ে গিয়ে ভিন্ন তাৎপর্য তৈরি করেছিল। সেটা কীরকম? বাংলার মূল দার্শনিক জায়গাগুলো অর্থাৎ সাংখ্য, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যে যুগল অভিন্নতার ভিতর দিয়ে প্রাণ-প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছিল যা বহিরঙ্গের রূপবৈচিত্র্যের ভিতরে অন্তর্জগতের বিমূর্ত পরমের কথা বলে, সেই সকল দার্শনিকতার প্রাচীন মিথ হচ্ছে ‘হরগৌরীর আখ্যান’। রাধাকৃষ্ণের আইডিয়ার থেকেও বঙ্গে এই হরগৌরী বা অর্ধনারীশ্বরের চিন্তা অনেক প্রাচীন। যা একই সঙ্গে বস্তু ও ভাবের অভিন্নতার ডিসকোর্সকে হাজির করে। বঙ্গে ভাব আর বস্তু আলাদা নয়। ভাব ও বস্তু একে অন্যের সঙ্গে লীলা সম্পর্কের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। ভাব ও বস্তুর মধ্যেকার দ্বান্দ্বিকতাকেই বলা হয় ‘লীলা’। এই লীলার ভিতর মধ্যে দিয়েই ভাব ও বস্তু মিলেমিশে যায়। হরগৌরী কিংবা রাধাকৃষ্ণের মিথ আসলে ওই বস্তু ও ভাবের একাত্মতার মেটাফর। প্রকৃতিস্বরূপার ভিতরে বিমূর্ত, অধরা, অচিন্ত্য যে পরম তা অরূপ। এবং সেটি কর্তা। আর প্রকৃতি হলো শক্তি ও ক্রিয়া।
‘মেঘে ঢাকা তারা’র মূল চরিত্র নীতা। ছবিতে জানা যায় নীতা জন্মেছিল জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। জগদ্ধাত্রী হচ্ছেন জগতের প্রকৃতিস্বরূপা যিনি জগতকে ধারণ করেন। তো নীতা আসলে জগদ্ধাত্রী, কারণ সে তার সংসারকে ধারণ করে রেখেছে। নিজের রূপ-লাবণ্য-স্বাদ-আহ্লাদকে তুচ্ছ করে সে তার বাপ-মা-ভাই-বোনের সংসারের জন্য প্রাণপাত করছে। নীতাকে ছোটবেলা থেকে পাহাড় টানে। এই পাহাড় হচ্ছে লিঙ্গ বা শিবলিঙ্গের মেটাফর। ‘শিব’ যিনি বিমূর্ত। আর শিবলিঙ্গ হচ্ছে গৌরী ও শিবের (হর) মিথুনাযুগল, অনন্ত মৈথুনভাস্কর্য। লিঙ্গ ও যোনি মিলেমিশে থাকে শিবলিঙ্গের ভাস্কর্যে।

তো যাইহোক, এই ছবিতে নীতার যক্ষা ধরা পড়ে, তাকে চিকিৎসার জন্য পাহাড়ে নিয়ে যেতে হয়, সেখানে মৃত্যুই তার পরিণতি। নীতা একদিকে বঙ্গদেশের মেটাফর হয়ে হাজির হন। বাংলাভাগ ও বাংলাকে লুঠপাট করে দেওয়ার মধ্যে যেভাবে এই বঙ্গভূমিকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে তেমনই নীতার পারিপার্শ্বিকতা, পরিজনেরা তার থেকে কেবল নিয়েই গেছে, বিনিময়ে সে কেবল পেয়েছে রোগভোগ, জরাজীর্ণতা। অন্যদিকে বিমূর্ত অরূপরতন পরমের কাছে সত্ত্বার রূপবৈচিত্র্যের সমর্পণের প্রতীক হয়ে উঠেছে নীতা চরিত্রটি। কালিদাস বিরচিত ‘কুমারসম্ভব’-এ যেমনভাবে গৌরী শিবের বিরহে বিবর্ণ অপর্ণায় পরিণত হয়েছিলেন এবং তারপর একসময় যেভাবে হর (শিব) ও গৌরীর মিলন হয়ে তৈরি হয় অভিন্নযুগল রূপ হরগৌরী। নীতার যক্ষা ধরার পর তার পাহাড়ে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার সময় একইভাবে দেখি তার মুখে স্নিগ্ধ-লাজুক হাসি, বাইরে ঝড়–বৃষ্টিপাত, নীতা বুঝতে পেরেছে মহাকাল-রুদ্রের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনের আভাস। তাই তার মুখে প্রেমিকার লাজুক হাসি। নীতা জগদ্ধাত্রী, প্রকৃতিস্বরূপা, তাই সে গৌরীও। গৌরী চলেছেন অভিসারে। পাহাড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যু অর্থাৎ মহাকালের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। মহাকাল অর্থাৎ শিব।
এই ছবির শেষে নীতার মৃত্যু দেখতে গিয়ে কেবল তার কণ্ঠে ‘দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম’- এই বাঁচার আকুতিটুকুই আমরা শুনতে পেয়েছিলাম! এই আকুতি প্রতিধ্বনিত হয়তে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে, চরাচরে, প্যানোরামায়…
নীতার মৃত্যু একদিকে খণ্ডিত বাংলার প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এই সিনেমায়, তেমনই হরগৌরীর মিলনের আখ্যানকে ছবির কাহিনীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করে রাখার মধ্যে দিয়ে বৃহৎ বঙ্গের আত্মভুবন পাঠের মাধ্যমে খণ্ডিত বাংলার সাংস্কৃতিক মিলন ও গণঐক্যের আশাও প্রতিফলিত হয়েছে। ‘দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম’ আকুতি সারা বাংলার গণমানুষের আর্তনাদ, আবার তেমনই নীতার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে হরগৌরীর মিলন আখ্যানের যে মিথ ও তার বিনির্মাণ- পুননির্মাণের মিথিওপিয়া (Mythopoeia) খণ্ডিত বঙ্গের সাংস্কৃতিক পুনর্মিলনের সম্ভাবনার আশাও বপন করে রাখলেন ঋত্বিক।

কোমলগান্ধার
সিনে-আখ্যানের অন্তরালে পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানের বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের সার্থক প্রয়োগ ঋত্বিকের তিনটি ছবিতে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’র ব্যাপারে আলাপ করলাম। বাকি দুটো ছবি, ‘কোমলাগান্ধার’ ও সুবর্নরেখা’।
‘কোমলগান্ধার’-এ এই বিষয়টা প্রকটভাবেই দেখা গেছে। খণ্ডিত বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্মিলনের স্বপ্ন ও আকাঙ্খার সিনেভাষ্য নির্মাণ করতে গিয়ে কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানম শকুন্তলম’-এর আশ্রয় নিয়েছেন। ‘অভিজ্ঞানম শকুন্তলা’তে শকুন্তলার সাথীর নাম অনসূয়া। কিন্তু ‘কোমলগান্ধার’-এর প্রধান চরিত্র অনসূয়াই স্বয়ং শকুন্তলা। এই ছবিটির প্রেক্ষাপট খণ্ডিত বাংলা। আর সিনেমার ন্যারেটিভ অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও তার ভিতরকার পেটিবুর্জোয়া ক্রাইসিস।
‘কোমলগান্ধার’-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র অনসূয়া কমিউনিস্ট ও কালাচারল এক্টিভিস্ট। নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাকে বিদেশে চলে যেতে হবে সবকিছু ছেড়ে, যেভাবে কালিদাসের শকুন্তলাকে তার আশ্রমের গাছপালা, সখী, সাথী ও প্রিয় হরিণশাবককে ফেলে রেখে চলে যেতে হয়েছিল রাজা দুষ্মন্তের কাছে। কিন্তু তাকে বিদেশ যেতে হয় না, বরং তার কমরেড, নাট্য আন্দোলনের সাথী ভৃগুর সঙ্গে প্রণয় সফল হয়। তাদের মিলনেরর মধ্যে দুইয়ে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্মিলনের সম্ভাবনা মূর্ত হয়। বেজে ওঠে বঙ্গদেশের বিয়ের গান, ‘আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া/ আইলেন গো সোন্দরীর জামাই মুটুক মাথায় দিয়া/’’
এই ছবিতে নাট্য আন্দোলন ও নাটকের দল ন্যারেটিভের অংশ। দেখা যায়, দুটি দল যৌথভাবে ‘শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা’ আখ্যানটির নাট্যরূপ প্রযোজনা করছে। ওই নাটকে শকুন্তলা চরিত্রে অভিনয় করবে অনসূয়া। দেখা যায়, যখন মঞ্চে শকুন্তলা চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অনসূয়ার কিছুটা খামতি থেকে যাচ্ছে, তখন ঐ যৌথ নাট্যপ্রযোজনার নির্দেশক ভৃগু (চরিত্রটি ‘কোমলগান্ধার’-এর আরেকটি কেন্দ্রীয় চরিত্র) অনসূয়াকে বলছে, “ইমোশনাল মেমরি ইউজ করো। বাঙালি মেয়েদের তো আটকানোর কথা নয়, বিশেষত এই যুগে— সাতচল্লিশ সালে ফিরে যাও— যেদিন উৎখাত হয়ে চলে আসতে হয়েছিল নিজের বাড়ি ছেড়ে, নিজের চেনাশোনা সবকিছু থেকে— কেন মনে করো না এই কলকাতাই তোমার তপোবন— ওই যে মিছিল চলেছে, ওই যে নবমালিকা, বনজ্যোৎস্না, হয়তো মনে করো কোনো ভিখিরি তোমার কাছে পয়সা চায়— সেই-ই ওই মাতৃহীন হরিণ শিশুটি, ভেবে দ্যাখো আবার যদি এই বাংলাদেশ, এই কলকাতা থেকে তোমাকে চিরকালের মতো চলে যেতে হয়, এই কলকাতার সবকিছু তোমার পায়ে পায়ে আঁকড়ে জড়িয়ে ধবে না?” এই দৃশ্যের সঙ্গে কন্টিনিউটি বজায় রেখে পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায়, একদিকে রাজনৈতিক মিছিল, তার পাশেই রাস্তায় একটি শিশু অনসূয়ার শাড়ির আঁচল টেনে ধরেছে। ঠিক যেভাবে শকুন্তলার পথ আটকে ছিল হরিণশাবক।

এই ছবিতে একদিকে গণনাট্য আন্দোলনের কর্মীদের পাতিবুর্জোয়া রোম্যান্টিকতা ও তার জেরে ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির যেমন চূড়ান্ত সমালোচনা করা হয়েছে, তেমনই খণ্ডিত বাংলার পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধাঔপনিবেশিক সমাজবাস্তবতার অবসান চাওয়া হয়েছে নয়াগণতান্ত্রিক কৃষিবিপ্লবের বার্তা প্রকাশ করে। এই নয়াগণতান্ত্রিক কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমেই দুই বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্মিলন ও জাতীয়-গণতান্ত্রিক পরিসরের ইমেজ গঠনের চেষ্টা চালিয়েছেন ঋত্বিক। ছবিতে যখন অনসূয়ার আঁচল ধরে শিশুটি বলছে, “দিদি আমাকে দুটো টাকা দাও”— তখন দেখা যায় কিয়ারোস্কিউরো আলোয় লো-অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা রেখে মিডশটে এমনভাবে অনায়াসে চিত্রায়িত করা হচ্ছে যেখানে পিছনে একটি বাড়ির খিলানকে দেখে মনে হচ্ছে মূর্তমান কাস্তে। আর তার নীচে অনসূয়া, ফোরগ্রাউণ্ডে ক্ষুধার্ত বাচ্চা।
চিত্রকল্পের মাধ্যমেই অনসূয়া হয়ে উঠলেন গ্রেট মাদার আর্কিটাইপ, কৃষি বিপ্লবের দেবী। এই মেটাফরের প্রকাশ নয়াগণতান্ত্রিক কৃষিবিপ্লবের প্রস্তাব ও প্রস্তবনার ভিতর থেকে এবং খণ্ডিত দুই বাংলার বঙ্গীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক পুনর্মিলনের (সাংস্কৃতিক পরিসরে) স্বপ্ন ও আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে। আর তাই ছবির একেবারে শেষে অনসূয়া ও ভৃগুর যুগল মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের ইমেজে চলচ্চিত্রের সুখী-সমাপন বার্তা নয়, বরং বঙ্গ ঐক্যের ঋত্বিকীয় আকাঙ্খা।
এই ছবিতে একদিকে গণনাট্য আন্দোলনের কর্মীদের পাতিবুর্জোয়া রোম্যান্টিকতা ও তার জেরে ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির যেমন চূড়ান্ত সমালোচনা করা হয়েছে, তেমনই খণ্ডিত বাংলার পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধাঔপনিবেশিক সমাজবাস্তবতার অবসান চাওয়া হয়েছে নয়াগণতান্ত্রিক কৃষিবিপ্লবের বার্তা প্রকাশ করে। এই নয়াগণতান্ত্রিক কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমেই দুই বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্মিলন ও জাতীয়-গণতান্ত্রিক পরিসরের ইমেজ গঠনের চেষ্টা চালিয়েছেন ঋত্বিক।
সুবর্ণরেখা
এই সিনেমার প্রেক্ষাপট বাংলাভাগ। বাংলাভাগের ইতিহআস অতি-পরিচিত। ঔপনিবেশিক শাসন, বাংলাভাগ, উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা শরনার্থীর ঢাল এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে যাওয়া শরনার্থী হিসাবে আরও একদল মানুষের ঢল। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলিমের শিকড়চ্যুত হওয়ার সঙ্কট! ঋত্বিক ঘটকের পরিবারের মতো আরও হাজার হাজার পরিবারকে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়েছিল যেমন, তেমনই পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার বাঙালি মুসলিমকে চলে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। এই ঐতিহাসিক কালখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের আত্মিক ও দার্শনিক সঙ্কটের ইতিবৃত্ত এবং পরিশেষে এখানেও সেই নয়া-স্বপ্নসম্ভাবনার আকাঙ্খা প্রকট করে বঙ্গীয় সিনেমার রাজনৈতিক মহাকাব্য নির্মিত হয়েছে সুবর্ণরেখায়। একইসঙ্গে অনার্য-অবৈদিক নিম্নবর্গের বঙ্গের সমাজ-রাজনৈতিক সিনে-ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছে আর্যীয় টেক্সট রামায়ণের বঙ্গীয় বিনির্মাণে।
বাংলার আবহমানকালের নদীমাতৃক সভ্যতার কৃষিজ জীবনচক্র ও তার প্রাণস্পন্দন এবং জমির উর্বরতাকে তুলে ধরতেই এই কৃষিপ্রজনন তত্ত্বকে প্রাসঙ্গিক মনে করেন ঋত্বিক। বাংলার জমির এই উর্বরতা শাশ্বত জীবন সম্ভাবনা, যা কিনা সামন্ততান্ত্রিক তথা ঔপনিবেশিক শক্তির কারসাজিতে গণমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। বঙ্গের কৃষিদর্শনকে সিনেমায় তুলে এনে ঋত্বিক যে রাজনৈতিক ইশারা পেশ করেছেন তা হলো কৃষিবিপ্লবের প্রস্তাব।
বাংলারে আভমানকালের নদীমাতৃক সভ্যতার কৃষিজ জীবনচক্র ও তাঁর প্রাণস্পন্দন এবং জমির উর্বরতাকে তুলে ধরতেই এই ছবিতে কৃষি প্রজনন তত্ত্বকে প্রাসঙ্গিকভাবে উত্থাপন করেছেন ঋত্বিক। বাংলার জমির উর্বরতা উর্বরতা শাশ্বত জীবন প্রবাহের সম্ভাবনা, যা কিনা সামন্ততান্ত্রিক তথা ঔপনিবেশিক শক্তির কারসাজিতে গণমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই অবস্থায় বঙ্গের কৃষিদর্শনকে সিনেমায় তুলে এনেও কৃষিবিপ্লবের প্রস্তাব পেশ করেছেন ঋত্বিক।
আমরা জানি রামায়ণে সীতা ধরিত্রীকন্যা। তাই সে সকলের কাছে ‘মা’। সুবর্ণরেখার অন্যতম কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রের নাম ‘সীতা’। সুবর্ণরেখার সীতাও অপর আরেক চরিত্র (সীতার বড় ভাই বা দাদা) ঈশ্বরকে বলতে শোনা যায়, “আমি তো তোমার মা”। ছবির দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় সীতার পুত্র বিনুও তার মাকে ‘সীতা মা’ সম্বোধন করছে।
ঈশ্বর যখন সীতা ও অভিরামের পিতার মতো তখন সে একই দেহে সীতার পিতা জনক এবং দশরথ। আবার ঈশ্বর যখন আদর্শচ্যুত হয়ে অবদমিত কামনা-বাসনা ও ভোগবাদী মানসিকতার শিকার হয়ে পতিতাপল্লিতে গিয়ে আবিষ্কার করে নিজের বোনকে তখন সেই আবিষ্কারের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার মধ্যে রাবণ চরিত্র উন্মোচিত হয়। হরপ্রসাদ বিভীষণ, মুখার্জী কালনেমি। আর ঈশ্বর চরিত্রটি যতক্ষণ অবধি সৎ ততক্ষণ অবধি সে দশরথের ইমেজ ক্যারি করেছে। আর সমানে তাকে নানাভাবে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়েছে তার মাড়োয়ারি বন্ধু। উল্লেখ্য এই মাড়োয়ারি-গুজরাতি-হিন্দুস্তানিরাই পশ্চিমবঙ্গের পুঁজি লুঠ করে চলেছে চল্লিশের দশক থেকে এখন অবধি, তাদের কারণেই অবিভক্ত বাংলায় নেমে এসেছিল মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ। তো ওই মাড়োয়ারি বন্ধু চরিত্রটি আসলে রামায়ণের কৈকেয়ির প্রতিফলন। উল্লেখ্য, এই ছবিতে অভিরাম চরিত্রটি আর্য-রামের অনার্য মাইথোপিক বিনির্মাণ। কারণ, অভিরাম নিম্নবর্ণের। রামায়ণের সঙ্গে হুবহু মিল না রেখেও এই ছবির কাহিনী বিন্যাস রামায়ণের আদলকে ধরে একেবারে শেষে দার্শনিকতার স্তরে উন্নীত হয়। ছবির উপকথাবৃত্তিয় পরিণতি নৈরাশ্যজনক-হতাশাব্যঞ্জক সমাজবাস্তবতা অতিক্রম করে স্বপ্নবাস্তবতায় পোঁছায়। সীতার মুখোমুখি বহুরূপীর মধ্যে দিয়ে উগ্রকালীর রূপকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর মাধ্যমে ঋত্বিক যেমন মহাকালের ধ্বংস নিনাদের সুরকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনই ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে এক নিষ্পাপ শিশুপ্রতিমাকে তিনি মূর্ত করলেন, মহাকালের ধ্বংসলীলা ও নবজীবনের প্রাণস্পন্দনের দ্বন্দ্ব সূচিত হলো ছবিতে।

‘সুবর্ণরেখা’য় সীতার আত্মহত্যা, ঈশ্বরের নৈতিক মৃত্যু, বাসদূর্ঘটনায় অভিরামের মৃত্যু, নীতিবাদী হরপ্রসাদের পদস্খলন— এত কিছু নেতিবাচকতার মাঝেও বিনু বেঁচে থাকে। যেন তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের পুনর্জন্ম হয়। মামা ঈশ্বর ভাগ্নে বিনুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুবর্ণরেখা নদীর পাশে নতুন বাড়ির সন্ধানে।
যেখানে—
“আঁকাবাঁকা নদী আর দূরে নীল –নীল পাহাড়, সেইখানে পরিরা ঘুরে বেড়ায় আর গান গায়…”
নতুন বাড়ির সন্ধানে বিনুকে সঙ্গে নিয়ে ঈশ্বরের যাত্রার মধ্য দিয়ে ঋত্বিক মনে করিয়ে দেন যুধিষ্ঠিরের স্বগর্যাত্রার পুরাকথাকে। বিনুর মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তোলেন নবজীবনের বার্তা।
এই ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘শিশুতীর্থ’ কবিতাটির, যা কিনা আবার যীশুখ্রিষ্টের জন্মকথাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা মানব ইতিহাসের ভাষ্য— জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম; চির নতুনের জয়গান। একদিকে রামায়ণে সীতার মিথ অন্যদিকে ‘শিশুতীর্থ’-এর মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের দার্শনিকতায় নদীমাতৃক সভ্যতার কৃষিপ্রজনন তত্ত্ব বা ফার্টিলিটি কাল্টের ডিসকোর্সকে তুলে আনলেন ঋত্বিক। যার মূল কথা হলো, ‘জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের মাধ্যমে সৃষ্টি তথা প্রাণের লীলা ও প্রবাহমানতা’। বাংলার আবহমানকালের নদীমাতৃক সভ্যতার কৃষিজ জীবনচক্র ও তার প্রাণস্পন্দন এবং জমির উর্বরতাকে তুলে ধরতেই এই কৃষিপ্রজনন তত্ত্বকে প্রাসঙ্গিক মনে করেন ঋত্বিক।

তিতাস একটি নদীর নাম
ঋত্বিক বলছেন, “নদীমাতৃক সভ্যতা আমাদের পূর্ববাংলা। তোমরা পূর্ব বাংলাকে কতটা দেখেছ আমি জানি না, কতটা গভীরে ঢুকেছ তাও জানি না।আমি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে গভীরে ঢুকেছি। তিতাস একটি নদী— এই নদী হচ্ছে সাস্টেইনিং ফোর্স। সেই নদীটা শুকিয়ে যাচ্ছে; তারপর সে নদী শুকিয়েও গেল! তখন নদীর মধ্যে যে জমিটা জেগে উঠলো তা আর জেলেদের থাকলো না। চাষীরা ফোরফ্রন্টে চলে এলো… সভ্যতার মৃত্যু নেই। সভ্যতা পরিবর্ধিত হয়। কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের, সেখানে তিতাসের ধানের ক্ষেত জন্মেছে। আরেকটা সভ্যতার সূচনা হচ্ছে’’- (সাক্ষাৎকার, ঋত্বিক ঘটক, ‘চিত্রবীক্ষণ’)।
অদ্বৈত মল্লবর্মনের উপন্যাস ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এর কাহিনী সবারই জানা। তিতাসকে কেন্দ্র করে মালোদের জীবনচর্যা, উচ্চবর্ণীয়দের শোষণ, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এই ছবির আখ্যানের আউট লাইন। ঋত্বিক এই ছবিতে উপন্যাসের ডিটেলিংকে ফলো করেছেন। কিন্তু এপিকধর্মী উপন্যাসের শেষে যে সভ্যতার মৃত্যু, নিরাশার অন্ধকার ব্যপ্ত হয়েছে, ঋত্বিক তাকেই দাঁড় করালেন আশার আলোর সামনে। ছবির শেষে দেখা গেল, তিতাস শুকিয়ে গেলেও তার চরে জন্ম নিয়েছে ধানের চারা। অর্থাৎ নদীমাতৃক সভ্যতার মৃত্যু নেই। ঋত্বিক বলছেন, “নদীমাতৃক সভ্যতা আমাদের পূর্ববাংলা। তোমরা পূর্ব বাংলাকে কতটা দেখেছ আমি জানি না, কতটা গভীরে ঢুকেছ তাও জানি না। আমি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে গভীরে ঢুকেছি। তিতাস একটি নদী— এই নদী হচ্ছে সাস্টেইনিং ফোর্স। সেই নদীটা শুকিয়ে যাচ্ছে; তারপর সে নদী শুকিয়েও গেল! তখন নদীর মধ্যে যে জমিটা জেগে উঠলো তা আর জেলেদের থাকলো না। চাষীরা ফোরফ্রন্টে চলে এলো… সভ্যতার মৃত্যু নেই। সভ্যতা পরিবর্ধিত হয়। কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের, সেখানে তিতাসের ধানের ক্ষেত জন্মেছে। আরেকটা সভ্যতার সূচনা হচ্ছে’’- (সাক্ষাৎকার, ঋত্বিক ঘটক, ‘চিত্রবীক্ষণ’)।
নদীমাতৃক সভ্যতা থেকে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা আর তার ফার্টিলিটি কাল্টকে এই চলচ্চিত্রে প্রকাশ করলেন ঋত্বিক।। ছবিতে অনন্তর মুখে শোনা যায় ‘ভগবতী সবার মা’, এই ভগবতী গ্রেইট মাদার আর্কিটাইপ যা নদীমাতৃক সভ্যতার প্রতিমাস্বরূপা।

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো
‘নিম্নমধ্যবিত্ত মাতাল, পচে যাওয়া সমাজের বুদ্ধিজীবী’ নীলকন্ঠ বাগচীর মধ্য দিয়ে পর্দা জুড়ে ঋত্বিক বানালেন সেলফ-পোস্টমর্টেম, পার্সোনাল ফিল্ম ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো। তবে এই ছবিকে পার্সোনাল ফিল্ম’ বলা হলেও এই আত্মবিশ্লেষণকে যদি যৌথ সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণের নিরিখে দেখা যায়, তবে এই ছবি আর পার্সোনাল নয়, বরং ৬০-৭০ দশকের পশ্চিমবঙ্গ-সহ বৃহত্তর বঙ্গদেশের চ্ছিন্নমূল আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের নন-ন্যারেটিভ সিনে-প্রোজেক্ট। ধীমান দাশগুপ্তের মতো চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের এমনটাই অভিমত। ঋত্বিকের রাজনৈতিক তথা দার্শনিকচিন্তার বিশেষ নজির এই ছবি। কারণ, এই ছবিতে রাজনৈতিক পোস্টমর্টেমের অন্তরালে দর্শন মিশেছে যথারীতি মহাকাব্যিক আঙ্গিকে ও লৌকিক আখ্যানের ভঙ্গিমায়।

নীলকন্ঠ বাগচী যে কিনা মদ খাওয়ার জন্য মিথে কথা বলতে পারে, এমনকি চুরি করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নয়, সে কিন্তু নিজস্ব নাম-বল ও আর্থিক প্রতিপত্তির জন্য একটাও মিথ্যা কথা বলতে রাজী নয়। সে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার মদ্যপানের অব্যাসের জন্য তার স্ত্রী দুর্গা তাকে ছেড়ে গেছে। তার সঙ্গী হয়েছে সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা বেকার যুবক নচিকেতা ও উদ্বাস্তু ধর্ষিতা যুবতী বঙ্গবালা এবং আরেক উদ্বাস্তু জগন্নাথ মাষ্টারমশাই।
নীলকন্ঠ তার একদা বন্ধু, বুদ্ধিজীবী শত্রুজিৎ প্রসঙ্গে বলে, ‘এক সময় প্রগতির কথা বলে শিল্পীজীবন শুরু করেছিল, এখন পোকামাকড়, পর্নগ্রাফি এইসব বেচে খায়!’ এভাবেই ঋত্বিক তার পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে দ্রোহ তৈরি করেছেন। আর বঙ্গবালা আসলে অখণ্ড বঙ্গদেশের প্রতীক। সাতচল্লিশ এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে একভাবে বঙ্গদেশ ধর্ষিত ও রক্তাক্ত হয়েছে। তার ফলঃশ্রুতিতে অখণ্ড বঙ্গসন্তান নীলকন্ঠ বাগচী তথা ঋত্বিক ঘটকের জীবনে নেমে এসেছে নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য। কিন্তু এই নৈরাশ্য আর নৈরাজ্যের পরিকাঠামোয় নিজেকে বেঁধে ফেলতে চাননি ঋত্বিক। আর তাই শহরকে ছাপিয়ে গিয়ে ছবিতে ফুটে এসেছে নিম্নবর্গের গ্রামবাংলা। মাধব সর্দারের গ্রামে মূর্ত হয়েছে ভূমিহীন কৃষকের জমির লড়াই। সিনেমা ফিকশনাল ন্যারেটিভকে ছাপিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় হয়ে উঠেছে প্রামাণ্যচিত্রমালা। জমির লড়াই দেখাতে গিয়ে কৃষকের দ্রোহকে আর্কিটাইপাল ভঙ্গিতে চিত্রায়িত করা হয়েছে বীররসে পরিপূর্ণ রাঢ়বঙ্গের ছোনাচে।
বঙ্গবালাকে ছৌ-এর মুখোস হাতে দ্রোহপ্রতিমার রূপ দেওয়া হয়েছে ছবিতে। বৈদিক, ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের ঘেরাটোপ থেকে বঙ্গবালাকে ( বাংলার মেয়েদের এবং গোটা বঙ্গদেশকে) বের করে আনতে নিম্নবর্ণের মাধব সর্দারের মুখে সংলাপ বসানো হয়েছে, “লাচো (নাচো) তোমরা না লাইচলে কিচ্ছুটি হওয়ার নয়’। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার মাদার কমপ্লেক্স-এর ইয়ুং চিন্তার সঙ্গে মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মেলবন্ধন এই ছবিতে চূড়ান্ত আকার নিয়েছে। একদিকে জমির লড়াই, অন্যদিকে ছৌ-এর মুখোস হাতে বঙ্গবালার ঋজু চেহারা। এমনকি এই ছবিতে সংস্কৃত ভাষা ও তত্ত্বে শিক্ষিত জগন্নাথ মাষ্টারের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মাধব সর্দারের তর্কের অবতারণা করে ব্রাহ্মণ্যবাদকে খারিজ করতে চেয়েছেন বঙ্গীয় নিম্নবর্গীয় ভূমি-অভিসন্দর্ভ থেকে। জগন্নাথ মাষ্টার যখন বৈদিক পুরাণের প্রসঙ্গ তোলে তখন মাধব সর্দার বলে, “যে মাকে মা ডাকতে পারে না সে হচ্ছে বিদেশী… পুরাণ আবার কী? মা পুরানা হবে কেন? সে সবসময় নতুন!’

এই ছবিতে ভারতীয় রাষ্ট্রবাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো নকশালবাড়ির গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গী হয়েছেন ঋত্বিক। কিন্তু ইউরোপের সমাজবাস্তবতা ও তাদের অগ্রসরতার ইতিহাসকে আমদানি করে এনে ইউরোসেন্ট্রিক চোখ দিয়ে বাংলার সমাজবাস্তবতা ও ইতিহাসপর্যালোচনা যে করা যাবে না, তা স্পষ্টভাবে নীলকন্ঠ বাগচীর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন ঋত্বিক।
কৃষিভিত্তিক সভ্যতার মাদার কমপ্লেক্স-এর ইয়ুং চিন্তার সঙ্গে মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মেলবন্ধন এই ছবিতে চূড়ান্ত আকার নিয়েছে। একদিকে জমির লড়াই, অন্যদিকে ছৌ-এর মুখোস হাতে বঙ্গবালার ঋজু চেহারা। এমনকি এই ছবিতে সংস্কৃত ভাষা ও তত্ত্বে শিক্ষিত জগন্নাথ মাষ্টারের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মাধব সর্দারের তর্কের অবতারণা করে ব্রাহ্মণ্যবাদকে খারিজ করতে চেয়েছেন বঙ্গীয় নিম্নবর্গীয় ভূমি-অভিসন্দর্ভ থেকে।
লোকায়ত জীবনচর্যা, মার্ক্স-ইয়ুং, বুর্জোয়া এনলাইটেনমেন্টের সমান্তরাল বঙ্গযাপন ও কার্নিভালিস্ট দ্রোহ
ঋত্বিক ঘটকের ছবি থেকে লোকায়ত জীবনচর্যার যে ভাষ্য তৈরি হয় তা ইউরোপীয়ান সমাজ পর্যালোচনার পয়েন্ট অব ভিউ থেকে তৈরি হওয়া বস্তবাদী বিবেচনা নয়। বরং মার্ক্স ইউরোপীয়ান সমাজের ইতিহাসের গতিপ্রবাহের যেভাবে অবসান চেয়েছে, সেভাবেই মার্ক্সীয় বস্তুবাদের সেই স্পিরিটটাকে ধরে রেখে বঙ্গীয় তথা উপমহাদেশীয় আত্মভুবনের সমান্তরাল সমাজ পর্যালোচনা ভিতর থেকে ঔপনিবেশিকতা ও তার পৃষ্ঠপোষকতায় অনড় সামন্তবাদ ও সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের বিরুদ্ধে দ্রোহচিত্র নির্মাণ করে গেছেন ঋত্বিক।
অনেক চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ঋত্বিকের ছবির মধ্যে ‘ভাববাদ’ খুঁজে পান! এর উত্তরে পালটা প্রশ্ন উঠে আসে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মোটাদাগের রাজনৈতিক প্রয়োগে অর্থনীতিকেই সমাজ পর্যালোচনা ও পরিবর্তন ভাবনায় মূল কেন্দ্র হিসাবে দাঁড় করানো এবং কেবলামত্র বস্তুগত স্বার্থের সীমাবদ্ধতায় মানবজীবনকে আটকে রাখার মতো বিষয় কতটা মার্ক্সীয়? লেনিনও তাঁর ‘কী করিতে হবে’ নামক পুস্তকের ‘রাজনৈতিক আলোড়ন ও এবং অর্থনীতিবাদীদের দ্বারা রাজনৈতিক সংকোচন’ বিষয়ক আলাপে এই বিষয়টাতেই আলোকপাত করেছ্ন এবং এই অতি-অর্থনীতিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। নিও-মার্ক্সিস্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সমাজবিজ্ঞানী এরিক ফ্রমও মনে করেন, ‘ধনতন্ত্রের এবং সমস্ত কায়েমী শক্তির প্রভাবেই এই বস্তুগত স্বার্থের সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। মার্ক্স আসলে বিশ্বাস করতেন, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিশেষ বিশেষ কৌশলে মানুষকে বাধ্য করে বস্তুগত স্বার্থবাদে অন্য কোথাও না তাকাতে!’ প্রতিযোগিতা, শোষণ ও শত্রুতা, আধিপত্য ইত্যাদি বিনাশের স্বপ্নই মার্ক্স দেখিয়েছেন। এই ধরণের নির্ভরতা থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। জার্মানির নিও-মার্ক্সিস্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ধনতন্ত্রের ক্ষতিকারক দিক হিসাবে সম্পদের অসম বন্টনের পাশাপাশি মানবিকবোধের ধ্বংসসাধনকেও চিহ্নিত করেছেন, সেভাবেই আমরা দেখতে পাই ঔপনিবেশিক শাসন, আধুনিকতা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চূড়ান্ত ক্রিটিক করতে গিয়ে বিকল্প প্রস্তাবনায় ঋত্বিক শাশ্বত বঙ্গযাপনকে তুলে আনছেন, ইউরোপীয়ান যুক্তিকাঠামোয় সমাজপর্যালোচনা ও বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে দাঁড়িয়ে।
এটা করতে গিয়ে ঋত্বিক যেমন মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নন্দনতাত্ত্বিক পরিকাঠামোর দ্বারস্থ হয়েছেন, ঠিক তেমনই প্রত্নখনন করে নিজের সমাজের লোকায়ত সভ্যতার বিস্তার ও বিবর্তনের মধ্যে থেকে সাংস্কৃতিক চিহ্নকে তুলে এনেছেন, যেসব চিহ্ন, মেটাফর, ইঙ্গিত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির চাপে পড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেছিল। এজন্য ইয়ুং-এর ‘যৌথ নির্জ্ঞান’ তত্ত্ব ঋত্বিকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি, উপনিবেশবাদ যতই একটা সমাজের নিজস্ব দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো ও প্রকরণকে গায়েব করে দিক না কেন, তা থেকে যায় সমষ্টির নির্জ্ঞানে। সূর্য, নদী-খাল-বিল-হাওর-সমুদ্র-অরণ্যমুখরিত বঙ্গের লোকজগত ও যৌথ নির্জ্ঞানকে ধরতে ঋত্বিক ওই কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর সূর্য উপকথা তত্ত্বের জন্মচক্রের ধারণাকে সম্বল করে কৃষিপ্রজননভাব বা ফার্টিলিটি কাল্টকে প্রকাশ করেছেন কৃষিবিপ্লবের প্রস্তাব রাখতে। ইয়ুং-এর তত্ত্বের প্রকরণ অনুধাবন করলে অবশ্যই এই মনোবিশ্লেষককে ভাববাদী বলে মনে হতে পারে। কিছুটা তাই। কিন্তু ঋত্বিক মোটেও ইয়ুংকে এককভাবে তার চলচ্চিত্র অভিসন্দর্ভের উপাদানে গ্রহণ করেননি। বরং যৌথনির্জ্ঞান তত্ত্ব, ফার্টিলিটি কাল্ট ও গ্রেইট মাদার আর্কিটাইপের ধারণাগুলির প্রয়োগ করেছেন বঙ্গীয় ইতিহাস ও সমাজচেতনার প্রেক্ষিতে এবং মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের যুক্তিকাঠামোর সঙ্গে নিজের মতো করে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার মাধ্যমে। তাছাড়া ইয়ুং-এর সঙ্গে ঋত্বিক সম্ভবত এই ব্যাপারে একমত— পশ্চিমা আলোকায়ণের বা দীপায়ন পর্বের যুক্তিকাঠামো মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা/ পরিচিতিকে গুরুত্ব দেয় না। প্রাণ ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে খারিজ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়ুং স্পষ্টতই বলছেন যে এনলাইটেনমেন্ট এবং তার যুক্তিবাদের বিরাট ফাঁক ছিল। ইয়ুং বলছেন, ‘The mere act of an enlightenment have destroyed the spirit of nature, but not the psychic factors that correspond to them, such suggestibility lack of criticism, fullness fear propensity to superstition and prejudice in short, all those qualities which makes possession possible. Even though mature is depschychized the psychic conditions which breed demons are as actively at work as ever,’ (‘After the Catastrophe’, ‘Essays on Contemporary Events’- C.G Jung)।
অনেক চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ঋত্বিকের ছবির মধ্যে ‘ভাববাদ’ খুঁজে পান! এর উত্তরে পালটা প্রশ্ন উঠে আসে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মোটাদাগের রাজনৈতিক প্রয়োগে অর্থনীতিকেই সমাজ পর্যালোচনা ও পরিবর্তন ভাবনায় মূল কেন্দ্র হিসাবে দাঁড় করানো এবং কেবলামত্র বস্তুগত স্বার্থের সীমাবদ্ধতায় মানবজীবনকে আটকে রাখার মতো বিষয় কতটা মার্ক্সীয়?
ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক অ্যাডোর্না ও হর্কহেইমারও ‘ডায়ালেকটিক অব এনলাইটমেন্ট’ বইতে আলোকায়ন বা দীপায়ন প্রকল্পের সমালোচনা করেছেন। কারণ, দীপায়ন মানুষকে জ্ঞানতত্ত্বের সন্ধান দেওয়ার নামে প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে শেখালো মানুষকে, আর এই ক্রমাগত প্রকৃতির ওপর মানব নিয়ন্ত্রণের ফলাফল হলো প্রকৃতি থেকে মানবসভ্যতার বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতাকে সামনে রেখেই দীপায়ন বা এনলাইটেনমেন্ট তার বুর্জোয়া দার্শনিক পরিকাঠামো থেকে জ্ঞান ও সংস্কৃতির মধ্যে কৃত্রিম ঐক্য।
উপনিবেশবাদের ক্রিটিকের অন্তরালে, বাংলা তথা উপমহাদেশের চিন্তা জগত ও নন্দনতাত্ত্বিক পরিকাঠামো থেকে পশ্চিমা এনলাইটেনমেন্টের যুক্তি পরিকাঠামো ও তার বুর্জোয়া দর্শনচিন্তা ও নন্দনচিন্তাকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন ঋত্বিক। সে কারণেই ঋত্বিকের ছবিতে বারবার সামনে উঠে এসেছে প্রান্তিক জীবনচর্যা, অরণ্যমুখরতা, লোকসমাজের যৌথনির্জ্ঞান, উপমহাদেশীয় মহাকাব্য ও তার বঙ্গীয় বিনির্মাণ, লোকায়ত ভাবচর্যা, ফকির-দরবেশ-মুর্শিদি গান, লোকনৃত্য ইত্যাদি। পশ্চিমা চিন্তা জগতের সমান্তরালে বঙ্গীয় তথা উপমহাদেশীয় সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো বহুমুখী স্বতন্ত্র ধারায় যে প্রবাহমান তা ঋত্বিক মনে করিয়ে দিয়েছেন বারবার। ঔপনিবেশিক শাসন ও তার পরিণতিতে বাংলা ভাগ এবং তারপর ভারত জুড়ে, ভারতের অন্তর্গত বাংলা জুড়ে যে আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো মূলবাসী ও ভূমিমানুষকে ক্রমশই প্রান্তিকতার মধ্যে ঠেকে দিয়েছে ঋত্বিক তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছেন। এবং একই সাথে খারিজ করতে চেয়েছেন বৈদিক/ আর্যীয়/ ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিকে যা ভূমিচেতনার বিরোধী, কেননা এরাও বহিরাগত।
যেভাবে মিখাইল বাখতিন দেখিয়েছেন মধ্যযুগের ইউরোপে রাষ্ট্র, পুরোহিতন্ত্রের খচিত সরকারী বয়ান ও সামন্ততান্ত্রিক বিধির বিপ্রতীপে অপ্রাতিষ্ঠানিক লোকায়ত জীবনচর্যার কার্নিভাল থেকে থেকে বারবার উঠে এসেছে প্রত্যাঘাত, “During the century long development of medieval carnival, prepared by thousands of year of ancient comic, ritual including the primitive Saturnalia, a special idiom of forms and symbol were evolved— an extremely rich idiom that expressed the unique yet complex Carnival experience of people.” (‘Rabelais and his World’- Mikhail Bakhtin)। সরকারি প্রাতিষ্ঠানিকতার সমান্তরাল লোকায়ত স্তরের জীবনচর্যা থেকে যে সংস্কৃতি, লোকাচার-উপাচার হাসি-গান, প্যারোডি, কৌতুক উঠে আসে তা প্রতিষ্ঠানিকতার প্রতি লোকায়ত দ্রোহ। বাখতিন আরও বলছেন, ধনতান্ত্রিক যুগের পরিশীলিত-বৌদ্ধিক পাঠকৃতিতেও এ ধরনের কার্নিভালিয় প্রত্যাঘাত দেখা যায়। এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় সরকারী আধিপত্য আর আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা প্রসঙ্গেও বাখতিন জানিয়েছেন, দমনমূলক পরিস্থিতির অবসানের লক্ষ্যে, কানির্ভাল বাস্তবতার পালটা বয়ান তৈরি করে। মনে রাখা দরকার, মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের বিরোধিতা আসলে বাখতিন করেননি, বরং তাকে আরও পূর্ণতর করে তোলায় জন্য লোকসমাজের সমান্তরাল বয়ানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
তেমনই ঋত্বিকের ছবিতে লোকায়ত জীবনচর্যা, আদিবাসী জীবন খুব বেশী করেই এক লৌকিক কার্নিভাল-পলিটিক্সের সম্ভাবনা ও তার অস্তিত্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষত ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ ছবিতে লোকায়ত প্রত্যাঘাতে চলচ্চিত্র নির্মানের প্রাতিষ্ঠানিক যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ততার বিপরীতে আসলে তথাকথিত ত্রুটিপূর্ণ পরিকাঠামোয় প্রান্তিক জীবনের ভিতর দিয়ে প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামো এবং তার ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। ‘অযান্ত্রিক’-এ যন্ত্র ও যুক্তির পারষ্পরিক ঔপনিবেশিক গতির বিপরীতে লোকায়ত-আদিম জনসমষ্টির জীবনস্পন্দন ফুটে ওঠে। এমনকি ‘সুবর্ণরেখা’য় ঈশ্বরের স্খলন ও তার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা ভোগবাদী সংস্কৃতি ঔপনিবেশিক শোষণের ফলশ্রুতি। যেই শোষণের আর এক ফলাফল শিকড়বিচ্ছিন্ন উদ্বাস্তু শরনার্থীর ঢল। ঐ ছবির শেষ দৃশ্যে নতুন বাসস্থানের সন্ধানে নবজন্মের মেটাফর লোকায়ত প্রত্যাঘাত চিন্তারই প্রকাশ। ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’তে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে বিশেষ নৃত্যরীতির মাধ্যমে তুলে ধরার বিষয়টাও আসলে রাজনৈতিক স্থবিরতায় বাখতিনীয় বয়ানের মতো লৌকিক প্রত্যাঘাতের ব্যঞ্জনা। ক্যামেরার লেন্সে বাংলা মদ ঢেলে দেওয়াও কার্নিভালীয় বিদ্রোহের প্রকাশ একপ্রকার।

অতএব ঋত্বিকের লোকায়ত ভাবনার অন্তরালে যে রাজনৈতিক বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে তা থেকেই উঠে এসেছে ঔপনিবেশিক ও বহিরাগত সংস্কৃতি, বুর্জোয়া যুক্তিবাদের সমান্তুরালে বঙ্গীয় দেশজ লৌকিক জনজীবনের জীবনবোধের ভাষ্য। এবং এই ভাষ্যে প্রতিফলিত ফার্টিলিটি কাল্টের মাধ্যমে কৃষিবিপ্লবের প্রস্তাব, অনার্য বৃহৎ বঙ্গীয় জনজীবনকে উপমহাদেশীয় জীবনচর্যার আধার হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা। এটাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ও তার সংস্কৃতির সমান্তরালে বঙ্গীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চলচ্চিত্রায়িত অভিসন্দর্ভ, যা নির্মাণ করে গেছেন ঋত্বিক, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঋত্বিকের একটি সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। ঋত্বিকের নিরপেক্ষ পর্যালোচনায়, যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করা উচিত।

তেমনই ঋত্বিকের ছবিতে লোকায়ত জীবনচর্যা, আদিবাসী জীবন খুব বেশী করেই এক লৌকিক কার্নিভাল-পলিটিক্সের সম্ভাবনা ও তার অস্তিত্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষত ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ ছবিতে লোকায়ত প্রত্যাঘাতে চলচ্চিত্র নির্মানের প্রাতিষ্ঠানিক যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ততার বিপরীতে আসলে তথাকথিত ত্রুটিপূর্ণ পরিকাঠামোয় প্রান্তিক জীবনের ভিতর দিয়ে প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামো এবং তার ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়।
সীমাবদ্ধতা
কবি ও চিন্তাবীদ ফরহাদ মজহার সর্বপ্রথম ঋত্বিকের এই সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকে চিহ্নিত করেন তাঁর একটি ফেসবুক পোস্টে। তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন তা হলো, ঋত্বিকের ছবিতে বঙ্গীয় লোকায়ত ও নিম্নবর্গীয় প্রেক্ষাপট ফুটে উঠলেও সেখানে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক চিহ্ন অনুপস্থিত। ঋত্বিকের ব্যাপারে এই সমালোচনা একশো শতাংশ যুক্তিযুক্ত। ফকিরি গান বা ‘দোহাই আলি’ সংলাপ এইগুলো বাদে বঙ্গের বৃহৎ বাঙালি মুসলমান জনসমষ্টির চিহ্ন অনুপস্থিতই থেকে গেছে। অথচ ঋত্বিক নিজে বলছেন, বাংলা ভাগ হওয়ার পেছনে ঔপনিবেশিক শাসন যেমন দায়ি তেমনই পূর্ব বাংলার বাবু বাঙালি বর্ণহিন্দুদের অস্পৃশ্যতার সংস্কৃতিও দায়ি। অথচ এ কথা বলার পরেও তাঁর ছবিতে বাঙালি মুসলমানের অন্তর্জগত প্রকাশিত হলো না কেন, সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তিনি কেন কেবল সনাতনী মিথ নিয়েই কাজ করলেন?

পরিশেষে এর পেছনে যুক্তি খুঁজতে গিয়ে ঋত্বিককে সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। কারণ তিনি আর্যীয় বা বৈদিক সাংস্কৃতিক প্রকরণকে বিনির্মাণ করেছেন অনার্য নিম্নবর্ণের সংস্কৃতি জগিতে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের জগত উঠে আসেনি। এর কারণ বোধহয়, ঋত্বিককে পূর্ব বাংলা ছেড়ে যেকোনো কারণেই চলে আসতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। এবং পশ্চিমবঙ্গের মনোজগতকে ধরতে গিয়ে তিনি সনাতনী সংস্কৃতি ধারার ভিতর দিয়েই আর্যতত্ত্বের বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন। তাঁর স্বল্প জীবন যদি আরো কিছুদিন সময় পেতেন অন্য কিছু দেখার সম্ভাবনাও হয়তো থাকতো বৃহৎ বঙ্গের দর্শক সমাজের। কিন্তু তিনি তাঁর শেষ ছবি যুক্তি-তক্কোতে যেভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, তাও কম কথা নয়।
ঋত্বিক নিজে বলছেন, বাংলা ভাগ হওয়ার পেছনে ঔপনিবেশিক শাসন যেমন দায়ি তেমনই পূর্ব বাংলার বাবু বাঙালি বর্ণহিন্দুদের অস্পৃশ্যতার সংস্কৃতিও দায়ি। কিন্তু তারপরেও তার ছবিতে বাঙালি মুসলমানের অন্তর্জগত প্রকাশিত হলো না। এটা দুঃখজনক। অথচ ঋত্বিক কেবল সনাতনী মিথ নিয়েই কাজ করলেন।
অন্যদিকে, ঋত্বিকের ওপর ফ্যাসিবাদী তকমা চাপানো্র বিরুদ্ধে বা তাঁকে বিকৃত করে যেভাবে তাঁকে ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক হিসাবে দাঁড় করানোর নয়া-প্রচারণা পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে, সেটাও ভুয়া। কারণ জাতীয় সমাজবাদের স্লোগানের আড়ালে লোকায়ত বৈচিত্র, নিম্নবৈর্গীয় যাপন ও খেটে খাওয়া মানুষের হককে খারিজ করে ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ, কিন্তু ঋত্বিক দাঁড়িয়েছেন এর বিপরীতে, তিনি না তো বাঙালি জাতিবাদের কথা বলেছেন, না তো নিজেকে হিন্দু পুনরুত্থান প্রকল্পের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের তাত্ত্বিক হিসাবে করেছেন, বরং নাগরিক বিস্মৃতি আড়ালে হারিয়ে যাওয়া লোকসভ্যতার মাধ্যমে ঋত্বিক এক বঙ্গীয় গণমুক্তির সম্ভাবনা হদিশ দিয়েছেন কৃষিবিপ্লব প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে। ঋত্বিকের সিনেমার ফ্রেমিং ও কম্পোজিশনে যেরকম অ্যাসেন্ট্রিক ফ্রেমিং ও ডেফথ অব ফিল্ড প্রত্যক্ষ করা যায়, যেভাবে লোকায়ত বঙ্গের মানসপ্রতিমার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে তিনি লো-অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা রেখে চরিত্রগুলিকে করে তোলেন আইকনিক, আর্কিটাইপাল, জীবন্ত-কিংবদন্তী, সেভাবেই ঋত্বিকের দার্শনিক ও রাজনৈতিক অবস্থান হেজিমনির বিরুদ্ধে, কেন্দ্রিকতার বিপরীতে বিকেন্দ্রিকতায় এবং তাই তাঁর ছবির আখ্যান ও চরিত্রায়ণে ফুটে ওঠে ভূমিবাংলা ও বঙ্গের ভূমিসম্পৃক্ত নিম্নবর্গের বাঙালি, আদিবাসী প্রমুখেরা যারা বৈচিত্র্যপূর্ণ বঙ্গযাপনের নানা রঙের মানুষ। ঋত্বিকের ছবিতে এই সকল প্রান্তিক আমজনতা লো- অ্যাঙ্গেলে হয়ে ওঠেন আর্কিটাইপাল, লোকেশ্বর। ঋত্বিক মানুষের এবাদতে মাতেন। আর সেই এবাদতের মন্ত্র/ আয়াত হয়ে ওঠে কৃষিবিপ্লবের সুর।
আজকের সময়ের প্রেক্ষিতেও কৃষিবিপ্লবের এই প্রস্তাব নয়া উদার গায়েবী লগ্নিপুঁজি প্রযোজিত হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানি জাতিবাদের সমান্তরালে বৃহৎ বঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐক্যের সম্ভাবনার যে চর্চা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমরা ঋত্বিকের সীমাবদ্ধতার জায়গাটুকুর কথা মাথায় রেখেই বাংলার অনার্য সনাতনী ধারা, বাংলার ইসলাম ও বাংলার লোকায়ত ভূমিমানুষের জগতকে একত্রিত করে নির্মাণ করতে পারি বৃহৎ বঙ্গের বহুত্ববাদী জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির যৌথপ্রস্তাব। যা বড় বাংলার মানুষ ভজনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সিনেমাতে মানুষই শেষ কথা বলে।
গ্রন্থসূত্র
১। ‘চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু’, ঋত্বিক ঘটক
২। ‘অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট’, ঋত্বিক ঘটক
৩। ‘ঋত্বিক: পদ্মা থেকে তিতাস’, সুরমা ঘটক
৪। ‘ঋত্বিক চলচ্চিত্রকথা’, বাঁধন সেনগুপ্ত
৫। ‘স্বগত ইউলিসিস’, কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং
৬। ‘ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ও মার্ক্সবাদ’, সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। ‘Marxist Cultural Movement in India’, Sudhi Pradhan
৮। ‘The shorter OED’, C.G Jung (trans. Onions, T.)
৯। ‘The Ideological Stuggle and Literature’, Albart Belysev
১০। ‘Rabelais and his World’, Mikhail Bakhtin
অতনু সিংহ
কবি, গদ্যকার। ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক।