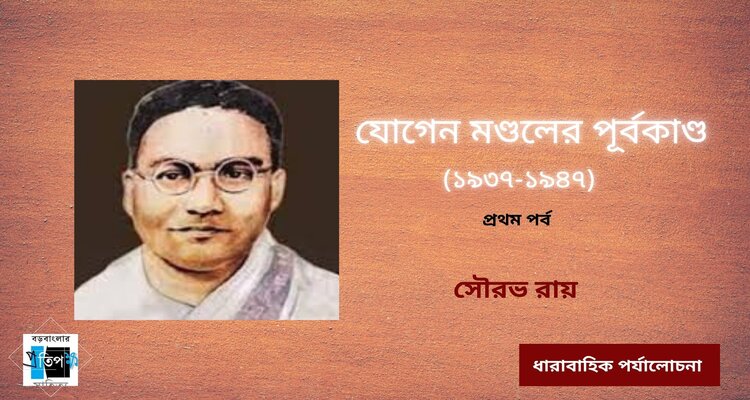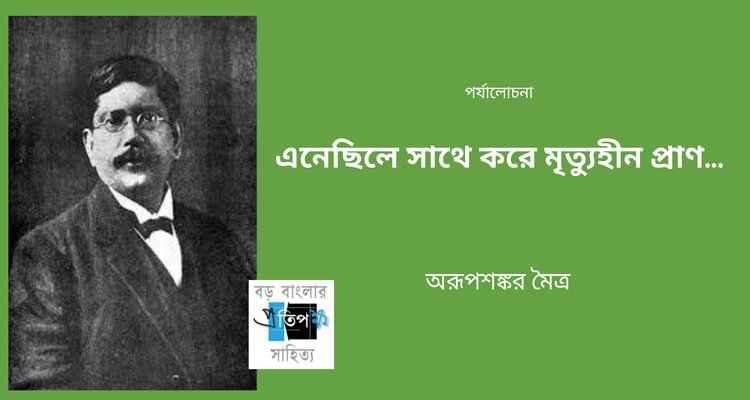
।। অরূপশঙ্কর মৈত্র ।।
বাংলায় মুসলমানদের নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ কেননা, তাঁরা প্রশাসনের নানা জায়গায় ঠিকঠাক প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছেন না। তার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম হল সার্বজনিক ভোটাধিকার না থাকা। ভোটের অধিকারের সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে যুক্ত করা আছে। বাংলায় অধিকাংশ মুসলমান তথাকথিত রাষ্ট্রীয় লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত, তারা মারাত্মক দরিদ্র। ফলে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় থাকেই না। এটা দেশের অন্য অঞ্চলগুলোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু তাই নয়। এখানকার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জগতও বাঙালির মতই। ঠিক মুসলমান প্রধান অংশ নিয়ে দেশ ভাগ হলে যে বিড়লাদের কোনও অসুবিধে হবে না, তা বিড়লারা জানত। হিসেবও দিয়েছিল। ১৯৩৮এ। ক্ষতি হবে বাংলা আর পাঞ্জাবের মানুষের। চিত্তরঞ্জন উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি দুটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমত হিন্দু মুসলমান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মুসলমান নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে একটা চুক্তি। যে চুক্তি ইতিহাসে বন্দিত হয় বেঙ্গল প্যাক্ট নামে। শরত বোস, যতীন সেনগুপ্ত, বিধান রায়, আবদুর রহিম, আক্রম খাঁ ইত্যাদিরা এই চুক্তির অংশীদার। তরুণ মুসলিম লীগ সদস্যরাও ছিল। এই সিদ্ধান্ত এক মতিলাল নেহেরু ছাড়া পশ্চিমের কোনও নেতা মেনে নিলেন না। তীব্র বিরোধিতা শুরু হল। বিশেষ করে গান্ধি ও প্যাটেল। এখানে গান্ধি-প্যাটেলের অনুগামীরাও বিরোধিতা করলেন। বিপিন পালও মেনে নেননি। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার মেনে নিয়ে কেন্দ্র রাজ্যসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক সভায় অংশ নেওয়া নিয়েও গান্ধির সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ শুরু হল চিত্তরঞ্জনের।
এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ…

১৬ জুন, ১৯২৫এ দার্জিলিংএ চিত্তরঞ্জন দাশ সামান্য কিছুদিনের জন্য জ্বরে ভুগে মারা গেলেন। ১৮ জুন শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁর মরদেহ এলে জনারণ্য তৈরি হয়েছিল। বহু মানুষ আক্ষরিক অর্থেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন। সেই সময় চিরত্তরঞ্জন ছিলেন বাঙালির মস্তিষ্ক। আকস্মিক মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে একটা অংশের (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের) বাংলা এবং বাঙালি কোমায় চলে গেল। যদিও বড় বাংলার পূর্বপ্রান্তে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি অনেকাংশেই সফল। যা এক সময় পূর্ববঙ্গ এবং তারপর পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল ১৯৭১ সালে রাজনৈতিকভাবে সেই ভূখণ্ডই বাংলাদেশ হতে পেরেছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। এটা জোরের সঙ্গে বলাই যায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা কিন্তু দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট। কিন্তু চিত্তরঞ্জন কোমায় চলে যাওয়ার পরেই কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিম বাংলার বাঙালিরাও ক্রমে কোমায় চলে গেছে। আনকনশাস। আজও তার চেতনা ফেরেনি।
আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি-সহ এখানকার ভুমিসন্তানদের জীবনে চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণ যে কত মারাত্মক আমরা তা আজও উপলব্ধি করেছি কিনা জানিনা। সাধারণ একটি মৃত্যুও ইতিহাসে অনেকসময় সন্ধিক্ষণ হয়ে যায়। সাধারণ বলছি, কেননা, মানুষ মাত্রেই মরণশীল এই নিয়ে তো স্কুলে রচনা লিখতে হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই, ৫৫ বছর বয়স ঠিক মৃত্যুর বয়স নয়। কিন্তু এমন মৃত্যু তো হয়েই থাকে। তবু এই মৃত্যু বাঙালিকে অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আজও দিশেহারা বাঙালি টুকরো টুকরো হয়ে বেরোবার পথ হাতড়ে বেরাচ্ছে। বাংলার সেই কঠিন সময়ে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথও বিচলিত হয়েছিলেন। বিচলিত হবেন, স্বাভাবিক। যদিও চিত্তরঞ্জন সমকালীন কায়দামতো ঠিক রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুবার দ্বিমত হয়েছেন, সমালোচনাও করেছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সব লেখা তাঁর ভালো লাগে না। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় রবীন্দ্রনাথ সেইসময়ের সদ্যজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করলেন। রবি ঠাকুর বললেন, বাঙালি ক্রমশঃ কূপমণ্ডূক হয়ে উঠছে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, রবীন্দ্রনাথ নেশন এবং ন্যাশানালিজম নিয়ে তাঁর ভিন্ন ভাবনা বারবার বলেছেন। বলেছেন, নেশন হল ভৌগলিক দৈত্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল কার্যত বিভিন্ন জাতীর বা নেশনের মধ্যে কর্তৃত্বের লড়াই। তাঁর এই বক্তব্য পেশ করার কারণে তিনি জাপানে কার্যত নিগৃহীত হয়েছিলেন। ১৯২১সালে গান্ধীর নয়া কর্মসূচী অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের আবেগ তুঙ্গে। চিত্তরঞ্জনও ব্যতিক্রম নন। মাত্র ৫০ বছর বয়সে বিপূল আয়ের আইনব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, দামি জামাকাপড় খুলে ফেলে সাদামাটা খদ্দরের ধুতি জামা পরে মোটা মোটা আইনের বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতে চরকা নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। যদিও চরকা চালিয়ে এক চিলতে সূতোও বের করতে পারতেন না বলে গান্ধির তির্যক মন্তব্যও তাঁকে শুনতে হয়েছিল। দেশের দুইপ্রান্তের দুই ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন আর গান্ধি ছিলেন প্রায় সমবয়সী। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনের সমালোচনায় ক্ষুব্ধ চিত্তরঞ্জন তখন সদ্য রাজবন্দি হয়েছেন। তিনি কারাগার থেকেই আমেদাবাদ কংগ্রেসে তাঁর লিখিত ভাষণে সোজাসাপটা রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবোধকে ঠাট্টা করে বললেন, নিজের বাড়ী না থাকলে অতিথিপরায়ণ হওয়া যায় না।
অথচ চিত্তরঞ্জনই আবার বলতেন, ন্যাশানালিজমের বাড়াবাড়িই বিশ্বযুদ্ধের কারণ। তো ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে বিচলিত হয়েছিলেন, আরও অনেকেই হয়েছিল। সেই সময়ে বাংলার অবিসংবাদিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর রবি ঠাকুর লিখেছিলেন, “এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। “সেইসময়ের মাত্র ২৬ বছর বয়সের নজরুলও লিখে ফেললেন “পয়গম্বর ও অবতার যুগে জন্মিনি মোরা কেহ/ দেখিনিক মোরা তাঁদের, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেব।/ কিন্তু যখনই বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ তলে/ না জানিতে কিছু না বুঝিওতে কিছু নয়ন ভরেছে জলে…” আরও এক তরুণ কলম ধরেছিলেন। নজরুলেরই সমবয়সী। তিনি কবি নন, অন্ততঃ তখনও তাঁর কবি পরিচয় গুপ্ত ছিল। আবার কবিতা নিয়ে তাঁর ধ্যানধারণাও তৎকালীন কাব্যজগতের সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়। তবু তিনিও লিখে ফেললেন “বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা/ অশান্ত সন্তান ওগো, বিপ্লবিনী পদ্মা ছিল তব নদীমাতা…।” তখনও গুপ্ত এই কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। এই তিন কবির শোকগাথা প্রমাণ করে চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যু বাঙালির মনে কত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।
চিত্তরঞ্জন যখন স্থায়ীভাবে রাজনীতিতে এলেন, তখন বাংলার রাজনৈতিক অস্ত্বিত্ব ক্রমশ ক্ষীয়মান। লাল-বাল-পালের যুগ শেষ। বিপিন পাল কার্যত আর তেমন সক্রিয় নয়। বরং চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতাই করেন। সুরেন ব্যানার্জীর অবস্থাও তেমন নয়। ততদিনে রাজনীতির ঘুর্ণীঝড় বাংলা ছেড়ে পৌঁছে গিয়েছে সুদূর পশ্চিমে। গুজরাটে গান্ধী, জিন্না, প্যাটেল। উত্তরে মতিলাল জহরলাল। গান্ধীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতাদর্শগত বিরোধ শুরু হল। সিপাহী বিদ্রোহের পরেই বৃটিশরা ধীরে ধীরে দেশীয়দের হাতে অল্প অল্প ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর কারণ, সেই বিদ্রোহের সময় তারা এখানকার উচ্চবর্ণ অভিজাতদের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিল। তাছাড়াও তাঁদের বাণিজ্য পুঁজি ক্রমশঃ শিল্পপুঁজি হয়ে উঠছে। আগে দরকার ছিল স্থানীয় বণিকদের সহযোগিতা, এখন দরকার স্থানীয় মুৎসুদ্দি পুঁজির সাহায্য। আর তারজন্য তাঁদের হাতেও কিছু কিছু ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। অনেকটা বিদেশি বড় কোম্পানীর ডিরেক্টরস বোর্ডে জায়গা দেওয়া। সুন্দর পিচাই। ১৮৬১সালে প্রথম আইন হল, স্থানীয়দের জায়গা দিতে। সেটা প্রায় জমিদারবাড়িতে উঠোনের প্রান্তে স্থানীয় নিচুজাতের চাষার একটু দাঁড়াবার জায়গার মতো। তারপর অনেকগুলো গভ অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট করে করে ১৯১৯সালে আবার একটা আইন হল। মণ্টেগু চেমসফোর্ড অ্যাক্ট। কেন্দ্রে আর রাজ্যে আইন পরিষদ ইত্যাদি। নির্বাচনের মাধ্যমে। যদিও সার্বজনিক ভোটাধিকার ছিলনা। করপোরেশন এবং স্থানীয় অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদিতো ছিলই। এইখানে একটু ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির ক্ষমতার সম্পর্ক বোঝা দরকার। বাংলায় অর্থনীতি ছিল মূলতঃ ভূমিরাজস্বকেন্দ্রিক। জমিদারি প্রথা। পশ্চিমে ঠিক বিপরীত। ছিল বৃটিশ পুঁজির আজ্ঞাবহ মুৎসুদ্দি পুঁজির বিকাশ। বাংলায় নাটোর, কৃষ্ণনগর,শিলাইদহের জমিদারি থেকে যে উদ্বৃত্ব তৈরি হয়, তা পুনর্বিনিয়োগ হয়না। হয় নানা আভিজাত্যের কুৎসিত প্রদর্শনীতে। সে দুর্গাপূজা হোক, বেড়ালের বিয়ে হোক অথবা সাংস্কৃতিক হৈহৈ হোক। বাংলা শিল্পসাহিত্যে বিপূল উন্নতি করল। উন্নতি কি? বিতর্ক হতেই পারে। বাংলার রাজনীতি, সে সুরেন ব্যানার্জি হোক, বিপিন পাল হোক, সবই কিন্তু ওই জমিদারি-আশ্রিত অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। পশ্চিমে ঠিক এর বিপরীত। জামসেদজি টাটা, জিডি বিড়লা, যমুনালাল বাজাজ প্রমুখ শিল্পপতিরা সরাসরি কংগ্রেসের পাশে এসে দাঁড়াল। তাঁদের কাছে গান্ধী, প্যাটেল, অনেক বেশি কাছের মানুষ। গান্ধী তো বরাবর বিড়লার প্রশ্রয়েই থাকতেন। ফলে সারা দেশের রাজনীতি এক বিচিত্র খামখেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। সারা দেশে নানা ভাষা, নানা ধর্ম। ভাষা প্রায় সারা দেশেই দাবার ছকের মত নানা ভৌগলিক এলাকায় ছড়িয়ে। বাংলা, তামিল, রাজস্থানী, ভোজপুরি, কাশ্মীরি, সিন্ধি। কিন্তু ধর্ম?
চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর রবি ঠাকুর লিখেছিলেন, “এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।” মাত্র ২৬ বছর বয়সের নজরুলও লিখে ফেললেন “পয়গম্বর ও অবতার যুগে জন্মিনি মোরা কেহ/ দেখিনিক মোরা তাঁদের, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেব।/ কিন্তু যখনই বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ তলে/ না জানিতে কিছু না বুঝিওতে কিছু নয়ন ভরেছে জলে…” আরও এক তরুণ কলম ধরেছিলেন। নজরুলেরই সমবয়সী। তিনি কবি নন, অন্ততঃ তখনও তাঁর কবি পরিচয় গুপ্ত ছিল। আবার কবিতা নিয়ে তাঁর ধ্যানধারণাও তৎকালীন কাব্যজগতের সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়। তবু তিনিও লিখে ফেললেন “বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা/ অশান্ত সন্তান ওগো, বিপ্লবিনী পদ্মা ছিল তব নদীমাতা…।” তখনও গুপ্ত এই কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। এই তিন কবির শোকগাথা প্রমাণ করে চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যু বাঙালির মনে কত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।
একদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বিদের সংখ্যা শুধু উত্তর পশ্চিমে আর দক্ষিণপুর্বে অনেক বেশি। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম ও অমুসলিম প্রায় সমান সমান। বাকি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর ইসলাম ছাড়া অজস্র স্থানীয় ধর্মকে গিলে নিয়ে উনিশ শতক থেকেই বৈদিক হিন্দু ধর্মের তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে সাঁওতাল থেকে ব্রাহ্মণ, চাঁড়াল থেকে ক্ষত্রিয় সবাইকে টেনে হিঁচড়ে আনা শুরু হয়ে গেছে। যদিও বর্ণাশ্রম প্রথার উপযোগিতা গান্ধী থেকে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। তাঁবুর নিচেই সবাই থাকবে, বর্ণভেদও থাকবে। তাঁবুর বাইরে বোর্ডে লেখা ‘হিন্দুত্ব’। ১৮৯৫-৯৬ সালে বঙ্কিমের অনুসারী চন্দ্রনাথ বসু বই লিখলেন ‘হিন্দুত্ব’ নামে। বৃটিশ সাহেবদের ক্ষমতার রুটির টুকরো ছুঁড়ে দেওয়া নিয়ে শুরু হল হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্ব। বৃটিশ সাহেবদের এ ব্যাপারে বায়াস ছিলই। মুসলমানদের ভাগে ক্ষমতার রুটির টুকরো প্রায় যাচ্ছিলই না। তারা ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। তৈরি হল মুসলিম লিগ। পাশাপাশি হিন্দু মুসলমানে ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টাও জারি রইল। ঠিক এইখানে এসে সমস্যাটা বিচিত্র চেহারা নিল। ১৯১৫ সালে সবে গান্ধী দেশে ফিরেছেন। ১৯১৫সালেই কংগ্রেসের অধিবেশনে জিন্নাহ-এর তৎপরতায় মুসলমানদের পৃথক ইলেকটোরেটের দাবি কংগ্রেস মেনে নিল। উত্তেজিত সরোজিনী নাইডু জিন্নাকে “হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অ্যাম্বাস্যাডার” উপাধি দিয়ে বসলেন। আসলে পশ্চিমী রাজনীতির মুখপাত্র গান্ধী, জিন্না, প্যাটেলের সুবিধে ছিল, উত্তরপশ্চিমে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল শুধু সম্পূর্ণ মুসলিম প্রধান। ওগুলো নাহয় মুসলিম লিগের হাতেই যাবে। কিন্তু দক্ষিণ পুর্ব নিয়ে সমস্যা। কলকাতা এবং বাংলার পশ্চিম অংশে ব্যবসা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেশটাকে ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা করার ভাবনা অনেক আগেই পুঁজির গবেষণাগারে এসে গেছে। পরে যার ফল হবে, বাংলা ভাগ। কেননা, বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তা ঠিক উত্তর পশ্চিমের মত নয়। এখানে দুইপক্ষ প্রায় সমান সমান। বাংলার পশ্চিমে যে পশ্চিমের বিশাল বিনিয়োগ আছে।
বাংলায় মুসলমানদের নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ কেননা, তাঁরা প্রশাসনের নানা জায়গায় ঠিকঠাক প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছেন না। তার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম হল সার্বজনিক ভোটাধিকার না থাকা। ভোটের অধিকারের সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে যুক্ত করা আছে। বাংলায় অধিকাংশ মুসলমান তথাকথিত রাষ্ট্রীয় লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত, তারা মারাত্মক দরিদ্র। ফলে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় থাকেই না। এটা দেশের অন্য অঞ্চলগুলোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু তাই নয়। এখানকার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জগতও বাঙালির মতই। ঠিক মুসলমান প্রধান অংশ নিয়ে দেশ ভাগ হলে যে বিড়লাদের কোনও অসুবিধে হবে না, তা বিড়লারা জানত। হিসেবও দিয়েছিল। ১৯৩৮এ। ক্ষতি হবে বাংলা আর পাঞ্জাবের মানুষের। চিত্তরঞ্জন উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি দুটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমত হিন্দু মুসলমান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মুসলমান নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে একটা চুক্তি। যে চুক্তি ইতিহাসে বন্দিত হয় বেঙ্গল প্যাক্ট নামে। শরত বোস, যতীন সেনগুপ্ত, বিধান রায়, আবদুর রহিম, আক্রম খাঁ ইত্যাদিরা এই চুক্তির অংশীদার। তরুণ মুসলিম লীগ সদস্যরাও ছিল। এই সিদ্ধান্ত এক মতিলাল নেহেরু ছাড়া পশ্চিমের কোনও নেতা মেনে নিলেন না। তীব্র বিরোধিতা শুরু হল। বিশেষ করে গান্ধি ও প্যাটেল। এখানেও গান্ধি-প্যাটেলের অনুগামীরা বিরোধিতা কর। বিপিন পালও মেনে নেননি। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার মেনে নিয়ে কেন্দ্র রাজ্যসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক সভায় অংশ নেওয়া নিয়েও গান্ধির সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ শুরু হল চিত্তরঞ্জনের। চৌরিচৌরার মত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে অসহযোগ আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী করে দেওয়াও চিত্তরঞ্জন মেনে নিতে পারেননি। এইসব বিরোধিতাকে আমল না দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই তাই একটি পৃথক দল তৈরি করলেন চিত্তরঞ্জন। স্বরাজ্য পার্টি।
আচমকা চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু পর গান্ধি-সহ পশ্চিমা নেতৃত্বের তীব্র বিরোধিতায় বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হয়ে গেল। পরের বছরেই শুরু হল কলকাতায় কুখ্যাত দাঙ্গা। চিত্তরঞ্জন বৃটিশসাহেবদের সংস্কারের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও প্রশাসনিক নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলেন, কেননা, তাতে যে মুসলমানদের এতদিন দুঃখ ছিল, প্রশাসনে তাঁদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব থাকে না, তারা যোগ্য সম্মান পাবে। বাংলায় হিন্দু মুসলমানের একতা সমস্ত ধর্মীয় বাধা অতিক্রম করে বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমান নয়, বাঙালি, বাঙালি হয়ে উঠবে। যারা প্রশাসনিক নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহি ছিল, তাদের বলা হত, প্রো চেঞ্জার। যারা বিরোধিতা করত তাঁদের বলা হত নোচেঞ্জার। বাঙালি কত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা সুভাষ বসুর এই বিলাপ পড়লেই বোঝা যাবে। এটি যখন তিনি লিখছেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬। তিনি লিখছেন-
আমি আজ একটা খুব বড়ো দুঃখের কথা বলবার জন্য কলম ধরেছি। এ দুঃখটা হয়তো অনেকের কাছে কাল্পনিক– কিন্তু আমার ক্ষুদ্র প্রাণের পক্ষে এ দুঃখটা সত্য ও গভীর। গয়াতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশনে কার্যকরী সমিতি (Working Committee) গঠনের কথা যখন উত্থাপিত হয়, তখন বাঙ্গলা দেশ থেকে কাকে নির্বাচন করা হবে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। পূর্বরীতি অনুসারে যে প্রদেশের লোক সভাপতি হয় সেই প্রদেশ থেকে অন্তত পক্ষে একজন সম্পাদক হবার কথা। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শাসমলের নাম সম্পাদক পদের জন্য প্রস্তাবিত হয়, কিন্তু তাঁরা ওই পদ গ্রহণ করতে রাজি হন না। তারপর বাঙ্গলা দেশের পরিবর্তনবিরোধীদের (No Changer) মধ্যে কাহাকেও সম্পাদক করা হয় না। পরিবর্তনবিরোধীগণও এ বিষয়ে এতদূর নিশ্চেষ্ট ও নিরপেক্ষ ছিলেন যে কার্যকরী সমিতিতে একজন বাঙ্গালিও সভ্যরূপে নির্বাচিত হন না। তার ফলে পরিবর্তনবিরোধীদের দলে নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালির এখন কোনও স্থানই নাই। ব্যাপারটা দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালির নাম লুপ্ত দেখতে আমরা চাইনি। বাঙ্গলা দেশে কি এমন কোনো সভ্য ছিলেন না যিনি কার্যকরী সমিতির সভ্য হবার উপযুক্ত বা যিনি ওই সমিতির সভ্য হতে পারতেন? যদি ছিলেন, তবে পরিবর্তনবিরোধীগণ তাঁকে উপেক্ষা করে নিজেদের এবং বাঙ্গালি জাতির মর্যাদাহানি ঘটালেন কেন? যদি এমন কোনো ব্যক্তি না ছিলেন, তবে এই দল কোন সাহসে দেশবন্ধুর মতো নেতার বিরুদ্ধাচারণ করে বাঙ্গলাদেশে কংগ্রেসের কাজ চালাবার ভরসা করেছিলেন? যে নিখিল ভারতীয় কার্যকরী সমিতিতে এক সময় বাঙ্গালির গৌরবময় স্থান ছিল, সেই সমিতিতে আজ একজন বাঙ্গালিও নাই।
আরও দুঃখের হল, সেই পশ্চিমা পুঁজির নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ। “ভূতপূর্ব আইন ব্যবসায়ী সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজের টাকাতে একটা ‘ফন্ড’ করা হয়; সেই ‘ফন্ডের’ নাম দেওয়া হয় ‘বাজাজ ফন্ড’ (কংগ্রেস ফন্ড বা তিলক স্বরাজ্য ফান্ড নয়)। এই সাহায্য বিতরণের জন্য প্রত্যেক প্রদেশ থেকে একজন লোক মনোনীত হন। বাঙ্গলার ভার শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের উপর অর্পিত হয়। সেনগুপ্ত মহাশয় যখন ওই পদত্যাগ করেন, তখন পরিবর্তন-বিরোধীদের দলে এমন একজন লোক পাওয়া গেল না যিনি ওই ভার গ্রহণ করতে পারেন। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে লোক পাওয়া গেল কিন্তু বাঙ্গলার ভাগ্যবিধাতা হলেন শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ।” (বোল্ড হরফ আমার)
বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি শুনুন। বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু মুসলমানে ঐক্য ওপর থেকে নিচে নিয়ে আসা। অর্থনীতিতে যেমন ট্রিকল ডাউন। আসলে সাধারণ ‘নিম্নবর্ণ’ হিন্দু আর আতরাফি মুসলমানে বরাবরই ঐক্য ছিল। ওপরওয়ালারা মাঝ মাঝে গোলমাল পাকিয়ে দিত, নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাশের বেঙ্গল প্যাক্ট থাকলে ১৯৪৭-এ দেশভাগ (বাংলা ভাগ) হতো না।
১৯২৫ সালের ১৬ জুন বাংলা কোমায় চলে গেছেন। আজও তাঁর চেতনা ফেরেনি।
অরূপশঙ্কর মৈত্র
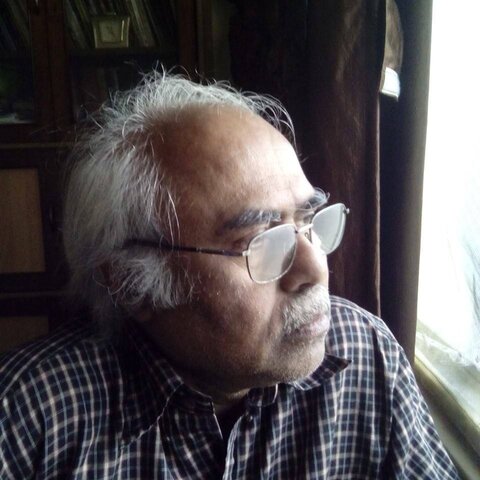
নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও লেখক। নিবাস: দক্ষিণ কলকাতা।