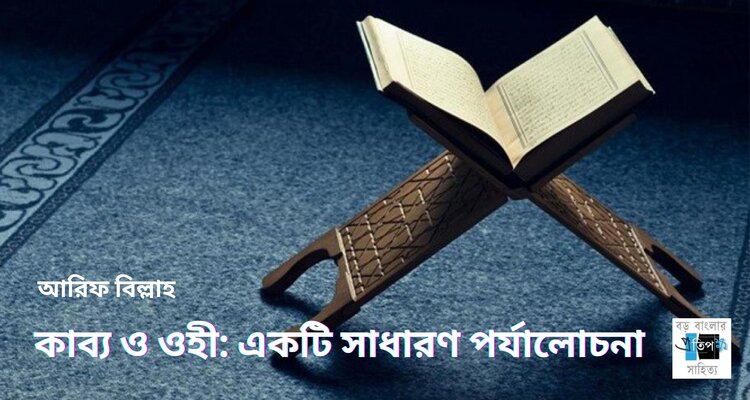
।। আরিফ বিল্লাহ ।।
আরবের মধ্যে যে কাব্যের বিকাশ ঘটেছে, সেটা মানুষের মুখের মধ্য দিয়েই, একান্তই দেহাত্মক ও শারীরিক শক্তি আকারে হাজির হয়েছে। মানুষের ধর্ম শারীরিক বা শরীরের মধ্যে আস্বাদন করবার যে উপস্থিত সুখ, তার মধ্যেই তারা ধর্মের ঐশ্বরিক আনন্দ খুঁজে পেত। কাজেই আরব দেশে কাব্য ও কবির ভূমিকা কোনো ধরনের আশমানি অবতারের চাইতে কম ছিল না। তবে এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, ‘কাব্য’ তার বিশেষ একটি স্তরে মানুষকে সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ভূমিকা নিয়েছে। এই ভূমিকার কারণে কবিকে একইসঙ্গে গীতিকার হতে হয়েছে। কবির অঙ্গভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, স্বরের কৌশল ইত্যাদি মানুষের কাছে তার কবিতার মূল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হত। এই কারণে আরবে কবিতা ও গানের মধ্যে তেমন কোনো ফারাক দেখা যায় না। জাহেলি আমলে কাব্য ও সংগীত একই ছাঁচে তৈরি হয়েছিল।
এই আলোচনায় আমাদের পথ প্রথাগত ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতির দ্বারা নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার মধ্য দিয়েই জটিল-অস্পষ্ট ও অপ্রকাশিত নানা প্রশ্ন, ইশারা ও ইঙ্গিত ধরে ধরে বিস্তীর্ণ অনুসন্ধান ও তল্লাশি চালানো হয়েছে।
তবে আমি সম্পূর্ণ রূপে তার শর্ত ও পদ্ধতির ব্যাপারে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করেছি। তাফসির পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের কাঠামো দ্বারা এখানে প্রতিটি ধারণা অন্যান্য মুফাসসির, এক্ষেত্রে যারা অভিধান ও শব্দ ব্যুৎপত্তির ওপর বিশেষজ্ঞ, তাদের কথাগুলিকেই আমি পরিষ্কার আঙ্গিক দান করেছি। এই আলাপ গড়ে উঠেছে ইসলামে তর্ক তৈয়ারির অত্যন্ত ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক পদ্ধতি থেকে। আমি শুধু এটাই খুঁজেছি যে ইতিহাসে মানুষের সম্ভাবনা, মাহাত্ম্য ও মহিমার উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোরানুল কারিম ও তার পরম্পরায় ইসলামি জ্ঞানকাণ্ড কোন ধরনের তাৎপর্য প্রদান করেছে।
তবে ইতিহাসের এই কালপর্বে যা কিছু পশ্চিমা দর্শন নিজের ঐতিহ্য ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরিষ্কার রূপে আমাদেরকে দেখিয়েছে: বুদ্ধির সর্দারি ও মানুষের মহিমা; আমার গরজ ও উদ্দেশ্য এই পরিষ্কার সূত্র থেকেই শুরু করা। তবে তাকে বিনির্মাণ করার জন্য সেই ভাষাও অনুসন্ধান করা— যার দ্বারা আমি নিজের এই হালতের মধ্যে অবলুপ্ত না হয়ে ক্রমশ তাকে যেমন আত্মস্থ করতে পারি, তেমনই তাকে নিজের কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা, এবং সেখান থেকেই আবার শুরু করার পথ তৈরি করা।
সেই জন্য কোন পথটা সঠিক সেটার জন্য আমার অবশ্য বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে হয়নি। আমি যা পড়তেছি বা যা পড়ব, তার ওপরই আমি পুরোপুরি ভরসা করেছি। এই এলেম ও বিদ্যা যেহেতু নবি-রাসুলের নবুওয়াতি প্রজ্ঞা থেকে উৎসারিত, অতএব এই কাজটা নবি-রাসুলেরই কাজ। নবি-রাসুলেরা তাদের জীবন দিয়ে আমাদের জীবনের সঙ্গে যে ছাপ ফেলে গিয়েছে, আমাদের সেইদিকেই গভীরভাবে তাকাতে হবে। সেই ছাপ বা ইতিহাসের অর্থ করার মধ্য দিয়েই আমরা আবার সেই প্রজ্ঞার স্বাদ বা মজা পেতে পারি।
‘নবুওয়াত’ বা ‘নবি’ শব্দপদ থেকে আমি প্রাথমিকভাবে অনুমান করি মানুষ ‘কথা বলে’। মানুষ যার সাথেই কথা বলুক, সে কথা বলে এবং কথোপকথন করে। এইভাবে নবুওয়াতেরই যে সারার্থ ব্যক্ত হয়, তার চিহ্ন: ‘ভাষা’ (১)। আমার সামনের যত কথা ফলে খোদ নবুওয়াতেরই এই মহৎ দলিল ধরে আপন পথ খুঁজে নিয়েছে।
প্রস্তাব
আমরা বলি ‘ভাষা’ হল মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে যোগাযোগ, ভাব-বিনিময় ও ভাবপ্রকাশের সজীব ও সক্রিয় পরিসর। এই কারণে ভাষার মধ্য দিয়ে যোগাযোগ ও আদানপ্রদান ঘটার জন্য সর্বনিম্ন দুইজন জীবন্ত মানুষের ‘পরিসর’ প্রয়োজন। সাধারণত আমরা যখন জীবন্ত মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি বলাবলি ও বাতচিত করি, তখন অপর ব্যক্তি বক্তা-নির্দেশিত কথার কর্তব্যের প্রতি তৎপর হয়ে ওঠে। এই তৎপরতার তাৎপর্য কী? শুধু কি এটাই যে, মানুষ নিজেকে ‘নির্দেশের’ বিষয় করে তুলবে, নাকি সেই ‘নির্দেশে’ মানুষ নিজের সঙ্গে নিজের জিজ্ঞাসার সামনাসামনি হয়ে পড়ে (যা মূলত মানুষের কর্তাসত্তা নির্ধারণের প্রশ্নও বটে)।
এই জীবন্ত সম্বন্ধ কেবল ‘মুখের’ (২) সঙ্গে মুখের নয়। কেননা ‘মুখ’ দিয়ে আমরা কেবল দুনিয়ায় কথা বলি, কিন্তু আল্লার উসিলায় আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাক্ষ্য হয়ে উঠি। কিংবা তা কেবল বাগেন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন নানা শব্দের মধ্যে শব্দের সম্বন্ধ ঘটায় না। কেননা শব্দ আমাদের উদ্দেশ্য না, বরং শব্দের পরদার আড়ালে যে অসংখ্য অর্থ লুকিয়ে থাকে, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা গোড়ার এই প্রশ্নসমূহ তলিয়ে দেখি, ‘ভাষা’ নিজেকে প্রথম হাজির করে ‘জিজ্ঞাসা’ আকারে। মানুষের নিজের জিজ্ঞাসা বা বলতে পারি ‘আত্মজিজ্ঞাসা’। কিন্তু ‘আমি’ সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসা কোরানের বর্ণনায় হাজির হয় আল্লার জিজ্ঞাসার অধীন, জিজ্ঞাসা হয়, ‘আমি কি তোমাদের রব নই?’ (৩) আবার এই ‘আদ্য জিজ্ঞাসা’ মনুষ্য প্রজাতির মধ্য দিয়ে জারি থাকা, বা খোঁজাখুঁজির দিক থেকে তার উপস্থিতি, অর্থ ও ব্যঞ্জনার মাধ্যমে বিস্তৃত ও বিকশিত হয়ে চলেছে (৪)। যেন মানুষের সমাজ, প্রজাতিগত ইতিহাস ও সিলসিলার মধ্য দিয়ে সেই জিজ্ঞাসার সাক্ষ্য হিসাবেই আমরা বর্তমান হই বা হাজির থাকি। তাই কোরানে মানুষকেই প্রশ্ন করা হয়। যাতে মানুষ জগতে নিজের হাজিরা ও উপস্থিতির মাকাম ও শান অনুধাবন করতে পারে।
কোরানের তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির একটি মেসাল হিসাবে আমরা এ নিয়ে চিন্তা করে আসছি। ভাষার ‘কথোপকথন পরিসর’ চিন্তার মূলে এই ভাবধারা ভেবে আমরা ‘ভাষা’ নিয়ে নতুন করে ভাববার তাগিদ বোধ করেছি। যাতে আমরা এর মধ্য দিয়ে মানুষের সক্ষমতা ও সম্ভাবনার সাধ্য নির্ণয় করতে পারি। সেই সক্ষমতা, যা মানুষের উপস্থিতির দলিল হিসাবে মানুষের মধ্যেই ক্রিয়াশীল। আমরা কি পারব নিজের দলিলে নিজের জিজ্ঞাসা, কর্তব্য ও কর্মের সাক্ষ্য হয়ে উঠতে?
‘ভাষা’ বলতে বুঝি যা নানান উচ্চারণ, বিশেষ অবস্থা ও পরিপার্শ্ব এবং তার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য অর্থ-উৎপাদন করার চিহ্ন হিসাবে হাজির হয় বাইরে— অর্থাৎ ‘অপর’-এর কাছে। ‘অপর’ যাকে নিজের কথায় নির্দেশ করাই বা আত্মস্থ করাই ভাষার সাধনা হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার সমস্ত ভাষাই এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ওঠানামা করে। ভাষার মধ্যে এই প্রকাশের যন্ত্রণা কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ সবাই ভোগ করে চিরজীবন। কেউ কি পারে সেই বাহির, সেই যা ‘এই’ বলার মধ্যে নাই, কিংবা ধরেও ধরা যাচ্ছে না, সেই উপলব্ধির অধরাকে সমগ্রভাবে ধরতে? আরবি ভাষার অভিজ্ঞতায় মানুষ নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হল। এই ভাষায় ‘অপর’ বলতে যিনি বসে আছেন তিনি নিজেই ‘গায়েব’। ইসলামে সেই গায়েবকে ভাষার মধ্য দিয়ে অনুভব করবার এক নতুন ঘোষণার দ্বারা ভাষার হদ ও সীমা নতুনভাবে নিরূপণ করে দেয়।
ওহী ও কাব্যের ভেদ–অভেদ
প্রাচীন ইহুদি-খ্রিস্টীয় ধর্মে মানুষ ফলকে অঙ্কিত ও পাথরে খোদাই করা ধর্মের কেতাব পাঠ করতেন। ধর্ম সব সময়েই ছিল বাইরের বিষয়। কিন্তু চৌদ্দোশো বছর আগে দ্বীনের নবি মুহাম্মদ গায়েব থেকে তার কলবের ফলকে ইব্রাহিম, মুসা, ইসহাক ও ইসমাইলের দিব্যতা ধারণ করে হাজির হলেন। তিনি আরবের এলাহি নিদর্শনকে একত্ববাদ ঘোষণার জন্য নিয়োজিত করেন। আরব দেশে সেই এলাহি নিদর্শন রয়েছে তার বয়ানে, ভাষায়। কবিতা ও কাব্য কিংবা শায়েরি ইতিহাসে দিব্যতাকে সর্বোচ্চ শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা প্রদান করল। সেই দেশে এ ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব। এমন ঘটনা— মা লা আইনা রাআত ওয়ালা উজনা সামিয়াত ওয়ালা খাতারা আলা কালবি বাশার (যা কোনো চোখ দেখে নাই, কোনো কান যা শোনে নাই, কোনো মানুষের অন্তরে যা কখনো উদয় হয় নাই)।
আরবি ভাষায় ‘ওহী’র দিক থেকে এটা স্পষ্ট হল যে ‘কাব্য’ বা মানুষের দৈনন্দিন ভাষাচর্চার সীমার বাইরেও আল্লার বরাতে মানুষ নতুন কোনো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারে। ফলে বিশ্ব-ইতিহাসে আবার ‘ভাষা’ ও ‘কাব্যের’ সম্পর্ক নিরূপণ আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। ‘কাব্য’ ও ‘ভাষা’ মানে এই না যে একদল মানুষ কবিতা করে এবং আরেক দল মানুষ করে ভাষা। অথবা আমার উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, ভাষা ও কবিতা মানগত দিক থেকে আলাদা। প্রথমত এর কারণ হল মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে ‘ভাষা’ কোনো প্রকার বিভাজন বা শ্রেণিকরণের মধ্যে নিষ্পন্ন করা অসম্ভব। কেননা মানুষ এবং ভাষা নিজের অভিপ্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটাবার মধ্য দিয়ে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে কাব্য ও ভাষা মানুষের ক্ষমতার প্রকাশের দিক থেকে তখনই বোঝা সম্ভব যখন উভয়কে ‘জীবন্ত মানুষের’ জায়গা থেকে আমরা বুঝব। এই কারণেই আমরা ভাষার মধ্যেই কাব্যের উপাদান বলবৎ দেখি, এবং কাব্যের মধ্যে ভাষার ক্ষমতাই ক্রিয়াশীল পাই। এই দিক থেকে ‘কাব্য’ হল মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে ভাষার অন্তর্গত একটি সাধারণ অভিব্যক্তি। তাই আমরা আরবের মতো পৃথিবীর বহু প্রাচীন সভ্যতায় মুখ ও স্মৃতিনির্ভর জাতিগোষ্ঠী পাই। তাদের মধ্যে কাব্য, গীত বা সংগীত চর্চার (الإنشاد والنشيد) প্রাবল্য দেখি। কেননা মানুষ নিজের ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা, মাধুর্য ও যা তার মধ্যে না থেকেও আছে এবং থেকেও নাই— তাকে প্রকাশ করবার হাতিয়ার হিসাবে কাব্যিক বা রূপকভাবে ‘কথা’ তৈরি করে।
এর ফল দাঁড়িয়েছে কাব্য মাত্রই বিদ্যমান ভাষাব্যবস্থা নির্ভর, কিন্তু একইসাথে এই বিদ্যমানতার মধ্যে থেকেও অতিরিক্ত অর্থ ও উপলব্ধি আদায়ে সক্ষম। এই কথা কোরানের ওপরেও খাটে, কিন্তু কোরান বলে ‘ভাষা’ জীবন্ত মানুষের সঙ্গে রুহানি সম্পর্ক তৈরির হাতিয়ারও বটে। এর মধ্যে তিনটি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। যেমন,
১. ভাষাব্যবস্থার প্রতি নির্ভরতা
২. গতবাঁধা ভাষার মধ্যে নতুন অর্থ ও দ্যোতনা তৈরির ক্ষমতা। এই দুটো উপাদান কবিতা ও কাব্যের মধ্যে থাকলেও তৃতীয় উপাদানটি একমাত্র ‘ওহী’র মধ্যেই পাওয়া যায়। সেটা হল,
৩. কোরান নাজিলের মধ্য দিয়ে ‘ভাষার’ একইসঙ্গে জীবন্ত মানুষের সঙ্গে যিনি ‘গায়েব’, নাই ও নিরন্তর অনুপস্থিত, তাঁকে অনুভব করবার রুহানি হাতিয়ার হয়ে ওঠা।
এখান থেকে পরিষ্কার আল্লার কালাম মানুষের ভাষাব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই হাজির হয়। এর মানে আল্লাহ মানুষের মতো কথা বলেন, মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে দাম দেন। ‘ওহী’ একইসাথে মানুষ ও মানুষের জাগতিক ও বৈষয়িক সম্পর্ক আল্লার সম্পর্ক আকারেই হাজির করে। তাই এ হিসাবে আল্লার কালামের পক্ষে আরবের কাব্যিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই হাজির হতে হয়েছে। এই হুজ্জাতেই আমি কাব্য ও সাধারণ ভাষার মধ্যে গোড়ায় কোনো পার্থক্য অনুমান করি নাই। কেননা ভাষার প্রকাশ ও অর্থ-উৎপাদন সম্ভাবনার কারণে ভাষার মধ্যেই কাব্যিকতা উপস্থিত থাকে। কাজেই কোরানের কাব্যিকতা ও একইসাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটনা থেকে আমরা বুঝি, মানুষের মধ্যে বিশেষ দেশকালপাত্রে কোরান যে রুহানি অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত, তার বাইরেও তার অন্তহীন ব্যঞ্জনা রয়ে যায়। কোরানের মধ্যে তিনটি উপাদানই মৌলিকভাবে বিদ্যমান। প্রথম দুইটি আরবি কাব্যের মাধ্যমে ইতিহাসে দারুণভাবে বিকশিত হয়েছে। ফলে আরবে কাব্য ও ভাষা কার্যত একই অর্থে ব্যক্ত হয়েছে। এর দলিল হিসাবে আবু হাইয়ান তাওহীদির (মৃ. ৪০০) বরাত টানা যায়। এ সম্পর্কে খালদুনও একমত হবেন। তাওহীদি কথাটা তাঁর উস্তাদ আবু সুলাইমানের মুখের কথা হিসাবে উল্লেখ করেন। তাওহীদি উস্তাদের কাছে সোয়াল উঠালেন, ফালাসেফা ও মুতাকাল্লেমিনদের আলাপের পদ্ধতি কী? উস্তাদ আবু সুলাইমান এই আলোচনার মধ্যে তাঁর উস্তাদ ইয়াহইয়া বিন আদি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, “নাহু, শে’র, ভাষা কোনো বিদ্যা নয়— এর দলিল হল, তুমি এই মরুভূমিতে এমন পোড়খাওয়া বুড়া মানুষের দেখা পেতে পারো, যে লোক জীবনে কোনো শহুরে বাবু বা ভিনদেশি মানুষের সাথে মেশে নাই বা দেখে নাই, যে লোক জীবনে তার উটের যত্ন করা ছাড়ে নাই বা নদী-নালায় গিয়ে নিয়মিত গোসল করে নাই, তার মুখমোবারক ধূলিমাখা, আমরা কেউই তাকে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারব না। এই লোকরে তুমি যদি বলো, তোমার কি ‘এলেম’ আছে? এর জবাবে সে ‘না’ বলে উড়িয়ে দিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখা যাবে, তিনি আরবদের নানান প্রবাদ, প্রবচন, উপমা (أمثال العرب) আবৃত্তি করছেন, কবিতার পর কবিতা রচনা করছেন, কিংবা চমৎকার ভঙ্গিতে সুসজ্জিত বাক্য বলে যাচ্ছেন। উপস্থিত কেউ যদি তার কথা শোনে, সে এটাকে আদব বা সাহিত্য হিসাবে গণ্য করবে এবং তা বর্ণনাও করবে। এটা পরিণত হবে গুরুত্বপূর্ণ হুজ্জাতে।” ইয়াহইয়া বিন আদি আরও বলতেন, “সমস্ত আদব ও এলেম হচ্ছে হেকমাতের ছোলা। সেখান থেকে সময়ের পরিক্রমায় কিছু বিক্ষিপ্ত হতে পারে না। কেননা এইসব বিষয়ে যে কিয়াস হাজির থাকে বা যে দলিল দাবি হিসাবে থেকে যায়, সেটা স্বয়ং মানতেকি বুরহান বৌদ্ধিক সিদ্ধসূত্র, (البرهان المنطقي), দিব্যচিহ্ন (الرمز الإلهي) ও দার্শনিক উপলব্ধির (الإقناع الفلسفي) মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। এই বিষয়টি আরাস্তুতালিস কিতাবুল জাদালের (‘The Topics’) পঞ্চম প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।” (৫)
খালদুনের মধ্যে আমরা গোটা আরবি ভাষাকে আরবের মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের দিক থেকে একটা ‘মৌখিক কথোপকথন’ (الخطاب الشفهي) হিসাবে হাজির হতে দেখি (৬)। আরবি সভ্যতা প্রকৃতিগত দিক থেকে মুখ ও স্মৃতিনির্ভর। মানুষে মানুষে সজীব ও সপ্রাণ কথোপকথনের বাইরে কোনো খাতাকলমের জ্ঞানে তাদের মনোযোগ ছিল না। এটা তৎকালীন আরবদের ভাষায় ‘শব্দ’ বা ‘উচ্চারণ’কে ‘কালেমা’ বলার মাধ্যমেও আমরা টের পাই। কালেমার শক্তি ও দ্যোতনা সাধনার মধ্যে তারা ঐশ্বরিকতার মজা পেত। আরবে কাব্যের যে মর্যাদা সেটা ঐতিহাসিকভাবে ধর্মবিশ্বাস আকারে গড়ে উঠেছিল।
ইমাম খলিল বলেন (মৃ. ১৭০),
“আরবি ‘কালেমা’ (الكَلِمةُ) হেজাজি উচ্চারণ রূপ। বনি তামিম গোত্র ‘কিলমাহ’ (الكِلْمةُ) রূপেও এটা উচ্চারণ করে। উচ্চারণ যা-ই হোক, এর আদ্যার্থ হল জখম করা বা আহত করা (الجرح)। যেমন, আমি তাকে ‘কালেমা’ করি, আমি তাকে ‘কালেমা’ করব (كلمته أكلِمه كَلماً،) বা আমি কালেমাগ্রস্ত (وأنا كالمٌ، وهو مَكلومٌ), এর মানে হল আমি তাকে ক্ষত করেছি, আহত করেছি (جرحته) বা আমি আহত।” (৭)
এই বিষয়ে বিখ্যাত তুর্কি গবেষক ফুয়াদ সেজগিনের মতামত উল্লেখযোগ্য। তিনি একটি প্রস্তাব হিসাবে বলেন, “আমাদের কাছে এ পর্যন্ত যেসব আরবি ‘বয়াত’, ‘ছন্দ’, ‘কবিতা’ ও ‘কছিদা’ এসে পৌঁছেছে, সেখান থেকে এটা স্পষ্ট, আরবরা কালেমার জাদুশক্তির ওপর বিশ্বাস করত। এই আকিদা শুরুর দিকের আরবি আদবে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। বরং তারা বিশ্বাস করত শায়েরের কালেমা বা শব্দশক্তি কারও জন্য বরকত ও লানতেরও কারণ হতে পারে।” (৮)
আরবের মধ্যে যে কাব্যের বিকাশ ঘটেছে, সেটা মানুষের মুখের মধ্য দিয়েই, একান্তই দেহাত্মক ও শারীরিক শক্তি আকারে হাজির হয়েছে। মানুষের ধর্ম শারীরিক বা শরীরের মধ্যে আস্বাদন করবার যে উপস্থিত সুখ, তার মধ্যেই তারা ধর্মের ঐশ্বরিক আনন্দ খুঁজে পেত। কাজেই আরব দেশে কাব্য ও কবির ভূমিকা কোনো ধরনের আশমানি অবতারের চাইতে কম ছিল না। তবে এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, ‘কাব্য’ তার বিশেষ একটি স্তরে মানুষকে সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ভূমিকা নিয়েছে। এই ভূমিকার কারণে কবিকে একইসঙ্গে গীতিকার হতে হয়েছে। কবির অঙ্গভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, স্বরের কৌশল ইত্যাদি মানুষের কাছে তার কবিতার মূল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হত। এই কারণে আরবে কবিতা ও গানের মধ্যে তেমন কোনো ফারাক দেখা যায় না। জাহেলি আমলে কাব্য ও সংগীত একই ছাঁচে তৈরি হয়েছিল। ‘শায়েরে রাসুল’ খ্যাত হাসসান বিন সাবেত রাঃ বলেন,
تغن في كل شعر أنت قائله … إن الغناء لهذا الشعر مضمار
তুমি যে কবিতার রচয়িতা সেটা গানেও গেয়ে যাও। গানই কবিতার মর্ম প্রকাশের হাতিয়ার (৯)।
এই কবিতাকে সাক্ষী মেনে তাহের বিন আশুর বলেন, আরবি কাব্য ওজন দেবার মাপকাঠি ‘মিউজিক প্রকরণের’ (১১)। এই দিক থেকেই আমরা বলতে পারি, আরবিতে কবিতা ও কাব্য যত কিসিমের, সংগীতও ঠিক তত কিসিমের। আসলে আরব দেশে কবিতা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ব পাবার কারণে তাকে সংগীতও হয়ে উঠতে হয়েছে। কবিদের এর মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়েছে। তাই কবিতা কোরান নাজিল হবার আগে নিজেকে বিধাতা ও ঐশ্বরিকতার মর্যাদায় ভূষিত করতে পেরেছিল। কবিতার উদ্দেশ্য, ভাবালুতা ও কল্পনার মধ্য দিয়ে মানুষকে নিজের কর্তাসত্তা অনুভব করতে হয়েছে। এইখানে আমরা যেসব দলিল-প্রমাণ দিয়েছি, তারপরে এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু দার্শনিক তর্কে আসতে পারি।
১. কেরাত: মানুষ ও খোদার অভিমুখ বিচার
শুরুতেই বলে এসেছি আমরা কোরানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তখনই বুঝতে পারব, যখন মানুষের ভাষার মধ্যে ওহী ও কালামের বিশেষ ঘটনা বোঝাও সম্ভব হবে। এই তর্ক গোড়ায় আরবি ভাষার মামলা না শুধু, বরং আরবি ভাষার অভিজ্ঞতায় দুনিয়ার সমস্ত ভাষায় এই প্রশ্নটা ভাষার মৌলিক উপাদান গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এখন আমরা ছাপাখানার মেশিনে আল্লার কালামটা ছাপা হয়ে আসতে দেখি। তাই ধারণা করি যে এর বাইরে কোরানের আর কোনো অস্তিত্ব নাই। যার ফলে আমরা আরবে কোরান নাজিলের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী সেটাও বুঝি না। আমরা যদি কোরান সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, আরবদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক স্তর সম্পর্কে পর্যালোচনা করা শিখতে হবে। আরবরা ছিল কণ্ঠ ও স্মৃতি নির্ভর জনগোষ্ঠী। তারা জীবন্ত সম্পর্ক ও মুখের কথা, প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিবাক্যের ওপর প্রবল বিশ্বাস রাখত। তারা কথা বলা, ভাব-বিনিময় ও সম্পর্ক নির্মাণ করার জন্য কণ্ঠ ও সংগীতের আশ্রয় নিত। আমরা যেহেতু এখন এটা ভুলে গেছি এবং কোরানের বোঝাপড়ায় ‘আরব্য ফিতরত’ বিশ্লেষণ করা দরকারি মনে করি না, ফলে কোরান পড়ায় (যে কোনো বই বা অক্ষরের লাইন হতে পারে) অক্ষরই আমাদের সাধনা ও উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে। এর ফলে মানুষ বইয়ের পাতার বাইরেও যে সজীব ও সপ্রাণ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও স্মৃতি ধারণ করে, যা একইসাথে ‘অপর’কে ‘আমি’তে রূপান্তর করে, যা দূরে তাকে কাছে পরিণত করে, কিংবা যা ছড়ানো তাকে ‘একত্র’ করতে সাহায্য করে, তার সঙ্গে আমরা কোনো বোঝাপড়ায় আসতে পারি নাই। এই কারণে কোরানের সঙ্গে সর্বপ্রথম মানুষের জীবন্ত সম্পর্ক, অর্থাৎ ভাষা, ভাব ও তার সজীব সম্বন্ধসমূহ পরিচ্ছন্ন করে তোলা জরুরি।
মানুষের সঙ্গে মানুষের এই জীবন্ত ও আছেময় সম্পর্ক কেবল ‘নিজেকে অন্যের সাক্ষ্য’ করার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হতে পারে। আমরা কোরানের মধ্যে আল্লার সাক্ষ্য হাজির হতে দেখি প্রথমত ‘পাঠ’ বা ‘পড়াজনিত শব্দে’। সুরা আলাকে ইরশাদ করেন—
اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ
خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ
পড়ো তোমার রবের ইসমে, যিনি সৃষ্টি করেন।
যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে,
পড়ো হে, আর জানিয়ে দাও তোমার রব সবচেয়ে মহান।
আরব প্রতিভায় আগে কখনো পড়া বা পাঠ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই আয়াতের মধ্য দিয়ে আরবি ভাষায় নতুন করে ‘পড়া’ (কেরাত, قراءة) কথাটা প্রাণ পেল। আরবিতে ‘পড়া’ শব্দটি এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মুখের কথা মানুষ শোনে, পড়ার নির্দেশ থাকলে পড়তেও হয় (১২)। পড়া দেখে হয়, কিংবা কেউ বলে দিলে পড়তে পারা যায় (১২)। এই আয়াতের শব্দে একটা নতুন বুনন দেখি। একেবারে নতুন ব্যবহারে সেই বুননের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের মধ্য দিয়ে একদিকে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, অন্যদিকে অসীম হয়ে ওঠার স্বাদ অর্জন করে। ‘রবের ইসমে’— ফলে ‘পড়া’ কোনো ইসমের সাথে যুক্ত, যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি সবার প্রতিপালন করেন। এই যে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ কথা, এইখানে ‘পড়া’ পরিণত হয়েছে ‘ভাষায়’ এবং সমস্ত জগৎ পরিণত হয়েছে ভাষার সম্বোধনক্ষেত্রে। এই দিক থেকে ‘পড়া’ ধারণার ওপর ভিত্তি করে দুই ধরনের ‘কথারূপ’ (الكلام) হাজির হয়:
ক) ‘এলাহি কালামের দিক থেকে পড়া’ (القراءة من جهة الكلام الإلهي): এর মানে হল মানুষের কথা বলার ও অপরের সাক্ষ্য বা ‘অনুপস্থিতির উপস্থিতি’ হয়ে উঠবার শক্তি। এই কারণে অন্য সব জীবের মধ্যে মানুষ নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারে এবং চাইলে অপরকেও নিজের সম্বোধনে ধরতে পারে। ফলে মানুষ পড়া কিংবা পাঠের মধ্য দিয়ে নিজেকেই আত্মস্থ করে, এবং সত্যের তাজাল্লি অর্জন করে। কেননা পাঠ মানে নিজের সীমানায় অনন্ত ব্যঞ্জনার বিশেষ প্রকাশ ঘটা। এই পাঠ শুরু হয় মানুষের ভাষায় আল্লার প্রকাশ ঘটার মধ্য দিয়ে। ফলে মানুষ নিজের ভাষা ও কথোপকথন সম্পর্কের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও নির্দেশ সম্পর্কে সচেতন হয়। মানুষের মুখের ভাষা, কথোপকথন একান্তই কোনো বিশেষ নির্দেশ নিয়ে হাজির হয়। এর মধ্য দিয়ে জীবন্ত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক কথাবার্তা একইসঙ্গে একটি নৈতিক ও ব্যবহারিক বোঝাপড়া হয়ে ওঠে। ফলে মানুষ পারে না নিজেকে অস্বীকার করতে, কিংবা পারে না নিজের অপরকে অপরায়ন করতে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এইভাবে ‘পড়া’ (কেরাত, قراءة) কথাটি একটা ব্যবহারিক ও বৌদ্ধিক কাজ হিসাবে পরিগণিত হয়।
খ) ‘মানুষের দিক থেকে পড়া’ (القراءة من جهة الناطق الإنساني): এই আয়াতে এটাও দেখি মহান আল্লাহ কোরানের মধ্যে মানুষকে নিজের কথার ক্ষমতাসম্পন্ন করেছেন। তিনি মানুষকে আশমান থেকে সরাসরি বই দিয়ে পড়াতে পারতেন, কিন্তু এই পড়া হয়েছে বইয়ের নয়, কালামের। বরং পড়ার মধ্য দিয়ে আরও তিন ধরনের ‘পড়া’ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। ১. ‘আমি’র পাঠ, ২. রব নামের প্রকাশ পাঠ, ৩. ‘অপর’ বা ‘নাই’ নামের পাঠ। সংখ্যার দাগ দিয়ে এই তিনটি স্তর ভাগ ভাগ করা গেলেও তারা আবার ফিরে আসে কামালিয়াতের দিকে। আদিতে দার্শনিক ও মুহাক্কিক সুফিয়ানে (১৩) কেরাম ভাষিকসত্তা বা বাক্শক্তিসম্পন্ন জীবসত্তা (النفس الناطقة) বলে মানুষের প্রজাতিগত প্রকৃতি নির্দিষ্ট করতেন। মনুষ্য প্রজাতি তার বাইরের জীবজগৎ থেকে পৃথক ও আলাদা, এর দ্বারা তাঁরা বুঝতে চান। এই জীবসত্তা নিয়ে তাঁরা আলাপ করেন মানুষ ও জগতের এই দ্বিধাকরণ ও বিভাজনের আলোকে। কিন্তু মানুষকে জগৎ থেকে পৃথক করা হলেও জগৎ আর মানুষ স্রেফ ‘নফস’ দ্বারা তো পৃথক হয় না। ‘নফস’ নিজেও একটা নির্বিশেষ ও বিমূর্ত শব্দ। ফলে এই নফসকে আরও তিন-চারটা পৃথকীকরণ শব্দ দ্বারা বিশেষায়িত করতে হয়। যেমন মানুষ জন্তু নয়, মানুষ গাছপালা বা ইটপাথর নয়। এইভাবে নফস ধরা পড়লেও মানুষ আসলে ধরা পড়ে না। তাই মানুষের ওপর এই ধরনের নির্বিশেষ কোনো বিশেষণ বা কল্পনা আরোপ না করে বোঝার চেষ্টা করছি। মানুষকে শুধু ভাষা, বা নফস দিয়ে ধরাবাঁধা সম্ভব কি না, সেটা গুরুতর প্রশ্ন। এটা অবশেষে একইসাথে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মামলা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ওপরের ওই তিনটি স্তর দিয়ে আমরা সমগ্র মানুষটাকে ধরার কোশিশ করছি। তবে তিনটি স্তরে, ‘পর্যায়ক্রমে’ পাঠ করলে আমরা এই প্রসঙ্গে কোনো অর্থপূর্ণ পাঠ হাসিল করতে পারব না। তাই এই তিনটি স্তর একজন মানুষের পাঠে কীভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই দিকেই আমার নজর দিতে হবে। কেননা মানুষই আল্লার ওহী ও কালামের একমাত্র সম্বোধনক্ষেত্র। মানুষের মধ্য দিয়েই এলাহি কালাম দলিল ও হুজ্জাত হিসাবে পাঠ ও পড়ার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। মানুষ আল্লার প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই তিনটি স্তরকেই পড়ে। যদিও এই তিনটি স্তরে মানুষের পূর্ণ হয়ে উঠবার জন্য দৈহিক সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করতে হতে পারে (১৪)। কেননা মানুষের নিজেকে চেনার জন্য নিজের সবচেয়ে বড় দলিলের মুখোমুখি হতে হয় সবার আগে। ‘দেহ’ বা সীমার উপলব্ধি তাই অসীমের উপলব্ধির জন্য শর্ত। ফলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, এইখানে ‘দেহ’ বলতে কি শুধুই ‘সীমা’? তাহলে সীমা (متناهية) কীভাবে অসীমতার শর্ত হয় (غير متناهية)? যদি এরকম হয় তাহলে অসীমতা বলে কিছুই থাকে না, কেননা শর্ত (الشرط) এবং ‘শর্তের অধীন’ (المشروط) একই হুকুমের অন্তর্গত, আর যদি এর উলটা হয়, তাহলে সবকিছুই অর্থহীন বলে গণ্য হবে। তাহলে তর্ক দাঁড়াল, দেহের বাইরে কোনো ‘অসীমতা’ বা ‘অপর’ কিংবা অধরা থাকার মানে কী? কীভাবে ‘আছে’ ও কোন অর্থে ‘আছে’?
১.২ দেহ : সীমা ও অসীম
এই বিষয়ে কথা বলা প্রয়োজন। কেননা ভাষার প্রশ্নে যোগাযোগ, আদানপ্রদান বা ‘দেখাদেখি’, কিংবা মুখোমুখিতার মধ্যে ‘অপর’ বা কথারূপ তৈরির পরিসর (الدائرة الكلامية) চিন্তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক একইভাবে নবিজির মধ্যে যে বিশেষ দ্যোতনায় ওহীর মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেটা এখান থেকেই আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব। কেননা এর মধ্যেও অনন্ত ব্যঞ্জনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ‘অনন্ত বা অসীম’ ইসলামে পাঠ বা ব্যক্তির সম্মুখে আল্লার নিজের প্রকাশ হবার ঘটনায় বিশেষ একটি ধারণায় আমরা প্রকাশ করি। সেটা হল ‘আয়াত’ (الآية)। ফলে বাইরের সবকিছুই ব্যক্তির সামনে আল্লার আয়াত আকারে হাজির, ফলে কোরান, কিতাব, মানুষ ও সমস্ত জীবজগৎ মানুষের প্রকাশক্ষেত্র হয়ে উঠছে। ‘আয়াত’ নিজ অর্থে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এর মধ্যে এই দ্যোতনা আছে— যা কিছু মানুষের সামনে আছে, সেটা মানুষের জন্যই আল্লার তরফে তৈরি করা। এই কারণে রাসুলের কাছে ‘রবের নামে’ অর্থাৎ মানুষের সামনে সীমাবদ্ধ অর্থে যে অধরা পেশ হতে পারে, তারই নামের উসিলা ধরতে বলা হয়েছে। এই হিসাবে আমরা দেখি এই ‘দেহ’ কথাটি যদিও অসীমতা উপলব্ধির সামনে ধাঁধা বা প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে নিজের দৈহিক সীমাবদ্ধতা বোঝার মাধ্যমে ‘অসীমতা’ উপলব্ধি করাও সম্ভব হয়ে থাকে। কোরানুল কারিমে এই দিকে ইশারা করেই বলা হয়েছে,
سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ
আমি আমার সমস্ত আয়াত তাদেরকে দেখাই এই দিগন্তে এবং দেহের মধ্যে, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য। তোমার প্রতিপালকের একথা কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সকল বিষয়ের সাক্ষী? (সুরা ফুচ্ছিলাত, ৪১:৫৩)
চিহ্ন বা ‘আয়াত’ নিজে একা, পৃথক ও নানান বস্তু তার মধ্য দিয়েই আলাদা ও স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু এই আলাদা আলাদা হয়ে কোনো কিছুই আয়াত হিসাবে নিজেকে দলিল বা অর্থময় করে তুলতে পারে না। মানুষ ও জগতের সমস্ত কিছু আল্লার আয়াত আকারে দেখলেই আমরা সমস্ত কিছুর মধ্যে বুদ্ধি ও চিন্তার দলিল খুঁজে পেতে পারি। এই আয়াত একান্তই আল্লাহ মানুষের জন্য বানিয়েছেন। মানুষই নিজের দেহ ও এই ব্রহ্মাণ্ডকে ‘আয়াত’ হিসাবে অনুভব করতে সক্ষম। ফলে মানুষই আল্লার সমস্ত আয়াতের উদ্দেশ্য। কেমন যেন খোদ আল্লাই মানুষকে বলছেন, ‘আমার আয়াত দেখো ও পড়ো’। এই দেখা মানে একইসাথে পড়াও বটে। কিন্তু মানুষ নিজের ‘দেহ’ বা সীমা সম্পর্কে যে উপলব্ধি হাসিল করে, সেটা কি বুদ্ধি দিয়েই করতে পারে নাকি অন্য কিছু? কেননা বুদ্ধি দিয়ে করলে কেবল ‘দেহ’ বোঝা হয় না, কেননা বুদ্ধি সরাসরি দেহকে বুঝতে পারে না। দেহ তো পরদা, আর বুদ্ধি হোল ‘নূর’, যা একইসাথে বিমূর্ত ও অ-লৌকিকও বটে। আমরা বুদ্ধিকে চিনি কোনো বস্তুর বিশেষ গুণ বা আকার মানুষের মধ্যে হাসিল করতে গেলে। বুদ্ধির রূপ বুদ্ধির প্রকাশ আকারেই বুঝা যায়। একইভাবে ইন্দ্রিয়ের রূপ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ দিয়েই আমরা বুঝি। কিন্তু ‘দেহ’কে অনুভব করা, বোঝা বা আস্বাদন করা মানে সমগ্র জিনিসটাই বোঝা ও হাসিল করা (حصول الشيء الكلي)। কাজেই ‘দেহ’ বা সীমার জ্ঞান কোনো খণ্ডের জ্ঞান নয়, বরং অখণ্ড বা সামান্যের জ্ঞানও বটে। ‘বুদ্ধি’ শুরুতেই দেহকে উপেক্ষা করতে পারে, কিংবা পারে খণ্ড করতে। কিন্তু মানুষ নিজের সম্বন্ধে এই জীবন্ত উপলব্ধি ঘটলেই একটা সমগ্র ও সর্বজনীন সত্তার ধারণায় উপনীত হতে পারে। মানুষের বাইরে যা আছে, তা সবই ফলে খণ্ড বা বিশেষ। মানুষ নিজের জ্ঞান, আরও পরিষ্কারভাবে বললে নিজের সীমার উপলব্ধি অর্জন করলেই সমস্ত খণ্ড ও বিশেষের জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। ফলে দেহের সীমা একটা নির্বেশেষ ও সামান্য ধারণা হিসাবে যা খণ্ডে খণ্ডে অসীমভাবে ছড়িয়ে আছে, তাকে ধারণ করার বিশেষ পাত্রও বটে। এই অর্থেই আমরা বলি, মানুষের শরীর পাত্রের মতো (مثل الآنية) জগতনামী সমস্ত কিছুকে ধরে আছে।
২. আরবি কাব্যে ভাষার প্রকাশ ও ‘দেহ’
এই যে আমার দেখায় আমি ‘আল্লার আয়াত’ (آياتنا) এবং আমাকে যে আমিই পড়তে পারি, এই বোধ কেবল ইসলামের মধ্য দিয়েই প্রথম আরবি ভাষায় হাজির হয়েছে। আমি বলেছি আরবি কাব্যে ‘পড়া’ (قراءة) বিষয়টাও নতুন। কোরানের মাধ্যমে মানুষ গীতিকার, সুরকার বা শ্রোতা হবার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুনভাবে ‘পড়া’ ধারণাটি যুক্ত হয়েছে। কেননা পড়ার মধ্যে পেছনের তিনটি স্তর দিয়ে সবচেয়ে কঠিন কর্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়। পড়া বা পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে ‘সৃজনশীলতা’ কিংবা বলা যায় তার ‘বিচারিক ও বিবেকবান শক্তির’ বিকাশ ঘটে। পড়ার তিনটি স্তরে মানুষ নিজেকেই বারেবারে রূপান্তর করে নিজেকেই রূপদান করে। কেননা আমি নিজেকে পড়ার ‘বিষয়’ বানালেই আমি পড়তে পারি। এইভাবে আমি নিজেই আল্লার বাস্তবিক দলিল হিসাবে হাজির হই। এই যা আছে, যা উপস্থিত, সেটা আমার মধ্য দিয়েই সমগ্রে রূপান্তরিত হয়। ‘আয়াত’ মানে নিজ কর্তাকে বিষয়ে রূপ দেওয়া, আরও সরল ভাষায় বললে নিজেকেই ‘আগে’ অনুমান করা। সেই কারণে কোরান ‘আমি’ বা অপর, কিংবা চিন্তার কর্তা ও বিষয় বলে কোনো বাইনারি বা ফারাক কাটা হয় নাই। মানুষ নিজের সঙ্গে জগতের সজ্ঞান সম্পর্ক নির্ধারণ করার মধ্য দিয়েই ‘আল্লার আয়াত’ হিসাবে হাজির হয়। ফলে মানুষ পড়া এবং তার মধ্য দিয়ে জগৎকে উপলব্ধি করার দ্বারা আল্লার ‘রব নামের উসিলা’ বোঝে। ইসলামে আরবি কাব্য ও ভাষার পরিমণ্ডলে নতুনভাবে পড়ার কথা বলতে হয়েছে।
এই আয়াতের বুননে মানুষ ‘রবের ইসমে’ বলার মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে আল্লার সবচেয়ে জীবন্ত ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মুখোমুখি হয়। কোরানে ‘আল্লার নামের উসিলা’র ব্যবহার দেখি, এটা সবাই জানে। এতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু সুরা আলাকে নবিজি আল্লার রুবুবিয়াতের দলিলে পড়ার নির্দেশ লাভ করেন। রুবুবিয়াতের দলিল হয়ে উঠছে আল্লার সবচেয়ে বাস্তব আয়াত বা চিহ্নের দলিল। হেরা গুহার নির্জন ও নিঃসঙ্গ অন্বেষার মধ্যে নবিজির ‘ওহী’ রবের নাম পড়ে শুরু হয়। ‘ওহী’ হাজির হয়েছে রুবুবিয়াতের সাক্ষ্য মেনে।
এই হিসাবে মানুষের ভাষা, কল্পনা, উপলব্ধি বা বুদ্ধি সমস্ত কিছুর অধীনেই আল্লার রব নামের প্রকাশ ঘটা সম্ভব। মানুষ নিজেকে পড়ার মাধ্যমে সেই রব নামই পাঠ করে। কেননা সে নিজেও এই সর্বজনীন রুবুবিয়াতের অধীনে প্রজাতিরূপ সত্তা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই পড়ার ঘটনাটা মানুষের উপলব্ধির স্তরে আল্লার সর্বজনীন প্রকাশ ঘটাও বটে। বলাই বাহুল্য তৎকালীন কাব্যের মধ্যে এই ধরনের অভিব্যক্তি আসে নাই। কাব্য নিজেকে যুদ্ধের হাতিয়ার বানিয়েছে, ধর্মের মহিমা গ্রহণ করেছে, মানুষকে শুধু নিজের বৈষয়িক বাসনার মধ্যেই সীমিত করেছে কিংবা একটা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা টিকিয়ে রাখবার মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র হয়েছে। আরবি কবিতা এর বাইরে আল্লার আয়াত হিসাবে কবির কর্তাসত্তাকে হাজির করতে পারে নাই। কোরানের বরাতে আমরা বুঝি কবির কর্তাসত্তা মানে, তার মধ্যে নিজেকে পাঠ করার হিম্মত, কিংবা নিজের সীমার মধ্যে গায়েবে আত্ম-সমর্পণ করার ক্ষমতা। এই অবস্থায় আরবি কাব্য কাব্যিকতা ও ভাবুকতার দিক থেকে যদিও কবি ও কবিতার বিষয় নির্ধারণ করতে পেরেছে, কিন্তু জাহেলি যুগের কাব্য নিজের ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। কাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরবদের বিভক্তি, যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানির ক্ষেত্র। কাব্যের বিভিন্ন রূপ দেখেই বোঝা যায় আরবরা কাব্যকে শত্রুপক্ষ ঘায়েল করার জন্যই ব্যবহার করত। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের জাহেলি কবি বাশার বিন আবু খাজেম আসাদি (بشر بن أبي خازم الأسدي) তাঁর দুশমনদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন—
.. وينصرنا قوم غضاب عليكم
متى نَدْعُهم يوماً الى الحرب يركب
…وخيلُ تُنادى من بعيد ، وراكب
حثيث بأسباب المنية يضرب
এই শত্রুরা, হুঁশিয়ার থাকো! আমাদের সাহায্যে আসতেছে একদল রগচটা লোক তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আমরা যখনই তাদেরকে যুদ্ধের ডাক দেব, তারা ঘোড়ায় চড়বে। ঘোড়া এবং যোদ্ধারা যখন মিলিত হবে, তারা খুব ক্ষিপ্রভাবে হাতে মরণের সব অস্ত্র নিয়ে তোমাদের আঘাত করবে (১৫)।
আরবি ভাষায় কাব্যচর্চার এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেখে আমরা বুঝি, এইখানে ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘অপর’কে নাই করবার ময়দান (المنفي)। ‘নাই’ বলতে বুঝিয়েছি অপরকে অপসারণ ও অপরায়ন (alienation) (১৬)। কিংবা অপরকে খুন করবার হাতিয়ার। আরও সহজ ভাষায় বললে এই ভাষা জীবন্ত মানুষের পরিসরে, দুই দিকের সম্পর্ক একটি বাতচিতের পরিসর তৈরি না করে দ্বন্দ্ব তৈরির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। এই নাইকরণের মধ্য দিয়ে আরবি ভাষা আসলে নিজের ভাষিক বিকাশের মধ্যে ‘অপর’ কী তার স্বরূপ চিনতে পারে নাই। কিন্তু এর মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিসত্তাও অত্যন্ত নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়। কেননা এই সকল মানুষই নিজের কর্তব্য ভুলে গিয়ে নিজের অপরকে নাই করে তোলার ফেরে পড়ে। তারা বোঝে নাই এই মানুষের দলিলে কী ‘নাই’ (العدم) হয়, আর কী ‘আছে’ (الوجود) হয়। কিংবা কীভাবে কোনো কিছু ‘নাই’ করা যায়, আর কীভাবে কোনো কিছু ‘আছে’ হয়? অথবা উজুদের ভাণ্ডে কীভাবে ‘নাই’ থেকে আছে হয় বা ‘আছে’ থেকে ‘নাই’ হয়? এই প্রশ্নগুলি ইসলামের আগমনে ‘গায়েবের’ পাঠ ও পর্যালোচনায় রূপ নেয়। যা আসলে ‘নাই’ কথাটির পুরাপুরি বাস্তব ও রাজনৈতিক সমাধান আকারেই নাজিল হয়।
শুরুর কথা হিসাবে বলে রাখি কোরানে এই আমি বা অপরের মাঝখানে এই ধরনের কোনো বিভাজন মানা হয় না। কেননা মানুষ তার ভাষা, চিন্তা বা কল্পনার মধ্যে বাইরে যা প্রক্ষেপ করে, সেটা তার নিজেরই কর্তাসত্তার অংশ। কিন্তু সেই ‘অপর’ বা ‘নাই’ কিংবা অসীমতা আরবি ভাষার স্বভাবে যে চরিত্র পরিগ্রহ করেছে, সেটা কখনো উপলব্ধি হয় নাই। আল্লার কালাম ও ওহীর দিক থেকে তাকে চিহ্নিত করা গেলে আমাদের এই আলাপের ‘সারটুকু’ এসেছে বলে মনে হবে। আরবি ভাষার স্বভাবে ‘নাইকরণের রূপ’ কী হতে পারে, সেটা নিয়ে অনেকের কথাই বলা যায়। কিন্তু এই উপলব্ধি একজন পরিচ্ছন্ন মনের কবি হিসাবে এদোনিস মশাইকে খুবই সরল ভাষায় বলতে দেখি। তিনি দাবি করছেন, আরবের ভাষা নিজের সন্তানকেই নফি করে হাজির হয়। এদোনিস মশাই ঠিকই ধরেছেন—
“আমি যে ভাষায় লিখি সে যে আমাকেই নফি করে।
মা নিজের সন্তানকে নফি করে, কাব্যিকভাবে বললে— যখন তার গর্ভে সে গঠন লাভ করে: এই প্রতীকী ছবিতে আরব কবি ও তার ভাষার বাস্তব সম্পর্কটা ফুটে ওঠে।” (১৭) এরপর আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলেন—
“তবে ইসলামের নবুওয়াত এই নীতির অধীনে গড়ে উঠেছে আরেকটি নতুন সময়ের জন্য। সে ভাষাকে নেতিকরণের ময়দান থেকে নিয়ে এসে জমিনে প্রতিষ্ঠা দেয়। ওহীর সাম্রাজ্যে তার ঘর বানিয়ে দেয়। আর ওহী এই নেতিকরণের জমিনে মুক্তি ও মাহাত্ম্যের রেসালা নিয়ে আসে। যাতে এই জমিনকে সে আশমানে পরিণত করে তুলতে পারে।”
এদোনিস মশাইয়ের এই বরাতে এটা স্পষ্ট, আরবি ভাষার মধ্যে ‘নাইকরণের’ ঘটনা আদিকাল থেকেই আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে হুঁশে-বেহুঁশে জারি আছে। কিন্তু ‘নাই’ বলতে অনেক কিছুই বুঝাই। অন্তত আরবি ভাষার মধ্যে ‘নাই’ বলতে একটা নতুন ধারণা হাজির হয়েছে ইসলামে। কিন্তু এদোনিস মশায় এত হুঁশিয়ার লোক হয়েও এটা ধরতে পারেন নাই। তিনি ‘নাইকরণ’ বলতে কাব্যিকভাবেও অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি সংজ্ঞায়ন করেছেন:
“সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যেই নফি বা নেতির নানান রূপ ও ধরন রয়েছে। এটা শুধু বঞ্চিত করা বা আলাদা করার অর্থে নয়, বরং আরও অনেক অর্থ দেয়। কেননা এটা একইসাথে একটা সংজ্ঞারূপ বা চলার সুনির্দিষ্ট পথও বটে। কেননা ওই সবকিছুর আগে এটা মানুষকে নিজের অন্তর্নিহিত রসিকজনা থেকে বের করে বাইরে সাধারণ আকারে হাজির করে। এদোনিস বলেন— আরবের যে কোনো প্রতিভাবান লোক এই নেতিকরণের শিকার হয়েছেন। যেমন— দাসত্ববরণ, কারা-নির্যাতন, দেশ থেকে তাড়ানো কিংবা জুলুম।”
এদোনিসের কবির মন এর চাইতে বেশি দূর দেখতে পারে নাই। এটা নিয়ে আফশোসের কিছু নাই। তবে তাঁকে আমার শুকরিয়া জানাই। তিনি বুঝতে পেরেছেন আরবি ভাষার স্বভাবে নেতিকরণের ধারণা দানা বেঁধেছে। কিন্তু একজন তালেবুল ইলম হিসাবে আমার কৌতুহূলের জায়গা হোল ইসলামের আগের আরব কাব্যকে ভাষাগত প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে তার দুর্দান্ত প্রতিভা ও অবদান। কিন্তু জাহেলি যুগের পরে ইসলামের দিক থেকে ভাষা ও চিন্তার বিকাশে আরবি ভাষায় যেসব নতুন ও মৌলিক উপাদান দৃশ্যমান হয়েছে, সেই দিকে তিনি ভিন্ন চোখে দেখেন। এইখানে এলে তার আগে ও পরের মধ্যে একটা দ্বিধা তৈরি হয়। কেমন যেন তিনি হাতিয়ারকে আলাপের বিষয় অনুযায়ী না বানিয়ে বিষয়কে হাতিয়ারের লক্ষ্যে পরিণত করছেন। তাঁকে পড়তে গেলে এই বিভ্রাট যে কারও নজর কেড়ে নেয়। যা-ই হোক, আমাদের এখানে এটা প্রমাণ করার বিষয় না। বরং আরবি ভাষার স্বভাব ও গতিপ্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে কোনো সহজ পথ আছে কি না, সেটা খুঁজে বের করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমি এই দাবির পক্ষে আরবের কবি মুহালহাল বিন রবীআর (১৮) কবিতা থেকে একটি দলিল পেশ করছি। তিনি বলেন,
وصار الليل مشتملاً علينا
كان الليل ليس له نَهارُ
এই রাত আমাদের ওপর ছেয়ে গেছে,
সে রাত এমন যার নাই কোনো দিন।
এই কাব্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে দিনকে ‘নাই’ করে রাত দখল করে নিয়েছে কবির সকল ভাবনাকে। কবিতার আগপিছ মিলালে বুঝি মুহালহাল নিজের অসহায় জীবন নিয়ে শান্তিতে ছিলেন না। তাই এই লোক দিনকে নিজের রাতনামী প্রতীকী অবস্থার বাইরে একটা দুরধিগম্য অবস্থান মনে করে বসে আছে। ফলে রাতের পরিবেশে এই বিশাল শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে তিনি একা ভয়ে কাতর থাকেন। রাত দেখে মরুভূমির মধ্যে নির্জীব ও নিথর জড়বস্তুগুলি তার সামনে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে। এই কবি তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে ডাক দেয়, কিন্তু কেউ তার পাশে নাই। কেউ আশমানের বৃষ্টি দিয়ে এই নিথর ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে না। এই উপলব্ধি কেমন যেন মানুষের ভীতিকাতর অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তায় মানুষের উপলব্ধি হয় না (ক) ‘নাইকরণ’ মানে নিজের মধ্য থাকা নানা কল্পনা, শক্তি বা বৃত্তি নেতিকরণ করে বাইরে পেশ করা। এবং (খ) নিজের প্রজাতিসত্তা, যাকে সে ‘অপর’ করে তুলেছে, সেটা তার মধ্যে থাকা নানান রসবৃত্তি, যেমন প্রেম, বন্ধুত্ব, মাতৃত্ব বা ভ্রাতৃত্ব বোধ দিয়ে আবার আত্মস্থ করাও সম্ভব। এই দুটো বিভাজনের আলোকে এবার আমরা আরবি কাব্যের মধ্যে আল্লার ওহী ও কালামের দিক থেকে আরবি ভাষার সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবতে পারি।
৩. আল্লার ওহী ও কালামের প্রকাশ এবং ভাষা
কোরান নাজিলের মাধ্যমে আরবি ভাষার স্বভাবে যে নতুন অর্থ ও দ্যোতনা যোগ হয়েছে, সেটা অনস্বীকার্য। আরবি ভাষায় জাহেলি কবিরা যেসব পদ্ধতি ও প্রকরণের অধীন কাব্য ও বাক্য রচনা করত, সেটা তাদের ধর্মবোধ আকারেই গড়ে উঠেছে। এই হিসাবে আল্লার কালাম মানুষের ভাষার বাইরে বিমূর্ত কোনো ভাব, আদর্শ বা কল্পনা হাজির করলে সেটা তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারত না। আরবে সাহিত্য ও কাব্যিকতায় কবিদের যে প্রতিভা ও শক্তির বিকাশ ঘটেছে, কোরানের পক্ষে সেটা মোকাবিলা করাও অসম্ভব হয়ে যেত। কোরানুল কারিমের ভাষা তাই আরবি ভাষার সম্বোধন ও গাঠনিক-প্রকৃতির অনুসরণ না করে মানুষের সামনে আল্লার মো’জেজা হিসাবে হাজির হয়েছে। ফলে আরব জীবনের ভাষা ও ভাব কোরানের দলিল হয়ে উঠেছে। কোরানের নাজিলে আরবি ভাষার সমস্ত ছকবাঁধা পদ্ধতি ও কাঠামো ভেঙে পড়েছে। ভাষার জগতে এই প্রথম মানুষ নিজের কথায়, নিজের সুনির্দিষ্ট স্তর থেকে আল্লার সঙ্গে কথা বলার স্বাদ অর্জন করে। আরবরা যখন চারদিকে এক অনিশ্চয়তার গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোরানই তাকে আল্লার দলিল ও কালেমায় পরিণত করে। কোরানই মানুষকে ভাষার মধ্যে নিজের হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে শিখায়। কেননা কোরানের ভাষা মানুষের ভাষা ও সম্বোধন হিসাবেই হাজির হয়। কোরান যেহেতু নিজেকে আল্লার হুজ্জাত এবং আয়াত হিসাবে হাজির করে, এর ফলে মানুষ নিজের প্রজাতিগত সত্তার মধ্যে আল্লার দলিল হয়ে ওঠে। মানুষ নিজের ‘অপরকে’ অপরায়নের বদলে নিজের কাজে লাগাবার উপায় হাসিল করে। ফলে আরবি ভাষার স্বভাবে মানুষ নিজেকে নাই করার বদলে নিজেকে চিনবার নতুন হাতিয়ার অর্জন করে। আরব কবিরা যখন দিনের আশা না দেখে রাতকেই নিজের জন্য সাব্যস্ত করে, কোরান তখন ‘ঈমান বিল গায়েবের’ কথা নিয়ে হাজির হল। ঈমান বিলগায়েব কথাটা সেই পুরানা আরব কবিদের পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাসের গোটা মর্মকেই গোড়া থেকে কেটে ফেলে। ফলে কাব্য ও কাব্যশক্তি নিজের গুরুত্ব আর ধরে রাখতে পারেনি। আরবি কাব্য কোরানের প্রকাশভঙ্গির সামনে দুর্বল হয়ে পড়ে। ইবনে খালদুন মশায় বলেন,
জেনে রাখো, কাব্য ছিল আরবদের দেওয়ান (কাব্য-ভাণ্ডার); তাতেই তাদের শাস্ত্র, ইতিহাস ও হেকমাত সংগৃহীত হত এবং আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কাব্যচর্চায় প্রতিযোগিতা করত। উকাজের মেলায় তারা কবিতা গাইতে উপস্থিত হতেন এবং সবাই যার যার কবিতার পরচা সেখানকার স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সামনে পেশ করতেন। এমনকী আরবরা তাদের কবিতাগুলো হজ্জব্রত পালনের স্থান, তাদের পূর্বপুরুষ হজরত ইব্রাহিমের উপাসনাগৃহ পবিত্র কাবার বিভিন্ন স্তম্ভে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য মারামারি খুনাখুনি পর্যন্ত গড়াত। যেমন— ইমরুল কায়েস ইবনে হাজর, নাবিগাতু যুবিয়ানী, যুহাইর ইবনে আবু সুলমা, আনতারা ইবনে শাদ্দাদ, তরফা ইবনে আবদ, আলকামা ইবনে আবদা, আল আ’শা এবং ‘ঝুলানো সাত কবিতা’র (সাব’আয়ে মু’আল্লাকা) অন্যান্য কবিরা করেছেন। আসলে এভাবে কবিতা ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি তাদের পক্ষেই সম্ভব হত, যারা গোত্রীয় শক্তি ও আসাবিয়াত (গোঁড়ামিপনা) এবং একইসাথে মুজার জনসমাজে প্রয়োজনীয় প্রভাব-সহ কাব্য সম্পদের অধিকারী ছিল। এ কারণেই এসব কবিতার নাম ‘ঝু্লিয়ে রাখা কবিতা’ হয়ে দাঁড়ায়।
অতঃপর ইসলামের প্রথম দিকে আরবরা এমন প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। কারণ তখন তারা ইসলাম, নবুওয়াত ওহী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কোরানের ভঙ্গি, বিন্যাস ও বাক্যরীতি তাদেরকে তখন অভিভূত করে ফেলে। ফলে তারা কিছুকাল বাক্শক্তিটাই হারিয়ে ফেলে এবং গদ্য-পদ্য সম্পর্কে তাদের অনুসন্ধিৎসাও থেমে যায় (১৯)।
খালদুনের লেখায় আরবদের পরিস্থিতির যে চিত্রটা ফুটে উঠেছে, সেটা আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের উপলব্ধির জায়গায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। ভাষার ইতিহাসে এরকম ঘটনা অনেক পাওয়া যাবে। আমরা বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাবে দেখি মানুষ নিজের বর্তমানতার দিক থেকে পেছনের ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে বিযুক্ত মনে করে। কারণ এই নতুন অবস্থায় ধর্ম মানুষকে আস্থা ও বিশ্বাসের নতুন শক্তি দেয়। মানুষ তখন ধর্মের বাক্যকেই নিজের বিদ্যমানতার অধীনে প্রকাশ করে। কিন্তু এর ফলে সাধারণ ভাষার স্বভাবের সঙ্গে দীর্ঘ বিরতি ঘটতে পারে। কারণ এই আবির্ভাব মানুষের কল্পনা, বুদ্ধি ও ভক্তিবৃত্তির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে। মানুষ যা কল্পনা করে, ভাবে, ভক্তি করে বা আস্বাদন করে, ইসলামের মধ্য দিয়ে আল্লার কালাম সেখানে তার নিজেকেই চূড়ান্ত হুজ্জাত আকারে হাজির করে। আল্লায় কথা বলেন মানে মানুষের সঙ্গে আল্লাহ স্বয়ং দরবার বসিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলেন সরাসরি, কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া, তিনি প্রশ্ন করেন, উপমা দেন, ভাব ও মর্মের মধ্যে কারিগরি করেন। তিনি নিজেই মানুষের মধ্যে, মানুষের ভাষায় মুখোমুখি হলেন। কাজে কাজেই কোরানের আল্লাহ নিজেকে মানুষের ‘অপরায়নের’ মধ্যে ধরা দেন নাই। বাইরের বাক্শক্তিহীন প্রকৃতিকে বা নিজের দুশমনকে ভাষার মধ্যে অপরায়ন করা যায়। কিন্তু যিনি নিজে গায়েব, যে খোদা নিজেকে হাজির করলেন, গায়েব হিসাবে, যিনি নাই, অনুপস্থিত ও অধরা— তাঁকে কী করে অপরায়ন করা যায়?
ইসলামে প্রকৃতি বা জগৎ কিংবা এই মনুষ্য প্রজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ কোরান আকারে খোদ ভাষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মুশরিকরা যেহেতু ‘গায়েবে আত্মসমর্পণ’ কথাটা বোঝে নাই, তাই এই জগতের কীর্তিকর্মা দেখে নিজের হুঁশ হারিয়ে বসেছিল। মরুভূমিতে বৃষ্টির অভাব সবচেয়ে বেশি। বৃষ্টি না হলে তাদের সমস্ত সম্পদ সূর্যের তাপে কয়লা হয়ে যেত। আরবরা তাই বৃষ্টির জন্য হুবালের পূজা শুরু করে। ইট, পাথর, বালির মধ্যে তারা নিজের হারিয়ে ফেলা আকাঙ্ক্ষা ও শক্তির প্রকাশ অনুভব করত (২০)। এর ফলে আরবি ভাষা ইন্দ্রিয়কে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করবার শক্তিসম্পন্ন ভাষা হয়ে ওঠে। কিন্তু আরবি ভাষায় এভাবে মানুষ নিজেকে একান্তই বৈষয়িকতা বা ইহলৌকিকতার দাসে পরিণত করে। মানুষ কেমন যেন ইহলোক বা ইন্দ্রিয়জগতের তাঁবেদার বা বিষয়ে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয়কে অনুভব করবার মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দ আছে, জীবনকে সয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, কিংবা রুহানিয়াতের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে জগতের খলিফা হিসাবে হাজির করতে পারে না। কেননা রুহানিয়াতের অধীন হওয়া মানেই খলিফার জীবনযাপন করা। যা কিছু মানুষের জাগতিকতার মধ্যে মানুষকে হাজির করার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে, তাকে বিলয় ঘটিয়েই আগমন ঘটে রুহানিয়াতের।
এইখান থেকে আমরা বুঝি, কোরান আরবদের মধ্যে চালু যেসব বিশ্বাস, কল্পনা ও আন্দাজ, সেগুলোর বিপরীতে বুদ্ধির চূড়ান্ত হুজ্জাত হাজির করে। তাদের ভাষা, চিন্তা ও উপলব্ধির সামনে বয়ান ও ফুরকান আকারে হাজির হয়। তাই কোরান নিজেকে ‘বই’ বা ‘লিখিত গ্রন্থ’ হিসাবে হাজির করবার বদলে নিজেকে হাজির করেছে ‘কিতাব’ আকারে। আল্লার আয়াত যা বাইরে সাধারণ আকারে হাজির রয়েছে, কোরান হয়েছে তার পক্ষে আল্লার আয়াত, এবং গোটা জগৎই কোরানের পক্ষে হয়েছে আল্লার সাক্ষ্য। কোরান বিশেষ ভাষার মধ্যে বিশেষ প্রকাশ, অতি স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সাবলীল ও মাধুর্যমণ্ডিত। কোরান নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ভাষাকে হাতিয়ার বানিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সমস্ত হুজ্জাত ও দলিলের সাক্ষ্য হিসাবে ইতিহাসে আল্লার খলিফার ঘোষণা হল। খলিফা; যার ভাষা আছে, যার ভাষায় আল্লাহ কালাম দেন, ওহী নাজিল করেন। খলিফা; যার মধ্যে শাহেদ (সাক্ষী) এবং মাশহুদ (সাক্ষ্যরূপ) (২১) উভয়ই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। যার মধ্য দিয়ে জগৎকে দেখা যায়, এবং যাকে জগতের মধ্য দিয়েই দেখা যায়। কোরানে খলিফার মেসাল ও উসওয়া হিসাবে নবিজিকে তাই বলা হল ‘পড়ো’। কেননা মানুষ নিজেকে আয়াতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে ওহীর করুণা ও বৃষ্টিতে নিজেকে সিক্ত করতে পারে। বলা যায় মানুষ এইবার নিজের সচেতন ও সজ্ঞান বৃত্তির মধ্য দিয়ে অপরকে আত্মস্থ করা শিখল।
ফলে কোরানে মানুষ হয়ে উঠেছে খলিফা, যার মধ্য দিয়ে গোটা জগতের মধ্যে মানুষ নিজ কর্তব্য আদায়ে তৎপর হয়। যেখানে মানুষ কেবল বুদ্ধির কর্তারূপে ব্যক্ত নয়, বরং তার আমল বা কর্ম-সহই ব্যক্ত হয়। মানুষ তার আবেগ ও অনুভূতির মূল্য বোঝে, বোঝে প্রকৃতির সঙ্গে তার আমানতদারির সম্পর্ক, ফলে ‘প্রকৃতি’ একজন মুমিনের নিকটে, এমনকী বাইরের ওই অচেনা, অপরিচয় কিংবা জানের জান দুশমনও তার কাছে আল্লার আমানত আকারে হাজির হয়। ইসলামে প্রকৃতির সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব জাহেলি যুগের কবিরা করে কিংবা যারা এই ধরনের শিরকে আক্রান্ত তারা করে। তারা জানে না মানুষ নিজের এই সীমার মধ্যেই জগৎ ও প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে আল্লার ইচ্ছায় স্বাধীন। এই প্রাণপ্রকৃতি তার স্বভাব ও বুদ্ধির অনুকূলেই গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে এই জগৎ মানুষের সামনে আল্লার আয়াত আকারে হাজির হয়েছে। যাকে সে বুঝতে পারে, চাইলে অনুভব করতে পারে, কিংবা তাকে নিজের দলিল ও ভাষার অধীনেও প্রকাশ করতে পারে। ফলে কোরানের ভাষার যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সবচেয়ে জীবন্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্য থেকে। এই ধরনের দলিল নিজ যোগ্যতায় অসংখ্য অর্থ, অনুভূতি ও ব্যঞ্জনা তৈরি করতে সক্ষম। মানুষ যখনই যোগাযোগ করতে চায়, তার বাইরের এই জীবন্ত সত্তার, এই জীবন্ত মানুষ কিংবা নিজের ভাষায় এই জগৎকেই প্রকাশ করতে চায়, তখন এই দলিলকে নিজের সীমায় ধরার জন্য আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ‘নামের উসিলা’ (بإسم) নেয়। এই উসিলা ফলে সমস্ত কথা ও ভাষার যোগাযোগ ও চিহ্নব্যবস্থার শর্ত।
এটাই হাজির হয়েছে আরবি ভাষায় (বলুন, সমস্ত ভাষায়) একমাত্র সত্য হিসাবে। এমন সত্য যেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না (২২)। কোরান এই কারণে সন্দেহের কোনো সুযোগ রাখে নাই। সন্দেহ দ্বারা নিজের চিন্তারূপ সত্তার এলেম হাসিল করা গেলেও নিজের বাস্তবসত্তা, যা মানুষের বাস্তব কর্তব্য ও কর্মের ক্ষেত্র সেইখানে কাজে লাগে না। ফলে কোরানুল কারিম নিজেকে প্রকাশ করেছে মানুষকে বাস্তবতার মুখোমুখি করতে। বাস্তবতার মুখোমুখি মানে নিজের ভাষা ও চিন্তার জগতে আল্লার সঙ্গে ইসবাত ও নফির সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই কারণে যা কিছু নেতিকরণ হয়ে মানুষের বাইরে আলাদা কল্পনা করা হয়, সেটা মানুষের কাছেই আবার ফেরত নিয়ে আসার পথ দেখাতে হয়েছে। মানুষ যদি আল্লার আয়াত হয়ে থাকে, মানুষকে একইসঙ্গে ভাষা ও ভাবের দলিল হয়ে উঠতে হয়। নিজেকেই হয়ে উঠতে হয় কোরান ও ওহীর উৎস। কিন্তু মানুষের ভাষার সীমায় এই উপলব্ধি হাজির করবার জন্য কোরানে বলতে হয়েছে, আগে ‘নিজেকে গায়েবে সমর্পণ করো’। যা কোনো সন্দেহ থেকে মুক্ত, যা ওহীর মধ্য দিয়ে সত্য আকারে হাজির হয়েছে। কবিরা তোমার যা কিছু নাই করে দিয়ে বসে আছে, কিংবা যা তুমি নিজের সীমার মধ্যেই বন্দি করে রেখেছো, তাকে মুক্ত করো। ফলে কোরানে গায়েবের ধারণা একইসাথে দুই ধরনের বর্গায়নের বিপরীতে দুই ধরনের অর্থে ব্যক্ত হয়েছে।
আরব কবিরা দাবি করতে পারে: ভাষার মধ্যে ‘অপর’ বলে যা আছে সেটা তোমার অন্তর্গত নয়, বরং তোমার বাইরের শত্রু। তখন কোরান বলবে সেই ‘অপর’ নিজেই নাই, তাকে নাই করার প্রয়োজনও নাই। কেননা নাইকে নাই করা স্রেফ অর্থহীন কর্মই নয়, বরং নির্বুদ্ধিতাও বটে। কোনো কিছু নাই হয়ে থাকলে তাকে নাই করা মানে নিজের বর্তমান কর্তব্য উপেক্ষা করা। মানুষের কর্তব্য হল আল্লার খলিফা হওয়া। দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে নিজের আমানত মনে করা। ফলে ইসলাম একটা বিশ্ব উম্মাহর কথা বলে, যারা সবাই গায়েবে আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে নিজেকে খলিফার মহিমায় ভূষিত করেছে।
কবিরা বলতে পারে: তুমি নেতি করো যা তোমার অংশ নয়, যা তোমার পাবার নয়, এবং ‘নেতি’ থেকে কোনো অর্থ বের না করে তার শক্তি চিন্তা করো। কোরান বলবে মানুষ কোনো অংশে অংশে, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয়। মানুষ কোনো কিছু ‘নাই’ করে দিলে সেটা ‘নাই’ হয় না। এই পরিস্থিতি একান্তই মানুষের উজুদের অসীম ব্যঞ্জনা বা অর্থবহতা সম্পর্কে নিজের অন্তর্গত জাহেলিয়াতের ফল। মানুষের মধ্যেই ‘নাই’ থেকে আছে করার ক্ষমতা এবং ‘আছে’ থেকে নাই করবার ক্ষমতা একইসঙ্গে কাজ করে। এই কারণেই ‘মিন কিতমানিল আদামি ইলা আসালাতিল উজুদ’ (من كتمان العدم إلى أصالة الوجود) মানে ‘নাইয়ের’ মধ্যেও গোপনীয়তার পরদা হাজির থাকা। মানুষের নাইকরণ ফলে আছেকরণের শর্ত হয়ে ওঠে। কেননা মানুষের দলিলেই মানুষ নিজের পরদা অতিক্রম করতে পারে। ফলে যদি মানুষ বলে ‘আল্লাহ নাই’, তখন আছে বলাও তার মধ্যে গোপন থাকে। কোরানের তাই বলতে হয়েছে—
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ
আমি তোমার আগে যে রাসুলকেই পাঠিয়েছি, তার ওপরই আমি এই ওহী নাজিল করেছি— ‘আর কোনো ইলাহ নাই, কেবলমাত্র আমিই আছি। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।’ (২৩) (সুরা আম্বিয়া ২১:২৫)
ইসলামে ওহী ও আল্লার কালাম নিজেকে কবিদের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে নাই। বরং ভাষার মধ্যে আল্লার মহিমা ও মাহাত্ম্য কায়েম করাই তার উদ্দেশ্য। যাতে মানুষ কবি ও অকবির ফারাক মিটিয়ে দিয়ে গায়েবে আত্মসমর্পণ করতে পারে। যাতে অযথা প্রশ্ন ও সন্দেহের মধ্যে না পড়ে নিজের কাজে মনোযোগ দিতে পারে। মানুষ এখানে আল্লার ওহী ধারণ করে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। কেননা মানুষ নিজেকে প্রমাণ করবার দলিল ও শক্তি অর্জন করে। যা কিছু সে নাই করে দিতে পারে, সেটা তখন উজুদ ও নাইয়ের মর্মের বাইরে বের হয়ে যায়। তিনিই হয়ে ওঠেন আমার উজুদের শর্ত, তিনি সকল নান্দনিকতা, সৌন্দর্যবোধ, এশেক ও মোহাব্বাতের মোকসুদ হয়ে পড়েন। আমি যখন তাকে অনুভব করি, আমি নিজের অনুভব থেকে আরও ওপরে উঠে যাই। আমি যখন তার চিন্তা করি, আমি চিন্তার দলিল খুঁজে পাই, যখন তাকে মাশুক বানাই, আমি হয়ে যাই তার আশেক। সেই ‘মাশুক’ বা ‘দলিল’, আমি নিজেই। কেননা আমার মধ্যে এই এশেক আছে বলেই আমি প্রেম করি, আমি আছি বলেই আমি চিন্তা করি। আমিই এখানে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির কর্তব্যের একমাত্র বাস্তব লক্ষ্য। ফলে গায়েবে ঈমান আনার মধ্য দিয়ে ‘আমি’ই লক্ষ্য হই। কিন্তু আমি তো একজন মানুষ না, আমি এই মনুষ্য প্রজাতির একটি সদস্য মাত্র। আল্লাহ যদি এই প্রজাতির অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি বা ভাষিক ব্যঞ্জনা আকারে হাজির হন— তিনি হয়ে পড়েন কূলহীন দরিয়া। তাতে যার যত গভীরতা, সে তত বেশি ডোবে। যার কোনো গভীরতা নাই, সে কূলে দাঁড়িয়ে শুকিয়ে মরে।
গ্রন্থসূত্র :
১। এই সাধারণ অনুমান বা সিদ্ধসূত্রটি আমার অপ্রকাশিত আরেকটি লেখায় ব্যাখ্যা করেছি। লেখাটির নাম: ‘আহলুল কিতাব ও কোরআনের ঐতিহাসিক ধর্মচিন্তা’।
২। শরীরী বস্তু, মুখমণ্ডল কিম্বা ‘চেহারা’ উদ্দেশ্য।
৩। এই অর্থে বিশেষত এই আয়াতের দিকে ইশারা করা হয়েছে,স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়েছিলেন (আর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে,) আমি কি তোমাদের রব নই? সকলে উত্তর দিয়েছিল, ‘কেন নয়? আমরা সকলে সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ (এ স্বীকারোক্তি আমি এজন্য নিয়েছিলাম) যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, ‘আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।’
৪। এই প্রসঙ্গে সুরা নূরের এই আয়াতের দিকে আমি ইশারা করেছি। বিস্তারিত আলোচনা করেছি সুরা সাফফাতের মওত সংক্রান্ত লেখায়। এ সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালির বিখ্যাত কিতাবের নাম ‘মিশকাতুল আনওয়ার’। ইরশাদ করা হয়েছে,
আল্লাহ দুনিয়া ও আসমানের নূর। তাঁর নূরের মেসাল— যেন একটি তাকে একটি প্রদীপ রাখা আছে। প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের ভেতর। এ যেন নক্ষত্র, মুক্তার মত চকমকা। প্রদীপটিতে আগুন লাগানো বরকতপূর্ণ যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা, তার আলো না (কেবল) পুবে পড়ে, না (কেবল) পশ্চিমে। মনে হয়, যেন আগুনের ছোঁয়া না লাগলেও তা এমনিই আলো দেবে। নূরের উপর নূর, ‘নূরুন আলা নূর’। আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ নূরের উসিলায় হেদায়েত করেন। আল্লাহ মানুষের সামনে নানান মেসাল বর্ণনা করেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানী। (আন-নূর ২৪:৩৫)
৫। আবু হাইয়ান তাওহীদি, (১৯৯২, ২২৪), ‘আল মুকাবাসাত’, দারু সা’আদ আস সাব্বাহ।
৬। ইবনে খালদুন বলেন, “নবিজির যুগে সকল হুকুম-আহকাম তাঁর কাছ থেকেই আসত। সেই সব আহকাম তার মধ্যে ওহী করা হত এবং তিনি সেসব সরাসরি নিজের বক্তব্য এবং কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে ‘মৌখিক কথাবার্তার’ মধ্য দিয়ে পৌঁছে দিতেন। তখন কোনো বাড়তি চিন্তা বা বিশ্লেষণ খাটানোর প্রয়োজন ছিল না।” দেখুন: ইবনে খালদুন, (২০১৫, ৪৭২), ‘আল মুকাদ্দিমাহ’, মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, ISBN 978-9933-23-029-6।
৭। খলিল বিন আহমাদ ফারাহিদি, (৫: ৩৭৮), ‘কিতাবুল আইন’, দার ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, মিশর।
৮। ফুয়াদ সেজগিন, (১৯৯১, ২, ১: ১৪-১৫), ‘তারীখুত তুরাস আল আরাবি’, অনু. মাহমুদ ফাহমি হিজাযী, জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়্যাহ, রিয়াদ। ফুয়াদ সেজগিন এই আলাপে গোল্ডজিহারের একটি গবেষণারও সন্ধান দিয়েছেন। লেখাটা হল: Goldziher, ‘Bemerkungen zur arabischen Trauerpoesie’, in: WZKM 16/1902/607 ff.; und Gesammeltel Schriften IV, 361 ff.
৯। মুহাম্মাদ বিন এইদমার আল মুস্তা’সিমি, (২০১৫, ৫/৩৯৩), ‘আদ দুর্রুল ফারিদ ওয়া বাইতুল কাসীদ’, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন।
১০। তাহের বিন আশুর, (২০১৫, ৩/ ১৪৮১), ‘জামহারাতু মাকালাত ওয়া রাসায়েল’, দারুন নাফায়েস, জর্ডান।
আব্দুল্লাহ তাইয়িব আল মাজযুব, (১৯৮৯, ৪/১৯৪), ‘আল মুরশিদ ইলা ফাহমি আশআরিল আরব’, দারুল আসার আল ইসলামিয়া, কুয়েত।
১১। আয়াতের প্রথম অংশের দিকে ইঙ্গিত।
১২। আয়াতের দ্বিতীয় অংশের দিকে ইঙ্গিত।
১৩। মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবি, ‘আল ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ’ (৩/২৩৭), মুয়াসসাতু আহলি বায়িত (অনলাইন, eshia)।
ইবনে সিনা, ‘রিসালাহ ফী মা’রিফাতিন নাফসিন নাতিকাহ’ (২০১৮, ৯-১০), কায়রো, ISBN 978-1-5283-1560-0।
১৪। আমি এই বিষয়ে সহীহ সনদে বোখারি-সহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবে বর্ণিত ওহী নাজিলের ঘটনার দিকে ইশারা দিয়েছি। ওহীর প্রথম নাজিল হবার মুহূর্তে যখন জিব্রাঈল আমীন নবিজিকে পড়তে বলেন, নবিজি ‘পড়া’ কথাটা বুঝে উঠতে পারেন নাই। কেননা তখনই নবিজি নিজের শরীরের সীমা আন্দাজ করতে পারেন নাই। ‘নবিজির শরীর’ ফলে ‘চাপ দেবার’ ঘটনা আকারে হাজির হয়েছে নীচের এই হাদিসে। রেওয়ায়েতে এসেছে, হেরা গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওহী আসল। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বলল, ‘পাঠ করুন’। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম’) বলেন: আমি বললাম, ‘আমি পড়তে জানি না’। তিনি বলেন: অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুব কষ্ট হল। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘পাঠ করুন’। আমি বললাম: ‘আমি তো পড়তে জানি না’। সে দ্বিতীয় বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুব কষ্ট হল। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘পাঠ করুন’। আমি উত্তর দিলাম, ‘আমি তো পড়তে জানি না’। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম’) বলেন, অতঃপর তৃতীয় বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে, পড়ো হে, আর জানিয়ে দাও তোমার রব যে সবচেয়ে মহান”— (সূরা আলাক্ব ৯৬/১-৩)। অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লার রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম’) ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩, ৩৩৯২, ৪৯৫৩, ৪৯৫৫, ৪৯৫৬, ৪৯৫৭, ৬৯৮২; মুসলিম ১/৭৩ হাঃ ১৬০, আহমাদ ২৬০১৮)
১৫। এদোনিস (১৯৯৬, ১/৪৫), ‘দিওয়ানুশ শি’র আল আরাবি’, দারুল মাদা, বৈরুত।
১৬। এই ধারণাটা ল্যুদভিগ ফয়েরবাখের। তবে বলে রাখি, এইখানে ফয়েরবাখের ধারণাটা পরিষ্কার করে হাজির করা আমার উদ্দেশ্য না। ফয়েরবাখের বরাত ধরে এই আলাপ করতে গেলে অনেক কথাই বলতে হবে। এই আলাপটা ধরার জন্য শুধু এতটুকু বলে রাখি, ফয়েরবাখের দিক থেকে পুরা জার্মান ভাবাদর্শের প্রতি একটা কড়া অভিযোগ হল জার্মানির গোটা ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিকেরা (Philosophers of religion) রোমান পৌত্তলিক দর্শনকেই খ্রিস্টান ধর্মের বিশেষ উপলব্ধি বোঝার জন্য ব্যবহার করেছেন। ফলে এই ধারণাটা খ্রিস্টান ধর্মের খোদাকে সমস্ত পৌত্তলিক দোষগুণ থেকে পরিষ্কার করার জন্য তিনি ব্যবহার করেন। আমিও আরব পৌত্তলিকদের বোঝার জন্যই এটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু ফয়েরবাখ এটা ব্যবহার করে পুনরায় খ্রিস্টান খোদাকেই নফি করার কর্তব্য পালন করেন। ফয়েরবাখ দেখিয়েছেন, খ্রিস্টানিটির ঐতিহাসিক উপলব্ধির মধ্যেই নাস্তিকতা বা খোদাকে নেতিকরণ করার অর্থটা রয়ে গেছে। পশ্চিমা দর্শনের এই গুরুতর জিজ্ঞাসার সমাধান দেবার কারণে ফয়েরবাখ অবশ্যই কৃতিত্বের ভাগীদার। তবে এইখান থেকেই আবার ফয়েরবাখ এবং আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে। আমরা ‘ঈমান বিলগায়েব’-এর সোয়ালে প্রবেশ করি।
১৭। এদোনিস (১৯৯৩, ১৪-১৫) ‘আন নাচ্ছুল কুরানী ওয়া আফাকুল কিতাবাহ’, দারুল আদাব, বৈরুত।
১৮। মুহালহাল বিন রবী’আহ আরবদেশের কিংবদন্তী কবি হিসাবে পরিচিত। ধারণা করা হয়, তিনি ষষ্ঠ হিজরির মধ্যে বেঁচে ছিলেন। ইবনে সাল্লাম জুমহীর মতে মুহালহাল আরবি ভাষায় প্রথম কসিদা রচনা করেন। তাঁর কবিতায় তাঁর ভাই কুলাইবের মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। যাকে জুসসাস নামের এক লোক হত্যা করে। এর ফলে বনি বকর ও তাগলিবের মধ্য দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে যুদ্ধ জারি ছিল। তাঁর আসল নাম হল আদি। ভাষার সাবলীলতা, মাধুর্য ও সৌন্দর্যের কারণে তাঁকে ‘মুহালহাল’ বলা হত। দ্রষ্টব্য: ইবনে সাল্লাম জুমহী (মাকতাবায়ে শামেলা, ১/৩৯), ‘তাবাকাতু ফুহুলিশ শু’আরা’, দারুল মাদানি, জেদ্দা; ‘মু’জামুশ শু’আরাইল আরাব’ (৮৪৭ পৃ.), মাকতাবায়ে শামেলা (অনলাইন); যিরাকলী (৪/২১৯-২২০), ‘আল আ’লাম’, দারুল ইলম, মাকতাবায়ে শামেলা (অনলাইন)।
১৯। ইবনে খালদুন (২০১৫, ৬৫৩), ‘আল মুকাদ্দিমাহ’, মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, ISBN 978-9933-23-029-6।
২০। ইমাম ইবনে কাসীর ‘আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া’র মধ্যে বর্ণনা করেন: ইবন হিশাম (র) বলেন, একদল আহলে ইলম আমাকে জানিয়েছেন যে, একবার আমর ইবনে লুহাই কোনো এক কাজে মক্কা থেকে সিরিয়া গমন করে। বালকা অঞ্চলে মা’আব নামক স্থানে গিয়ে সে দেখতে পায় যে, সেখানকার লোকজন প্রতিমা পূজা করছে। ওই অঞ্চলে তখন বসবাস করত আমালীক সম্প্রদায়। তারা ‘ইমলাক’-এর বংশধর।
কেউ কেউ বলেন, তারা হল আমলীক ইব্নে লাও ইব্নে সাম ইবন নূহ (আ)-এর বংশধর। প্রতিমা পূজায় লিপ্ত দেখে সে বলল, এগুলো কেমন প্রতিমা যে তোমরা এগুলোর উপাসনা করছ? তারা বলল, আমরা এ সকল প্রতিমার উপাসনা করি, ওগুলোর নিকট বৃষ্টি চাইলে ওরা আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করে। আমরা ওগুলোর নিকট সাহায্য কামনা করলে ওরা আমাদেরকে সাহায্য করে। আমর বলল, তোমরা কি আমাকে একটি প্রতিমা দিবে যে, আমি সেটি নিয়ে আরব অঞ্চলে যাব এবং আরবগণ এটির উপাসনা করবে? ওরা তাকে ‘হুবল’ নামের একটি প্রতিমা দান করে এবং লোকজনকে সেটির উপাসনা করার এবং সেটির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়।
ইবনে কাসির এরপর বলেন: ইবন ইসহাক (র) বলেন, হজরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা প্রচলনের সূচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ধারণা এই যে, মক্কায় জনজীবন সংকুচিত ও সংকটাপন্ন হয়ে পড়লে তাদের কোনো কাফেলা তা থেকে মুক্তিলাভ ও স্বচ্ছতা অর্জনের আশায় অন্য এলাকায় সফর করত। তখন তারা হারাম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও বরকত লাভের আশায় হারাম শরীফের এক একটি পাথর সাথে নিয়ে যেত। তারা যেখানে তাঁবু ফেলত, সেখানে ওই পাথর রাখত এবং কা’বা শরীফের তাওয়াফের ন্যায় সেটির চারিদিকে তাওয়াফ করত। এভাবেই তাদের রীতি চলে আসছিল। এক সময় তাদের প্রিয় ও পছন্দের পাথর পেলেই তারা উপাসনা শুরু করে দেয়। অবশেষে আগমন ঘটে তাদের উত্তরসুরিদের। এরা সরাসরি মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয় এবং সূচনা পর্বের রীতি ও উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যায়। দেখুন: ইবনে কাসির (২০০৪, ৩/১৮৭-১৮৮), ‘আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া’, দারু হিজর, মিশর।
২১। বাংলা ভাষায় ‘শাহাদাহ’ (الشهادة) কথাটা সাধারণত সাক্ষ্য (الشهادة), প্রমাণ (الدليل) বা উপস্থিতির (الحضور) ব্যঞ্জনায় হাজির হয়েছে। এই কথাটা যুক্তিবিদ্যার ভাষা না। বরং নিঃশর্তে উজুদ বা ‘আছে’ কথাটা বুঝতেই বেশ কাজে লাগে। কোরানে ভাষার পরিসরে বিশেষ ধরনের ভাব ও অর্থে, একান্তই ইহলৌকিক ভাব, অর্থ ও প্রকাশক্ষমতার মধ্যে গায়েবকে আস্বাদন করার কাজে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে এই হিসাবে ‘আল্লাহ’ ধারণাটি মানুষ যখন ‘সাক্ষ্য’ হিসাবে গ্রহণ করে, তখন চিন্তার কর্তা ও বিষয় হিসাবে আল্লাহ মানুষের সাক্ষ্যের মধ্যে হাজির হন। কেননা আল্লাহ নাইচিহ্ন হবার কারণে তাঁকে চিন্তার কর্তা বা বিষয় কোনোভাবেই হাজির করা যায় না, বরং যে ব্যক্তি তার সাক্ষ্য দেয়, তার অভিব্যক্তির মধ্যেই একটা বিশেষ উপস্থিতির অভিগমন ঘটে মাত্র। এই শব্দটার মধ্যে অনুপস্থিতির উপস্থিতি টের পাবার একটা দারুণ স্বাদ পাওয়া যায়। সুফিরা এই শব্দটার গোড়ার এই অর্থ ধরতে না পেরে নিজেকে নফি করে ‘আল্লাকেই’ ইসবাত করে বসেছিল। সুফির উপলব্ধি হয় তার উপস্থিতি সে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু এই দেখা যে আল্লার নিরন্তর অনুপস্থিতির একটা সাময়িক প্রকাশ ছিল, সেটা সে বুঝতে পারে না। এই অবস্থাকে ‘সাহিবুল মুশাহাদা’র অবস্থা বলা হয়েছে (صاحب المشاهدة)। এই বক্তব্য ইমাম গাজ্জালির কাছ থেকে নেওয়া। দেখুন: ইমাম আবু হামিদ গাজ্জালি, (প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৬, ১৪৭) ‘মিশকাতুল আনওয়ার ওয়া মিছ্ফাতুল আসরার’, আলামুল কুতুব, বৈরুত।
২২। এই কথার সাবুদ হিসাবে সুরা বাকারার নিচের চারটা আয়াত দেখুন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:
(১) الٓمٓ
(২) ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَۛ فِيهِۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
(৩) ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ
(৪) وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
(১) আলিফ-লাম-মীম
(২) এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হিদায়াত, কেবল মুত্তাকিদের জন্যে।
(৩) যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তার মধ্যে অপরের জীবিকার হক আদায় করে।
(৪) এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও এবং তারা আখিরাতের একিন অর্জন করে।
২৩। এই আয়াতে আমরা আক্ষরিক অনুবাদের বদল ঘটিয়েছি। এই আলাপ নিরপেক্ষভাবে পড়লে যে কেউ এটার যথার্থতা বুঝতে পারবেন। কোরানে ‘লা ইলা ইল্লাল্লাহ’ কথাটা আরবি ভাষায় আরবদের মাকাসেদ, উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই বলা হয়েছে। আরবি কাব্যের ‘নেতিকরণ’ কথাটার ক্রিটিক হিসাবে নেতি ও ইতির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা কোরানের উদ্দেশ্য। এই জন্য কালেমায়ে তাইয়েবা ঈমানের শর্ত হিসাবে পড়ানো হয়।
আরিফ বিল্লাহ

বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে জন্ম। সেখানেই বড় হয়েছেন। তবে ছেলেবেলার অধিকাংশ সময়েই কাটিয়েছেন চাটগাঁয়। কওমিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা। চিন্তা ও প্রজ্ঞার পুরানা চর্চার মাদ্রাসাগুলো খুঁজে খুঁজে পড়াশুনা করেন, লেখেন। তাঁর নিজের থেকে যা কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে নিজেকে তিনি জোড়া লাগান।


