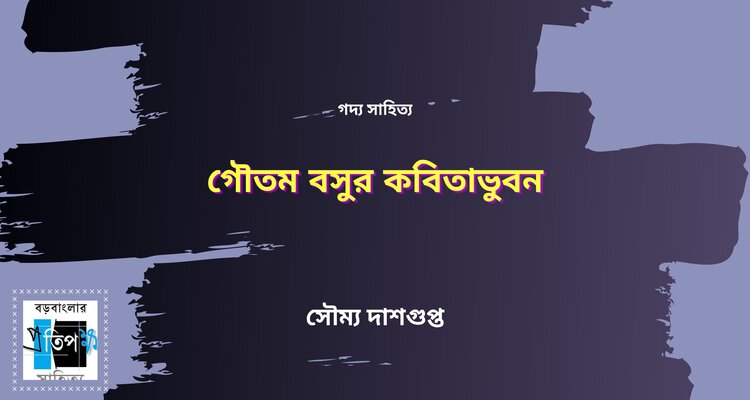
।। সৌম্য দাশগুপ্ত ।।
কবি গৌতম বসুকে আমরা আমাদের সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা একজন ক্রিয়াশীল কবি মনে করি, যিনি চলে যাওয়ার দীর্ঘ, দীর্ঘদিন পরেও তিনি কবিতা পাঠকের কাছে জীবন্ত থাকবেন। এর জন্য তাঁকে আগামী সমাজের ভাষা খুঁজতে হয় নি, তিনি সুদূর অতীত থেকেও এক দ্যুতি গ্রহণ করে তাকে আত্মস্থ করে, নিজস্ব রুচিনির্মাণের বলয়ে তাকে পুনরাবিষ্কার করে আমাদের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।
তোমার নতুন কবিতাগুচ্ছ
দেখবার আশে দু’তিন দশক
অপেক্ষা করি, তারপরে যেই
গিরিশিলা থেকে কয়েক স্তবক
মুক্তধারায় মঙ্গলালোক
নেমে আসে যার ভিতরে উহ্য
মানবনিয়তি, আগামী কবিতা
আমি জানি তুমি তার রচয়িতা
(গৌতম বসুকে – অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ২০০৫)
গৌতম বসুর কবিতাভুবন
১।
চারপাশের চেনা ছবি – তা সে বস্তু, মানুষ, বা প্রকৃতিই হোক, তার মধ্যে এক পরিধি-অতিক্রম-করা অবাঙমানসগোচর’কে প্রত্যক্ষ করা, বা তাকে ফুটিয়ে তোলা গৌতম বসুর জাদুকরী বৈশিষ্ট্য।

একাশি সাল থেকে দুহাজার-এক অবধি প্রতি দশ বছরে একেকটি করে শীর্ণ কাব্যগ্রন্থ, এইভাবে আত্মপ্রকাশ আমাদের সময়ের অন্যতম প্রধান কবি গৌতম বসুর। অলোকরঞ্জনের দু-তিন দশক অপেক্ষা করা উক্তির সত্যতা ছাড়াও এর মধ্যে হয়ত এই ইঙ্গিত আছে যে প্রধান কবি হতে গেলে বহুপ্রজ হতে হয় না। সংক্ষিপ্ত তাঁর জীবন, আর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র আটটি (অন্নপূর্ণা ও শুভকাল – ১৯৮১, অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে – ১৯৯১, রসাতল – ২০০১, নয়নপথগামী – ২০০৭, স্বর্ণগরুড়চূড়া – ২০১৩, ‘মঞ্জুশ্রী’ – ২০১৬, জরাবর্গ – ২০১৮, ও ‘সুকুমারীকে না-বলা কথা’ – ২০১৯)। কবির বই-এর আয়তনগুলি দেখে মনে হয় একবার বসলেই শেষ করে ওঠা যায়। সমস্যা হলো, তাঁর কাব্যসমগ্র, বা কোনো কবিতার বই-ই একবার বসে শেষ করা অসম্ভব। প্রতিবারই ওই গিরিশিলা থেকে মুক্তধারায় মঙ্গলালোকের দ্যুতি নতুন করে আমাদের আচ্ছন্ন করে, আর প্রতিবারই শেষ করা হয় না, নতুন করে বারবার ফিরে ফিরে পড়তে হয়। কখনো কখনো একটি কবিতার সামনে আমরা চুপ করে বসে থাকি অনেকটা সময়; সারাদিন ওই অভিভব আমাদের মাথায় ঘুরতে থাকে, সব কাজ তুচ্ছ হয়, পণ্ড মনে হয়; সব চিন্তা, প্রার্থনার সকল সময়, শূন্য মনে হয়।
অন্নপূর্ণা ও শুভকাল-এর কবিতাগুলির নাম নেই, এক থেকে বাইশ সংখ্যায় চিহ্নিত। তবে এগুলিতে একটি সামগ্রিকতার সুর আছে বলে হয়ত একটিই দীর্ঘ কবিতা হিসেবেও পাঠ করা যায়। বইটির বিষয় সর্বকালের – সমকালের, এবং মহাকালেরও, তা যেন প্রথম লেখাটির থেকেই স্পষ্ট –
জলের পরিবর্তে এই শ্রাবণ
আর সহজ নয়,
ভূমি হয়ে উঠেছে হতশ্রী বাহু
দক্ষিণ, ক্লিন্ন গৃহশেষের শান্তি।
(১, অন্নপূর্ণা ও শুভকাল)
কবিতাগুলির মধ্যে একটি নিবেদনের সুর যেমন, তেমনই মানবজীবন, মানবনিয়তির হাহাকার, বা দ্য হিউম্যান কন্ডিশন বলা হয় যাকে, তার একটি বেদনার্ত ছবি পাওয়া যায়। জল, আগুন, বায়ূ, ও পঞ্চভূতের প্রতীকী ছবিতে প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যেও এই দুর্ভাগা মানবজীবন ফুটে ওঠে। থালার বৃত্তকার ক্ষুধা, শিশুর নিদ্রায় আতঙ্কের কাহিনী, ঝরে যাওয়া গহনার ধ্বনির আর্তি, এই সবের মধ্যেই ‘সরল’ কালযাপন, আহারের জন্য শান্তিময় প্রতীক্ষা। এই দ্বন্দ্বই অন্নপূর্ণা ও শুভকালের প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। যেন মহাভারতের কাল থেকে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তা আজও অব্যাহত –
‘একটি মানুষ ঘাসের জনতায়
রয়ে গেছে, যখন ফলকের সঙ্গে ফলকের সংঘাত
ধাতুর ক্রোধে বীর পড়েছে ভূতলে, রথ
টলতে-টলতে প্রবেশ করল যুদ্ধের আরো ভিতর;
…
একসময়ে সূর্য আলো ফিরিয়ে নিলেন, মনে হল
…
উপর দিয়ে হাহাকার বয়ে চলে, আকাশের বিরুদ্ধাচারী
রাশি-রাশি ছুটন্ত হাত, একটি ঘুড়ি আজকের ভোজন।’
(৩, অন্নপূর্ণা ও শুভকাল)
বাচ্যার্থ অতিক্রমী চিত্রকল্পনির্ভর কবিতাই বেশি গৌতম বসুর; কয়েকটি শব্দের প্রতি অনুগ্রহ ও প্রস্তাবনা বারবার ফিরে পাই তাঁর কবিতায়। জীবনানন্দের মতোই ঘাস এসেছে তাঁর কবিতায়, কিন্তু বিপ্লবের বেশে; তেমন ক্ষুধা ও দাহ, অন্ন ও নিরন্নতা, ছবির সাযুজ্য ও সহসংস্থানের মধ্য দিয়ে জীবনের নানা পর্বকে তুলে ধরে। অন্ধের যষ্টি নিয়ে যে-ধূপ বিক্রেতা দিন আনে, দিন খায়, তার শিকল জলে রূপান্তরিত হয়, আর সেই জল যেন প্রকৃত শ্মশানবন্ধু, ‘এই জল রামপ্রসাদ সেন’। বহুশ্রুত, বহু-উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলি পড়ার সময় যে আচারধর্মের ছবি সঙ্গোপনে ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায়, তার প্রতিকল্পে রয়েছে কবির এক বহুসংস্কৃতিবিস্তৃত চেতনাও, বাংলার বুক থেকে যার আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে সময় লাগে না। এর পিছনেও আছে তাঁর বিপুল বিশ্বসাহিত্যপাঠ এবং সমগ্রবঙ্গের আচার-চেতনার মেলবন্ধন।

এই বইয়েই ১২ নম্বর কবিতাটি রাশিয়ান অ্যাকমেইস্ট কবি ওসিপ মান্দেলস্তাম-এর প্রতি নিবেদিত (তাঁর জন্মসনটি ১৮৯১ হবে, ভুল করে ১৮৮১ লেখা আছে)। তাঁকে তিরিশের দশকে স্তালিন-বিরোধী কবিতা লেখার জন্য নির্বাসনে পাঠানো হয়। অ্যাকমেইজম একটি কাব্যিক আন্দোলন, যা ১৯১০-এর দিকে আকার নিতে শুরু করে। এঁরা প্রতীকবাদ-কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করতেন, যা অজ্ঞাত, তাকে শব্দের অর্থ দিয়ে জানা যায় না। অতএব প্রতীকের মাধ্যমে যে-বোধগম্যতা গড়ে ওঠে, তা থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। অ্যাকমেইস্টরা তাঁদের পথ-কে আদমবাদ বলেছিলেন, বাইবেলের আদমের সাথে সংযোগ করে বিশ্বের একটি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা। এই কবিরা তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন সাহিত্যকে জীবনে, জিনিসে, মানুষে, প্রকৃতির কাছে ফিরিয়ে আনতে। মনজুরুল হক মান্দেলস্তাম-এর কিছু কবিতার ভাবনুবাদ করেছেন কালি ও কলম পত্রিকায় (নভেম্বর, ২০১৯), আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন। অস্পষ্ট প্রতীক থেকে এই প্রাকৃতিক সত্যের দিকে যাওয়ার কথা ভেবেই কি মান্দেলস্তামের উদ্দেশে নিবেদিত এই লাইনগুলি -–
‘একটি মানুষ ঘাসের জনতায়
রয়ে গেছে, যখন ফলকের সঙ্গে ফলকের সংঘাত
ধাতুর ক্রোধে বীর পড়েছে ভূতলে, রথ
টলতে-টলতে প্রবেশ করল যুদ্ধের আরো ভিতর;
…
একসময়ে সূর্য আলো ফিরিয়ে নিলেন, মনে হল
…
উপর দিয়ে হাহাকার বয়ে চলে, আকাশের বিরুদ্ধাচারী
রাশি-রাশি ছুটন্ত হাত, একটি ঘুড়ি আজকের ভোজন।’ (
(৩, অন্নপূর্ণা ও শুভকাল)
অথচ বাচ্যার্থাতিক্রমী এইসব কবিতাতেও আত্মজীবনীর অংশ কি প্রবেশ করেনি, যেখানে ‘…অকস্মাৎ/ শৈশবে চুরি করে আনা স্ট্যাম্প-সংগ্রহ বেরিয়ে পড়ল/ এবং পুনরায় গোপন করবার আগেই, … /খানিক ওড়ে / খাতার বাঁধাই শিথিল, পাতা খসে পড়ে, ভাসে, / লোকে বলে বিবাহের ছড়া ।’
চারপাশের চেনা ছবি – তা সে বস্তু, মানুষ, বা প্রকৃতিই হোক, তার মধ্যে এক পরিধি-অতিক্রম-করা অবাঙমানসগোচর-কে প্রত্যক্ষ করা, বা তাকে ফুটিয়ে তোলা গৌতম বসুর জাদুকরী বৈশিষ্ট্য। যে কবিতা শুরু হয় রিক্সার উদরে তিন মদ্যপের ছবি দিয়ে, নাট্যকর্মী, পর্দার তার, কলমবিক্রেতা, টিউশনশ্রমিক, ভিয়েনের বামুন, ও ব্যর্থ প্রাবন্ধিকের মত বাস্তব চরিত্র দিয়ে, তার শেষ লাইনে পৌঁছে কবির চোখে পড়ে ‘এদের দৃষ্টির অনেকটাই অনুনয়, পুনর্বাসনের আশায় যারা পথে পথে চরে ’। কিংবা ভাতের থালা তুলে ধরার কথা বলেন যে কবিতায়, সেখানেই তিনি বলেন ‘যে জানে শেষাংশ কীভাবে গীত হবে সেই জন সমাপ্তির রাজা/ সেই বিদ্যা একমাত্র বিদ্যা, আমি মূঢ়/ আমার সঙ্গে বলো, অন্নপূর্ণা ও শুভকাল।’
২।
একেকটি কবিতায় স্থানগুলির নামও কিন্তু অভৌগোলিক মনে হয়, সন্দেহ হয়, ওইরকম কি কোনো জায়গা আছে কোথাও? ‘শ্রী’, ‘পাদুকা’ বা ‘মহাদেবের দুয়ার’ কবিতাগুলির শিরোনামগুলি সেই সন্দেহ জাগায়, যদিও কবিতাগুলির মধ্যে তার সন্ধানও দেন না, কেবল অনুভূতিটি ফুটিয়ে তোলেন।

মাত্র বাইশটি কবিতার ‘অন্নপূর্ণা ও শুভকাল’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর আমাদের দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে’-এর জন্য (১৯৯১)। সূচীপত্রেই মনে হয় স্থানমাহাত্ম্যের কবিতার সংকলন হিশেবে একটি লেন্স দিয়ে বইটি দেখা যায় – কবিতার নামগুলি ‘যশোহর’, ‘শাহী শেরপুর’, ‘বারাসাত লোকাল’, ‘শ্রীপুর’, ‘জেলাসদর বহরমপুর’, ইত্যাদি। তবে কবিতাগুলি পড়লেই সেই স্থানগুলির পরিচিত ছবিগুলি অপসারিত করে যেন তাদের আত্মাকে উদ্ধার করেন গৌতম বসু, বা সেই স্থানগুলি যেন সহসা তাদের লক্ষণ অতিক্রম করে কবির দর্শনের জগতে অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে নিয়ে যায় পাঠককে। এক দিক থেকে অনুসন্ধিৎসা জাগে বৈ কী, ওই অন্তর্বর্তী দশ বছরে কি কবি নানা জায়গায় ভ্রমণ করলেন? কী ঘটেছিল তখন? কোনো ইতিহাসের বোধও কি নির্ণয় হবে আমাদের ওই কবিতাগুলি পাঠের অভিজ্ঞতায়? কিন্তু ডুব দিতে গেলেই সেই অনুসন্ধিৎসা এক লাফে বিস্তৃত হয়ে যায় –
সেই ক্রোধ যাকে প্রদান করা হয়েছিল,
কামারশালার পিছনে নিশাচ্ছন্ন
যার কৃষ্ণকেতন স্ফুলিঙ্গে, হাওয়ায়, ধোঁয়ায়, ছড়িয়ে রয়েছে,
অগ্নির, তবু অগ্নির নয়”।
(যশোহরি, অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে)
একেকটি কবিতায় স্থানগুলির নামও কিন্তু অভৌগোলিক মনে হয়, সন্দেহ হয়, ওইরকম কি কোনো জায়গা আছে কোথাও? ‘শ্রী’, ‘পাদুকা’ বা ‘মহাদেবের দুয়ার’ কবিতাগুলির শিরোনামগুলি সেই সন্দেহ জাগায়, যদিও কবিতাগুলির মধ্যে তার সন্ধানও দেন না, কেবল অনুভূতিটি ফুটিয়ে তোলেন। মহাদেবের দুয়ার কবিতাটি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা। কবিতাটির শিরোনামও উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতর। তাহলে কবিতাটি কি কোনো স্থানমাহাত্ম্যের, না ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিবেদিত? জানা গেল, দেওঘরের কাছে সত্যিই ওই নামে একটি জায়গা রয়েছে।
মুনাইকান্দ্রা মুর্শিদাবাদের কান্দির কাছে একটি গ্রাম, নামটি কবির ভাষায় ‘ধ্বনিমাধুর্যহীন’, তার আলপথ রৌদ্রতাপে ব্যাকুল, কিন্তু তারপরেই একটি হারিয়ে যাওয়া অভিমানে গ্রামটির ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে – ‘কোন বিজনে, কোথায় তার নাকের নোলক, গলার মালা গচ্ছিত আছে’। একইরকম হাহাকারের কথা দেখি ‘বিশ্রামতলা’ কবিতাটিতেও – ‘সে কোথায়, কোথায় তার সুরমাখা কঙ্কণ, শূন্যতা ছুঁয়ে আছি/ এ-শূন্যতায় বুকের আলো বুকে নিভে যায়’। ‘উত্তরপাড়া নিজ’ বহড়ুর কাছে একটি গ্রাম, সেখানে এবাজুদ্দিন লস্করের বাড়ির পথ (এই এবাজুদ্দিন আসবেন আবার অনেক পরে লেখা আরও কয়েকটি কবিতায়ও), আর সেখানেও তিনি গৃহস্থের অগোচরে রোপণ করেন খেদ – ‘ওই কেশদামে কেবলই মেঘ ও রৌদ্র, দিগন্তরেখে কোথায়!’ গঙ্গানারায়ণপুর কবিতাটিই তিনটি স্তবকের, আর বিরহবেদনার অপূর্ব সৌন্দর্যময় আর্তি এখানেও –
অবশেষে, কোনও এক মধ্যাহ্নে
বাঁশবনের ধারে, যদি কেউ ললাট স্পর্শ করে
ধীরে, অতিধীরে, তাকে দিও, আমার বিরহ।
৩।
মৌনতার থেকে খুব সামান্যই শ্রাব্য স্বরে তিনি যেন বর্ণনা করছেন দৃশ্য, নিয়ে আসেন মিথ ও ইতিহাস, পুরাণ ও লোককথা, ক্রমশ তা হয়ে ওঠে এক সূক্ষ্ম ও কালাতিক্রমী ব্যথার অনুভব। তবু সমকালের মানুষ ও তাদের যাপিত জীবন থেকে তিনি দূরে চলে যান না, তাঁদের সঙ্গেই তিনি যেন কালাতিক্রমী এক ভ্রমণের সহযাত্রী।
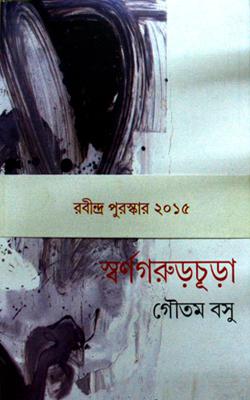
আঠাশটি টানা গদ্যে লেখা কবিতা নিয়ে ‘রসাতল’ কাব্যগ্রন্থটি আরো দশ বছর পর প্রকাশিত হল, ২০০১ সালে, হোমারের অডিসির সেই উদ্ধৃতি দিয়ে, যেখানে অডিসিয়াসের স্ত্রী পেনিলোপি আর তাঁদের পুত্র তেলিমেকাস ট্রোজান যুদ্ধের পর দশ বছর ধরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে নানা শত্রুর মোকাবেলা করেছিলেন – “With that she breathed indomitable valour into her son…”। এছাড়া বইটির উৎসর্গপত্রে আমরা কবির প্রিয় পূর্বসূরি সাহিত্য ও শিল্পব্যক্তিত্বের নাম দেখে জানতে পারি তাঁর রুচিপছন্দের বলয় – সেখানে আছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ, কমলকুমার মজুমদার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিককুমার ঘটক, নিখিল বিশ্বাস, মণীন্দ্র গুপ্ত, আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু, যুগান্তর চক্রবর্তী ও গণেশ পাইন। এটা লক্ষ করবার যে, অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথের সেই ভ্রমণানুভব এখানেও তার উৎসারে উজ্জ্বল, একেবারে প্রথমেই তার বিভাব কবিতায় –
… ‘পার্থিব সম্পদের উপর অধিকারপ্রতিষ্ঠার সূত্রে মানবসমাজ স্তরবিভক্ত, স্তরগুলি
বিবাদের রক্তস্রোতে ভেসে চলেছে, এ-অবস্থাই আমার বন্ধন, তবু বন্ধনমাত্র
নয়, আমি মুক্তির পথেই রয়েছি।’
আমরা ততক্ষণে বাঁশবনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। পথ এখানে
অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, ছায়াসকল তীক্ষ্ণ, যে কাঁচা রাস্তায় গিয়ে উঠব সেটি ধরে
উত্তর দিকে হাঁটলে রামকৃষ্ণপুর, দক্ষিণে বুড়োর ঘাট, আর সম্মুখে দেখতে
পাচ্ছি শাহজাদপুর অঞ্চলের অন্তর্গত একটি গ্রাম, গঙ্গানারায়ণপুর। একটি
তেজস্বী মধ্যাহ্নের প্রশ্বাসে গঙ্গানারায়ণপুর কেমন মিশে রয়েছে।
”
এই জায়গাগুলির নাম আমরা আগের বইটিতে দেখেছি। দুটি ব্যাপার এই কবিতায় লক্ষ করার – এক, প্রথম পংক্তিটি একটি দার্শনিক উত্তর (শীতল ও রুক্ষ বাতাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ‘বন্ধন কীসে?’), যার পরের স্তবকে একটি যাত্রাবিবরণ শুরু। দুই, বাংলার গ্রাম-মফস্বলের নামগুলিও কবিতা হয়ে উঠেছে তাঁর ছবি আঁকার কুশলতায়। কিন্তু এ যেন ছবি আঁকা নয় কেবল, সেই বস্তুদৃশ্যের মধ্যেও এক জীবনদর্শনকে তুলে ধরা।
টানা গদ্যে লেখা কবিতাগুলির কিছু কিছু অংশে বাচ্যার্থকে কবি অতিক্রম করেন নি। বরং মৌনতার থেকে খুব সামান্যই শ্রাব্য স্বরে তিনি যেন বর্ণনা করছেন দৃশ্য, নিয়ে আসেন মিথ ও ইতিহাস, পুরাণ ও লোককথা, ক্রমশ তা হয়ে ওঠে এক সূক্ষ্ম ও কালাতিক্রমী ব্যথার অনুভব। তবু সমকালের মানুষ ও তাদের যাপিত জীবন থেকে তিনি দূরে চলে যান না, তাঁদের সঙ্গেই তিনি যেন কালাতিক্রমী এক ভ্রমণের সহযাত্রী। পূর্ণিমা কবিতায় শুরু করেন ‘কপিলাবস্তু থেকে শান্তিনগরের দূরত্ব সামান্যই’ – এই অভিভাষণে, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের হারিয়ে যাওয়ার পথ ধরে কয়েকটি আধুনিক প্রান্তিক চরিত্রের কথা বলেন, ফিরে আসেন প্রকৃতিতে, আর শেষ করেন এক সুন্দর দৃশ্যে – ‘…জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্যবলে সে দু’চোখ ভরে স্পষ্ট দ্যাখে, মুণ্ডিতমস্তক, ভাবমগ্ন এক অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ নগ্নপদে চলেছেন, চলেছেন’।
মীরার মন্দির দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় একাধিকবার আসবে, মীরার গল্পে নিহিত বিষাদঘন আত্মনিবেদনের সুরেই। এই তিন লাইনের কবিতাটি উদ্ধার করা যায় –
একটি পাথরের ঘরে একলা ব’সে, সে ডাকে। যার দেখা পাওয়া যায় না কোনওদিন,
পুথিগুলি যার কাছে পৌঁছতে পারে না বলে মাথা কোটে, তাকে, সে ডাকে। নাম যার
সহস্রভাবে ঘুমায় অনলে আর অনিলে, নিশাকালের ঘন রুধির যে, তাকে, সে ডাকে।”
(মীরার মন্দির, রসাতল)
মীরার কথা থেকে খানিক এগিয়ে আমরা পাই জর্মন মধ্যযুগীয় চিত্রকর ম্যাথিয়াস গ্রুনেওয়াল্ড (নামান্তরে মাথিস পাওয়া যায়, কবি মাথিয়ুস লিখছেন)-এর, যাঁর বয়সও তাঁর শিক্ষানবিশির কাজের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় (কবি ১৪৭০ লিখে প্রশ্নচিহ্ন দিয়েছেন সঙ্গত কারণেই)। গ্রুনেওয়াল্ডের সবথেকে পরিচিত কাজের নাম আইজনহাইম অল্টারপিস, যেখানে শিল্পী আন্তোনাইন সন্তদের প্লেগরুগীদের শুশ্রূষার কথা স্মরণ করে রোগাক্রান্ত যীশুর ছবি এঁকেছিলেন। কবির চিন্তায় ‘বাসের জানলার ধারে বসে আকাশ দেখি, আর অনিবার্যভাবে আপনার কথা উঠে আসে। … সহসা, রাস্তার ধারে কামারশালা থেকে ধাতব শব্দ ছিটকে আসে, মনে হয়, কিছুমাত্র ঘটেনি এতকাল, শুধুই যুদ্ধারম্ভ, সব যুগ মধ্যযুগ – ভাগ্যহীন প্রাণীদের, অসহায় মহাত্মাদের মধ্যযুগ…”
কিম্বা লিও টলস্টয়ের অন্তিম চিঠির এক লাইন উদ্ধার করে তিনি তাঁকে কৃষ্ণের তুলনায় নিয়ে আসেন, নিজেকে বলরামের ভূমিকায় দর্শক হিশেবে দেখে – “এইবার স্থির হই, সর্পশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণবর্ণরেখা; মুখগহ্বর থেকে বাহির হয়ে তুমি যেন চলেছ সাগরের দিকে; অন্তরীপে ক্ষয়স্নাত, আমি বলরাম।‘
৪।
এই প্রথম আমরা বেশ কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা পেলাম গৌতম বসুর – বইয়ের শীর্ষ কবিতাটি (স্বর্ণগরুড়চূড়া) ছাড়াও মিথিলানগরী, উপত্যকা, পিতৃশ্রাদ্ধ, মরণলেখ, অশ্বারোহী রেবন্ত – এই কবিতাগুলির ভাষাও আটপৌরে, যদিও তার পরতে পরতে রয়েছে অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের কালাতিক্রমী দর্শন; ইতিহাস, লোকাচার, মিথ, পুরাণ, ও সমাজচেতনার বহুস্তরিক অনুসন্ধান। যে মূল্যবোধে কবির গোড়া থেকেই অবস্থান, তার থেকে নড়চড় হয় নি এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করেও।

২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় ‘নয়নপথগামী’, প্রচ্ছদ প্রতিলিপিতে আনা আখমাতোভার ছবি। উৎসর্গ করেছেন সেই মধ্যযুগের মীরা দাসী (১৫৪৭-১৬১৪) ও আনা আখমাতোভা (১৮৮৯-১৯৬৬) এই দুই নারীকে। মীরা বাঈ-এর গল্প সবার জানা, কিন্তু আমাদের আগ্রহ হয় কবি কেন আনা আখমাতোভাকে এক সাযুজ্যের অভিধায় প্রতিস্থাপিত করেন। দুজনেরই বিপ্লবী চরিত্র; মীরা তাঁর স্বামী হিশেবে নিজের স্বামীকে অস্বীকার করে বরণ করেছিলেন কৃষ্ণকে, আর আনা আখমাতোভা স্তালিনের জমানার বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁর স্বজনদের হারিয়েছিলেন। আমরা এর আগে ওসিপ মান্দেলস্তামের কথা বলেছি, সেই কবির সঙ্গে ১৯১০ সালে হাত মিলিয়েছিলেন আনা। সেই সিম্বলিজম-বিরোধিতার জায়গা থেকেই এই করমর্দন ও শেষাবধি সখ্য। নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীতা হয়েও পুরস্কার পাননি যিনি, তাঁর শিষ্য যোসেফ ব্রডস্কি নোবেল পেলেন ১৯৮৭ সালে!
এই অভিধা মাথায় রেখে কবিতাগুলি পড়লে মনে হয় এই দুই দীর্ঘকালবিদূরিত মহিয়সীর প্রতি নিবেদিত পংক্তিমালায় কবিতাগুলি এক দর্শনের কথা বলে, যেখানে ‘সুদীর্ঘ, শান্ত এক অপেক্ষা/আমায় ঘিরে রয়েছে; সত্য তোমার প্রকাণ্ড শূন্যতা, ক্রন্দসী।‘ সৈকত কবিতায় বলেন, ‘ওই ছায়াপথ ভেঙে পড়েছে মাথায়।/ চোখের মণি অবধি উঠে-আসা পাপ, ডাকে, আমি শুনি/ রসুল, রসুল।’ রসুলের শরণ শেষ কবিতাটিতেও –
এমন সুখের অনুভব এমন যে ব্যথা
এমন অশ্রুর বনে নেমে-আসা দৈব আলো
অমল যে দুঃখরাতে তুমি আত্মহারা মেঘ
এমন যে মরণকালের তরণী, রসুল।’
(বিসমিল্লা, নয়নপথগামী)
প্রায় কোনো কবিতাতেই প্রচলিত দুলুনির ছন্দ দেখি না গৌতম বসুর কবিতায়, হয়ত তা বিষয়ের গভীরতার দাবিতেই সমাকীর্ণ, কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ে এমন কিছু লাইনও –
পাহাড়ের মতো গড়িয়ে পড়তে শিখিনি
অশনির মতো ঘুমোতে পারিনি আকাশে
পলিভাষাটির কোল খালি করে মরেছি
বুকে গেঁথে দাও তমলুক, ছেঁড়া পতাকা।‘
অষ্টম শতাব্দীর চিনের সুবিখ্যাত কবি তূ ফূ-র লাইন উদ্ধার করেন (A slip of cloud comes black overhead / Before it rains my sonnet must end!) একটি কবিতায়, আর আমাদের মধ্যে এই চিন্তা প্রতীয়মান হতে থাকে যে নিপীড়নের শিকার যেসব কবি ও শিল্পী, তাঁদের জন্য গৌতম বসুর এক আশ্চর্য প্রতিশ্রুতি- ‘শয্যা দাও, দুগ্ধ দাও, দাও পরিধান/ আমি শান্ত অগ্নিশিখা, ক্রোধে কম্পমান।’
২০১৩ সালে স্বর্ণগরুড়চূড়া প্রকাশিত হওয়ায় এই দশকবিস্তৃত অপেক্ষার অবসান ঘটলো, তবু ছ বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে! এই বইটিতে লক্ষ করি কবির পূর্বেই টানা গদ্যে লেখা কবিতার বিষয়-বস্তু-ক্রিয়ার বিধি গ্রহণ করার ইচ্ছেটি এক নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছে। বাইরে থেকে একনজরে পড়লে যা মনে হয় বাচ্যার্থাশ্রয়ী, কিন্তু খানিক পরেই তিনি আবার রহস্যাবৃত করে তোলেন নিজেকে। একটি স্কুলবাড়ির সামনে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দেখা বাচ্চাদের স্কুলভ্যানে করে আসার দৃশ্য, তাদের কর্মচঞ্চল মায়েদের আলুথালু বেশে আসার দৃশ্য, এগুলি আমাদের চেনা দৃশ্য। কিন্তু শেষে গিয়ে তিনি লেখেন –
… কী ঘটবে তারপর? আমার পানে যেই নজর
পড়বে একজনের, সমগ্র বিশ্ব হেসে উঠবে,
শনিদেবতার থানের ডানদিকের পথ ধরে
হাসতে-হাসতে সমগ্র বিশ্ব অদৃশ্য হয়ে যাবে।
ভবিষ্যপুরাণ আর আমি যবে নির্বাসিত হই
সেদিনের কথা মনে পড়ে যায়, লজ্জানিবারণ,
কথা শোনো, আমায় এইভাবে একা ফেলে যেও না।
(গাছতলায় লেখা, স্বর্ণগরুড়চূড়া)
রায়শেখর পদকর্তার একটি পদ থেকে উদ্ধার করেছেন প্রথম চারটি পংক্তি (সামান্য অদলবদল আছে শব্দের, তবে ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ‘যায়’ শব্দটি ‘বিদরিয়া’ শব্দের পরে দিলাম মূল বইটি দেখে, কবি উদ্ধার করেছিলেন ‘যায় বিদরিয়া’) –
হিয়ায় আগুনি ভরা আঁখি বহে বহু ধারা
দুখে বুক বিদরিয়া যায়।
ঘর পর যে না জানে সে জন্য চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সহে মায়।।
কবির উদ্ধারে আরো কিছু অসঙ্গতি আছে, কিন্তু এই পদকর্তাদের টেক্সট কতটা নির্ভরযোগ্য ভাবে হাতবদল হয়ে বদলে গেছে সেটা বলা মুশকিল। কবির উদ্ধারটি ছিল এইরকম –
হিয়ায় আগুনি ভরা আঁখি বহে অসুধারা
দুখে বুক যায় বিদরিয়া।
ঘর পর যে না জানে সে জনা চলিলা বনে
এ তাপ কেমনে স’বে মায়।।
এবার দেখুন, কবিতাটির উপক্রমণিকা যে পদ-এর, তার রসবোধ কেমন আধুনিক ভাষায় লৌকিক পরিসরে কবি নিয়ে আসেন এইভাবে –
… যাই, বেলা বাড়ার আগে চানটা সেরে আসি –
এমন একটা ভরা সংসার এইখানে
এতকাল ছিল, তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে
দেখি বহুদূর থেকে নিজেরই পানে হাত
নাড়ছি, কামনা করছি, যাত্রা শুভ হউক।
(‘হিয়ায় আগুনি ভরা’, স্বর্ণগরুড়চূড়া)
এই প্রথম আমরা বেশ কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা পেলাম গৌতম বসুর – বইয়ের শীর্ষ কবিতাটি (স্বর্ণগরুড়চূড়া) ছাড়াও মিথিলানগরী, উপত্যকা, পিতৃশ্রাদ্ধ, মরণলেখ, অশ্বারোহী রেবন্ত – এই কবিতাগুলির ভাষাও আটপৌরে, যদিও তার পরতে পরতে রয়েছে অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের কালাতিক্রমী দর্শন; ইতিহাস, লোকাচার, মিথ, পুরাণ, ও সমাজচেতনার বহুস্তরিক অনুসন্ধান। যে মূল্যবোধে কবির গোড়া থেকেই অবস্থান, তার থেকে নড়চড় হয় নি এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করেও। ভাষাভঙ্গিতে আরেকটি ব্যাপার লক্ষ করি যে তিনি সাধু ও চলিত ভাষার বেশ কিছু সংমিশ্রণ করেছেন, কখনো কখনো একই কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের লাইনও এসে পড়ছে কথ্যভঙ্গির সুরে –
… সব উত্তর ক্ষণকালের,
কেবলমাত্র প্রশ্নসকল সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালের অধিকারী।
হাঁটতে-হাঁটতে স্বর্ণগরুড়চূড়ার কাছে এসে পড়েছি, বাকি পথ দেবতাদের –
আগুন পোহাবার সময় এখন, বোঝা নামিয়ে
ভাঙা ডাল, শুকিয়ে-যাওয়া পাতা সংগ্রহ করছি, দেখি
দুই ঝরাপাতার ফাঁকে আরো একটি ঝরাপাতা, সেইখানে
আরও একখানা প্রশ্ন:
‘এত যে শপথগ্রহণ করিলে ইহজীবনে, কী পরিণতি হইল তাহার?’
তড়িৎ প্রবাহের চাবুক খেয়ে, ডালপালা নিয়েই মাটিতে বসে পড়লাম
সহসা ডালপালা তোর উতলা যে, ও চাঁপা ও করবী।
(স্বর্ণগরুড়চূড়া, ঐ)
নানা মিশেলের ভাষাশৈলি বা দার্শনিক মূল্যবোধের বাইরে গিয়েও যদি প্রশ্ন ওঠে, কেবল ঘটনামূলক বিবৃতিধর্মেও কি গেঁথে দেয়া যায় না কবিতাদর্শনের অমোঘ সত্য? পিতৃশ্রাদ্ধ কবিতাটিতে একটি চলমান ছবি দেখি আমরা, আর সেই ছবির নানা বিন্যাসেও কবি একটি চেতনার সন্ধান করেন, যা আচ্ছন্ন করে আমাদের –
…একবার, কি প্রসঙ্গে মনে নাই, বাবাকে আমি শেলীর অকালমৃত্যুর
দুখজর্জর কাহিনীর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়েছিলাম,
বৃত্তান্তটি কিছুক্ষণের জন্য বাবাকে সম্পূর্ণ বিকল করে দিয়েছিল।
এখন ভাবি, মানুষের অভিজ্ঞতার জগতের,
তার চিত্তের পরিধির একটা সম্পূর্ণতা আছে
বাহির থেকে তাকে আক্রমণ করা এক প্রকার নিষ্ঠুরতা,
একটি নিটোল জগৎকে আমি
অজ্ঞানতাবশত, আক্রমণ করে ফেলেছিলাম।
গমন, নির্গমনের পথ আপনিই গড়ে ওঠে,
সবার অগোচরে, আপনিই ভেঙে যায়, আমি কি জানতাম?
…
মৃত্যু যা সংযুক্ত করতে সক্ষম, জীবন তা যেন আর পৃথক না করে
(পিতৃশ্রাদ্ধ, ঐ)
৫।
‘আমি নদীতীর তুলে নিলাম, অশ্রুকণা পেলাম না, নামিয়ে রাখলাম, তুলে নিলাম নিজমুণ্ড, নামিয়ে রাখলাম। হায়, শব্দের প্রেত, তোমারেও তুলে নিলাম এবং নামিয়ে রাখলাম’ – এই ধরনের চিত্রকল্পও এই কাব্যগুচ্ছে পাওয়া যাবে, যে-নিমগ্ন ভাষায় তাঁর কাব্যচর্চার ধারা শুরু হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে।
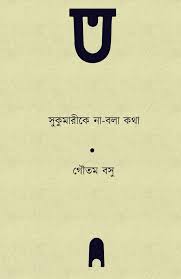
অগ্রন্থিত বেশ কিছু কবিতা পাই আমরা তাঁর কবিতাসমগ্রে, তবে সেগুলির থেকে এখনও, তাঁর মৃত্যুর পরে, প্রকাশিত হতে চলেছে আরো কয়েকটি বই। এর মধ্যেই ২০১৯-২০ সালে লেখা কিছু কবিতা নিয়ে ভাষালিপি থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘লয়’ বইটি। উৎসর্গ আমাদের সময়ের আরেক প্রধান কবি প্রয়াত পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালকে। প্রকাশক নবনীতা সেন-ও এই বইটি দেখে যেতে পারেননি। মাত্র বারোটি কবিতা আছে ‘লয়’ কাব্যগ্রন্থটিতে, এবং তার প্রতিটিই টানা গদ্য, এবং নাতিদীর্ঘ। বীরসিংহ গ্রামে আর কখনো ফিরে না যাওয়ার মর্মান্তিক সেই বিদ্যাসাগরের চিঠির উদ্ধার করে প্রথম কবিতাটি (নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র) শুরুতেই এক বেদনার সঞ্চার করে আমাদের মনে। কবি, গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যকে (১৯০৬-১৯৪৩) নিবেদন করেছেন একটি লেখা, পুরোটাই যেন ব্যক্তিগত কথোপকথন, ছোটো গদ্যের ভঙ্গিতে। কিন্তু এরই মধ্যে কবিতার জাদু মিশেল আমাদের স্পর্শ করে –
…আপনাকে জানানো হয়নি, আমাদের বারান্দা বেয়ে যে ফুলগাছ উঠে গেছে,
তার কাণ্ড এখন ভারি শক্ত, পাতার ফাঁক দিয়ে একটা মৌচাক দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে
মৌচাক ঘুমায়, আর কখনও-কখনও আমি ব’সে থাকি সেই অন্ধকারে। একের পর
এক, সুদূর অতীতের দৃশ্য ভেসে ওঠে, অচিরে শুন্যে মিলিয়ে যায় …
…দোতলার দালান থেকে কথা ও সুর, শুভ্রতম পালকের প্রায়, ধীর গতিতে
ভাসতে-ভাসতে নিচে নেমে আসতে দেখলাম। ‘ঝরিল সে, ঝরিল, ঝরিল পথের
ধারে’। বিশ্বাস করুন, ওভাবে কেউ আর লেখে না। বিশ্বাস করুন, কোনও ক্রিকেট
স্কোর-রক্ষক পালকের ঘায়ে চৈতন্য হারিয়েছে, এমন কথাও আপনি অন্য কোথাও
শুনতে পাবেন না।
(‘ছিল চাঁদ, মেঘের পারে’)
তবে প্রতিটি কবিতাই অতটা কথ্যভঙ্গির নয়, বাচনভঙ্গিতে জাদুবাস্তবতা মাঝে মাঝেই মুখ দেখায় আমাদের। ‘আমি নদীতীর তুলে নিলাম, অশ্রুকণা পেলাম না, নামিয়ে রাখলাম, তুলে নিলাম নিজমুণ্ড, নামিয়ে রাখলাম। হায়, শব্দের প্রেত, তোমারেও তুলে নিলাম এবং নামিয়ে রাখলাম’ – এই ধরনের চিত্রকল্পও এই কাব্যগুচ্ছে পাওয়া যাবে, যে-নিমগ্ন ভাষায় তাঁর কাব্যচর্চার ধারা শুরু হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে।
মিহালি শিকঝ্যেন্তমিহাল্যি তাঁর ‘ক্রিয়েটিভিটি’ বইয়ে ১৯৯৬ সালে লিখেছিলেন যে কোনো-কোনো কবি বা শিল্পী তাঁদের সমকালের তুলনায় অতিদূর ভবিষ্যতেও জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল হতে পারেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে ফ্লোরেন্সের অপরূপ যেসব ভাস্কর্য ১৪০০ থেকে ১৪২৫ এর ভিতর নির্মিত হয়েছিল, তার সমাদর হতে একশো বছরেরও বেশি সময় লেগে গিয়েছিল। কিন্তু সমাদর হলো যখন, তখনই আমরা বলব যে সেইসব মৃত ভাস্করেরা ক্রিয়াশীল হলেন। কবি গৌতম বসুকে আমরা আমাদের সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা একজন ক্রিয়াশীল কবি মনে করি, যিনি চলে যাওয়ার দীর্ঘ, দীর্ঘদিন পরেও তিনি কবিতা পাঠকের কাছে জীবন্ত থাকবেন। এর জন্য তাঁকে আগামী সমাজের ভাষা খুঁজতে হয় নি, তিনি সুদূর অতীত থেকেও এক দ্যুতি গ্রহণ করে তাকে আত্মস্থ করে, নিজস্ব রুচিনির্মাণের বলয়ে তাকে পুনরাবিষ্কার করে আমাদের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।
সৌম্য দাশগুপ্ত

আটের দশকের কবি, প্রাবন্ধিক, এবং অগ্রবীজ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক, যিনি আশির দশক থেকেই দুই বাংলার সাহিত্যিকদের নিয়ে সেতুনির্মাণ করে কাজ করে চলেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম “রাজার জামা পরা মায়াবী সাতদিন” (১৯৯৪), “কবিতা, ডালাস” (১৯৯৯), “মহাপৃথিবীর ওয়েবসাইট” (২০০০), এবং “আলো, আলোতর, আলোতম” (২০০৮)। এছাড়া অনুবাদ কবিতার বই “কবিতা, ডাউন আন্ডার” (অস্ট্রেলিয়ার কবিতা, ২০০৭), “টোমাস ট্রান্সট্রোমারের কবিতা” (২০১২)।
পেশায় তিনি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন সংস্থা সাচি এন্ড সাচি র কর্মকর্তা, এবং সাদার্ণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত অধ্যাপক। থাকেন লস এন্জেলেস ও কলকাতা মিলিয়ে, এবং নিয়মিত ঢাকা-চট্টগ্রামে যান। shoumyo@gmail.com ।
+1-(714)-814-2547

