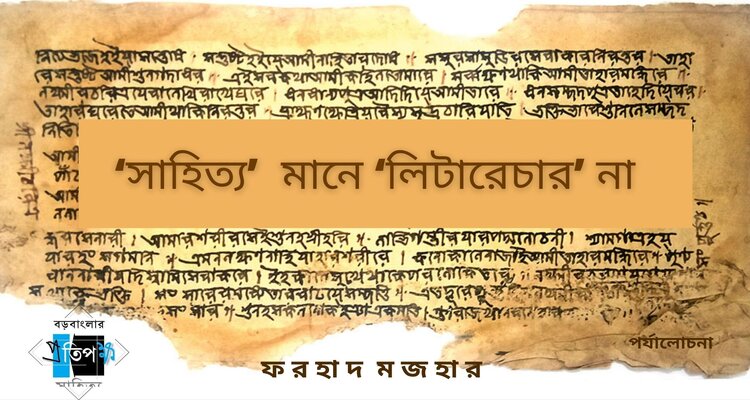
।। ফরহাদ মজহার ।।
“বাংলা ভাষায় ‘সাহিত্য’ ধারণা যে মূলে ইংরেজি ‘লিটারেচার’-এর অনুবাদ নয়, সেটা বুঝে নেওয়া জরুরী। প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বাংলা ভাষায় ‘সাহিত্য’ সংক্রান্ত ধারণা ও অন্যান্য বিবেচনা সম্পর্কে আমাদের বোঝাবুঝি যথাসম্ভব হালনাগাদ করে তোলা। কোনো নতুন সাহিত্যতত্ত্ব বানাবার দায় মাথায় নিয়ে এই পুনর্পাঠ নয়। বরং সাহিত্যের যে তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মজুদ রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করা প্রাথমিক কাজ। তাই ‘সাহিত্য’ ব্যাপারটা আসলে কী এবং সাহিত্য চর্চা করতে চাইলে গোড়ার জিজ্ঞাসাগুলো কেমন ছিল, সেই সব ভুলে না গিয়ে আবার স্মরণে আনা দরকার। এরপরের কাজ হচ্ছে টেকনিক বা টেকনলজির যুগে নতুন ভাবে সাহিত্য ধারণাকে ছেঁচে তোলা। টেকনিক, টেকনলজি বা কৃৎকৌশলের বিচারকে সাহিত্য বিচারের অন্তর্গত করা না গেলে সাহিত্য চর্চার নতুন ক্ষেত্র বা দিগন্ত আরও পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়বে না। আমরা পুরানা কাসুন্দি ঘাঁটতে থাকব। পাশাপাশি টেকনলজি কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় অভ্যাস বদলে দেয়, দিয়েছে এবং দিচ্ছে সেই সবের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে আমরা বুঝব কিভাবে আমরা বদলে গিয়েছি এবং বদলে যাচ্ছি…”
লিখছেন ফরহাদ মজহার-
‘সাহিত্য’ মানে ‘লিটারেচার’ না
“যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
“প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
‘সাহিত্য’ : ‘ব্যুৎপত্তি’ ও ‘তাৎপর্য’
‘প্রতিপক্ষ’ যখন আমরা নতুন করে ‘বড় বাংলার সাহিত্য’ হিশাবে বের করতে শুরু করি তখন একটা প্রশ্ন আমাদের মোকাবিলা করতে হয়। সেটা হলো, ‘বড় বাংলা’ বলার পেছনে আমাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা। সঙ্গত প্রশ্ন। যথা, দুই বাংলা একত্রীকরণ জাতীয় চিন্তা। এর সহজ ও সরল উত্তর, না।
তবে এই প্রকার প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই আসলে অর্থহীন। ‘উদ্দেশ্য’ মানে কোন একটা আগাম তৈরি আইডিয়া বা চিন্তা মাথায় রেখে বাস্তবায়নের মামলা। এরককম কোনো আগাম বানানো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ‘প্রতিপক্ষ’ ওয়েবজিনের নাই। দ্বিতীয়ত, উপমহাদেশের দুই বৃহৎ সম্প্রদায় মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে পরস্পরকে বোঝা ও জানার প্রকট অভাব রয়েছে। চাইলেই হিন্দু-মুসলমানে রাতারাতি ভাব হয়ে যাবে না। তার বিস্তর কারন আছে। কয়েকটি বলছি:
আধুনিক জাতিবাদ, ধর্মকে স্রেফ পরিচয়বাদে পর্যবসিত করেছে। ধর্মীয় পরিচয় ধর্মীয় জাতিবাদ বা সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দেয়। পরস্পরের মধ্যে বিভেদ জারি থাকার কারণও প্রধানত এই পরিচয়বাদী আধুনিক জাতিবাদে। ফলে ধর্মের পর্যালোচনা বা ধর্মের মধ্য দিয়ে ভাষা, কল্পনা, চিন্তা, ইচ্ছা, বাসনার বিকাশও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বড় বাংলার ভক্তি আন্দোলন, সুফি-বয়াতি ধারাসহ অপরাপর লৌকিক চর্চার মধ্যে আমরা টের পাই গুরুতর বহু মানবিক জিজ্ঞাসা বিভিন্ন পুরান, নবী-রসুলদের কেচ্ছা, লৌকিক কাহিনী এমনকি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তোলা হয়েছে। সাহিত্য, ভাব, দর্শন বা চিন্তার দিক থেকে যাদের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্যের আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের অনুকরণ করতে গিয়ে ‘আধুনিকতার’ তোড়ে নিজেদের জিজ্ঞাসা ভুলে গিয়েছি। দূরত্ব আরও বেড়েছে। এরপর রয়েছে অর্থনৈতিক কারন। পুঁজিতান্ত্রিক অসম উন্নয়ন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কারনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এককালের বৃহৎ বাংলার মধ্যে বিস্তর অদল বদল ঘটিয়েছে। ফলে দুই বাংলার একত্রীকরণ এখন অবাস্তব ধারণা, বড় জোর রোমান্টিক অভিক্ষেপ মাত্র। তবে পশ্চিম বাংলায় আমরা সম্প্রতি একদিকে ‘জয় শ্রীরাম’ আর তার বিপরীতে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান শুনছি। ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে আমাদের পুলকিত হবার কিছু নাই। প্রথমত এই শ্লোগান স্থানীয় ভোটের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিম বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে তাকালে বোঝা যায় উচ্চ বর্ণের হাতে তৈরি ‘বাঙালি’ ধারণার বিশেষ হেরফের হয় নি। এই ধারণার মধ্যে ঔপনিবেশিক আমলের মতো মুসলমান বাঙালি অনুপস্থিত। হিন্দু-মুসলমানসহ সবাইকে নিয়ে ‘বড় বাংলা’র কল্পনা অনেক দূরের ব্যাপার। অন্যদিকে ভারত হিন্দুত্ববাদের উত্থান এবং বাংলাদেশের প্রতি দিল্লীর নীতির কারণে বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা প্রবল হয়েছে। ফলে দুইবাংলা একত্রীকরণ জাতীয় কোন রোমান্টিক উৎকল্পনার জায়গা নাই বললেই চলে।
আমাদের ইতিহাস বোধের বড়ই অভাব। তদুপরি, বাঙালি বড়ই রোমান্টিক প্রাণী! তাই আমামদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নে আমরা বেশ আমোদ বোধ করেছি ! প্রশ্নের তোড় দেখে বুঝে যাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী – দুনিয়ার যেখানেই থাকুক – এখনও বাস্তবতা এবং রোমান্টিকতার ভেদ বুঝতে অক্ষম। রোমান্টিকতা খারাপ কিছু না। কিন্তু রোমান্টিকেরও মাটিতে ও ইতিহাসে পা রেখে বাস্তবিক হতে হয়।
কিন্তু নিজেদের বাসনা সম্পর্কে এই উত্তর শেষাবধি অর্থহীন। কোন কাজই রাজনীতি বা রাজনৈতিকতার বাইরে নয়। আরও নয় যদি সেই কাজ বা চর্চার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমাদের কল্পনা, স্মৃতি, চেতনা ও চিন্তাকে রূপ দেবার সামর্থ রাখে, আমাদের ইচ্ছা ও সংকল্পে রূপান্তর আনে। রূপান্তরের ফল রাজনীতিতে পড়ে। সেই দিক থেকে সাহিত্য চর্চা রাজনীতি বা রাজনৈতিকতারই চর্চা। সাহিত্য ক্ষমতার বিন্যাস কিংবা পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখে। কখনও পরোক্ষ ভাবে, কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে। সাহিত্য চর্চা বিপজ্জনক কাজ। বিদ্যমান, অনুমান, কল্পনা, চিন্তাচেতনা ও ক্ষমতার ভারসাম্য ছারখার করে দেবার ক্ষমতা সাহিত্যের আছে। একদিকে সাহিত্য চর্চা ক্ষমতা চর্চা কিংবা রাজনীতি থেকে আলাদা। কিন্তু অপরদিকে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন কোন পরিসর নয়। আদতে যাহা বাহান্ন তাহাই তেপ্পান্ন।
সাহিত্য রাজনীতির বাইরের কিছু না। কিন্তু আমাদের কাছে ‘বড় বাংলা’ একান্তই সাহিত্যোচিত ধারণা। এই অর্থে যে সাহিত্য চর্চাই আমাদের উদ্দেশ্য। এটা কোনো রাজনৈতিক প্রকল্প না। অর্থাৎ বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা ‘বড় বাংলা’ কথাটা প্রচার করছি না। বরং নিজেদের নিয়ে সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে ভাববার অভ্যাস থেকে আমরা মুক্ত হতে চাইছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে তাদের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সীমা বা বৃত্ত থেকে আমরা মুক্ত রাখতে চাই। আমরা এতোটুকুই দাবি করি যে ‘বাংলাভাষী’ হিশাবে আমাদের কিছু সাধারণ স্বার্থ আছে, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সেই সাধারণ লক্ষ্যের অন্তর্গত। তাই ভূগোল ও রাজনৈতিক বৃত্তে বন্দী না থেকে আমরা নিজেদের আরও বড় পরিসরে ভাবতে চাই। আরও বড় পরিসরে অন্য আরও অনেকের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা যুক্ত হওয়াই আমাদের বাসনা। সাহিত্য ব্যাপারটাই তাই। অপরের ‘সহিত’ যুক্ত হওয়া এবং বিরাজ করবার বাসনা। সাহিত্য সেই বিরাজমানতার শর্ত তৈরি করে।
কথাটা আমরা বলছি বটে, কিন্তু সেটা ব্যাখ্যার দাবি করে। স্বীকার করি ‘সাহিত্য’ কথাটা আমাদের আবার নতুন ভাবে বোঝা এবং অন্যদের বোঝাবার একটা দায় তৈরি হয়েছে। সেটা শুরুতে কিভাবে করা যায়, তা নিয়ে আমরা ভেবেছি। এই নিবন্ধটি সেই ভাবনারই ফল। ‘প্রতিপক্ষ’ সাহিত্য’ বলতে কী বোঝে, এখানে তা নিয়ে কথা বলব।
আমাদের মনে হয়েছে ‘সাহিত্য’ নিয়ে আলোচনা আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’ রচনাটি আরেকবার পড়ার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করতে পারি। শুরুতে এখানে প্রবন্ধটি নতুন করেপড়ার কাজটাই আমরা করব। লেখাটির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতিমূলক কাজটা হয়ে গেলে তথাকথিত ‘মিডিয়া’ বা মাধ্যমের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বিচারে আমরা মনোযোগী হব। যেমন, ছাপাখানা। এরপর, ফটোগ্রাফি, সিনেমা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ইত্যাদি।
ছাপাখানা, বাজার ব্যবস্থা , প্রমিত ভাষা ইত্যাদি মিলে যে সমপ্রকৃতি ও সমরূপের ‘বাঙালি’ নামক কল্পনা ঔপনিবেশিকতার ঔরসে বর্ণ হিন্দু তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, সেই নির্মাণে মুসলমান বাঙালি অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং তার অনিবার্য রাজনৈতিক পরিণতির আলোকে বিচার করা জরুরী। শুধু নিজেদের ঐতিহাসিক ভাবে বোঝার জন্য নয়, সাহিত্যের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের আত্মবিশ্বাস আবার দৃঢ় করবার জন্য। সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক হলেও যদি বাংলা সাহিত্য আমাদের ‘বাঙালি’ হিশাবে ভাবতে শিখিয়েছে, তাহলে সাহিত্য নিজগুণে সেই সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি চাইবে, এটা আশা করা যায়। তাই আমরা মনে করি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ত্রুটি সাহিত্য নিজেই আবার মীমাংসা করবার পথ ও প্রকরণ প্রদর্শন করতে সক্ষম। সাহিত্য আমামদের ‘বড়’ বা ‘বৃহৎ’ করবে। হয়তো দীনেশ্চন্দ্র সেন এই বাসনা মনে রেখেই ‘বৃহৎ বাংলা’ রচনা করেছিলেন। বড় বাংলা কথাটা নিজেদের বড় ভাববার বাসনার সঙ্গেও যুক্ত বলা যায়।
পূর্ব বাংলার জমিদারি এবং বাজার ব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠা কলকাতা শহরে আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে। ‘সাহিত্য’ ধারণার উদ্ভবও একই শতকে, বিশেষ ভাবে উনিশ শতকে। অন্যদিকে খ্রিস্টান পাদ্রিদের ধর্মান্তঃকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খ্রিস্টিয় সুসমাচার জাতীয় সাহিত্য স্থানীয় ভাষায় প্রচারের তাগিদে ছাপাখানার আমদানি এবং বইয়ের বাজার গড়ে ওঠে। সবই একই সূত্রে ‘সাহিত্য’ নামক ধারণার অন্তর্গত। একই ইতিহাস ‘বাঙালি’ নামক ধারণাটিরও ঐতিহাসিক উদয় ঘটাবার বাস্তব শর্ত। এটাও মনে রাখা দরকার, আগেই উল্লেখ করেছি, ‘বাঙালি’ ধারণার মধ্যে বাংলাভাষী ‘মুসলমান’ বিস্ময়কর ভাবে শুরু থেকেই অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিণতি আছে। তাহলে বুঝতে হবে ‘সাহিত্য’ মানে স্রেফ লেখালিখি না।
এই দিকটা গোড়াতেই সাফ করা দরকার। জাতি হিশাবে ‘বাঙালি’ নামক কল্পনা তৈরির বাস্তব ভিত্তি আধুনিক বাংলা সাহিত্য। ‘বাঙালি’ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। এই গ্রন্থির জট ছাড়ালে আমরা দেখব আমরা ইতিহাসের তৈরি পদার্থ, তথাকথিত ‘আবহমান’ কিম্বা চিরায়ত কোনো সত্তা না। আমরা অতীতে যা হয়েছি, বর্তমানে সেটা আর নই। আগামিতেও একই প্রকার থাকব না। বাংলাভাষী এখন নিজেদের খণ্ড খণ্ড কল্পনা করতে ও ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আগামিতে তার বিকাশ নাকি বিলয় ঘটবে তাও এখন আমরা হলফ করে বলতে পারি না। বাংলা সাহিত্য এবং তার চর্চা এই বিখণ্ডীভবন ও বিলয় প্রবণতা এড়িয়ে আরও বড় বা বৃহৎ পরিসরে বাংলা ভাষীদের কল্পনা করবার শক্তি জোগাতে পারে কিনা সেটা একালে বৃহৎ একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলে আমরা মনে করি। ‘প্রতিপক্ষ’ এই চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে সাহিত্য চর্চায় এসেছে। তাই সাহিত্য বলতে আমরা নিজেরা কি বুঝেছি, সেটা পেশ করে রাখা দরকার।
‘সাহিত্য’ নামক ধারণা নিয়ে আলোচনা আমরা রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করব। এরপর অন্যত্র যাব। এখানে রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’ লেখাটি আমরা আবার নতুন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়ব।
পূর্ব বাংলার জমিদারি এবং বাজার ব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠা কলকাতা শহরে আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে। ‘সাহিত্য’ ধারণার উদ্ভবও একই শতকে, বিশেষ ভাবে উনিশ শতকে। অন্যদিকে খ্রিস্টান পাদ্রিদের ধর্মান্তঃকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খ্রিস্টিয় সুসমাচার জাতীয় সাহিত্য স্থানীয় ভাষায় প্রচারের তাগিদে ছাপাখানার আমদানি এবং বইয়ের বাজার গড়ে ওঠে। সবই একই সূত্রে ‘সাহিত্য’ নামক ধারণার অন্তর্গত। একই ইতিহাস ‘বাঙালি’ নামক ধারণাটিরও ঐতিহাসিক উদয় ঘটাবার বাস্তব শর্ত। এটাও মনে রাখা দরকার, আগেই উল্লেখ করেছি, ‘বাঙালি’ ধারণার মধ্যে বাংলাভাষী ‘মুসলমান’ বিস্ময়কর ভাবে শুরু থেকেই অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিণতি আছে। তাহলে বুঝতে হবে ‘সাহিত্য’ মানে স্রেফ লেখালিখি না। এই দিকটা গোড়াতেই সাফ করা দরকার।
‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’: রবীন্দ্রনাথ
‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’ রচনাটি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সভার বার্ষিক অধিবেশনে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি আমাদের আবার নতুন করে পড়বার স্বার্থ আছে। সেটা হলো ‘সাহিত্য’ সম্পর্কে প্রতিপক্ষের পর্যালোচনামূলক ভাব ও চর্চার জায়গাটা বাংলা সাহিত্যের নিজের ‘সাহিত্য’ সম্পর্কে ধারণার আলোকে হাজির করা। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ভেতর থেকে বোঝা।
সাহিত্য, সাহিত্য চর্চা এবং সাহিত্যের পর্যালোচনা আজ অবধি টেকনলজি বা কৃৎকৌশলের পর্যালোচনা থেকে আলাদা করে করাই রীতি হয়ে উঠেছে। প্রতিপক্ষ এই বদ্ধমূল ও বিদ্যমান ধারণার পর্যালোচনা করতে চায়, যাতে বাংলা ভাষার মধ্যে গড়ে ওঠা ‘সাহিত্য’ ধারণার ব্যাপকতা ও গভীরতা আমরা ধরতে পারি এবং তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। টেকনলজি হিশাবে ছাপা বই এবং তার বাজার কিভাবে সাহিত্যের চরিত্র বদলে দিয়েছে তাকে জানা ও বোঝা খুবই জরুরী। ছাপাখানা মুখস্থ সাহিত্য, অর্থাৎ শ্রুতি ও কণ্ঠ নির্ভর সাহিত্যচর্চাকে মুদ্রিত সাহিত্য থেকে আলাদা করেছে। এর ফল সুদূর প্রসারী, বিপুল, ব্যাপ্ত ও গভীর। সাহিত্য নিয়ে এই গোড়ার আলোচনাও আমরা এখনও বাংলা ভাষায় শুরু করতে পারি নি। এরপর রয়েছে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ডিজিটাল মিডিয়া, কমিউনিকেশান ইন্ড্রাস্ট্রি, ইত্যাদি। ছাপাখানার সাহিত্য সাহিত্যের একমাত্র রূপ নয়। টেকনলজি বা কৃৎকৌশলের বিচার ছাড়া সাহিত্য বিচার সম্ভব, এটা আমরা মনে করি না।
এই কথাগুলো শুরুতে অপরিচিত মনে হবে। তবে আশা করি প্রাথমিক আলোচনার পর্ব শেষ হলে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এই সকল বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করব। এখন প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সাহিত্য, সাহিত্যের ‘মাধ্যম’ ইত্যাদিকে টেকনিক বা কৃৎকলার জায়গা থেকে নতুন করে বোঝার জায়গাটা সাফ করে নেওয়া। বাংলা ভাষায় ‘সাহিত্য’ ধারণা যে মূলে ইংরেজি ‘লিটারেচার’-এর অনুবাদ নয়, সেটা বুঝে নেওয়া জরুরী। প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বাংলা ভাষায় ‘সাহিত্য’ সংক্রান্ত ধারণা ও অন্যান্য বিবেচনা সম্পর্কে আমাদের বোঝাবুঝি যথাসম্ভব হালনাগাদ করে তোলা। কোনো নতুন সাহিত্যতত্ত্ব বানাবার দায় মাথায় নিয়ে এই পুনর্পাঠ নয়। বরং সাহিত্যের যে তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মজুদ রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করা প্রাথমিক কাজ। তাই ‘সাহিত্য’ ব্যাপারটা আসলে কী এবং সাহিত্য চর্চা করতে চাইলে গোড়ার জিজ্ঞাসাগুলো কেমন ছিল, সেই সব ভুলে না গিয়ে আবার স্মরণে আনা দরকার। এরপরের কাজ হচ্ছে টেকনিক বা টেকনলজির যুগে নতুন ভাবে সাহিত্য ধারণাকে ছেঁচে তোলা। টেকনিক, টেকনলজি বা কৃৎকৌশলের বিচারকে সাহিত্য বিচারের অন্তর্গত করা না গেলে সাহিত্য চর্চার নতুন ক্ষেত্র বা দিগন্ত আরও পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়বে না। আমরা পুরানা কাসুন্দি ঘাঁটতে থাকব। পাশাপাশি টেকনলজি কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় অভ্যাস বদলে দেয়, দিয়েছে এবং দিচ্ছে সেই সবের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে আমরা বুঝব কিভাবে আমরা বদলে গিয়েছি এবং বদলে যাচ্ছি। এ লেখাটি পড়বার আগে ‘প্রতিপক্ষ ও সাহিত্য’ লেখাটি পড়ে এলে পাঠকের সঙ্গে আমাদের দেয়া-নেয়ার জায়গাটা শুরুতেই মজবুত ভাবে শুরু হতে পারে।
একটা খুবই সাধারণ কথা দিয়ে শুরু করি। বাংলাভাষায় আমরা ‘সাহিত্য’ কথাটা আসলে ইংরেজি Literature-এর অনুবাদ হিশাবে এখন ব্যবহার করি। এটা ঔপনিবেশিকতার জের, অন্যদিকে এই অনুকরণ নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে উৎপন্ন ধারনা ও বর্গের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ছেদও বটে। আমাদের সাহিত্য ভাবনায় ‘লিটারেচার’ জাতীয় কোনো ধারণা কস্মিনকালেও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’ তার একটি প্রমাণ বটে। লেখাটির প্রতি আমাদের আগ্রহের জায়গাও এখানে। রবীন্দ্রনাথের লেখাটি নিয়ে শুরুতে দীর্ঘ আলোচনার এটাই প্রধান কারণ।
সাধারণত বলা হয় ‘সাহিত্য’ শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে। এটা মেনে নিতে অসুবিধা নাই যে শব্দ হিশাবে ‘সাহিত্য’ শব্দটি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। যেমন, ‘সহ’ বা ‘সহিত’ শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হলেও ‘সাহিত্য’ শব্দটি যে তাৎপর্য বাংলা সাহিত্যে লাভ করেছে সেটা একান্তই তার নিজস্ব। এই তাৎপর্য সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ‘সাহিত্য-পরিচয়’ গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ তর্ক তুলে বলছেন:
“এই সাহিত্য শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কারণ অতি প্রাচীন গ্রন্থে এই শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মূল অর্থ “একসঙ্গে বা একত্র থাকা” দুটো জিনিস একত্র আছে এই তাৎপর্য বুঝাইতে একথা বলা চলে যে তাহাদের সাহিত্য আছে। আবার কোনও লোকের সহিত সঙ্গ করাকে তাহার সাহিত্য করা বলা চলে”।
(দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৩)
আমরা বাংলায় সাহিত্য শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি সেই অর্থে প্রাচীন কালে সংস্কৃতে কাব্য শব্দটি ব্যবহার করা হোতো। অর্থাৎ ‘সাহিত্য’ ধারণাটির যে তাৎপর্য বাংলা সাহিত্যে গোড়া থেকে তৈরি হয়্যেছে তার উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্য নয়। এটা বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব জিনিস।
সুরেন্দ্রনাথ ‘ব্যুৎপত্তি’ ও ’তাৎপর্য’ – এই দুই ধারণার মধ্যে যে ভেদ করেছেন তা সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তর্ক। এই তর্কের সঙ্গে এখন যেন আবার সক্রিয় ভাবে যুক্ত হতে পারি তার জন্য একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেব।
“কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারা সেই শব্দে ভাষায় প্রচলিত তাৎপর্যের নির্ণয় করা যায় এ কথা বলা চলে না। গম্ ধাতু হইতে গো শব্দের উৎপত্তি তাই বলিয়া যাহা চলে তাহাই গো এই ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়া গরু অর্থে ব্যবহৃত গো শব্দের তাৎপর্য বাহির করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যাহা চলে গমন করে তাহাকেই গোরু বলা চলে না এবং ব্যুৎপত্তির অনুরোধে অর্থ করিতে গেলে গৌস্তিষ্ঠতি বা গোরু বসিয়া আছে এরূপ বলা চলে না। কারণ, সচল বস্তুকেই যদি গৌঃ বলিতে হয় তাহলে বসিয়া থাকিলে তাহার সে নাম সম্ভব হয় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসন্ধান করিলে তাৎপর্যের যে বীজটি পাওয়া যায়, কালক্রমে চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের সাহায্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রম পরিণতির ধারাটি লক্ষ্য করিয়া চলিলে, তাহার ভাষায় প্রকৃত তাৎপর্যটির সার্থকতা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ভাষায় একটি শব্দের নানা অর্থে ব্যবহার দেখা যায় তাহাদের সঙ্গতি করিতে হইলে অনেক সময় এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাহায্য নিতে হয়। মানুষের চিত্তে ক্রম পরিবর্তন ভাবধারা হইতে একটি আদিম অর্থ আপনাকে নানা শাখা-প্রশাখায় ব্যক্ত করিয়া বিভিন্ন অর্থ রূপে প্রকাশ করে” ।
(দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১)
‘সাহিত্য’ শব্দ হিশাবে সংস্কৃত থেকে এসেছে বটে, কিন্তু বাংলায় যে তাৎপর্য অর্জন করেছে তা একেবারেই তার নিজস্ব। ভাষার মধ্যে এই কারবার কিভাবে ঘটে সেটা বোঝাতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ভাষায় কোনো শব্দ, ধারনা বা বর্গের তাৎপর্য বিচারকে তার ব্যুৎপত্তি বিচার থেকে আলাদা করছেন। কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ‘অর্থ’ আর সেই ভাষায় সেই শব্দের ‘তাৎপর্য’ এক নয়। অর্থাৎ অর্থ এবং তাৎপর্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সুরেন্দ্রনাথ তার বইয়ের শুরুতেই সেটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। কোন শব্দের একটা বিচ্ছিন্ন আভিধানিক কিংবা আক্ষরিক মানে থাকতেই পারে। কিন্তু সেটাই সাহিত্যে তার অর্থ নির্ণয়ে নির্ধারক ভূমিকা রাখে না। বরং একটি বাক্যে, গদ্যাংশে, গল্পে, বয়ানে কিভাবে সেই শব্দ বা অক্ষরচিহ্নটি ব্যবহার হোল, সামগ্রিক সাহিত্য তার ফল কি দাঁড়াল তার দ্বারা আমরা শব্দটির অর্থ বুঝি। এই বোঝা বা সামগ্রিক ভাবে অর্থ নির্ণয়কে সুরেন্দ্র তাৎপর্য বলেছেন। তাৎপর্যও অর্থ বিচার বটে, কিন্তু আভিধানিক বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নয়।
এই ভেদ ধরতে পারল আমরা পাশ্চাত্যের অবিনির্মাণ তত্ত্বের (Deconstruction) সাহিত্য বিচার পদ্ধতি আগাম কিছুটা আঁচ করতে পারি। সেই সুবাদে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা এবং ভাষার দর্শনে প্রবেশের একটা দরজাও আমরা পেয়ে যাই। সেই সূত্রে আমরা জাক দেরিদা, ল্যুডভিগ হুইৎঝেন্সটাইন, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ও আর অনেকের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ের নতুন ক্ষেত্রও হয়তো পরবর্তী কোনো লেখায় চিহ্নিত করতে পারব। আরও মহারথীদের আলোচনা করার ফুরসতও পেয়ে যাব। কিন্তু আগে ‘সাহিত্য’ কথাটা বাংলায় কিভাবে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে হাতে পেয়েছি সেটা পরিষ্কার করতে চাই।
সুরেন্দ্রনাথ থেকে আরেকটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:
ইহাও দেখা যায় যে ভাবধারার পরিববর্তনে মূল অর্থটি ভাষা হইতে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যায় এবং শব্দকে আশ্রয় করিয়া একেবারে নূতন অর্থের উৎপত্তি হয়, অথচ তাহার সহিত সম্পর্ক একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এই অর্থ-পরম্পরার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মানুষের চিত্তে কোনও একটি বীজ-ভাবকে (Concept) অবলম্বন করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। সে তাহার মধ্যে নূতন নূতন অর্থ, নূতন নূতন তাৎপর্য্য অনুসন্ধান ও সৃষ্টি করিয়া আপনাকে সম্মুখের পথে চালিত করিতে থাকে এবং এই জন্য একটি শব্দের বৃন্তে নানা দেশে নানা কালে বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন তাৎপর্য ফুটিয়া উঠে
(দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ২)
দেখা যাচ্ছে সুরেন্দ্রনাথ ‘সাহিত্য’ কথাটিকে কনসেপ্ট বা ‘বীজভাব’ গণ্য করে নি। অর্থাৎ একে কোনো সামান্য ধারণা গণ্য করে সার্বজনীন বা চিরায়ত কোন বর্গে পরিণত করতে চান নি। শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, কিন্তু যে ভাব নিয়ে তার আরম্ভ সেটা সংস্কৃতের নয়, বাংলার একদমই নিজস্ব। আবার, ধারনাটি কোন বীজভাব নয় যে তাকে আবর্তন করেই বাংলায় সাহিত্যের তাৎপর্য নির্ণয় হচ্ছে। বরং তাৎপর্য তৈরি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসের মধ্যে।
তাই সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন:
“সেই জন্য কোন বিশিষ্ট শব্দের যে কি তাৎপর্য তাহার কোনও একটি নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না। অর্থ ও তাৎপর্যের জিজ্ঞাসা হইলেই প্রশ্ন ওঠে এ অর্থ কোন্ কালের? কোন্ দেশের? কোন্ সমাজের? কোন্ ভাবুকের চিত্তবৃত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল? ক্রম পরিবর্ত্তমান অর্থ-সঞ্চয়ের মধ্য দিয়া কিসের অনুসন্ধান চলিয়াছে তাহার অনুসন্ধান না করিলে সেই শব্দের তাৎপর্য-নির্ণয় দুঃসাধ্য হয়। এই জন্য গায়ের জোরে বা গলার জোরে মত স্থাপনের যে রীতি রীতি দেখা যায় তাহাতে দ্বন্দ্ব বাড়িয়া উঠে, কিন্তু মীমাংসা হয় না” ।
(দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ২)
তাহলে ‘সাহিত্য’ নামক ধারণারও কোন চিরায়ত বা শ্বাশ্বত তাৎপর্য নাই। দেশকালপাত্র ভেদে তার বিচার করতে হবে। ‘সাহিত্য’ সংস্কৃত ভাষা থেকে আসতেই পারে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে‘সাহিত্য’ ধারণার তাৎপর্য ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তার বিচার করতে হলে সাহিত্যের ‘ক্রম পরিবর্ত্তমান অর্থ-সঞ্চয়-এর মধ্য দিয়ে আমরা আজ অবধি কি অনুসন্ধান করছি সেটা জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ‘জাতীয় সাহিত্য’ রচনাটি নতুন করে পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা সেই কাজটা শুরু করতে চাইছি।
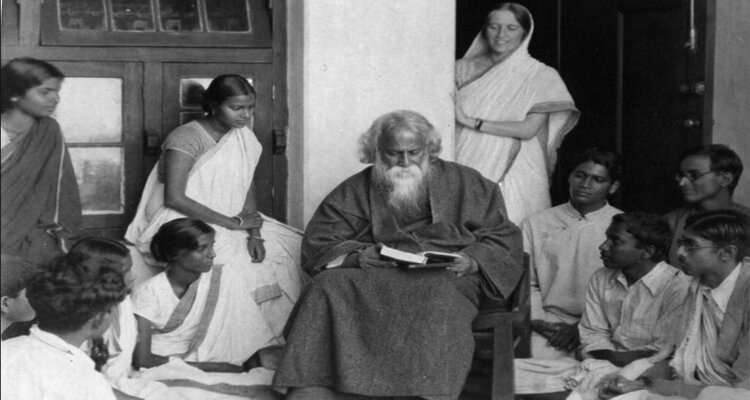
যদি আমরা ‘জাতীয় সাহিত্য’ লেখাটি ঘনিষ্ঠ ভাবে পড়ি তখন দেখব, ‘সাহিত্য কথাটির তাৎপর্যকে রবীন্দ্রনাথ আরেকটি ধারণাগত স্তরে উন্নীত করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘সাহিত্য’ কথাটা সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। ইংরেজি ‘লিটারেচার’ কথাটার মানে হচ্ছে লিখিত কাজের সমাহার বা সংগ্রহ। তবে লেখালিখি মানেই লিটারেচার বোঝাত না, বরং শব্দাক্ষর বিন্যাসের বিশেষ রূপকেই ‘লিটারেচার’ বোঝানো হোতো। যেমন গল্প, নাটক, কবিতা ইত্যাদি। একসময় মৌখিক সাহিত্য (Oral Literature) সাহিত্য ধারণার অন্তর্গত হোল, কিন্তু সেটা ট্রান্সক্রাইব বা লিখিত করে নিয়ে।
বাংলাভাষায় আমরা ‘সাহিত্য’ কথাটা আসলে ইংরেজি Literature-এর অনুবাদ হিশাবে এখন ব্যবহার করি। এটা ঔপনিবেশিকতার জের, অন্যদিকে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে উৎপন্ন ধারনা ও বর্গের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ছেদ। আমাদের সাহিত্য ভাবনায় ‘লিটারেচার’ জাতীয় কোনো ধারণা কস্মিনকালেও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’ তার একটি প্রমাণ বটে। লেখাটির প্রতি আমাদের আগ্রহের জায়গাও এখানে। রবীন্দ্রনাথের লেখাটি নিয়ে শুরুতে দীর্ঘ আলোচনার এটাই প্রধান কারণ।
ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে ‘লিটারেচার’ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন literatura/litteratura থেকে। যার অর্থ শেখা, লেখা, ব্যাকরণ ইত্যাদি। আদিতে যার অর্থ ছিল ‘বর্ণমালা দিয়ে লেখ্য রূপ দান করানো (litera/littera “letter”) । ইংরেজিতে ‘literature’ কথাটার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘writing’ বা লেখালিখি ( ল্যাটিনে litera, থেকে literature), বর্ণমালা বা অক্ষর দিয়ে তৈয়ারি জিনিস। ইংরেজি সাহিত্যে এবং তার ইতিহাসে তার তাৎপর্য ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আমরা তাকেই আদর্শ জ্ঞান করে বাংলা সাহিত্য করি। বাংলায় ‘সাহিত্য’ ধারণার যে তাৎপর্য তার সঙ্গে আমাদের ছেদ ঘটে গিয়েছে। সেই ছেদ চিহ্নটা শনাক্ত করা যেমন দরকার, তেমনি বাংলা সাহিত্যে ‘সাহিত্য’ নামক ধারণার যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তার উপযোগিতা এবং সম্ভাবনা নিয়ে আমরা নতুন করে ভাবতে পারি।
এটা তাহলে শুরুতেই আমরা দাবি করতে পারি, বাংলা ভাষায় ‘সাহিত্য’ খুবই মৌলিক একটি ধারণা। উপনিবেশের ভারে আমাদের ভাব ও চর্চার জগত থেকে এই তাৎপর্যপূর্ণ ধারণাটি হারিয়ে গিয়েছে। ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকাটি যখন আমরা শুরু করি তখনই আমরা ‘সাহিত্য’কে আবার সাহিত্য বিচারের কেন্দ্রে নিয়ে আসার কথা ভাবতে শুরু করি। একটা কারণ হচ্ছে সাহিত্যকে লিটারেচার থেকে মুক্ত করা, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারণা ও বর্গাদি থেকে বেরিয়ে আসা; দুই. বাংলা ভাষায় ‘সাহিত্য’ ধারণার সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং পাশ্চাত্য প্রভাব বলয়ের বাইরে নিজের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে নিজেদের চিন্তা ভাবনার সীমা ও সম্ভাবনা বিচার করা। আমরা উপলব্ধি করি যে গোড়ার কোদালি কাজগুলো করে না এলে বাংলা সাহিত্যে নতুন ও মৌলিক কাজ করার শর্ত আমরা তৈরি করতে পারব না। ঔপনিবেশিকতা আমাদের নিজেদের সঙ্গে নাড়ির বন্ধন কেটে ফেলেছে, সেই ক্ষতস্থানগুলো চেনা এবং ক্ষত যথাসম্ভব সারিয়ে তোলা না গেলে নিজের হিম্মতে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে আমরা নিজের মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়াতে পারব না। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিকতার গোলাম হয়ে থাকব।
তাহলে প্রথম সবক হচ্ছে এই: ‘সাহিত্য’ মানে লিটারেচার বা লিটারেচার জাতীয় কিছু না। সাহিত্যের ধারণা স্পষ্ট হলে সাহিত্যের সঙ্গে ছাপাখানার সম্বন্ধ এবং একালে ইলেক্ট্রনিক ও ডিজিটাল মিডিয়ার সম্পর্ক বিচার আমাদের জন্য সহজ হবে। কারণ সাহিত্য মাধ্যম, বা টেকনলজি নিরপেক্ষ নয়। সাহিত্য চর্চার অর্থ কোনো না কোনো মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা, কোনো না কোনো টেকনলজি বা কৃৎকলার আশ্রয় নেওয়া। সেটা যেমন কণ্ঠস্বর বা শ্রুতি হতে পারে, তেমনি হতে পারে খাতা, কলম, ছাপাখানা, ইলেক্ট্রনিক টেকনোলজি কিম্বা ডিজিটাল কৃৎকৌশল। মাধ্যম বা টেকনলজি অতএব সাহিত্য বচারের অবিচ্ছেদ বিষয়। কিন্তু এই শেষের কথাগুলো আলোচনার শুরুতে এখনো অস্পষ্ট মনে হবে। তবে আমাদের আগামী আলোচনার নোক্তা হিশাবে বলে রাখতে হচ্ছে। তবে প্রথমে রবীন্দনাথের বরাতে ‘সাহিত্য’ ধারণাটি আমরা আগে বুঝে নিতে চাই।
‘সহিত থেকে সাহিত্য’
‘‘সহিত’ শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের, সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন” ।
রবীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।
‘সাহিত্য’ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মূলত দাবি করছেন, সাহিত্যই ‘সমাজ’ তৈরির শর্ত। তাঁর এই দাবিটি প্রচ্ছন্ন, অতএব তা স্পষ্ট করার দরকার আছে।
জীবের সমষ্টি হিশাবে আমরা মানুষদের দেখি। কিন্তু জীবের সমষ্টি সমাজ নয়। সমাজ জীবন্ত। এই সপ্রাণতার কারন মানুষের সঙ্গে মানুষের ‘সজীব বন্ধন’। আমরা মানুষ দেখি বটে, কিন্তু মানুষের সমষ্টিকে ‘সমাজ’ গণ্য করা ভ্রান্তি। মনুষ্য জাতীয় জীব মণ্ডল আর ‘সমাজ’ যে এক নয় সেটা একদমই আমরা ধরতে পারি না।
দ্বিতীয়ত ‘সমাজ’ একটি সাধারণ বা সামান্য ধারণা, তার রূপ বিভিন্ন ও বিচিত্র। অর্থাৎ সমাজের রূপ নানান রকম হতে পারে। সেই রূপের বিচার বিশ্লেষণ ও বোঝাবুঝির পদ্ধতি ও চর্চা আলাদা। সেটা অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদির বিষয়। রূপের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র একটি সমাজকে অন্য সমাজ থেকে আলাদা করে। রবীন্দ্রনাথ যাকে ‘সজীব বন্ধন’ বলছেন তাকে আরও কংক্রিট ভাবে বুঝতে হলে একটি ‘সজীব’ সমাজের উৎপাদন বিতরণ, বিনিময় ও ভোগের সজীব বন্ধন সমূহকেও বুঝতে হবে। সমাজ যার উপর টিকে থাকে।
‘সাহিত্য বুঝতে হলে আমাদের সাহিত্যের জায়গা থেকে ‘সমাজ’ বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি আমরা বিশদ আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি কারণ সমাজকে সাহিত্যের জায়গা থেকে বোঝার একটা সুবিধা সম্ভবত আমরা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারি।
‘সমাজ’ আপনা আপনি কোনো দেশে বা কালে আগাম হাজির থাকে, রবীন্দ্রনাথ এটা অনুমান করেন নি। তাঁর সাহিত্যের ধারণা একই সঙ্গে সমাজ ও সামাজিকতার ধারণা। কারণ সাহিত্য মানে ‘ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন’ মাত্র নয়। সাহিত্যের কাজ ‘মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক’ নির্মাণ। সাহিত্য ভাবের নির্মাণ নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্মাণ — রবীন্দ্রনাথ এই দুর্দান্ত দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের প্রথাগত অনুমান – সাহিত্য ভাব, ভাষা ও গ্রন্থের কারবার, ঠাকুর গোড়াতেই তাকে চ্যালেঞ্জ করছেন।
এই সম্পর্ক স্রেফ বর্তমানের সম্পর্ক না, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, দূরের সঙ্গে নিকটের ‘অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন’। ‘অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন’ কথাটির অন্দর মহলে পরে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। সতর্ক করে রাখছি, আপাতত, যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে ‘কমিউনিকেশান’ কিংবা ‘সহৃদয় হৃদয় সংবেদ’ জাতীয় ধারণা গণ্য করেন নি। এই দিকে আমাদের শুরু থেকেই সতর্ক নজর রাখতে হবে।
একই ভাবসূত্রে তিনি ‘পরস্পর সজীব বন্ধন’ ধারণারও প্রস্তাব করছেন। দাবি করছেন, “যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন”।
কেন? সজীব বন্ধন এবং সজীব বন্ধন থেকে বিযুক্তি, অর্থাৎ সজীব এবং মৃত বন্ধনের মধ্যে ফারাক কী?
রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ‘জীবন্ত যোগ’ প্রতিষ্ঠা দরকার। ‘সাহিত্যের অনুপস্থিতি’তে কি পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন থাকে না? থাকে। নিদেন পক্ষে আমরা জীব হিশাবে এলেম কোথা থেকে এই জিজ্ঞাসা তো থাকেই। ফলে একটা ‘যোগ’ জারি থাকে বটে, কিন্তু সেটা “কেবল পূর্বাপর প্রচলিত জড়প্রথা বন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন”, সেটা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “তাহা যোগ নহে, তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্বপুরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনো রক্ষিত হইতে পারে না”। অর্থাৎ ‘যোগ’ আর ‘বন্ধন’ দুটো আলাদা ধারণা। সাহিত্য চর্চার অনুপস্থিতিতে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের ‘পূর্বাপর প্রচলিত জড়প্রথা বন্ধন’ থাকতে পারে, কিন্তু সেটা ‘যোগ’ নয়। যোগ সবসময়ই সজীব ও সক্রিয়, এটা স্রেফ আচার, অনুষ্ঠান, পূর্বপুরুষদের জন্য ধর্মীয় কৃত্যাদি নয়। দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের ‘বন্ধন’ আর সাহিত্যের সজীব ‘যোগ’ আলাদা ব্যাপার। ধর্মাচার ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে ফারাকের ইঙ্গিতটুকুও এখানে আমরা পাচ্ছি।
সজীব যোগ আর মৃত বন্ধনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ফারাক করছেন কেন? প্রাচীনকালের সঙ্গে আধুনিক কালের প্রথাগত বন্ধন আছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দাবি ‘একটা নাড়ির বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে’।
“আমাদের দেশের প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক কালের যদিও প্রথাগত বন্ধন আছে, কিন্তু এক জায়গায় কোথায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যে, সেকাল হইতে মানসিক প্রাণরস অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া একাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেমন করিয়া চিন্তা করিতেন, কার্য করিতেন, নব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতেন—সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি সমাজতন্ত্রের মর্মস্থলে তাঁহাদের জীবনশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি জাগ্রত থাকিয়া কী ভাবে সমস্তকে সর্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত—কীভাবে সমাজ প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিত, পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইত, আপনাকে কেমন করিয়া চতুর্দিকে বিস্তার করিত, নূতন অবস্থাকে কেমন করিয়া আপনার সহিত সন্মিলিত করিত—তাহা আমরা সম্যক্রূপে জানি না”।
রবীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।
খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। প্রাচীন কাল চিত্তবৃত্তির দিক থেকে মৃত, এটা রবীন্দ্রনাথের দাবি না। আধুনিক কাল মাত্রই ভাল ও সজীব – এটাও তাঁর দাবি না। অর্থাৎ তিনি আধুনিক কালকে প্রাচীন কালের বিপরীতে অগ্রসর বা সামনের কাতারের বলে দাবি করছেন না। আসলে প্রগতি ও পশ্চাতপদতার বাইনারিকে তিনি এখানে আক্রমণ করছেন। খানিকটা প্রছন্ন বটে, কিন্তু অস্পষ্ট নয়। একালে আমরা প্রাচীন কাল সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছি। প্রাচীন কালেরও একটা সজীব ‘জীবনশক্তি’ ছিল। সেই জীবনশক্তি দ্বারা প্রাচীন কালের মানুষ তাদের ‘চিৎশক্তি জাগ্রত’ রাখত। চিৎশক্তি জাগ্রত রেখে তারা “কী ভাবে সমস্তকে সর্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত—কীভাবে সমাজ প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিত, পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইত, আপনাকে কেমন করিয়া চতুর্দিকে বিস্তার করিত, নূতন অবস্থাকে কেমন করিয়া আপনার সহিত সন্মিলিত করিত—তাহা আমরা সম্যক্রূপে জানি না”। মুশকিল ঘটেছে এই চরম অজ্ঞতার কারণে। প্রাচীন কালের চিৎশক্তি সম্পর্কে সম্যক রূপে না জানার বিপদটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রধান। আমরা আমাদের প্রাচীনতা বিষয়ে যারপরনাই অজ্ঞ হয়ে পড়েছি। এটা মারাত্মক।
এখানে বোঝাবুঝির চাবিটা হচ্ছে ‘চিৎশক্তি’। ধারণা হিশাবে একালে চিৎশক্তি কথাটা আমাদের কিছুটা বিমূর্ত ও মিস্টিক মনে হতে পারে। তবে যারা আধুনিক ‘বিষয়বিদ্যা’ (Phenomenology), স্মৃতি ও কৃৎকলার দার্শনিক পর্যালোচনা অনুসরণ করছেন তাঁরা ঠাকুরকে অনায়াসে এখন বৈশ্বিক চিন্তার কেন্দ্রে রেখে নতুন করে বুঝবার সুবিধা আদায় করে নিতে পারবেন। আমার চেষ্টাটা সেই দিকেই, কারণ রবীন্দ্রনাথকে মৃত ভেবে গঙ্গাতীরে ফেলে যাওয়া আমার জন্য অসম্ভব।
অতএব প্রশ্ন, “মহাভারতের কাল এবং আমাদের বর্তমান কালের মাঝখানকার অপরিসীম বিচ্ছেদকে আমরা পূরণ করিব কী দিয়া?” এটা পরিষ্কার একটা প্রকট অভাব হাজির হয়েছে। এখানে পরিষ্কার করা দরকার ‘মহাভারতের কাল’ বলে রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মুশকিল নিয়ে চিন্তিত না। তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে, “যখন ভুবনেশ্বর ও কোনারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া যায় তখন মনে হয়, এই আশ্চর্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোনো আকস্মিক আন্দোলনে কতকগুলি প্রস্তরময় বুদ্বুদের মতো হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল? সেই শিল্পীদের সহিত আমাদের যোগ কোন্খানে? যাহারা এত অনুরাগ এত ধৈর্য এত নৈপুণ্যের সহিত এই-সকল অভ্রভেদী সৌন্দর্য সৃজন করিয়া তুলিয়াছিল, আর আমরা যাহারা অর্ধ-নিমীলিত উদাসীন চক্ষে সেই-সকল ভুবনমোহিনী কীর্তির এক-একটি প্রস্তরখণ্ড খসিতে দেখিতেছি অথচ কোনোটা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং পুনঃস্থাপন করিবার ক্ষমতাও রাখি না, আমাদের মাঝখানে এমন কী একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল যাহাতে পূর্বকালের কার্যকলাপ এখনকার কালের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়?”
প্রাচীন আমাদের কাছে শুধু অপরিচিত হয়ে গিয়েছে, তা নয়। একটা ভাঙা প্রাসাদের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ইঁটগুলো খসে যাচ্ছে, তার স্থাপত্য আর আমরা ধরতে পারি না। কিভাবে ইঁটগুলোকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল, গেঁথে গেঁথে একটা রূপ প্রদর্শিত হয়েছিল, সেই রূপের হদিস এখন যেমন আমাদের জানা নাই, তেমনি যে বিদ্যা বা সাহিত্য এই বিপুল ঘটনা ঘটিয়ে রেখে গিয়েছে সে সম্পর্কেও আমাদের আর কোনো জ্ঞান নাই।
এটা রবীন্দ্রনাথের স্রেফ আক্ষেপ না। তিনি যেটা দাবি করতে চাইছেন সেটা হলো এই ‘অভাব’ ইতিহাস দিয়েও পূরণ করা সম্ভব না। অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাস জানলে প্রাচীনের ‘চিৎশক্তি’ও আমরা জেনে যাব, কিংবা আমাদের আয়ত্বে আসবে এটা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। আর খেয়াল করতে হবে, মামলাটা ইতিহাসের না, সাহিত্যের। ‘সহিত’ হতে না পারার সমস্যা। সাহিত্যের ভূমিকা ইতিহাস চর্চা দিয়ে পালন সম্ভব না। এই জায়গায় রবীন্দ্রনাথ দারুন হুঁশিয়ার। সাহিত্য এবং ইতিহাসের ফারাক নিয়ে তিনি একদম নতুন কথা বলছেন, যা আমরা এর আগে এভাবে শুনিনি। এটা তিনি স্বীকার করেন যে জাতীয় জীবন-ইতিহাসের মাঝখানের কয়েকটি পাতা কে বা কারা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। যার ফলে তখনকার চিত্ত-বৈভবের সঙ্গে বর্তমানকে আর মেলানো যাচ্ছে না। কিন্তু সেই পাতা খুঁজে ছেঁড়া পুস্তকে জুড়ে দিলেও আমরা আর আমাদের প্রাচীন জীবনযাপনের সঙ্গে ‘যুক্ত’ হতে পারছি না। কারণ ‘যুক্ত’ থাকার ক্ষমতাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। যার ফলে, ‘তখনকার’ সঙ্গে আমাদের এখনকার ‘অর্থ’আমরা মেলাতে পারছি না।
‘সমাজ’ আপনা আপনি কোনো দেশে বা কালে আগাম হাজির থাকে, রবীন্দ্রনাথ এটা অনুমান করেন নি। তাঁর সাহিত্যের ধারণা একই সঙ্গে সমাজ ও সামাজিকতার ধারণা। কারণ সাহিত্য মানে ‘ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন’ মাত্র নয়। সাহিত্যের কাজ ‘মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক’ নির্মাণ। সাহিত্য ভাবের নির্মাণ নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্মাণ রবীন্দ্রনাথ এই দুর্দান্ত দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের প্রথাগত অনুমান – সাহিত্য হচ্ছে ভাব, ভাষা ও গ্রন্থের কারবার, ঠাকুর গোড়াতেই তাকে চ্যালেঞ্জ করছেন।
অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অর্থ মেলানোটাই এখানে ইস্যু। ইতিহাস নয়। আর সেই অর্থ মেলানোকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বা সজীব যোগ চর্চা বলে অভিহিত করছেন। এটা ইতিহাস চর্চার কাজ না, সাহিত্যের কাজ।
তাহলে ‘প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সহিত’ এই প্রকট বিচ্ছেদের চরিত্র আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে “তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমরা হারাইয়াছি”। আমরা মনে করি, “সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন-পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল ছিল এখন তাহা মলিন হইয়াছে, সেকালে যাহা দৃঢ় ছিল এখন তাহাই শিথিল হইয়াছে; অর্থাৎ আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া কিঞ্চিৎ ঝক্ঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলেই সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে”। না ফিরে আসে না। যা আসে সেটা আধুনিক হিন্দুত্ববাদ, প্রাচ্যবিদ্যা ও গোলকায়িত পুঁজির ‘পূঁজ’। আমরা একটা পঁচা সময়ের গর্তে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছি।
রবীন্দ্রনাথ বলছেন আমাদের কাছে ‘প্রাচীনদের বিধানগুলি’ শুধু আছে। কিন্তু যিনি বিধানদাতা তিনি নাই। শিল্পী নাই। কিন্তু প্রাচীনদের শিল্পনৈপুণ্যে দেশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কারণ বর্তমানেও তাদের কাজ আমাদের দৃশ্যগোচর, আমাদের আশপাশেই তারা বিরাজ করছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে হচ্ছে, “আমরা যেন কোন্ এক পরিত্যক্ত রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাস করিতেছি; সেই রাজধানীর ইষ্টক যেখানে খসিয়াছে আমরা সেখানে কেবল কর্দম এবং গোময়পঙ্ক লেপন করিয়াছি; পুরী নির্মাণ করিবার রহস্য আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত”। যে সজীব চিত্তবৃত্তি ও চর্চা একদা শিল্প বা সাহিত্যের রাজপ্রাসাদ বানিয়েছে, এখন আমরা সেই নির্মাণের রহস্য আর ধরতে পারি না। ভুলে গিয়েছি। সেই হিম্মত আমরা হারিয়ে ফেলেছি।
প্রাচীন কাল সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের এখনকার মনে প্রকট সেটা নিছকই নতুন আর পুরাতনের প্রভেদ। আমরা মনে করি, সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন-পুরাতনের প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, নতুন-পুরাতনের প্রভেদ বোধ এখন এমন ভাবে জারি আছে যাতে “প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিতে গেলেই নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়”।
রবীন্দ্রনাথ বলছেন আধুনিক হিন্দু মনে করে “প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন; তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন”। এই ওরিয়েন্টালিজম বা ঔপনিবেশিক গোলামিজাত ভাবনার আধিপত্যের ফলে আমাদের ধারণা ভারতে মানুষ বাস করত না। তারা টিকি পরে টোলে বসে শুধু শ্লোক পড়াতেন। কিন্তু প্রাচীনেরা যুদ্ধ করতেন, রাজ্যরক্ষা করতেন,শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করতেন, সমুদ্র পার হয়ে বাণিজ্য করিতেন। “তাঁহাদের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মতবৈচিত্র্য ছিল, এক কথায় জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না”। প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করতে গেলেই ‘নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তি’র যে ধারণা আধুনিকদের মধ্যে বহাল, রবীন্দ্রনাথ এই মর্মান্তিক পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা বলছেন।
এই ‘আত্যন্তিক ব্যবধানের অন্যতম প্রধান কারণ’ কী? সেটা হলো প্রাচীনের কাল ও জগত থেকে ‘এখন পর্যন্ত সাহিত্যের মনোময় প্রাণময় ধারা অবিচ্ছেদে বহিয়া আসে নাই’। যদি আদৌ নগণ্য কিছু এসে থাকে তবে সেই সব এসেছে ‘বিক্ষিপ্ত ভাবে’, পরস্পরের মধ্যে কোন কোন সজীব সম্পর্কের কোন প্রকার দিশা না দিয়ে। “সাহিত্যের যাহা-কিছু আছে তাহা মাঝে মাঝে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত”। এই আসার কোনো ফল নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেছেন:
“তখনকার কালের চিন্তাস্রোত ভাবস্রোত প্রাণস্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে, কেবল তাহার নদীখাতের মধ্যে মধ্যে জল বাঁধিয়া আছে; তাহা কোনো-একটি বহমান আদিম ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট নহে, তাহার কতখানি প্রাচীন জল, আর কতটা আধুনিক লোকাচারের বৃষ্টি-সঞ্চিত বলা কঠিন”। অর্থাৎ কোনো সজীব প্রবাহমান ধারার অস্তিত্ব নাই। প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের মেশামিশি হয় নি এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ মানছেন সেটা হয়তো ঘটছে, কিন্তু কিন্তু সেটা কতখানি ‘প্রাচীন জল’ আর কতখানি ‘আধুনিক লোকাচারের বৃষ্টি-সঞ্চিত’ তা নির্ণয় করা কঠিন”।
রবীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।
“এখন আমরা সাহিত্যের ধারা অবলম্বন করিয়া হিন্দুত্বের সেই বৃহৎ প্রবল নানাভিমুখ সচল তটগঠনশীল সজীব স্রোত বাহিয়া একাল হইতে সেকালের মধ্যে যাইতে পারি না। এখন আমরা সেই শুষ্কপথের মাঝে মাঝে নিজের অভিরুচি ও আবশ্যক-অনুসারে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাকে হিন্দুত্ব নামে অভিহিত করিতেছি। সেই বদ্ধ ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দুত্ব আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; তাহার কোনোটা বা আমার হিন্দুত্ব, কোনোটা বা তোমার হিন্দুত্ব; তাহা সেই কণ্ব-কণাদ রাঘব-কৌরব নন্দ-উপনন্দ এবং আমাদের সর্বসাধারণের তরঙ্গিত প্রবাহিত অখণ্ডবিপুল হিন্দুত্ব কি না সন্দেহ”।
এই বিকট বিচ্ছিন্নতার কারণ একটাই। সেটা হচ্ছে ‘সাহিত্যের অভাব’। সাহিত্যের অভাবেই ‘পূর্বাপরের সজীব যোগবন্ধন বিচ্ছিন্ন’ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের অভাব ঘটবার কারণ কি? একটা প্রধান কারণ, ‘জাতীয় যোগবন্ধনের অসদ্ভাব’। কিন্তু ‘জাতীয় যোগবন্ধনের অসদ্ভাব’ কী?
রবীন্দ্রনাথ সেই অসদ্ভাবেরও ব্যখ্যা দিয়েছেন। সেখান দেখা যায়, তিনি কোন একাটা এক প্রকার হোমিজিনিয়াস ভহারতের কল্পনা করেন নি। প্রাচীন যুগে সেটা সম্ভবও ছিল না। হিন্দুত্ববাদ যে ‘অখণ্ড ভারত’ কল্পনা করে সেটা আধুনিক কালের আধুনিক জাতিবাদী হিন্দুর কল্পনা।
“আমাদের দেশে কনোজ কোশল কাশী কাঞ্চী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন পথে চলিয়া গিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরকে সংক্ষিপ্ত করিতেও ছাড়ে নাই। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজতরঙ্গিণীর কাশ্মীর, নন্দবংশীয়দের মগধ, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ইহাদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কোনো ধারাবাহিক যোগ ছিল না। সেইজন্য সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের উপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন কালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক-এক জন সাহিত্যকার আপন কীর্তি স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস কেবল বিক্রমাদিত্যের, চাঁদবর্দি কেবল পৃথ্বীরাজের, চাণক্য কেবল চন্দ্রগুপ্তের। তাঁহারা তৎকালীন সমস্ত ভারতবর্ষের নহেন, এমন-কি তৎপ্রদেশেও তাঁহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না”।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।
‘সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের ওপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপন’ করতে পারে নি। বিচ্ছিন্ন ভাবে রাজা রাজড়া , রাজ্য বা স্থান বিশেষে সাহিত্য হয়েছে। কিন্তু তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের চর্চা হিশাবে তাদের কোনো ইতিহাস গড়ে ওঠে নি। ‘সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়’ নীড় না বাঁধলে সাহিত্যের বংশরক্ষা হয় না। তখন সাহিত্য তার নিজের বংশধারা রক্ষা করবার তাগিদে বহুদূর অবধি অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ দাবি করছেন, ‘সহিতত্ব’ই সাহিত্যের প্রধান উপাদান। ‘সহিতত্ব বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য নাই সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে।
রবীন্দ্রনাথ বলছেন আধুনিক হিন্দু মনে করে “প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন; তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন”। এই ওরিয়েন্টালিজম বা ঔপনিবেশিক গোলামিজাত ভাবনার আধিপত্যের ফলে আমাদের ধারণা ভারতে মানুষ বাস করত না। তারা টিকি পরে টোলে বসে শ্লোক পড়াতেন। কিন্তু প্রাচীনেরা যুদ্ধ করতেন, রাজ্যরক্ষা করতেন,শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করতেন, সমুদ্র পার হয়ে বাণিজ্য করিতেন। “তাঁহাদের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মতবৈচিত্র্য ছিল, এক কথায় জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না”। প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করতে গেলেই ‘নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তি’র যে ধারণা আধুনিকদের মধ্যে বহাল, রবীন্দ্রনাথ এই মর্মান্তিক পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা বলছেন।
সাহিত্য ও ধর্ম
“যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না”। দাবি রবীন্দ্রনাথের। দেখা যাচ্ছে ‘সাহিত্য’ বলতে রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছেদ অতিক্রম করবার দুঃসাধ্য কাজ গণ্য করেছেন। আর, আগে যা বলেছি: সাহিত্য ও সমাজ পরিগঠন প্রক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথ একই কাতারে বা সমান্তরালে বিচার করছেন। সাহিত্যই সমাজ গঠন করে, সাহিত্য ভেদে সমাজেরো রূপভেদ বা প্রকারভেদ হয়।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিসে লোকে এক হয়? কিম্বা কিভাবে ‘অনেক’ নিজেদের ‘এক’ ভাবতে শেখে, ‘এক’-এর উপ্লব্ধি ঘটে? এর উত্তর কেন দরকার? কারণ “কিসে লোকে এক হয় সেটাই সাহিত্যের চরিত্র নির্ণয় করে। রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিচ্ছেন, “আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয়? ধর্মে। সেইজন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্মসাহিত্যই আছে। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি। রাজপুতগণকে বীরগৌরবে এক করিত, এইজন্য বীরগৌরব তাহাদের কবিদের গানের বিষয় ছিল”।
তবে বাংলায় সাধারণ সাহিত্যের যে হাওয়া দেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, সেটা একটা সন্ধিক্ষণের গল্প। হাতে লেখা পুঁথিপত্তর আগেই এসে গিয়েছে, সবে ছাপাখানা আসছে। সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, ধর্মপ্রচার থেকেই সাহিত্যআরম্ভ। এটা আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,
“প্রথমে যাঁহারা ইংরাজি শিখিতেন তাঁহারা প্রধানত আমাদের বণিক ইংরাজ-রাজের নিকট উন্নতিলাভের প্রত্যাশাতেই এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন; তাঁহাদের অর্থকরী বিদ্যা সাধারণের কোনো কাজে লাগিত না। তখন সর্বসাধারণকে এক শিক্ষায় গঠিত করিবার সংকল্প কাহারো মাথায় উঠে নাই; তখন কৃতী-পুরুষগণ যে যাহার আপন আপন পন্থা দেখিত”।
তাহলে বঙ্গে ‘সাহিত্য’ চর্চা শুরু হলো কিভাবে? সেটা শুরু করেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারিগণ। ঠিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোনই ভুল করেন নি। কারন সাহিত্য স্বাধীন পরিসর হিশাবে গড়ে ওঠার শর্ত হচ্ছে যার দ্বারা মানুষ একত্রিত হয়, সেই ‘সহিতত্ব’ চর্চা। ঔপনিবেশিক আমলে সাহিত্য চর্চার তাগিদ এসেছে ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে। আশা করি এই কুতর্ক আমরা করবো না যে এর আগে সাহিত্য চর্চা হয় নি। হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সেটা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে হয়েছে। অতএব রবীন্দ্রনাথ তাকে পুরাপুরি সাহিত্য চর্চা হিশাবে স্বীকার করেন নি। বলছেন,
“বাংলার সর্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব খৃস্টীয় মিশনরিগণ সর্বপ্রথমে অনুভব করেন, এইজন্য তাঁহারা সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এ কার্য বিদেশীয়ের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর নহে। নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন”।
দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ আসলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের কথা বলছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো, সাধারণ ভাবে ‘সাহিত্য বা সহিতত্বের যে ধারণা তিনি দিতে চাইছেন, তার সঙ্গে সম্পর্ক গদ্যের, কাব্য বা কবিতার নয়। তাই তিনি দাবি করেছেন বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছে রামমোহনের গদ্য রচনায় মনোনিবেশের মধ্য দিয়ে। আধুনিক গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব আর ‘সহিতত্ব’ চর্চার তাগিদ তার কাছে সমান্তরাল ব্যাপার বলে পরিগণিত হয়েছিল।
তাহলে সাহিত্যের আবির্ভাব ও চর্চার দিক থেকে পদ্য ও গদ্যের ভেদ-বিচারের রাবিন্দ্রীক পদ্ধতিও আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। “সর্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব” থেকে ‘সাহিত্যের উদ্ভব”। সেই দায় কি কাব্যের নাই? এটা একটা প্রশ্ন হয়ে উঠলো তাহলে। মনে রাখতে হবে কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের মতো একজন কবি লিখছেন। সাহিত্য যদি ‘সহিতত্ব’ চর্চা হয়ে হয়ে থাকে তাহলে সাহিত্যের আবির্ভাব একমাত্র গদ্যের আবির্ভাবের পরেই ঘটতে পারে। তাহলে কাব্য ও সাহিত্যকে এই ভেদরেখার ওপর দাঁড় করিয়ে আমরা বিস্তর কথা বলতে পারি। সেটা এই মূহূর্তে অপ্রয়োজনীয়। সেটা আমরা এই নিবন্ধের বাইরে করতে পারব। এখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারছি কিনা সেটা আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার। ‘সর্বসাধারণকে এক শিক্ষায় গঠিত করিবার সংকল্প’ যতক্ষণ সমাজে তৈরি না হচ্ছে ততক্ষন আমরা গদ্য সাহিত্য উদ্ভবের কথা ভাবতে পারি না। আর গদ্য সাহিত্য উদ্ভব ও চর্চাই হচ্ছে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র, সকলের ‘সহিত’ যুক্ত হবার বাসনা ও চর্চা।
কাব্য কী তাহলে? কাব্যের সংকল্প কী? কবি কি তাহলে‘সামাজিক’ নন?
প্রথমত রবীন্দ্রনাথ সহিতত্বের জায়গা থেকে যে ভেদবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন সেটা রবীন্দ্রনাথকে বোঝার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর এই গদ্য-কাব্যের ভেদ জ্ঞান একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সংক্রান্ত চিন্তার সীমাবদ্ধতাও বটে। যদি ‘ধর্ম’ আমাদের এক করে, আমাদের সকলের ‘সহিত’ সজীব যোগ ঘটাবার তাগিদ হয়, তাহলে বাংলা ‘সহিতত্ত্ব’ বা সাহিত্যের দুর্দান্ত যুগ হচ্ছে সুলতানী আমলে চৈতন্যের ধর্ম সাধনা। গৌরাঙ্গের রাধা ভাবে উপাসনার স্রোতে ভেসে বড় বাংলার সাহিত্য চর্চা ‘ডুবু ডুবু’ হয়েছিল। চৈতন্যকে অবতার বলে সমাজ স্বীকার করে নিয়েছিল। যিনি জীবের মুক্তি ঘটান বা জীবকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন। বিপরীতে শিক্ষিত বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ ঋষি বটে, কিন্তু চৈতন্য বড় বাংলায় যে তুফান ও ঝাঁকুনি দিয়ে গিয়েছে আধুনিক সাহিত্যে তার তুলনা নাই বললেই চলেও। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার উদাহরণ নন। “সর্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব” চৈতন্য যেভাবে মিটিয়েছেন তার তুলনা নাই। গোটা সুলতানি আমল ও চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাস বিচার ছাড়া তাই রাবিন্দ্রীক অর্থেও ‘সাহিত্য’ ধারণা পরিচ্ছন্ন করা কঠিন। রীতিমতো অসম্ভব। বড় বাংলার ভক্তি আন্দোলন বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ‘সাহিত্য’ ধারণাটি তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন সেটা আর দাঁড়ায় না।
কিন্তু ফারাকটা হচ্ছে মৌখিক সাহিত্য আর ছাপাখানার সাহিত্যের পার্থক্য। সেই ফারাক রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট ছিল না। সাহিত্য ভাবের নির্মাণ নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্মাণ — রবীন্দ্রনাথ এই দুর্দান্ত দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন বটে, কিন্তু ছাপাখানা ও গদ্য যে ভাবে সেই সম্পর্ক ও সমাজ বানায় মুখস্থ বা মৌখিক (Oral) সাহিত্য সেটা করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে। এটা বোঝার জন্য আমামদের আলাদা ভাবে শ্রুতি ও কন্ঠ নির্ভর মৌখিক সাহিত্য’ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে। গুটেনবার্গের ছাপাখানা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরির স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে বিশাল বদল ঘটায়। ফলে কন্ঠ ও শ্রুতির জগতের সঙ্গে ছাপাখানার জগতের পার্থক্য বিচার ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব আমরা পুরাপুরি বুঝব না। এর সীমাবদ্ধতাও ধরতে পারব না। টেকনলজির বিচার ছাড়া আমরা রবীন্দ্রনাথার ‘সহিতত্ব’ বা সাহিত্যতত্ত্বের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতার বিচার ঠিক ভাবে করতে পারব না। এই বিচার ছাড়া চৈতন্য ও রামমোহনের ফারাক বুঝব না। তাদের সংস্কারের চরিত্রও বোঝা যাবে না। সোজা কথায় ছাপাখানার যুগের সাহিত্য চর্চার সঙ্গে ছাপাখানার আগের সাহিত্য চর্চার পার্থক্য ধরতে পারব না। উভয়েই ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষকে একত্র করেছিল। চৈতন্যের প্রণোদনায় গড়ে উঠেছে নতুন ধর্মান্দোলন। শুধু বৈষ্ণব ধর্ম নয়, নদীয়ার অন্যান্য ভাবান্দোলনের প্রেরণাও চৈতন্য থেকেই। অন্যদিকে রামমোহনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে আরেকটি ধর্ম আন্দোলন, ব্রাহ্ম সমাজ। টেকনলজি এইপার্থক্য নির্ণয়ে কিভাবে ভূমিকা রেখেছে সেটা সাহিত্য নিয়ে গবেষণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।
শিক্ষিত বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ ঋষি বটে, কিন্তু চৈতন্য বড় বাংলায় যে তুফান ও ঝাঁকুনি দিয়ে গিয়েছে আধুনিক সাহিত্যে তার তুলনা নাই বললেই চলেও। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার উদাহরণ নন। “সর্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব” চৈতন্য যেভাবে মিটিয়েছেন তার তুলনা নাই। গোটা সুলতানি আমল ও চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাস বিচার ছাড়া তাই রাবিন্দ্রীক অর্থেও ‘সাহিত্য’ ধারণা পরিচ্ছন্ন করা কঠিন। রীতিমতো অসম্ভব। বড় বাংলার ভক্তি আন্দোলন বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ‘সাহিত্য’ ধারণাটি তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন সেটা আর দাঁড়ায় না।
এখানে ‘পুঁথির’ প্রসঙ্গ বাদ রইলো। কিন্তু অক্ষর ও লিখন পদ্ধতি একই সঙ্গে নতুন কলাবিদ্যা, টেকনিক বা টেকনলজি। ‘পুথি’ একই ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্মাণের মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে বুঝতে হলে পুঁথি নিয়েও তাহলে আমাদের বিস্তর কথা বলার থাকে। সেটা বলব নিশ্চয়ই অন্যত্র। । সারকথা হচ্ছে টেকনিক বা টেকনলজির প্রসঙ্গ উহ্য রেখে সহিত বা সাহিত্যের আলোচনা অসম্ভব। সাহিত্য বিচারের নামে এ যাপতকাল যা হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার ছিলেন না। অর্থাৎ সাহিত্য চর্চায় টেকনলজির ভূমিকা প্রসঙ্গ হিশাবে তোলা দূরে থাকুক, রবীন্দ্রনাথ সেটা অনুমান ও আন্দাজও করতে পারেন নি। অথচ সাহিত্যের ইতিহাস একই সঙ্গে টেকনলজির ইতিহাসও বটে।
অন্যদিকে ‘আধুনিক’ সাহিত্যের আলোকে আধুনিক বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ও সাহিত্যের তর্ক অনেক গভীর ও জটিল বিষয়। এর সঙ্গে ঔপনিবেশিক আমলে ছাপাখানা বা গুটেনবার্গ টেকনলজির আবির্ভাব, পূর্ব বাংলার কৃষক ও কৃষি ব্যস্থার শোষণের ওপর গড়ে ওঠা জমিদারি-মহাজন ব্যবস্থা, কলকাতা শহরের বিকাশ ও জৌলুসের ইতিহাস এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিকতার গর্ভে পরিস্ফূট হতে থাকা বাজার ব্যবস্থার বিচার ছাড়া ‘আধুনিক সাহিত্য’ আমরা বুঝব না। প্রাক-আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের মস্তো বড় ফারাক আছে। আধুনিক সাহিত্যের বিচার যুগপৎ টেকনলজি এবং বাজার ব্যবস্থার বিচার ছাড়া সম্ভব না। রবীন্দ্রনাথ ‘সহিত’ থেকে সাহিত্য’ বলতে যে ধারণার পুননির্মাণ করতে চাইছেন সেই আলোকেই আমাদের দেখাতে হবে টেকনলজিও ‘সহিত’ বা সাহিত্য ব্যাপার ঘটাতে পারে। অন্যদিকে ‘বাজার’ অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের পণ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যে সহিত বা সজীব সংযোগ স্থাপিত হয়, তাকেও সাহিত্য- ধারণা পর্যালোচনার বাইরে রাখা যাচ্ছে না।
এই প্রসঙ্গে এখানে বিস্তৃত আলোচনার অবসর হবেনা। তবে ‘প্রিন্ট ক্যাপিটালিজম’ সম্পর্কে একটু নোক্তা দিয়ে রাখি যা আধুনিক জাতিবাদ পর্যালোচনায় আমাদের কাজে আসে। আমরা যখন নিজেদের কোন বিশেষ ‘জাতি’ বা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠির অন্তর্গত ‘কল্পনা’ করি, সেই কল্পনা বাস্তবে সম্ভব হয় যদি ছাপাখানার কারনে সবার বোধগম্য একটি ‘সাধারণ ভাষা’ গড়ে ওঠে। সেই ভাষা গড়ে উঠতে পারে যদি তার জন্য একটা পুঁজিতান্ত্রিক বাজার হাজির থাকে। এই শর্তগুলো থাকলে ব্যবসায়ীরা সংস্কৃত, ল্যাটিন কিংবা প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষায় বই না ছাপিয়ে লৌকিক বা সাধারণের ভাষায় বই ছাপতে শুরু করে। এর ফলে স্থানীয় ডায়ালেক্ট বা ভাষার জায়গায় সবার বোধগম্য ছাপাখানা ও পুঁজি মিলে একটি ‘প্রমিত’ ভাষা গড়ে তোলে। বই ব্যবসায়ে যারা পুঁজি বিনিয়োগ করে তারা সবার বোধগম্য ভাষায় বই প্রকাশের তাগিদ বোধ করে। তখন মানুষ বিচ্ছিন ও বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা বা ডায়ালেকটের জায়গায় ছাপাখানা ও বাজারের বদৌলতে সর্ব সাধারণের বোধগম্য ভাষা রপ্ত করতে সক্ষম হয়, সবার বোধগম্যতার আলোকে ভাষাও ‘প্রমিত’ হয়ে ওঠে। এর ফল হয় সবার মধ্যে একটা সাধারণ কথোপকথন বা ডিসকোর্সের ক্ষেত্র তৈরি হওয়া।এই যুক্তিতে বেনেডিক্ট এন্ডারসন দাবি করেছেন ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠার পেছনে ‘প্রিন্ট ক্যাপিটালিজম’-এর বিশেষ ভূমিকা আছে। সর্বসাধারণের ভাষা গড়ে উঠলে সেই ভাষায় নিজেদের একই ‘জাতি’ ভাববার শর্তও গড়ে ওঠে। (দেখুন, Anderson, Benedict (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism (Revised and extended. ed.). London: Verso. pp. 224. ISBN 978-0-86091-546-1. Retrieved 5 September 2010) । রবীন্দ্রনাথ যখন ‘জাতীয় সাহিত্য’ নিয়ে এই নিবন্ধটি লিখছেন তখন তাঁর চিন্তাও প্রিন্ট ক্যাপিটালিজমের বাইরে ঘটছে না। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বংশসূত্রে জমিদার বটেন, কিন্তু সাহিত্য সূত্রে প্রিন্ট ক্যাপিটালিজমের প্রডাক্ট। তিনি ও রামমোহন আধুনিক ছাপাখানা থেকেই তৈরি হয়েছেন।
‘প্রিন্ট ক্যাপিটালিজম’ সম্পর্কে একটু নোক্তা দিয়ে রাখি যা আধুনিক জাতিবাদ পর্যালোচনায় আমাদের কাজে আসে। আমরা যখন নিজেদের কোন বিশেষ ‘জাতি’ বা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠির অন্তর্গত ‘কল্পনা’ করি, সেই কল্পনা বাস্তবে সম্ভব হয় যদি ছাপাখানার কারনে সবার বোধগম্য একটি ‘সাধারণ ভাষা’ গড়ে ওঠে। সেই ভাষা গড়ে উঠতে পারে যদি তার জন্য একটা পুঁজিতান্ত্রিক বাজার হাজির থাকে। এই শর্তগুলো থাকলে ব্যবসায়ীরা সংস্কৃত, ল্যাটিন কিম্বা প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষায় বই না ছাপিয়ে লৌকিক বা সাধারণের ভাষায় বই ছাপতে শুরু করে। এর ফলে স্থানীয় ডায়ালেক্ট বা ভাষার জায়গায় সবার বোধগম্য একটি ‘প্রমিত’ ভাষা ছাপাখানা ও পুঁজি মিলে গড়ে তোলে। বই ব্যবসায়ে যারা পুঁজি বিনিয়োগ করে তারা সবার বোধগম্য ভাষায় বই প্রকাশের তাগিদ বোধ করে। তখন মানুষ বিচ্ছিন ও বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা বা ডায়ালেকটের জায়গায় ছাপাখানা ও বাজারের বদৌলতে সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা রপ্ত করতে সক্ষম হয়, সবার বোধগম্যতার আলোকে ভাষাও ‘প্রমিত’ হয়ে ওঠে…
সাহিত্য ও রামমোহন
“এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
‘সাহিত্য’ ধারণার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ যাঁকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি রামমোহন। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার পূর্ণ পক্ষপাত আছে। কিন্তু সেটা আধুনিক প্রিন্ট টেকলজির যুগের সাহিত্য ধারণা। রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্য’ ধারণার তাৎপর্য আধুনিক কালে সীমিত নয়, কিন্তু তিনি নিজে সাহিত্যের উদাহরণ যাকে সামনে এনেছেন তিনি একান্তই প্রিন্ট টেকনলজির তৈরি। কিন্তু শুধু তাই নয়। তিনি ছাপা অক্ষর পাঠের অনভ্যাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মুখস্থ ও মুদ্রিত ভাষার ফারাক বুঝতে পারলেও টেকনলজির সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ রামমোহন কিম্বা রবীন্দ্রনাথ কারো চিন্তাকেই আলোড়িত করে নি। তারপরও সত্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বিশাল সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছেন । সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে নয়। কেন করেছেন সেটা তাহলে বোঝা দরকার।
১. রামমোহনের আগে সাহিত্য কেবল পদ্যে বদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন ‘সাহিত্য’ — অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে এসেছেন। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক চর্চার জায়গা তৈরির দরকার তিনি বোধ করেছিলেন। তার জন্য তাঁর দরকার ছিল গদ্য। রামমোহনের হাতেই এমন এক গদ্য হাজির হোল যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘সর্বসাধারণের ভাষা’ তৈয়ারি।
২. রামমোহন রায়ের ‘উদ্দেশ্য সাধন’ পদ্যে হোত না, কবিতা দ্বারা সেটা সম্ভব হোতো না। কারন দরকার ছিল ‘যুক্তির ভাষা’। এটাও রবীন্দ্রনাথ দারুণ বলেছেন, কারণ আধুনিক যুক্তির ভাষা তৈরির শর্তও ছাপাখানা , অর্থাৎ ছাপা বই। যা আমরা সরল রৈখিক ভাবে একদিক থেকে পড়ি এবং বাক্য শেষ না করা অবধি ‘অন্বয়’ করি না। বা করতে পারি না। এটাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, সাহিত্য এবং সাহিত্যের বিচার যদি আমরা করতে চাই তাহলে বই কিভাবে আমাদের চিন্তার চরিত্র বদলে দিয়েছে সেই দিকে নজর দিতে হবে। দিতে আমরা বাধ্য।
রবীন্দ্রনাথ বলছেন,
“কেবল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা নহে; যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ববিষয়ের এবং সর্বসাধারণের ভাষা তাঁহার আবশ্যক ছিল। পূর্বে কেবল ভাবুকসভার জন্য পদ্য ছিল, এখন জনসভার জন্য গদ্য অবতীর্ণ হইল। এই গদ্যপদ্যর সহযোগ-ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। খাস-দরবার এবং আম-দরবার ব্যতীত সাহিত্যের রাজ-দরবার সরস্বতী মহারানীর সমস্ত প্রজাসাধারণের উপযোগী হয় না। রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম-দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন”।
রবীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’
এখানে আমরা নতুন কথা পাচ্ছি।“গদ্যপদ্যর সহযোগ-ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না”। গদ্য ‘সহিতত্ব’ বা সাহিত্য চর্চা আবির্ভাবের শর্ত যেমন, তেমনি গদ-পদ্যের সহযোগ ছাড়া সাহিত্য সম্পূর্ণ হবে না। গদ্যকে আমলে নিতে হবে।
কিন্তু সর্ব সাধারণকে রামমোহন গদ্য লিখতে এবং পড়াতে গিয়ে যে মুশকিলে পড়েছিলেন সেই দিকটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারন, “আমরা আশৈশবকাল গদ্য বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু গদ্য যে কী দুরূহ ব্যাপার তাহা আমাদের প্রথম গদ্যকারদের রচনা দেখিলেই বুঝা যায়।
“পদ্যে প্রত্যেক ছত্রের প্রান্তে একটি করিয়া বিশ্রামের স্থান আছে, প্রত্যেক দুই ছত্র বা চারি ছত্রের পর একটা করিয়া নিয়মিত ভাবের ছেদ পাওয়া যায়; কিন্তু গদ্যে একটা পদের সহিত আর-একটা পদকে বাঁধিয়া দিতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখিবার জো নাই; পদের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। ছন্দের একটা অনিবার্য প্রবাহ আছে; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভারসামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়, সেই পদব্রজ-বিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টল্মলে হইয়া থাকে। গদ্যের সুপ্রাণালীবদ্ধ নিয়মটি আজকাল আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গেছে, কিন্তু অনধিককাল পূর্বে এরূপ ছিল না।”
রবীন্দ্রনাথ,’বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।

রামমোহন যখন গদ্য রচনা করছেন তখন গদ্য করা কঠিন ছিল তা নয়। শ্রুতি-নির্ভরিতা থেকে চক্ষু নির্ভরতার অভ্যাস তখন সবে গড়ে উইঠছে। বই পড়া মানে চোখ দিয়ে শনা। পড়ছি চোখ দিয়ে, কিন্তু মনে মনে শুঞ্ছি কান দিয়ে। এটা চোখ ও কানের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলছেন,
“তখন লোকে অনভ্যাসবশত গদ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি, কবিতায় হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ ও ছন্দ এবং মিলের ঝংকার-বশত কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে। সেইজন্য রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন গদ্য বুঝিবার কী প্রণালী তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন”।
রবীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।
গদ্য বোঝার রামমোহনীয় প্রণালী রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছিলেন। আমরাও এখানে টুকে দিতে চাই। নতুন টেকনলজি কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যবহারের অভ্যাস বদলায় এবং তাকে আয়ত্ব করার মধ্য দিয়ে আমরাও বদলে যাই – এই দিকটা আমরা সাধারণত ধরতে পারি না। বোঝা দূরের কথা।
‘এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।’
অতঃপর কী করিলে গদ্যে বোধ জন্মে রামমোহন তার উপদেশও দিয়েছেন।
‘বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যেই স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন’ ইত্যাদি।
এরপর রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষন পেশ করেছেন।
রামমোহন যখন বাংলা গদ্য তৈরী করছেন, তখন কিছুই প্রস্তুত ছিল না। গদ্য শুধু নয়, এমনকি গদ্যেবোধও ছিল না। তাই তাকে কিভাবে প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয়, অনুসরণ করে গদ্য পড়তে হয় সেটাও শেখাতে হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের এই অবদানকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু বড় করে দেখান নি। রামমোহনের মহত্ত্ব অন্যত্র।
‘সেই আদিমকালে’ রামমোহন পাঠকদের জন্য বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ ‘উপহার’ দিচ্ছেন। কিন্তু রামমোহন শাস্ত্র চর্চায় সর্বসাধারণকে অযোগ্য জ্ঞান করেন নি। অর্থাৎ চুটকি কিছু করেন নি। হাতে আমলকি হরিতিকি ধরিয়ে দেন নি। বরং রামমোহনই মূলত যাকে আমরা ‘সর্বসাধারণ’ বলি তাদের সামাজিক-ঐতিহাসিক আবির্ভাবের শর্ত তৈরি করেছেন। কিভাবে?
রামমোহনের আগে সাহিত্য কেবল পদ্যে বদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন ‘সাহিত্য’ করতে এসেছেন। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক চর্চার জায়গা তৈরির দরকার তিনি বোধ করেছিলেন। তার জন্য তাঁর দরকার ছিল গদ্য। রামমোহনের হাতেই এমন এক গদ্য হাজির হোল যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘সর্বসাধারণের ভাষা’ তৈয়ারি।
রামমোহন রায়ের ‘উদ্দেশ্য সাধন’ পদ্যে হোত না, কবিতা দ্বারা সেটা সম্ভব হোতো না। কারন দরকার ছিল ‘যুক্তির ভাষা’। এটাও রবীন্দ্রনাথ দারুণ বলেছেন, কারণ আধুনিক যুক্তির ভাষা তৈরির শর্তও ছাপাখানা , অর্থাৎ ছাপা বই। যা আমরা সরল রৈখিক ভাবে একদিক থেকে পড়ি এবং বাক্য শেষ না করা অবধি ‘অন্বয়’ করি না। বা করতে পারি না। এটাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, সাহিত্য এবং সাহিত্যের বিচার যদি আমরা করতে চাই তাহলে বই কিভাবে আমাদের চিন্তার চরিত্র বদলে দিয়েছে সেই দিকে নজর দিতে হবে। দিতে আমরা বাধ্য।
রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন, সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথিসৎকার করিব; আমার অরণ্যে ইহার উপযুক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিয়া দিব”। ছাপাখানা এবং রামমোহন একই সঙ্গে ‘সর্বসধারণ পরিগঠিত হবার শর্তও বটে। রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য সমাজতাত্ত্বিক দূরদৃষ্টি ছিল।
রামমোহন চাইলে পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করতে পারতেন। তাঁর দরকার ছিলনা সাধারণ মানুষকে বাংলা ভাষায় শাস্ত্র ব্যখ্যা করা। কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষ নিয়েই ভেবেছেন। জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জন বিদ্বান রামমোহন জন্য খুবই সহজ ছিল। তিনি সেপথে গেলেন না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন”। এখানেই রামমোহন আধুনিক গদ্য সাহিত্যের মহারাজ। যে দরবার সর্বসাধারণ নিয়ে পরিগঠিত। “এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল।
এরপরে বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা সহজ। “বড়ো একটি উন্নত ভাবের উপর বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে”। বড় একটা উন্নত ভাব হচ্ছে সাহিত্যের দরবারে রাজা ‘সর্বসাধারণ’। রামমোহন এই দুরূহ কাজ শুরু করেছেন এমন সময় যখন এ কাজের জন্য খ্যাতি কিম্বা সমাদর ছিল না। বাংলা ভাষা চর্চা থেকে খ্যাতি আসার সম্ভাবনাও অসম্ভব ছিল। বাংলা ভাষার নিজের এমন কোনো যোগ্যতাও ছিল না, বাংলায় ভাব প্রকাশও দুরূহ ছিল। ভাব প্রকাশ করে তারপর তা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার ছিল আরও দুরূহ। বাংলাভাষা সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও দুঃসাধ্য ছিল। বাংলা ভাষা ছিল নিরাশ্রয়। রাজা-মহারাজা কিংবা শিক্ষিত শ্রেণী্র কাছে বাংলার কোনো মূল্য ছিল না। যারা ইংরাজি চর্চা করতো তারা বাংলাকে উপেক্ষা করতো। যারা বাংলা জানতেন তারা রামমোহনের কাজের মর্যাদা কিংবা তাৎপর্য কোনটিই বুঝতেন না। ইংরাজি-পণ্ডিতেরা মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাদের পাণ্ডিত্য নিজের মধ্যেই বদ্ধ থাকত, দেশের লোককে সেই পাণ্ডিত্য দান করতে পারত না। এইজন্য সেই পাণ্ডিত্য কেবল বিরোধ এবং অশান্তির সৃষ্টি করত। প্রথম-প্রথম যারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, তারা “চতুষ্পার্শ্ববর্তীদের প্রতি অনাবশ্যক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন এবং স্থির করিয়াছিলেন মদ্য, মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ”।
যথার্থ সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি হচ্ছে সাধারণ মানুষ, ‘সুবৃহৎ জনমণ্ডলী’। আর, সম্মুখে ‘সুদূর ভবিষ্যৎ’ এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, “প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী”। সেই লক্ষ্য থাকে বলেই “সাহিত্য মানবের সহিত মানবকে যুগের সহিত যুগান্তরকে প্রাণবন্ধনে বাঁধিয়া দেয়”। যে সম্পর্ক ও বন্ধন চর্চার ক্ষেত্র রামমোহন করে গিয়েছেন তাতে সাহিত্যের ‘উন্নতি ও ব্যাপ্তি-সহকারে’ কেবল ‘সমস্ত বাঙালির হৃদয় অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে তাহা নহে এক সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকেও বঙ্গসাহিত্য আপন জ্ঞানান্নবিতরণের অতিথিশালায়, আপন ভাবামৃতের অবারিত সদাব্রতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে”। সাহিত্য শুধু বাংলাভাষীদের প্রাণবন্ধন মজবুত করে বাঁধবে তা নয় অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রাণবন্ধনের শর্তও তৈরি করবে।
রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন সাহিত্যের কাজ একা করা কঠিন। সাহিত্য স্বভাবগুণে সামষ্টিক চর্চা। এ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা একক ভাবেই কাজ করিয়াছেন। কারণ, “সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান সহিতত্ব”।
“যে সমাজে জনসাধারণের মনের মধ্যে অনেকগুলি ভাব সঞ্চিত এবং সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, যেখানে পরস্পরের মানসিক সংস্পর্শ নানা আকারে পরস্পর অনুভব করিতে পারিতেছে, সেখানে সেই মনের সংঘাতে ভাব এবং ভাবের সংঘাতে সাহিত্য স্বতই জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই মানবমনের সজীব সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র দৃঢ় সংকল্পের আঘাতে সঙ্গিহীন মনকে জনশূন্য কঠিন কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা, একলা বসিয়া চিন্তা করা, উদাসীনদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার একান্ত চেষ্টা করা, সুদীর্ঘকাল একমাত্র নিজের অনুরাগের উত্তাপে নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা এবং চিরজীবনের প্রাণপণ উদ্যমের সফলতা সম্বন্ধে চিরকাল সন্দিহান হইয়া থাকা—এমন নিরানন্দের অবস্থা আর কী আছে?”
রামমোহন চাইলে পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করতে পারতেন। তাঁর দরকার ছিলনা সাধারণ মানুষকে বাংলা ভাষায় শাস্ত্র ব্যখ্যা কোঁড়া। কিন্তু তিনি সেই কাজটিই করেছেন। জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জন বিদ্বান রামমোহন জন্য খুবই সহজ ছিল। তিনি সেপথে গেলেন না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন”। এখানেই রামমহন আধুনিক গদ্য সাহিত্যের মহারাজে। যে দরবার সর্বসাধারণ নিয়ে পরিগঠিত। “এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল!
বাংলা বনাম ইংরেজী শিক্ষা
ইংরেজি এবং ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথার মত হচ্ছে ইংরেজি বাঙালি যখন নতুন নতুন শিখেছে তখন নানা অসঙ্গতি তৈরি হয়েছে। প্রথম-প্রথম নূতন শিক্ষায় সম্পূর্ণ ভালো ফল না পেলে আমরা অতিমাত্রায় ভীত হয়ে পড়ি। তখন সে শিক্ষাকে রোধ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘সদ্বিবেচনার’ কাজ না। কারণ যা “স্বাধীনভাবে ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহা আপনাকে আপনি সংশোধন করিয়া লয়, যাহা বদ্ধ থাকে তাহাই দূষিত হইয়া উঠে”। অন্যদেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নে তার নীতি ছিল স্বাধীন ভাবে ব্যাপ্ত হতে দেওয়,। ইংরেজি সাহিত্য ও শিক্ষা যখন যখন ‘সংকীর্ণ সীমায় রুদ্ধ ছিল’ “তখন সেই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ইংরাজি সভ্যতার ত্যাজ্য অংশ সঞ্চিত” হয়েছে। ইংরেজি সভ্যতার সেই বর্জ্য সব কিছুই কলুষিত করে তুলছিল।
এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে। সেটা হলো, “ইংরাজি শিক্ষা যে ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নহে। বাংলা সাহিত্যই তাহার প্রধান সহায় হইয়াছে” । অর্থাৎ ইংরেজি শিখার বিস্তৃতির কারণ বাংলা সাহিত্য। কেন? কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি এক সময়ে ইংরেজের দালালি করেছে। তারাই ইংরাজ রাজ্য স্থাপনের সহায়তা করেছে। তখন ভারতবর্ষের মধ্যে “বঙ্গসাহিত্য ইংরাজি ভাবরাজ্য এবং জ্ঞানরাজ্য -বিস্তারের প্রধান সহকারী” হয়েছে। বাংলাসাহিত্যযোগে ইংরাজিভাব ঘরে বাহিরে সর্বত্র সুগম হয়েছে। এই সুগমতার ইতিবাচক ফল হচ্ছে ইংরাজি সভ্যতার অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য সচেতনতা। তার মানে বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ‘ইংরেজি ভাব ঘরে ঘরে’ বিস্তৃত হবার কারণেই তার ইতিবাচক ফল হিশাবে আমরা ‘ইংরেজি সভ্যতার দাসত্ব’ থেকে মুক্তি পাবার সংকল্প করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলা সাহিত্যের একটি নীট ফল হচ্ছে উপনিবেশ বিরোধী চেতনা শাণিত করা। ইংরাজি শিক্ষা সমাজে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়েছে বলেই বাঙালি ‘স্বাধীনভাবে’ তার ভালোমন্দ মুখ্যগৌণ বিচারের অধিকারী হয়েছে। ইংরেজি সভ্যতা পর্যালোচনার হিম্মত বেড়েছে। ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা বাঙালির মন সজীব হয়েছে এবং ‘বাঙালির মনকে আশ্রয় করিয়া সেই শিক্ষাও সজীব হয়ে উঠেছে। “আমাদের দেশীয় ভাষায় দেশীয় সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে…এখন যাঁহারা ইংরাজিতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারা বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাকে গৌরব জ্ঞান করেন; এখন অতিবড়ো বিলাতি-বিদ্যাভিমানীও বাংলাপাঠকদিগের নিকট খ্যাতি অর্জন করাকে আপন চেষ্টার অযোগ্য বোধ করেন না … সেইজন্যই আজ উপযুক্ত কালে এক সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, আমাদের বিদ্যালয়ে অধিকতর পরিমাণে বাংলা শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক”।
কিন্তু কেন আবশ্যক? “কারণ, শিক্ষাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা ভাষা ব্যতীত তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। শিখিয়া যদি কেবল সাহেবের চাকরি ও আপিসের কেরানিগিরি করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু শিক্ষায় আমাদের মনে যে কর্তব্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে তাহা লোকহিত। জনসাধারণের নিকটে আপনাকে কর্মপাশে বদ্ধ করিতে হইবে, সকলকে শিক্ষা বিতরণ করিতে হইবে, সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে, সকলকে জাতীয় বন্ধনে যুক্ত করিতে হইবে” । এই কাজগুলো দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের অবলম্বন ছাড়া অর্জন অসম্ভব। অর্থাৎ মোটের ওপর ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপকার হয়েছে।
কিন্তু আক্ষেপ আছে রবীন্দ্রনাথের। সেটা হলো, “আমরা ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে উদ্দেশ্য শিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপায় লাভ করিতেছি না”।
উদ্দেশ্য শিখছি উপায় লাভ করতে পারছি না। উদ্দেশ্য ও উপায়ের একটা ফারাক করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি শিক্ষার একটা ভাল ফল আছে। সেটা হলো নতুন একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি। সর্বসাধারণের জন্য সঞ্চয় করবার ইচ্ছ। ইংরেজি শিখে যে সকল সিদ্ধান্ত তৈরি হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা সাধারণের সামনে প্রমাণ করবার এবং ইংরেজির দ্বারা যা ভোগ করেছি তা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করবার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বেড়েছে। কিন্তু কিভাবে সেটা সর্ব সাধারণের মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব সেই ‘উপায়’ পাওয়া যাচ্ছে না। কিংবা সুলভ হচ্ছে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন ‘উদ্দেশ্য’ পেলাম বটে, কিন্তু ‘উপায়’ তো পাচ্ছি না।
এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তর্কের অবতারণা করেছেন। সেটা হলো, সেই সময় একটি পক্ষ দাবি করছিল‘বিদ্যালয়ে বাংলা প্রচলনের আবশ্যক নাই। কারণ হলো বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারাই হয়েছে। কারন ইংরেজি শিক্ষত ব্যাক্তিরা তাদের ‘নিজ অনুরাগেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথা বলছিলেন। কারণ ইংরেজি শিক্ষার আগেও বাংলা ভাষা ছিল, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু ইংরেজির সংঘাতে যে নব্য আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেটা ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির বাংলা সাহিত্যের প্রতি নিজের অনুরাগেই হয়েছে। অতএব বাংলা সাহিত্য বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবসাটাই দরকার, বাংলা শিক্ষা নয়। যদি তাই হয় তাহলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা শিক্ষা প্রচলনের দরকার কি? বরং ইংরেজি শিক্ষার যে ধারা তৈরি হয়েছে তাকেই শক্তিশালী করতে হবে।
এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি হচ্ছে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ক্ষমতাশালী লেখকদের হাতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতিও বদলে গিয়েছে। ‘সময়ে পরিবর্তন’ হয়েছে। এখন কেবল ক্ষমতাশালী লেখকের ওপর বাংলা সাহিত্য নির্ভর করছে না। বাংলা সাহিত্য এখন ‘সমস্ত শিক্ষিত-সাধারণের সামগ্রী। এখন প্রায়ই ‘কোনো-না-কোনো উপলক্ষে বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের উপরই সমাজের দাবি দেখা যায়’। কিন্তু বাংলা সাহিত্য চর্চায় সকলের শক্তি সমান নয়। অশিক্ষা ও অনভ্যাসের বাধা আছে। তা অতিক্রম করা সহজ নয়। আর সহজ নয় বলে বাংলা সাহিত্য চর্চার যা দাবি উঠেছে সেই কর্তব্য-পালন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। বাংলা ‘অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা’। তাকে কাজে লাগাতে হলে ‘সবিশেষ শিক্ষা এবং নৈপুণ্যের আবশ্যক’।
রবীন্দ্রনাথ বলছেন,
রবীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।
“এখন বাংলা খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, সভাসমিতি, আত্মীয়সমাজ, সর্বত্র হইতেই বঙ্গভূমি তাহার শিক্ষিত সন্তানদিগকে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে আহ্বান করিতেছে। যাহারা প্রস্তুত নহে, যাহারা অক্ষম, তাহারা কিছুনা-কিছু সংকোচ অনুভব করিতেছে। অসাধারণ নির্লজ্জ না হইলে আজকাল বাংলা ভাষার অজ্ঞতা লইয়া আস্ফালন করিতে কেহ সাহস করে না। এক্ষণে আমাদের বিদ্যালয় যদি ছাত্রদিগকে আমাদের বর্তমান আদর্শের উপযোগী না করিয়া তোলে, আমাদের সমাজের সর্বাঙ্গীণ হিতসাধনে সক্ষম না করে, যে বিদ্যা আমাদিগকে অর্পণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাহার দানাধিকার যদি আমাদিগকে না দেয়, আমাদের পরমাত্মীয়দিগকে বুভুক্ষিত দেখিয়াও সে বিদ্যা পরিবেশন করিবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে—তবে এমন বিদ্যালয় আমাদের বর্তমান কাল ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে”।
একই যুক্তিসূত্রে রবীন্দ্রনাথ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সেটা হলো “পরের শিক্ষাকে যতক্ষণ নিজের ডাঙায় না টানিয়া তোলা যায় ততক্ষণ আমরা বুঝিতেই পারি না বাস্তবিক কতখানি আমরা পাইয়াছি”। অর্থাৎ ইংরেজি শিখে আমরা আদৌ মহৎ বা বড় কিছু অর্জন করেছি কিনা সেটা বুঝতে হলে বড়শী গাঁথা মাছ পানিতে ছলবল করলেও তাকে বড় ভাবার দরকার নাই। ডাঙায় তুললেই বোঝা যাবে মাছ বড় নাকি ছোট। ইংরেজি শেক্ষার বঁড়শিতে মাছ লেগেছে বটে, কিন্তু কি আটকাল সেটা মাছকে ডাঙায় না তুললে বোঝা যাবে না। বঁড়শিতে বেঁধা মাছ পানিতে বিশাল মনে হয়। ডাঙায় তুললেই বোঝা যায় তার ওজন ও প্রস্থ কতো। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,
“রচনাকালে দেখা যায় একটা ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে অস্ফুট অপরিণত আকারে থাকে ততক্ষণ সেটাকে অত্যন্ত বিপুল এবং নূতন মনে হয়, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলেই তাহা দুটো কথায় শেষ হইয়া যায় এবং তাহার নূতনত্বের উজ্জ্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায় না—যেমন স্বপ্নে অনেক ব্যাপারকে অপরিসীম বিস্ময়জনক এবং বৃহৎ মনে হয়, কিন্তু জাগরণমাত্রেই তাহা তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে—তেমনি পরের শিক্ষাকে যতক্ষণ নিজের ডাঙায় না টানিয়া তোলা যায় ততক্ষণ আমরা বুঝিতেই পারি না বাস্তবিক কতখানি আমরা পাইয়াছি। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যাই বঁড়শিগাঁথা মাছের মতো ইংরাজি ভাষার সুগভীর সরোবরের মধ্যে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, আন্দাজে তাহার গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া খুব পুলকিত গর্বিত হইয়া উঠিয়াছি। যদি বঙ্গভাষার কূলে একবার টানিয়া তুলিতে পারিতাম তাহা হইলে সম্ভবত নিজের বিদ্যাটাকে তত বেশি বড়ো না দেখাইতেও পারিত; নাই দেখাক, তবু সেটা ভোগে লাগিত এবং আয়তনে ছোটো হইলেও আমাদের কল্যাণরূপিণী গৃহলক্ষ্মীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে, অমিশ্র অনুরাগ এবং বিশুদ্ধ সর্ষপতৈল -সহযোগে পরম উপাদেয় হইতে পারিত”।
রবীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।
বড়শিতে মাছ গাঁথা এবং মাছ ডাঙায় তোলার যুক্তি ছাড়াও বাংলা সাহিত্য – অর্থাৎ বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। সেটা হলো সাহিত্যের ডিস্কোর্সের বিকাশ না হলে সাহিত্যের শিক্ষা আমাদের আপনার হতে পারে না। সাহিত্য বিকাশের জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাহিত্য চর্চার দরকার আছে। আলোচনা ব্যতীত কোনো শিক্ষা সজীবভাবে আপনার হয় না। “নানা মানবমনের মধ্য দিয়া গড়াইয়া না আসিলে একটা শিক্ষার বিষয় মানবসাধারণের যথার্থ ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠে না”।
বিজ্ঞান শিক্ষা একটা উদাহরণ। যে দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা বহুকাল থেকে প্রচলিত সে দেশে বিজ্ঞান ‘অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভাবে সর্বত্র সংলিপ্ত’ হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞান একটা অপরিচিত শুষ্ক শুকনা জ্ঞান না হয়ে ‘মানবমনের সহিত মানবজীবনের সহিত সজীবভাবে নানা আকারে মিশ্রিত’ হয়ে আছে। তাই সে দেশে অতি সহজেই বিজ্ঞানের অনুরাগ অকৃত্রিম এবং বিজ্ঞানের ধারণা গভীরতর হয়। ‘নানা মনের মধ্যে অবিশ্রাম সঞ্চারিত’ হয়ে বিজ্ঞান সেখানে প্রাণ পেয়ে যায়। ঠিক তেমনি যে দেশে সাহিত্যচর্চা প্রাচীন ও পরিব্যাপ্ত সে দেশে সাহিত্য কেবল গুটিকতক লোকের শখের মধ্যে বদ্ধ নহে: “তাহা সমাজের নিশ্বাসপ্রেশ্বাসের সহিত প্রবাহিত, তাহা দিনে নিশীথে মনুষ্যজীবনের সহিত নানা আকারে মিশ্রিত হইয়াছে এইজন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ, সাহিত্যবোধ স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট নাই এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকালের পূর্বে অতি যৎসামান্যই ছিল”। বিদ্যালয়ে বাংলা চর্চা দরকার বাংলা সাহিত্যের বিকাশ নইলে সম্ভব হবে না। কারণ, দেশীয় সাহিত্যের সম্যক বিস্তার-অভাবে সমাজে অনেকের মধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,
“আলোচনার অভাবে বিদ্বান ব্যক্তিগণ চতুর্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নিজের মধ্যেই বদ্ধ। তাঁহাদের জ্ঞানবৃক্ষ চারি দিকের মানবমন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনরস আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। …”
“আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরানন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অভাব তাহার অন্যতম কারণ। কী করিয়া কালযাপন করিতে হইবে আমরা ভাবিয়া পাই না। আমরা সকালবেলায় চুপ করিয়া দ্বারের কাছে বসিয়া তামাক খাই, দ্বিপ্রহরে আপিসে যাই, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া তাস খেলি। সমাজের মধ্যে এমন একটা সর্বব্যাপী প্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখে, যাহাতে আমদিগকে একসঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমরা যে যার আপন আপন ঘরে উঠিতেছি বসিতেছি গড়াইতেছি এবং যথাকালে, অধিকাংশতই অকালে, মরিতেছি। ইহার প্রধান কারণ, আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের শিক্ষার সহিত সমাজের, আদর্শের সহিত চরিত্রের, ভাবের সহিত কার্যের, আপনার সহিত চতুর্দিকের সর্বাঙ্গীণ মিশ খায় নাই। আমরা বীরত্বের ইতিহাস জানি কিন্তু বীর্য কাহাকে বলে জানি না, আমরা সৌন্দর্যের সমালোচনা অনেক পড়িয়াছি কিন্তু চতুর্দিকে সৌন্দর্য রচনা করিবার কোনো ক্ষমতা নাই; আমরা অনেক ভাব অনুভব করিতেছি কিন্তু অনেকের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিব এমন লোক পাইতেছি না। এই-সকল মনোরুদ্ধ ভাব ক্রমশ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহা ক্রমে অলীক আকার ধারণ করে। অন্য দেশে যাহা একান্ত সত্য আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসারশূন্য হাস্যকর আতিশয্যে পরিণত হইয়া উঠে”।
রবীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’।
যে দিকটা পরিষ্কার সেটা হলো রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য কথাটা সবসময়ই ‘সহিত’ বা ‘সহিতত্ব’ সংক্রন্ত ধারনা থেকে বিস্তার করেছে। সাহিত্যের কাজ অপরের সহত একান্ত হওয়া ‘সহিত’ হওয়া। যদি আমরা পস্পরের মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ তৈরি করতে না পারি এবং সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে ‘সর্ব সাধারণ’-এরর জন্ম, উদয় বা পরিগঠন নিশ্চিত বা অবশ্যম্ভাবী করতে না পারি তাহলে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের কোন কাজে আসবে না।
কারণ, ‘ইংরাজি বিদ্যা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সেই জড় নিশ্চল বরফ-ভারের মতো; দেশীয় সাহিত্যযোগে তাহা বিগলিত প্রবাহিত হইলে তবে সেই বিদ্যারও সার্থকতা হয়, বাঙালির ছেলের মাথারও ঠিক থাকে এবং স্বদেশের তৃষ্ণাও নিবারিত হয়। অবরুদ্ধ ভাবগুলি অনেকের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়া তাহার আতিশয্যবিকার দূর হইতে থাকে। যে-সকল ইংরাজি ভাব যথাযথরূপে আমাদের দেশের লোক গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ যাহা বিশেষরূপে ইংরাজি নহে, যাহা সার্বভৌমিক, তাহাই থাকিয়া যায় এবং বাকি সমস্ত নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের মধ্যে একটা মানসিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, সাধারণের মধ্যে একটা আদর্শের এবং আনন্দের ঐক্য জাগিয়া উঠে, বিদ্যার পরীক্ষা হয়, ভাবের বাংলা জাতীয় সাহিত্য নহে, তেমন আবশ্যক কাজ আর আমাদের আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহাকে আমাদের আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পাছে তাঁহার মলিন বসন লইয়া তিনি আমাদের ধনশালী নবকুটুম্বদের চক্ষে পড়েন এইজন্য তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখি; প্রশ্ন করিলে বলি চিনি না”।
রবীন্দ্রনাথ বুঝেছলেন বাংলা সাহিত্য ‘দরিদ্র ঘরের মেয়ে। তাহার বাপের রাজত্ব নাই। সে সম্মান দিতে পারে না, সে কেবলমাত্র ভালোবাসা দিতে পারে’। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যারা ভালোবাসে তাহাদের পদবৃদ্ধি হয় না, তাদের বেতনের আশা থাকে না, রাজদ্বারে তাদের কোনো পরিচয়-প্রতিপত্তি নাই। “কেবল যে অনাথাকে সে ভালোবাসে সেই তাহাকে গোপনে ভালোবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়। এবং সেই ভালোবাসার যথার্থ স্বাদ যে পাইয়াছে সে জানে যে, পদমান-প্রতিপত্তি এই প্রেমের নিকট তুচ্ছ”।
কথাগুলো আবেগী মনে হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্য’ কথাটা যেভাবে বুঝেছেন সেই বুঝ আমরা ধরতে পারলে বাংলা ‘গরিবের ঘরের মেয়ে’ কথাটার তাৎপর্য আমাদের বুকে শেলের মতো বিঁধতে বাধ্য।
তাই বাংলা সাহিত্যের ভাবী আশা সুয়ো রানীর ঘরে নাই। সেখানে সাহিত্য নিস্ফল। সুয়ো রানীর ঘরে কোন সন্তান এলো না। এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে তিনি মহিষী হয়ে আছেন কিন্তু পয়দা করেছেন ‘প্রথম-প্রথম গোটাকতক কবিতা এবং সম্প্রতি অনেকগুলা প্রবন্ধ’। সংবাদপত্রশয্যাতেই তারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সংবাদপত্ররাশির মধ্যেই তাদের সমাধি ঘটে।
অতএব দুয়ারানীর আমাদের ভরসা। সুয়োরানীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশাভরসা, আমাদের হতভাগ্য দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করেছে। । এই শিশুটিকে আমরা বড়ো একটা আদর করি না; একে উঢ়ানে উলঙ্গ ফেলে রাখি। সমালোচনা করিবার সময় বলি, ‘ছেলেটার শ্রী দেখো! ইহার না আছে বসন, না আছে ভূষণ; ইহার সর্বাঙ্গেই ধুলা!’ ভালো, তাই মানিলাম। ইহার বসন নাই, ভূষণ নাই, কিন্তু ইহার জীবন আছে। এ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এ মানুষ হইবে এবং সকলকে মানুষ করিবে”। কিন্তু মৃতবৎসা সুয়ারানীর মৃত সন্তানগুলিকে বসনে ভূষণে আচ্ছন্ন করে হাতে-হাতে কোলেকোলে নাচিয়ে বেড়ালেও কিছুতেই আমরা ‘উহাদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে পারিব না’।
বোঝা যাচ্ছে সেকালে ইংরেজি শিক্ষিত দরবারি সাহিত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা ক্ষোভ ছিল। কিন্তু সেটা নিছকই আবেগী ব্যাপার ছিল না। তবে আমাদের আলোচনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সর্বসাধারণের অভিমুখী করতে চেয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের ধারণা ‘সমাজ’-এর ধারণা থেকে আলাদা কিছু নয়। সাহিত্যই ‘সর্বসাধারণ’কে দৃশ্যমান কিংবা কার্যত জন্ম দিয়ে থাকে। ‘সহিত’বা সাহিত্যের ধারনা থেকে তিনি মানুষে মানুষে মানুষে, ভাষায় ভাষায়, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরস্পরের মধ্যে বিরাজ করবার বাসনার বীজ দেখতে পেয়েছিলেন। দূরত্ব ও কাঁটাতারের যেসকল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে নিত্যদিন রক্তাক্ত করে চলেছে তাকে মোকাবিলা করবার গোড়ার জায়গা। পাশ্চাত্যের লিটারেচার না। লিটারেচারের অনুবাদ করে ‘সাহিত্য’ চলবে না। ‘সাহিত্য’ – সকলের সতি সম্পর্ক স্থাপন, সকলের মধ্যে যুক্ত হওয়া এবং বিরাজ করবার বাসনা – এই অতি মৌলিক বঙ্গীয় ধারণাই আমামদের আশ্রয় এবং অস্ত্র। প্রতিপক্ষ সে কারণেই ‘সাহিত্য’ ধারনাটির প্রতি তীব্র আগ্রহ বোধ করে।
“আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন সে আপন ভাবী সম্ভাবনাকে আপনি সচেতনভাবে অনুভব করিতেছে। এইজন্য বর্তমান প্রত্যক্ষ ফল তুচ্ছ হইলেও সে আপনাকে অবহেলাযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে নবাঙ্কুর এবং তরুশাখায় নবকিশলয়ের প্রচুর উদ্গম অনারব্ধ আছে, যখন বনশ্রী আপন অপরিসীম পুষ্পৈশ্বর্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই, তখনো সে যেমন আপন অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে শিরায়-উপশিরায় এক নিগূঢ় জীবনরসসঞ্চার, এক বিপুল ভাবী মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসন্ন যৌবনগর্বে সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠে—সেইরূপ আজ বঙ্গসাহিত্য আপন অন্তরের মধ্যে এক নূতন প্রাণশক্তি, এক বৃহৎ বিশ্বাসের পুলক অনুভব করিয়াছে; সমস্ত বঙ্গহৃদয়ের সুখদুঃখ-আশাআকাঙ্ক্ষার আন্দোলন সে আপনার নাড়ির মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে; সে জানিতে পারিয়াছে সমস্ত বাঙালির অন্তর-অন্তঃপুরের মধ্যে তাহার স্থান হইয়াছে; এখন সে ভিখারিনীবেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত এবং দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। এখন হইতে সে শয়নে স্বপনে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সমস্ত বাঙালির—
রবীন্দ্রনাথ দেশকালের বাইরে কেউ নন। তাঁকে সমালোচনা-পর্যালোচনার বিস্তর জায়গা আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে পেছনে ফেলে আমরা সাহিত্য চর্চা করতে পারছি না। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা্র যে অর্থ ও অভিমুখ তা নয়ে এরপর আরও বহুকিছু বলার রয়েছে। যা আমরা ধীরে ধীরে বলার চেষ্টা করব। কিন্তু শুরুতে মোদ্দা কথা হচ্ছে আপাতত এটা প্রমাণ করা যে ‘সহিত’ , ‘সহিতত্ব’ বা ‘সাহিত্য’ একান্তই বঙ্গীয় ধারণা, যার উন্মেষ রবীন্দ্রনাথে। হয়তো সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সাফল্যের চাবি সাহিত্য সম্পর্কে এই মৌলিক বঙ্গীয় ধারণার মধ্যে নিহিত রয়েছে।
আমরা ‘সাহিত্য’ ধারণাটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এবং সাদরে তুলে নিয়েছি। এর ওপর দাঁড়িয়ে আগামিতে আমাদের টেকনিক, টেকনলিজি বা তথাকথিত ‘মাধ্যম’ নিয়ে বিস্তর কথা আছে। আমরা আস্তে আস্তে তা পেশ করবার চেষ্টা করব, যেন আমরা বড়বাংলার বড় পরিসরে রবীন্দ্রনাথের ‘সর্বসাধারণের’ আবির্ভাব বঙ্গীয় অর্থে সাহিত্য চর্চায় মধ্য দিয়ে নিশ্চিত আবির্ভাব ঘটাতে পারি।
সেকালে ইংরেজি শিক্ষিত দরবারি সাহিত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা ক্ষোভ ছিল। কিন্তু সেটা নিছকই আবেগী ব্যাপার ছিল না। তবে আমাদের আলোচনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সর্বসাধারণের অভিমুখী করতে চেয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের ধারণা ‘সমাজ’-এর ধারণা থেকে আলাদা কিছু নয়। সাহিত্যই ‘সর্বসাধারণ’কে দৃশ্যমান কিংবা কার্যত জন্ম দিয়ে থাকে। ‘সহিত’বা সাহিত্যের ধারনা থেকে তিনি মানুষে মানুষে মানুষে, ভাষায় ভাষায়, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরস্পরের মধ্যে বিরাজ করবার বাসনার বীজ দেখতে পেয়েছিলেন। দূরত্ব ও কাঁটাতারের যেসকল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে নিত্যদিন রক্তাক্ত করে চলেছে তাকে মোকাবিলা করবার গোড়ার জায়গা। পাশ্চাত্যের লিটারেচার না। লিটারেচারের অনুবাদ করে ‘সাহিত্য’ চলবে না। ‘সাহিত্য’ – সকলের সতি সম্পর্ক স্থাপন, সকলের মধ্যে যুক্ত হওয়া এবং বিরাজ করবার বাসনা – এই অতি মৌলিক বঙ্গীয় ধারণাই আমামদের আশ্রয় এবং অস্ত্র। প্রতিপক্ষ সে কারণেই ‘সাহিত্য’ ধারনাটির প্রতি তীব্র আগ্রহ বোধ করে।
সূত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা জাতীয় সাহিত্য. রবীন্দ্র রচনাবলী: https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6905
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,
সাহিত্য-পরিচয়. কলকাতা.
ফরহাদ মজহার

কবি, চিন্তক, বুদ্ধিজীবী ও কৃষক। জন্ম: ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায়। পড়াশুনা করেছে ওষুধ শাস্ত্র ও অর্থনীতি বিষয়ে যথাক্রমে ঢাকা ও নিউইর্কে। পেশা সূত্রে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের ‘নয়াকৃষি আন্দোলন’-এর প্রধান সহযোদ্ধা। লালন ধারা-সহ বৃহৎ বঙ্গের ভাবান্দোলন পরম্পরার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সমাজ ও রাজনীতি চিন্তা এবং দার্শনিক বিষয়ে বহু গদ্য রচনা করেছেন। এছাড়াও লিখেছেন নাটক। অনুবাদও করেছেন।
তাঁর বইগুলি-
কাব্যগ্রন্থ:
খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ (১৯৭২) ।। ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি (১৯৭৭) ।। আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে (১৯৮৩) ।। সুভাকুসুম দুই ফর্মা (১৯৮৫) ।। বৃক্ষ: মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ক কবিতা (১৯৮৫) ।। অকস্মাৎ রপ্তানিমুখী নারীমেশিন (১৯৮৫) ।। খসড়া গদ্য (১৯৮৭) ।। মেঘমেশিনের সঙ্গীত (১৯৮৮) ।। অসময়ের নোটবই (১৯৯৪) ।। দরদী বকুল (১৯৯৪) ।। গুবরে পোকার শ্বশুর (২০০০) ।। কবিতার বোনের সঙ্গে আবার (২০০৩) ।। ক্যামেরাগিরি (২০১০) ।। এবাদতনামা (২০১১) ।। অসময়ের কবিতা (২০১১) ।। কবিতাসংগ্রহ (২০১১) ।। তুমি ছাড়া আর কোন্ শালারে আমি কেয়ার করি? (২০১৬) ।। সদরুদ্দীন (২০১৮)
গদ্যগ্রন্থ:
প্রস্তাব (১৯৭৬) ।। সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান প্রসঙ্গে (১৯৮৫) ।। রাজকুমারী হাসিনা (১৯৯৫) ।। সাঁইজীর দৈন্য গান (২০০০) ।। জগদীশ (২০০২) ।। সামনা সামনি: ফরহাদ মজহারের সঙ্গে কথাবার্তা (২০০৪) ।। বাণিজ্য ও বাংলাদেশের জনগণ (২০০৪) ।। মোকাবিলা (২০০৬) গণপ্রতিরক্ষা (২০০৬) ।। ক্ষমতার বিকার ও গণশক্তির উদ্বোধন (২০০৭) ।। ভাবান্দোলন (২০০৮) পুরুষতন্ত্র ও নারী (২০০৮) ।। সাম্রাজ্যবাদ (২০০৮) ।। রক্তের দাগ মুছে রবীন্দ্রপাঠ (২০০৮) ।। সংবিধান ও গণতন্ত্র (২০০৮) ।। নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০৮) ।। তিমির জন্য লজিকবিদ্যা (উপন্যাস, ২০১১)
প্রাণ ও প্রকৃতি (২০১১) ।। মার্কস পাঠের ভূমিকা (২০১১) ।। ডিজিটাল ফ্যাসিবাদ (২০১২)
যুদ্ধ আরো কঠিন আরো গভীর (২০১৪) ।। ব্যক্তি বন্ধুত্ব ও সাহিত্য (২০১৬) ।। মার্কস, ফুকো ও রুহানিয়াত (২০১৮)
নাটক:
প্রজাপতির লীলালাস্য (১৯৭২)
অনুবাদ:
অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার একটি ভূমিকা (মূল: কার্ল মার্ক্স) (২০১০)
খুন হবার দুই রকম পদ্ধতি (মূল: রোকে ডাল্টন) (২০১১)
