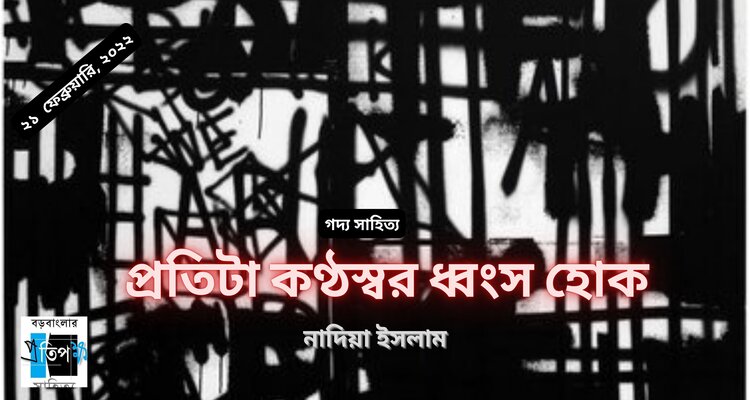
।। নাদিয়া ইসলাম ।।
“লেখা বিষয়টিকে আমার অর্থহীন মনে হয়। ভাষাকেও। আমি বিশ্বাস করি, ভাষা আধিপত্যবাদী, ভাষা কেন্দ্রিয় ক্ষমতা স্থাপনের যন্ত্র, ভাষা চিন্তার আদিকল্প ভাঙ্গার বিভাজনকারী শক্তি। আমি নামক কর্তাসত্তার জন্ম আর অর্গানাইজড বিহেভিয়ার তৈরি হয় ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু তারপরেও আমি এবং আমরা লিখি। আমরা, মানুষরা প্রাণী হিসাবে অদ্ভুত সন্দেহ নাই। আমরা প্রাণী হিসাবে সারাক্ষণ অর্থহীন পরষ্পরবিরোধী কাজ করে যাই। আমরাই বানাই, আমরাই ভাঙি। আমরাই ভাষা নামক অদ্ভুত চিহ্ন তৈরি করি, আবার সেই চিহ্ন দিয়েই জিজ্ঞেস করি, ভাষার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। আমরাই বই লিখি, আবার আমরাই বই লিখে বলি, বই কেন অপ্রয়োজনীয়। তবে এই কনট্রাডিকশান বিষয়টা সুন্দর। এই যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরপাক খাওয়া, এই যে কিছুই না জেনে খুব জ্ঞানী ভাব নিয়ে দিন কাটানো, এই যে কিছুতেই কিছু হয় না জেনেও সবকিছু করতে করতে ইস্কুল পাশ করতে করতে বিয়ে করতে করতে সন্তান জন্ম দিতে দিতে মরে যেতে টেতে সময়ক্ষেপণ, এই যে অদরকারী সব লেখা দিয়ে পৃথিবীর এনট্রোপি বাড়ানো, এই যে কী খুঁজি তা না জেনেই আমাদের সারাদিন খোঁজাখুঁজি, এই যে এইভাবে ভেসে যাওয়া, এই যে উৎপল কুমারের ‘তারপর ঘাষের জঙ্গলে পড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি’র মতো, মৃত বাড়িতে ধুপ জ্বালানোর ধোঁওয়ার মতো, ঠিক আপনার পাশেই আপনার বেড়ালের শুয়ে থাকার মতো এই বিষয়টা সুন্দর। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে লেখক আর কবিরা অদরকারী। আর অদরকারী বলেই তারা দরকারী।”
প্রতিটা কণ্ঠস্বর ধ্বংস হোক
ভাষা বিষয়টাকে আমার খামখেয়ালি ‘ছিলো বেড়াল হয়ে গেলো রুমাল’ জাতীয় উদ্ভট বিষয় বলে মনে হয়। ভাষা খামখেয়ালি না অবশ্যই, ভাষা সিনক্রনিক ডায়াক্রনিক দুইক্ষেত্রেই স্ট্রাকচারাল অবশ্যই, কিন্তু আমি ভাবি, আচ্ছা আমের নাম আম হলো কেন, হাতি হলো না কেন? আমের নাম আম না হয়ে হাতি হলে আমেরই কী যায় আসতো, হাতিরই বা কী যায় আসতো? ‘আমি আম খাই’ না বলে ‘আম খাই হাতি’ বললেই বা কী হতো? তাতে কি মনের ভাব প্রকাশ পেত না? আমি কর্তাসত্তা না হয়ে যদি আম যদি কর্তাসত্তা হতেন বা কেউ যদি কিছু নাই হতেন, তাহলেই বা কী হতো? অর্থাৎ বস্তুকে কেন তার গুণ দিয়েই নির্ধারিত হতে হবে? শব্দকে কেন রিফ্লেক্টিভই হতে হবে? এই রিফ্লেকশান আসছেই বা কোথা থেকে? আম বোঝাতে আমরা যদি মিষ্টি বুঝে থাকি আর হাতি বলতে আমরা যদি বড় বুঝে থাকি, তাহলে প্রশ্ন আসে, একমাত্র আমই কি মিষ্টি বা একমাত্র হাতিই কি বড়? এই যে চিহ্ন দিয়ে একটা আম বা হাতি বা আমের মিষ্টতা বা হাতির বড়ত্বকে সিগনিফাই করার ব্যবস্থা, সেই চিহ্ন ব্যবস্থার উৎপত্তি কোথায়? এই যে শব্দের মাধ্যমে তৈরি হওয়া সিগনিফায়ার এবং সিগনিফায়েডের মিথস্ক্রিয়া, এর ফলে শব্দের সাথে আমাদের যে মনগত সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, তা কি আদতে খামখেয়ালি বিষয় না? ‘না’ শব্দটা বাংলায় ‘না’, ইংরেজিতে ‘নো’, ফ্রেঞ্চে ‘নঁ’, সার্বিয়ানে ‘নে’, জার্মানে ‘নাইন’, শিঙ্ঘলে ‘নেতে’ হলেও আরবীতে ‘রাকোম’, ফিনিশে ‘এই’, স্লোভাকে ‘চে’, মালায়লামে ‘ইল্লা’, তেলেগুতে ‘সাংখিয়া’, মাওরিতে ‘কাহোরে’, মাসেডোনিয়ানে ‘বার’, টার্কিশে ‘হাইর’। এখন নেতিবাচক উত্তর দিতে আমি ‘না’ বলে থাকলে আপনি হঠাৎ করে ‘হাইর’ বলে উঠলেন কেন? ইচ্ছা হলো, তাই? আপনার জন্য হাইর বলা সহজ ছিলো, তাই? আর আপনার জন্য হাইর বলা সহজ হলে আমার জন্য সহজ হলো না কেন? ‘না’র বদলে ‘হাইর’ বলা কী কারণে একজনের সাধারণ প্রবৃত্তি হলো? সাধরণ প্রবৃত্তি কী কারণে এক অঞ্চলের চাইতে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য হলো? কী কারণে আপনার মনের ভাব আর আমার মনের ভাব আলাদা হলো? আর কেনই বা মনের ভাব প্রকাশ করতে হলো? ভাব প্রকাশের জন্য লিখতেই বা হলো কেন? সেই লেখার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মই বা থাকতে হলো কেন? সবাইকে নিজের কথা বোঝানোর, সবাইকে একই শব্দ দিয়ে চিন্তা করানোর আমাদের এত আগ্রহ কেন? কেন সবার সবাইকে বুঝতে হবে? কেন কথা বলতে হবে? কেন যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে অন্যের সাথে? কেন মানুষকে সবকিছুর কেন্দ্রে থাকতে হবে? কেন মানুষকে কেন্দ্রে রেখে আমকে পৃথিবীর সব জায়গাতে আমই হতে হবে? কেন আমাকে সব জায়গাতে আমিই হতে হবে? আমাকে কেন্দ্র করে আমকে মিষ্টি বানানোর প্রক্রিয়া বা ‘না’র বদলে ‘হাইর’ বলার আরবিট্রারি প্রক্রিয়াকে আমি স্বেচ্ছাচারী ও খামখেয়ালি বলে ভাবি। কারণ মিষ্টি হিসাবে সিগ্নিফায়ার ও আম হিসাবে সিগ্নিফায়েডের মধ্যে নিত্য ও অনিবার্য সম্পর্ক নাই। এই যে একেকটা ভাষা একেকটা অঞ্চল দিয়ে মানুষকে এবং তার মনকে এবং সেই সূত্রে তার চিন্তাকে আলাদাভাবে ভেঙে ফেলছে, এই বিভাজন প্রকাশ পায় ভাষার নির্দিষ্ট প্রত্যয় এবং সেই সূত্রে প্রপঞ্চ দিয়ে। আর সে কারণেই আম বা হাতির অস্তিত্ব শব্দ হিসাবে আম বা হাতির আবিষ্কারের আগে বা প্রাক-শব্দগত নয়, কারণ প্রাক-শব্দগত হলে সব ভাষাতেই একই শব্দের সমার্থক শব্দ পাওয়া যেত। কিন্তু সব ভাষায় সব কিছুর সমার্থক শব্দ নাই। ডেনিশ শব্দ ‘হুগা’ (Hygge)-র কোনো ইংরেজি সমার্থক শব্দ নাই। হুগা অর্থ আগুনের ধারে বসে বা আরামদায়ক উষ্ণতায় বন্ধুদের নিয়ে সময় উপভোগ করা। আরবী শব্দ ‘ইয়া-আবারনি’ (يا’عبرني) অর্থ প্রিয়জনের আগে নিজে মারা যাবার আকাঙ্খা। ম্যান্ডারিন ‘উয়ানফিন’ (缘分) শব্দের অর্থ দুইজন মানুষ, বিশেষত প্রেমিক প্রেমিকার জন্য নির্ধারিত ভাগ্য। ছোটোবেলায় আমি ভাবতাম ভাষা বিষয়টা খুব অর্গানিক। ভাবতাম গাছের মতো করে ভাষা জন্মায়, গাছের মতো আলো বাতাসের তারতম্যে তার পরিবর্তন আসে, বছর ঘুরে ডালপালা গজায়, পাতারা ঝড়ে যায়, আবার নতুন পাতাও গজায়। ভাবতাম ভাষার আগে নিশ্চয়ই চিন্তা। কিন্তু আমাদের চিন্তাতে যে ভাষা লাগে, সেই ইন্টারনাল ভাষাটা আসছে কোথা থেকে? একজন শিশু যিনি এখনও কথা বলতে শেখেন নি, তার মাথায় ভাষার উপাত্তগুলি আসছে কী করে? এরিক লেনবার্গের ‘বায়োলজিকাল ফাউন্ডেশান অভ ল্যাঙ্গুয়েজ’ লেখাটা এইক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ লেখা, যেখানে দেখানো হয় আমাদের মনস্তত্বের সাথে ভাষার উৎপাদন ও রূপান্তরক্ষম ব্যকরণ কিভাবে আমাদের জিনেটিক্সে মিশে আছে। কিন্তু এই আলাপের সমস্যা হচ্ছে এই ধরণের বায়োলজি প্রসূত ভাষাবিজ্ঞান ভাষাকে ইউনির্ভাসাল বানিয়ে ফেলে। অথচ ভাষা ইউনিভার্সাল নয়, অর্গানিকও নয়। এটা আমার কথা না, উইলিয়াম উইটনি, নোম চোমস্কিদের কথা। হুয়ান ওয়ার্তের কাজের উপর ভিত্তি করে যে ভাষার সাইকোলজিকাল থিওরির ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করানো হয়, সেখানে ভাষাকে বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের নিক্তি হিসাবে ধরা হয়, মূলত মানুষের সাথে অন্যান্য পশুপাখির পার্থক্য তৈরির মাধ্যমে। যদিও রোমান্টিসিজমের উদ্ভবের সাথে সাথে এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে পরিপার্শ্ব থেকে মুক্ত সত্তা ধরার মাধ্যমে এই অস্বয়ংক্রিয় শারীরবৃত্তীয় (অর্থাৎ যান্ত্রিক) রাশনালিস্ট মনস্তত্ব আর ভাষাতত্ত্ব খানিক খারিজ হয়ে যায়। দেকার্তেও ভাষাকে বিশেষভাবে মানুষের মৌলিক অধিকৃত বিষয় বলে ভাবতেন। তিনি ভাবতেন পশুপাখির ভাষার সাথে মানুষের ভাষার পার্থক্য হচ্ছে, পশুপাখির ভাষায় শুধুমাত্র কন্ডিশান এবং এসোশিয়েশানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্রে থাকে না। দেকার্তে এবং এ ধরণের অন্যান্য কার্তেশিয়ান চিন্তার সূত্রপাত পশুপাখির কবিতা লেখার মতো আপাত নিরর্থক সৃষ্টিশীল ভাষার অভাবকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। পশুপাখিকে এই যে শুধুমাত্র বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক দিয়ে বিচার করার স্থূল একমাত্রিক চিন্তা, তা আমার কাছে সমস্যাজনক বলে মনে হয়। আমি বিশ্বাস করি, পশুপাখিরা যে মোটা দাগে হলেও ল্যাঙ্গু ও প্যারোল অর্থে নিজেদের ভাষাকে একমাত্রিক করে ফেলছেন না, সেটা তাদের মানুষের চাইতে প্রাজ্ঞ অবস্থান। তবে এটাও ঠিক, আমাদের জানামতে পশুপাখিরা কবিতা লেখেন না। লিখলেও (অর্থাৎ তৈরি করলেও) সেটা আমরা টের পাই না। কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, তা শুধু আমরাই লিখি। কিন্তু আমরা কবিতা কেন লিখি, এটাও একটা প্রশ্ন। কোন্ তাড়নায় মানুষ অস্থির হন, সকালে অফিস আছে জেনেও রাত তিনটায় ঘুম থেকে উঠে লিখতে বসে যান, না লিখলে কেন তার অসহ্য লাগতে থাকে, কী কারণে এসব হয় আমি জানি না। খুব সরলভাবে দেখলে এই প্রেক্ষিতে ভাষা দুই ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগে থাকে, আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ কথাবার্তা, গার্হস্থ্য অর্থনীতির বাজারের ফর্দ আর হাসপাতালের বিলের হিসাব, রাজনৈতিক স্লোগান, প্রেমিকাকে পাঠানো টেক্সট মেসেজ পত্রিকা প্রতিবাদ আর ফেইসবুকের এ্যাকটিভিজম। দ্বিতীয় ভাগে থাকে অনর্থক বাক্য, পেট ভরবে না এমন কবিতার শব্দ, যা বললেও পৃথিবীর কিছু যায় আসবে না, না বললেও কিছু যায় আসবে না, যার অধিকাংশই শুধুমাত্র চিন্তা ফর দা সেইক অভ ইট, যার সমগ্রই লেখকের শরীর থেকে উগড়ে দেওয়া, প্রসব করা একেকটা অবাঞ্ছিত অনুভূতি- যার বক্তা ও শ্রোতা লেখক নিজেই।
লেখা কি ঈশ্বর সাধনার মতো কোনো বিষয়? ঈশ্বর কি শব্দে থাকেন? হয়তো থাকেন। হয়তো থাকেন না। নাকি লেখক সত্তা আর ঈশ্বর সত্তা মূলত একই?
আমি কেন লিখি, আমি খুব একটা জানি না। ফেইসবুকের এ্যাকটিভিজম থেকে এক ধরণের লেখা আমি লিখি, এখানে ধর্ষিত হয়েছেন একজন, ওখানে কোন্ এক মন্ত্রী উলটাপালটা নারীবিদ্বেষী বক্তব্য দিচ্ছেন, টিভিতে একটা এ্যাড চলছে পুরুষতান্ত্রিক- এইসব এইসব এইসব নিয়ে। কিন্তু তার বাইরেও আমি লিখি। যেই লেখার কোনো প্রয়োজন নাই। আইসল্যান্ডের ভলকানিক ইরাপশানে যখন ছাই দিয়ে গাড়ির কাচ ধূসর কালো হয়ে যায়, যখন ইয়র্কশায়ার ডেলের পাহাড়ে হাইকিং করতে করতে পাথরে পা পিছলে আপনি পাহাড় থেকে কয়েক হাজার ফিট নিচে পড়ে যাচ্ছেন, জানেন হয়তো মারা যাচ্ছেন এখুনি, তখনও লেখা মাথায় আসে কেন? ফ্রান্সের এক প্রত্যন্ত গ্রামের একটা গলির ভেতরে তস্য গলিতে এক পুরানো বাড়ির জানালায় লাল রঙের পর্দা দেখে কেন আমার লিখতে ইচ্ছা হয় আমি জানি না। কেন মনে হয়, আচ্ছা আমি তো জানালায় লাল পর্দা দেই না, কে জানালায় লাল রঙের পর্দা দেন? আচ্ছা, ঐ বাড়িতে কি ম্যাডোনা তার লা ইসলা বোনিতা গান লিখেছিলেন? তিনিই বা কেন একটা লাল পর্দাওয়ালা ঘরে বসে অনেক দূরের একটা দ্বীপের কথা ভাবছিলেন? আচ্ছা ভাবলেনই না হয়। কিন্তু লিখলেন কেন? এই লেখা কার সাথে যোগাযোগ? পাঠকের সাথে? মোটেই তা না। লেখকরা পাঠকের জন্য লেখেন না। লেখক লিখেন নিজের জন্য। রঁলা বার্থ বলেছিলেন, লেখকের মৃত্যু হয় পাঠকের জন্মের ভেতর দিয়ে। আমি অবশ্য পাঠককে দ্বিতীয় সত্তা বলে ভাবি না। লেখকের লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি নিজেই পাঠক হয়ে ওঠেন। তিনি তাই দিনশেষে নিজের জন্যই লিখেন। হয়তো নিজের অন্তর্গত সত্তার জন্য লেখেন। হয়তো প্রেমে লেখেন, হয়তো কষ্টে লেখেন, হয়তো নিজেকে বুঝতে চাইতে লেখেন, হয়তো কিছুই না ভেবে জীবন নামক এই জার্নিকে টুকে রাখতে, হয়তো একটা প্রাচীন শহরের এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মাথায় আসা ভাবনাদের ধরে রাখতে, ঘাসের ভিতর পড়ে পাওয়া একটা ফুটা পয়সার সাথে সেই পয়সার অতীত প্রভুর কাল্পনিক যোগাযোগ তৈরি করে নিজেকেও তার সাথে সম্পর্কিত মনে করে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে লেখেন। কিন্তু আদতে কি কারুর সাথে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় সেই লেখার মাধ্যমে? আদতে কি কারুর সাথে যোগাযোগ হয় সেই শব্দ দিয়ে? লেখকের মাথার চিন্তা, তার এই যে হাত থেকে রক্ত ঝড়ার তীব্র কষ্টের অনুভূতি, তার ইন্টারনাল স্ট্রাগলকে কি আদৌ ধরা যায়? তিনি নিজেই কি নিজেকে ধরতে পারেন নিজের লেখা পড়ে? তিনি যখন নিজের লেখা পড়ে কাঁদেন, তখন কি তিনি সেই লেখার চরিত্র হিসাবে কাঁদেন নাকি নিজের ব্যথায় কাঁদেন? লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ঐ লেখার সাথে লেখকের আর সম্পর্ক কি আর থাকে? আমি ছোটোবেলায় কিছু পড়ে মনে দাগ কাটলে সেগুলি ডায়েরিতে লিখে রাখতাম। সেগুলি মনে কেন দাগ কাটতো আমি জানি না। এই যে “You promise heavens free from strife, Pure truth and perfect change of will, But sweet, sweet is this human life, So sweet I fain would breathe it still, Your chilli star I can forgo- This warm kind world is all I know” বা ‘দা ওমেন’ এর জেনিংস আর থর্নের কনভার্সেশানে “Maria Avedici Santora, Bambino santora, In Morte et in Nate Amplexarantur Generationes” যার অর্থ “মারিয়া আভেদিচি সান্তোরা ও সান্তোরার শিশু, জন্ম ও মৃত্যুতে আলিঙ্গন করছে প্রজন্মকে” বা “শান্তা দৌঃ শান্তা পৃথিবী, শান্তম্ ইদম্ উর্বন্তরিক্ষম, শান্তা উদন্ততীর আপঃ, শান্তা নঃ সন্তু ওষধীঃ” এই বাক্য আমি কেন লিখে রেখেছিলাম ডায়েরিতে? এই বাক্যের গুরুত্ব কই? কেন রাস্তার মাঝখান থেকে আমার এই বাক্যটাই টুকতে হলো? এই বাক্যরা কি আমার মনস্তত্ব তৈরি করছিলো? কিন্তু আমরা যা লিখি, তা কি আমাদের মানুষ হিসাবে আমাদের চরিত্র দাঁড় করায়? লেখা কি মূলত নিজেকে ডিফাইন করার, নিজেকে চেনার মাধ্যম? লেখা কি ঈশ্বর সাধনার মতো কোনো বিষয়? ঈশ্বর কি শব্দে থাকেন? হয়তো থাকেন। হয়তো থাকেন না। নাকি লেখক সত্তা আর ঈশ্বর সত্তা মূলত একই? ‘ছিলো বেড়াল হয়ে গেলো রুমাল’ এর মতো ম্যাজিক রিয়ালিটিতে বিলং করে নিজেকে ক্ষমতাধর ভাবার একটা ঐশ্বরিক এ্যাবসার্ড পাওয়ার প্রাকটিসের কারণে লেখা তৈরি হয়? এই যে জেমস জয়েসের ইউলিসিসের ‘ব্যকরণ মানি না’ ২৪ হাজার শব্দে দুইটা দাড়ি একটা কমা দিয়ে তৈরি প্যারাগ্রাফ বা Soliloquy-র ৪ হাজার (+) শব্দে লেখা পৃথিবীর দীর্ঘতম বাক্যের এলোমেলো চিন্তা, এইসব কি শুধুমাত্র লেখক হিসাবে একজন মানুষের নিউরোটিসিজম নাকি পাওয়ার প্রাকটিস?
লেখা বিষয়টিকে আমার অর্থহীন মনে হয়। ভাষাকেও। আমি বিশ্বাস করি, ভাষা আধিপত্যবাদী, ভাষা কেন্দ্রিয় ক্ষমতা স্থাপনের যন্ত্র, ভাষা চিন্তার আদিকল্প ভাঙ্গার বিভাজনকারী শক্তি। আমি নামক কর্তাসত্তার জন্ম আর অর্গানাইজড বিহেভিয়ার তৈরি হয় ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু তারপরেও আমি এবং আমরা লিখি। আমরা, মানুষরা প্রাণী হিসাবে অদ্ভুত সন্দেহ নাই। আমরা প্রাণী হিসাবে সারাক্ষণ অর্থহীন পরষ্পরবিরোধী কাজ করে যাই। আমরাই বানাই, আমরাই ভাঙি। আমরাই ভাষা নামক অদ্ভুত চিহ্ন তৈরি করি, আবার সেই চিহ্ন দিয়েই জিজ্ঞেস করি, ভাষার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। আমরাই বই লিখি, আবার আমরাই বই লিখে বলি, বই কেন অপ্রয়োজনীয়। তবে এই কনট্রাডিকশান বিষয়টা সুন্দর। এই যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরপাক খাওয়া, এই যে কিছুই না জেনে খুব জ্ঞানী ভাব নিয়ে দিন কাটানো, এই যে কিছুতেই কিছু হয় না জেনেও সবকিছু করতে করতে ইস্কুল পাশ করতে করতে বিয়ে করতে করতে সন্তান জন্ম দিতে দিতে মরে যেতে টেতে সময়ক্ষেপণ, এই যে অদরকারী সব লেখা দিয়ে পৃথিবীর এনট্রোপি বাড়ানো, এই যে কী খুঁজি তা না জেনেই আমাদের সারাদিন খোঁজাখুঁজি, এই যে এইভাবে ভেসে যাওয়া, এই যে উৎপল কুমারের ‘তারপর ঘাষের জঙ্গলে পড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি’র মতো, মৃত বাড়িতে ধুপ জ্বালানোর ধোঁওয়ার মতো, ঠিক আপনার পাশেই আপনার বেড়ালের শুয়ে থাকার মতো এই বিষয়টা সুন্দর। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে লেখক আর কবিরা অদরকারী। আর অদরকারী বলেই তারা দরকারী। এইসব এ্যাকটিভিজম আর সংসার যাপনের পাঙাশ মাছের ঝোলের ভেতর ডালের বড়ির মশারির ভেতর নিঃশব্দ যৌন সঙ্গমের পলাশির যুদ্ধের চাইনিজ ফোল্ড আর ইন্ডিয়ান ব্লকের ডেমোগ্রাফিকাল জিনেটিক কোডিংয়ের বাইরের একটা সম্পূর্ণ অদরকারী you expected to be said in the fall, part of you died each year when the leaves fall, from the trees and the branches এর জগত, তা লেখক আর কবিরা ছাড়া কে দেখাতে পারতেন মানুষকে? আমি যে গুরুত্বহীন, এবং গুরুত্বহীন বলেই আমি গুরুত্বপূর্ণ, সে কারণেই আমি রাত্রির স্তরে স্তরে আমার অয়ুধ, প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, হৃৎ, চিৎ আর অহম রেখে যাচ্ছি শব্দের ভিতর, যদি শব্দ বলে ডিপ স্ট্রাকচারে কোনো শব্দ থেকে থাকে, এবং যদি শব্দে কিছু রেখে যাওয়া যায়। Ferdinand de Saussure যেটাকে স্ট্রাকচারালিস্ট তত্ত্বায়নের মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বের স্কোপের বাইরের “free creation” বলেছেন। ফ্রি ক্রিয়েশানে আমি বিশ্বাস করি না, এমনকি কোনো রকম স্ট্রাকচারালিস্ট এ্যাপ্রোচে না গিয়েও। আমি বিশ্বাস করি সৃষ্টি মুক্ত না। ভিক্তর স্ক্লভশ্কি বিষয়টা খুব আর্টিস্টিকালি লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “উপকূলে বাস করা যেই মানুষ সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে বড় হন, তারা সমুদ্রের অস্ফূট উচ্চারণ শুনতে পান না। আমরাও যেই শব্দ উচ্চারণ করি, তার খুব কমই শুনতে পাই। আমরা তাকাই, কিন্তু দেখি না। পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের জানাবোঝা হয়ে গেছে, আমাদের উপলব্ধিও ক্ষয় হয়ে গেছে। যেটা বাকি আছে, তার নাম শুধুমাত্র ঠাহর করা।” আর সে কারণেই সৃষ্টি মুক্ত এবং একলা স্বাধীন স্বত্ত্বা না। সৃষ্টির পেছনে কালেক্টিভ আনকনশাসনেস আছে, পুরানো গল্প আছে। যেই গল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ, অথচ গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমরা তা চোখে দেখি না। ভিগটেনস্টাইনও এই ধরণের কিছু একটা বলেছিলেন। আমার স্মৃতি ভুল না করে থাকলে তিনি বলেছিলেন, আমাদের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা কখনো দেখি না। আমারও তাই মনে হয়। আমরা অপরিচিতর জানালায় অগুরুত্বপূর্ণ লাল রঙের পর্দা দেখি, বাতাসে বৃত্তাকার পথে তুষারকণা উড়তে দেখি, রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে আমরা আর্মেনিয়ান ছেলের বাঁ চোখ দিয়ে পানি গড়াতে দেখি, আর ভাবি, আহা, ছেলেটা কাঁদছেন কেন? এই ভাবনায় এনজিওসুলভ সাহায্যের বাসনা নাই, এই ভাবনা দায়িত্ব নেয় না, ছেলেটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে না তিনি কেন কাঁদছেন? কিন্তু এই এক চোখ থেকে নেমে আসা পানির চিন্তায় আপনার রাতে ঘুম আসে না, আপনি এলোমেলো বিছানায় উঠে বসেন, বাইরের স্ট্রিট লাইটের আলো আপনার জানালার শার্শির ভেতর দিয়ে ঢুকে দেয়ালে সমান্তরাল ছায়া ফেলে, আপনি পাশে ঘুমিয়ে থাকা প্রেমিকের শরীরে হাত রাখেন, উনি ঘুমের মধ্যে খানিক শব্দ করে শ্বাস টেনে পাশ ফিরে একবার আপনার দিকে তাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন, আর আপনি ভাবতে থাকেন ভাবতে থাকেন ভাবতে থাকেন, রাস্তায় বসে এ্যাকোর্ডিয়ান বাজানো আর্মেনিয়ান ছেলের এক চোখের পানির কথা। কর্মসকল আপনাকে লিপ্ত করে না, কর্মে আপনার ফলস্পৃহা নাই, অথচ আপনি কর্মে যুক্ত হন। প্রতিদিন।
অথচ দেখেন।
ভাষা আপনার যোগাযোগের মাধ্যম না।
শব্দ কোনো চিন্তা করার যন্ত্র না।
অথচ শব্দ বাক্য দাড়ি কমারা নিজের কাছে নিজ হয়ে ওঠার, নিজের বাস্তবতাকে নিজে তৈরির মাধ্যমে, Hygge يا’عبرني 缘分 শব্দ দিয়ে স্ট্রাকচার খারিজ করার ভেতরে নিজস্ব কনোটেটেড অভিজ্ঞতা দিয়েই ভাষার রূপ দেওয়ার মাধ্যমে, যদি কর্তাসত্তা বলে কোনো শব্দ থেকে থাকে, সেই শব্দ যদি আমি যা বোঝাই, তা বোঝাতে পারে, তাহলে তারা আমার কর্তাস্বত্ত্বাকে খুঁজতে থাকার
একটা
সার্চ
এঞ্জিন
ছাড়া
আর
কী?
এই ছেলেটাকে নিয়ে আমি একটা গল্প লেখা শুরু করেছিলাম। খুব একটা সামনে আগাতে পারি নাই যদিও। ছেলেটার চরিত্র নিয়ে আমি অনেকদিন ভেবেছি। আমার গল্পের চরিত্রদের আমি শরৎচন্দ্র জাতীয় ফেইলিওরের জায়গা থেকে দেখি না। একইসাথে তারা আনরিয়ালিস্টিক সুখী প্রাণীও না। তারা নন-শ্যালন্ট হু-কেয়ার্স চরিত্র। তাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট স্ট্রাগল আছে, কিন্তু তাতে তাদের তেমন কিছু যায় আসে না। তারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে সব ঝামেলা ফেলে দেন। এই ছেলেটাও অনেকাংশে তাই। উনার নাম তিগরান। ব্রিটেনে আশ্রয় পাওয়া একজন রিফিউজি। উনার আনুশ নামের একজন কন্যাশিশু ছিলেন। সেই কন্যাশিশুকে নিয়ে ব্লাক সি পাড়ি দিয়ে রোমানিয়া ঢোকার পথে উনি নিউমোনিয়ায় মারা যান। তিগরান মেয়ের কথা খুব একটা ভাবেন না। তিনি সকালে জব-সেন্টারে যান কাজের সন্ধানে। দুপুরবেলা বেগুনি রঙের জাইরো হাতে পোস্ট অফিসে কিউয়ে দাঁড়ান সপ্তাহের ভাতা তুলবেন বলে। এরপর চিকেন এ্যান্ড চিপসের দোকান থেকে এক পাউন্ড দিয়ে একটা মুরগীর ঠ্যাং আর এক ক্যান ফান্টা কেনেন। এরপর সন্ধ্যা হলে স্ট্রাটফোর্ডের শপিং সেন্টারের সামনে বসে এ্যাকোর্ডিয়ান বাজান। কিছু মানুষ ভাংতি পয়সা দেন, বেশিরভাগই তার দিকে একবারও না তাকিয়ে ঢুকে যান শপিং সেন্টারে। কিন্তু এই গল্পটা আমি লিখে শেষ করতে পারি নাই। অবশ্য লেখা কখনো শেষও হয় না। যেই লেখাগুলি শেষ হয়ে ছাপার অক্ষরে বের হয়ে যায়, সেগুলিও শেষ হয় না। আমি জানি না অন্য লেখকদের কী হয়, কিন্তু আমার গল্পের চরিত্রদের সাথে আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকি। আমি তাদের সাথে সাথে সকালে জুতার ফিতা বাঁধি, দেখি, ডান পায়ের জুতা বাঁ পায়ের চাইতে বেশি ক্ষয় হয়েছে, আমি তাদের সাথে সাথে মুরগীর হাড় চিবাই, একদম একদম একদম শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না হাড় চিবানো লালচে খয়েরি শুকনা ছোবড়া ছাড়া সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, আমি পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে বসা মেয়ের হাত থেকে টাকাগুলি নিয়ে দুইবার তিনবার চারবার গুণি, প্লাস্টিকের ব্যাগে টাকা ঢুকিয়ে জ্যাকেটের ভেতরের পকেট জিপার টেনে আটকাই। আমি তিগরান ভার্দানিয়ানের সাথে রাস্তায় বসে এ্যাকোর্ডিয়ান বাজাই, আমি টের পাই আমার শুধুমাত্র একটা চোখ দিয়ে পানি নামছে।
আমার লেখা
শেষ
হয়
না
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২

2018
silkscreen ink and spray paint on canvas
213.4 x 152.4 cm; 84 x 60 in. by Adam Pendleton.
নাদিয়া ইসলাম

লেখক, গবেষক, ভিগান, অজ্ঞেয়বাদী, বিড়ালপ্রেমিক, নারীবাদী এবং কনস্পিরেসি থিওরির একনিষ্ঠ ভক্ত। জন্ম ১৯৮৫ সালে।


ভালো লাগলো পড়ে। অনুভব করা যাচ্ছিলো চিন্তার অবিন্যাস/বিন্যাস। মুগ্ধতা।
tremendous writing indeed
দিলেন চিন্তার জট লাগিয়ে!