
।। অরূপশঙ্কর মৈত্র ।।
যাহ বাবা! রচনাকারের কি মাথার গণ্ডগোল আছে? প্রজন্ম, মেটান্যারেটিভ, পোস্টমডার্নিজম থেকে হঠাৎ একলাফে কোভিড? নিউ নর্মাল? এ যেন, আমি এখানে কফিহাউসে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লাম, একসপ্তাহ পরে আটলান্টিকে সামুদ্রিক ঝড় হয়ে গেল, এইরকম কার্য-কারণ সম্পর্কের যুক্তি। তো এই যুক্তিও কিন্তু চিন্তকেরা নাকচ করে দেয়নি। তারা বলছে, হ্যাঁ হতে পারে। কফি হাউসের ধোঁয়ায় আটলান্টিকে ঝড় উঠতে পারে। একে বলে কেওস থিওরি।
গ্র্যান্ডফাদার
একথা বোধহয় বলাই যায়, সারা ভারতে বাঙালিরাই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানচর্চা করে (মানে নয়, পরিমাণে।) বাঙালি বলতে পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোক বাঙালির কথা বলছি। যারা মঞ্চে থাকে। থাকে মিছিলের সামনের সারিতে, অধুনা ওয়েবিনারে বক্তা হিসেবে থাকে। যারা বেশিরভাগ উচ্চবর্ণ। শ্রমজীবী নয়। লেখাপড়া জানে। প্রবন্ধ লিখলে যারা অবধারিতভাবে অজস্র উদ্ধৃতি দেয়, ফুটনোট, বিবলিওগ্রাফি। এদের মধ্যে যারা কলেজে অধ্যাপনা বা গবেষণায় যুক্ত তাদের বাজারদর বেশি। প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, জেএনিউ প্রাক্তনী হলে তো কথাই নেই। উনিশশতকের শেষে এদের শিক্ষিত সম্প্রদায় বলা হত। আজকাল বুদ্ধিজীবী বলা হয়। স্কুল ড্রপ আউটকে যারা অবলীলায় বলতে পারে “বিলেত ফেরনি? … এই তব বিদ্যে? ছিঃ”। কিন্তু রবি ঠাকুরও তো স্কুল ড্রপ আউট ছিল! হ্যাঁ, তা ছিল, কিন্তু কোন বংশ দেখতে হবে তো! বাপ ঠাকুর্দা কারা? এই বাঙালি জ্ঞানচর্চকদের ‘বর্ণ’পরিচয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিই তাদের বাপ-পেতেমোর পরিচয়। এরা লিটলম্যাগ করে, নাটক করে, সিনেমা করে, সাহিত্য, সাহিত্যের আসর বাসর ইত্যাদি করে। এরা দেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প সাহিত্য নানা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে। কেন স্কুল ড্রপ-আউটরা এদের কাছে ব্রাত্য? কারণ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের লিগ্যাসি আমাদের দুটো জিনিস শিখিয়েছে। ‘কী’ বলছে’র থেকে ‘কে” বলছে’র গুরুত্ব অনেক বেশি। ‘কে’ বলছে? সে কি উপবীতধারী ব্রাহ্মণ? তবেই তার বেদ ব্যাখ্যা করার অধিকার আছে। যদি বেনারসের আশ্রমের সাধু ব্রাহ্মণ হয়? তবেতো কোনো প্রশ্ন ছাড়াই শুধু শ্রবণ। একবার পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের জন্য সৈয়দ মুজতবা আলী নাকি ব্রাহ্মণ সেজে মন্দিরে গিয়ে এমন মন্ত্র আর ব্যাখ্যাট্যাখ্যা শুরু করেছিলেন যে পাণ্ডারাই প্রায় পায়ে পরে যায়! এ আমাদের আজন্মলালিত অভ্যাস। প্রশ্ন উঠবে এই বুদ্ধিজীবীরা কি তাহলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে মান্যতা দেয়? না, দেয় না। কিন্তু শৈশবের লালনপালনের মধ্যেই অবচেতনে এই অভ্যাস প্রোথিত হয়ে যায়।
কজ অ্যাণ্ড এফেক্ট লজিক হোক অথবা ডায়ালেকটিক্স, বারবার ‘কেন’ নিয়েই তো হৈহৈ করতে হবে। আসলে সমস্ত কেন’র আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক দানবাকৃতি গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ। এক প্রহেলিকা, যা বারবার বিভ্রান্ত করে। কেন’র সবচেয়ে বড় অপরাধ সে সন্দেহ করতে শেখায়।
টোলট্যাক্স+ট্রাফিক-পুলিশ+মালিকের ঝামেলার সঙ্গে যখন লকডাউন যুক্ত হল, তখন লক্ষ লক্ষ ট্রাক ড্রাইভারদের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ট্রাকড্রাইভারস অ্যাসোসিয়েশনের যে নেতা আলোচনায় আসবেন, হয় তিনি ট্রাক ড্রাইভার নন, নয়তো কোনও এক কালে ড্রাইভিং করলেও তিনি এখন কোনো রাজনৈতিক দলের পেশাদার ইউনিয়ন নেতা। এবং বলাই বাহুল্য, তার উচ্চবর্ণ হবার সম্ভাবনা প্রবল। সম্প্রতি দিল্লির সীমান্তে কৃষকরা আমাদের একটু বিপদে ফেলেছে। ওরা নিজেদের কথা নিজেরাই বলছে। ওরা বিলেতফেরত কোনো অর্থনীতিবিদের ধার ধারছে না। ওরা মিডিয়াকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। গোদি-মিডিয়া বলে মশকরা করছে। আমাদের এখানে ভাবাই অসম্ভব। রিকসাওয়ালা কিম্বা সবজি-বিক্রেতা লকডাউনে অর্থনীতির ওপর প্রভাব নিয়ে বলবে আর আমরা কফি-হাউস আঁতেলরা বসে বসে শুনব? হাহাহা- (এই রচনাকারের পরিচয়ে যদি শুধু সমাজকর্মী বা নাট্যকার লেখা থাকে, তাই থাকার কথা, তাহলে, হিহি, চার-পাঁচ লাইন পড়েই, মনে মনে ধুউস বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু যদি অক্সফোর্ড থাকে? যদি পরিচয়ে আনন্দবাজারীয় ট্যাগ থাকে? হুমমম, লেখাটা বড় কিন্তু পড়তে হবে।)- যে কোনো ধর্মে আর একটা রীতি হল, কী এবং কীভাবে প্রশ্ন করা জায়েজ। ‘কেন’ প্রশ্ন নয়। মন্দিরের সামনে শিশু জানে কী? মন্দির। জানে কীভাবে হাত জোড় করে ঠাকুর প্রণাম করতে হয়। শিশু জানে নামাজ আদায় কী, কিভাবে নামাজ আদায় করতে হয় তাও জানে। কিন্তু শিশু যেই প্রশ্ন করবে কেন প্রণাম? কেন নমাজ আদায়? অমনি বজ্রপাত। সব ধর্মেই ‘কেন?’ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইওরোপে যখন র্যাশনালিজম বা রিজনিংএর ঝড় উঠল তখনতো ‘কেন’ নিষিদ্ধ হলনা। বরং ‘কেন’ই তো টেনে নিয়ে গেল নতুন নতুন জ্ঞানচর্চায়। সেটা কজ অ্যাণ্ড এফেক্ট লজিক হোক অথবা ডায়ালেকটিক্স, বারবার ‘কেন’ নিয়েই তো হৈহৈ করতে হবে। আসলে সমস্ত কেন’র আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক দানবাকৃতি গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ। এক প্রহেলিকা, যা বারবার বিভ্রান্ত করে। কেন’র সবচেয়ে বড় অপরাধ সে সন্দেহ করতে শেখায়।
সম্ভবত, বাঙালির মধ্যেই কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক, শিল্পীর পারসেন্টেজ সবচেয়ে বেশি (মানে নয়, পরিমাণে)। বাঙালি চরিত্রগতভাবেই ইনটেলেকচুয়্যাল। বুদ্ধিজীবী। আঁতেল। (এই লেখায় বাংলা বা বাঙালি বলতে শুধু পশ্চিমবঙ্গ ধরা হয়েছে।) যদি গত একশবছরে এদের বিবর্তনের ইতিহাস জানতে ইচ্ছে হয়, গত একশবছরের আনন্দবাজার ফলো করুন। একেবারে ঝকঝকে ছবি পেয়ে যাবেন। এই বছরেই আনন্দবাজার একশ পূর্ণ করল। আনন্দবাজার গ্রুপ আজও এই চিন্তকদের ফ্রেন্ড ফিলজফার, গাইড। বাঙালির এই আঁতেলিয় চর্চার শেষ প্যারাডাইম সিফট শুরু হয়েছিল বছর পঞ্চাশ আগে। সেইসময়ে জ্ঞানচর্চার জগতে মার্ক্সবাদের ছিল কার্যত একছত্র প্রভাব। যদিও মার্ক্সবাদের নানা গোত্র তৈরি হয়ে গেছিল, কেউ হঠকারি, তো কেউ সংশোধনবাদী, কেউ অতিবাম, তো কেউ নয়াসংশোধনবাদী। অর্থাৎ কেউ কুলীন তো কেউ কৌলিন্য হারিয়েছে। প্রত্যেকেই অবশ্য নিজেদের বংশের কুলপঞ্জিকা তৈরি করে অপরের দিকে আঙুল তুলে জ্ঞানচর্চা করে যাচ্ছে। তবু শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদই ছিল বাঙালির মননচর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে। গতশতকের সাতের দশকে কয়েকটা ঘটনায় বাংলার সামাজিক পরিস্থিতির কিছুটা চারিত্রিক বদল ঘটে যায়। নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং সেই আন্দোলন দমনের জন্য বাঙালি তরুণ সমাজের ওপর ভয়াবহ, নৃশংস আক্রমণ। একের পর এক কাশীপুর, বরাহনগর, বারাসতের গণহত্যা। বেলেঘাটার খালপার কুখ্যাত হয়েছিল শুধু কিশোর তরুণদের গুলি করে খুন করার জন্য। হাজার হাজার কিশোর তরুণ রাজবন্দী। জেলখানায় অত্যাচার ক’রে পুলিশকর্মীরা যে স্যাডিস্টিক প্লেজার পেত, তা হয়ত জার্মানির কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পকেও লজ্জা দেবে। সেইসময়েই অর্চনা গুহ’র ওপর রুনু গুহনিয়োগীর কুখ্যাত পাশবিক অত্যাচার। ১৯৭৫সালে বিপ্লব হবে এমন ভবিষ্যৎবাণী অগ্রাহ্য করে ইতিহাস রচনা করল জরুরি অবস্থা। সমগ্র তরুণসমাজের মনের আড়ালে এক অদ্ভুত নৈরাশ্য বা বিষন্নতার জন্ম হল। যে জীবনানন্দ জীবিতকালে ছিলেন কার্যত অপরিচিত, সাতের দশকে তিনিই হঠাৎ প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। কেননা ততদিনে পাণ্ডুলিপি ধূসর হয়ে গেছে। পালক ঝরে গেছে।
“আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার:
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ; অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো!”
“কীএক ইশারা যেন মনে রেখে এক-
একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি;
অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হ’য়ে চ’লে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে:”
“ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো— ধীরে— পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগবো না জেনে—
কোনোদিন জাগবো না আমি— কোনোদিন আর।“
জেলখানায় অত্যাচার ক’রে পুলিশকর্মীরা যে স্যাডিস্টিক প্লেজার পেত, তা হয়ত জার্মানির কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পকেও লজ্জা দেবে। সেই সময়েই অর্চনা গুহ’র ওপর রুনু গুহনিয়োগীর কুখ্যাত পাশবিক অত্যাচার। ১৯৭৫সালে বিপ্লব হবে এমন ভবিষ্যৎবাণী অগ্রাহ্য করে ইতিহাস রচনা করল জরুরি অবস্থা। সমগ্র তরুণসমাজের মনের আড়ালে এক অদ্ভুত নৈরাশ্য বা বিষন্নতার জন্ম হল। যে জীবনানন্দ জীবিতকালে ছিলেন কার্যত অপরিচিত, সাতের দশকে তিনিই হঠাৎ প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। কেননা ততদিনে পাণ্ডুলিপি ধূসর হয়ে গেছে। পালক ঝরে গেছে।
পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাগের পর সবচেয়ে বড় ঘটনা নকশালবাড়ি। তার কর্মকাণ্ডের বিপূল বিস্তৃতির জন্য নয়, প্রভাবের জন্য। পঞ্চাশ বছর পরেও ‘নকশাল’ শব্দটার অনুররণ অন্যরকম। এত দ্রুত আর কোনো ঘটনা এপার বাংলার লক্ষ লক্ষ কৈশোর, যৌবনকে নাড়া দিতে পারে নি। ১৫~১৬ বছরের কিশোর হাতে বোমা তুলে নিয়েছিল বিশ্বাসে, নিঃশ্বাসে। নকশাল প্রজন্ম ছিল, ‘৪৭-এ বাংলাভাগের কয়েকবছর আগে পরে জন্মানো শিশুরা। তারও আগের প্রজন্ম, যারা শৈশবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠণ দেখেছে, কৈশোরে আজাদ হিন্দ ফৌজের দিল্লিচলোর আহ্বান শুনেছে, চল্লিশলক্ষ মানুষের “ফ্যান দাও” কান্না শুনেছে, কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন দেখে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, কলকাতা নোয়াখালির দাঙ্গা দেখেছে, শেষে বাংলা ভেঙে দু’টুকরো, উদ্বাস্তু আর গৃহহারাদের দল, তারাও ‘৪৭এর পর একইরকম বিষন্নতার বলি হয়েছিল। তারা উত্তমসুচিত্রার মধ্যে বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজেছে। তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই পরে নকশাল হয়ে গেল। এই যে নকশাল জেনারেশন, যাকে কোনো কোনো পণ্ডিত “মিডনাইটস চিল্ড্রেন জেনারেশন” বলে, তারা সাতের দশকে ধীরে ধীরে ঘর-সংসারে ঢুকে পড়লো। আর ঠিক সেইসময়ে, ১৯৭৪সালে, আমেরিকায় হেনরি কিসিঞ্জার এবং সিআইএ’র কর্মকর্তারা মিলে এক অভিনব পরিকল্পনা শুরু করল। ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীব্যাপি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্যতম টার্গেট ভারত। ইতিমধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটমি। এর পর এল পিল, কনডোম। সঞ্জয় গান্ধী উঠেপড়ে লাগল নাসবন্দী করতে। সাতের দশকেই এক বা দুই সন্তানের তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সংসারের আকার ছোট হতে শুরু করল। (এখন বাংলায় গড়পড়তা সংসারের সাইজ ৪.৫)। সিঙ্গল-চাইল্ড পরিবারের প্রাদুর্ভাব ঘটল। যে বাঙালির পূজনীয় বৌদ্ধিক পরিবারের চোদ্দটি সন্তানের একটি রবীন্দ্রনাথ, সেই বাঙালির পরবর্তি প্রজন্মে কনিষ্ঠ সন্তান মিসিং হয়ে গেল। ফলে তবলা-বাদক অথবা নকশাল পাওয়া হয়ে উঠল দুষ্কর। এই নবপ্রজন্মের নাম দেওয়া হয়েছে এক্স জেনারেশন। যারা নকশালবাড়ির কিছু আগে কিম্বা পরে জন্মেছে। আজ তারা ৪০~৫০। তারাই আজ ক্ষমতায়। তাদের স্মৃতিতে নকশাল নেই। কিন্তু মার্ক্সবাদ? না তাদের মননে চিন্তনের নেতৃত্বে মার্ক্সবাদও আর নেই। মার্ক্সবাদ তাদের কাছে এখন কাকু, আঙ্কল। রুশো, কান্ট, হেগেল, স্মিথের মতই আর একজন চিন্তাবিদ কার্লমার্ক্স। অর্থনীতি থেকে সমাজ সব বিষয়ে তার ভাবনাচিন্তার গুরুত্ব আছে কিন্তু এই প্রজন্ম তাদের জ্ঞানচর্চার নেতৃত্ব মার্ক্সবাদের হাতে সঁপে দিতে নারাজ। লক্ষ্য করে দেখবেন, পরবর্তীকালে অনেক নকশালপন্থীর সন্তানেরা কেউই তেমন আর রাজনীতিতে আসে নি। না-নকশাল কম্যুনিস্টদেরও না। বড়জোর কলেজে উঠে বাম ছাত্রসংগঠন। প্রচুর শ্লোগান, মিছিল, ধর্না, আড্ডা, গাঁজা, রাতজেগে পোস্টার, গোপন হাফ-হার্টেড শরীরী প্রেম, আর সারারাত প্রিন্সিপাল ঘেরাও, বাস। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিই পেশা? না না। এমনকি লেখাপড়া শেষ হয়ে যাবার পর কলেজের সেই মিছিল, ধর্না, আড্ডা, গাঁজা নস্টালজিয়ায় পরিণত হয়ে যায়। রাজনীতি থেকে বহুদূরে, কারিয়ারে মগ্ন তখন প্রাক্তন কম্যুনিস্টদের সন্তানেরা। সন্তানকে বিদেশে যাবার তাড়া দিচ্ছে সেই প্রাক্তনীরাই। হয়তো ব্যতিক্রম নিয়মের প্রমাণ হয়ে আছে। এমনটাতো হবার কথা ছিলনা। বাংলায় পেশার ক্ষেত্রে বংশপরম্পরার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। চিকিৎসকের ছেলে চিকিৎসক হবে, বিচারকের ছেলে আইনিজীবী বা বিচারক। অভিনেতার সন্তান হবে অভিনেতা, চলচিত্র পরিচালকের ছেলে পরিচালক। এরকম হামেশাই দেখি আমরা। আমরা বলি রক্তের ধারা। তাহলে কম্যুনিস্ট রাজনীতি বা বিপ্লবী রাজনীতি যিনি পেশা করেছিলেন, তার সন্তান কেন রাজনীতি বা বিপ্লবের পেশায় যায় না? খোঁজ নিয়ে দেখবেন, প্রাক্তন বিপ্লবীর সন্তান হয়তো মুম্বাই, বাঙালোর অথবা লস এঞ্জেলসে। প্রাক্তন কম্যনিস্টের সন্তান অধ্যাপক বা স্কুল শিক্ষক। কেন? (না কেন প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ কেন’র আড়ালে যেমন গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ আছে, তেমনি আছে সন্দেহ। ডাউট অর্থে সন্দেহ। সন্দেহ খুবই বিপজ্জনক।)
ঠিক আছে, মার্ক্সবাদ না হয় কাকা। তাহলে, এই এক্স জেনারেশনের দাদা কে হল? তার আগে ওই সাতের দশকের আর একটা বড় পরিবর্তন বুঝে নেওয়া দরকার। ১৯৭৭সালে প্রথম বামফ্রণ্ট সরকার হল। কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় এলো। বা, বলা যায়, মার্ক্সবাদ ক্ষমতায় এলো। বাংলায় প্রথম একটি রেজিমেন্টেড সরকার। ফলে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষমতার নোডাল পয়েন্টে অবস্থানের জন্য এতদিন যে না-বলা যোগ্যতাগুলো মাস্ট ছিল, বর্ণপরিচয়, বংশপরিচয়, লেখাপড়া, তারসঙ্গে আরও একটি পরিচয় যুক্ত হল। রাজনৈতিক অবস্থান। বাম তো? আচ্ছা বাম না হলেও চলবে কিন্তু না-বাম হওয়া যাবে না। ঠিক এইসময়েই চিন্তনজগতে এক নতুন দাদার দাদাগিরি শুরু হল। উত্তর-আধুনিকতা। যার মোদ্দা কথা হল (শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায়কে নকল করে বলছি) মোদ্দা কথা বলে কিছু নেই। ঠিক মার্ক্সবাদের উল্টো মেরুর অবস্থান। গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ বলে কিছু হয় না। খ্রিষ্টানধর্মের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ ছিল গড, ইসলামের আল্লাহ, উপনিষদের পরম ব্রহ্ম। সব বোগাস। মার্ক্সবাদ বলেছিল এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই পরস্পর যুক্ত। অর্থনীতি, রাজনীতি থেকে এমনকি ইতিহাস-রচনার কায়দা কিম্বা ভূগোলও একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মার্ক্সবাদ হল বিশ্ববীক্ষা। সমস্ত কিছুই দ্বন্দ্বমূলক এবং মায়া বা ভাবের কোনও জায়গা নেই, বস্তুবাদই শেষ কথা। বোগাস। সবই মাইক্রো, মাইক্রো, ন্যানো। ম্যাক্রো বলে কিছু হয়না। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার কোনও যোগাযোগ নেই। প্রেক্ষিত আবার কী? প্রত্যেকটা প্রশ্নকে আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন করে দেখতে হবে। কোনও মোদ্দা নেই। কেউ কেউ হয়তো কিছু এদিক ওদিক থেকে তথ্য এনে বোঝাতে চাইবেন, উত্তর-আধুনিকতা ঠিক এরকমটা নয়, কিন্তু এইরকমই। মেটা ন্যারেটিভ হয় না। কিন্তু “মোদ্দা কথা, মোদ্দা কথা বলে কিছু হয়না” বললে, এই মোদ্দাটাও তো নাকচ হয়ে যায়। (এটা অনেকটা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু যদি, গড/আল্লাহ/ভগবানের সৃজন হয়, তাহলে গড/আল্লাহ/ভগবান কে সৃজন করল? উত্তর, মানুষ। তেমনই ওই, “মোদ্দাকথা হয়না”, এই মোদ্দাও তৈরি কিছু চিন্তকের, যাদের উত্তর-আধুনিক বলা হয়।) কিছু শব্দ আশি, নব্বইয়ের দশকে তরুণ জ্ঞানচর্চক মহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ডিসকোর্স, ন্যারেটিভ, অনির্ণেয়তা (আনডিটারমেনেবিল), টুকরো টুকরো (ফ্র্যাগমেন্টেশন), ছড়িয়ে দেওয়া (ডিসেমিনেশন), ছলনা (সিমুলেশন), বিকেন্দ্রীকরণ (ডিসেন্টারিং), বহুমাত্রিকতা (প্লুর্যালিজম) ইত্যাদি। দেরিদা, ফুকো, অ্যালথুজার, জিজেক, লয়ত্যর, রনজিত গুহ বিখ্যাত সব পোস্ট-মডার্নিস্ট। এখানে তারা জনপ্রিয় হয়ে উঠল রাতারাতি। গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ, প্রেক্ষিত টেক্ষিত ভোগে চলে গেল।
এইখানে একটা মজার তথ্য জানাই। এই উত্তর আধুনিকতার সূত্রপাত প্রথম হয় সাহিত্যে। বিশেষ করে কবিতায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইওরোপে ব্যাপক হতাশা বিষণ্ণতা জন্ম নেয়। তার প্রভাব পরে তাদের সাহিত্য ভাবনায়। একদিকে সেই ভাবনা এসে বাংলায় পৌঁছল, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনোর মধ্যে দিয়ে। প্রায় সমসময়ে এসে হাজির মার্ক্সবাদ। রুশ বিপ্লবের প্রেরণায়। স্কুল-ছুট নজরুল যুদ্ধ থেকে ফিরে মুজফফর আহমেদের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ায় যুক্ত হয়ে পড়ল। আর তারই সমবয়সি অপর এক তরুণ ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করে ইওরোপিয় পোস্ট মডার্ন ভাবনায় প্রাণিত হয়ে কবিতা চর্চা শুরু করল। জীবনানন্দ। বাংলা কবিতার ইতিহাসটা মজার। একশ বছরই দেখা যাক। নজরুল, জসীমুদ্দিন, সত্যেনদত্তের পাশাপাশি জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণুদে। দুটো ভিন্ন ধারা। দ্বিতীয় ধারার সবাই ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল। সুকান্ত, সুভাষ মাথাচাড়া দিয়েও ক্ষীণ হয়ে গেল। বুদ্ধদেব জীবনানন্দ ধারা চলে এল শক্তি, সুনীল, বিনয়ে। যারা অবশ্যই উত্তর-আধুনিক। বিনয়ের ব্যর্থ প্রেমও উত্তর-আধুনিক। গায়ত্রী স্পিভাক একজন নামি উত্তর আধুনিকতাবাদী। তার সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ চিন্তার জগতে বিশাল প্রভাব ফেলেছে।
ইতিমধ্যে আরও এক নতুন প্রজন্ম এসে হাজির। যাদের মিলেনিয়াম জেনারেশন বলে। যারা এখনও তিরিশ পেরোয় নি। যারা লিটল ম্যাগ নয়, ওয়েবম্যাগ করে। নাটক, সিনেমা নয়, শর্ট-ফিল্ম। এদের কাছে মার্ক্সবাদ গ্র্যান্ডফাদার। গ্র্যান্ডফাদার মানে ইতিহাস। অনেকটা মার্ক্সবাদীর কাছে উনিশশতকের ব্রাহ্মভাবনার মতো গ্র্যান্ডফাদার। পোস্ট-মডার্ন ভাবনাচিন্তাও তাদের কাছে প্রায় কাকা গোছের হতে শুরু করেছে। তারাও কিন্তু গ্র্যান্ড ন্যারেটিভকে বুড়ো আঙুল দেখায়। নেগেশন অফ নেগেশন এখানে কাজে লাগল না। আর ঠিক এই আবহেই এসে হাজির কোভিড। কোভিডের হাত ধরে নিউ-নর্মাল।
যাহ বাবা! রচনাকারের কি মাথার গণ্ডগোল আছে? প্রজন্ম, মেটান্যারেটিভ, পোস্টমডার্নিজম থেকে হঠাৎ একলাফে কোভিড? নিউ নর্মাল? এ যেন, আমি এখানে কফিহাউসে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লাম, একসপ্তাহ পরে আটলান্টিকে সামুদ্রিক ঝড় হয়ে গেল, এইরকম কার্য-কারণ সম্পর্কের যুক্তি। তো এই যুক্তিও কিন্তু চিন্তকেরা নাকচ করে দেয়নি। তারা বলছে, হ্যাঁ হতে পারে। কফি হাউসের ধোঁয়ায় আটলান্টিকে ঝড় উঠতে পারে। একে বলে কেওস থিওরি।
সবই মাইক্রো, মাইক্রো, ন্যানো। ম্যাক্রো বলে কিছু হয়না। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার কোনও যোগাযোগ নেই। প্রেক্ষিত আবার কী? প্রত্যেকটা প্রশ্নকে আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন করে দেখতে হবে। কোনও মোদ্দা নেই। কেউ কেউ হয়তো কিছু এদিক ওদিক থেকে তথ্য এনে বোঝাতে চাইবেন, উত্তর-আধুনিকতা ঠিক এরকমটা নয়, কিন্তু এইরকমই। মেটা ন্যারেটিভ হয় না। কিন্তু “মোদ্দা কথা, মোদ্দা কথা বলে কিছু হয়না” বললে, এই মোদ্দাটাও তো নাকচ হয়ে যায়। (এটা অনেকটা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু যদি, গড/আল্লাহ/ভগবানের সৃজন হয়, তাহলে গড/আল্লাহ/ভগবান কে সৃজন করল? উত্তর, মানুষ। তেমনই ওই, “মোদ্দাকথা হয় না”, এই মোদ্দাও তৈরি কিছু চিন্তকের, যাদের উত্তর-আধুনিক বলা হয়।) কিছু শব্দ আশি, নব্বইয়ের দশকে তরুণ জ্ঞানচর্চক মহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ডিসকোর্স, ন্যারেটিভ, অনির্ণেয়তা (আনডিটারমেনেবিল), টুকরো টুকরো (ফ্র্যাগমেন্টেশন), ছড়িয়ে দেওয়া (ডিসেমিনেশন), ছলনা (সিমুলেশন), বিকেন্দ্রীকরণ (ডিসেন্টারিং), বহুমাত্রিকতা (প্লুর্যালিজম) ইত্যাদি।
কিন্তু আমি ভাই, গ্র্যান্ডফাদারের দিকে ঝুঁকে আছি। মেটান্যারেটিভ বা প্রেক্ষিত আমি দেখবই। বার্ডস আই ভিউ। এই যে এতক্ষণ ধরে পশ্চিমবাংলার চিন্তকদের ভাবনার জগতের বিবর্তনের একটা হাফ-উইট ন্যারেটিভ তৈরি করলাম, তার মাইক্রো ন্যানোতে ঢুকে পড়ার আদৌ ইচ্ছে এবং ক্ষমতা আমার নেই। নেশা কাটাতে পারছিনা। পারছি না কারণ, গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ বাদ দিয়ে কিছু উপলব্ধি করা অসম্ভব।
কারণ গত পঞ্চাশ বছরের আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতির বিবর্তন, আর তারসঙ্গে বাঙালির চিন্তনজগতের পরিবর্তনের যোগাযোগটা বোঝা খুব জরুরি। নাহলে আমরা নিউ-নর্ম্যালে পৌঁছতে পারব না।
গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ এবং ন্যানো ন্যারেটিভ দুইই সমান সত্য। কিন্তু সারা পৃথিবীর চিন্তন জগতের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের দায়িত্ব আজ নিয়ে নিয়েছে হাতে গোণা কিছু কর্পোরেটদের কনগ্লোমারেট। একটা মোটাদাগের উদাহরণ দেই। ধরা যাক, কোনও একটা বিষয়ে মানুষ কী ভাবছে, সেই নিয়ে সমীক্ষা। এই মুহূর্তে আমজনতা ঠিক কী ধরনের খবর দেখতে-শুনতে চায়? দর্শকের পালস বোঝার জন্য সার্ভে বা সমীক্ষা। বিশেষ নিয়ম মেনে সেই সমীক্ষা চলল। তো এতে পাওয়া গেল টিআরপি। টোট্যাল রেস্পন্স প্রোফাইল। কীভাবে? র্যান্ডম স্যামপ্লিং করে বেশকিছু টিভিসেটে পিপলস মিটার বসানো আছে। কিন্তু সারা দেশের সমস্ত টিভির ০.০০২% এর বেশি নয়। অথচ ফেসবুকে সমস্ত গ্রাণ্ড ডেটা মার্ক জুকেরবার্গের কাছে আছে। গুগলের কাছে আছে কোন প্রোগ্রামগুলো কত লোক দেখেছে কে বা কারা দেখেছে, কতক্ষণ দেখেছে দর্শকদের সব তথ্য এমনকি কোথায় বসে দেখেছে তাও। গ্র্যান্ড ডেটা। আর এই গ্রাণ্ড ডেটা থেকে গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের দায়িত্ব গুগলের, ফেসবুকের। আপনার আমার জন্য ঐ ন্যানো। ২০১৬সালে হিলারি বনাম ট্রাম্পের মল্লযুদ্ধের সময়, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া থেকে সকলেই ধরে নিয়েছিল হিলারিই আসছে। কিন্তু এল ট্রাম্প। আসলে সকলে সোশ্যাল মিডিয়ায় কে কী বলছে লিখছে লক্ষ্য করেছে। কিছু না বলে কে কী লাইক করছে তা লক্ষ্য করেনি। বলা আর লাইক করার তফাৎ। আলোচনায় আপনি কিছু বলছেন না। কিন্তু অন্য যারা বলছে তার যে প্রতিক্রিয়া আপনার চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে সেটুকুও যথেষ্ঠ আপনার মতামত বুঝতে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও সেইটে লাইকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। আপনার পছন্দও বিগডেটা হয়ে এখন ওই ডাইনোসরদের হাতের মুঠোয়। গ্র্যাণ্ডন্যারেটিভ তাদের প্রেরোগেটিভ। আপনি ন্যানোতে থাকুন। এই ডাইনোসরদের দেশে দেশে খুদে খুদে প্রতিনিধি আছে। কফিহাউস কিম্বা প্রেসির ল্যাব, জেএনইউর সমাজতত্ত্বের গবেষকের দায়িত্ব শুধু তাদের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যানো ডিসকোর্সের। তারা বিশেষ বিষয়ের বিশেষ কোনও কিছু নিয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করবে। তাদের কোনও অধিকার নেই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের ওপর খবরদারি করার। কড়া নজরদারি চলছে। প্রশ্ন হল এই অবস্থায় আমরা পৌঁছলাম কী করে?
অর্থনীতি দিয়ে এই গ্র্যান্ড-ন্যানোর যুদ্ধ বোঝার চেষ্টা করা যাক। এককালে এই বাংলা ছিল তাঁতের জন্য বিখ্যাত। এই শিল্পের সঙ্গে কারা যুক্ত ছিল? তুলো চাষি। ধুনুচি। তুলো থেকে সুতো কাটার কাটারী। চরকা তৈরির শিল্পী। তাঁতি। স্থানীয় বণিক। নৌকা। নৌকা বানানোর কারিগর। মাঝি। এরপর হাট। হাটে বিদেশি বণিক। সেও জাহাজে এসেছে, হয়তো সুদুর আরব থেকে। জাহাজের মাঝিমাল্লা। জাহাজ তৈরির কারিগর। অ্যাবিসিনিয়া হয়ে জাহাজ পৌঁছে গেল মক্কার বন্দরে। সেখান থেকে উটে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর একদল বণিক। ধীরে ধীরে পৌঁছে যাচ্ছে ইউরোপ। এই বাণিজ্যে যেসব কারিগর বা বণিকেরা যুক্ত তারা সবাই কিন্তু তাদের মত করে এই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ জানত। কোনো রহস্য লুকিয়ে ছিলনা। তাদের এই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ তৈরি হোতো বংশানুক্রমে। সেইমতো তারা নিজেদের কাজ ঠিকঠাক করত। করতে করতে পরিবর্তন তাদের নজরে পরত। তার নিজের কাজে অবশ্যই দক্ষতা ছিল। কিন্তু সে শুধু সুতো কাটা বা নৌকার হাল ধরার বিশেষজ্ঞ নয়। প্রেক্ষিত তার জানা। সে মাইনে করা স্পেশ্যালিস্ট নয়।
এরপর যখন ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল ক্যাপিট্যালের জমানা তৈরি হল, তাঁত ধ্বংস করা হল। সবটাই বিশাল একটা শেডের নিচে কারখানায় তৈরি হয়ে ফিনিসড গুড হয়ে আসছে। এইখানে মজদুরদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষজ্ঞ তৈরি করা হয়। সমস্ত প্রোসেসটা অর্থাৎ গ্র্যান্ড ন্যারেটিভটা তার মননের আড়ালে রেখে শুধু তার নিজের কাজটুকুর দক্ষতা। বিশাল শেডের নিচে বিশাল মেশিনের মধ্যে দিয়ে লোহার পাতের মত কিছু একটা যাচ্ছে একেবারে ঘড়ি ধরে। কান ঝালাপালা করা আওয়াজ। কাজটা হল, প্রতি তিন সেকেন্ড অন্তর সেই গতিশীল পাতের ওপর লাগানো স্ক্রু টাইট করা। পিঠ চুলকোলেও উপায় নেই, চুলকোতে গিয়ে একটা স্ক্রু যদি মিস হয়ে যায়, তাহলেই মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে। কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। মডার্ন টাইমসে চার্লিকে মনে আছে? তাকে কি করতে হবে সে জানে, কিভাবে করতে হবে তাও জানে, কিন্তু কেন করতে হবে জানেনা। এই কেন’র গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ জানে শুধু পুঁজি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুঁজি। চার্লিকে ওই স্ক্রুয়ের ন্যানো বিশেষজ্ঞ হয়েই থাকতে হবে। ছুটির পরেও বেচারার হাতের টুইস্ট বন্ধ হতে চায় না। স্ক্রু টাইটের স্পেশ্যালাইজেশন যেন তার শরীরের অঙ্গই হয়ে গেছে।
ম্যাক্রো নজরদারী চালাচ্ছে ওই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দশ-বারোটা কর্পোরেট। একসময় কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিও চালু হয়ে গেল। (সিএসআর) । কর্পোরেটদেরও সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি? পিসিমার গোঁফ। আর এইসময়েই পোস্ট-মডার্নিজম জনপ্রিয় হল। প্রাক্তন মার্ক্সবাদী অ্যালথুজারের হাত ধরে।
ইনডাস্ট্রিয়াল পুঁজির সঙ্গে টক্কর দিতে এসে গেল ফিনান্স ক্যাপিট্যাল বা লগ্নিপুঁজি। এমন সময় আচমকা তৈরি হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেখানে অন্যধরনের এক অর্থনীতির এক্সপেরিমেন্ট শুরু হল। রাজনীতি অথবা অর্থনীতির গ্র্যান্ড ন্যারেটিভে মজদুরদের অ্যাক্সেস দেওয়া হল কিনা বলতে পারি না। কিন্তু পুঁজির ঠিকাদারদের রীতিমত দুশ্চিন্তা শুরু হল। তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেল। খুব একটা সুবিধে হলনা। ইতিমধ্যে পুঁজির ওপর খবরদারির ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে চলে গেছে আমেরিকার হাতে। এমন সময় বিনামেঘে বজ্রপাত। ১৯২৯সালে ওয়াল স্ট্রিটে স্টক এক্সচেঞ্জ ক্র্যাস। শুরু হয়ে গেল গ্রেট ডিপ্রেশন। কেইনস একটা প্রেসক্রিপশন দিলেন। এতদিনের মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এই প্রথম রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। বাজারে জোগান বেশি, চাহিদা নেই। চাহিদা ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে। মানুষের হাতে টাকা নেই। টাকা পৌঁছে দিতে হবে। কে দেবে? রাষ্ট্র। দরকার হলে টাকা ছাপিয়ে। অকারণ পুকুর খনন করে সেই পুকুর আবার ভরাট করাও। মজদুরদের হাতে টাকা তুলে দাও। রাষ্ট্র একটু চমকে উঠেছিল। এতদিন তো রাষ্ট্র শুধু খাজনা আদায় করত। এখন কিনা বাজারে হস্তক্ষেপ করতে হবে? উপায় নেই, করতেই হবে। পুঁজির স্বার্থেই। কিন্তু এ জিনিস কতকাল চলবে! কৃত্রিম চাহিদার পরিবর্তে সত্যিকারের চাহিদা কীভাবে তৈরি হবে? হ্যাঁ, একটা উপায় আছে। যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই অস্ত্রশস্ত্র। বিশাল আকারের ওয়ার ইকনমি। লাগ লাগ লাগ। লেগে গেল যুদ্ধ। দুই পক্ষ। মিত্রশক্তি বনাম অক্ষশক্তি। জার্মানি সোভিয়েত আক্রমণ করে বসল। আহা।
এবার এই মার্ক্সবাদের সলিল সমাধি অবধারিত। টানা ছয় বছর যুদ্ধ চলল। ঘায়েল হয়ে থামল শেষে। প্রায় ৬ কোটি মানুষের মৃত্যু। তার সিংহভাগ ইয়োরোপের। সবচেয়ে বেশি সৈনিক মারা গেল সোভিয়েতের। কিন্তু মার্ক্সবাদতো নির্মূল হলই না, উলটে পুর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকা মার্ক্সবাদের আওতায় চলে গেল। এমনকি জার্মানিও দুটুকরো হয়ে গেল। ওদিকে এশিয়ায় ভিয়েতনাম কোরিয়া আধাআধি হয়ে উত্তর দিকটা মার্ক্সবাদি হয়ে গেল। কয়েকবছর পরেই চীনও কম্যুনিস্ট হয়ে গেল। কেলেঙ্কারি। তাহলে কি পুঁজির মৃত্যু অবধারিত? ভাবতে বসল পুঁজি। ইতিমধ্যে ফিনান্স ক্যাপিট্যাল নেতৃত্বে এসে গেছে। শিল্পপুঁজি তারই অধীনস্থ। শিল্পপুঁজির দরকার ছিল সরাসরি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ। ফিনান্স পুঁজির তা দরকার নেই। তাই প্রায় সমস্ত উপনিবেশের ছুটি হয়ে গেল। এখন থেকে তারা স্বাধীন। তারা ফিনান্স পুঁজির বাজার। (মার্ক্সবাদি কাকার ভাষায় নয়া-উপনিবেশ।) আন্তর্জাতিক এই ফিনান্স পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটার পর একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গজিয়ে উঠল। লিগ অফ নেশন্স হয়ে গেল ইউনাইটেড নেশন্স। লীগ নয়, ইউনাইটেড। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইনটারন্যাশানাল মনেটরি ফাণ্ড ইত্যাদি। ১৯৭১সালে গজিয়ে উঠল ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম।
অর্থনীতি? পুঁজির অস্তিত্ব তো সংকটে। যুদ্ধই চালিয়ে যেতে হবে। কোরিয়া ভিয়েতনামে সুবিধে হচ্ছে না। কোল্ড ওয়ারের যুগ শুরু হল। কিন্তু আর একটা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধকে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে যাতে ওয়ার ইকনমি চালিয়ে যাওয়া যায়। ভিয়েতনাম কোরিয়া শেষ হল। শুরু হল ‘জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ বা ‘ওয়ার অন টেরর’। সাদ্দাম থেকে খোমেইনি, আলকায়দা থেকে তালিবান সবই আমেরিকার হাতে তৈরি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু হল। জঙ্গি। জঙ্গি। টেরর একটা ইজমে পরিণত হল আম্রেরিকার বদৌলতে। সারা পৃথিবী জুড়ে তরুণ প্রজন্মের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছিল মার্ক্সবাদ। স্তালিনের প্রশ্রয়। পরে মাওসেতুং, হোচিমিনের প্রশ্রয়। এরমধ্যেই একেবারে ঘাড়ের ওপর কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রো মার্ক্সবাদ নিয়ে এসে হাজির। সঙ্গে চে গুয়েভারা নামে এক দাড়ি-ওয়ালা লাতিন আমেরিকায় গিয়ে বিপ্লব ফেরী করতে শুরু করল। যাক, তাকে শেষ অব্দি নিকেষ করা গেল। কিন্তু তারুণ্যের এই উন্মাদনা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? সব আঠারো-উনিশ বুকে চে গুয়েভারার টুপি-দাড়িওয়ালা গেঞ্জি পরে ঘুরছে। বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।
আপনার পছন্দও বিগডেটা হয়ে এখন ওই ডাইনোসরদের হাতের মুঠোয়। গ্র্যাণ্ডন্যারেটিভ তাদের প্রেরোগেটিভ। আপনি ন্যানোতে থাকুন। এই ডাইনোসরদের দেশে দেশে খুদে খুদে প্রতিনিধি আছে। কফিহাউস কিম্বা প্রেসির ল্যাব, জেএনইউর সমাজতত্ত্বের গবেষকের দায়িত্ব শুধু তাদের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যানো ডিসকোর্সের। তারা বিশেষ বিষয়ের বিশেষ কোনও কিছু নিয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করবে। তাদের কোনও অধিকার নেই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের ওপর খবরদারি করার। কড়া নজরদারি চলছে।
মনস্তত্ত্ববিদেরা জানালেন, আসলে আঠারো বছর বয়সটাই দুঃসহ। স্পর্ধায় মাথা তোলবার ঝুঁকি নিতে চায়। এককালে গ্রিসে এলিট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা করতে উৎসাহ দেওয়া হত। কার্যত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সিলেবাসের অঙ্গ ছিল। এই বয়স মানুষের জন্য কিছু করতে চায়, প্রতিষ্ঠানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়। যদি এই প্রতিবাদ ইত্যাদিকে সংগোপনে প্রাতিষ্ঠানিক করে ফেলা যায়, তাতে আখেরে রাষ্ট্রের লাভ। মার্ক্সবাদ তো তরুণদের এই রুখে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটাকেই উস্কে দেয়। এই ইচ্ছেটাকেই দখল করতে হবে।
তাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী একটা কনসেপ্ট বাজারে এল। সরকারের বাইরে মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ। এনজিও। নন-গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন। টাকা? আরেহ ভাই, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। এই মুহূর্তে ভারতে রেজিস্টার্ড এনজিও তিরিশ লক্ষ। সকলেই মানুষের জন্য কাজ করছে। তরুণ প্রজন্মের ইচ্ছা পুরণের কী সুন্দর ব্যবস্থা।
পথশিশুদের নিয়ে হোক অথবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠিই হোক, কাজ হচ্ছে। আবার খোঁজ নিয়ে দেখুন, নানা রিসার্চ সংস্থা, (আসলে এনজিও) নানা ধরনের গভীর গবেষণামূলক কাজ করে চলেছে। জ্ঞানচর্চা। মানুষের জন্য। কিন্তু সমস্ত কাজ মাইক্রো লেভেলে, ন্যানো লেভেলে। ম্যাক্রো নজরদারী চালাচ্ছে ওই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দশ-বারোটা কর্পোরেট। একসময় কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিও চালু হয়ে গেল। (সিএসআর) । কর্পোরেটদেরও সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি? পিসিমার গোঁফ। আর এইসময়েই পোস্ট-মডার্নিজম জনপ্রিয় হল। প্রাক্তন মার্ক্সবাদী অ্যালথুজারের হাত ধরে।
ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, রকফেলার ফাউণ্ডেশন, গেটস ফাউন্ডেশন। হাজার হাজার ফাউন্ডেশন। তারা সামাজিক উপকারের জন্য টাকা দেয়। কেন?
ওহ! আবার সেই ‘কেন’।
আসলে যে কাজটা এককালে শুধু মিডিয়া দিয়ে হত (চোমস্কির ম্যানুফ্যাকচারিং কন্সেন্ট), আজকাল আর তা হচ্ছে না। নতুন একদল মিডিয়া পারসন চাই। তারা হল বিশেষজ্ঞ। স্পেশ্যালিস্ট। তাদের কথার মর্যাদাই আলাদা। বিশেষজ্ঞ ম্যানুফ্যাকচারিংএর জন্য, নতুন নতুন এনজিও হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ডিসিপ্লিনে নানা আকর্ষণীয় প্রোজেক্ট হবে। তারা ছোট্ট একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে যাবে। সেটাই হয়ে উঠবে তাদের পৃথিবী। মধ্যপ্রদেশের বিশেষ একটি ট্রাইবের ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী গবেষণা। নর্মদা নদী বাঁধের জন্য পরিবেশ দুষণ। হুসেন শাহর সময়ে বাংলা-ভাষার বিবর্তন কীভাবে হল। ছোট ছোট গর্ত। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আকাশ দেখার সময় তাদের নেই। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। আজ তারাই মানুষের কনসেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিংএর দায়িত্বে। মানুষ মনে করে মিডিয়া তো ব্যবসা করে। রাজনীতির লোকেরা রাজনৈতিক কথা বলে। তাদের কথা সবসময়ে ধরতে নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা? তারা রীতিমত গবেষণা করে অনুসন্ধান করে আমাদের ভালোর জন্যই তো বলছে। মিডিয়া তো ব্যবসা। বিজ্ঞাপন, টিজ্ঞাপন দিয়ে অনেক টাকা দিয়ে ওই ওরা কিনে নেয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা? তারাতো কষ্ট করে গবেষণা করে। কজন জানে এই গবেষণার পয়সা কোত্থেকে আসে? এমআইটিতে অতিথি বক্তা হয়ে যাবার ব্যবস্থা কারা করে দেয়?
অর্থনীতির ক্ষেত্রে আবার ধাক্কা। ২০০৮সালে আবার ডিপ্রেশন। এবার ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রি কুপোপাত। মোটামুটি বিশ শতকের সাতের দশক থেকেই পুঁজির অসুখবিসুখের ডাক্তার বদলে গেছে। কেইনসিয়ান হোমিওপ্যাথি ছেড়ে ফ্রিডম্যানের অ্যালোপ্যাথি। চাহিদা আর ম্যানুফ্যাকচারিং নয়। বাজারকে আবার স্বাধীনতা দিয়ে দাও। ট্রিকল ডাউন থিওরি। আমাদের এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল ১৯৯১-৯২। নরসিমহা রাওয়ের সরকার, মনমোহন সিংএর হাত ধরে এলপিজি শুরু করল। লিবারালিজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন। সংখ্যালঘু সরকারকে ঘুরিয়ে বাঁচানোর দায়িত্ব নিল বামফ্রণ্ট। তারা অবশ্য পথসভা আর নানাধরনের বিতর্কসভা আয়োজন করে এলপিজির বিরোধিতার নাটক চালিয়েছিল। আজও ভায়া মনমোহন হয়ে নির্মলার হাত ধরে প্রায় একই ট্রিকল ডাউন অর্থনীতি চলছে। শুধু পদ্ধতির ক্ষেত্রে মারাত্মক অথারিটেরিয়ান বা ফ্যাসিবাদি স্টাইল। ওদিকে সোভিয়েত ভেঙ্গে খানখান। কম্যুনিজম শেষ। চীনে অন্য ধরনের পুঁজির বিকাশ শুরু হল। শুধু জ জঙ্গিদের নাম করে মুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তো অর্থনীতি টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ফিনান্স ক্যাপিট্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিট্যালকে বিশ্বব্যাপি জালে আটকে দিয়েছে এক বিচিত্র নেট। অনেকটা যেমন সমুদ্রে হাঙ্গর আছে, আবার তিমিও আছে, কিন্তু তাদের অজান্তেই তারা একটা জালে আটকে গেছে। নেট। সমস্ত শক্তি দিয়েও তারা বেরোতে পারছে না। সমুদ্র বাজারে তাদের যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, তা আর নেই। এই নেটের দড়ি যাদের হাতে, তারাই এখন ওই হাঙ্গর তিমিদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। এই নেট তৈরি করেছে নতুন এক পুঁজি। ডিজিট্যাল পুঁজি। ক্রমশঃ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণও তারা হাতে নিতে চাইছে। এমনকি রাষ্ট্রের একছত্র অধিকার মুদ্রাব্যবস্থা, সেটাও তারা তাদের আওতায় আনবে। ক্রিপ্টোকারেন্সি। তারাই রাষ্ট্র। সর্বোচ্চ স্তরে গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজন ইত্যাদি ডাইনোসেয়াররাই এবার পৃথিবী শাসন করবে সরাসরি। এই জঙ্গলে জ্ঞানচর্চার জগতেও তাই গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ ডাইনোসররা ছোট ছোট মৌমাছিদের জ্ঞানচর্চার চাক বাঁধতে সাহায্য করবে। সেখানে যে মধু সঞ্চিত হবে তা চলে যাবে ওই ডাইনসরদের কাছে। ফাইনান্স ক্যাপিট্যালের ওপরে উঠে আসছে ফিলানথ্রোক্যাপিট্যাল। নতুন যুদ্ধ চাই। আর জঙ্গি নয়, ওটা পুরনো হয়ে গেছে। টুকটাক খুচখাচ চলতেই পারে। কিন্তু নতুন এক যুদ্ধের জন্য শত্রু চাই। ভাইরাস। সেই যুদ্ধ অসামান্য দক্ষতায় শুরু হয়ে গেছে। আমরা ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রামের মত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছোট ছোট গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে নানা গবেষণামূলক কাজ করে যাব। এইসব জ্ঞানচর্চকদের জ্ঞানপাপী করে তুলতে হবে। বাংলা থিয়েটার দেখুন। কেন্দ্র, রাজ্য উভয় সরকারই বিপূল আর্থিক সাহায্য দেয়। কেউ কেউ গাড়িবাড়ি করে ফেলেছে। গোবরডাঙ্গা থিয়েটার-নগরী হয়ে উঠছে। অজস্র খুদে খুদে প্রতিভা। গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তাই বাংলায় অসমে যখন গুলি করে খুন করে বুকের ওপর উঠে সরকারী কর্মী ভারতনাট্যম নাচে আমরা কেউ কেউ একটু একটু প্রতিবাদ করি। কেউ আবার ভারতনাট্যমের ভারতেই খুশি। খেয়াল করে দেখবেন, এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চেয়ে উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের চরিত্র নিয়ে হৈ হৈ অনেক বেশি। ১৯৭১সালে তৈরি ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের সিইও ক্লাউস সোয়াব বলেছেন, এই নিউ নর্ম্যালে গিয়ে মানিয়ে নিতে আমরা বাধ্য। তিনি বলেছেন, অর্থনীতিতে একদিকে বিশাল হাঙ্গর যেমন থাকবে, উল্টোদিকে থাকবে শুধু চারাপোনা। মাঝখানটা সাফ। তেমনি জ্ঞানচর্চাতেও একদিকে গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ হাঙ্গর থাকবে। উল্টোদিকে চারাপোনা ক্ষুদে ক্ষুদে মৌমাছির চাক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “… একটা অত্যন্ত পুরনো কথার নতুন প্রমাণ জুটল এই যে, কারো সঙ্গে কারো বা মতের মিল হয়, কারো সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ-বিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তারা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তারা ছাঁটাই কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই-কাঠি বের করে আনেন।“
হ্যাঁ, মৌমাছিরা যে মধু রচনায় সক্ষম এতেও কোন সন্দেহ নেই। দেশলাই কাঠিতে যে আগুন জ্বলে তাও একশভাগ সত্যি। রবীন্দ্রনাথের সেই সমাজ-বিধাতার দল এখন আন্তর্জাতিক ডিজিট্যাল কর্পোরেটদের সমবায়। (হেহে। আমিও উদ্ধৃতি দিলাম। জাতে উঠলাম কি?)
রবীন্দ্রনাথ বলছেন “গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরি করতে গেলে সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁটতে হয়।“
এই ছাঁটা গাছেরাই আজকের বিশেষজ্ঞর দল। আমরা বাংলার জ্ঞানচর্চকেরা মেনে নিয়েছি।
কিন্তু কেন?
আঃহ। আবার সেই কেন!
বুঝতে হবে বাঙালির বুকের টিসার্টের ওপরের চে গুয়েভারার ছবি কবে মুছে গেছে।
সেখানে এখন বড় বড় করে লেখা:
কোনোদিন জাগবো না আমি— কোনোদিন আর।
অরূপশঙ্কর মৈত্র
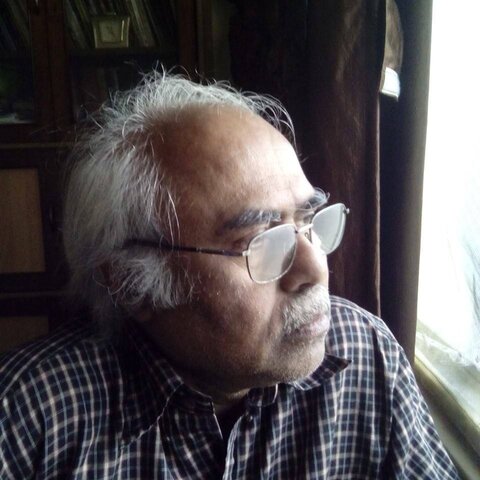
নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও লেখক। নিবাস: দক্ষিণ কলকাতা।

