
।। জেসমিন নাহার ।।
“বড় সাহিত্যিকরা কেন ‘গণদেবতা’ পড়তে বলেন, এর একটা কারণ আমি বুঝি এই অর্থে যে পুরাণের দেবতাদের নয়, সাধারণ সামাজিক মানুষই একালের দেবতা— তারাশঙ্কর সেটা আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। চিন্তাটা ভাল লেগেছে আমার, কারন এতো গভীরে ভাবতে পারাটা সাহিত্যিক মুন্সিয়ানার লক্ষণ। তারাশঙ্করের (গণ)দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব না। কিন্তু তারপরও দেবতাদের প্রলয় ও সৃষ্টির ভূমিকার মতো মানুষের সমাজে ভাঙাগড়া আছে, একদিকে সমাজ ধ্বংস হচ্ছে, অন্যদিকে গড়েও উঠছে। ভাঙাগড়ার নায়কেরাও আছেন, কিন্তু কোন একজন দেবতা কিম্বা অসুর নন। তারা মানুষ। ‘গণদেবতা’ পুরাণোত্তর আধুনিক সমাজের ভাঙাগড়ার গল্প। তারাশঙ্করের গণদেবতায় পৌরাণিক দেবতারা কেউই নাই। কিন্তু অনিরুদ্ধ, পাতু, বিষহরি, দুর্গা, দেবু, পদ্ম ইত্যাদি চরিত্রগুলো আছে। এরা মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের মতোই ঝগড়া বিবাদ করে, কিন্তু এই নায়কদের জীবন ও জীবিকার মধ্য দিয়ে সমাজ ভাঙে এবং আবার গড়ে ওঠে। চণ্ডীমণ্ডপের বিধান বা শাসন এখানে বিশেষ কাজ করে না। ধর্মীয় আইন ও সামাজিক অনুশাসন ও বিধিবিধানের উর্ধে আরেক প্রকার মহাকাল অলক্ষ্যে নিজের সামাজিক চেহারা দেখিয়ে দিয়ে বয়ে বয়ে যায়। সেখানে চণ্ডীমণ্ডপের বাইরের বা চণ্ডীমণ্ডপ বিদ্রোহীরাও অন্তর্ভূক্ত। কেউই সমাজ থেকে বাদ থাকে না।”…
তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’
‘গণদেবতা’ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) লিখেছেন ১৯৪২ সালে। উপন্যাসটির জন্য তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরষ্কার ‘জ্ঞানপীঠ’ পেয়েছিলেন ১৯৬৬ সালে। চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার ১৯৭১ সালে উপন্যাসটি নিয়ে একটি ছবিও করেছেন। তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’ এবং ‘পঞ্চগ্রাম’ দুটি ভিন্ন উপন্যাস হিশাবে আমরা পড়ি। আসলে কিন্তু দুটো দুই খণ্ডে লেখা একই উপন্যাস। এক অংশের নাম ‘চণ্ডীমণ্ডপ’, অপর অংশের নাম ‘পঞ্চগ্রাম’। এই দুই অংশের একসঙ্গে সাধারণ নাম ‘গণদেবতা’। কিন্তু ‘চণ্ডীমণ্ডপ’ অংশের নামকরণ ‘গণদেবতা’। সেই নামেই উপন্যাসখানি মশহুর। কিন্তু তাই বলে ‘গণদেবতা’ এই খণ্ডাংশের নয়, দুই খণ্ড মিলে নাম।
আমি উপন্যাসটি পড়েছি অনেকটা ছাত্রের আগ্রহ নিয়ে। কারণ, আমি উপন্যাস লিখতে চাই। বাংলাদেশের খুবই সামনের সারির বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান লেখক নানান সময়ে আমাকে বলেছেন, বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর অসাধারণ। উপন্যাস লিখতে চাইলে নবীন লেখকদের অবশ্যই স্কুলপাঠ্য বইয়ের মতো তারাশঙ্কর পড়তে হবে। তারাশঙ্করের সব বই না পড়লেও এই কথার মর্ম আমি বুঝি। কারণ তারাশঙ্কর কম লেখেননি। ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি গল্পের বই, ১২ খানা নাটক, ৪টি প্রবন্ধের বই, ৪টি আত্মজীবনী, এমনকি ভ্রমণ কাহিনীও আছে তাঁর দুইটা। তারাশঙ্করের উপন্যাস, গল্প ও নাটক নিয়ে ছবি হয়েছে বিস্তর। প্রায় চল্লিশটির মতো। সত্যজিৎ রায়ও তারাশঙ্করের ‘জলসাঘর’ এবং ‘অভিযান’ উপন্যাস নিয়ে ছবি করেছেন। মেলা পুরষ্কারও পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। যেমন, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। তো বাংলা সাহিত্যের এহেন একজন দিকপাল না পড়ে আপনি উপন্যাস লিখবেন, সেই সঙ্কল্প বোকামিতে পর্যবসিত হতে পারে।
বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায় তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে এসেছে। এই জগতটা আমার অচেনা। বাংলা সাহিত্যের হিন্দু লেখকদের লেখায় মুসলমান জনজীবন অনুপস্থিত থাকে। আমরা যারা এখন লেখালিখি করতে এসেছি, আমাদের কাছে সেটা একদিকে বিস্ময়কর, হিন্দু বাঙালিরা বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানে না। তারাশঙ্করও ব্যাতিক্রম নন। আবার অন্যদিকে এই নাজানাটা অস্বাভাবিকও মনে হয় না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারের ছেলে ছিলেন, তাঁর আরও না জানার কথা। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই ২৪ পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। তাই বীরভূম বারবারই তাঁর লেখায় ছায়া ফেলেছে।
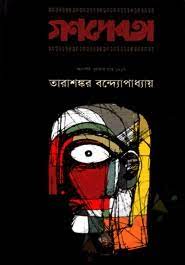
‘গণদেবতা’ পড়তে গিয়ে শুরুতে একটু বোরিং লেগেছিল। তারপরও ‘গণদেবতা’ বেছে নিয়েছি কারন সমাজতত্ত্বের বই না লিখে তারাশঙ্কর কিভাবে গ্রামীণ বাংলার সমাজ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ও বোঝাবুঝি উপ্ন্যাসে তুলে ধরেছেন, সেটা বুঝতে চেয়েছি। সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্যের পার্থক্য বোঝার জন্যই আমার এই নিবিড় পাঠ।
বড় সাহিত্যিকরা কেন ‘গণদেবতা’ পড়তে বলেন, এর একটা কারণ আমি বুঝি এই অর্থে যে পুরাণের দেবতাদের নয়, সাধারণ সামাজিক মানুষই একালের দেবতা— তারাশঙ্কর সেটা আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। চিন্তাটা ভাল লেগেছে আমার, কারন এতো গভীরে ভাবতে পারাটা সাহিত্যিক মুন্সিয়ানার লক্ষণ। তারাশঙ্করের (গণ)দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব না। কিন্তু তারপরও দেবতাদের প্রলয় ও সৃষ্টির ভূমিকার মতো মানুষের সমাজে ভাঙাগড়া আছে, একদিকে সমাজ ধ্বংস হচ্ছে, অন্যদিকে গড়েও উঠছে। ভাঙাগড়ার নায়কেরাও আছেন, কিন্তু কোন একজন দেবতা কিম্বা অসুর নন। তারা মানুষ। ‘গণদেবতা’ পুরাণোত্তর আধুনিক সমাজের ভাঙাগড়ার গল্প। তারাশঙ্করের গণদেবতায় পৌরাণিক দেবতারা কেউই নাই। কিন্তু অনিরুদ্ধ, পাতু, বিষহরি, দুর্গা, দেবু, পদ্ম ইত্যাদি চরিত্রগুলো আছে। এরা মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের মতোই ঝগড়া বিবাদ করে, কিন্তু এই নায়কদের জীবন ও জীবিকার মধ্য দিয়ে সমাজ ভাঙে এবং আবার গড়ে ওঠে। চণ্ডীমণ্ডপের বিধান বা শাসন এখানে বিশেষ কাজ করে না। ধর্মীয় আইন ও সামাজিক অনুশাসন ও বিধিবিধানের উর্ধে আরেক প্রকার মহাকাল অলক্ষ্যে নিজের সামাজিক চেহারা দেখিয়ে দিয়ে বয়ে বয়ে যায়। সেখানে চণ্ডীমণ্ডপের বাইরের বা চণ্ডীমণ্ডপ বিদ্রোহীরাও অন্তর্ভূক্ত। কেউই সমাজ থেকে বাদ থাকে না।
আধুনিককালে ‘গণশক্তি’ এবং ‘জনগণ’ কথাগুলি যে রাজনৈতিক অর্থ নিয়ে হাজির থাকে সেই আলোকে অনেকে ‘গণদেবতা’র ধারণা বুঝতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। তবে ‘গণদেবতা’য় চণ্ডীমণ্ডপ মাঝে মধ্যেই সামাজিক বা গোষ্ঠীজীবনের প্রতীকী রূপ নিয়েছে। প্রাচীন ধর্মীয় আচার, বিধান বা প্রতিষ্ঠানের জায়গায় নতুন আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে বুঝা যায়, কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য পুরাপুরি বোঝা যায় না। এক অর্থে বলা যায় ‘গণদেবতা’ এবং ‘পঞ্চগ্রাম’ একালের হিন্দু বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাষ্য।
মাটি, মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনচিত্র, স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের দূর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ব্যক্তির মহিমা ও বিদ্রোহ, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ধনতন্ত্রের বিজয় গণদেবতায় এই দিকগুলো আমার ভালো লেগেছে। তারাশঙ্কর কিভাবে উপন্যাসের মধ্যে বিষয়গুলো এনেছেন সেটাই খুব শিক্ষণীয় কাজ। মানুষের চরিত্রের নানা জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য নিয়ে কারবার করেছেন তিনি, সেই সব অবশ্য উপন্যাসে থাকবারই কথা। কিভাবে ধীরে ধীরে জমিদারি বিলুপ্ত হয়, আর পাশাপাশি কিভাবে নতুন ধনী শ্রেনীর উদ্ভব ঘটে, কিভাবে দিকে দিকে কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে – এই দিকগুলো তুলে ধরবার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের কৌশল আমার ভাল লেগেছে।
গ্রাম সমাজের ভাঙন এবং শহরজীবনের বিকাশ তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাধারণ একটি বিষয়। সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও আছে। গ্রামের মানুষের উপর অত্যাচারের বর্ণনা, সামাজিক দলাদলিতে মানুষের অপরিসীম নীচতা এবং কাপুরুষ চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করেননি তিনি। সমস্ত গ্রামের সুখ-দুঃখ, আচার-ব্যবহারকে একটা সাধারণ আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণি ও ব্যক্তিকে তার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, ছোট-বড়ো, ইতর-ভদ্র, উঁচু-নীচু সকলের মধ্যে একটা স্নেহভক্তি ভালোবাসা সৃষ্টির মধ্যে একটা ত্রুটি ফুটে বেরিয়ে পড়ে। সেটা হচ্ছে উচ্চবর্ণের উপর নিম্নবর্ণের একান্ত দ্বিধালেশহীন নির্ভরতা। তারাশঙ্কর যেভাবে সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন সেখনেই তাঁর মুন্সিয়ানা আমার মনে ধরেছে। কারন তিনি কোন মানদণ্ড হাতে নিয়ে ভালমন্দ বিচার করতে বসেননি। এটা লেখকের কাজ না। যে ছবিটা তিনি এঁকেছেন সেখান থেকে বাস্তবকে বুঝে নেওয়া পাঠকের কাজ। একই সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধের জটিলতাও। তারাশঙ্কর সমাজ কী চীজ সেটা আমাদের বুঝিয়ে দেন, কিন্তু সমাজ সম্পর্কে কোন সাধারণ সূত্র তিনি তৈরি করেন না।
মাটি, মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনচিত্র, স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের দূর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ব্যক্তির মহিমা ও বিদ্রোহ, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ধনতন্ত্রের বিজয় গণদেবতায় এই দিকগুলো আমার ভালো লেগেছে। তারাশঙ্কর কিভাবে উপন্যাসের মধ্যে বিষয়গুলো এনেছেন সেটাই খুব শিক্ষণীয় কাজ। মানুষের চরিত্রের নানা জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য নিয়ে কারবার করেছেন তিনি, সেই সব অবশ্য উপন্যাসে থাকবারই কথা। কিভাবে ধীরে ধীরে জমিদারি বিলুপ্ত হয়, আর পাশাপাশি কিভাবে নতুন ধনী শ্রেনীর উদ্ভব ঘটে, কিভাবে দিকে দিকে কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে – এই দিকগুলো তুলে ধরবার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের কৌশল আমার ভাল লেগেছে।
এই দ্বিধালেশহীন নির্ভরতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেছে কালীপুর গ্রামের কামার অনিরুদ্ধ কর্মকার এবং গিরিশ সূত্রধর। তারা তাদের কাজের বিনিময়ে ঠিকমতো ধান এবং টাকা না পাওয়াতে গ্রাম ছেড়ে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপারে শহরে দোকান করেছে। ফলে গ্রামের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সকলে তাদের উপরে রুষ্ট হয়ে মজলিশ বসায়। মজলিশে সকলের মুখের উপরে অনিরুদ্ধ কর্মকার উদাহরণ সহ কারণ দেখিয়ে গ্রামের মানুষের কাজ করতে পারবে না বলে দেয়। আর তখনই সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রত্যেক ব্যবস্থাই অপ্রতিহত যথেচ্ছার, নির্লজ্জ স্বার্থসিদ্ধি ও হৃদয়হীন পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। শিবপুর এবং কালিপুর, শিবকালিপুর দুইখানা গ্রামের নতুন সম্পদশালী ব্যক্তি প্রকাণ্ড চেহারা, প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি শ্রীহরি পাল অপমানিত হয়ে অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির আধপাকা ধান নিঃশেষে কেটে তুলে নিয়ে যায়। অনিরুদ্ধের দেখাদেখি গ্রামের নিম্নবিত্ত তারা নাপিত, পাতু বায়েন, লুটনি দাই, পেতো মুচি,ধোপা সকলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সকলে বলে দেয় নগদ ব্যতিত কেউ কোনো কাজ করে দিতে পারবে না। শ্রীহরি নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা বশত এবং সকল কে তার অনুগত করার প্রয়াসে সমস্ত হরিজন পল্লীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। অনিরুদ্ধ, গিরিশ ছুতার, দেবু ঘোষ এবং জগন ডাক্তার ব্যতিত শ্রীহরির এই ভাতের মারে হরিজন পল্লীর অন্য সকলে জব্দ হয়ে শ্রীহরির আশ্রয়েই বেঁচে যায়। দেবনাথ ওরফে দেবু ঘোষকে সরকারি জরিপের কাজে বাধা দেওয়া ও সার্ভে ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী আমিনকে প্রহার করার অপরাধে জেলে যেতে হয়। দেবুর জেলে যাওয়ার পরে গ্রামে অকস্মাৎ স্বদেশী আন্দোলনে তরুণ যুবক যতীন ধরা পড়ে নজরবন্দি হয়ে আসে। হিন্দু সমাজ এবং সমাজপতিতের আধিপত্যে যতীন বুঝতে পেরে ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ বাঁচাতে সরকারের চোখ উপেক্ষা করে নিজে সোচ্চার হয়। দেবু ফিরলে তাকে নিয়ে সভা-সমিতি গঠন করে। দীনতা-হীনতা, হিংসায় জর্জর মানুষ, দারিদ্র্য -দুঃখ-রোগপ্রপীড়িত শিবকালিপুরকে রক্ষা করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে। স্বদেশী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে চায় সাধারণের মাঝে ইংরেজ রাজত্বকে হটিয়ে দিঘি সরোবর কাটানো বাপ দাদার ঐতিহ্য রক্ষা করার চেষ্টা চলে।
মানুষকে ঠকিয়ে, ঘরে আগুন লাগিয়ে, অন্যের স্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ফেলে, সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্যের স্ত্রীকে তুলে নিয়ে নিজের রক্ষিতা বানিয়ে, মানুষকে সুদ সমেত টাকা দিয়ে পথের ভিখিরি তৈরি করে, রাতারাতি অন্যের জমির আল ভেঙে নিজের জমিতে পরিনত করে গড়ে ওঠা জমিদার শ্রেণিকে তারাশঙ্কর উলঙ্গ করেই তুলে ধরেছেন। এই জমিদার শ্রেণীর হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে গিয়ে মানুষের জীবন কিভাবে বিপন্ন হয়েছে তা তিনি বিশেষ দরদে চিত্রিত করেছেন। শ্রীহরির বাগানবাড়ি তৈরির পরিকল্পিত জমির সকল গাছ কেটে অনিরুদ্ধ দুই মাসের জন্য জেলে চলে যায়। জেল থেকে ঘরে না ফিরে জংশনের দোকানিকে নিয়ে পালিয়ে যায়।
নারী চরিত্রের প্রতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়ায়ের মমতা অপরিসীম। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী অবহেলিত। কিন্তু তারাশঙ্কর ‘গণদেবতা’য় নারীকে অবহেলার পাশাপাশি দিয়েছেন স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য। শ্রীহরির স্ত্রী ব্যতিত অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্ম, দেবুর স্ত্রী বিলু, রাঙাপিসি, পাতুর স্ত্রী সকলে নিজ অবস্থানে সুখী। বিয়ের পরে শ্বাশুড়ির যোগ সাজসে পুরুষের ভোগ্য ও হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো পাতু বায়েনের বোন দূর্গা। তারপরে দুর্গা ভিন্ন পথ বেছে নিলেও তার মধ্যে লেখক সৃষ্টি করে দিয়েছেন প্রেমিক পুরুষ বেছে নেয়ার ক্ষমতা। জনসম্মুখে লম্পট পুরুষদের নাম ধরে ধরে তাদের লাম্পট্য প্রকাশের স্বাধীনতা। অনাথ উচ্চিংড়ে কে দিয়েছে মা হিশেবে পদ্মকে। মাতৃত্ব করেছে ঠাণ্ডা।

আধুনিককালে ‘গণশক্তি’ এবং ‘জনগণ’ কথাগুলি যে রাজনৈতিক অর্থ নিয়ে হাজির থাকে সেই আলোকে অনেকে ‘গণদেবতা’র ধারণা বুঝতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। তবে ‘গণদেবতা’য় চণ্ডীমণ্ডপ মাঝে মধ্যেই সামাজিক বা গোষ্ঠীজীবনের প্রতীকী রূপ নিয়েছে। প্রাচীন ধর্মীয় আচার, বিধান বা প্রতিষ্ঠানের জায়গায় নতুন আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে বুঝা যায়, কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য পুরাপুরি বোঝা যায় না। এক অর্থে বলা যায় ‘গণদেবতা’ এবং ‘পঞ্চগ্রাম’ একালের হিন্দু বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাষ্য।
দুই
গল্পটা একটু বলি।
গণদেবতা উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে পাশাপাশি দুইটি গ্রাম শিবপুর এবং কালিপুর নিয়ে, গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে। শিবকালিপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিচুবংশ যেমন কামার,সূত্রধর, বায়েন, নাপিত এবং ধোপাদের বসবাস বেশি। পৈতৃক সূত্রে তারা গ্রামে তাদের বর্ণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ গুলো করে। উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে গিয়েছে এই নিচু জাতের মানুষকে কেন্দ্র করে। পার্শ্ববর্তী মহাগ্রাম, পঞ্চগ্রাম এবং কঙ্কনায় জমিদার শ্রেণির মানুষের বসবাস। শিবকালীপুর গ্রামের নিচু বংশের মানুষগুলো অবস্থাপন্ন কৃষক এবং জমিদারদের হাতের পুতুল। তাদের নিজস্বতা বলে কিছু নাই। কামার লোহার জিনিস তৈরি করে দেয় ধানের বিনিময়ে, ছুতার, বায়েন, নাপিত, ধোপা, দাই প্রত্যেকেই এরকম ধানের বিনিময়ে কাজ করে দেয়। কখনো ধান পায়, আর না পেলে বাকি পড়ে থাকে। ধান আদায়ের নির্দিষ্ট কোনো পথ নাই। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারনে দূর্ভিক্ষ লেগে আছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছে। বিদেশী দ্রব্যের কদর বেড়ে গিয়েছে যার ফলে কামার, ছুতারদের ব্যবসার ধ্বস নেমেছে। কামারের গড়া পেরেক, গজাল, হাতা,খুন্তির বদলে তারা সস্তায় বিদেশ থেকে আসা সামগ্রী বাজার থেকে কিনে নিচ্ছে। একারণে কামার অনিরুদ্ধ এবং ছুতার গিরশ তাদের গ্রামের ব্যবসা উঠিয়ে জংসন শহরে গিয়ে দোকান তৈরি করেছে। তাতে গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক থেকে শুরু করে নিম্ন শ্রেণির মানুষেরও বেশ কাজের কষ্ট হয়েছে জমিতে ফসল রোপনের সময়। গ্রামের মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মজলিশ বসায়। মজলিশে কারণ দর্শিয়ে অনিরুদ্ধ বলে দেয় তারা গ্রামে আর কাজ করতে পারবে না। গ্রামের নতুন ধনী শ্রীহরি পালের সাথে তার বাকবিতণ্ডা বেঁধে যায় পুরানো পাওনার হিসাব নিয়ে। অনিরুদ্ধ মিটমাট করে নিলেও রাতের আধারে শ্রীহরি অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির ধান কেটে নেয়।
শিবকালীপুর গ্রামে প্রথমে উচুবংশের বিরুদ্ধে নিচুবংশের বিরুদ্ধতা, প্রতিবাদ দেখা দেয়। অনিরুদ্ধের দেখাদেখি গ্রামের পাতু বায়েন, তারা নাপিত, লুটনি দাই এবং ধোপা প্রভৃতি মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তারা নগদ ছাড়া কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। গ্রামের উচ্চবংশীয় মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়ে। চিন্তিত মানুষদের মধ্যে দেবু ঘোষ অন্যতম। গণদেবতা উপন্যাসের নায়ক দেবনাথ ঘোষ। দেবু ঘোষ স্বতন্ত্র মানুষ। অসচ্ছল পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে ভালো ছাত্র হয়েও লেখাপড়া ছেড়ে সংসারের হাল ধরতে হয়। গ্রামের স্কুলে পড়ায়। স্কুলের লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও সে যখন যেখানে যে বই পায় তাই পড়ে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে। দেবু ঘোষ বুঝতে পারে কামার, ছুতার, বায়েন, ধোপা এবং দাই শ্রেনির মানুষের গ্রামের উচু শ্রেনির মানুষের প্রতি বিরুদ্ধতা কেনো। শ্রীহরি পালের মতো মানুষ যেখানে প্রধান ব্যক্তির ভূমিকা পালন করে এবং তাকে কেউ শাসন করতে পারে না সেই গ্রামে বিরুদ্ধ প্রতিবাদ আসবেই। শ্রীহরি পাল ওরফে ছিরু পাল নতুন গড়ে ওঠা ধনী ব্যক্তি। জমিদারদের সমকক্ষ একজন। দূর্ধর্ষ আর গোঁয়ার, প্রকৃতির একজন মানুষ। প্রকাশ্যে লোকে তাকে সম্মান দিলেও মনে মনে ঘৃণা করে। শ্রীহরি তা জানে। জানে বলেই সে গ্রামের মানুষের প্রতি নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য মানুষের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে বেশি। জমির আল বাড়িয়ে নেয়। মানুষের সীমানার কিনারায় রাতারাতি দেয়াল তুলে জমি বাড়িয়ে নেয়। নিজের আধিপত্য স্বীকার করানোর জন্য গ্রামের নিচু শ্রেনির নিরীহ মানুষের ঘরে আগুন লাগায়। নিজে গিয়ে তাদেরই সাহায্য করে। প্রকাশ্যে যৌন জীবন যাপন করে। পরের স্ত্রীকে প্রবল ভাবে কামনা করে। যৌন ব্যধিতে মুখের সমস্ত দাঁত পড়ে গেছে তার। খ্যাতির আকাঙখায় টাকা যে পথে উপার্জন করে সেই পথেই লুটায়। তবুও মানুষ তাকে ঘৃণাই করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ ঘোষ এবং শ্রীহরি পালকে তার উপন্যাসের নায়ক এবং দুবৃত্ত লোক হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীহরি পাল খ্যাতির মোহে এমন কোনো গহির্ত কাজ নেই যা করে না। অন্যদিকে দেবনাথ ঘোষ ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। ন্যায় ব্যতিত অন্যায় সে করে না। গ্রামের মানুষের নীচতায় ও অজ্ঞতায় সে হতবাক হয়ে যায় আবার এই মানুষেরই প্রতি অপরিসীম মায়াবোধ করে। তাদের বিপদে এগিয়ে আসে।
জগন ডাক্তার স্বার্থপর কিন্তু পরোপকারি একজন মানুষ। দেবুর সহচর্যে স্বার্থ ভুলে পরোপকারে আরো মনোনিবেশ করে। ঘরপোড়া মানুষের পোড়া ঘরের হিসাব করে উপরে সাহায্য আবেদনের জন্য পাঠায় । গ্রামের মানুষের প্রতি অপরিসীম ক্ষোভ আছে তার, কিন্তু কেউ অসুস্থ হলেই তাকে সেবা দিতে তার কসুর নাই। হরেন ঘোষাল শিক্ষিত নারী লোলুপ যুবক। নিজের গ্রামকে বাঁচানোর স্বার্থে তিনিও যোগ দেয় দেবনাথ ঘোষের সাথে। দিনরাত প্রজা সমিতি প্রজা সমিতি করে দাপিয়ে বেড়ায় গ্রামময়। সরকারি জরিপের কাজে বাঁধা এবং কানুনগোর খারাপ আচরণের প্রতিবাদ করায় দেবু ঘোষ কারাগারে গেলে গ্রামের মানুষের মধ্যে দেখা যায় সৌহার্দ্য এবং প্রীতি। ফুটে ওঠে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ। রাঙাপিসি যে অহরহ দেবতাকে অভিসম্পাত করে সে দেবুর জন্য দেবতার কাছে কাঁদে। শ্রীহরির মা এবং বউ খাদ্য নিয়ে গিয়ে দেবু ঘোষের স্ত্রী বিলুকে দিয়ে আসে। অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রী পদ্ম বিলুর দুঃখে অপরিসীম দুঃখ অনুভব করে। রাঙাপিসি ধান সিঁদুরে লক্ষ্মী পেতে দিয়ে আসে। পাড়ার মেয়েরা ঘাট থেকে জল দিয়ে আসে। যুবকেরা যায় খেলতে দেবু ঘোষের ছোট ছেলেটির সাথে। বৃদ্ধ বিশ্বনাথ চৌধুরী ঘরে বসে দোয়া করে দেবনাথের জন্য। ছিরুপালের মতো বদলোক দেবুর সমস্ত জমি নিজ দায়িত্ত্বে সেটেল করে দেয়। দেবুর অপরে ভোগকৃত জমিও দেবুর নামে বন্দোবস্ত করে দেয়। স্বৈরিণী দূর্গা নিজের শরীর দিয়ে বাঁচাতে চাই দেবু ঘোষ কে। রাতের আধারে তাই সেটেলমেন্ট অফিসারের ঘরে থেকে জেনে আসে দেবুর দু’বছরের জেলের খবর। মাকে সে শোয়ার জন্য পাঠায় বিলুর ঘরে।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ ঘোষ এবং শ্রীহরি পালকে তার উপন্যাসের নায়ক এবং দুবৃত্ত লোক হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীহরি পাল খ্যাতির মোহে এমন কোনো গহির্ত কাজ নেই যা করে না। অন্যদিকে দেবনাথ ঘোষ ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। ন্যায় ব্যতিত অন্যায় সে করে না। গ্রামের মানুষের নীচতায় ও অজ্ঞতায় সে হতবাক হয়ে যায় আবার এই মানুষেরই প্রতি অপরিসীম মায়াবোধ করে। তাদের বিপদে এগিয়ে আসে।
দূর্গাকে লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছে হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে। দূর্গাকে অন্য নারী থেকে দিয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সুন্দরী, লাস্যময়ী, পূর্ণ যৌবনা দূর্গা পুরুষের কামনার বস্তু। বিয়ের পরে শ্বাশুড়ির যোগসাজসে সে গ্রামের জমিদারের ভোগের বস্তুতে পরিণত হলে বাপের বাড়ি ফিরে এসে মায়ের প্রলোভনে সে এই পথটিই বেছে নেই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে সে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নিজের ঘরে। দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক ব্যতিত সে কখনো মনের সম্পর্কে গড়াই নি ছিরু পালের সাথে। যখন জানতে পারে ছিরু পাল তাদের পাড়ায় আগুন লাগিয়েছে তখন সে দারুন ঘৃণা এবং আক্রোশে ছিরু পালকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অনিরুদ্ধ কামার এবং দেবু ঘোষকে তার ভালো লেগেছে। পদ্ম অসুস্থ হলে অনিরুদ্ধকে সে ভালোবাসা দিয়েছে, আর্থিক সাহায্য করেছে। মোহ কেটে গেলে অনিরুদ্ধকে সে আর তার ঘরে ঢুকতে দেয় নি। আপন গোত্রের মানুষকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। শ্রীহরি, গোমস্তা, দারোগা মিলে যতীনকে ধরিয়ে দেবার পরিকল্পনা এবং প্রজা- সমিতি ভেঙে দেয়ার পরিকল্পনা করলে দূর্গা কৌশলে সাপে কাটার অভিনয় করে শ্রীহরি পালের গোপন পরিকল্পনার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। অনিরুদ্ধ মাতাল হয়ে গেলে বিলুর হাতে টাকা পাঠিয়ে সে পদ্মকে সাহায্য করেছে। রঙ্গরসে দেবু এবং যতীনের সাথে ঠাট্টা করেছে। ইয়ার্কি করে বিলু এবং পদ্মের কাছে পরজন্মে বর ধার চেয়েছে। বিলু এবং তার সন্তান কলেরায় মারা গেলে দেবুর বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করেছে দেবুকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। উপেন কলেরায় আক্রান্ত হলে সবার আগে সে ছুটে গিয়েছে। সেবা করেছে উপেনকে। নজরবন্দি যতীনকে সে পছন্দ করেছে। রাঙাপিসির ভাষায়, ‘তুই মানুষ তো ভালো তবে বড় নচ্ছার’। সমগ্র উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দূর্গাকে সমস্ত অত্যাচার, আন্দোলন এবং প্রতিবাদের গুপ্তচর হিসেবে তৈরি করেছেন। জমিদার, থানার দারোগা, সেটেলমেন্ট অফিসার, গোমস্তা, চৌকিদার, পাড়ার সাধারণ সকলের খবর তার নখদর্পণে। মুখরা দূর্গা দেবুর স্ত্রী বিলু এবং তার সন্তান মারা যাবার পরে ধীর হয়ে যায়। উচ্ছল যৌবন, রঙ্গরস, লীলারস তার অজান্তেই স্তিমিত হয়ে ঘরোয়া হয়ে যায়। নজরবন্দি যতীন চলে যাওয়ার সময় তাদের সামনে না দাঁড়িয়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে শুধু চেয়ে থেকে বিদায় জানায়।
দেবনাথ ঘোষ কারাগারে যাওয়ার পরে শিবকালীপুর গ্রামে স্বদেশী আন্দোলনকারী আঠারো উনিশ বছর বয়সের যুবক যতীন নজরবন্দি হয়ে আসে। ইংরেজ রাজত্বকে দূর করতে এই যুবকেরা নিয়েছে হাতের মুঠোই প্রান। বাঁচাতে বদ্ধ পরিকর ভারতের শহরের, গ্রামের, অলিগলির ইতিহাস ঐতিহ্য। দূর্গা দারোগাকে বলে যতীনকে থাকার জন্য অনিরুদ্ধের বাইরের ঘরটি ভাড়া করিয়ে দেয়। যতীন অনিরুদ্ধের মূর্ছারোগী বন্ধ্যা স্ত্রী পদ্মের সাথে মা-মণি সম্বন্ধ পাতিয়ে নেয়।
যতীন শিবকালীপুর গ্রামে এসে তার বেড়ে ওঠা শহর কলকাতা থেকে গ্রামের জীবনযাত্রার অনেক পার্থক্য দেখতে পায়। গ্রামে নিম্নবিত্তের উপরে উচ্চবিত্তের নির্মম অত্যাচার এবং উৎপীড়ন দেখতে পায়। গ্রামের সকল কিছু জমিদারের, প্রজা পুতুল মাত্র। তাকে যে মাপে তৈরি করা হবে সে সেই আকার ধারণ করবে। শ্রীহরি গ্রামের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গাঁইয়ে মানে না আপনি মোড়ল অবস্থা। নিজেকে সম্মানীয় করার প্রচেষ্টায় সে নিষ্ঠুরতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামতে দ্বিধা করে না। চণ্ডীমণ্ডপ নিজের করে নেয়। আলাদা স্কুল ঘর তৈরি করে দেয়। অপ্রকাশ্যে জমিদার হওয়ার প্রয়াসে সমস্ত নিম্নপন্থা সে অবলম্বন করে। প্রকাশ্যে জনদরদি ভাবেরও কোন অভাব রাখে না। পনেরো মাস পরে দেবু ঘোষ বাড়ি ফিরে দেখে গ্রাম আগের মতই আছে। পূজাপার্বণ তেমন ভাবেই চলে। ধর্ম কর্মে মানুষের তেমনই মতি। নীচতায় হীনতায় জরাজীর্ণ শিবকালীপুর গ্রামের মানুষ হীন জীবনকে অবলম্বন করেই বেঁচে আছে। কারাগারে বসে ঠিক করেছিলো নিজের সংসার নিয়ে বেঁচে থাকবে। গ্রামের কোন বিষয়ে মাথা দেবে না। কিন্তু গ্রামে ফিরে নজরবন্দি যতীন আলাদা মানুষে পরিণত হয়ে যায়। কংগ্রেস কমিটি, প্রজা-সমিতি গঠন করে যতীন। প্রজা-সমিতির সভাপতি তৈরি করে দেবু ঘোষকে। গ্রামের সাধারণ মানুষের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে সে। কালবৈশাখী ঝড়ে গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরের চাল উড়ে গেলে তারা তালপাতা কেটে ঘরে চাল দেওয়ার জন্য নিতে চাইলে শ্রীহরি তাদের বাঁধা দেয়। দেবু ঘোষ তাদের তালপাতা নিয়ে বাড়ি যেতে বলে। অধিকার নিজেদের দ্বারাই আদায়ের জন্য বলে। শ্রীহরি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। জমিদারের ভাগাড়ে গরু চরাতে দিলে সেই জমি কালু শেখকে ভাড়া করে খোঁয়াড়ে ভরে দেয়। দেবু ঘোষ ছেলের বাজু বন্দক রেখে গরু ফেরত নিয়ে আসে। কোন প্রকারেই জনগনকে পোষ মানাতে না পেরে শ্রীহরি তাদের গাছ কেটে নিতে চায়। সকলের গাছ কাটতে দিলেও দেবু ঘোষের গাছ কাটতে বাধা প্রদান করলে বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী এবং দেবু ঘোষের মাথায় আঘাত লাগে। লাঠিয়ালরা তাদের ঠেলে গাছের গুঁড়ির উপরে ফেলে দেয়। অনিরুদ্ধ একজনের পিঠে লাঠি মেরে পালায়। জগন ডাক্তার এবং হরেন ঘোষাল থানায় জানাতে যায়। কোনোপ্রকার নিজেদের উন্নয়ন প্রজা সমিতিরা করে উঠতে পারে না। শ্রীহরিরও ক্রোধ কমে না। পরেরদিন সকালে দেবু ঘোষের গাছের গুড়ি শুধু পড়ে থাকে। গাছের পাতা আর কিছু আম ছাড়া অন্য কোন অংশ চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাগের বশে অনিরুদ্ধ কর্মকার শ্রীহরির পরিকল্পিত বাগানবাড়িতে লাগানো বিভিন্ন কাঠের গাছ, ফলের গাছ, ফুলের গাছ কেটে দেয়। দারোগা এসে দেবু ঘোষকে ধরলে অনিরুদ্ধ দোষ স্বীকার করে। তার দুইমাসের সাজা হয়।
গ্রামের সমস্ত কিছু প্রজাদের দখলে চলে যেতে যেতে প্রজাদেরই বড়ো রকমের ক্ষতি হয়ে যায়। জমিদারের হয় লাভ। বড় করে পহেলা বৈশাখ পালন করে শ্রীহরি পাল। তাতে বাসি পঁচা ফুলুরি খেয়ে গরিব মানুষের হয় কলেরা। সেই বিষে গ্রামের অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অন্যের প্রাণ বাঁচাতে দেবু ঘোষ নিজের শরীরে বয়ে নিয়ে আসে জীবাণু। তাতে প্রাণ যায় তার স্ত্রী এবং সন্তানের। নিঃস্ব, একাকিত্বে দেবুর অবলম্বন হয় গ্রামের মানুষ। সে সম্মান চেয়েছিলো। স্বতন্ত্র সম্মান। পেলো কিন্তু সবকিছু হারানোর বিনিময়ে। অপরদিকে শ্রীহরি গোমস্তা থেকে নতুন জমিদার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। জমিদারি কেনার আগে, গ্রামের সকল মানুষের রাজা হওয়ার আগে সে সরাতে চাইলো তার পথের জঞ্জাল স্বদেশী আন্দোলনকারী নজরবন্দি যতীন কে। অন্যদিকে তার প্রচণ্ড কামনার লালসা আছে পদ্মের প্রতি। অনিরুদ্ধ জেল থেকে না ফিরে জংসনের দোকানিকে নিয়ে পালিয়েছে। কোপ মারার এই তার সুযোগ। যতীনের নামে জনগনকে উসকে দেয়ার অভিযোগ দিলো দারোগার কাছে। যতীনের বদলির নির্দেশ হলো। পদ্ম নিরবে চোখের পানি ফেলে উচ্চিংড়ে আর গোবরে কে সম্বল করে যতীনকে বিদায় দিলো।
পাড়ার প্রত্যেকে যতীনকে একে একে বিদায় দিলো। কুচক্রী শ্রীহরি মৃদু হেসে যতীনকে বিদায় দিলো শুধু বিদায় দিলো না দূর্গা। সে দূরে দাঁড়িয়ে দেবু আর যতীনের দারোগার পিছনে হেঁটে যাওয়া দেখলো। যতীন দেবুকে আলিঙ্গন করে বিদায় দিয়ে পেছনে ফেলে শিবকালীপুর গ্রামকে প্রণাম করে করে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেল। আর ভাবতে ভাবতে গেলো গ্রামের সাধারণ মানুষের সুসময় আসবে। সমস্ত উৎপীড়নের অবসান হবে। জমিদারের সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়াবে। দেবুর মতো বিদ্রোহী মানুষ প্রত্যেক গ্রামে গড়ে উঠবে। তাদের বিদ্রোহী আত্মা সকল বাঁধাকে অতিক্রম করবে। তাদের জীবন বিকাশের সকল প্রতিকূল শক্তিকে ধ্বংস করবে তাতে তার সংশয় নেই আজ। ভারতের জীবনপ্রবাহ বাধাবিঘ্ন ঠেলে আবার ছুটবে।
গণদেবতায় পৌরাণিক দেবতারা কেউই নাই। কিন্তু অনিরুদ্ধ, পাতু, বিষহরি, দুর্গা, দেবু, পদ্ম ইত্যাদি চরিত্রগুলো আছে। এরা মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের মতোই ঝগড়া বিবাদ করে, কিন্তু এই নায়কদের জীবন ও জীবিকার মধ্য দিয়ে সমাজ ভাঙে এবং আবার গড়ে ওঠে। চণ্ডীমণ্ডপের বিধান বা শাসন এখানে বিশেষ কাজ করে না। ধর্মীয় আইন ও সামাজিক অনুশাসন ও বিধিবিধানের উর্ধে আরেক প্রকার মহাকাল অলক্ষ্যে নিজের সামাজিক চেহারা দেখিয়ে দিয়ে বয়ে বয়ে যায়। সেখানে চণ্ডীমণ্ডপের বাইরের বা চণ্ডীমণ্ডপ বিদ্রোহীরাও অন্তর্ভূক্ত। কেউই সমাজ থেকে বাদ থাকে না।
চরিত্রগুলো নিয়ে ভাবছি আমি। উপন্যাসের গল্পে সম্ভবত চরিত্রগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে হাজির করাই আসল কাজ। তারাশঙ্কর কাজটা কিভাবে করেন, সেটাই হচ্ছে বোঝার বিষয়। বলা বাহুল্য যারা আসলেই উপন্যাস লিখতে চান তাদের ‘গণদেবতা’ নানান দিক থেকে নানান ভাবে বেশ কয়েকবারই পড়তে হবে। এতে উপকার ছাড়া অপকার নাই।
জেসমিন নাহার

তরুণ গল্পকার। উপন্যাস লিখনেও হাত দিয়েছেন। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকাতেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যশোহর জেলার শার্শা উপজেলায় বাড়ি। গোরপাড়া সর্দারবাড়ির মেয়ে। বাবা নুরুল ইসলাম (রহঃ) চিশতিয়া তরিকার ফকির ছিলেন। সেই কারণে ফকিরি ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে। মা রওশানারা বেগমের সঙ্গে বাস করেন জেসমিন। আধুনিকতার মধ্যে নামসাকিন হারিয়ে বিমূর্ত হতে চান না। প্রকৃতির মাঝে যাপিত জীবনকে মূর্তভাবে পরখ করতে চান। গদ্যেও জীবনের মূর্তভাবকে প্রকাশ করার ইচ্ছায় লেখালেখি করেন।


