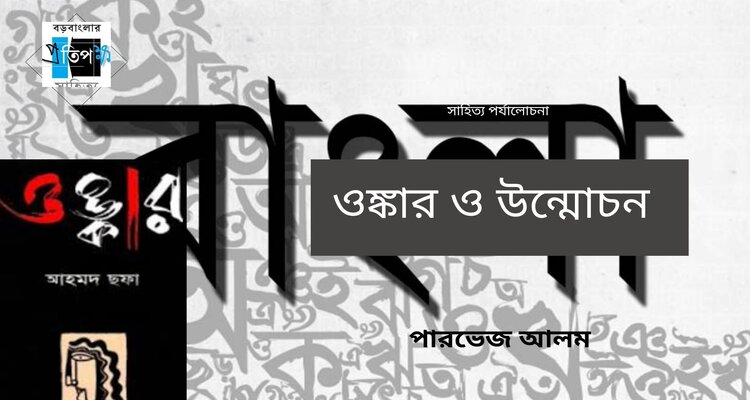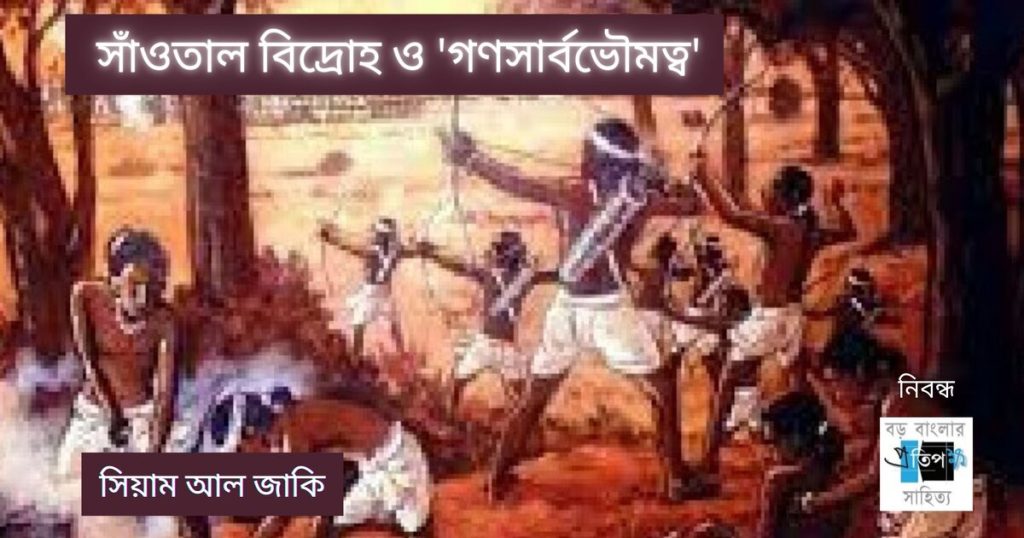
।। সিয়াম আল জাকি ।।
সাঁওতাল বিদ্রোহ শুধুমাত্র অস্ত্রধারণ না; তারা রাষ্ট্রের ভাষা, ইতিহাস, জমির সংজ্ঞা সবকিছুর প্রতিপাদ্যই চ্যালেঞ্জ করে। এটা একখানা discursive shift। তারা বলে, রাষ্ট্র তোমার মতো হইতে হবে না রাষ্ট্র হইতে পারে আমাদের মতোও। রণজিৎ গুহ ‘Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India’ বইতে বলেন, “এইসব বিদ্রোহ নিছক কর বিদ্রোহ না; এগুলা “acts of self-representation”। অর্থাৎ জনগণ নিজেরা নিজেদের ভাষায় বলে “আমরা কারা, আমাদের জমি কই, আমাদের শাসন কেমন হবে।”
“এই দেশ তোমাগো না, এই জমি আমাদের— আমরা কুড়াল ধরি, দা ধরি, লাঠি ধরি, কিন্তু অন্যায়ের সামনে মাথা নত করি না।”
– সাঁওতাল প্রবচন
ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন যেইসব অঞ্চলের উপর সর্বপ্রথম ভর কইরা বসে, তার একটা আছিল সাঁওতাল পরগনা। সেখানে ১৮৫৫ সালের এই বিদ্রোহ নিছক জমি দখল বা কর না দেওয়ার লড়াই আছিল না, এইটা আছিল একখানা মর্ডানিজমের আগেকার এক “গণসার্বভৌমত্বের” জাগরণ। এই বিদ্রোহের লগে লগে উঠে আসে কিছু বড় থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন, যেমন: ফিউডালিজমের বৈধতা, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার অনুপ্রবেশ, মর্ডানিজম নামক পরাশক্তির ছদ্মবেশ, আর সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস কই।
এই লেখাতে আমরা এই বিদ্রোহটারে একখানা ‘পিপল’স সোভারেইন্টি’-র প্রতীক রূপে দেখমু। সাঁওতাল বিদ্রোহ কীভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র আর জমিদারী ফিউডাল সিস্টেমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইছিল, কীভাবে তাহার তাত্ত্বিক ভিত্তি রচে, আর কীভাবে উহা আমাদের নয়া যুগের গণআন্দোলনের একটা মডেল হিসাবে দাঁড়ায় এইসবের উপর মূলত আলোকপাত করব।
বিদ্রোহের পটভূমি দেখা দরকার স্বল্প পরিসরে। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন, সিধু, কানু, চাঁদ আর ভৈরব নামে চার ভাইয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতাল লোক অস্ত্র হাতে তুইলা নেয় ইংরেজ শাসন, মহাজনি শোষণ আর জমিদারি ফিউডালিজমের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন দুঃসহ ভূমি বন্দোবস্ত ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ আছিল শুদ্ধ গণঅভ্যুত্থান।
মূল অভিযোগ আছিল:
১. জমিদার আর মহাজনের চক্রবূহ্য শোষণ
২. ঋণের ফাঁদ ও অর্থনৈতিক নিঃস্বতা
৩. ভূমির উপর ঐতিহ্যগত মালিকানার অস্বীকৃতি
এটা নিছক সাঁওতালদের বিদ্রোহ আছিল না, বরং ছিল একখানা সাবলীল প্রশ্ন যে, “ভূমি কার? রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের উৎস কোথায়?”
ফিউডালিজমের সঙ্গে জমিদারির একটা লম্বা সম্পর্ক আছে, এমনকী পুঁজিবাদের সঙ্গেও। এটার সাঁওতাল বিদ্রোহের চোখে দেখা দরকার। সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা যায় একরকম ফিউডালিজমের খোলসে আগত পুঁজিবাদী গ্লানির বিরুদ্ধচিন্তা। জমিদাররা, যারা কোম্পানির সহযোগী আছিল, তাঁরা উহা ব্রিটিশদের লগে যৌথ স্বার্থে পরিচালিত করত। যেমন পেরি অ্যান্ডারসন (1974) বলেন, “Feudalism in the colonies did not vanish under modern capitalism; it mutated.” অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভার্সনে ফিউডালিজম বিলুপ্ত হয় নাই; বরং একখানা নব্য পুঁজিবাদী রূপ লইয়া হাজির হয়। এইখানে ‘মিউটেশন’ মানে হলো— জমিদারি ব্যবস্থার ধাঁচ বজায় থাকলেও, তার ভেতর ঢুকে পড়ে নতুন ধরণের শোষণ কাঠামো, যেইটা পুঁজির লগে যুক্ত।
এই mutating feudalism’র নিচে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী হারায় তার ন্যাচারাল ভূমি মালিকানা। এইখানে ‘ভূমি’ কেবল উৎপাদনের উপকরণ না, এইটা সংস্কৃতির বাহক, ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি। তাদের প্রতিরোধ আছিল একখানা লোক-সার্বভৌম চর্চা। সিধু কানুর নেতৃত্ব কেবলমাত্র সামরিক নেতৃত্ব না, এটা আছিল নৈতিক নেতৃত্ব যেইখানে জনগণ নিজেরা রাষ্ট্রক্ষমতার ন্যায্য মালিক হিসাবে উঠিয়া দাঁড়ায়। টমাস ম্যাককলি পুঁজিবাদ ও মর্ডানিজম এর জরুরী বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখান ১৮৫০ এর দশকে কীভাবে পুঁজিবাদ তার ঔপনিবেশিক রূপে ভারতের গায়ে চেপে বসে। টমাস ম্যাককলি তাঁর 1835 সালের Minute on Indian Education-এ বলেন, “We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern…”
এই “ইন্টারপ্রেটার ক্লাস” গড়ার পেছনে ছিল আইন, শিক্ষাব্যবস্থা, রেলপথ, বাজার সবকিছুর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমাজকে ‘মডার্ন’ করবার অজুহাত। কিন্তু এই ‘মডার্নাইজেশন’ আদতে একপ্রকার কালোনিয়াল ডিসিপ্লিনিং মেকানিজম। এইখানে রেলপথ মানে শুধু যোগাযোগ না, বরং রাষ্ট্রের পক্ষে জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণের একখানা অবকাঠামো।
মার্ক্সীয় সমালোচনায় উপনিবেশ ও উৎপাদন নিয়ে বলা দরকার এমতাবস্থায়। মার্ক্স যেমন বলেন, “The bourgeoisie… has pitilessly torn asunder the motley feudal ties…” (Communist Manifesto, 1848)। এই tearing asunder যখন আসে উপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে, তখন ইহা একরকম নয়া ফিউডাল পুঁজিবাদ। যেখানে ভূমি অধিকার নাই, শুধু উৎপাদন আছে। এইখানে “জমি” আর কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ না, বরং একখানা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বত্বা। এই পুঁজিবাদের মুখে একমাত্র জবাব আছিল জনগণের অস্ত্রধারণ। এইখানে সাঁওতাল বিদ্রোহ একখানা post-capitalist জাতীয় মুক্তি-ভাবনার রূপরেখা হাজির করে।
জেমস স্কট, readable state ও স্থানিক বিদ্রোহের এসেন্স বুঝতে পারা জরুরী। জেমস স্কট (1998) তাঁর বই Seeing Like a State-এ বলেন,“High modernist states attempt to impose legibility on society by standardizing people, land, and practices.”
অর্থাৎ মর্ডান স্টেট চায় সবকিছুকে ‘পড়া যায় এমন’, মানে একটা ইউনিফর্ম ফর্মুলায় ফেলা যায়। কিন্তু সাঁওতাল সমাজ decentralized, organic, জটিল। এইজন্য রাষ্ট্র তাদের ভাষা, ভূমি ব্যবহার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবকিছুর উপর আগ্রাসন চালায়।
এইখানে সাঁওতাল প্রতিরোধ ছিল একখানা epistemological rebellion। তারা রাষ্ট্রের ভাষা-চিন্তা-ব্যবস্থাকেই প্রত্যাখ্যান করে। একরকম বাচনভিত্তিক সত্তার পুনর্নির্মাণ ঘটে।
এই পয়েন্টে রুশো ও গণ সার্বভৌমত্বের সম্পর্ক বুঝা দরকার।
“The sovereign is the people. Not the king, nor the law.”.
জ্যাঁ জ্যাক রুশো, The Social Contract (1762).
রুশোর ধারণায় “সার্বভৌমত্ব” মানে জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাই শেষ কথা। এইটা সরকারের হাতে না, কোনো আইনের অধীন না, বরং জনগণের ঐক্যবদ্ধ চেতনাতেই সার্বভৌমত্ব নিহিত। সাঁওতাল বিদ্রোহ এই চিন্তার একখানা খাঁটি প্রাক-আধুনিক, অর্গানিক বাস্তবায়ন। এইখানে কোনো নির্বাচিত সরকার নাই, আইনি কাঠামো নাই; শুধু জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। এইটাই হইতেছে ‘গণ সার্বভৌমত্ব’ ফর্মাল না, কিন্তু আত্মিক; আইনি না, কিন্তু প্রকৃত। হোমি ভাভা ও ডিসকার্সিভ প্রতিরোধের একটা নোক্তা দি এখানে। হোমি কে. ভাভা তাঁর “Nation and Narration” বইতে বলেন,“Subaltern insurgency often challenges not the political structures directly, but the discursive foundations of those structures.” এইখানে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুধুমাত্র অস্ত্রধারণ না; তারা রাষ্ট্রের ভাষা, ইতিহাস, জমির সংজ্ঞা সবকিছুর প্রতিপাদ্যই চ্যালেঞ্জ করে। এটা একখানা discursive shift। তারা বলে, রাষ্ট্র তোমার মতো হইতে হবে না রাষ্ট্র হইতে পারে আমাদের মতোও। রণজিৎ গুহ ‘Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India’ বইতে বলেন, “এইসব বিদ্রোহ নিছক কর বিদ্রোহ না; এগুলা “acts of self-representation”। অর্থাৎ জনগণ নিজেরা নিজেদের ভাষায় বলে “আমরা কারা, আমাদের জমি কই, আমাদের শাসন কেমন হবে।”
সাঁওতাল বিদ্রোহ এইরকম একখানা জনগণের ভাষায় রাষ্ট্রগঠনের চর্চা। বিদ্রোহ কেবল ইতিহাস না, ভবিষ্যতের দিশা।আজকের দিনে, যেইখানে রাষ্ট্র সার্বভৌম না, বরং কর্পোরেট আর রাজনৈতিক এলিটের দখলে, সাঁওতাল বিদ্রোহ আমাদের শেখায় গণ সার্বভৌমত্ব হইল আত্মপ্রত্যয়, অস্ত্রধারণ, ঐক্য, আর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর দাঁড়ানো।
এই বিদ্রোহ পুনর্বার পড়া দরকার
Climate justice আন্দোলন, Indigenous rights আন্দোলন, ভূমি অধিকার আন্দোলনের মতো জায়গায় সাঁওতাল চিন্তা এখনও প্রাসঙ্গিক।আপাতত শেষ হিসাবে বলি, সাঁওতাল বিদ্রোহ কেবল ইতিহাস না, এটা একখানা তাত্ত্বিক প্রস্তাব। যেইখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়, আর জনগণের যৌথ চেতনা একমাত্র সত্য ক্ষমতা হিসাবে উঠে আসে।
এইটা একরকম পূর্ববঙ্গীয় ‘কমিউনাল রিপাবলিক’-এর ধারণা যেইখানে শাসন আসে নিচ থাইকা। আজকের দিনে যখন রাষ্ট্র প্রশ্নবিদ্ধ, আন্দোলন দিশাহীন, তখন সাঁওতাল বিদ্রোহ আবারো নতুন করে পথ দেখায়
“ভূমি যদি আমাদের, তবে শাসনও আমাদেরই।”
সূত্র
Anderson, Perry (1974). Lineages of the Absolutist State. Verso.
Marx, Karl & Engels, Friedrich (1848). The Communist Manifesto.
Scott, James C. (1998). Seeing Like a State. Yale University Press.
Rousseau, Jean-Jacques (1762). The Social Contract.
Bhabha, Homi K. (1994). Nation and Narration. Routledge.
Guha, Ranajit (1983). Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford University Press.
Macaulay, Thomas (1835). Minute on Indian Education.
সিয়াম আল জাকি

জন্ম ও বসবাস বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত।