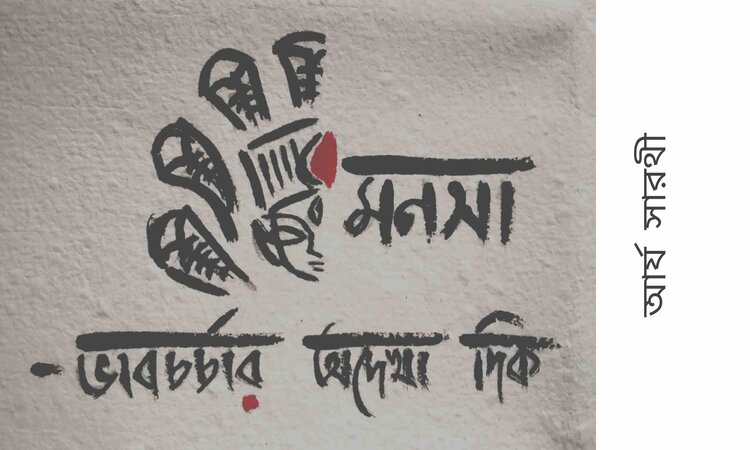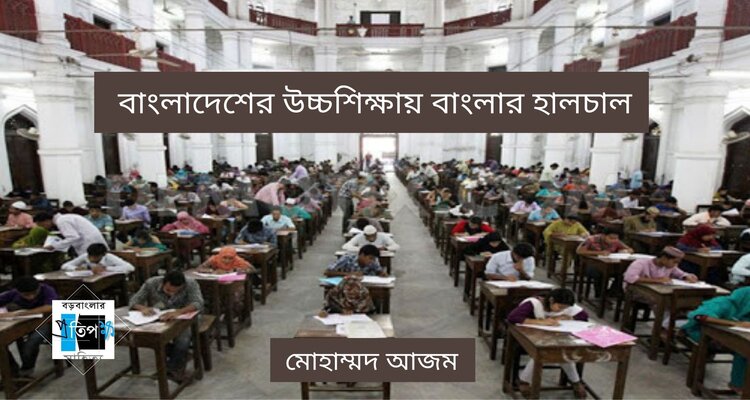।। আজাদ খান ভাসানী ।।
যারা মনে করেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা হয় মুক্তিযুদ্ধ বোঝেন না, নয়তো চেতনা ব্যবসায়ী। তাঁরা চব্বিশের তরুণদের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে সক্ষম হবেন না। একাত্তর থেকে চব্বিশ— আমাদের যে একটা অসমাপ্ত লড়াই রয়ে গেছে, ব্যক্তি আর গোষ্ঠীস্বার্থে তারা তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। ভুলিয়ে দিয়েছিল। ’৪৭, ’৫২, ’৬৯, ’৭১ আর ’৯০-এর প্রতিশ্রুত বাংলাদেশ গড়ার ব্যর্থতা চব্বিশের তরুণদের অবধারিতভাবে রাজপথে নামিয়ে এনেছে। একাত্তরের অসমাপ্ত লড়াইটাই চব্বিশ আবার নতুন করে আমাদের সামনে হাজির করেছে। এই লড়াই শুধু ক্ষমতার পালাবদলের লড়াই নয়। ফ্যাসিবাদী ব্যাবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের লড়াই। ইতিহাসের বাঁক বদলের লড়াই। কথিত বড়োভাই, মেজোভাইদের কাছে ন্যায্য হিস্যার লড়াই। বিশ্বকে পথ দেখাবার লড়াই। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লড়াই।
সাতচল্লিশে বাংলাদেশ ছিল মাতৃগর্ভে। রূপক অর্থে নাবালক ধরে নিতে পারি। সেই অর্থে ভারত ছিল বড়োভাই আর পাকিস্তান মেজোভাই। সীমানা বাটোয়ারার ক্ষেত্রে ছোটোভাই নাবালক বাংলাদেশের জন্য পোকায় খাওয়া একটা ভূখণ্ড বা মানচিত্রই আমাদের ভাগে রেখে দ্রুত রাষ্ট্র-ক্ষমতায় বসেছিল তৎকালীন ভারত-পাকিস্তানের কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সরকার। মাতৃগর্ভে থাকা অথবা নাবালক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য তাদের দায় ও দরদ ছিল অনেকটা বিমাতাসুলভ। ভৌগোলিকভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ১,২০০ মাইল দূরত্ব রেখে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণের বিপরীতে ১৯৭১ সালে জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অবধারিত বাংলাদেশ। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর অতীতের সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ’২৪-এর তরুণদের রক্তদান আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান। ’৪৭, ’৫২, ’৬৯, ’৭১, ’৯০-এর বেহাত স্বপ্ন গুচ্ছ আকারে ’২৪-এর গণ আকাঙ্ক্ষায় যুক্ত হয়েছে। এ এক নতুন বাংলাদেশ।
১৯৪৬ সালের মার্চ মাস। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের বিরোধপূর্ণ দাবিগুলো সমাধানের জন্য ভারতে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠায়। ক্যাবিনেট মিশন একটি ফেডারাল স্কিমের অধীনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যগুলো নিয়ে তিনটি ইউনিয়ন গঠন করার কথা বলেন। প্রথম ইউনিয়নে থাকবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান। দ্বিতীয় ইউনিয়নে থাকবে বাংলা এবং আসাম। ভারতের বাদবাকি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে তৃতীয় ইউনিয়ন। বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ— এই তিনটি ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রেখে বাদবাকি সকল ক্ষমতা প্রদেশগুলোর হাতে থাকবে। এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার বাধ্যতামূলক গ্রুপিং ব্যবস্থা, প্রদেশগুলোর নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাসে ১৯৪৬ সালের ৬ জুন মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লিগ এই প্রস্তাব মেনে নেয়। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।
ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে যে আশার আলো দেখা দিয়েছিল, কংগ্রেসের পরামর্শে ক্যাবিনেট মিশন এবং ভাইসরয় কর্তৃক তাঁদের কৃত ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তা নির্বাপিত হয়। এই পরিস্থিতিতে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বোম্বাইয়ের লিগ কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ বলেন, “মুসলিম লিগ ক্যাবিনেট মিশনের সাথে আলোচনায় কংগ্রেসকে একটির পর একটি সুবিধা দান করেছে (made concession after concession)। কারণ আমরা চেয়েছিলাম একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ও শাস্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হতে। যাতে করে শুধু হিন্দু ও মুসলমানই নয়, বরঞ্চ উপমহাদেশে বসবাসকারী সকল মানুষ স্বাধীনতা লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস তাদের নীচতাপূর্ণ বাকচাতুরি ও দর কষাকষির দ্বারা ভারতবাসীর বিরাট ক্ষতি করেছে। সমগ্র আলাপ আলোচনায় ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেসের সন্ত্রাস ও ভীতির শিকারে পরিণত হয়।” নেহরুর ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীভূত ভারতের বিরোধিতার কারণে এটি শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে।
১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন পরবর্তী ভাইসরয় হিসাবে ভারতে আসেন এবং ৩ জুন ভারত শাসন আইনের অধীনে ভারতের সীমানা নির্ধারণকারী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে র্যাডক্লিফকে নিযুক্ত করেন। ৮ জুলাই র্যাডক্লিফ ভারতে আসেন এবং ভারত ভাগ করে নতুন দু’টি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের মানচিত্র এবং আন্তর্জাতিক সীমা নির্দেশ করে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে দু’টি বড় প্রদেশ ছিল, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিমরা ছিল প্রায় সমান সংখ্যক। এর একটি হল পূর্ব দিকে বাংলা আর অন্যটি পশ্চিম দিকে পাঞ্জাব। র্যাডক্লিফের দায়িত্ব ছিল এই দু’টি প্রদেশের মধ্যে বিভক্তি লাইন টেনে দেয়া, যা ছিল অত্যন্ত জটিল কাজ। এ কাজটি করতে তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে নেহরুর পরামর্শ, পুরোনো মানচিত্র আর জনসংখ্যার ভুল চিত্র সম্বলিত পরিসংখ্যানের উপর। শেষমেশ নেহরুর সঙ্গে আঁতাত করে র্যাডক্লিফ বানরের পিঠা ভাগের মতো ভারত ভাগ করলেন। এদিকে মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ যতটা না পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে নিরাপস ছিলেন, বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ নিয়ে ততটাই তাদের মধ্যে উচ্ছন্নতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে আসাম প্রশ্নে তো চরম উচ্ছন্নতা দেখা যায়। এর মধ্য দিয়েই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দু’টি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।
প্রশ্ন ওঠে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম আসনে মুসলিম লিগ বিজয়ী হলেও আসামের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা কীভাবে ভারতে থেকে যায়? সিলেটে গণভোটে বিজয়ী হবার পরেও করিমগঞ্জ কীভাবে ভারতের হয়? ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পরও করিমগঞ্জে পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যায়। কিন্তু সপ্তাহখানেক পর করিমগঞ্জ ভারতের দখলে চলে যায়। পরবর্তীতে গোয়ালপাড়া-সহ অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাও মুসলিম লিগের উদাসীনতা আর কংগ্রেসের চক্রান্তে ভারতের ফরে চলে যায়। এক্ষেত্রে তৎকালীন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীই একমাত্র কাণ্ডারি হয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। ফলশ্রুতিতে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতার সময় তাঁকে আসামের কারাগারে পুষে রাখা হয়। ফলে পোকায় খাওয়া মানচিত্র নিয়েই পূর্ব বাংলাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।
সাতচল্লিশের দেশভাগের পর আশাভঙ্গ ও হতাশার ২৩ বছরে ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরে রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মেজোভাইয়ের যুগের অবসান হলেও বড়োভাই আবার কাঁধের ওপর চেপে বসে। ভারতের সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের কাছে আমাদের মুক্তির স্বপ্ন জিম্মি হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত সহযোগিতার হাত বাড়ালেও শেষ পর্যন্ত তা ইন্দো-পাক শক্তি প্রদর্শনের ক্রীড়নক হয়ে যায়।
১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের করা সাত দফা গোপন চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতের আসল উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়। চুক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ:
এক: যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকিদের চাকুরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
দুই: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন থাকবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনর্নিরীক্ষণের জন্য দু’দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
তিন: বাংলাদেশের কোনো নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।
চার: অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।
পাঁচ: সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান; মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।
ছয়: দু’দেশের বাণিজ্য হবে খোলা বাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হিসাব হবে বছরওয়ারি এবং যার যা পাওনা সেটা স্টারলিং-এ পরিশোধ করা হবে।
সাত: বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যত দূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে। [সূত্র: হক কথা সমগ্র, ঘাস ফুল নদী প্রকাশন, পৃষ্ঠা: vii]
অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের পরপরই তিনি মূর্ছা যান। [মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ‘র’ এবং সিআইএ, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ৭৪]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানীকে বাদ দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ বিতর্কের সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বলেন, “প্যারিস থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে কলকাতা ফেরার পরপরই ওসমানী সাহেব আমাকে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত খালেদ মোশাররফকে দেখে আসতে অনুরোধ করেন। খালেদ মোশাররফ নিজে আমাকে দেখতে চেয়েছেন। খালেদ মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের অত্যন্ত প্রিয়জন। কলকাতা থেকে সরাসরি লক্ষ্ণৌর ফ্লাইট না পাওয়ায় দিল্লি হয়ে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি। দিল্লিতে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষাতে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, ‘সব ঠিক হয়ে গেছে, আপনারা ডিসেম্বরে ঢাকা ফিরতে পারবেন। প্রবাসী সরকারের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয়েছে।’ আশ্চর্য হলাম, ওসমানী সাহেব তো আমাকে কিছুই বলেননি।
“লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল কমান্ড হাসপাতালে খালেদ মোশাররফ আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘আমাকে লন্ডনে নিয়ে চলুন। ভারতীয়রা আমাদেরকে ভুটান-সিকিম বানাবে। তারা আমাদের চাইনিজ অস্ত্র নিয়ে ভারতীয় নিম্নমানের অস্ত্র দিচ্ছে, আমাদেরকে তাদের পদানত করে রাখার জন্য।’ আমি বললাম, ‘আপনার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা তো আমিই করতে পারি, কিন্তু ভারতীয়রা আপনাকে ভারত ছাড়ার অনুমতি দেবে তো? বিষয়টি আমি সর্বাধিনায়ককে জানাব।’
“ফেরার পথে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। দিল্লি-কলকাতার একটা ফ্লাইট লক্ষ্ণৌ হয়ে যায়। প্লেনে উঠে দেখি আমার পাশে আবদুস সামাদ আজাদ এমএনএ। তিনি নিম্ন থেকে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তিনি ন্যাপ-ভাসানী দল করতেন। অনেকটা সময় জেলে ছিলেন। চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এলে, ওনার পুলিশ গার্ডকে আমাদের ক্যান্টিনে বসিয়ে ভালো করে খাওয়াতাম এবং সামাদ ভাইকে গোপনে তাঁর আগামসি লেনের বাসায় পাঠিয়ে দিতাম। স্ত্রীর সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে বিকেলে জেলে ফেরত যেতেন। তাঁর চিকিৎসাপত্রে পুনরায় পরের সপ্তাহে চিকিৎসার জন্য আসার নির্দেশ লিখে দেবার ব্যবস্থা করতাম। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক, আমার দোর্দন্ড প্রতাপ, আমি সবার প্রিয়। সামাদ ভাই বললেন, ‘তুমি কিন্তু আমাকে দেখোনি। কাউকে বলবে না। এয়ারপোর্টে আমার গাড়ি থাকবে, সেটা নিয়ে তুমি চলে যেও। আমার জন্য অন্য একটি গাড়ি থাকবে। তুমি আমার কথা কাউকে বলো না।’
“আমার অনুসন্ধিৎসা বাড়ল, জিজ্ঞেস করলাম, ‘দিল্লিতে কী করলেন? কোনো চুক্তি হয়েছে কি?’ সামাদ ভাই উত্তর দিলেন না। আমার সন্দেহ দৃঢ় হল। কলকাতা পৌঁছে সোজা থিয়েটার রোডে ওসমানী সাহেবের রুমে গেলাম। রেগে বললাম, ‘দেশ তো বেচে দিয়েছেন’। তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। আমি খালেদ মোশাররফ ও আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে আমার কথোপকথনের কথা বললাম। আবদুস সামাদ আজাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তাঁদের সঙ্গে আলাপের বিস্তারিত তথ্য জানালাম। আরও জানালাম দিল্লির বিশিষ্টজন আমাকে কী বলেছেন। ওসমানী সাহেব সোজা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের ঘরে ঢুকে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, You sold the country, I will not be a party to it. তাজউদ্দীন সাহেব কর্নেল ওসমানীকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, নিচু স্বরে কী বললেন, আমি শুনতে পেলাম না। আমি দরজার বাইরে ছিলাম।
“কয়েক দিন পরে উভয়ের মধ্যে পুনরায় বাকবিতন্ডা ভারতীয় একটি প্রস্তাবনা নিয়ে। ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হলে আইনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বেশ কয়েকজন ভারতীয় বাঙালি প্রশাসনিক ও পুলিশ অফিসাররা বাংলাদেশের সব বড় শহরে নির্দিষ্ট মেয়াদে অবস্থান নেবেন। ওসমানী সাহেব বললেন, ‘এটা হতে পারে না, আমাদের বহু বাঙালি অফিসার আছেন। কেউ কেউ পাকিস্তানে আটকা পড়েছেন। এরা নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।’
“ওসমানী সাহেবের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীদের মতপার্থক্যের কথা জেনে ভারতীয়রা আরও সতর্ক হলেন। ওসমানী সাহেবকে তাঁরা কড়া নজরে রাখলেন। কাগজে-কলমে যৌথ কমান্ডের কথা থাকলেও বস্তুত তাঁরা ওসমানী সাহেবকে একাকী করে দিলেন। ভারতীয়রা সব কমান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলেন। ওসমানী সাহেবের সঙ্গে ভারত কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটল।
“১৬ ডিসেম্বরের বিমান দুর্ঘটনা, তাৎপর্যটা কী? পরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশি গেরিলাদের সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী অতর্কিতে সরাসরি যশোর সীমান্তে আক্রমণ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। যৌথ কমান্ড বাহিনীর অন্যতম এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানীর যশোর পরিদর্শনে বাধা সৃষ্টি করা হলে তিনি ছাত্রনেতা কে এম ওবায়দুর রহমান ও আমাকে ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ যশোরের অবস্থা দেখে আসার জন্য নির্দেশ দেন। ওই দিনই আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়ি। ভারতীয় সেনারা একের পর এক পাকিস্তানি অফিসারদের বাসস্থানের এসিসহ বিভিন্ন সামগ্রী, অস্ত্রাগার, এমনকি যশোর সিএমএইচের যন্ত্রপাতি লুট করছে। বলছে, ‘বেঙ্গল রেজিমেন্ট এত বৈভব ও আরাম-আয়েশে ছিল, কেন বিদ্রোহ করেছে!
“বিষয়টা ফোনে ওসমানী সাহেবকে জানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে ৭ ডিসেম্বর আমি কলকাতা ফিরে আসি। ওবায়দুর রহমান তাঁর জেলা ফরিদপুরের পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। কলকাতায় পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে আমি পুরো বিষয়টি ওসমানী সাহেবকে জানানোর পর, তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদকে সেটা অবহিত করেন। ভীষণ দুঃখের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বললেন, ‘তাহলে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তফাৎটা কোথায়?’ ওসমানী সাহেব বললেন, ‘বুঝতে পারছেন, ভারতীয়রা আমাকে কেন সরাসরি সমরাঙ্গনে যেতে দিচ্ছে না, তাদের উদ্দেশ্য ভালো না।’
“কয়েক দিন অক্লান্ত চেষ্টার পর, কুমিল্লা হয়ে সিলেট পরিদর্শনের জন্য একটি বড় হেলিকপ্টার, সম্ভবত এম-৮ দেয়া হলো ব্রিগেডিয়ার গুপ্তের তত্ত্বাবধানে। ১৩ ডিসেম্বর বিকেলে আমরা কুমিল্লা পৌঁছি। বিশ্রামের জন্য কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পৌঁছে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। ওসমানী সাহেবকে হাত বাড়িয়ে ‘রিসিভ’ করছেন কয়েকজন ভারতীয় বাঙালি। একে একে পরিচয় দিলেন, ‘আমি মুখার্জি IAS, আমি গাঙ্গুলী IPS, ইত্যাদি।’ তাঁরা বললেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে গতকাল এখানে পৌঁছেছি কুমিল্লা মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা দেবার জন্য। অবশ্য এখনও কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধ চলছে।’
“ওসমানী সাহেব ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করতে রাজি না হওয়ায় আমরা ওয়াপদা গেস্ট হাউসে যাই। পরের দিন ভোরবেলা থেকে ওসমানী সাহেব কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা পরিদর্শনে বিভিন্ন পথে গেরিলাদের পাঠান এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর সেনাদের সম্মুখ আক্রমণে উৎসাহ দান করেন। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল ভেঙে যায়। পরের দিনই তারা আত্মসমর্পণ করে। খবর পাই, ঢাকার পতন আসন্ন। আমরা ঢাকা যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি।
“১৬ ডিসেম্বর সকালে ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত জানালেন, আজ ঢাকায় পাকিস্তান সেনারা আত্মসমর্পণ করবে। ভাবলাম নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের কাছে। কিন্তু আশ্চর্য, ওসমানী সাহেব একবারে চুপ, কোনো কথা বলছেন না। খটকা লাগল।
“জেনারেল ওসমানীর এডিসি আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামাল আমাকে বলল, ‘স্যার কখন রওনা হবেন, তা তো বলছেন না। জাফর ভাই, আপনি যান, জিজ্ঞেস করে সময় জেনে নিন। অধীর আগ্রহে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।’ আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করায় ওসমানী সাহেব বললেন, I have not yet received PM’s order to move to Dacca. আমি বললাম, ‘আপনাকে অর্ডার দেবে কে? আপনি তো মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক।’ ওসমানী বললেন, I decide tac-tics, my order is final for firing, but I receive orders from the cabinet through PM, Mr. Tajuddin Ahmed. কথাগুলো বললেন অত্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে। পরিষ্কার হলো, তিনি আসন্ন ঢাকা পতনের সংবাদ জানেন এবং প্রবাসী সরকারের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন।
“আমাদের অস্থিরতা বাড়ছে আর বাড়ছে। শেখ কামাল বারবার আমাকে চাপ দিচ্ছে পুনরায় ভালো করে বুঝিয়ে বলে ওসমানী সাহেবকে রাজি করাতে ঢাকা রওনা হবার জন্য। ঘণ্টাখানেক সময় পরে, পুনরায় ওসমানী সাহেবের সামনে দাঁড়ানোর পরপরই তিনি অত্যন্ত বেদনার্ত কণ্ঠে যা বললেন তার মর্মার্থ হলো, ‘আমার ঢাকার পথে অগ্রসর হবার নির্দেশ নেই। আমাকে বলা হয়েছে পরে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে একযোগে ঢাকা যেতে, দিনক্ষণ তাজউদ্দীন সাহেব জানাবেন। গণতন্ত্রের আচরণে যুদ্ধের সেনাপতি প্রধানমন্ত্রীর অধীন, এটাই সঠিক বিধান।’ মনে হলো, তিনি জেনেশুনে বিষপান করছেন। পরে ব্রিগেডিয়ার গুপ্তকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সিলেটের কী অবস্থা?’ ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত জানালেন ‘সিলেট ইজ ক্লিয়ার’।
“ওসমানী বললেন, ‘তাহলে চলুন আমরা সিলেট যাই, সেখানে গিয়ে আমার পিতামাতার কবর জিয়ারত করব, শাহজালালের পুণ্য মাজারে আমার পূর্বপুরুষরা আছেন।’ ওসমানী সাহেব শেখ কামালকে ডেকে সবাইকে তৈরি হতে বললেন। আধাঘণ্টার মধ্যে আমাদের আকাশে নিরুপদ্রব যাত্রা। ভারতীয় এম-৮ হেলিকপ্টারে সিলেটের পথে চলেছি। পরিষ্কার আকাশ। হেলিকপ্টারের যাত্রী জেনারেল ওসমানী ও তাঁর এডিসি শেখ কামাল, মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল এম এ রব এমএনএ, রিপোর্টার আল্লামা, ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত, ভারতীয় দুই পাইলট এবং আমি। কেউ কথা বলছেন না, সবাই নীরব।
“অতর্কিতে একটি প্লেন এসে চক্কর দিয়ে চলে গেল। হঠাৎ গোলা বিস্ফোরণের আওয়াজ, ভিতরে জেনারেল রবের আর্তনাদ। পাইলট চিৎকার করে বলল, ‘উই হ্যাভ বিন অ্যাটাকড।’ রবের উরুতে আঘাতের পরপরই তার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলো। আমি এক্সটার্নাল কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দিতে শুরু করি। পাইলট চিৎকার করলেন, ‘অয়েল ট্যাংক হিট হয়েছে, তেল বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি বড়জোর ১০ মিনিট উড়তে পারব।’ কো-পাইলট গুনতে শুরু করলেন— ওয়ান, টু, থ্রি… টেন…. টুয়েন্টি … থার্টি … ফোরটি…… ফিফটি …. নাইন সিক্সটি-ওয়ান মিনিট গন। এভাবে মিনিট গুনছেন উদ্বিগ্ন চিন্তিত সহ-পাইলট। অন্য পাইলট ধীরস্থিরভাবে পাইলটের আসনে বসা। ওসমানী সাহেব লাফ দিয়ে উঠে, অয়েল ট্যাংকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, ‘জাফরুল্লাহ, গিভ মি ইয়োর জ্যাকেট’। আমি আমার জ্যাকেটটা ছুড়ে দিলে, ওসমানী সাহেব সেটা দিয়ে তৈলাধারের ছিদ্র বন্ধের চেষ্টা করতে থাকলেন। বললেন, Do not worry my boys, I know Sylhet like the palm of my hands. কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দেবার ফাঁকে ফাঁকে আমি ভাবছিলাম, আজ ১৬ ডিসেম্বর, দেশ স্বাধীন হবে। কিন্তু আজ আমরা সবাই কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাব। আগামীকাল পত্রিকায় শোক সংবাদ কলামে কী লেখা হবে? বীরের মৃত্যু, অপঘাতে মৃত্যু? কার গোলাতে এই দুর্ঘটনা?
“পাকিস্তানের সব বিমান তো কয়েক দিন আগেই ধ্বংস হয়েছে কিংবা গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। তাহলে আক্রমণকারী বিমানটি কাদের? গোলা ছুঁড়ে সেটি কোথায় চলে গেল? গৌহাটির পথে?
“চিন্তা বিঘ্নিত হলো ওসমানী সাহেবের চিৎকারে। নিচে একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, Land here। আরও বললেন, Let me land first to taste the enemy attack if there is one. লাফ দিয়ে তিনি নামলেন, ‘ধরুন’ বলে আমি জেনারেল রবকে ছুড়ে দিলাম, সঙ্গে নামলাম নিজেও। আমার পিছনে পিছনে অন্যরা লাফিয়ে নামলেন। হেলিকপ্টারটা আমাদের চোখের সামনে দাউ দাউ আগুনে পুড়ছে।
“হঠাৎ গ্রামবাসী এসে ওসমানী সাহেবকে ঘিরে ধরল, ‘দুশমন আইছে রে বা দুশমন আইছে, দুশমনরে ধর।’ পরপরই ভালো করে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ‘আমাদের কর্নেল সাব রে বা।’ তারপর তাঁকে নিয়ে নাচতে শুরু করল।… হেলিকপ্টারে ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত এবং শেখ কামালও সামান্য আহত হয়েছিলেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কখনও এই ঘটনার তদন্ত প্রকাশ করেননি।”
[সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ জুন ২০১৩ সংখ্যা]
একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির ভারতের পূর্বাঞ্চলের এবং বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের ঘটনা আপনাদের সবার জানা।
আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তানের আত্মসমর্পণকৃত তিরানব্বই হাজার সৈন্যকে জিম্মি করে ভারত সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করে নেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তির মুখে ডিসেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে এবং যুদ্ধবন্দি হিসেবে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে এদের বিচার করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারত তাদের নিজেদের স্বার্থে তা হতে দেয়নি। এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সিমলায় এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়ে (২৮ জুন হতে ২ জুলাই ১৯৭২) দীর্ঘ আলোচনার পর একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে ভারত ও পাকিস্তান তাদের সকল বৈরিতার অবসান ঘটানো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে বিরাজমান স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এই চুক্তির অধীনে ভারত সকল যুদ্ধবন্দিকে বিনা বিচারে পাকিস্তানে ফেরত পাঠায়। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অমীমাংসিত বিষয়গুলো ঝুলে যায়। শিমলা চুক্তির দফাগুলো নিম্নরূপ:
১. দুই দেশ সম্মিলিতভাবে নির্ণয় করল ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে সর্বশেষ পাকিস্তান আর্মি ভারতীয় সেনাদের নিকট অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে কাশ্মীর সীমান্তে যাদের সৈনিক যে অবস্থান গ্রহণ করেছে, সেই সেই দেশের সীমানা মানা হবে। এই সীমানাকে ভারত পাকিস্তান এলওসি বা লাইন অব কনট্রোল মেনে নিল ।
২. সিমলা চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানি ৯৩ হাজার বন্দী সেনাদের ভারত ছেড়ে দিল, এই শর্তে যে তাদের বিচার পাকিস্তান নিজেই করবে যারা পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে যুদ্ধকালীন অপরাধে জড়িত ছিল ।
৩. উপরন্তু, পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় সৈনিক দ্বারা কবজাকৃত সীমানা ভারত ছেড়ে দিল বিনা শর্তে ।
৪. ভবিষ্যতে ভারত পাকিস্তান কোনো সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা থেকে দুই দেশই বিরত থাকবে ।
৫. দুই দেশের সেনারা কোনোভাবেই এলওসি সীমানা অতিক্রম করবে না ।
৬. সাধারণ জনগণের আসা যাওয়ার জন্য বর্ডার থাকবে, যাতে করে দুই দেশের জনগণ আত্মীয়-পরিজনের সাথে মিলিত হতে পারে।
[সূত্র: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১ অক্টোবর ২০১৬]
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়কে ‘ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়’ দাবি করে গত ১৬ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টুইট বার্তা একাত্তর নিয়ে পাকিস্তানের প্রোপাগান্ডাকেই সত্যি বলে প্রমাণ করে। একাত্তর নিয়ে ‘ভারতের বাংলাদেশ যুদ্ধ’ ক্রমশ নতুন প্রজন্মের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ভারতের স্বার্থের কারণে ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্ত আর দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর পরও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের গণ আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হয়ে যায়। আমাদের জনযুদ্ধ ভারতের ক্রীড়নক বনে যায়। ফলে স্বাধীনতার তেপান্ন বছর পরে কথিত বড়োভাই ভারতের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু বুঝে নেবার তাগিদ জন্ম নিয়েছে এই প্রজন্মের মাঝে। সাবালক অবস্থায় সে তার ন্যায্য হিস্যা বুঝে চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক। এইসব প্রশ্নের মীমাংসা ব্যতীত ভারতকে উপরিভাগ মায়াকান্না ও আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব পরিবারকে স্বাধীনতার ধ্বজাধারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তবেই বাংলাদেশের অসমাপ্ত মুক্তির যুদ্ধ সমাপ্ত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ভারত যত তাড়াতাড়ি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ততই আমাদের দুই দেশের মাঝে সম্পর্ক অকৃত্রিম ও জনতানির্ভর হয়ে উঠবে। এই বাস্তবতা ঐতিহাসিক এবং অবধারিত।
যারা মনে করেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা হয় মুক্তিযুদ্ধ বোঝেন না, নয়তো চেতনা ব্যবসায়ী। তাঁরা চব্বিশের তরুণদের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে সক্ষম হবেন না। একাত্তর থেকে চব্বিশ— আমাদের যে একটা অসমাপ্ত লড়াই রয়ে গেছে, ব্যক্তি আর গোষ্ঠীস্বার্থে তারা তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। ভুলিয়ে দিয়েছিল। ’৪৭, ’৫২, ’৬৯, ’৭১ আর ’৯০-এর প্রতিশ্রুত বাংলাদেশ গড়ার ব্যর্থতা চব্বিশের তরুণদের অবধারিতভাবে রাজপথে নামিয়ে এনেছে। একাত্তরের অসমাপ্ত লড়াইটাই চব্বিশ আবার নতুন করে আমাদের সামনে হাজির করেছে। এই লড়াই শুধু ক্ষমতার পালাবদলের লড়াই নয়। ফ্যাসিবাদী ব্যাবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের লড়াই। ইতিহাসের বাঁক বদলের লড়াই। কথিত বড়োভাই, মেজোভাইদের কাছে ন্যায্য হিস্যার লড়াই। বিশ্বকে পথ দেখাবার লড়াই। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লড়াই।
আজাদ খান ভাসানী
সদস্য সচিব, ভাসানী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি