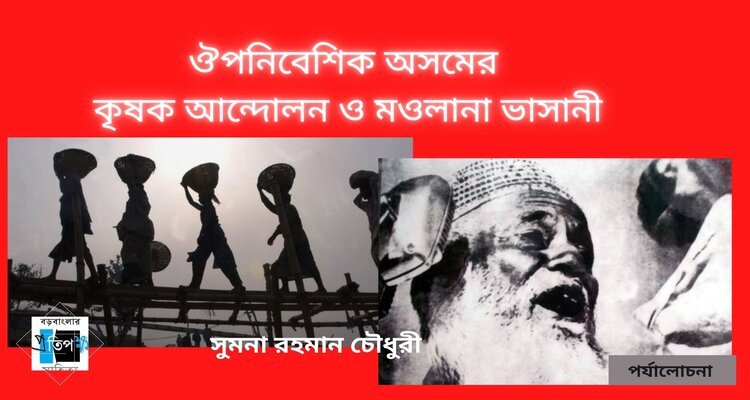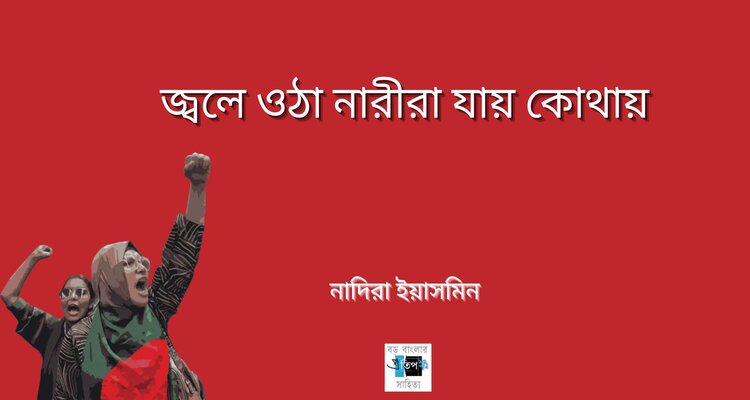
।। নাদিরা ইয়াসমিন ।।
আমাদের অর্থনীতি, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, আইন, শিক্ষা ইত্যাদি নারীদের রাজনীতির সঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক রাখার মতো অনুকূল কি না, শুরুতেই যদি এই প্রশ্ন করি, তাহলে উত্তর মিলবে, না! শ্রমজীবী নারীকে ৩ বেলা পেটের আহার জোগাড় করতেই দিনের সব সময় এবং শরীরের সব শক্তি ফুরিয়ে যায়। অন্য কিছুর দিকে ফিরে তাকানোর মতো ফুরসত, শক্তি, মানসিকতা আর অবশিষ্ট থাকে না তাদের। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষের তুলনায় নারীর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে লেগে থাকার ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা হয়ে সামনে আসে। এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মূলে রয়েছে পৈত্রিক সম্পত্তির প্রাপ্তিহীনতা ও অনিশ্চয়তা। ‘জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট’ (১৯৯৫) শীর্ষক প্রবন্ধে অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত নারী কীভাবে নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব হারান। তিনি দেখান, সামাজিক ন্যায়বিচারের মৌলিক ও আবশ্যিক অনুষঙ্গ হচ্ছে লৈঙ্গিক সমতা। আর সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার সেই সমতার প্রাথমিক ধাপ, যা আমাদের দেশে নারীদের নেই।
কোনো আন্দোলন সংগ্রাম কতটা সফল হবে তা অনেকটা নির্ভর করে সেই আন্দোলনে কী পরিমাণ নারীর অংশগ্রহণ, সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল তার উপর। কেননা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ কেবল আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিই বদলে দেয় না, নিষ্ক্রিয় দোদুল্যমান পুরুষদেরও আন্দোলনের দিকে টেনে নিয়ে আসে। এটা নিকট অতীতের যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন (১৯৯৮), শামসুন্নাহার হল আন্দোলন (২০০২), কোটা সংস্কার আন্দোলন (২০১৮), নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন (২০১৮), প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাট-বিরোধী আন্দোলন (২০১৫) শুধু না, দূর অতীতের বিদ্রোহ, যুদ্ধ, আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। সদ্য ঘটে যাওয়া জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শুরু থেকেই বিপুল সংখ্যক নারী শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এবং ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্বিচার হামলা আন্দোলনের মোড়ই পালটে দিয়েছিল। প্রথম দিকে কেবল বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোর মধ্যে চলা শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এরপর আর তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা দেশের শিক্ষার্থী ও সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশি গণমাধ্যমগুলোতেও নারী শিক্ষার্থীদের ওপর এই নির্যাতনের চিত্র সেদিন গুরুত্ব সহকারে স্থান করে নিয়েছিল।
২
বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মেয়েদের শুধু অন্যায্য মুক্তিযোদ্ধা কোটা না, তাদের নিজেদের জন্য বরাদ্দ কোটা সুবিধার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়েছিল। ফলে তাদের প্রত্যেকের নিজেদের সাথে এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে শুরুতে। এছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক বাধাবিপত্তি তো ছিলই। ৩ আগস্ট শেষ বিকালে কর্মসূচি শেষে তাহমিদ চত্বর থেকে ফেরার পথে আন্দোলনে যাওয়া শিবপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সাদিয়া আফরিন বলছিলেন, গত দুই দিন তাকে বাড়ি থেকে কর্মসূচিতে আসতে দেওয়া হয়নি বলে আসতে পারেননি। সেজন্য তিনি ওই ২ দিন বাড়িতে অনশন করেছেন এই বলে যে, “মৃত্যু হতে পারে বলে যদি আন্দোলনে যেতে না দেয়া হয়, তাহলে বাড়িতে থেকে অনশন করে মরে যাব।” পরে বাধ্য হয়ে অভিভাবক তাকে ৩ আগস্ট আন্দোলনে আসতে দিয়েছে! ৪ আগস্টও একটা মেয়ে বলছিল, “গত ২ দিন আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিল। আজ ছাড়া পেয়ে চলে এসেছি।” নরসিংদী সরকারি কলেজে সায়েন্সে পড়া একটা মেয়ে বলছিলেন, “কলেজের এক ম্যাডাম ফোন দিয়ে হুমকি দিয়েছে, আন্দোলনে গেলে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় নম্বর দিবে না, ফেইল করিয়ে দিবে।” বাসায় মাকে ঔষধ কিনতে যাওয়ার কথা বলে ৫ মাসের অন্তঃসত্তা নারী অঙ্গনের অ্যাডমিন প্যানেলের সদস্য ও নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী নাহিদা আঁখি ১৬ তারিখে আন্দোলনে গিয়েছিলেন। ১৮ জুলাই, ২ আগস্টও বাড়িতে না জানিয়ে লুকিয়ে তিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।
আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এখনও নারী কোটা রাখার বিরুদ্ধে হলেও নারী অঙ্গনের অধিকাংশ বন্ধু ও নারী সংগঠনগুলো নারী কোটা রাখার পক্ষে থাকায় আমার নিজের ও নারী অঙ্গনের বন্ধুদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে শুরুর দিকে। কিন্তু আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। ১১ জুলাই বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘নারী অঙ্গন’ (নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করার একটি প্ল্যাটফর্ম) তাদের সমর্থন জানায়। প্রায় প্রত্যেকটা মেয়েরই এইরকম কোনো না কোনো গল্প আছে দেখা যাবে, যা অতিক্রম করে তারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এত সব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এবং তাঁরা সংগঠক, নেতা ও কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন সমান তালে।
৩
উমামা ফাতেমা একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে বলছিলেন, জুলাইয়ের শুরুর দিকে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছেলেদের চেয়ে বেশি ছিল। সেটা ৬০-৭০ পার্সেন্টও হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ভ্যাকেন্ট করে দেওয়ায় ১৮ তারিখের পর নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অনেকটা কমে যায়, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এমনটাই দেখেছি। এই সময়টা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, স্কুলের শিক্ষার্থী এবং শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, হকার ও সাধারণ জনগণ আন্দোলনের মাঠে ছিল মূলত। ইন্টারনেট পুনরায় চালু হলে এবং গ্রেফতার, হয়রানি, খুন কিছুটা কমে এলে জুলাইয়ের শেষ দিকে নারীদের উপস্থিতি আবারও বেড়ে যায়। সন্তানদের সাথে নিয়ে অনেক বাবা মা-ও আন্দোলনে নেমে আসেন। বছরের পর বছর ধরে আর্থিক ও বিবিধ সরকারি সুবিধাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-নাতি-পুতিরা চাকরি সহ সকল ক্ষেত্রে এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে তাদের সন্তানদের কোটা সুবিধার জন্য মরিয়া, সেখানে কোটা তথা বাড়তি সুবিধাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে সম অধিকার প্রদানের পক্ষে নারীর সম্মতি, অবস্থান ও বাস্তবায়নের লড়াইয়ে তাদের এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান। আন্দোলনের সময় অনেক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কোটা পদ্ধতি নিয়ে। তাঁরা সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরি পেতে চান, কোনোরকম দয়া করুণার মাধ্যমে না!
৪ জানুয়ারি নরসিংদীতে নাগরিক কমিটির এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালে এইচএসসি পাশ করা মীম নামের আন্দোলনকারী এক শিক্ষার্থী জানান, ছাত্রলীগ পরিচয় দিয়ে তাকে এবং আরও কিছু নারী শিক্ষার্থীকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এতে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমি নিজেও পরে তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি। মীম জানান কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলেও তাঁরা ভীত নন। তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবেন।
৪
গত ২২ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মাণিক মিয়া সেমিনার কক্ষে গণঅভ্যুত্থানে শহিদ, আহত ও অংশগ্রহণকারী নারীদের নিয়ে কাজ করা দু’টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (লড়াকু ২৪ ও এমপাওয়ারিং আওয়ার ফাইটার্র) আয়োজিত গণঅভ্যুত্থানের নারীদের সংলাপ ‘নারীরা কোথায় গেল?’ অনুষ্ঠানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে লেখক ও নৃবিজ্ঞানী রেহনুমা আহমেদ, নারী বিষয়ক কমিশনের প্রধান শিরিন পারভিন হক সহ গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে কাজ করা নারীদের চাঁদের হাট বসেছিল। তাঁরা অনেকেই অভ্যুত্থান ও অভ্যুত্থান পরবর্তী অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেদের ভাবনা, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছেন।
বিগত জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সারা দেশে নেতৃত্ব দেওয়া নারীদের মধ্যে উমামা ফাতেমা অন্যতম, যিনি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্বে ছিলেন। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নেতৃত্ব দেওয়া নারীদের সাথে তার এক প্রকার যোগাযোগ তৈরি হয়, যোগাযোগ আছে। নিজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আরও কয়েকজন নারী নেতৃবৃন্দের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে তিনি জানান, “৫ আগস্টের পর কেন্দ্র থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মেয়েদেরও আন্দোলনের আয়োজকদের পক্ষ থেকে কর্নার করে ফেলার চর্চা হয়েছে। ৫ আগস্টের পর থেকে দেখি সিনারিও থেকে আমি কমপ্লিটলি নাই, টোটালি ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছি!” নরসিংদীতেও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করা কারও কারও কাছ থেকে এমন অনুভূতির কথা বলতে শুনেছি। কর্নার করে দেওয়ার এই অনুভূতির মুখোমুখি আমি নিজেও হয়েছি বিজয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই। যদিও আন্দোলনে অংশগ্রহণের খবর নিউজ মিডিয়ায় কয়েক দিন আসায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মান, প্রশংসা পেয়েছি এবং এখনও পাই। ট্রেনিং শেষে ২২ জুলাই ঢাকা থেকে ফেরার পর জুলাইয়ের শেষ দিকে আন্দোলনের সবচেয়ে সংকটময় সময়টাতে নরসিংদীর আন্দোলনকারীদের সাথে আমার যোগাযোগ হয়। এরপর তারা অনেকেই আমার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছে। কিন্তু দেখা গেল ৫ আগস্টের সপ্তাহখানেক পরেই নরসিংদীতে শহিদ পরিবারের সদস্য, আহত ও আন্দোলনকারীদের সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাক্ষাৎ এবং আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাকে ইনভাইট করা হয়নি। পেশাগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিজয় পরবর্তী বাংলাদেশে সরাসরি যুক্ত থেকে দেশ গড়ায় ভূমিকা রাখার ইচ্ছে থাকলেও নিজেকে এরপর তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছি। যদিও তাদের কারও কারও সাথে মাঝে মাঝে আলাপ হয়, কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা হয়।
৫
২০১৪ সালে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি নরসিংদীতে বদলি হয়ে আসি। এর আগে প্রায় আড়াই বছর শ্রীমঙ্গলে ছিলাম। সেখানে অবস্থানকালে ব্যাংক কর্মকর্তা ও টুকটাক লেখালেখির সাথে যুক্ত এক পুরুষ বন্ধুর সাথে একটা সাহিত্য পত্রিকা বের করার উদ্যোগ নেই শ্রীমঙ্গল থেকে। পত্রিকা বের করার আইডিয়া ও প্রস্তাব দুটোই আমার ছিল। কথা ছিল দু’জনেই সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করব। পত্রিকার নাম, লেখাপত্র, কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ চলছিল। এর মধ্যে ৮/১০ দিনের একটা ছুটি পেয়ে যাওয়ায় ঢাকায় বরের কাছে চলে যাই। ঢাকায় অবস্থানকালেও পত্রিকার কাজ নিয়ে আলাপ এগিয়ে চলছিল। ঢাকা থেকে ফেরার কয়েক দিন পর হঠাৎ একদিন সেই বন্ধুটি আমাকে সারপ্রাইজ দিতে বাসায় চলে আসে এবং সাথে নিয়ে আসে কলেজ রোড নামে একটা ২ ফর্মার পত্রিকা! আমার হাতে সেদিন পত্রিকাটি তুলে দিয়ে জন্মের সারপ্রাইজ করে দিয়েছিল বন্ধুটি! এমনই সারপ্রাইজ যে, আজও ভুলিনি সে কথা!
এক দশক আগে নরসিংদীতে বদলি হয়ে আসার কিছু দিনের মধ্যেই এখানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সাথে জড়িয়ে যাই। আমাকে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কীভাবে কর্নার করার, অপাঙ্ক্তেয় করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, সে ইতিহাস লিখতে বসলে নরসিংদীতে এক দশক নামে কয়েকশো পৃষ্ঠার ঢাউস সাইজের একটা বই হয়ে যাবে। সেই ইতিহাস লেখার সুযোগ এখানে নেই। তবে সাম্প্রতিক কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ না করলে সক্রিয়-প্রাগ্রসর-সম্ভাবনাময়-পরিশ্রমী নারীদের কীভাবে কর্নার করার চেষ্টা করা হয়, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যাবে না।
শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র আমিই আন্দোলনের পক্ষে নিজের অবস্থান জানান দিয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি, শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে আমাদের ক্যাডারের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট দিই। এবং সেটা শিক্ষার্থীরা প্রায় নিশ্চিত জয়ের কাছাকাছি জেনে আগস্টে এসে না, ১৬ জুলাই যেদিন প্রথম সারা দেশে আবু সাঈদ-সহ গুলিতে ৬ জন শিক্ষার্থী শহিদ হয়, সেদিন সন্ধ্যায়ই। সেদিন আমাকে কিছু সহকর্মী স্ক্রিনশট রেখে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নরসিংদীর শিক্ষকদের মধ্যেও একমাত্র আমিই সংকটময় মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের পাশে রাজপথে নেমে আসি। অনলাইনে তো সক্রিয় ছিলামই। আমি শিক্ষার্থীদের সাথে এসে যোগ দেওয়ায় অন্য শিক্ষকরাও যেন ঢাল হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান, সেই প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে তখন শিক্ষা নগরী নামে পরিচিত নরসিংদীর শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দানা বাঁধে। শিক্ষার্থীরা ৩১ জুলাই নরসিংদী সরকারি কলেজের শিক্ষকদের গায়েবানা জানাজা পড়ার ঘোষণা ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন। শিক্ষার্থীদের ক্ষুব্ধ মনোভাব টের পেয়ে এবং নিশ্চিত বিজয়ের আভাস বুঝতে পেরে শিক্ষার্থীদের সমর্থনে ৪ আগস্ট নরসিংদীর শিক্ষকরা নরসিংদী সরকারি কলেজের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করে দুপুর ১২টার দিকে। যে জন্য এত কথা বলা, আয়োজকরা সেই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখা সকল শিক্ষকের বক্তব্য লাইভ সম্প্রচার করলেও আমারটা করেনি।
গত ২৮ নভেম্বর স্কুল, কলেজ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কার্যালয়গুলোতে বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনে শহিদ ও আহতদের নিয়ে স্মরণসভা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয় মন্ত্রণালয় থেকে। এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কলেজে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। জুলাই অভ্যুত্থানে আমি ছাড়া নরসিংদী সরকারি কলেজের শিক্ষকদের কী ভূমিকা ছিল, নরসিংদীর সবাই যেমন জানেন এবং আমার ভূমিকাও কলেজের সবাই জানেন। কিন্তু গণঅভ্যুত্থান নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটিতে, এমনকী কোথাও আমাকে রাখা হয়নি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিট ও আনন্দকে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ২ মাসব্যাপী চলমান ‘তারুণ্যের উৎসব-২০২৫’-এর কমিটিতেও আমাকে রাখা হয়নি।
আমি কলেজের কাজের বাইরে সারাদিন মেয়েদের নিয়ে থাকি, তাদের অধিকার, সুযোগসুবিধা নিয়ে কথা বলি, পরামর্শ দিই, পড়াশোনা করি, লেখালেখি করি, খোঁজখবর রাখি। কিন্তু কলেজের ছাত্রী হয়রানি প্রতিরোধ কমিটিতে আমি নেই, আমাকে রাখা হয়নি। যাদের এইসব নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই, সময় নেই, নেই পড়াশোনা, জানা-বোঝা, তাদের রাখা হয়েছে সেই কমিটিতে! ক্ষুব্ধ হলেও মনে মনে হেসেছিলাম সেদিন, কলেজে ছাত্রী হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার পর এর প্রধান এসে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, নাদিরা, এইটা কী জিনিস? মজার ব্যাপার হল, নারী শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত ব্যাপারে কলেজ প্রশাসন জানার আগেই আমি জেনে যাই সব। কারণ ছাত্রীরা এইসব ব্যাপারে সবার আগে আমার কাছে আসে। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং না? বছর দেড়েক আগে কলেজের দুই জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী শিক্ষার্থীদের সাথে যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে আমার কাছে ছাত্রীরা এলে কলেজ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করার পরামর্শ দিই। কিন্তু কলেজ প্রশাসনের কাছে গেলে তারা আশ্বাস দিয়েও পরবর্তীতে কোনোরকম ব্যবস্থা নেননি সেই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ভবিষ্যতে এইরকম কোনো অভিযোগ আমার কাছে প্রমাণ-সহ এলে আমি নিজেই সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করব।
ব্রহ্মপুত্র নামে নরসিংদীতে জেলাভিত্তিক একটা মাসিক ফিচার পত্রিকা ছিল। ছিল বলছি, কারণ কয়েক মাস আগে পত্রিকাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর সম্পাদক, প্রকাশক ও এর সাথে যুক্ত সবাই আমার খুব পরিচিত, যারা নরসিংদীতে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে এতদিন লিডিং পোজিশনে ছিল। এরা নরসিংদীতে জন্মগ্রহণ করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিদের নিয়ে, উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও অনুষ্ঠান নিয়ে নিয়মিত ফিচার প্রতিবেদন ও নিউজ করত। আমরা বছর তিনেক ধরে নারীদের নিয়ে নিয়মিত পাঠ আড্ডা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, আলোচনা অনুষ্ঠান, পত্রিকা প্রকাশ, সাইক্লিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও মেয়েদের ফ্রি সাইক্লিং প্রশিক্ষণ দিয়ে আসলেও আমাদের নিয়ে তাদের পত্রিকায় কোনো নিউজ, আলাপ নেই। যদিও নরসিংদীর দশটা সংগঠন মিলে অনুষ্ঠান করলে যে পরিমাণ উপস্থিতি থাকে, আমাদের একলা নারী সংগঠনের কয়েক গুণ বেশি উপস্থিতি সত্ত্বেও সেইসব সংগঠনের আড্ডা, কালেভদ্রে করা আলোচনা অনুষ্ঠান কখনোই তাদের পত্রিকার নজর না এড়ালেও, আমাদেরটা তাদের নজরে আসত না। শুধু তা-ই না, নরসিংদী সরকারি কলেজের প্রায় ৪০ কোটি টাকা মূল্যের ৩০ শতকের মতো জায়গা শিক্ষা-স্বার্থ ও ছাত্র-স্বার্থের জন্য ব্যবহার না করে বাইরের লোকজনের ব্যবহারের জন্য কলেজের একাডেমিক কাউন্সিল ও শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সভায় কোনোরকম আলোচনা, মতামত ও সম্মতি ছাড়া দিয়ে দেওয়া নিয়ে এবং আরও ভালো পদে যাওয়ার আশায় একই পদ্ধতিতে কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের নাম নরসিংদীর কোনো নারীর নামে নামকরণ না করে ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নামে করা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করে এবং কলেজের বর্তমান সুস্থ পরিবেশ তৈরির পিছনে আমার সংগ্রাম ও ত্যাগের কথা সবই এরা জানলেও এর পিছনের পুরো কৃতিত্ব এরা বছর দুয়েক আগে ’২১ সালের শেষ দিকে আসা কলেজের অধ্যক্ষকে দিয়েছে এই পত্রিকার মাধ্যমে, যিনি এখানে এসে তৈরি একটা কলেজ পেয়েছিলেন। অথচ যার সূচনা হয়েছিল এই কলেজে বদলি হয়ে আসার পরে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমার প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। তাদের পত্রিকার নৈতিক জায়গা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু করলে শেষমেশ গত মার্চে (২০২৪) আমার একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে ব্রহ্মপুত্র নেহাত ঠেকায় পড়ে ।
গত এপ্রিলে (২০২৪) পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর সমান উত্তরাধিকার নিয়ে প্রথমে নরসিংদী সরকারি কলেজে এবং পরবর্তীতে নরসিংদী প্রেসক্লাবে একটা আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলাম আমরা নারী অঙ্গনের পক্ষ থেকে। সেই আলোচনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শুধু নরসিংদী না, সারা বাংলাদেশ সপ্তাহখানেক উত্তপ্ত ছিল। অনুষ্ঠান পণ্ড করে আমাকে ধর্মবিরোধী ঘোষণা দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মিছিল করা থেকে শুরু করে হুমকি ধামকি, চাকরিচ্যুতির প্রচেষ্টা, এমন কিছু নেই যা করেনি। এরপরও এই ঘটনা নিয়ে অখ্যাত একটা পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো পত্রিকা নিউজ করেনি, নরসিংদীর কোনো সাংবাদিক যোগাযোগ করেনি আমার সাথে এবং নরসিংদীর এতগুলো প্রগতিশীল সংগঠনের কোনোটা প্রত্যেক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমার পক্ষে অবস্থান নেয়নি। অথচ অনেকেই আমাকে চেনে এবং জানে। এর পিছনে দুইটা কারণ থাকতে পারে: প্রথমত, আমি এমন একজন নারী যে নারী অধিকার ও নাগরিক অধিকারের এমন সব প্রশ্ন তোলার সাহস ও যোগ্যতা রাখি, যা একটা মফস্সল শহরে বাস করে রাখার কথা ভাবতে পারেন কম জনই এবং আমার সাহস, যোগ্যতা, সততা পিতৃতন্ত্রের রক্ষক ও ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা কারও কারও আসন টলিয়ে দিতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, আমি আওয়ামীপন্থী নারী অধিকারকর্মী নই। এছাড়া আর কোনো কারণ খুঁজে পাইনি।
৬
কোনো ক্ষেত্রেই নারীর লিডিং পোজিশনে যাওয়া, নারীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া, নারীর পুরুষের চেয়ে এগিয়ে থাকা, আমাদের মধ্যবিত্তীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রগতির তকমা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো পুরুষও কদাচিত সহজ ও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেন। এমনকী অন্য নারীরাও মেনে নিতে পারেন না সবসময়। অবশ্য সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা খুবই কম। ফলে এখানে নারীকে জ্ঞানগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক বাধা অতিক্রম করার পরও আরও একটা প্রায় অলঙ্ঘনীয় বাধা অতিক্রম করার লড়াইয়ে নামতে হয় নারী হওয়ার জন্য। এটা নারীর লড়াইয়ের দ্বিতীয় ধাপ। প্রথম ধাপেই কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবাই আটকে যান। দ্বিতীয় ধাপে যাওয়া স্বল্প সংখ্যক নারীদের কাজকে, তাদের উপস্থিতিকে নাই করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা চলে নিরন্তর।
এককালে নারী প্রচলিত সমাজের বেঁধে দেওয়া বিধানের বাইরে গেলে, মেনে নিতে অস্বীকার করলে, সেইসব বিদ্রোহী নারীদের ডাইনি আখ্যা দেওয়া হত ও পুড়িয়ে মারা হত। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ তাঁর নারী, পুরুষ ও সমাজ গ্রন্থে জানান, “বিভিন্ন হিসেবে ডাইনি নামে নারী হত্যা হয়েছে কয়েক লাখ থেকে ১ কোটি পর্যন্ত। সবচাইতে গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হচ্ছে ৬০ লাখ। যুদ্ধ ছাড়া এটিই হচ্ছে সবচাইতে বড় গণহত্যা (মারিয়া মাইজ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৮০-১১০)। অন্যান্য নির্যাতনের ঘটনা তো আছেই। এগুলো যে পুরুষতান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক সমাজ আধিপত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টাতেই হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এইসব বর্বর নারকীয় ঘটনাগুলো হয়েছে ‘ধর্ম’, ‘সমাজ’, ‘পরিবার’ রক্ষার নামে এবং বিদ্যমান বিধি-আইন ও ধর্মীয় অনুশাসনের অধীনে। সতীদাহ প্রথাও ছিল জীবন্ত নিরপরাধ সদ্যবিধবা নারীকে পুড়িয়ে মারার হিন্দুধর্ম স্বীকৃত একটি রীতি। এই প্রথায় ডাইনিকে পুড়িয়ে মারা হত না ঠিক, কিন্তু নারীকে ডাইনিতে রূপান্তরিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার অজুহাত ছিল।
নিউইয়র্ক ট্রিবিউন-এ কার্ল মার্কস নিয়মিত কলাম লিখতেন। এক সুপরিচিত অভিজাত পরিবারের বধূকে তার স্বামী অ্যাসাইলামে পাঠিয়েছেন। চারদিকে তা নিয়ে চলছে কানাকানি, ফিসফাস। ১৮৫৮ সালে মার্কস তাঁর কলামে ঘটনাটির উল্লেখ করে লেখেন, খোপে না ফেলতে পারলেই পুরুষ মানুষ নারীকে পাগল বানায়। তিনি জানান, স্বাধীনচেতা এই ভদ্রমহিলাকে তিনি চেনেন এবং জানেন। মার্কস মনে করেন তার মধ্যে পাগলামির বিন্দুমাত্র লক্ষণও নেই। আজকাল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ফ্রেমের বাইরে চলা নারীদের ডাইনি, রাক্ষসি আখ্যায়িত করে হয়তো পুড়িয়ে মারা হয় না কিংবা পাগল বানিয়ে গারদে পুরে রাখা হয় না হয়তো, কিন্তু তাদের বেশ্যাকরণ হয় হরহামেশাই। তাদের পাগলি, মাথা গরম, বেয়াদব, উচ্ছৃঙ্খল, ধর্মবিরোধী ইত্যাদি ট্যাগিং করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সবরকম আয়োজন চলে।
আন্দোলনে দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা, লৈঙ্গিক বিভেদ ভুলে লাখ লাখ নারী পুরুষ রাজপথে নেমে এসেছিল এবং একে অপরকে বুক আগলে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে শেষ পর্যন্ত। চট্টগ্রামে আন্দোলনস্থল থেকে পুলিশ ভ্যানে তুলে নেওয়া পুরুষ সহযোদ্ধাদের ছাড়িয়ে নিতে ভ্যানের সামনে বুক পেতে হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া সেই মেয়েটির কথা মনে থাকার কথা অনেকেরই। আন্দোলনের সময় আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় ছিল, নারীদের ওপর গুলি-হামলা-নির্যাতন-গ্রেফতারের সম্ভাবনা কম থাকায় মিছিলের অগ্রভাগে নারীরা অবস্থান করে মিছিলকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেরাও সবরকম নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে মেয়েদের। যেই দেশে দিনের বেলাতেই অহরহ ঘরে বাইরে সর্বত্র নারীদের নানান কিসিমের যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়, সেই দেশে দিনের পর দিন নারী পুরুষ রাজপথে একসাথে অবস্থান করেছে ও লড়েছে, অথচ একটাও অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শোনা যায়নি। নেকাব, টপ্স, শার্ট, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদির ভিন্নতা আমাদের একত্রিত হওয়ার পথে বাধা হতে পারেনি তখন। হাতে লাঠি নিয়ে পাশাপাশি নেকাব পরা ও টি-শার্ট ট্রাউজার পরা দুই নারী শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে আন্দোলনে যাওয়ার একটা ভিডিয়ো ১৫ জুলাই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। অথচ ৫ আগস্টের পর থেকেই একটা গোষ্ঠী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখা কিছু নারীকে বেশ্যাকরণে উঠে পড়ে লেগে যায়।
শুরুর দিকে চরিত্রহনন, কুৎসা রটনা, অন্য নারী ও সমাজের মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে অপপ্রচার চালিয়ে যাতে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। ফারজানা সিঁথি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সাহসী ভূমিকা রাখায় তখন অনেকেই তার ভিডিয়ো শেয়ার করে বাহবা দিয়েছিল। কিন্তু যখন সে পরবর্তীতে নারী ইস্যু নিয়ে ভয়েস রেইজ করতে গিয়েছে পুরুষের বিরুদ্ধে, অমনি দলবেঁধে অনলাইনে তাকে তারই পূর্বের শেয়ার করা ছবি দিয়ে ও নানা রকম অপপ্রচার চালিয়ে বেশ্যা বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসবেও সফলকাম না হলে, জ্বলে ওঠা নারীকে থামিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে, তাদের কাজকে ও তাদেরকে কর্নার করে ফেলার চেষ্টা চলে, যেন তারা পাদপ্রদীপের আলোয় না আসতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্য যেসব নারী সমাজের কাঙ্ক্ষিত মডেল অনুযায়ী ও পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন এবং বিদ্যমান সমাজকাঠামো ও পিতৃতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ না হন, সেই সাথে পুরুষকে মুরুব্বি হিসেবে মেনে কাজ করতে চান, সেইসব নারীর প্রতি কিছুটা সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয় বটে। আমরা ‘নারী অঙ্গন’ থেকে যখন গত এপ্রিলে ‘পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা’ শিরোনামে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, তখন একটা পক্ষ থেকে বারবার বলছিল, শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ ‘নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা’ নিয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু প্রথম অংশ, অর্থাৎ ‘সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার’-এর প্রসঙ্গ ও দাবি কেন আনলাম, সেটা নিয়ে তাদের আপত্তি ও বিরোধিতা। অর্থাৎ নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে হলে পিতৃতন্ত্রের রক্ষকদের বেঁধে দেওয়া পথেই আমাদের আগাতে হবে। এতে কয়েক হাজার বছর লাগে, লাগুক, তাতে তাদের কী!
৭
জুলাই অভ্যুত্থানে সংগঠক হিসেবে কাজ করা রিপা রহমানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এখন আর বৈষম্য-বিরোধী প্ল্যাটফর্মের কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত নেই কেন? তিনি জানালেন, “ফ্যাসিস্ত আওয়ামী লীগের পতনের জন্য আন্দোলনে গিয়েছিলাম। আন্দোলনের পরে দেখি, যাদের সাথে আন্দোলন করেছি, তারা প্রায় সবাই বিএনপির। এরাও তো আওয়ামী লীগের মতোই। সেজন্য চলে এসেছি।” আন্দোলনের একজন নেতা ফাহিম ভূঁইয়া অভিও প্রায় একইরকম অভিজ্ঞতার কথা জানালেন, “মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলে, আওয়ামী লীগের পতনের জন্য এসেছিলাম। এখন আর আমাদের কিছু করার নেই।” আন্দোলনের আরেকজন নেতা এবং এখনও কাজে সক্রিয় সুমাইয়া সেতুর কাছে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা মেয়েদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, “আমি কি তাদের সাথে যোগাযোগ করব? কীভাবে করব? তারা যোগাযোগ করতে পারে না?”
বড়ো বড়ো আন্দোলনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা নারীরা অধিকাংশই সাধারণত সময়ের প্রয়োজনে দেশ ও জাতিকে রক্ষায় রাজপথে নেমে আসেন। সময়ের প্রয়োজন মিটে গেলে দিনশেষে পাখির নীড়ে ফেরার মতো তারাও প্রাত্যহিক জীবনে ফিরে যান। দেশ, সমাজ, রাজনীতি নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামান না। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রাজপথে সক্রিয় ভূমিকা রাখা অনেকের সাথে আলাপ করে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করে এমনটাই মনে হয়েছে। শামসুন্নাহার হল আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ফারজানা ববিকে তখন মনে হয়েছিল, ভবিষ্যতে তিনি দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। তাছাড়া তিনি একটা ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন। কিন্তু কয়েক মাস পরে বিয়ে হয়ে গেলে তিনি ছাত্র রাজনীতিতেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যান অনেকটা এবং এক পর্যায়ে পুরোপুরি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। যদিও একজন রাজনৈতিক কর্মীর সাথেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল।
৮
রাজনীতি একটা সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া। এখানে বড়ো ধরনের ভূমিকা রাখতে হলে এবং নিজের জায়গা করে নিতে হলে প্রতিনিয়ত নিজেকে যুক্ত রাখতে হয়, সময় দিতে হয়। যেতে হয় নানান ধরনের বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে। পরিবর্তন, পরিবর্জন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। সেটা নারী-পুরুষ উভয়কেই। যাঁরা সেটা করতে পারেন, কেবল তাঁরাই রাজনীতির আকাশে জ্বলজ্বল করা তারার মতো নিজেদের স্থায়ী আসন নিশ্চিত করতে না পারলেও দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে নিজেদের শামিল রাখতে পারেন। শুধু তাই না, নিজেকে প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত মানুষ হিসেবে তৈরিও করতে পারেন। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি ও সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততা রাজনীতির জন্য একটা প্রাথমিক ও অত্যাবশকীয় পাঠ। গত ১৭ ডিসেম্বর ‘সুলতানাদের স্বপ্ন-২০২৪’ অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে উমামা ফাতেমা বলছিলেন, “৩০ জুনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আগের মতো বিশ্রাম, ঘুমানোর সময়ও দিতে পারছি না নিজেকে।”
৯
“নেতার কি দায়িত্ব না, কর্মী সংগঠকদের সাথে যোগাযোগ রাখা?” এই প্রশ্নের জবাবে সুমাইয়া সেতু জানান, সবার সঙ্গে তো আর যোগাযোগ করা সম্ভব না। আগেও একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আলাপ করতে গিয়ে ওই দিনও সার্জিস আলমের সঙ্গে তাঁর যে প্রতিদিনই কথা হয়, সেটা তিনি জানান। এছাড়া তাঁরা এখন কেবল আহত ও শহিদদের নিয়ে কাজ করছেন। তেমন কোনো কাজও নেই তাঁর মতে। অর্থাৎ কাজ করতে হলে নেতৃবৃন্দের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হয়, লেগে থাকতে হয় কাজে। নেতারা যোগাযোগ করবেন না তা কিন্তু নয়, কিন্তু কর্মী সংগঠকদেরও যোগাযোগ রাখতে হয়। আমরা অনেক সময় উপর থেকে যোগাযোগ করার প্রত্যাশায় থেকে হতাশ হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাই।
১০
আমাদের অর্থনীতি, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, আইন, শিক্ষা ইত্যাদি নারীদের রাজনীতির সঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক রাখার মতো অনুকূল কি না, শুরুতেই যদি এই প্রশ্ন করি, তাহলে উত্তর মিলবে, না! শ্রমজীবী নারীকে ৩ বেলা পেটের আহার জোগাড় করতেই দিনের সব সময় এবং শরীরের সব শক্তি ফুরিয়ে যায়। অন্য কিছুর দিকে ফিরে তাকানোর মতো ফুরসত, শক্তি, মানসিকতা আর অবশিষ্ট থাকে না তাদের। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষের তুলনায় নারীর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে লেগে থাকার ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা হয়ে সামনে আসে। এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মূলে রয়েছে পৈত্রিক সম্পত্তির প্রাপ্তিহীনতা ও অনিশ্চয়তা। ‘জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট’ (১৯৯৫) শীর্ষক প্রবন্ধে অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত নারী কীভাবে নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব হারান। তিনি দেখান, সামাজিক ন্যায়বিচারের মৌলিক ও আবশ্যিক অনুষঙ্গ হচ্ছে লৈঙ্গিক সমতা। আর সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার সেই সমতার প্রাথমিক ধাপ, যা আমাদের দেশে নারীদের নেই।
এছাড়া আমাদের দেশে রাজনীতি এখনও অধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার না হয়ে শৌখিন-ধান্দাবাজ-আজাইরা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অবৈধ অর্থ-সম্পত্তি বানানোর উপায় হিসেবেই থেকে গিয়েছে অনেকটা। আমাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীদের পড়াশোনা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার লক্ষ্য এই একুশ শতকেও ভালো একটা বিয়ে। বড়োজোর চাকরি করা। মেয়েদের ডাক্তারির মতো ব্যয়বহুল ও কঠিন ডেকোরামের শিক্ষাও নিতে শুনেছি ভালো একটা পাত্র জোগাড় করার জন্য কেবল। আমার নিজেরও এমন একজন নিকটাত্মীয় আছেন। নারীর জন্য পরিবার ও সমাজ নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড আজও অনেকটা এমনই। এই নিরাপদ নিস্তরঙ্গ জীবনের বাইরে নারীরা যান না, যাওয়ার কথা ভাবেনও কদাচিত। আর ভাবলে, যেতে চাইলে চারদিক থেকে প্রতিবন্ধকতার দেওয়াল ঘিরে ধরে তাদের। এই দেওয়াল টপকানোর জন্য অনেক বড়ো দমের প্রয়োজন হয়।
১১
যারা পরিবার ও সমাজের বিধিনিষেধ, বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে যুক্ত হন, তাদের একটা বড় অংশই আবার স্থূল ভোগ-বিলাসিতা, ফেইক হিরোইজম, সাজগোজ, ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকেন। বৃহত্তর পরিসরে যুক্ত করার মতো করে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য পড়াশোনা-সময়-শ্রম-মনোযোগ দেন না, দিতে চান না। এর ফলে তারা খুব বেশি দূর যেতে পারেন না। এই ক্যাটাগরির নারীরা যারা দ্বিতীয় ধাপের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন, তাদের জন্যও অনেকটা হুমকিস্বরূপ। পরিবার ও সমাজ তাদের উদাহরণ যেমন নিয়ে আসে, তেমনই তাদের সঙ্গে সেইসব লড়াকু নারীদের মিলিয়ে সমাজের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।
১২
‘নলেজ ইজ পাওয়ার’ কথাটা এমনিতেই আসেনি। অনেক সময় জ্ঞানের পাওয়ার পারমাণবিক বোমার মতো শক্তিশালী। জ্ঞান যে কারও জন্যই অনেক বড়ো শক্তি, নারীদের জন্য তো বটেই। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জ্ঞান সবচেয়ে বড়ো বন্ধু হয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় এবং শক্তি জোগায়, পথ দেখায়। সেজন্য ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার বোঝাপড়ার জন্য বিভিন্ন গবেষণামূলক বই পড়া জরুরি। এই জায়গাটাতে আমার ধারণা নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে ঐতিহাসিক কারণে এবং নিজেদের সচেতনতা ও আন্তরিকতার অভাবে। তার মানে কিন্তু এই না যে, তারা বই পড়েন না, পড়েন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদরকারি বই পড়ে সময় নষ্ট করেন। এজন্যই আরও নারীদের আটকে দেওয়া সহজ হয়। শুধু তা-ই না, তাদের বিকাশও খুব বেশি দূর আগাতে পারে না কেউ চাইলেও।
এত সব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে নারীদের জ্বলে ওঠা এবং জ্বলে ওঠার পরে জ্বলন্ত অবস্থায় টিকে থাকা একটা দুরূহ কাজই। এসবের পরও মানসিক দৃঢ়তা, সততা, কঠোর পরিশ্রম, লেগে থাকার মানসিকতা, পড়াশোনা, দূরদৃষ্টি, স্বপ্ন দেখার সাহস, নিজের উপর আস্থা, আত্মমর্যাদাবোধ, লড়াকু মনোভাব, হার না মানার প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি যাদের মধ্যে থাকে এবং যারা আয়ত্ত করতে পারেন, তারা প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের বাধা অতিক্রম করতে সফলকাম হন একদিন না একদিন। কারও সাধ্য নেই, তাদের আটকে রাখার। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরেও দেখব, সংখ্যায় কম হলেও আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বে চলে এসেছেন কিছু নারী।
লেখাটি ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি মুদ্রিত সংখ্যায় প্রকাশিত।
নাদিরা ইয়াসমিন

সম্পাদক, নারী অঙ্গন