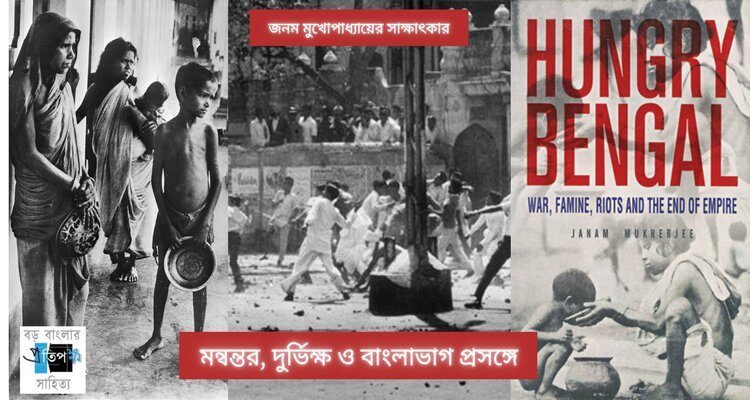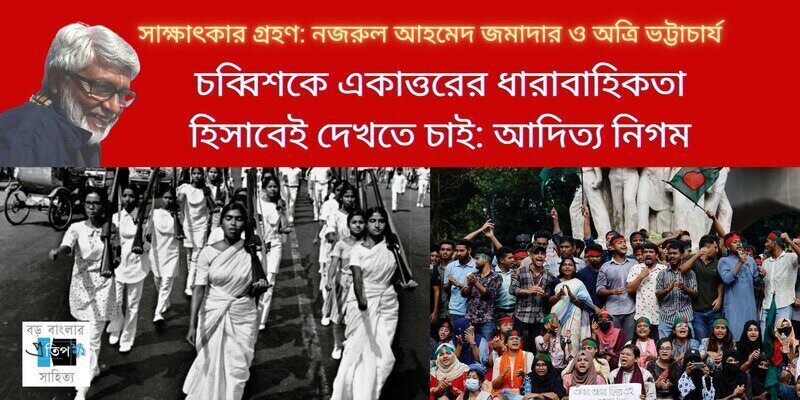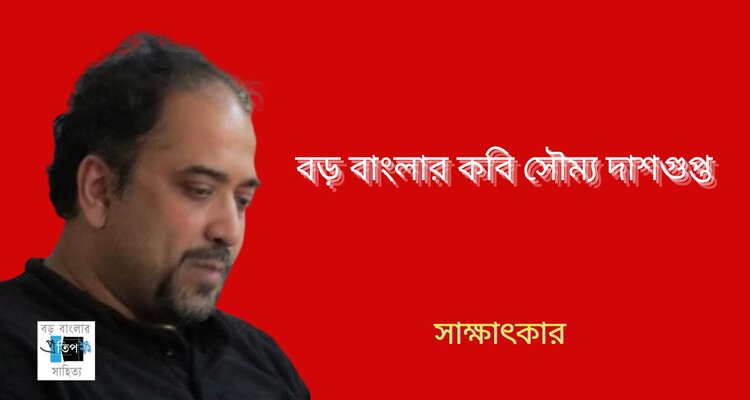
।। সাক্ষাৎকার ।।
”বাংলাদেশকে অপরায়নের জায়গা থেকে দেখার যে প্রবণতা কলকাতার, তা ভাঙতেই পত্রিকা তৈরি করেছিলাম।” বলছেন কবি সৌম্য দাশগুপ্ত, যিনি জন্মসূত্রে কলকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গের এবং পেশাসূত্রে মার্কিন দেশের মানুষ হলেও চেতনায়, কাব্যে, সাহিত্য ও সমাজচিন্তায় বড় বাংলার একজন কবি। পশ্চিমবঙ্গে যেকজন কবি, লেখক আছেন যাঁরা বাংলাদেশকে কলকাতার দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বঙ্গের দৃষ্টিপ্রসারতায় ধারণ করেন, সৌম্য দাশগুপ্ত তাঁদের মধ্যে একজন। গুরুত্বপূর্ণ এই কবি তাই বাংলাদেশেরও আপনজন। ২০২৪ সালের শীতে কলকাতায় তাঁর বাসায় তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেছিলেন ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক অতনু সিংহ। সেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় এই পত্রিকার ২০২৫, ফেব্রুয়ারি, মুদ্রিত সংখ্যায়। এবার সেই কথাবার্তা ‘প্রতিপক্ষ’ ওয়েবজিনে তুলে দেওয়া হল।

প্রতিপক্ষ: প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইছি যে, আপনার কবিতা লেখা প্রাথমিকভাবে কী করে শুরু হল? মানে, আপনি সাহিত্যজীবনে কীভাবে প্রবেশ করলেন?
সৌম্য দাশগুপ্ত: সাহিত্যজীবনে প্রবেশ করার মূল অনুষঙ্গটাই হল, আমার প্রয়াত বাবা— অধ্যাপক ড. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত— তিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কলেজগুলির মধ্যে বহু জায়গায় পড়িয়েছেন। যেমন— শিলচরের গুরুচরণ কলেজ, তারপরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ, হুগলি মহসীন কলেজ; আবার দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসটাই উনি নিয়েছিলেন। তারপরে অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি অবসর নেন। এবং পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বাংলার অধ্যাপনা করতেন, এমএ ক্লাসে পড়াতেন। এই যে পরিবেশ, যেখানে অনেক বই এবং বাল্যকাল থেকেই দেখেছি অনেক লেখক-কবি আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, এসবের সুবাদেই সাহিত্যের একটা পরিবেশ আমাদের বাড়িতে ছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে সংগীতেরও একটা পরিবেশ ছিল। আমার বাবা নিজে বেহালা বাজাতেন এবং আমাকে তবলা শিখতে পাঠানো হয়েছিল। ফলে ছন্দের কানটা খুব অল্প বয়সেই তৈরি হয়েছিল। আমি খুব দুরন্ত ছিলাম ছোটবেলায়। মোটামুটি যখন আমার বারো-তেরো বছর বয়স, তখন কৌতূহলবশত বাড়ির বইপত্র থেকে একটা একটা করে বই নিয়ে আমি পড়তে শুরু করি। একদম অল্প বয়সেই আমার রচনাবলিগুলো পড়া হয়ে গিয়েছিল— যেমন রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্র বা ত্রৈলোক্যনাথ। গদ্যটা তখনই অনেকটাই জানতাম। আর তার পরবর্তীকালে দু’-একটা কবিতার বই যখন হাতে আসছে, সেগুলো পড়ছি। তার মধ্যে রয়েছেন বিষ্ণু দে। ধরতে পারছি না পুরোটা, কিন্তু ধরতে পারছি না বলেই তখন আরও বেশি করে পড়তে ইচ্ছে করছে। হয়তো জীবনানন্দ দাশের বইগুলো পড়ে রয়েছে, সেগুলো খুলে দেখছি। ঝরা পালক কিংবা বনলতা সেন পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে যে এ-ও একটা অজানা জায়গা। এভাবে আস্তে আস্তে আমার পাঠটা শুরু হয়। কিন্তু তারপরে দেখলাম, কবিতার জগতে আমাকে সহজেই প্রবেশ করতে দিচ্ছেন সে যুগের তথাকথিত ন্যারেটিভ কবিরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এগুলো পড়তে পড়তেই কিন্তু আসলে কবিতায় ঢোকা গেল। তারপরে বড় একটা পরিবর্তন এল। আমার যখন আনুমানিক চোদ্দো বছর কি পনেরো বছর বয়স, তখন থেকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। এবং শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়তে পড়তেই হয়তো আমার মূল জায়গাটা তৈরি হল। অর্থাৎ একইসঙ্গে তাঁর দুটো ধরন বা শৈলী। একটা হচ্ছে খুব একটা নিঃশব্দ, নীরব এবং নিভৃত কবিতার জায়গা— যেটা হয়তো পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ-এ পাওয়া যায়। আর আরেকটা হচ্ছে খানিকটা আয়াসসাধ্য কবিতা, তার মধ্যে হয়তো কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক বক্তব্য রয়েছে, কিন্তু তা সহজে ধরা যায়। যেমন ধরুন— “ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই/সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই/…/আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে!/আমি কি নিত্য আমারও সমান/সদরে, বাজারে, আড়ালে?” এই ধরনের কবিতাগুলোর মধ্যে যে ছন্দ, যে সহজতা, সেটা টানছে। আবার পাশাপাশি, “ভোর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনও।/স্থির অমাবস্যা, আমি শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি দিগন্তের ধারে/দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে/আমার শরীর যেন আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে/বুক থেকে হাতে খুলে নিয়েছি পাঁজর আর তালে তালে নাচে সেই হাত/গ্রহনক্ষত্রের দল ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে।” এই শব্দচয়নগুলো যখন পড়ছি, তখন মনে হচ্ছে ধরতে পারছি কিন্তু পারছি না। একটা নীরবতা রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা আগুন জ্বলছে। তো শঙ্খ ঘোষ একটা প্রবল উত্থানের জায়গা আমার পক্ষে। এর পরে সমসাময়িক কবিদের পড়তে শুরু করলাম। বাবারই একজন বন্ধু, অধ্যাপক উদয় চক্রবর্তী আমাকে বললেন, “তুমি অলোকরঞ্জন পড়েছ?” তখন অলোকরঞ্জন পড়লাম। পাশাপাশি তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়ছি খুবই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাও পড়ছি। কিন্তু আমার ভাবনার কেন্দ্রে সবসময় ছিলেন শঙ্খ ঘোষ। এর পরবর্তী পর্যায়ে, ধরুন আমি যখন উচ্চমাধ্যমিক পড়ছি, কি তারও একটু আগে হাতে এল জয় গোস্বামীর কবিতার বই। তখন উন্মাদের পাঠক্রম সবে বেরিয়েছে। এবং সেই কবিতার যে অভিভব, সেটা পড়ে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই। আমার তখন মনে হয়, আমাকে আরও লিখতে হবে। এর আগে আমি কিছু ছোট ছোট কবিতা লিখেছি, বা হয়তো কয়েকটা বড়ও লিখেছি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ন্যারেটিভ রয়েছে, কিছু তার মধ্যে ছন্দ নিয়ে খেলা রয়েছে, ছন্দ নিয়ে নানারকম চেষ্টা রয়েছে। ছন্দে আমার কখনো সমস্যা হয়নি। কারণ ওই যে বললাম, যেহেতু সাংগীতিক একটা জায়গা আমার ছিল এবং একেবারে পাঁচ বছর বয়স থেকেই তবলাটা রীতিমতো গুরুর কাছে গিয়ে শেখার অভ্যাস ছিল, সেটা আমার কান তৈরি হয়ে দিয়েছিল। এবারে আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধরনের ছন্দের চাল, চলন, এগুলো বুঝতে শুরু করলাম। তারপরে জয় গোস্বামীর সঙ্গে গিয়ে আলাপও করলাম এবং তাঁর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতা হল। আর একইসঙ্গে তখন শঙ্খ ঘোষের কাছে যাচ্ছি। কবি বন্ধুবৃত্ত তৈরি হচ্ছে। জয় গোস্বামীর মাধ্যমেই আলাপ হল মৃদুল দাশগুপ্তর সঙ্গে, গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে, রাহুল পুরকায়স্থর সঙ্গে। এবং এঁদের কবিতাও পড়তে শুরু করলাম। রাহুল আটের দশকে আমাদের সহকবি বলা যেতে পারে। বয়সের দিক থেকে এবং ভাবনার দিক থেকেও আমাদের সাযুজ্য রয়েছে। এর আগে যাঁদের পড়ছি, তাঁরা মূলত সাতের দশকের কবি। এবং এই সত্তরের দশক আজও আমার কাছে কিন্তু একটা বিরাট জায়গা রাখে। কারণ সত্তর বা একাত্তর সাল এবং তার পরবর্তী কবিতা, দুই বাংলার দুটো আগুন— একইসঙ্গে ওদিকে চলছে মুক্তিযুদ্ধ, এদিকে চলছে গণঅভ্যুত্থান, নকশালপন্থী আন্দোলন এবং তার যে আদর্শবোধ— দুটোই আমাকে একইসঙ্গে আচ্ছন্ন করে। যার ফলে সেই সময়কার কবিতাগুলো পড়তে পড়তে আমি বুঝতে পারলাম যে, কবিতা তো আসলে নানা ধরনের হয়। সেই নানা ধরনের মধ্যে যে বৈচিত্র্য, তার মধ্যে যেতে শুরু করলাম। সেখানে এসে পড়লেন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, নিশীথ ভড়। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হলাম। সেখানে যখন আমি পরিসংখ্যানতত্ত্ব নিয়ে পড়ছি, তখন আমার চলাচল ছিল মূলত প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্যান্টিনেই। সেখানে আমাদের বন্ধুত্ব হল দু’-তিনজন উজ্জ্বল, মেধাবী কবিতার পাঠকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে একজনের নাম অচ্যুত মণ্ডল, তিনি আজ নেই। একজনের নাম অদ্রীশ বিশ্বাস, তিনি আজ নেই। একজনের নাম (সে কিছুটা সিনিয়র হলেও তাকে নিয়ে এসেছিলাম আমাদের আড্ডায়) জয়দেব বসু, তিনিও আজ নেই। সুতরাং আমাদের এই বন্ধুবৃত্তটি— যেখানে কবিতা নিয়ে খুব হইচই, আলোচনা হত, তারা এসে আরও বলল যে, নানান প্রান্তিক কবিদের কবিতা পড়তে হবে। প্রথম দিকে যদি বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ থেকে শুরু করি, তারপরে সত্তরের জায়গায় যাই, সেখান থেকে যদি আমি আরেকটু বিস্তৃতভাবে দেখতে শুরু করি, তাতে দেখা গেল যে আমাকে তখন বাংলাদেশের কবিতাও আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে। আল মাহমুদ পড়ছি, শামশুর রহমান পড়ছি। সেই সময় বাংলাদেশ থেকে আমার একটা আমন্ত্রণ এল। কিছু ধ্বনি বলে একটি পত্রিকা থেকে আমন্ত্রণ জানালেন আনোয়ার আহমেদ (তিনিও নেই আর), কবিতা পড়ার জন্য। ততদিনে আমাদের বাড়িতে এসেছেন কবি ফরিদ কবির, কবি তুষার দাশ, কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল। এবং তখন বাংলাদেশের সঙ্গে আমার একটা সেতুবন্ধন তৈরি হল। ওই অতি অল্প বয়সে, মাত্র একুশ বছর বয়সে বাংলাদেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাকে একেবারে আপ্লুত করল। সেখানে তখন যারা বন্ধু হয়েছে, তাদের সঙ্গে আমার আজ পর্যন্তও বন্ধুত্ব রয়েছে। আমাদের তুইতোকারির সম্পর্ক। যেমন ব্রাত্য রাইসু, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, মাসুদ খান— এঁরা আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। মাসুদ ভাই আমার থেকে খানিকটা সিনিয়র। তিনিও আমাকে স্নেহভরে তুই করেই বলেন। তাঁর কবিতা পড়ার পরে দেখলাম, বিজ্ঞান এবং কল্পবিজ্ঞানের একটা জগৎ খুলে গেল। আবার বাংলা কবিতার যে পশ্চিমবঙ্গীয় ধারা রয়েছে, ব্রাত্য রাইসু সত্যিই তার থেকে বাইরে বেরিয়ে একটা ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করলেন। এইভাবে শুরু হল। এবং যখন লিখতে শুরু করলাম, তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এগারো-বারো ক্লাসে পড়া অবস্থায় একদিন আমাকে দেশ পত্রিকার অফিসে যেতে হল— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমাদের কলেজের একটি ম্যাগাজিন, অনাময়, তার জন্য কবিতা চাইতে। কবিতা যখন চাইতে গেছি, তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, “তোমরা কেউ লেখো না?” আমার সঙ্গে সৌমিত্র বিশ্বাস বলে একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি গদ্যকার, এখন সরকারি কর্মচারী। আমি কিছু বলার আগেই সৌমিত্র আমার দিকে দেখিয়ে বলল, “ও কবিতা লেখে।” সঙ্গে সঙ্গে সুনীল বললেন, “আমাকে কবিতা দিয়ে যাও।” তা আমি সেটা ভাবতেই পারিনি। আমার দেওয়ার কোনো বাসনাই ছিল না, সেই উদ্দেশ্যে আমি ওখানে যাইওনি। আমি এ ব্যাপারে খুবই লাজুক। কিন্তু আমার ডায়েরিটি সঙ্গে ছিল, সেটা দিলাম। উনি পাতা উলটে উলটে পড়লেন। পড়ে বললেন, “এই লেখাটা আমাকে দিয়ে যাও।” তা আমি পরের দিন সেটা একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজে লিখে দিয়ে গেলাম। এবং ১৯৮৪ সালের ২২ ডিসেম্বরের যে দেশ পত্রিকার সংখ্যা, তাতে আমার কবিতা বেরোল। একদিকে আমার কবিতা, আরেক দিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা! দেখে আমি তো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমার বাবা বললেন, “দ্যাখ, তোর লেখা শক্তির সঙ্গে বেরোচ্ছে।” ওই একুশ বছর বয়সে যেটা হয় আর কী— এইরকম একটা ঘটনা ঘটলে আরও সিরিয়াসলি লিখতে ইচ্ছে করে। আরেকটু ইচ্ছে করে, মানুষের কাছে শুনি যে লেখাগুলো ভালো হচ্ছে কি না। তো সেই যে শুরু, তারপর পরবর্তী টানা সাত বছর ধরে আমি যে ক’টা লেখা যখনই দেশ পত্রিকার দফতরে দিয়ে এসেছি বা পাঠিয়ে দিয়েছি, সেগুলো প্রত্যেকটাই প্রকাশিত হয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশে যখন আমি গেছি, ততদিনে আমার একটা…
প্রতিপক্ষ: পরিচিতি তৈরি হয়েছে।
সৌম্য দাশগুপ্ত: পরিচিতি তৈরি হয়ে গেছে।
প্রতিপক্ষ: তারপর থেকে তো আপনি দেশ পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি যখন থেকে লেখালিখি শুরু করি, তখন আমরা আপনাকে একভাবে আভাঁগার্দ, প্রতিষ্ঠানবিরোধী, এই জায়গা থেকেই দেখি। আপনার এই বাঁকবদলটা কীভাবে হল?
সৌম্য দাশগুপ্ত: হ্যাঁ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ এটা বুঝতে হলে অনেকগুলো স্তর বুঝতে হবে। প্রথমত, আমার সঙ্গে তখন যাঁদের আলাপ হল এবং যাঁদের কবিতা পড়তে শুরু করলাম, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন গৌতম চৌধুরী, মৃদুল দাশগুপ্ত, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম বসু— এই ধরনের কবিরা। এবং দেখলাম, তাঁদের যে কবিতা, তার মধ্যে জনপ্রিয়তা বা লোকপ্রিয়তার কোনো ধরন নেই। তাঁরা ঢুকে গেছেন একটা গভীর অন্তস্থলে, মনোজগতের সঙ্গে সামাজিক জগতের, কিংবা ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির যে বিরোধ— এই সমস্ত মিলিয়ে খুব জটিল একটা জায়গায়। সেই জটিল জায়গাটা আমাকে খুব টানল, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার প্রসঙ্গে এখানে দুটো প্রতিষ্ঠানের থেকেও বড় কথা, কবিতার ভেতরের যে প্রতিষ্ঠান, সেইটাকে আইডেনটিফাই করতে শিখলাম। এবং তখন একটা ঘটনাও ঘটল। কৃষ্ণনগরে তখন একটা বড় কবি সম্মেলন করা হল। তার আগে আমি অবশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা কবি সম্মেলন করেছিলাম— এঁদেরকেই নিয়ে, যেখানে এঁরা কবিতা পড়তে এসেছিলেন। সেখানে জয় গোস্বামী, মৃদুল দাশগুপ্ত, রণজিৎ দাশ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চৌধুরী, গৌতম বসু, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, নিশীথ ভড়, অনুরাধা মহাপাত্র, ঈশিতা ভাদুড়ি, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়— এঁরা অনেকে এসেছিলেন কবিতা পড়তে। তারপরে কৃষ্ণনগরে ‘শত জল ঝর্ণার ধ্বনি’ নাম দিয়ে, অর্থাৎ জীবনানন্দের কবিতার লাইন থেকে নাম দিয়ে একটা বিষয় তৈরি করা হল। সেই বিষয়টা হল, একটা কাগজ যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো একটা সাহিত্যের ধারার প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে সেই কাগজের পছন্দের যাঁরা কবি, যাঁদের কবিতা পড়ার জন্য মানুষ পয়সা দিয়ে একটা পত্রিকা কিনবে, তাঁদের কবিতাই সেখানে বারবার নির্বাচিত হবে। যদিও সেই নির্বাচিতের তালিকায় আমিও ছিলাম, কিন্তু আমার মনে হল এ বড় অন্যায়। এর বাইরে বহু জায়গা থেকে কবিতা লেখা হচ্ছে এবং সেসব কবিতা পড়বার জন্য, জানবার জন্য আমার একটা আগ্রহ তৈরি হল। এই যে “শত শত-শত জল ঝর্ণার ধ্বনি”, এই কথাটার মধ্যে যে রূপকটা আছে, তা হল বাংলা কবিতা লেখা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। কেবল মাত্র কলেজস্ট্রিট এবং আনন্দবাজার গোষ্ঠী প্রকাশিত দেশ পত্রিকা থেকেই যে কবিতাকে ধরা যাবে তা নয়। ধরতে গেলে আমাকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বগুড়া, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, খুলনা, এমনকী উত্তরবঙ্গ, বরাক উপত্যকা, জলপাইগুড়ি— অর্থাৎ এক কথায় বৃহৎ বঙ্গের কবিতাকে জানতে হবে। সেইসব জায়গা থেকে প্রকাশিত কাগজগুলো আমি তখন জোগাড় করতে শুরু করলাম। আর তার মধ্যে দিয়ে অমূল্য সমস্ত লেখা, অমূল্য সব কবিকে আবিষ্কার করলাম। তারপর ‘শত জল ঝর্ণার ধ্বনি’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে (দু’-তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান ছিল) বহু শত কবি এলেন। সেখানে সবাই প্রায় একরকম ঘোষণাই দিলেন— সে যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখেই— যে আমরা মেইনস্ট্রিমের কোনো কাগজে লেখাই জমা দেব না। কারণ সেসব কাগজ যাঁরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশই কবিতার গভীরে দীক্ষিত নন এবং তাঁদের খুশি করবার জন্য আমাদের লেখাগুলো জোলো হয়ে যেতে পারে। সেই তুলনায় বরং কবিতার ধ্যানের জায়গাটাকে আমরা ধরে রাখব। এখানে অবশ্য সরাসরি প্রতিষ্ঠানের কথাই বলা হচ্ছিল। আর আমি নিজের মনের ভেতরের প্রতিষ্ঠানটাকে খানিকটা উৎপাটিত করার চেষ্টা করলাম। এবং সেই জন্য আমি দেশ পত্রিকায় লেখা দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। কেবল মাত্র লিট্ল ম্যাগাজিনে তখন লিখতাম— যে সমস্ত লিট্ল ম্যাগাজিন হাতে এসে পৌঁছত, সেখানে। জিজ্ঞাসা পত্রিকার শিবনারায়ণ রায় আমাকে খুব উৎসাহিত করতেন। উনি পছন্দ করতেন আমার লেখা এবং বারবার জিজ্ঞাসা-র জন্য লেখা চাইতেন। জিজ্ঞাসা, বারোমাস, এই পত্রিকাগুলো তো ছিলই। তার পরবর্তীকালে একদম অনামী যে সমস্ত লিট্ল ম্যাগাজিনে আমার কবিতা বেরিয়েছে, আমি সেগুলো অনেক সময় হাতেও পাইনি। তার কারণ ১৯৯০ সালে আমাকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে চলে যেতে হল। ’৯০ সালের ১৬ আগস্ট চলে গেলাম। তারপরে দু’ বছর বাদে, ’৯২ সালে ফিরলাম মাস্টার্স করে। তারপরে আবার গেলাম পিএইচডি করতে— ’৯৩ সালের জানুয়ারি থেকে ’৯৭ পর্যন্ত। তার মধ্যে কেবল ’৯৬ সালে কোনোভাবে একবার আসা। তখন এত সহজে এত ঘনঘন কলকাতায় আসা যেত না। কলকাতায় আসার মানে আমার কাছে কবিদের কাছেই আসা। ঢাকায় যাওয়া মানে আমার কাছে মূলত কবিদের কাছেই যাওয়া, চট্টগ্রামে যাওয়া মানে কবিদের কাছেই যাওয়া— এটা আমার ক্ষেত্রে সারা জীবন রয়ে গেছে। তো সেই জায়গা থেকেই এই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাটা আমার কাছে থেকে গেল, যদিও আমি সেটাকে কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠানের জায়গা থেকে কবিতার প্রতিষ্ঠানের জায়গায় নিজের মনে মনে নিয়ে গেলাম। ’৯৬ সালে বেরোল আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ— যার প্রচ্ছদ করেছিলেন সহকবি মৃদুল দাশগুপ্ত— তার নাম হল রাজার জামা পরা মায়াবী সাতদিন। সঞ্জীব ঘোষ এবং গৌতম চৌধুরী মিলে খুব যত্ন করে আমার বইটা বের করলেন।
প্রতিপক্ষ: আপনি যে কথা বললেন এতক্ষণ, এই প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যাওয়া, কবিতার মধ্যে শুদ্ধ স্বর খঁজা, আবার একইসঙ্গে কবিতা নিয়ে ভাঙাচোরা করা, সেই প্রসঙ্গে পরের প্রশ্নটা করব। আপনার আলো, আলোতর, আলোতম বইটিতে ‘কবি সম্মেলন’ নামে একটি কবিতা রয়েছে, সেখানে আছে খিলান চুরমার করে দেওয়ার কথা। তো আপনারা কি এরকম কোনো কিছু চুরমার করতে চেয়েছিলেন? আপনি প্রথমেই বললেন যে আপনার কবিতার মধ্যে সংগীত একটা প্রভাব ফেলেছে, যার সূত্রে আপনার কবিতার মধ্যে একটা বিশুদ্ধ স্বর লক্ষ করা যায়। আবার ঠিক একইরমভাবে, যাঁর কথা আপনি উল্লেখ করেননি, আপনার কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে একটা উৎপলীয় ধারাও রয়েছে। সেটা কি সচেতনভাবে, না রাজনৈতিক আবহ, আপনার বন্ধুবৃত্ত ইত্যাদির প্রভাবে?
সৌম্য: আমি পরে দেখেছি, উৎপলকুমার বসুর প্রভাব যতটা না পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে, তার থেকে বেশি হয়তো বাংলাদেশে পড়েছে— আমার বন্ধুদের মধ্যে। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।
প্রতিপক্ষ: এমনকী রাইসুর মধ্যেও…
সৌম্য: এমনকী ব্রাত্য রাইসুর মধ্যেও আছে। উৎপলকুমার বসুর যে বইটি পড়ে আমরা কলেজজীবনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে পুরী সিরিজ। এবং আবার পুরী সিরিজ। তখন বুঝতে পারছি, ওই জায়গার যে গহনতা, সেখানে প্রবেশ করতে সময় লাগছে, কিন্তু তা একেবারে উন্মাদও করে দিয়েছে প্রায়। না-বোঝার মধ্যে একটা উন্মাদনা আছে। উৎপলকুমার বসুকে ধরতে ধরতে, বারবার পড়তে পড়তে, পরতে পরতে তাঁর সমস্ত শৃঙ্খল খুলে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয় না উৎপলকুমার বসুকে আমি সচেতনভাবে এনেছি, হয়তো সেই সময় অচেতনভাবে তিনি ঢুকে থাকতে পারেন। কিন্তু সেই সময় আমরা যাঁর সঙ্গেই সঙ্গ করি না কেন, যে কবির কবিতা পড়ে আমাদের আরও লিখতে ইচ্ছে করত, বা ওইরকমভাবে লিখতে ইচ্ছে করত, তিনি প্রথম যুগে আমার ক্ষেত্রে ছিলেন শঙ্খ ঘোষ, পরবর্তী যুগে জয় গোস্বামী— এটা কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই। তারপরে যখন আমি সেখান থেকেও বেরিয়ে নিজের একটা ভাষা তৈরি করার চেষ্টা করছি— এই যে যেমন খিলান ভেঙে দেওয়ার কথাটা বললেন— তার মধ্যে একটা, ঠিক ভাঙচুর নয়, বরং সেটাকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। আমি যখন ’৯৬ সালে এখানে আবার অনেক বছর বাদে এলাম, তখন কয়েকজন তরুণ কবি এলেন। প্রসূন ভৌমিক, সাম্যব্রত জোয়ারদার— এঁরা বিজল্প বলে একটি পত্রিকা করতেন। ওঁরা আমার বাড়িতে এসেছিলেন। ওঁরাও আমাকে বললেন, “আপনি যে সময়টাকে ফেলে গেছেন, তার পরে জল অনেক গড়িয়ে গেছে। এখন কিন্তু আমরা এভাবে ভাবি না। কোন কাগজে লেখা দেব, কি কোন কাগজে লেখা দেব না।” এবং সেটাও কিন্তু একটা বড় চিন্তা, কারণ কোন কাগজে লেখা দেব, সেখান থেকে জিনিসটা শুরু হলেও মাথার ভেতরে কিন্তু লড়াইটা শুরু হয়ে যায় অন্যরকমভাবে— যে আমি এই ধরনের কবিতা লিখব বেশি, এই ধরনের কবিতা পড়ব বেশি, যা মনস্তত্ত্বের অনেক বেশি গভীরে এবং গহনে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেটা ব্যক্তি-সমষ্টি-রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে একটা ভাবনার বস্তুপিণ্ড হয়। সেইরকমভাবে ভাবতে ভাবতেই ওই ধরনের লেখাগুলো লেখা আর কী।
প্রতিপক্ষ: আপনার কবিতার যে রাজনীতি, সেখানে আবহমান বাংলা বা বৃহৎ বঙ্গ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আপনার মহাপৃথিবীর ওয়েবসাইট বইটিতে দু’টি জিনিস আপনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ— রবীন্দ্রনাথ এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। আপনি সেখানে স্পষ্টভাবেই বলেছেন, এছাড়া নাকি বাঙালির আর কিছু হয়ইনি। এই চিন্তার পিছনে রাজনীতির জায়গাটা যদি একটু বলেন।
সৌম্য: একাত্তরের ব্যাপারটা তো দুটো বাংলা মিলিয়েই, কারণ একাত্তরেই মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে, আবার একাত্তরেই নকশাল আন্দোলন চলছে। এই দুটোই কিন্তু একটা বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা থেকে নিপীড়িত জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জায়গা থেকে তৈরি হয়েছিল। দুটো দেশের মধ্যেই এটা একটা সাধারণ ব্যাপার হিসেবে চোখে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন হচ্ছে নিপীড়িত জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দিকে যাওয়া। আর নকশাল আন্দোলন হচ্ছে নিপীড়িত শ্রমিক-মজুরদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেখানে তাদের একটা প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এবং তার জন্য সেই যে প্রতিষ্ঠান, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। বাংলাদেশে দেখি সেটা পাকিস্তান সরকারের প্রতিষ্ঠান। আর পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার তখন রাজত্ব করছে, তার প্রতিষ্ঠান। এই লড়াই দুটো থেকে তৈরি হল বাঙালির (যেটাকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন) আত্মশক্তির পুনর্নির্মাণ। এই জায়গাটা যখন তৈরি হল, তখন আমার মনে হল এই লড়াই দুটোর ক্ষেত্রে জনগণের যে বিরাট বিস্তারের মধ্যে পৌঁছনো গেল, সেটা কিন্তু এর আগে কখনো হয়নি, বা এর পরেও কিন্তু আমরা এত বড় একটা স্কেলে আত্মশক্তির পুনর্নির্মাণ দেখিনি। সেটাই আমার ভাবনাতে এসেছিল।
প্রতিপক্ষ: এটা তো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বললেন। অন্য আরেকটি বিষয়ে ঢুকব। আমি যে পত্রিকার হয়ে এই সাক্ষাৎকার নিচ্ছি, আপনি সেই পত্রিকার ভেতরকারই মানুষ। সেই পত্রিকার ট্যাগ লাইন ‘বড় বাংলার সাহিত্য’। সেই সূত্রেই বলি, আপনি বলছেন রবীন্দ্রনাথ একটা বড় ঘটনা। আর তারপরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং নকশালবাড়ির ক্ষেত্রে আপনি ভেঙে যেটা বললেন। তো রবীন্দ্রনাথ যদি একটা সেতু হন, তার আগে যেগুলোকে কোট আনকোট মধ্যযুগের কবিতা বলা হচ্ছে, তারপরে রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ এলেন। জীবনানন্দকে সফল বুর্জোয়া কবি বলা যায়, কারণ তিনি আধুনিকতার অসাড়তাকে বুঝতে পারছেন। এছাড়া কল্লোল যুগের কবিরা বা বুদ্ধদেব বসুরা কবিতা লিখছেন প্রায় ফরাসি ভাষার মতো করে। এইখানে, মানে এই তিরিশের দশকে এসে কোথাও একটা কি বাংলা কবিতার আবহমানতার সঙ্গে ছেদ তৈরি হল?
সৌম্য: বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলছেন যে, আমরা সারাদিন রবীন্দ্র-বিরোধিতা করে রাত্রিবেলা রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা নিয়ে, সেই কবিতাগুলো পড়তে পড়তেই ঘুমোতে যেতাম। অর্থাৎ ওঁদের ভেতরে একটা ভক্তি ছিল, কিন্তু একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার যে দার্শনিক জগৎ, তার থেকে সরে গিয়ে তাঁরা একটা বাস্তব জগতে আসতে চাইছিলেন— যেখানে মানুষের শরীর, প্রেম, ভালোবাসা, তার মানবী যে সমস্ত প্রয়োজন, সেইগুলোও কবিতায় আসবে। এটা একটা বিষয়গত লড়াই ছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কল্লোল যুগ বলে যে বইটি আছে, সেটা পড়ার পরে (ক্লাস এইট নাগাদ পড়ি) আমি বুঝতে পারি যে ওঁদের ভাবনাটা কী ছিল। অর্থাৎ ওঁরা বিরোধিতা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই বিরোধিতার মধ্যেও কোথাও একটা রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিবেদনও ছিল। এই বিরোধিতাটা না করতে পারলে ওঁরা হয়তো ওঁদের মতো করে কাজ করতে পারতেন না। সেটাকে শিল্পের জায়গা থেকে একটা অভ্যুত্থান বলা যেতে পারে, বা নিজের স্বর খোঁজার একটা চেষ্টা বলা যেতে পারে। আজকের কবিরা হয়তো সেটা ব্যক্তিগতভাবে করবেন। তখন হয়তো সেটা সমষ্টিগতভাবে হত।
প্রতিপক্ষ: কিন্তু বাংলার যে ওরাল ট্র্যাডিশনের কবিতা, বা রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগে বাংলার বড় যে কবিরা ছিলেন, সেখান থেকে কল্লোল যুগ বা তিরিশের দশকে এসে একটা শিকড়-বিচ্ছিন্নতা, এক ধরনের ইউরোসেন্ট্রিক চেতনা কি বাংলা কবিতায় চলে এল না?
সৌম্য: হ্যাঁ,অবশ্যই। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। অরুণ মিত্রকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, “আপনি কি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে দেখেছেন?” উনি বললেন, “হ্যাঁ, দূর থেকে?” আমি বললাম, “কেন?” তখন উনি বললেন, “আসলে উনি বাংলায় কথাই বলতেন না।” তার মানে সুধীন্দ্রনাথ একজন কেতাদুরস্ত সাহেব ছিলেন। স্যুট পরতেন, হ্যাট পরতেন, ইংরেজিতে কথা বলতেন। কিন্তু অসাধারণ সমস্ত বাংলা কবিতা তো উনিই লিখেছেন। “একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী”— এ তো সুধীন্দ্রনাথেরই লেখা, যিনি বাংলায় কথাই বলতেন না। বুদ্ধদেব বসুও তুলনামূলক সাহিত্যের একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি সারা পৃথিবীর সাহিত্য পড়েছেন এবং আমেরিকায় গিয়ে থেকেছেনও। অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হওয়া ছাড়াও বস্টনে গিয়ে দীর্ঘকাল ছিলেন। নিজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন। জীবনানন্দ তো ইংরেজির অধ্যাপকই ছিলেন। দেখা যাচ্ছে তাঁরা অডেন, স্পেন্ডার থেকে শুরু করে ফ্রান্স থেকে বোদলেয়ারকে নিয়ে এসে এমন একটা জায়গা তৈরি করলেন যে সেখানে তাঁদের কবিতায় এই প্রভাবগুলোকে তাঁরা সরাসরি আসতে দিলেন। সেই প্রভাব কিন্তু আমার ক্ষেত্রেও এসেছে। যখন আমি পরে লিখতে গেছি, তখন সেটা নিয়ে আমি চিন্তাও করেছি। এ প্রসঙ্গে কেতকী কুশারী ডাইসনের একটা কথা বলি। তিনি অক্সফোর্ডে থাকেন, তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের সম্পর্ক। ১৯৯৯ সালে ডালাসে আমি একটা সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলাম। সেখানে তিনি এসেছিলেন। সেখানে তাঁকে আমি বলেছিলাম, ইউরোপ বা আমেরিকার যে জীবন, সেটা বাংলা কবিতায় আমি আসতে দেব কি না। উনি বলেছিলেন, “অবশ্যই দেবে, কারণ তুমি যদি কলেজস্ট্রিটের মতোই কবিতা এখানে এসেও লেখো, তাহলেও এখানকার জীবনযাপন, জীবনদর্শন, জীবনধারা তোমার কবিতায় যে একেবারেই আসেনি, সেটা ধরে নেওয়াটা খুব ভুল হবে। তাই সেটাকে সচেতনভাবেই আসতে দাও।” দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সেটা স্থান বা রাস্তা বা মানুষের নাম দিয়ে কেবল হবে না। নিজের ভেতরের অনুভবটাকে নিয়ে ভাবতে হবে। তখন আমি সেইভাবেও খানিকটা ভাবি। বুদ্ধদেবদের সময় যে ইউরোপীয় প্রভাবটা ছিল, সেটা সাহিত্য পাঠ এবং সাহিত্যচিন্তার মধ্যে দিয়ে ছিল। আমার ক্ষেত্রে যেটা হল, সেটা হচ্ছে আমি তো তাদের নিয়ে ঘর করি। সেই শ্রেণিকে আমি পড়াই। আমি সেখানে করপোরেটে চাকরি করি। এই ব্যাপারগুলোর সূত্রে বহু মানুষের সঙ্গে, বহু দেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার, জীবনযাপনের যে অভিজ্ঞতা, সেটা কিন্তু কবিতায় অন্যভাবে আসে। আমার মনে হয় যে সেই যাত্রাটা এখনও শেষ হয়নি, এই খোঁজাটা এখনও চলছে।
প্রতিপক্ষ: অখণ্ড বাংলা থাকাকালীন বা ঔপনিবেশিক যুগেরও আগে বাঙালি মুসলমান কবিদের পদাবলী সাহিত্য থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ যখন থেকে বাংলায় আধুনিক কবিতার উন্মেষ হল, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে মুসলমান কবিদের খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যাঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদের কথা আমরা বলতে পারি, যাঁর খুব বিখ্যাত লাইন— “রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?” কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিরিশের দশকের কবিদের নিয়ে আলোচনায় কোথাও ফররুখ আহমদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এমন নয় যে ফররুখ আহমদ খুব মুসলমান পরিচয়বাদী জায়গা থেকে কবিতা লিখছেন। কেউ কেউ তাঁকে সেভাবে চিহ্নিত করেন বটে, কিন্তু ফররুখ আহমদের কবিতা একেবারেই আধুনিক কবিতা, নাগরিক কবি তিনি। এ ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়? কেন এঁদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রয়াস করা হল?
সৌম্য: এখানে দুটো ব্যাপার লক্ষ করার মতো। প্রথমত এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, ইউরোপের কবিতা যে কলকাতাকেন্দ্রিক, পশ্চিমবঙ্গীয়, হিন্দু, শিক্ষিত মানুষকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল, তার একটা বড় কারণ তাঁরা ইংরেজি পড়েছিলেন। আর আপনার হয়তো মনে থাকবে যে, একটা সময় ছিল যখন দুই বাংলা মিলিয়েই (মানে তখন তো অখণ্ড বাংলা ছিল) মুসলমানরা ইংরেজিটা সেভাবে পড়েননি। আর তার মধ্যে একটা বিরোধিতার জায়গাও ছিল, যে আমরা আমাদের সাহিত্যটাই পড়ব। তাই সামগ্রিকভাবে আমার মনে হয় যে, তাঁদের মধ্যে খানিকটা ল্যাক অব এক্সপোজার হয়েছিল। এটা একটা ঘটনা কিন্তু। কারণ সেই সময় দেখা যাচ্ছে যে, তাঁদের মধ্যে খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ হয়তো বিলিতি ভাবনাচিন্তা, বিলিতি লেখাপড়া করছেন। দু’ নম্বর, যদিও সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ হয়, তার অনেক আগে থেকেই সমৃদ্ধ পরিবারের মানুষরা (যেমন আমার নিজের পিতামহ, বা পরিচিত আরও অনেকের প্রপিতামহ বা পিতামহ) পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেছেন। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ারও একটা ধারা তৈরি হয়েছিল। কাজেই ফররুখ আহমদ সেই ঘরানার মধ্যে পড়েন, শহীদ কাদরী সেই ঘরানার মধ্যে পড়েন, কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকও এই ঘরানার মধ্যে পড়েন, তিনি বর্ধমান থেকে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ,এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু কলকাতার। কলকাতাকেন্দ্রিক যে তথাকথিত ক্লাসিকাল, শুদ্ধ বাংলা এবং ইউরোপীয় চিন্তা— এগুলো এঁরা কিন্তু সহজেই পেয়েছিলেন। পেয়ে যখন তাঁরা পূর্ববঙ্গে যান, সেখানে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতার বলে, বা নিজেদের লেখার জগৎ, বা ভাবনার যে পরিপুষ্টতা, তার ফলে সেগুলোই ওখানে প্রচার করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিতও করতে চেয়েছেন। যার ফলে পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যে একটা বিরোধিতা তৈরি হল— যে পূর্ববঙ্গের মানুষ বলছেন, আমরা আমাদের মুখের ভাষায় কেন লিখব না, কেন আমাদের কলকাতার তথাকথিত শুদ্ধ ভাষায় লিখতে হবে, নাগরিক ভাষায় লিখতে হবে। কাজেই আমার মনে হয় এটা বহু বর্ষব্যাপী, বহু দশকব্যাপী একটা ঘটনা, যেটা আজকে হয়তো খানিকটা মোকাবিলার জায়গায় এসে পৌঁছেছে। যেমন ধরুন, কাঁচড়াপাড়া নিয়েও ফররুখ আহমদের একটা অসামান্য কবিতা আছে, যেটা আমরা বাংলাদেশে গিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যে পশ্চিমবঙ্গের সিলেবাসে ফররুখ আহমদ থাকবেন না কেন। আমার মনে হয় যে এটা একটা খুব জটিল ব্যাপার। তার মধ্যে রয়েছে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং তার একটা অভিভাবকতা। তার মধ্যে রয়েছে (যদি আমি জাতপাত বাদও দিই) ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ার আত্মশ্লাঘা, তারপরে আমরা নিজস্ব ভাষা কী তৈরি করছি, তার একটা আত্মশ্লাঘা। তার ফলে যেটা হল, এর বাইরে যাঁরা রয়েছেন, যাঁরা চৈতন্য-লালন থেকে শুরু করে পদাবলী পর্যন্ত পড়ে এবং তারপরে আলাওলের পদ্মাবতী ইত্যাদির সূত্র ধরে একটা ধারা তৈরি করেছেন, তাঁরা এবং তাঁদের সেই ধারাটা কিন্তু আমার মনে হয় অনেকটাই উপেক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে যখন বাংলাদেশ তৈরি হয়, তখন এখান থেকে যাওয়া অনেকেই ওখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপক বা কবি বা লেখক হয়েছেন।
প্রতিপক্ষ: এমনকী রাজনীতিবিদও…
সৌম্য: এমনকী রাজনীতিবিদ হয়েছেন। এঁরা কিন্তু কখনোই মনেপ্রাণে পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়েননি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়ে যাওয়া যে ধারণা, ভাবনা, ভাষা, ভঙ্গি, সাহিত্য, সেই সমস্ত কিছু নিয়েই তাঁরা তাঁদের পরিমণ্ডল তৈরি করেছিলেন। আর তার একটা বিপুলবিস্তারী প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবটাকে আইডেনটিফাই করতে পারাটাও কিন্তু মুশকিল, কারণ সবাই তখন এই প্রশ্নে আসছেন যে, তাহলে কি দুই বাংলা মিলিয়ে একটাই ভাষা হবে, নাকি তার যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা এবং তার বৈচিত্র্য রয়েছে, সেগুলোকেও আমরা কবিতায় আসতে দেব, বা সেগুলোকে একটা ধারা হিসেবে গণ্য করব। এখন কিন্তু সেই পর্যায়টা আর নেই, কারণ অনেক জায়গা থেকে এটার থেকে বেরিয়ে এসে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। যেমন ধরুন সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন পরানের গহীন ভিতর, বা ফরহাদ মজহার লিখেছেন এবাদতনামা— এগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে ওই প্রতিষ্ঠার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের কালানুক্রমিক যে ঐতিহ্য, সেটাকে ধরবার একটা চেষ্টা রয়েছে। আবার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমি মূলত ভাবছি উৎপলকুমার বসু থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের কালীকৃষ্ণ গুহ ধরুন, বা দেবারতি মিত্র ধরুন, বা মণীন্দ্র গুপ্ত ধরুন, বা তার পরে আমরা যদি আরও বেরিয়ে আসি, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়— এসব মিলিয়ে অনেক ধরনের ভাবছি। কিন্তু কেউ যখন পূর্ববঙ্গীয় লব্জ ব্যবহার করছেন, কিছু ইসলামি রেফারেন্স ব্যবহার করছেন, তখন সেটা কি আসলেই তাঁদের নিজেদের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠছে? এই প্রশ্নটা সম্প্রতি আমাদের একটা আড্ডাতেও ধরা হল। আমার বন্ধু কবি ব্রাত্য রাইসু এই প্রশ্নটা করেছিলেন এবং এ নিয়ে একটা পোস্টও দিয়েছেন ফেসবুকে। সেখানে রাইসু দেখাচ্ছেন যে তিনটে পথ রয়েছে বাংলাদেশের কবিদের ক্ষেত্রে। এক নম্বর, একদম কলকাতার মতোই ভাবব, কিন্তু সেটার মধ্যে খালি পূর্ববঙ্গীয় লব্জ ব্যবহার করব বা কিছু ইসলামি অনুষঙ্গ আনব। দু’ নম্বর, পশ্চিমবঙ্গীয়দের মতো করেই লিখব। আর তিন নম্বর হচ্ছে, (যেটা উনি বলতে চাইছেন) বাংলাদেশের যে জীবনযাপন, তার যে অভিভব, তার যে অনুষঙ্গ, সেগুলোর ভিত্তিতে আমি নিজের কথাই বলব, সেটা কোন ভাষায় বলব, তা তখন গৌণ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় যে এই ধারাটাকে আমাদের বুঝতে হবে। যদি আমরা ফররুখ আহমদ থেকে শুরু করে আজকের তরুণতম রুমান্না জান্নাত পর্যন্ত আসি, তাহলে দেখা যাবে অনেক পরিবর্তনের পরে এই যাত্রাটা হয়তো কোনো একটা দিকে এগোচ্ছে। তার জন্য যাঁরা দিশারি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের কথাই আমি উল্লেখ করব, অবশ্যই আল মাহমুদের কথাও উল্লেখ করব। যদিও আল মাহমুদ সম্পর্কে অনেকে বলেন, আসলে কিন্তু তিনি কলকাতার ধারাতেই লেখালিখি করেছেন।
প্রতিপক্ষ: কৃত্তিবাসীয় ধারা…
সৌম্য: হ্যাঁ, কৃত্তিবাসীয় ধারা। শহীদ কাদরীর কথাই ধরুন। তাঁর সঙ্গে তো আমার অনেক দিনের আড্ডা, পরিচয়, আলাপ। নিউইয়র্কে যখন তিনি থাকতেন, তখন ঘনঘনই তাঁর বাড়িতে যেতাম। তিনি আমাকে প্রথমেই বলেছিলেন যে, তাঁর ধারাটি খুব পরিষ্কার। সেটা হল বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। একটা নামও বাংলাদেশের নয়। অর্থাৎ ওই ধারাতে তিনি ভাবছেন, লিখছেন, কেবল অনুষঙ্গগুলো এসে যাচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনা থেকে। কিন্তু ‘তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা’— এটা হয়তো সুনীলও লিখতে পারতেন। সুতরাং শহীদ কাদরীর ধারাটি পশ্চিমবঙ্গীয় ধারাই। উনি সরাসরি বলেই সেটাকে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে এর পরে একটা পরিবর্তন হওয়ার দরকার ছিল। ১৯৯০/’৯২, কি তার সামান্য একটু পরে আমার হাতে এসে পৌঁছল একটি অসামান্য বই।
প্রতিপক্ষ: সেই অসামান্য বইটা কী?
সৌম্য: অসামান্য বইটা হল— এবাদতনামা। তখন আমি থাকি নিউইয়র্ক রাজ্যের বাফেলো শহরে। ঘন তুষারাবৃত একটি অঞ্চল। তখন আমি মাস্টার্সের ছাত্র। সেখানে সারাদিনের ক্লাসের পরে, হোমওয়ার্ক করার পরে যত কবিতার বই পাই, সেগুলো পড়ি। আমার বন্ধু আলম খুরশিদ (তিনি তারপরে চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে সেখানে ‘বিশদ বাংলা’ বলে একটা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন, বিস্তার বলেও তাঁদের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল) তখন ওখানে বাংলাদেশ থেকে বই আনাতেন। তিনি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। আমি বলব তিনি এমন একজন পুস্তক সরবরাহকারী, যিনি অতি শিক্ষিত, অতি মার্জিত, রুচিবান। তিনি এনে দিতেন এমন সব বই যেগুলো তখনও পর্যন্ত কেউ সেভাবে পড়েনি। কিন্তু তিনি মনে করতেন, সেই বইগুলো পাঠকদের পড়া উচিত। তিনি প্রায়ই এরকম করতেন যে, হয়তো বললেন, “সৌম্য, তুমি দশটা বই চেয়েছ, তোমাকে আমি দশটা বই পাঠালাম। এগুলো হচ্ছে তোমার চাওয়া বই। তোমার না-চাওয়া বইয়ের মধ্যেও আরও তিনটে পাঠালাম, এগুলো তোমার পড়া উচিত।” আমিও সানন্দেই সেগুলো কিনে নিতাম। তার মধ্যে ছিল ফরহাদ মজহারের এবাদতনামা বইটি। ওই বইটি পড়ার পরে আমার মনে হল যে, এই ভাষা এবং এই জগৎ বাংলা কবিতায় আমি কখনো দেখিনি। পরবর্তীকালে আমি যখন ফরহাদ ভাইয়ের একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম (সেটা অগ্রবীজ পত্রিকায় বেরিয়েছিল বছর দশেক আগে), তখন সেখানে উনি একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন। ওই বইটি যে ভাষায় বা ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে, তার মধ্যে যে ইসলামি অনুষঙ্গ আছে সেটা ঠিকই, কিন্তু বক্তব্যের ভেতরে একটা প্রতিবাদও রয়েছে। ফলে তাঁর একটা সংশয় ছিল যে, তথাকথিত যাঁরা ধার্মিক এবং নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি, তাঁরা হয়তো এই বইটি দেখে কোনোভাবে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।
প্রতিপক্ষ: মানে মোল্লারা?
সৌম্য: হ্যাঁ। একদিন দুপুরে তাঁর বাড়িতে একজন এলেন। তাঁকে দেখেই মৌলবি বলে মনে হয়। ফরহাদ ভাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার?” তিনি বললেন, “আমি আপনার মুরিদ হতে আসছি?” অর্থাৎ শিষ্য হতে এসেছি। তখন ফরহাদ ভাই বললেন, “সে কী? আমার তো ভয় ছিল যে আমার লেখার মধ্যে কোথাও কোথাও ধর্মীয় চিন্তার বিরোধিতার জায়গাও রয়েছে।” কারণ ফরহাদ ভাই তো আগে ছিলেন কমিউনিস্ট। তখন তিনি বললেন, “তা থাকতে পারে, কিন্তু তুমি তো আমার সঙ্গে কথা বলছ, তুমি তো আমার সঙ্গে কানেক্ট করছ। এইটাই হল বড় কথা।” এই যে যোগাযোগের সেতু তৈরি করা বা সেতুবন্ধন, এটা আমার নিজের দর্শনে কিন্তু সারা জীবনই ছিল। দুই বাংলার মধ্যে সেতু নির্মাণ, উত্তর বাংলা-দক্ষিণ বাংলা, এ বাংলা-সে বাংলা, আমেরিকার বাংলা, ইউরোপের বাংলা, অস্ট্রেলিয়া, এমনকী পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বগুড়া— এই সমস্ত জায়গার বাংলা কবিতাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। তবে এক জায়গায় নিয়ে আসা মানে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন নয়, এক জায়গায় নিয়ে আসা মানে হচ্ছে মোকাবিলা— তাদের মধ্যে একটা ডায়ালগ চলবে। তাই আমার মনে হল যে, এবাদতনামা বইটার মধ্যে দিয়ে সেই ডায়ালগটা যেন শুরু হল। কেবল সেই মুরিদ হতে চাওয়া ধর্মপ্রাণ মানুষটির সঙ্গে নয়, আমাদের মতো পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত, হিন্দু প্রিভিলেজড ক্লাস থেকে আসা পাঠকদের সঙ্গেও যেন সংযোগ, ডায়ালগ শুরু হয়ে গেল। তারপর লক্ষ করলাম… সৈয়দ শামসুল হক কত বড় কবি বা লেখক, তা নিয়ে নানান মানুষের নানান মত থাকতে পারে। আমি মনে করি তাঁর পরানের গহীন ভিতর ওই একইরকম জায়গা থেকে আমাকে একটা স্তোত্র তুলে দিল। “আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি”— এই ব্যাপারটা যেন ওই কবিতাগুলোর মধ্যেও এল। তারপরে তো আমরা দেখেছি যে সেটাকে ফলো করে অনেকে লিখেছেন এবং অনেকে সরেও এসেছেন। কিন্তু ওইটা একটা বড় পর্যায় আমার ক্ষেত্রে।
প্রতিপক্ষ: আপনার এতক্ষণের কথাবার্তার মধ্যে ঘুরেফিরে আসছে বড় বাংলার প্রসঙ্গ। বঙ্গের বাংলা অঞ্চল ছাড়াও গোটা বিশ্বে যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বা বাংলার মানুষ ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের জায়গা থেকে একটা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তৈরি করার ভাবনা আপনার আছে। দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের থেকে বাংলাদেশে আপনার জনপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ বেশিও বটে। বাংলাদেশে আপনার সহজ বিচরণ। এটা গৌতম চৌধুরীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকেই হয়তো বাংলাদেশে কবিতা পড়তে যান, বা অনেকেই বাংলাদেশের কবিদের সঙ্গে মেশেন। কিন্তু আপনি বা আপনার মতো কয়েকজন বাংলাদেশকে গভীরভাবে চেনেন (এখানে বাংলাদেশের কবিতার কথাই বলছি বা সাহিত্যের কথা বলছি, বা সমাজজীবনের কথাও বলছি)। আবার বাংলাদেশের লোকজনের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি একটা আকুতি আছে (আমি নিজে বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন ছিলাম, আপনি জানেন)। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের মধ্যে বাংলাদেশকে ‘অপর’ ভাবার, অপরায়নের জায়গা থেকে বাংলাদেশকে দেখার একটা প্রবণতা কোথাও আছে বলে কি আপনি মনে করেন না?
সৌম্য: আছে বলেই একদিন আমরা ছ’জন মিলে একটা বাংলা কাগজ তৈরি করি। তার নাম অগ্রবীজ। এই অগ্রবীজ-এর যে সম্পাদকমণ্ডলী, তাঁদের ঈষৎ পরিচয় দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। অগ্রবীজ-এর সম্পাদকদের মধ্যে আমি যেমন আছি, তেমনি আছেন কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, যিনি ঢাকার, কিন্তু থাকেন সিডনিতে। তাঁদের মধ্যে আছেন চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ, যিনি চট্টগ্রামের, কিন্তু থাকেন টেক্সাসের ফোর্টওয়ার্থে। তাঁদের মধ্যে আছেন সুবিমল চক্রবর্তী, যিনি ঢাকার, কিন্তু থাকেন ডালাসে। তাঁদের মধ্যে আছেন তাপস গায়েন, যিনি ঢাকার, কিন্তু থাকেন নিউইয়র্কে। তাঁদের মধ্যে আছেন সাদ গামালী, যিনি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের, সম্ভবত রাজশাহী অঞ্চলের এবং তিনি থাকেন কানাডায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর নানান প্রান্তে, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডায় ছড়িয়ে থাকা বাংলা ভাষার লেখক-কবিরা এক জায়গায় এসে সম্পাদনা করছেন এমন একটি কাগজ যাতে ওই সমস্ত অঞ্চলের লেখা তো থাকছে বটেই, তাছাড়া বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আমরা নিয়মিতভাবে লেখা চেয়ে নিয়ে, সেটা পিয়ার রিভিউ করিয়ে, যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রতি বছর একটা করে বের করি। সেই বিশেষ সংখ্যার নানান বিষয় ছিল, একবার ছিল বিশ্বায়ন, একবার ছিল কবিতা লেখা, কবিতা পড়া (যেটা আমার সম্পাদনা করা)। পরবর্তী সংখ্যার বিষয় হতে চলেছে (সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের সম্পাদনায়) অনুবাদ-চিন্তা। একটা বিষয় এর মধ্যে ছিল, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেখান থেকে আপনার এই প্রশ্নের অনেকগুলো উত্তর পাওয়া যাবে। সেই সংখ্যার বিষয়টাই ছিল— নানা বাংলা, নানা বাঙালি। আর আরেকটা সংখ্যায় আমাদের বিষয় ছিল— বাঙালির কাজ। সেই কাজটাকে আমরা পেশাগত জায়গা হিসেবে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। দুই বাংলা এবং তৃতীয় বাংলা, বা চতুর্থ বাংলা (যদি আমরা সারা বিশ্বকে ধরে নিই), সেই যে বাংলাগুলো রয়েছে— সেই সবটা মিলিয়েই একটা সংগ্রহযোগ্য সংখ্যা। সেই সমস্ত পেশার চূড়ান্ত পর্যায়ে যাঁরা আছেন, আবার সাধারণ পর্যায়ে যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সেখানে লিখেছেন। নানা বাংলা, নানা বাঙালি সংখ্যায় আমরা ভাষাটাকে ধরবার চেষ্টা করেছি— ভাষা পরিবর্তন, বিভিন্ন লৌকিকতা, তাদের ধর্মচিন্তা, তাদের সামাজিক চিন্তা, সাহিত্যচিন্তা, তাদের সাহিত্য করবার যে অভিলাষ, আর সেখান থেকে সাহিত্য করবার অভিজ্ঞতা, সেইগুলোর বদলের চিন্তা ইত্যাদি। আমার মনে হয়েছে যে, এখানে অপরায়নের থেকেও বড় কথা হল, যোগাযোগহীনতা। আমাদের সঙ্গে তো বিদেশের বহু মানুষের সকাল-বিকেল কথা হয়, যেহেতু আমরা বিদেশে থাকি। আমার পাশের বাড়িতে থাকেন একজন ইরানি ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব। তিনি প্রায়ই আমার বাড়িতে চা খেতে আসেন, আমিও তাঁর বাড়িতে চা খেতে যাই। আমার অপর পাশে থাকেন একজন ইহুদি ভদ্রলোক, তিনি ইজরায়েলের। তাঁর সঙ্গেও আমাদের খুব বন্ধুত্ব। আমি মনে করি, দুটো মানুষের মধ্যে যখন যোগাযোগ বা এক্সপোজার হয়— তা সে তারা যে শ্রেণিরই হোক, যে গোত্রেরই হোক, যে ভাষারই হোক— তাদের মধ্যে এই আলোচনাগুলো, আলাপগুলো, মোকাবিলাগুলো যখন হয়, তখন সবকিছু ভাঙতে শুরু করে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব কৌতুককর, কারণ একটা ফ্লাইটে কুড়ি মিনিট লাগে যেতে, যেটা কিনা বাগডোগরায় যাওয়ার থেকেও কম সময়। অথচ কেন তাহলে খুব বেশি সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা বাংলাদেশে যাচ্ছেন না? বা বাংলাদেশ থেকে আমি আমার বন্ধু ব্রাত্য রাইসুকে কলকাতায় আনতে পারিনি। সে বলছে, “দোস্তো, তুই যখন পরের বার আসবি, তখন যাব।” এরকম করে অনেক পরের বার হয়ে গেল। হয়তো সামনের বছর, ইনশাল্লাহ, আমি ওকে আনতে পারব। এখন এই যে ব্যাপারগুলো আমাদের মধ্যে চলছে, এই যোগাযোগহীনতাটা খানিকটা মুখ ফিরিয়ে থাকা— দু’দিকেই। আমার মনে হয়েছে বাংলাদেশের কবিরাও অনেক সময় মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন, যে “কলকাতার দাদা আইসে”। সেটাও যেমন তাঁদের ক্ষেত্রে খানিকটা অভিমানের জায়গা, যে কেন আমি অভিভাবকত্ব স্বীকার করব, সেখানে আমার উত্তর হচ্ছে অনুসন্ধান করতে হবে তাঁর নিজের মনের মধ্যে দিয়ে। সেটাকে ব্যক্তিগত আলাপের জায়গা থেকে বন্ধ না করাই শ্রেয়। একইসঙ্গে পশ্চিমবাংলার কবিদের প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে শঙ্খ ঘোষের সেই বিখ্যাত বক্তৃতার কথা, যেটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ১৯৮৯ সালে হয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, “কলেজস্ট্রিটের বোতল ভেঙে দাও”। অর্থাৎ পুরো কবিতার জগৎটা তখন কলেজস্ট্রিট-কেন্দ্রিক, কফি হাউজ-কেন্দ্রিক। তাঁরাই কেবল পরস্পরের কবিতা পড়ছেন। তাঁরা বাংলাদেশে যাবেন কী, তাঁরা শিলিগুড়ির কবিতাই পড়েননি। সেই জায়গা থেকে ‘শত জল ঝর্ণার ধ্বনি’ যখন তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম, তখন তার মধ্যেও একটা সেতুবন্ধন ছিল। আমার ক্ষেত্রে যেটা সুবিধে হয়েছিল, যে আমি অনেক অল্প বয়স থেকে বাংলাদেশে ঘনঘন গিয়ে এবং অনেক বন্ধু তৈরি করে সেই যাওয়াটা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলাম। এবং আমেরিকায় চলে যাওয়ার পরে এমনও হয়েছে যে আমি সেখান থেকে সরাসরি ঢাকায় গিয়ে, তারপর সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছি। বা কখনো পশ্চিমবঙ্গে এসেই পরবর্তী দিনে ঢাকায় চলে গেছি। এমনও হয়েছে যে সকালবেলা ঢাকায় গিয়ে, রাত্রে থেকে পরের দিন ভোরবেলায় ফিরে এসেছি, অগ্রবীজ-এর কাজ করে। সুতরাং এইটা আমাদের কাছে মনে হয় যে (যদিও অনেকটা দূরে থাকি), একই জায়গায়, একই অঞ্চলে যাচ্ছি, ঢাকা বা কলকাতা সেখানেই মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমার সেই দূরত্বটা এতটাই, এমনই মঙ্গল গ্রহে থাকি যে, এই দুটো এক জায়গায় এসে যাচ্ছে। কিন্তু এটা এখানকার বর্ডার পারের মধ্যে অতটা সম্ভব হয়নি। কেউ ডাকলে আসব, আমন্ত্রণ জানালে আসব— এরকম হয়েছে। শেষ যে কাজটা আমি করলাম, সেটা অগ্রবীজ-এর একটা কর্মশালা। আমরা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিলাম। সেখানে আমরা কবিতা লেখা, কবিতা পড়া, নয়ের দশকের কবিতা, শূন্য দশকের কবিতা, আটের দশকের কবিতা— এদের বোঝার চেষ্টা করেছি। কবিতা কী করে পড়তে হয়, লিখতে হয়, সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি। তখন বাংলাদেশ থেকে অনেককে আমরা এনেছিলাম। সলিমুল্লাহ খান, সাজ্জাদ শরিফ, ফরিদ কবির, চঞ্চল আশরাফ, সোহেল হাসান গালিব, রাশেদ্দুজামান— এঁরা সকলেই এসেছিলেন। তাঁরা আসার ফলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি কর্মশালা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তো জয় গোস্বামী, রণজিৎ দাশ ইত্যাদি অনেকেই বলেছেন। সভায় ছিলেন গৌতম চৌধুরী, সুব্রত সরকার, রাহুল পুরকায়স্থ, একরাম আলি, গৌতম বসু। ফলে এই জায়গাটাকে আমরা সবসময় একভাবেই ধরার চেষ্টা করেছি, হয়তো সেটাই আমার কাজ হয়েছিল এবং থাকবেও। আমার মনে হয় যে, সেতুবন্ধনের জন্য এই এক্সপোজারটা, এই আলাপটা, এই বোঝাপড়াটা, এই মোকাবিলাটা খুব জরুরি।
প্রতিপক্ষ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।