
।। সজলকান্তি সরকার ।।
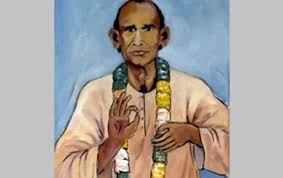
মূলত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক লোকসমাজই লোকসংস্কৃতির আধার। পল্লী অঞ্চলই লোকসংস্কৃতির লালনক্ষেত্র। এখানেই তার বাঁচা-বাড়া ও সজীব অবস্থান ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে শিক্ষিত সমাজে, শহরেও তার প্রচলন আছে সত্য কিন্তু পল্লীর সাধারণ লোকসমাজের তুলনায় অতি কম। পল্লীর মাটির মানুষগুলোর মাঝে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচরিত হয়ে আছে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি অর্থাৎ কবির ভাষায় বলা যায়- “পল্লীর প্রত্যেক পরতে পরতে লুকিয়ে আছে সাহিত্য এবং সাহিত্যের উপকরণ।” লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ লোকগীত। যার বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে ধামাইল নৃত্যগীত। বাংলার হাওরাঞ্চল যার পদচারণায় আজও অনেকটা মুখরিত। বাংলার হাওরাঞ্চলেই ধামাইল গানের একমাত্র জন্মমেদিনি বা আবাসস্থল। যেখানে জীবনের সাথে বাঁধা আছে তার আত্মজয়ী ধারা… ধামাইলের যথার্থ ব্যবহার শুরু হয় রাধারমণ দত্তের সময়ে… রাধা-কৃষ্ণের জলখেলি, প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ, মান-অভিমান, রূপ, বাঁশি ও মিলন নিয়ে রচিত বেশিরভাগ ধামাইল প্রচলিত আছে। যার মধ্যে রাধারমনের রচিত গানের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া দীন শরৎ, মহেন্দ্র গোসাই, প্রতাপরঞ্জন, শাহ আব্দুল করিম, মধুকবি, গৌরচাঁন, বাবুমোহন, গোপীধন, উপেন্দ্র, মহানন্দ, রামজয়, রসরাজ ও বিজয় সরকার তাঁদের রচিত গানগুলি আমাদের চেতনাকে শানিত করে নতুনভাবে। ভাটি অঞ্চলে ধামাইল গানের ৯৫ শতাংশই রাধারমণ রচিত। আর তাই ধামাইল বলতে সাধারণত রাধারমণের ধামাইলকেই বুঝায়… সাধারণত হাটে, ঘাটে, মাঠে, হাওরে-বাওরে, নৌকায় মাঝির কণ্ঠে ও সাধারণ মানুষের লোকউৎসবে যার গান পল্লীর সর্বত্রই গীত হয় তিনিই রাধারমণ। তাই তিনি লোককবি।
ভাটির ধামাইল ও রাধারমণ
মধ্যযুগে বাংলা ও দিল্লীর বিভিন্ন শাসনামলে অধিকার আদায়ে সংগ্রাম-বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে নির্যাতিত, বঞ্চিত. নিপীড়িত এবং প্রতিবাদী জনগণ স্থানত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। নিরাপদে বসবাসের জন্য তারা বিচ্ছিন্নভাবে গোপন আবাসস্থল খুঁজতে থাকেন। একসময় নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে বাংলার বিভিন্ন হাওর অঞ্চওকেই বসবাসের নতুন মেদিনী হিসেবে বেছে নেন। তন্মধ্য বাংলাদেশের হাওরাঞ্চল হিসেবে খ্যাত ৭টি জেলা যথা- সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলে শুরু হয় তাদের বিছিন্নভাবে অজ্ঞাতবাস। যেখানে ভাটি হিসেবে খ্যাত সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চল ছিল অতি নিরাপদ আবাসভূমি। কেননা অতি দুর্গম জলারণ্য সুনামগঞ্জ জেলা এক সময় কিংবদন্তীর কালীদহ সাগরের অংশ ছিল বলে জানা যায়। তাই সুনামগঞ্জ জনপদ হাওরের রাজধানী বলেও খ্যাত।
ধামাইল পদকার কবি রাধারমণ দত্তকে বাদ দিয়ে ধামাইলের কল্পনা কষ্টসাধ্য। রাধারমণের বিষয়ে আলাপ করব। তার আগে ধামাইলের ইতিহাসচর্চাটা জরুরী।
এককালে শ্রীহট্ট ও সুনামগঞ্জের উত্তর-পুর্বাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানগনের বসবাসের পুর্বে বন্য জাতিদের বসবাস ছিল। বিশেষ করে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত ‘জীবনবৃত্তান্ত’ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে— ‘মুসলমান রাজত্ব সময়ে নাগা, কুকি, খাসিয়া ও কুচগারদের অত্যাচারে হাওরাঞ্চলে হিন্দু-মুসলিমগন শান্তিতে বসবাস করতে পারতেন না।’ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ উত্তরাংশে উলেখ আছে— পূর্বকালে সুনামগঞ্জ জেলার পুর্বাঞ্চলে আতুয়া, জাতুয়া ও পাগলা নামে চঙ্গ জাতীয় তিন ব্যক্তি মৎস্য শিকারের জন্য এসে মৎস্যের প্রাচুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে বসতি স্থাপন করেন। তিন ব্যক্তির নামে সীমানা নির্ধারণ হয়ে স্থানের নামকরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের নামানুসারে স্থান তিনটি পরগনায় পরিণত হয়। তাছাড়া শ্রীহট্ট ও সুনামগঞ্জের নদ-নদী ও প্রাচীন জনপদের নামকরণ থেকে ধারণা করা যায় শুরুতে এখানে চঙ্গ, নাগা, কুকি, হাজং, খাসিয়া ও গারো প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিল। যেমন- দাড়াখাই, ধুপাখাই, চামটি, চেঙ্গেরখাল, খাশিমাড়া, করাঙ্গি, মাশিঙ্গ, সুতাঙ্গ, খওয়াই, লঙ্গাই, শীংলা, লংলা, মনাই ও মাগুরচামটি ইত্যাদি স্থান ও নদীর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। সুনামগঞ্জে প্রায় ৩২টি পরগনা ছিল যেখানে এরূপ নামকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তন্মধ্য আতুয়া, জাতুয়া ও পাগলা অতি প্রাচীন।
এদেশ যখন মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীন ছিল তখন নবাব বন্যজাতীদের অত্যাচার নিবারণ করতে অক্ষম হয়ে রাঢ় দেশ হতে দাসজাতীয় বহু সংখ্যক সৈনিক পুরুষ তন্নিবারনার্থে প্রেরণ করেন। সেই সৈন্যদের অধ্যক্ষ সেনাপতি ও তন্নিষ্ঠ কর্মচারী লস্কর নামে অভিহিত হয়। দাসগনকে সেনাশ্রেণী ভুক্ত করে যে যে স্থানে অসভ্য জাতিদের অত্যাচার বেশি সেই স্থানে প্রেরণ করা হয় এবং অত্যাচার যেখানে কম সেখানে লস্কর নিযুক্ত করা হয়। দাসযোদ্ধাদের প্রতাপে বন্যজাতি পরাভূত ও নিহত হয়। তাই এইসব অঞ্চলে দাস জাতি সাহসি, সহিষ্ণু ও সৎ। পূর্বে তারা যুদ্ধজীবী জাতি ছিল। পরবর্তীতে নবাব তাদের ভূমি দান করেন এবং এখানে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দেন। শুরুতে এভাবেও হাওরাঞ্চলে দাস জাতির বসতি স্থাপন হয় বলে জানা যায়।
হাওরাঞ্চলের দাসজাতি বর্তমানে ‘মাহিষ্যদাস’ নামে প্রচলিত আছে। মাহিষ্য শব্দের অর্থ যারা মহীকে বিদারণ করে অর্থাৎ কৃষি বৃত্তি অবলম্বনে জীবন নির্ব্বাহ করে। পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে যে, ‘ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য কন্যার উৎপন্ন পুত্রই মাহিষ্য’। মাহিষ্যদাসগন পরবর্তীতে বিভিন্ন উপাধিতে বিভক্ত হন। ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলীমের মেল বন্ধনে হাওরবাসী অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন করে। হাওরের বিশালতায় মুক্ত চিন্তা ও মানব প্রেমর মহিমায় গড়ে ওঠে হাওরবাসির জীবন ও সংস্কৃতি।
হাওর অঞ্চলের ইতিহাসে জলদুস্যদের অনেক গল্প কাহিনীও শোনা যায়। অনেকের মতে ধনু নদীর তীরে হাওরের প্রথম জনবসতি শুরু হয় । যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর বা রাজস্থান থেকে আসেন। যাঁরাই হাওরবাসীর পূর্ব পুরুষ বলে দাবিদার। মূলত হাওর বসতির ইতিহাস নিয়ে রয়েছে নানান কিংবদন্তীর নানা কথা।
হাওর বসতির শুরুতে মানুষের দস্যুভৃত্তি ও পরবর্তীতে মৎস্যজীবী হিসেবে জীবিকা নির্বাহই ছিল একমাত্র অবলম্বন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নের ফলে পরে মানুষ কৃষিকাজ বেচে নেয়। যেখানে ছিল পানির ভয়নঙ্করতা ও বিচিত্র প্রাণীর সমারোহ। হাওরের পানি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সহজপ্রাপ্য মিঠাপানির আধারের একটি অংশ। হাওর এক বিচিত্র কৃষিপ্রাণ নির্ভর জনপদ। এখানে কৃষিকাজ যেমন ব্যতিক্রম, বসতিগুলিও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ও বৈচিত্রময়তায় পূর্ণ। আর বেঁচে থাকা তো এক প্রত্যক্ষ জীবন সংগ্রাম। হাওরে বর্ষার করাল ঢেউ যেমন দ্বীপ সদৃশ্য ভাসমান বাড়িগুলো রক্ষার সাধ মিটিয়ে দেয়, হেমন্তে তেমনই সান-গোসলের পানি সংকট জীবনের স্বাদ ঘুচিয়ে দেয়। তাই হাওরাঞ্চলের সাহিত্য সংস্কৃতিও তেমনি জীবন ঘনিষ্ঠ সংগ্রামে-সংকটে রণময় ও প্রাণময়।
হাওরবেষ্টিত ভাটির লোকজন বর্ষাকালে অলস সময় কাটায়। বিশাল জলাশয়ে গ্রামগুলো তখন অসহায় ভেলার মতো ভেসে থাকে। একটু বাতাস পেলেই শুরু হয় তালমাতাল ঢেউ। “মাটির উপর জলের বসতি জলের উপর ঢেউ, ঢেউয়ের সাথে পবনের পিরিতি নগরে জানে না কেউ।” মাটির বাঁধে সবুজে ঘেরা গ্রামগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ভাটির মানুষগুলো সংগ্রাম করে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের মায়া সাঙ্গ করে। আবার হাওরের প্রকৃতি যখন শান্ত, কর্মহীনতায় অলস, তখন শুরু হয় ভাবজীবন ও সৃষ্টি সুখের গল্প। বিশেষ করে বর্ষাকালে অলস সময় বিলাসে হাওরের পাড়ায়-পাড়ায় বাড়ি-বাড়ি বিনোদনের অন্ত থাকে না। আলগঘরে তাসখেলা, বাউল আসর, কীর্তন, উড়ি গান, পদ্মপুরাণ, গীত, পালা গান, ঘাটু গান, বানেছার গান, গাজী গান, বাড়ির উঠানে মহিলাদের ধামাইল গানের আসর, ছোট ছেলে মেয়েদের কুত্-কুত্ খেলা, মার্বেল খেলা, অতি বয়ষ্কদের পুঁথি পড়া ও নাইয়রীদের আনাগোনা যেন বর্ষাকালে ভাটির গ্রামগুলোর সুখের দৃশ্য।
বিশাল শান্ত জলাশয়ের গা বেয়ে ধামাইল গানের সুরগুলো তখন ভেসে যায় দূর অজানায়। আমন্ত্রণ জানায় দূরের যে কোন অচেনা অতিথিদের। অলস সময় বিলাসে শান্ত পড়ন্ত বিকেলে কেউ ‘ইরের’ কাছে বসে থাকে বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে। আবার তার সাথে আরও কতগুলো অলস চোখ তাকিয়ে থাকে দূর সীমানায়, কে আসছে ‘নাও’ বেয়ে গ্রামের দিকে তার খেয়ালে। গ্রামে ভিড়ালে অতিথির নাও, আনন্দে জাগে সারা গাঁও। তোমার বাড়ির অতিথি আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ, এ যেন মধুর সম্পর্কের এক অনন্য উদাহরণ। ভাটির মাটির মানুষগুলো প্রকৃতি থেকে শুধু দুঃখই পায় না সুখও পায় অনেক। যা আজ আমরা হাওরবাসী মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করতে পারছি প্রকৃতির স্বাদ গন্ধহীন শহরের অট্টালিকায় থেকে। মন ও মননের স্বপ্নগুলো আজও হাওরপারের ভাটির মাটির মানুষগুলোকে নিয়ে জাল বোনে। অতীত স্মৃতিগুলো আজও আমাদেরকে ব্যাকুল করে তুলে। মন চায় এখনই ছুটে যাই ‘সেই আপন ঠিকানায়’।
হাওরবেষ্টিত ভাটির লোকজনের জীবনঘনিষ্ঠ লোকজধারার অন্যতম মাধ্যম ধামাইল নৃত্যগীত। বসতির শুরুতে হাওরবাসির জীবনযাপনের নানা পর্বে ধামাইল নৃত্যগীতের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। একসময় হেমন্তে কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে ধামাইল গান হাওরাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের মন সজীব রাখতো।
মূলত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক লোকসমাজই লোকসংস্কৃতির আধার। পল্লী অঞ্চলই লোকসংস্কৃতির লালনক্ষেত্র। এখানেই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা ও সজীব অবস্থান ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে শিক্ষিত সমাজে, শহরেও তার প্রচলন আছে সত্য কিন্তু পল্লীর সাধারণ লোকসমাজের তুলনায় অতি কম। পল্লীর মাটির মানুষগুলোর মাঝে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচরিত হয়ে আছে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি অর্থাৎ কবির ভাষায় বলা যায়- “পল্লীর প্রত্যেক পরতে পরতে লুকিয়ে আছে সাহিত্য এবং সাহিত্যের উপকরণ।” লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ লোকগীত। যার বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে ধামাইল নৃত্যগীত। বাংলার হাওরাঞ্চল যার পদচারণায় আজও অনেকটা মুখরিত। বাংলার হাওরাঞ্চলেই ধামাইল গানের একমাত্র জন্মমেদিনী বা আবাসস্থল। যেখানে জীবনের সাথে বাঁধা আছে তার আত্মজয়ী ধারা।
ধামাইল শব্দটি ‘ধামালী’ শব্দ থেকে সৃষ্ট। যার বিশেষ অর্থ হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি করে নাচ-গান। তবে হাওরাঞ্চলের জীবনাচারে ধামাইল শব্দের অনেক ব্যবহার রয়েছে। সে হিসেবে ধামাইল বলতে কোনো বিষয়ের চরম অবস্থাকে বুঝায়। ধামালীর অপিনিহিতজাত শব্দ ধামাইল। তবে ধামাইল শব্দের যথার্থ উৎস নিয়ে অনেক অভিমত ও মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে ধামান, দামান, ধামালি, ধামন শব্দ থেকে ধামাইল শব্দের উৎপত্তি। ধামাইলের সময়কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না তবে বড়– চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ধামালী শব্দটি বারবার ব্যবহার হয়েছে। এতে বোঝা যায় তার প্রচলন বড়– চণ্ডীদাস যুগেরও আগে তবে মধ্যযুগেও বিভিন্ন লোককবির কাব্যরচনায় ধামালীর উলেখ রয়েছে। অষ্টাদশ শতকেও ধামালী শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে।
ধামালি বা ধামালী আভিধানিক অর্থে দুরন্তপণা। কৌতুক বা চাতুরী যা প্রাচীন সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। ভাটিঅধ্যুষিত হাওর অঞ্চলে কৃষিকাজে ও মৎস্যশিকারে ধামালী শব্দের অনেক ব্যবহার রয়েছে। মাছেরা পানির উপরিভাগে এসে লেজ নেড়ে ধামালী দিয়ে তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দময় জলখেলায় মেতে ওঠে। আর এই ধামালী দেখেই মৎস্যশিকারীও বুঝতে পারে কোন রকমের কোন আকৃতির মাছ।তাছাড়াও কৃষি কাজে জমি চাষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে ধামালি দিয়ে লাঙ্গল চালানো ও জমিনে মই পেটানোর সুনাম হিসেবে ধামালির ব্যবহার রয়েছে। পল্লীর জনজীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে কোন বিষয়ের চুড়ান্ত অর্থে ধামালীর যথার্ত ব্যবহার রয়েছে। তাই বুধকরি সুর ও নৃত্যের চরম ও পরম বিবেচনায় ‘ধামালি’এর সাথে গান যুক্ত হয়ে ‘ধামাইল গান’ হাওরাঞ্চলের সংগীতের শ্রেষ্ঠত্বকে ধরে রেখেছে। তাছাড়া হাওরবাসীর জীবনের প্রয়োজনে ও হৃদয়ে ভালবাসা থেকেই এই ধামাইল গানের বিস্তৃতি। সে ব্যপারে কোন দ্বিমত নেই। এ বিবেচনায় বলতেই পারি ধামাইল গান হারাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ গান।
জলেজলাময় হাওরাঞ্চলে জলধামালী গানের প্রচলন এ ধারায় সর্বাগ্রে। বন্দনার পরেই জলধামালি গাওয়া হয়। ‘আমরা ভইরে আইলাম শীতল গঙ্গার জল ও কালায় কলসি ভইরা জল ঢালিয়া ও সে যে ঘাট করলো পিচল…।’ ‘শ্রীরাধা-কৃষ্ণলীলায় শ্রী রাধিকা যমুনার জলে সহচরী সঙ্গে ধামালি দিয়ে স্নান করে, ডুবাইয়ে লাই খেলে, মনোরঙ্গে হাত-পা নেড়েচড়ে যে গান গেয়ে ছিলেন তাই জলধামালি গান। যমুনার জলে নেমে রাধা-কৃষ্ণের স্নান ধামালি হতে ধামাইল গানের উৎপত্তি। তাই এটি জল ধামালি গান। এ জন্য বিয়ে উপলক্ষে বর-কনের স্নানের অনুষ্ঠানে জল ধামালি গাওয়া হয়। তাই বলা যায়, যে গানে অবরুদ্ধ মনোভাব অতি সহজে প্রকাশ পায় এবং চিত্তকে প্রফুল্লিত করে তাই ধামাইল গান।’ কথায় কথায় এমনটিই আমাকে বললেন ধামাইল গান গায়ক ও লেখক শ্রী অরুন কুমার সামন্ত।
ধামাইল গীত একটি দলগত পরিবেশনা। শুরুতে হাওরাঞ্চলের জীবনাচারে ধামাইল ছিল জীবন রক্ষায় লোকাচার ঘনিষ্ট দলিয় উপাসনা। চিত্ত বিনোদন নয় চিত্ত রক্ষাই ছিল ধামাইল গীত বন্দনার বা প্রার্থনার মূল কাজ। জীবন গঠনের নানান শাখায় দলীয় লোকাচারে ধামাইল গীত সত্য রক্ষা, সত্য প্রতিষ্ঠা ও মঙ্গলের ধারক বাহক। জীবন সংগ্রামে প্রকৃতি জয়ের দলীয় প্রর্থনার নাম ধামাইল। অবরুদ্ধ মনের ভাব প্রকাশে ও সৃষ্টিকর্তাকে অনুসরণ করে চলার এক সহজিয়া মাধ্যমের নাম ধামাইল নৃত্যগীত। ধামাইল গীত মানব জীবনের ব্রত কথাও বটে, তবে মন্ত্র নয়। তাই ধামাই মানব কল্যাণে ধর্মনিরপেক্ষ। ধামাইল গান সাধারণত মেয়েরা দল বেঁধে হাতে তালি দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গায়। তাছাড়া পুরুষরাও এ গান গেয়ে থাকে। যেখানে একজন শিল্পী গান শুরু করে একটি পদ গায় পরবর্তীতে সকলে মিলে দোহার দেয়। শুরুতে এক তালিতে গানটি গাওয়া হয়। তারপর দুই তালি, তিন তালি, আবার কখনও পাঁচ তালিতে গাওয়া হয়। শুরুতে ধামাইল গান করতাল ও হাতে তলি দিয়ে গাওয়া হত। অন্য কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হতো না। বর্তমানে ঢোলের ব্যবহার হয়ে থাকে ধামাইলের নৃত্যশৈলী বাড়াতে।
মূলত মেয়েলি ব্রতাচার গীত থেকেই ধামাইল নৃত্য গীত বা ধামাইল গানের বিস্তৃতি। বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানে বয়স্ক মহিলারা ঘরে বসে ব্রত কথাকে সুরে সুরে গাইতেন, যা ব্রত গীত। আর তরুনীরা এ গীতকে প্রাণবন্ত করতে হাতের তালি ও নৃত্যের ব্যবহার যোগ করে। যা ধামাইল নৃত্য গীত নামে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক লোক সমাজে আজও জনপ্রিয়। ধামাইল গানের সুর তাল লয় ও নৃত্যের সম্মিলিত মনোমুগ্ধকর সুনিপুণ পরিবেশনায় ধামাইল হয়ে ওঠে আরও দৃষ্টি নন্দন। নিজস্ব স্বকীয়তায় রূপ নেয় গীত হতে বিস্তৃত ধামাইল গান। তবে এক সময় সূর্য ব্রত সংগীতের জনপ্রিয়তা গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক লোক সমাজে বেশী ছিল। রাধারমন দত্তের পিতা রাধামাধব দত্ত ছিলেন সূর্যব্রত সংগীতের রচয়িতা। বর্তমানে হাওরাঞ্চরে সুর্যব্রত সংগিত সূর্যব্রত ধামাইল নামে প্ররিচিত। কেননা এ দুয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশী রক্ষ্য করা যায়। ধামাইলের যথার্থ ব্যবহার শুরু হয় রাধারমণ দত্তের সময়ে। যদিও ধামাইলের উৎপত্তিগত আদি মত পার্থক্য রয়েছে।
ধামাইলের সময়কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না তবে বড়– চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ধামালী শব্দটি বারবার ব্যবহার হয়েছে। এতে বোঝা যায় তার প্রচলন বড়– চণ্ডীদাস যুগেরও আগে তবে মধ্যযুগেও বিভিন্ন লোককবির কাব্যরচনায় ধামালীর উলেখ রয়েছে। অষ্টাদশ শতকেও ধামালী শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে। ধামালি বা ধামালী আভিধানিক অর্থে দুরন্তপণা। কৌতুক বা চাতুরী যা প্রাচীন সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। ভাটিঅধ্যুষিত হাওর অঞ্চলে কৃষিকাজে ও মৎস্যশিকারে ধামালী শব্দের অনেক ব্যবহার রয়েছে। মাছেরা পানির উপরিভাগে এসে লেজ নেড়ে ধামালী দিয়ে তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দময় জলখেলায় মেতে ওঠে। আর এই ধামালী দেখেই মৎস্যশিকারীও বুঝতে পারে কোন রকমের কোন আকৃতির মাছ।তাছাড়াও কৃষি কাজে জমি চাষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে ধামালি দিয়ে লাঙ্গল চালানো ও জমিনে মই পেটানোর সুনাম হিসেবে ধামালির ব্যবহার রয়েছে। পল্লীর জনজীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে কোন বিষয়ের চুড়ান্ত অর্থে ধামালীর যথার্ত ব্যবহার রয়েছে। তাই বুধকরি সুর ও নৃত্যের চরম ও পরম বিবেচনায় ‘ধামালি’এর সাথে গান যুক্ত হয়ে ‘ধামাইল গান’ হাওরাঞ্চলের সংগীতের শ্রেষ্ঠত্বকে ধরে রেখেছে।
ধামাইল অন্য যেকোনো লোক সংগীতের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা ধামাইল গানের মত এত সহজিয়া সংগীত হিসেবে আর কোনো গান এত জনপ্রিয় নয়। সাধারণ লোকগান বাদ্য যন্ত্র ও বাদকের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। গায়কের সাথে অন্যান্য সকল কিছুর অর্থাৎ সুর তাল লয় ও ছন্দময় ব্যবহারেই লোক গানের পূর্ণতা পায়। কিন্তু ধামাইল গানে তার নির্ভরশীলতা কম। যেটুকু আছে তা কেবল সহজিয়া ভাবে দলের সকল গায়িকাদের উপর। যাতে যান্ত্রিক নির্ভরশীলতা নয় দলগত আন্তরিকপ্রয়াসেই মূখ্য।
ধামাইল ভাটির উপত্যকার লোকসংস্কৃতির একটি জনপ্রিয় ও মুখ্য উপাদান। বিশেষ করে সুনামগঞ্জের মেঘালয় অঞ্চলে তার সজীব অবস্থান। পল্লী সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে ধামাইল গানে। ধামাইল আসরকে কেন্দ্র করে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একত্রে নিশি জাগরণ করে শ্রোতা হয়ে। মনে হয় এটি যেন মানবপ্রেমের মিলন মেলা। তাই ভাটি পল্লীর প্রতিটি মেয়েই তার সঙ্গীতচর্চা শুরু করে ধামাইল গান দিয়ে। ধামাইল গান জানা মেয়েদের একটি বিশেষ গুণ, যার জন্য সমাজ তাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে। ধামাইল গান নিছক শুধু গানই নয় এটি লোকসংস্কৃতি বা সাহিত্যের একটি অঞ্চলের, জাতির জীবনবোধের গল্পও বটে।
কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হাওরপাড়ের এই ধামাইল গান আজ আর আগের মতো নেই। পল্লীর প্রত্যেক পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা সাহিত্য আজ যেন হারিয়ে যেতে বসেছে অপসংস্কৃতির বেড়াজালে। শুরুতে কৃষিভিত্তিক লোক সমাজে ধামাইল গান প্রকৃতি জয়, কর্ম, শক্তি সঞ্চয় ও সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার ছিল। বর্তমানে তা কেবল বিনোদন মাধ্যম। ধামাইল গান সাধারণত বিয়ে কিংবা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই বেশি গাওয়া হয়। রাধা-কৃষ্ণের জলখেলি, প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ, মান-অভিমান, রূপ, বাঁশি ও মিলন নিয়ে রচিত বেশিরভাগ ধামাইল প্রচলিত আছে। যার মধ্যে রাধারমনের রচিত গানের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া দীন শরৎ, মহেন্দ্র গোসাই, প্রতাপরঞ্জন, শাহ আব্দুল করিম, মধুকবি, গৌরচাঁন, বাবুমোহন, গোপীধন, উপেন্দ্র, মহানন্দ, রামজয়, রসরাজ ও বিজয় সরকার তাঁদের রচিত গানগুলি আমাদের চেতনাকে শানিত করে নতুনভাবে।
গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় বিবাহের বাগদান, মঙ্গলাচরণ, জলভরা, আদ্যস্নান, গায়েহলুদ, অধিবাস, ফুলচন্দন, বাসিবিবাহ, বর বিদায়, কনে বিদায়, বধূবরণ, উপনয়ন, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, দুর্গাপূজা, মনসাপূজা, সরস্বতীপূজা ও সূর্যব্রতসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ধামাইল ছাড়া সম্পন্ন হয় না।ধামাইলে সাধারণত বন্দনা, জলভরা, গায়ে হলুদের গান, অধিবাসের স্নান, বর আগমন, বিয়ে, জামাই স্নান ও বরযাত্রাকে কেন্দ্র করে ধামাইল গানের আসর গড়ে উঠে।
ধামাইলে জামাই স্নানের একটি বিশেষ অংশ রয়েছে। বিশেষ করে নতুন জামাইসহ বাড়ির অন্য সকল জামাইদের একসঙ্গে বসিয়ে নানান রং তামাসায় ও রসিকতায় ধামাইল গান গাওয়া হয়। তবে দাবি আদায়ের জন্য ধামাইলে ‘বান্দা’ গানের প্রচলন রয়েছে। যেমন-“শুনতে শুন্ছি জামাইবাবু বড় ধনবান, পান চিনি খাওয়াইয়া টাকা করবেন দান”। এভাবে মহিলারা নতুন জামাইদের কাছ থেকে দাবি আদায় করে থাকে। অবশেষে জামাইদের স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পড়িয়ে মিষ্টিমুখ করে ধামাইল গানের আসর শেষ করা হয়।
তাছাড়া ‘করতাল ধামাইল’ও হাওরপাড়ে গাওয়া হয়। বিশেষ করে মাঘ ফাল্গুন মাসে সূর্যব্রত ও ধর্মব্রত অনুষ্ঠানে এবং সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে ‘করতাল ধামাইল’ গাওয়া হত। যে গানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকাশ পায়। তাছাড়াও গৃহস্থালি কাজ শেষ করে কৃষকগণ মেয়ে সেজে রাতের বেলায় ‘করতাল ধামাইল’ গাইত। যা ‘বাঘেরসিন্নি’ নামে পরিচিত। গ্রামের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন আলো জ্বালিয়ে একদল পুরুষ তামাসা করে ‘করতাল ধামাইল’ গেয়ে ‘বাঘেরসিন্নি’ মাগত। প্রতিটি বাড়ির উঠানে গিয়ে তারা প্রথমে
“সোনা বউ দিদিগো দরজা খোল, বাত্তি জ্বালাও চাই,
বাত্তিটি জ্বালাইয়া দেখ কমলিনী রাই”।
এই গানটি গেয়ে গৃহকর্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে জাগিয়ে তুলত। তবে বিশেষ করে হাওরাঞ্চলে পাহাড়ের নিকটবর্তী এলাকায় ‘বাঘের সিন্নী’ মাগতে গৃহস্থ পরিবারের যুবক ছেলেরাও এ গান গেয়ে থাকে। তাছাড়া ভাটি বাংলার রাখাল সমাজ রাতেরবেলায় হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধামাইল গান গেয়ে ‘বাঘের সিন্নী’ মাগত। সেক্ষেত্রে তারা করতালি ধামাইল বেশি পরিবেশন করত। যার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি হত একটু ভিন্নতর।
‘ময়না যাইছনারে জঙগলার মাঝে বাঘ আইতাছে’,
‘পিরিত কইরা যন্ত্রণা মন মিলে মানুষও মিলে সময় মিলে না’
এসব গান নিস্তব্ধ রাত্রিতে ঝংকৃত হয়ে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে জাগিয়ে তুলত। তারপর গৃহকর্তা খুশি হয়ে টাকা পয়সা অথবা চাল উপহার দিতেন। এসব টাকা পয়সা জমা করে পরবর্তীতে তারা গ্রামের সবাইকে নিয়ে বনভোজন করত। তাই গ্রামীণ সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ধরে রাখতে ধামাইল গানের গুরুত্ব অপরিসীম বর্তমানে যা প্রায় বিলুপ্তির পথে। হাওরপাড়ের ধামাইল আসরে কাঁদা মাটির গন্ধ, সুশীতল বাতাস, রোদ বৃষ্টির খেলা ও মানুষের হৃদয়জাগানো সুর মানুষকে অভিভূত করে। শুধু তাই নয় একে অপরের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত। জীবনের সুখ-দুঃখ, বিরহ-ভালবাসা, ও চাওয়া-পাওয়ার সকল সুর বেজে উঠেছিল সেই ধামাইলের আসরে। তাই ধামাইলের অস্তিত্ব রক্ষায় সকল জনপদের প্রত্যেকের প্রতি তার যথোপোযুক্ত মূল্যায়ন ও অনুশীলন অব্যাহত রেখে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশে আমাদের দায়িত্ববান হওয়া উচিৎ।
তবে বেশিরভাগ সময় সাধারণত দু’হাতে তালি দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে সমবেত কণ্ঠে ধামাইল গান গাওয়া হয়। যদিও অনেক ক্ষেত্রে করতালি ধামাইলের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। যা রামকরতাল বা ঢাক বাজিয়ে পরিবেশন করা হয়।
ধামাইল গানের মাধ্যমে সময় ও অনুষ্ঠানের উপযুক্ত বিষয়টাই ঝংকৃত হয় বলে তা সকলের মাঝে মোহময় আবেশের ঢেউ তুলে। মূলত সাতটি বিষয়ের উপর হাওরাঞ্চলের ধামাইল নৃত্যটি নির্ভরশীল-
১. হাতেতালি ২. হাতের আঙ্গুলে তুরি ৩. হস্তচালনা ৪. পদচালনা ৫. শিরচালনা ৬. আঁখিচালনা ৭. দেহচালনা।
এ সপ্তক্রিয়ার সমব্যবহারেই ধামাইল নৃত্যের পূর্ণতা আসে। ধামাইল সাধারণত দু’ধরণের হয়ে থাকে-
১. হাতেতালি ধামাইল
২. করতাল ধামাইল
তাছাড়াও ধামাইলের আরও শ্রেণি বিভাগ রয়েছে। যেমন-
১. শ্রম ও কর্মবিষয়ক ধামাইল
ক. গোষ্ঠ ধামাইল
খ. বাঘের সিন্নি ধামাইল
গ. গৃহস্থালী ধামাইল
২. সাধন-ভজন বিষয়ক ধামাইল
ক. প্রার্থনা-বন্দনা বিষয়ক ধামাইল
খ. তত্ত্ব বিষয়ক ধামাইল
গ. রূপ ধামাইল
ঘ. মিলন ধামাইল
ঙ. বিচ্ছেদ ধামাইল
৩. ব্রত অনুষ্ঠানের ধামাইল
ক. উদয় ধামাইল
খ. সূর্যব্রত ধামাইল
গ. ধানের খিরবাস ব্রত ধামাইল
ঘ. রূপসীব্রত ধামাইল
৪. উৎসব বা আনুষ্ঠানিক ধামাইল
ক. কীর্তন ধামাইল
খ. পূঁজা-পার্বন বিষয়ক ধামাইল
গ. বিয়ের ধামাইল
ঘ. জল ধামাইল
৫. দেশাত্ববোধক ধামাইল
৬. শিশুতোষ ধামাইল
৭. বিবিধ ধামাইল
ভাটি অঞ্চলে ধামাইল গানের ৯৫ শতাংশই রাধারমণ রচিত। আর তাই ধামাইল বলতে সাধারণত রাধারমণের ধামাইলকেই বুঝায়। সাধারণত হাটে, ঘাটে, মাঠে, হাওরে-বাওরে, নৌকায় মাঝির কণ্ঠে ও সাধারণ মানুষের লোকউৎসবে যার গান পল্লীর সর্বত্রই গীত হয় তিনিই রাধারমণ। তাই তিনি লোককবি।
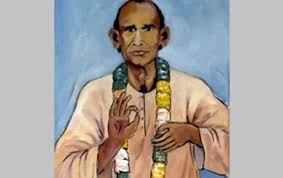
দশম শতাব্দীতে রাজা মহীপাল দেবের সভাচিকিৎসক নরহরি দত্ত ছিলেন রাধারমণ দত্তের পূর্বপুরুষ। তিনি ছিলেন বীরভূম জেলার সপ্তগ্রামের অধিবাসী। তাঁর দুই পুত্র নরোত্তম দত্ত ও নারায়ণ দত্ত। নারায়ণ দত্ত ছিলেন রাজা জয়পাল দেবের রসবত্যাধিকারী অর্থাৎ অন্যতম পরামর্শক। নারায়ণ দত্তের দুই পুত্র ভানুদত্ত ও চক্রদত্ত। চক্রদত্তের আরেক নাম চক্রপাণি দত্ত। চক্রপাণি দত্ত ছিলেন তখনকার সময়ের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। তিনি ‘আয়ুর্বেদীপিকা’ ও ‘ভানুমতী’ নামে দুটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উপাধি ছিল ‘ভিষগাচার্য’। তিনিও সভাচিকিৎসক ছিলেন। রাজবৈদ্য চক্রপাণি দত্ত সিলেটের রাজা প্রথম গোবিন্দকেশব দেব (ভাটেরা তাম্রশাসন অনুযায়ী ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দে) এর চিকিৎসার জন্য ৩ পুত্র উমাপতি দত্ত, মহীপতি দত্ত ও মুকুন্দ দত্তকে নিয়ে সিলেটে আসেন। রাজার আরোগ্য লাভের পর চক্রপাণি দত্তকে এদেশে বসবাসের অনুরোধ জানান তিনি। রাজার অনুরোধে তিনি ১ম পুত্র উমাপতিকে বীরভূম পাঠিয়ে মেজোপুত্র মহীপতি ও ছোটপুত্র মুকুন্দকে নিয়ে সিলেটে বসবাস করতে সম্মত হন। রাজা গোবিন্দকেশব তাঁদের অনেক ভূ-সম্পত্তি দান করেন। মহীপতি দত্তের নতুন বাসস্থানের নাম হয় সাতগাঁও যা তাঁর পূর্ববর্তী নিবাস সপ্তগ্রামের অনুকরণে। সেই থেকেই আমাদের দেশে বংশপরম্পরায় তাঁদের শাখা বিস্তার হয়।
মহীপতির পুত্র বিশ্বনাথ, তার পুত্র শ্যামসুন্দর, তার পুত্র শিবসুন্দর, তার পুত্র বাসুদেব, তার পুত্র পুরন্দর, তার পুত্র বলরাম, তার পুত্র গোপাল, তার পুত্র মদন, তার পুত্র বামন, তার পুত্র কল্যাণ, তার পুত্র প্রভাকর, তার পুত্র রুদ্রদাস, তার পুত্র জগন্নাথ, তার পুত্র সম্ভুদাস, তারপুত্র রামদাস, তার পুত্র মুকুন্দদাস, তার পুত্র রাজেন্দ্র দাস, তার পুত্র রামগোবিন্দ (অচ্যুতানন্দ) তার পুত্র দুর্লভরাম, তার পুত্র কৃষ্ণরাম, তার পুত্র রাধামাধব, তার ৩ ছেলে। রাধানাথ, রাধামোহন ও রাধারমণ। রাধামাধব দত্ত বাংলা ও সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। জয়দেবের কাব্য ‘গীতগোবিন্দ’য় টীকাকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল অনেক। তিনি সংস্কৃতি ভাষায় ‘ভারতসাবিত্রী’ ও ‘ভ্রমরগীতা’ দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া বাংলা ভাষায় ‘কৃষ্ণলীলাব্য’ ও ‘পদ্মপুরাণ’ পাঁচালীগ্রন্থ ‘সূর্যব্রত’ ও গোবিন্দভোগের গান দু’টি তাঁর সংগীত প্রতিভার প্রমাণ। তাই উত্তরাধিকার সূত্রেই রাধারমণ তা পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, রাধারমণ দত্তের গ্রাম কেশবপুর তাঁর পূর্বপুরুষদের নামানুসারে। তাছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষদের নামের সঙ্গে মিল রয়েছে সিলেট অঞ্চলের বালিশিয়া, সতরসতী, জগন্নাথপুর, প্রভাকরপুর, কেশবপুর, দত্তবিসনা, লাখাই, মিরাশি প্রভৃতি গ্রামের।
রাধারমণ দত্তের অসংখ্য গান বাংলার আনাচে-কানাচে গীত হচ্ছে যার সঠিক হিসাব এখনও শেষ হয়নি। তবে এ পর্যন্ত ১০২৩ টি গানের প্রকাশিত হিসাব পাওয়া গেছে। রাধারমণের গান নিয়ে প্রথমেই যিনি সংগ্রহের কাজে ব্রতী হন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৯০)। তিনি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ৫ পৌষ ৫৭টি গান সংগ্রহ করেন। তারপর গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) তিনি ১৯৩৯ সালে ৩ সেপ্টেম্বর ৪২৩টি গান সংগ্রহ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দেন।
রাধামাধব দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র রাধারমণের পুরো নাম রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ। তিনি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার কেশবপুর গ্রামে আনুমানিক ১৮৩৪ সালে (১২৪১ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। আবার কারো কারো মতে ১৮৩৩ সালে (১২৪০ বঙ্গাব্দে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে অতিস¤প্রতি কেশবপুর গ্রামের রাধারমণ দত্তের ভিটা খননকালে পিতলের তৈরি একটি প্রাচীন শীলমোহর পাওয়া গেছে যাতে লিখা আছে-
সন ১২৪১ তাং
শ্রীরাধাকিসব দত্ত
পাঁচ তারিক শ্রীরাধা
মাধব দত্ত আতু
য়াজান।
রাধাকিসব (রাধাকেশব) নামে রাধামাধব দত্তের কোন পুত্রের নাম তাঁদের বংশতালিকায় পাওয়া যায়নি। রাধারমণের পিতৃদত্ত নাম রাধাকিসব বা রাধাকেশব হতে পারে। গুরুদত্ত (গুরু প্রদত্ত) নাম হতে পারে রাধারমণ। রাধারমণের অনুজ কেউ ছিলেন না। কাজেই ১২৪১ বঙ্গাব্দ ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জন্মসাল বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। যা হতে পারে যেকোনো মাসের ৫ তারিখ। তাঁর মায়ের নাম সুবর্ণা দেবী। স্ত্রীর নাম গুণময়ী দেবী। তিনি ৪ পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন। রাসবিহারী, নদীয়াবিহারী, বিপিনবিহারী ও রসিকবিহারী।
রাধারমণ দত্ত ১২৫০ বঙ্গাব্দে শৈশবেই পিতৃহারা হন। তাই ছোটবেলা থেকেই বিচ্ছেদকাতর মনের অধিকারী রাধারমণ দত্ত সঙ্গীতে আত্মমগ্ন হয়ে মুক্তি খুঁজতেন। তিনি ১২৭৫ বঙ্গাব্দে মৌলভীবাজারের আধপাশা গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ সেন শিবানন্দের বংশীয় নন্দকুমার সেন অধিকারীর তনয়া গুণময়ী দেবীকে বিয়ে করেন। তিনি ঈশ্বরলাভের পদ্ধতি জানার জন্য বিভিন্ন সাধকের উপদেশসহ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবসহ বিভিন্ন মতবাদের অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু তার উত্তর খুঁজে পাননি।
পরবর্তীতে তিনি মৌলভীবাজারের নিকটবর্তী, ঢেউপাশা গ্রামের সাধক রঘুনাথ গোস্বামীর কাছে ধর্মীয় দীক্ষা নেন। দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁর ভাবান্তর হয় এবং তিনি সংসারের প্রতি বিরাগ অনুভব করেন। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর রাধারমণের হৃদয় কন্দরের শুষ্ক সুপ্ত প্রেম নির্ঝরিণী পরিপূর্ণ ও জাগ্রত হয়ে উঠে। ঠিক তখনি তাঁর তিন পুত্র ও স্ত্রী গুণময়ী দেবীর অকাল প্রয়াণে তিনি সংসার থেকে বিভক্ত হয়ে পড়েন। বিষয়বাসনা ত্যাগ করে বাড়ির অদূরে নলুয়া হাওরের পাশে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন সেখানেই সাধনায় মগ্ন হন। তার গানেও এর সমর্থন মেলে,
অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বাধিয়াছি ঘর
ভাই নাই বান্ধব নাই কে লইব খবর।
তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় গীতরচনা করতেন। ভক্তবৃন্দ গীত স্মৃতিতে ধরে রাখতেন। কেউ কেউ তা অক্ষরে প্রকাশ করে কালের ধুলোয় হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।যা আজ প্রজন্মান্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে চেতনাবোধকে শাণিত করছে।
রাধারমণ বৈষ্ণব তত্ত¡ানুসারে প্রার্থনা, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, গুরুভক্তি বিষয়ক পদ, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়, গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, দৌত, অভিসার, বাসকসজ্জা, খÐিতা, মান, বিরহ, মিলন নিয়ে তিনি পদ রচনা করেছেন। তাছাড়া বৈষ্ণব পঞ্চরসের মহাভাবের, অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের ও নাম মাহাত্ম্যের গীতিরূপ রচনায় তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।
তিনি তাঁর সাধনস্থানে ১৩২২ বঙ্গাব্দে ২৬ কার্তিক শুক্রবার, ১৯১৫ সালে, কারো মতে ১৯০৭, ১৯১৬ সালে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছেমত তাঁকে দাহ করা হয়নি। বৈষ্ণবমতে সমাহিত করা হয়। এইজন্য তাঁকে বৈষ্ণবকবিও বলা হয়। তাছাড়া সাধনপ্রণালী হিসেব করলেও তাকে বৈষ্ণবকবি বলাই ভাল। তবে তিনি বৈষ্ণব না বাউল কবি তা অত্যন্ত সূ² বিতর্ক। তবে শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর অভিমতÑবাউলেরা একটা স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী স¤প্রদায়। এদিক বিবেচনা করলে রাধারমণ দত্ত সে শ্রেণির বাউল নয়। তবে রাধারমণ দত্ত তাঁর একাধিক গানেও নিজেকে বাউল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
দীনহীন বাউলে কয় কথা মিছে নয়
চন্দ্রবলীর কুঞ্জে তুমি গেছিলা নিশ্চয়
রাধারমণ বাউলে বলে আমার সবের আশা পূর্ণ হইল না
আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন
আমার শাশুড়ি ননদী ঘরে ভয় বাসি মনে
ওরে কীসের সমন আমারÑযাইতাম গৌরার সনে
রাধারমণ বাউল বলে গুরুর চরণে
ওরে গুরুপদে প্রাণ সঁপিতাম এই বাসনা মনে
তিনি নিজেকে বাউল বলেই পরিচয় দিয়েছেন। সেই হিসেবে তাঁকে বাউলকবি হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে তাঁর গানে ও সুরে বৈষ্ণব ভাবধারাই বেশি প্রকটিত।
তবে তিনি মানবিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন নিয়ে গান রচনা করেছেন। গ্রামীণ পরিবেশে জলাভূমি, হাওর, নদীর প্রাধান্য তাঁর গানের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। ‘ভব নদীর পার’ তাঁর গানে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। তাছাড়া নিসর্গ, যেমন ফুল, লতা, নদী-নালা, হাওর, পাখি, গাছ-গাছালি সবই তাঁর গানে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া স্বদেশ সচেতনতা ও রাজনীতিতেও তাঁর গান লক্ষ করা যায়। যেমন-
বিলাতের কর্তা যিনি হইবি স্বাধীন
মনরে হবিগঞ্জ, নবিগঞ্জ, কলিকাতা, তেলিগঞ্জরে
আশুগঞ্জের লাইনের ভিতরে মন আমার
ঘোরাবি কতদিন
তাছাড়া নৈতিক অধপতনেও তিনি গেয়েছেন
দেখলাম দেশের এই দুর্দশা,
ঘরে ঘরে চুরের (চোর) বাসা
রাধারমণ দত্তের অসংখ্য গান বাংলার আনাচে-কানাচে গীত হচ্ছে যার সঠিক হিসাব এখনও শেষ হয়নি। তবে এ পর্যন্ত ১০২৩ টি গানের প্রকাশিত হিসাব পাওয়া গেছে। রাধারমণের গান নিয়ে প্রথমেই যিনি সংগ্রহের কাজে ব্রতী হন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৯০)। তিনি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ৫ পৌষ ৫৭টি গান সংগ্রহ করেন। তারপর গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) তিনি ১৯৩৯ সালে ৩ সেপ্টেম্বর ৪২৩টি গান সংগ্রহ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দেন। তাছাড়া রাধারমণ গানের উপর ব্যাপক আলোচনা,চর্চা ও গবেষণা করেছেন এবং ধামাইল গান নিয়ে প্রকাশনা, সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, মোহাম্মদ আজিজুল হক চুন্নু, আবদুল গফফার দত্তচৌধুরী, চৌধুরী গোলাম আকবর, মোহাম্মদ আবদুল হাই, মোহাম্মদ আসদ্দর আলী, নন্দলাল শর্মা, অমিতবিজয় চৌধুরী, তারেক আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ সুভাষউদ্দিন, মোহাম্মদ আলী খান, নৃপেন্দ্রলাল দাশ, ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, মোহাম্মদ নূরুল হক, ফজলুর রহমান, জাহান আরা খাতুন, মতিয়ার চৌধুরী, ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, শামসুল কবীর কয়েস, রব্বানী চৌধুরী, জুবায়ের আহমেদ হামজা, মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, অনিল সেন, ড. তপন বাগচী, সুমনকুমার দাশ প্রমুখ।
রাধারমন দত্তে¡র কালজয়ী সৃষ্টি গান বাংলার ধামাইল গানে যে বা যারা সুর তরঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাদের মধ্য অন্যতম এবং শ্রেষ্টত্বের দাবিদার এ কালের শিল্পী চন্দ্রাবতী বর্মণ। লোকগান, বিশেষ করে ধামাইলের সকল শাখায় ছিল যার সুরারুপের ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের অসীম ক্ষমতা। যার কন্ঠে গাওয়া ধামাইল গানের সুর এক মোহময় আবেশের সৃষ্টি করে। তাই তিনি গানের পাখি হিসেবে পরিচিত।
বর্তমানে এই মহান সৃষ্টি ধামাইল গান লালন ও চর্চা করতে ‘হাওরপারের ধামাইল (হাপাধা)’ বাংলাদেশ-সহ নানা সংগঠন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে অনেকেই যুক্ত হয়েছে তাঁদের প্রেমের মহিমায়। শুধু তাই নয় অনন্ত প্রেমের মহিমায় পরিপূর্ণ লোক সাহিত্যের সজীব উপাদান ধামাইল গান আবারো পূর্বের মত ঐতিহ্য ফিরে পেতে অনেকেই সংকল্প করে মিলিত হয়েছেন ধামাইলের পতাকা তলে। ভাটির কাদা মাটির মানুষের কোমল মননে আবারও জাগে উঠবে ধামাইল গানের চেতনাবোধ। প্রকৃতির শত বৈরীতার মাঝে বেঁচে থাকা কৃষিজীবীদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ধামাইল গান যে ভাবে বিনি সুঁতায় মালা গেঁথে ঐক্য ধরে রাখে তা ফিরে পেতে ক্ষুদ্র প্রয়াস ‘ধামাইল আসর’ যদি সুশীল সমাজ গঠনে এতটুকু অবদান রাখে তবেই হবে তার সার্থকতা। তাই চলুন ভাটির অনন্য সৃষ্টি ধামাইল ও মহান শিল্পীদের অন্তরের অন্ত:স্তল থেকে ভালবাসা দিয়ে তার উপযুক্ত আসন তৈরি করার কাজে ব্রতী হই।
সজল কান্তি সরকার

হাওর গবেষক ও ‘হাওরপারের ধামাইল (হাপাধা) বাংলাদেশ। মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।. +৮৮০১৭১৬-৮২৬১৩০
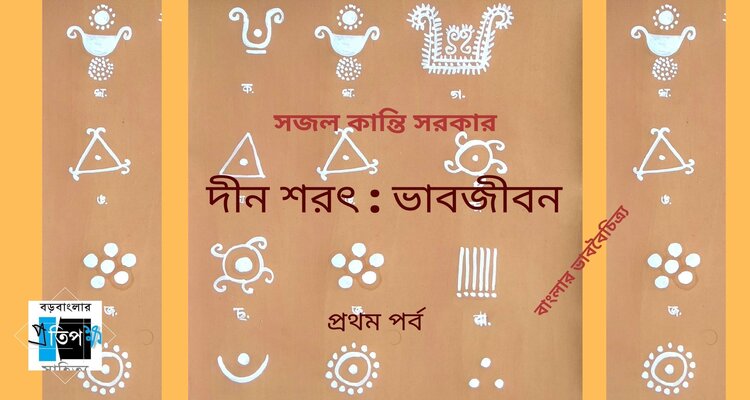
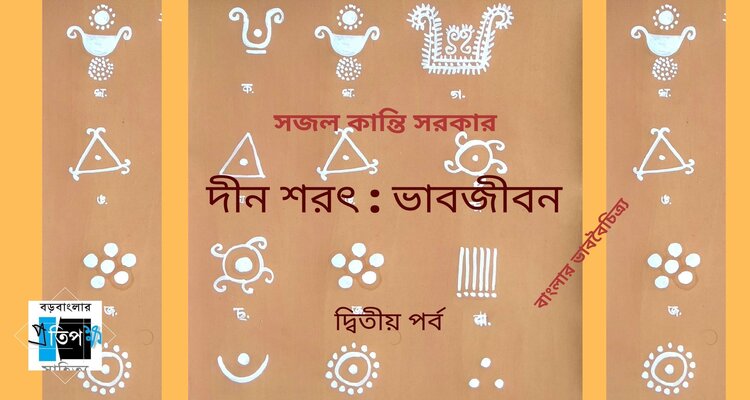

চমৎকার লেখা।