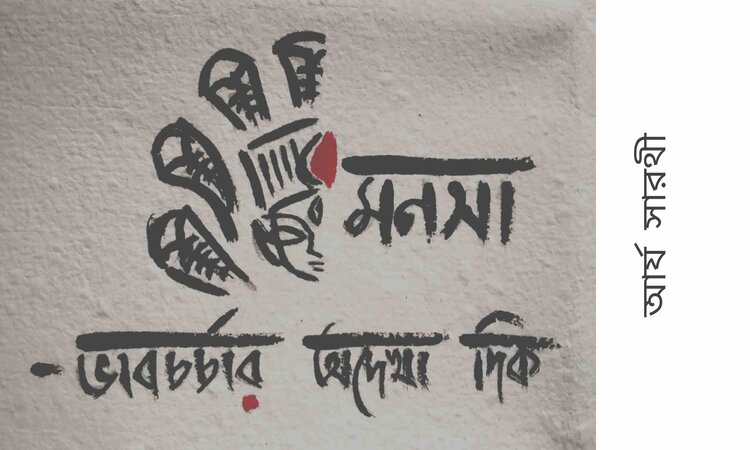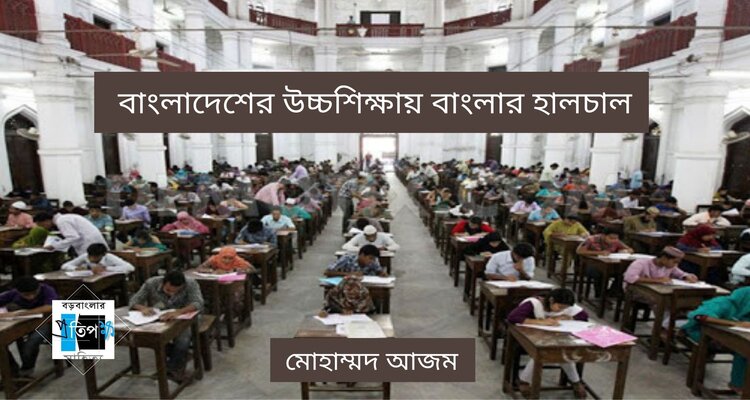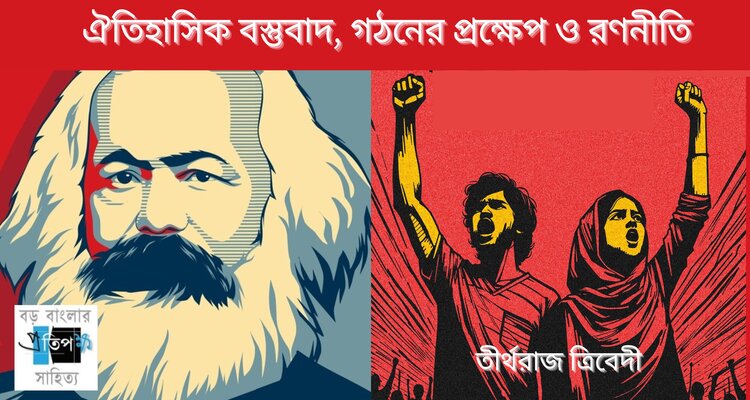
।। তীর্থরাজ ত্রিবেদী।।
এখন জুলাই অভ্যুত্থান প্রকৃতই বাংলাদেশের উর্বর উন্নত ভৌগোলিক ঐতিহাসিক গঠনকে চিহ্নিত করে একটি দেশ গঠনের অভিপ্রায়কে ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছে বলেই জুলাই অভ্যুত্থান এই আদর্শ ঐক্যের প্রতি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পা, যাকে মার্কিনিরা একদিকে ইসলামোফোবিয়া তৈরিতে কাজে লাগাবে, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী ইসলামি দলগুলির পিছনে টাকা ঢালবে, তাদের দিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা সফল করবার মাধ্যমে পৃথিবীর এই সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলটিকে পুঁজিবাদী করপোরেট ব্যবস্থার পরিপূর্ণ দখলে আনবার কর্মসূচিতে অযাচিত রক্তক্ষয় ঘটাবে। এর জন্য সাম্রাজ্যবাদ বদ্ধপরিকর। মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ এক্ষেত্রে যথার্থই সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ প্রবণতার প্রতিভূ। কিন্তু যে প্রকার জ্ঞান, সংগ্রাম, উৎপাদন, জীবন ও সমাজ কাঠামো এই করপোরেট উপনিবেশবাদকে পরাস্ত করে প্রগত থাকতে পারে, তার অবশ্যম্ভাব্যতাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু এই যে, কোনো বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সুসজ্জিত সামরিক জনতা ক্ষমতা দখল করছে না দেখলেই আজকের কমিউনিস্টরা সেটিকে সাম্রাজ্যবাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক হিসাবে ছাড়া আর দেখতে পারেন না, এটি তাদের নিজেদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা ঢাকবার নামান্তর মাত্র, কারণ সুসজ্জিত সামরিক বৈপ্লবিক শক্তি সংহতকরণের কাজটি অভ্যুত্থানের গণশক্তি তত্ত্বেও উপলব্ধি করেনি, হাতেকলমেও কোনোদিন গ্রহণ করবার অঙ্গীকার রাখেনি। অভ্যুত্থান জনতার বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রকট ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজির করে মাত্র, তাকে সফল করবার কাজ এই সচেতন বৈপ্লবিক শক্তির বা পার্টির স্বগৃহীত দায়িত্ব৷
“এই প্রণালীর (পুঁজিতান্ত্রিক) বুনিয়াদ হচ্ছে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব —শ্রমের উৎপাদনশীলতা, যা এই প্রক্রিয়ার ভিত্তি ও যাত্রাবিন্দু রূপে কাজ করে, সেটা প্রকৃতির দান নয়, সহস্র সহস্র শতাব্দীব্যাপী এক ইতিহাসের দান।” — কার্ল মার্কস
একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে পুঁজি তার সম্ভাব্য ক্ষমতাকে চিনিয়ে দিচ্ছে যখন, নেতাদের খেয়াল করা উচিত পুঁজির আত্মগঠনের প্রতিটি লুটের এলাকা উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে কীভাবে গর্জে উঠেছে। একে স্রেফ বহির্দেশীয় প্রশাসনের হানাদারির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা চলে না। এ হল প্রতিটি তল্লাটের সম্ভাষণী গর্জন, যে লুটেরা পুঁজির বিধ্বংসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা আত্মইতিহাসের ধ্বনি তোলে। একটি অঞ্চলে মানুষ পিচের চওড়া রাস্তা চাইছেন না, বা কয়লা খনির প্রকল্পে কাজ করে জীবন কাটাতে চান না, তার থেকে অর্ধেক বছর চাষ করে, অর্ধেক বছর মুখোশ বানিয়ে জীবন কাটাতে চান— এটিকে মার্কসবাদীরাও মেনে নিতে পারেন না, তাঁরা এহেন আদর্শকে প্রতিক্রিয়াশীলতা, কিংবা বড়োজোর পশ্চাৎপদতা বলে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ যে জীবন আমাদের চাপিয়ে দিচ্ছে, হাজারো বিদ্যা নামক বাটপারি দিয়ে নিজের প্রথানুগ শোষণের কায়দায় মনন নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে তার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস থেকে, জীবনের নান্দনিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে, তাকে মেনে না নিলে প্রগতির বিরোধিতা করা হয়, এই মত পোষণকারী পুঁজিতান্ত্রিক কমিউনিস্ট চিন্তকদের নিয়ে আমার আশা কম। এঁরা প্রতিশ্রুতি দেন ক্ষমতায় গেলে কমিউনিস্টরা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে মানুষের স্বার্থে প্রচালিত করবেন, কিন্তু ক্ষমতায় না যাওয়া অবধি স্বীকার করবেন না, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ বহুমুখী, তাই প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা তুললেই তাঁদের রাতের ঘুম উড়ে যায়, ফাঁপা ভঙ্গুর জীবননাশক পুঁজিতান্ত্রিক প্রযুক্তির চাহিদাকে নিজের চাহিদাবশতই এনারা সকলের চাহিদা জ্ঞান করেন; এমনকী কেউ তা জ্ঞান না করলে এঁরা তাঁদেরকে এইসব প্রযুক্তির শিকারে পরিণত করাকে প্রগতি মনে করেন। ধনতন্ত্র এইভাবেই কমিউনিস্টদের নিজের সন্তান বানিয়ে রেখেছে, আজ অবধি।
সর্বহারা শিল্প শ্রমিক শ্রেণি বাংলাদেশের ইতিহাসের সন্তান শ্রেণি নয়, বিনয় ঘোষ যে বাঙালির শিল্পোদ্যম দেখে উৎসাহ পেয়েছেন, তা থেকে বড়োজোর বাংলায় মার্কসবাদ চর্চার ঐতিহাসিক শঠতা, হতে পারে অবচেতন বা বিস্মৃতির, একরকম ওরিয়েনটাল মার্কস চর্চার এলেমবৃত্তি প্রমাণিত হয়। এখানকার ছাওয়ালদের যখন শিল্পে কাজ করতে পাঠানো হচ্ছে, তখন তাদের কী অবস্থা হচ্ছে, রক্তকরবী নাটকে তার প্রতিছাপ আমরা দেখতে পাই। উন্নত কারিগর কৃষি হকার সভ্যতার গৌরব বহনকারী সব স্বয়ম্ভূ কিংবদন্তী গ্রাম ও লোকের কথা ও গুরু শিষ্য পরম্পরার প্রবহমান জ্ঞানের প্রতিমূর্তি এক একটা প্রজন্ম, জীবন থেকে সংস্কৃতি যেখানে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, প্রকৃতির বিশেষ ভূমিকা যেখানে প্রধানত জীবনধারণের উপকরণ হিসাবেই, সেখানে শ্রম বেশি সরল ও দক্ষ, যথারীতি মূল্যবান (অর্থাৎ অল্প শ্রম যার ব্যবহারিক মূল্য নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের শ্রমের তুলনায় অনেক বেশি, আর প্রায়োগিক জটিলতা অনেক কম), সেখানে উলটো দিকে, উৎপাদকের সামান্য অবসর কেড়ে নিয়ে মানসিক শ্রমকে মানবিক প্রক্রিয়া হিসাবে শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সম্মিলিত উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত লুট ও ভক্ষণের ব্যবস্থায় উৎপাদকদেরকে তাঁদের জীবনের নান্দনিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে শুধু মানসিক শ্রমদানকারী অনুৎপাদক শাসক, অভিজাতদের প্রাপ্ত অবসর চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান, চিন্তা বিকশিত হবে, এই একমুখী ইতিহাসের বিকল্প মার্কস ইউরোপের ছাপাখানায় পাননি বলেই পৃথিবীর এই বিপুল গ্রীষ্মমণ্ডলের উৎপাদকদের প্রকৃতির সহায়েই অবসর অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের কোনো বিকাশের নজির তিনি দেখতে পান না। কারণ হিসাবে বলেন, “প্রকৃতি সেখানে জ্ঞান, শিল্প, বুদ্ধির বিকাশের কোনো প্রয়োজনীয়তা চাপিয়ে দেয়নি”।
‘অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য’ প্রবন্ধে মার্কস লিখছেন,
শ্রমের প্রাকৃতিক অবস্থায় পার্থক্যের ফল এই যে, শ্রমের একই পরিমাণ, বিভিন্ন দেশে, প্রয়োজনের বিভিন্ন পরিমাণকে মেটায়, আর তারই ফলে, অন্যান্য দিক থেকে সমতুল বিভিন্ন অবস্থায়, প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বিভিন্ন হয়। এই অবস্থাভেদ শুধু প্রকৃতিদত্ত সীমা হিসেবেই অর্থাৎ, অপরের জন্য শ্রম কোথা থেকে শুরু হতে পারে সেই বিন্দুটি নির্ধারণ করার মধ্য দিয়েই উদ্বৃত্ত-শ্রমকে প্রভাবিত করে। যন্ত্রশিল্প যে পরিমাণে অগ্রসর হয়, সমানুপাতে এই প্রাকৃতিক সীমাগুলি পশ্চাদপসরণ করে। আমাদের পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে, যেখানে উদ্বৃত্ত-শ্রমের মূল্য দিয়ে তবেই মাত্র শ্রমিক তার নিজের জীবিকার জন্য কাজ করার অধিকার ক্রয় করে, সেখানে এই ধারণা অতি সহজেই বদ্ধমূল হয় যে, উদ্বৃত্ত-উৎপাদ জোগানো মানবিক শ্রমের এক অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য।
এরই সূত্র ধরে প্রকৃতির ভূমিকাকে তিনি মানবজাতির বিকাশে প্রধানত দেখেছেন দুইভাবে। সবুজ গ্রীষ্মমণ্ডল, যেখানে প্রকৃতি মূলত জীবনধারণের উপকরণ হিসাবে ভূমিকা নিচ্ছে, আর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল যেখানে প্রকৃতির মূল ভূমিকা উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবে। সবুজ গ্রীষ্মমণ্ডলে সতর্কতা, রাজনীতি, জ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না তার কারণ হিসাবে মার্কস লেখেন,
প্রকৃতি যেখানে বড় বেশি উদার, সেখানে সে তাকে মুঠোর মধ্যে রাখে, আঁচল-ধরা শিশুর মতো। নিজেকে বিকশিত করার কোনো প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতি তার উপর চাপিয়ে দেয় না।
গত দুইশো বছরে আমরা আমাদের উন্নত গৌরবশালী সভ্যতা এবং তার ধূলিসাৎ হবার ন্যক্কারজনক ইতিহাস পরিচয় জানতে পেরেছি বলেই মার্কসের এই মতকে আমরা অমার্কসবাদী বলেই প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বলতে পারি, প্রকৃতির ভূমিকা গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রধানত জীবনধারণের উপকরণ হিসাবে বলেই প্রকৃতি এখানে লুটেরা পুঁজির বিকাশ কিংবা যুদ্ধাস্ত্র প্রযুক্তির বিধ্বংসী বিকাশে, এমনকী নিদেনপক্ষে সরাসরি উৎপাদকদের জীবন থেকে নন্দন ও সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করবার অভিমুখে পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে প্রচালিত করেনি, বরং সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই উৎপাদকদের নান্দনিক অভিব্যক্তিকে রাঙিয়ে তুলবার প্রকল্প দিয়েছে, যৌথ, সরল দক্ষ শ্রম ও সহজলভ্য প্রকৃতির সহায় স্বতন্ত্র উৎপাদন বিকেন্দ্রীভূত ভারসাম্যে জীবনকে সুখ ও আনন্দের সাধনায় প্রগত রেখেছে, তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আরও অনেক দেশের মতো এখানকারও আবিষ্কৃত আছে। ছাপাখানা আসবার পর থেকে ধনতন্ত্র জ্ঞানের সংজ্ঞা যা দাঁড় করিয়েছে, তা মানবজাতিকেই মূলগতভাবে মূর্খ প্রমাণ করে, কিন্তু বিবেকবানরা জানেন মূর্খদের গবেষণাতেই একমাত্র সকলেই মূর্খ বেরোয়, তাই ‘ছাপাখানা’ ঘিরে থাকা পৃথিবীর পঁচিশ শতাংশ এই কর্মহীন বিদ্যাচর্চী অভিজাত মূর্খদের পৃথিবী ধ্বংসকারী জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করবার হিংস্রতাকে জ্ঞান করেই প্রত্যেক মার্কসবাদীর আজ নতমস্তকে নতুন পৃথিবীর পরিকল্পনা করা উচিত।
উপনিবেশিক দখলে চলে না গেলে এই দেশে প্রাকৃতিকভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশ সংঘটিত হত কি না, এই প্রশ্নটি অবান্তর কারণ তার প্রাকৃতিক গুণেই পুঁজি নিজেই গঠিত হয়েছে প্রাথমিকভাবে যে সব উপনিবেশকে লুট করে, তার মধ্যে আমাদের দেশ অন্যতম। আজ আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত উপনিবেশিক লুণ্ঠনই পুঁজির গঠন ও বিস্তারকে বাস্তবায়িত করেছিল, যার অন্যতম রূপ আদিম সঞ্চয়নের পদ্ধতিটিও এই লুটের প্রকারফের। পৃথিবীর ইতিহাসের সামগ্রিক পরিক্ষেপে পুঁজি এমন একটি সম্পর্ক হিসাবে গ্রীষ্মমণ্ডলকে লুটে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছিল, যা প্রধানত পর্যবেক্ষণমূলক— শ্রমহীন অর্থাৎ প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন জ্ঞানচর্চার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে প্রকৃতির সাথে মানুষের আবহমান সংঘাতে প্রকৃতিকে বশ ও নিয়ন্ত্রণ করবার চূড়ান্ত লক্ষ্যে জীবতন্ত্র ও পৃথিবীকেই আজ খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে। আজকের যুগে বিপ্লবকে সফল করতে হলে ধনতান্ত্রিক এই জ্ঞানকাঠামোর উদ্দেশ্যকে নাকচ করে এই দেশের জীবনধর্ম ও সমাজ পদ্ধতির বস্তুবাদী ঐতিহাসিক অভিমুখে তাকে প্রচালিত করবার প্রকল্প নিতে কুণ্ঠা করা জালিয়াতি।
বিবেকবান বিপ্লবী নেতৃত্ব অবশ্যই রাষ্ট্র বিলোপের পর্যায় হিসাবে সমাজতন্ত্রকে দেখেন বলেই তারাই একমাত্র রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনমাফিক তার ক্ষমতাকাঠামোকে সীমাবদ্ধ রাখবার ধীর রাষ্ট্র অবলুপ্তির কাজকে ত্বরান্বিত করবার প্রকল্পের গুরুত্ব বুঝবেন। বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রতন্ত্রকে শিথিল ও অবলুপ্তির রাস্তায় নিয়ে যেতে প্রাথমিক ও প্রধান ভূমিকা স্থানীয় অর্থনীতির। গ্রীষ্মদেশের এই উপনিবেশ-পূর্ববর্তী সমাজের দীর্ঘকালের স্বনির্ভরতার শক্তি স্থানীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপকরণের উপর সরাসরি উৎপাদকের মালিকানা, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের সামাজিক মালিকানা, উৎপাদনে উৎপাদকের স্বনিয়ন্ত্রণ, সবার জন্য খোলা হাট, হকার ব্যবস্থাই প্রমাণ যে সম্পদকে সম্পত্তিতে পরিণত করবার বাধ্যতা প্রকৃতিই তার তরফ থেকে এই দেশের জীবতন্ত্রের উপর চাপিয়ে দেয়নি। এমনকী মরশুমি ও স্থানীয় উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণবাদের চাতুর্যকেও পর্যন্ত সর্বময় প্রভাব বাংলাদেশে কায়েম করতে দেয়নি, দিল্লি প্রশাসনকে তো দূরের কথা।
অর্থাৎ যে উৎপাদন ব্যবস্থা জ্ঞান বা প্রযুক্তি বা দক্ষতার ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাস করে না, অথচ ব্যক্তির বিকাশের প্রতিটি শর্তকে সামাজিক মালিকানায় রেখে, ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ সুন্দর বিকাশকে একটা সামষ্টিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির মাঝে অব্যাহত রাখতে পারে; যে ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত অসংখ্য এককে উৎপাদন ও বণ্টনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখে, অসংখ্য উৎপাদক, অসংখ্য বিক্রেতা, অসংখ্য ক্রেতার এই ত্রিভুজি পরস্পর নির্ভরশীলতার সেই ঐতিহাসিক মাস্টারস্ট্রোক ব্যবস্থা হল কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থা, যা সবুজ গ্রীষ্মমণ্ডলে ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করে একটি সাম্যবাদী অভিমুখে এই দেশকে নিয়ে যেতে উৎপাদন, বণ্টন ও তাকে ঘিরে মানুষের ধর্ম ও উপস্থাপন থেকে রাষ্ট্রকে কার্যত নিঃসাড় করবার প্রকল্প নিতে পারে। একটি অখণ্ড পৃথিবীর অংশ হিসাবে ধনতন্ত্রের যে দানগুলি গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য, তার সমুচিত ফায়দা তুলতেও আমাদের বদ্ধপরিকর থাকা উচিত। ক্ষমতা কাঠামো বা উৎপাদন কাঠামো দুটোই এমন জিনিস যাদের অসংখ্য এককে ভেঙে ফেলাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রগতি, উলটো দিকে এগুলির কেন্দ্রীভূত রূপই ফ্যাসিস্ত।
অতএব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে চীনের প্রাচীর তুলে আরও একশো বছর যদি তর্ক চলে কোনটা প্রকৃত স্তর, তাহলেও কোনো সদুত্তর প্রতিষ্ঠা পাবে না। পাত্রাধারে তৈল নাকি তৈলাধারে পাত্র, এই বিতর্কে মুন্ডুপাত না করে স্বীকার করে নেওয়া উচিত, একটা থাকবার বাসা যদি দশরকমভাবে বানানো যায়, বিপ্লবও দশরকমভাবে সম্ভব, অতএব সবচেয়ে সরলটির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই যেহেতু রাষ্ট্রবিলোপের কর্মসূচি হাতেকলমে নেয়, তাই রাষ্ট্রবিলোপ নামক ইউটোপিয়ান কাজটি সমাজতন্ত্রের শপথ নেওয়া একটি সমাজতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্র চরিত্রের রাষ্ট্রের হাতেই অর্পিত হতে পারে।
কলকাতার এক তরুণ চিন্তকের ‘বেসরকারি সমাজতন্ত্র’ নামক আইডিয়াটি আমার মনে হয়েছে এযাবৎ অরথোডক্স কমিউনিস্টদের চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ আইনি বিপ্লবের কর্মসূচি, যে সমাজতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রের মর্মবস্তুকে গ্রহণ করে তার রণনৈতিক বাস্তবতা ছাড়াই। বাকি সব সমানে মাইক হাতে, পত্রিকা হাতে রণনৈতিক বাস্তবতার কথা সোচ্চারে প্রচার করে গেলেও, এখনও খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতন ভূমিসংস্কারের জন্য জমি খুঁজে চলেছেন। যেখানে আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই ভূমি বণ্টিত হয়েছে, সেখানে প্রকল্পহীন হয়ে বিপ্লবী গেরিলা আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়েছে, সবুজ বিপ্লব তার ক্ষীর খেয়ে বপু বাড়িয়েছে। বাস্তবত বাংলার মতো সমতল ও খণ্ডীভূত চাষের জমি আর কারিগর হকার হাট ব্যবস্থার প্রদেশে নূতন দেশ গঠনের সম্ভাব্য সরল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতিমুখ এবং তার সমরনীতি নির্ধারণে কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের তাত্ত্বিক দুর্বলতার থেকেও ব্যভিচার বেশি দায়ী।
এত দূর পড়ে কেউ যদি কল্পনা করেন লেখক পুনরুত্থানবাদী বা নৈরাজ্যবাদী, বা দুটোরই মিশ্র রুশরূপ— নিদেনপক্ষে নারোদনিক, তাহলে তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো, অতীতে ফিরে যাওয়া যায় না। আগামীর পরিকল্পনা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানকারী সহমর্মী সহনশীল স্বনির্ভর সুন্দর সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ পদ্ধতিকে গ্রহণ করবার প্রসঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্র বিলোপের পথে আমাদের দেশে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও সমাজ বিকাশের সম্ভাব্য গতিমুখকে বিচার করবার চেষ্টা করছি। বস্তুত করপোরেট পুঁজি যে বাস্তবতা এই বিকাশের সামনে খাড়া করে রেখেছে, তার বিপরীতে পুঁজিকে পূর্ণত বয়কট করবার কাজটি সর্বহারা শ্রেণির দ্বারা অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে সম্ভব, কেন্দ্রীয় সকল প্রকার উৎপাদন সংগঠনকে যেখানে শ্রমিকরা দখল করে নিজেদের পরিচালনায় ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে আনবেন; কিন্তু এর অভীষ্টতা কেন্দ্রের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে বিলুপ্ত করবার কর্মসূচিটি সাম্যবাদী কর্মসূচি হিসাবে উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রশাসন, সুরক্ষা, বিচার, শিক্ষা ব্যবস্থার স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবার প্রকল্প না নিলে, তার সম্ভাব্যতা যথারীতিই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কে কে পুঁজিবাদের রোডার বেরুল, তার উপর নির্ভর করবে।
আমার ধারণা প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদ নামক একটি নতুন ধারণা আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পশ্চিমে আসতে চলেছে। পুঁজি যে সীমাবদ্ধ, ধনতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে মার্কস যে উদ্বৃত্ত মানুষদের দেখিয়েছিলেন, তাকে জ্ঞান করেই মার্কসবাদীদের এ বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। বিশেষত ‘তৃতীয় বিশ্ব’ নামক প্রাচ্যবাদী এলাকার মার্কসবাদীদের। একটা শহরেই পুঁজি সকলের অর্থনীতি ধারণ করতে পারে না, সারা বিশ্বে তো দূর, উপরন্তু যুদ্ধ মন্দা দুর্ভিক্ষে জর্জরিত করে সংখ্যাগুরু উৎপাদক ও উদ্বৃত্ত মানুষদের, সেখানে রক্তচোষা এই বাদুড় কীভাবে গোটা বিশ্বের সকল দেশের বিকাশের প্রয়োজনীয় পরিক্ষেপ হবে— এর উত্তর আজকের মার্কসবাদীরা একটু নতুনভাবে দিক। বরং পশ্চিমকে বাতিল করা রাষ্ট্র বিলোপের সমাজ প্রক্রিয়া খুব জলদি পশ্চিমকেও তার আদর্শ ঐক্যে অন্তর্ভুক্ত করবে, খুব অবাক হব না যদি গণতন্ত্র-পূর্ব সাম্রাজ্যবাদ ও গণতান্ত্রিক যুগের সাম্রাজ্যবাদের পর এশিয়া আফ্রিকার এই ‘সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ’ আকাডেমিয়া কাঁপায় এই বলে যে, ‘গেল গেল সব বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল গো, সব শিল্পের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল গো, কেউ আর কালচারে বিশ্বাস করছে না গো, কেউ আর মহাকাশে যেতে চাইছে না গো, কেউ আর খাবার চালের থেকে সত্তর গুণ বেশি দাম দিয়ে সেলুনে চুল কাটতেও যাচ্ছে না গো, এমনকী নতুন ডাক্তাররা পর্যন্ত আশি ভাগ চিকিৎসার প্রযুক্তিকে বাতিল বলে ফেলে দিচ্ছে গো, বলছে খুশিমতো গাড়ি কিনতে দেবে না, ট্রেনে তো এসি ভেঙেই দেবে, এমনকী ঘরেও এসি কিনতেও নাকি রাষ্ট্রীয় বাটপারি সহ্য করতে হবে গো, আমাদের মাত্র তিন জনের সংসার আর তেরো তলা বাড়ি বানিয়ে থাকতে পারব না গো! হায়!’
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের নেতির নেতি তত্ত্বের মধ্যে সাধারণ সত্যটি অনুপস্থিত যে, বিকাশ এক ধরনের দ্বান্দ্বিক ঐক্যে অর্থাৎ সংশ্লেষণে গঠিত হয়। কোনো সৃষ্ট সক্রিয় দ্বন্দ্ব নিরসিত হবার অর্থই হল সংশ্লেষণের মাধ্যমে একটা নূতন দ্বন্দ্বে উপনীত হওয়া, যা-ই বস্তুর বিকাশ। এই বিকাশের প্রধান শর্ত সেই সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি পুরাতন দ্বন্দ্বের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মাত্র, অর্থাৎ তাপশক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে এক সময় বিস্ফোরিত হলেও তা অন্তর্বস্তুতে তাপশক্তিরই নানারূপ বিকাশমান প্রকাশ। তার অবদান সাধারণভাবে এখানে একটি নূতন জারিত ঐক্যের অংশ।
যে কোনো আদর্শই সেই পবিত্র ঐক্য যা হল বিকাশের নির্ধারক শর্ত, তা ধর্মীয় হোক বা বৈজ্ঞানিক হোক। এই আদর্শ আসলে সামাজিক দ্বন্দ্ব বহির্ভূত কিছু নয়। এটি হল ঐক্যের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের নিরসিত হতে চাইবার প্রবণতা, বা বস্তুর বিকাশের গতিধর্ম। এই আদর্শ একটি নূতন ঐক্যের শপথ মাত্র। আদর্শ নামক ধারণাটিই প্রমাণ করে মানুষ একটি পরম প্রক্রিয়া হিসাবেই শ্রমকে অনুশীলন করে। অর্থাৎ যতই যুক্তি, বিজ্ঞানের ছটা বেরুক না কেন, মানবিক প্রক্রিয়া হিসাবে শ্রম এক প্রকার ফলাফল বা সংশ্লেষণ বা ঐক্যের সাধনক্রিয়া। ‘রণনীতি ও রণকৌশল’ শীর্ষক একটি ব্যক্তিগত নোটে আমি লিখেছিলাম, “মানবিক প্রক্রিয়া হিসাবে শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ‘প্রকল্পনা’ ও ‘ফলাফল’ একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিকাশমান মানবিক শ্রমের সেই প্রধান শর্ত যা সকল প্রকার ঐক্যকে ধারণ করছে। মানুষ তার শ্রমের এই বৈশিষ্ট্যটির জন্যেই কোনো আদর্শ ফলাফলের অভীষ্টে কোনো আদর্শ প্রকল্পনা ছাড়া বাঁচতে পারে না।”
এখন জুলাই অভ্যুত্থান প্রকৃতই বাংলাদেশের উর্বর উন্নত ভৌগোলিক ঐতিহাসিক গঠনকে চিহ্নিত করে একটি দেশ গঠনের অভিপ্রায়কে ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছে বলেই জুলাই অভ্যুত্থান এই আদর্শ ঐক্যের প্রতি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পা, যাকে মার্কিনিরা একদিকে ইসলামোফোবিয়া তৈরিতে কাজে লাগাবে, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী ইসলামি দলগুলির পিছনে টাকা ঢালবে, তাদের দিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা সফল করবার মাধ্যমে পৃথিবীর এই সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলটিকে পুঁজিবাদী করপোরেট ব্যবস্থার পরিপূর্ণ দখলে আনবার কর্মসূচিতে অযাচিত রক্তক্ষয় ঘটাবে। এর জন্য সাম্রাজ্যবাদ বদ্ধপরিকর। মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ এক্ষেত্রে যথার্থই সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ প্রবণতার প্রতিভূ। কিন্তু যে প্রকার জ্ঞান, সংগ্রাম, উৎপাদন, জীবন ও সমাজ কাঠামো এই করপোরেট উপনিবেশবাদকে পরাস্ত করে প্রগত থাকতে পারে, তার অবশ্যম্ভাব্যতাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু এই যে, কোনো বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সুসজ্জিত সামরিক জনতা ক্ষমতা দখল করছে না দেখলেই আজকের কমিউনিস্টরা সেটিকে সাম্রাজ্যবাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক হিসাবে ছাড়া আর দেখতে পারেন না, এটি তাদের নিজেদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা ঢাকবার নামান্তর মাত্র, কারণ সুসজ্জিত সামরিক বৈপ্লবিক শক্তি সংহতকরণের কাজটি অভ্যুত্থানের গণশক্তি তত্ত্বেও উপলব্ধি করেনি, হাতেকলমেও কোনোদিন গ্রহণ করবার অঙ্গীকার রাখেনি। অভ্যুত্থান জনতার বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রকট ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজির করে মাত্র, তাকে সফল করবার কাজ এই সচেতন বৈপ্লবিক শক্তির বা পার্টির স্বগৃহীত দায়িত্ব৷ অথচ তারা নিজেদের ব্যর্থতার কথা পর্যালোচনা করে নতুনভাবে ঝাঁপিয়ে অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে কার্যকরী করবার বদলে অভ্যুত্থানকেই সামগ্রিকভাবে একটা সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের প্রকাশ বা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন। এই বয়স্ক ও ব্রাত্য চিন্তার আলস্য ও সংকীর্ণতাকে বর্জন না করাটা জনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।
জুলাই অভ্যুত্থান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকল্পিত অভ্যুত্থান ও এর মধ্যমে ‘পালাবদল’-এ নতুন ক্ষমতায় আসা উপদেষ্টা সরকার যে মার্কিন সাম্রাজ্যের পুতুল হয়ে চলবে, এই মূল্যায়ন লেনিনবাদী নয়, কারণ এটি ফ্যাসিস্ত শাসনে বিপর্যস্ত জনতার প্রকৃত গণসংগ্রামের মাধ্যমে ন্যূনতম অর্জনকেও নস্যাৎ করে। এই অসাড় দম্ভের মূর্খামি কি জানে না একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান অর্থাৎ একটি পরাজিত বিপ্লবী অভ্যুত্থান সেই অঞ্চলে বিপ্লবের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র করে, শর্ত আরও প্রস্তুত করে, জনতার একটা বিপুল অংশের বৈপ্লবিক উদ্যমকে সচেতনভাবে কার্যকর রাখে, নতুন তত্ত্বায়ন বা রণনীতির বিকাশকে শোধরায়। রাশিয়ায় ১৯০৫-এর পরাজিত বিপ্লবও পৃথিবীর ইতিহাসে এমনই একটি ঘটনা, যা রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বস্তুভূমি প্রস্তুত করতে শুরু করেছিল। অভ্যুত্থানে জনতার অর্জন শুধু ‘ড. ইউনুস’ নয়। বরং একটা চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ত অপশাসনকে উৎখাত করতে পারা হচ্ছে গণঅভ্যুত্থানের প্রাথমিক অর্জন, একে স্বীকার না করতে পারার পক্ষে লেনিন কথা বললে লেনিনও লেনিনবাদী নন।
জনাব ফরহাদ মজহার লিখেছেন— দেশকে অভ্যুত্থানের বিপ্লবী প্রাণপথে প্রচালিত করতে গেলে করপোরেট নিও-লিবারাল বৃহৎ পুঁজি নিরপেক্ষ বিকেন্দ্রীভূত শক্তিশালী স্থানীয় অর্থনীতি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে ও গণপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো ধরনের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রবাদী আমলাতান্ত্রিক সেনা ব্যবস্থা বিপ্লবের দায় বহন করতে বা প্রকৃতই সুরক্ষিত রাখতে পারে না।
এই দুই প্রধান উপকরণকে ঘিরেই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে ‘অভ্যুত্থান’-কে তার সংজ্ঞা বা ধারণাগত বোঝাপড়ার কাঠামোয় বিচার করবার মূঢ়তা প্রকট হয়। তা এ যুগে এমন একটি বিপ্লবের প্রকল্প যার সফল হবার সম্ভাবনা দুই শতাংশেরও কম। বরং বিপ্লবের বাস্তব ও সরলতম পথ হিসাবে আজ দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত, কারণ অভ্যুত্থানের দীর্ঘকালীন প্রস্তুতিকাল এবং দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মধ্যে কোনো নীতিগত বা মৌলিক ফারাক নেই। এই প্রস্তুতিকে যুদ্ধ জয়ের জন্য এক দুর্বল অবস্থান থেকে চরিত্রে প্রাথমিকভাবে আত্মরক্ষামূলক শক্তিবৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয়ের কাল হিসাবে দেখা উচিত।
অভ্যুত্থানের সংজ্ঞা অনুযায়ী অভ্যুত্থান আসলে একটি বিদিত ব্যর্থ বিপ্লবের প্রকল্প। যা পদ্ধতিগতভাবে সফল হবার নয় তাকে প্রকল্প বলতেও আমার বাধে। বিপ্লবের প্রকল্প হিসাবে সফল হবার শর্তই হল সংগঠিত শক্তি, যা-ই মূলত দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ। অর্থাৎ বিপ্লবের নির্ধারক শক্তি হল দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে সংহত একটা শক্তি যে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লবকে প্রগত করবে। দীর্ঘদিন ধরে সংগঠিত এই শক্তি ছাড়া ব্যবস্থা বদলের অভিপ্রায় নিয়েও যে ‘অভ্যুত্থান’, এই কারণেই, তা মূলত একটি গণআন্দোলন যার নিজের দাবি হাসিল করবার বিদিত শক্তিটুকু স্পষ্টতই নাই। ইউরোপে সমাজতন্ত্র হয়তো সবশেষে স্থাপন হবে এই কারণেই যে সেইখানে জনতার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথটি সর্বতোভাবে কঠিন, কেননা বিদ্যমান ঐতিহাসিক ক্ষমতা কাঠামো কেন্দ্রীয় ফ্যাসিস্ত চরিত্রের এবং এ সম্পূর্ণতই বৃহৎ পুঁজির উদরে।
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কিংবা গণপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আবেদন— আসলে বাংলাদেশ গণঅভ্যুত্থানের আজকের বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দীর্ঘকালীন জনযুদ্ধের স্তর একটি গণপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গোপনে বিকশিত করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সাধারণভাবে সবচেয়ে জরুরি, মেয়াদি ও দুর্বিষহ কাজটি করবার রণনীতি নেয়, যা ক্ষমতা দখল করে একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই, যখন সেই অভ্যুত্থানটির বৈপ্লবিক প্রাণপথকে বাস্তবায়িত করবার শক্তি ও দক্ষতা সে ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। কিন্তু আজ আমরা যা দেখছি তার সার কথা হল— কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রবাদী আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ও সেনার বদান্যতায় অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক স্পিরিট পৃথিবী ধ্বংসকারী ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।
সত্তর দশকের পরে এই দেশের বিপ্লবী সংগঠনগুলি এমনভাবে প্রকাশ্যে বিপ্লব চর্চার অবাধ সুযোগসুবিধা নিল, তা বিপ্লবী সংগ্রামকে কার্যত আইনি জ্ঞানচর্চায় পর্যবাসিত করল। অন্ধ্রের জনযুদ্ধ, পশ্চিমবাংলা ও বিহার, ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্র, পার্টি ইউনিটি ইত্যাদি বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির চার দশকের ধারাবাহিকতায় সিপিআই (মাওবাদী) তার রণনীতি ও রণকৌশলে লিখেছিল, প্রকাশ্য বিপ্লবী গণসংগঠনগুলি আসলে কীভাবে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব খতম ও গ্রেফতারির জন্য রাষ্ট্রের অলক্ষ্য তরিকা হিসাবে কাজে লেগেছে। রাষ্ট্র তার দমনের ছকেই নজরদারির সৌজন্যে এমন সব সংগঠনকে ছেড়ে রাখে, যাকে লক্ষ্য করে গোপন শক্তিকে বিনাশ করা যায়। একটি অপ্রিয় উদাহরণ হল গত দুই বছরে পূর্ব ভারতের প্রধান ও অভিজ্ঞ সিংহভাগ বিপ্লবী নেতাদের ধারাবাহিক গ্রেফতারি। এমনকী নব্বই দশক পরবর্তী রাষ্ট্রবিরোধিতার পরিসরকেও নিছক গৃহযুদ্ধবিমুখী সংবিধানসম্মত জ্ঞানচর্চা ও গান বাজনা মিছিল সমাবেশে রূপান্তরিত করল; আর এখন তো সমাবেশ করা মাত্রেই পাপ, বেআইনি কাজ।
আর আজ কলকাতা শহরে এমন সব মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন যাঁরা পেঁয়াজের দামও জানেন না। কৃষি পশ্চাৎপদ, তাই তার অর্থনীতি সম্পর্কে উৎসাহ নেই, অথচ ভারতের বিপ্লবের সমস্যা মুদ্রাস্ফীতির কারণ-সহ উৎপাদন সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে চিন্তায় কেন প্রযুক্তি অনিবার্য, কেন স্বপ্ন আছে অথচ আশা বড়জোর একদিন জঙ্গল থেকে ছকে ছকে গেরিলাদল শহরে ঢুকে ক্ষমতা দখল করবে, শ্রমিকেরা একই সাথে নেচে উঠবে, আমরা সুযোগ বুঝে ক্ষীর খাব, গঠনমূলক মতামত দেব ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। নবজাগরণী থেকে ওরিয়েনটাল, মার্কসবাদীদের এই ব্যাপারটি রোগ নয়, বৈশিষ্ট্য।
বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিকাশের সরলতম পথে বাস্তবে এগুতে গেলে এখানে এমন একটি বিপ্লবী সাম্যবাদী পার্টির অস্তিত্ব নেই কিন্তু প্রয়োজন আবশ্যিক যে— মার্কসবাদী শ্রেণিসংগ্রামের ধ্রুপদী ও প্রথানুগ পদ্ধতিকে এই বিকাশের পথে যেচে নিয়ে, এখানকার বস্তুবাদী ইতিহাস বিকাশের সম্ভবপর বিপ্লবের দীর্ঘ, এলাকাভিত্তিক বা স্থানীয় শক্তি, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সংগঠনের প্রধানত গোপন, বেআইনি ও সশস্ত্র প্রস্তুতি কর্মসূচি নেবে। এই কাজ ছাড়া জনতার বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে সফলভাবে রূপ দেবার অন্য কোনো সহজ রাস্তা নেই। মতাদর্শগতভাবে সাম্যবাদী আদর্শের রণনীতিই একমাত্র ধারণ করতে পারে এমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক ধারাপাতের সম্ভবপর দিশাকে, যা তার ভৌগোলিক গঠন, অর্থনৈতিক পরাকাষ্ঠা ও জীবন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে নূতনভাবে, আপনা থেকে নয়। সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতায় এই গঠন একটি বাহ্যিক শক্তির বলকে দাবি করে, যে সুসংহত প্রয়াসে একে ত্বরান্বিত করবে।
কথা হল এই সাম্যবাদী পার্টিটির বুঝে নেওয়া প্রয়োজন বিপ্লবের ‘গোপন’ প্রাথমিক কাজটিও একা কোনো পার্টির ক্রিয়াকলাপ নয়। জনযুদ্ধের প্রতিরক্ষা বাহিনী বা গণফৌজ একটি গণ কিন্তু গোপন অংশ; অর্থাৎ চরিত্রে গণ কিন্তু কার্যপ্রক্রিয়ায় গোপন। তাকে তার মর্যাদা অনুসারেই সকল স্তরে বিকশিত করার কাজ আবশ্যিক। বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন বা ভাববৈঠকি আইনি পথে যে কাজটি গত এক দশকে করেছে, তার স্থানে ভারতে গণমুক্তি গেরিলা ফৌজ যে কাজটি গত দুই দশক ধরে করে চলেছে তার গুরুত্ব প্রাথমিক, কিন্তু প্রথম পর্যায় পার করে এই দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল সমতলীয় (আশি ভাগ সমতল সমেত) ভারত সাম্রাজ্যে বিপ্লবের যুদ্ধ ও ক্ষমতাকে সমতল প্রদেশের ধারেকাছে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারল না, তাকে মূলত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক কুপ্রভাব বলা যায়। ওরিয়েনটাল মার্কসবাদে দুষ্ট ক্রিয়া বিপ্লবের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দীর্ঘস্থায়ী গোপন প্রকল্প নিলেও বাস্তবে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিকে লক্ষ্যবর্জিত আত্মরক্ষার যুদ্ধে নেতা বানিয়ে রেখেছে। উলটো দিকে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন গত দশ বছরে যা-ই করুক, অভ্যুত্থানের নীতিগত ব্যর্থতার দোষে অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার একুশ শতাব্দীতে আর জনতার থাকে না, যদি না তার সংগঠকরা একটি দীর্ঘ প্রস্তুতিকালের মধ্যে দিয়ে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে থাকে। অর্থাৎ নতুন দেশ গঠনের তত্ত্বকে জনপ্রিয় করার মধ্যে দিয়ে নতুন দেশ গঠনের শর্ত প্রস্তুত করবার আবশ্যিক কাজটি যদি একটি গোপন বিপ্লবী গণসামরিক বাহিনীর কার্যক্রমের সাথে সুপরিকল্পিত, এলাকাভিত্তিক সমন্বয় বজায় রেখে অভ্যুত্থানকে পরিকল্পনা করে, এই স্বপ্ন ছাড়া এ অধম লেখকের আর কোনো জাত নেই।
অধমের চিন্তা বিপ্লবে জয় পেতে গেলে একটা সংগঠিত দক্ষ বিপ্লবী শক্তি পৃথিবীর যে কোনো শক্তির সাথে কূটনীতিক সম্পর্ককে বিপ্লবের স্বার্থে কাজে লাগাতেই পারে, কিন্তু প্রতিরক্ষাশক্তি-বিহীন অভ্যুত্থান আমলাতান্ত্রিক সামরিক শক্তির অধীনে চলে গেলে সাধারণত সাম্রাজ্যবাদের করুণ শিকারে পরিণত হতে খুব বেশি সময় নেয় না। তাই অভ্যুত্থান বিপ্লবের প্রকল্প তখনই, যখন তা একটি দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংগঠিত গণশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে।
চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে পুঁজি তার চরম সীমাবদ্ধতার কথা জানান দিচ্ছে। বিশ্বপুঁজির আন্তর্জাতিক শিল্পনীতি ও শিক্ষানীতি— বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষকেই তাদের ভবিষ্যৎ থেকে বাদ দিয়েছে। অতি সস্তায় শ্রম দেওয়ার জন্য ছাড়া তাঁদের বেঁচে থাকাতেই পুঁজি আর উৎসাহিত নয়। এমনকী ভোট দেবার যে ব্যাপারটি স্থানীয় দালালদের দিয়ে করানো হচ্ছিল, যুদ্ধের বাজার এত অস্থির যে সাজানো দালালদেরও আর কোনো ভূমিকা থাকছে না, সামান্য গড়বড় হলেই রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী সেখানে আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খপ্পরে পড়ে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ বিপর্যস্ত হবেন, নাকি আগত এই শতাব্দীর মহাধ্বংসের কালকেই নতুন দেশ গঠনের দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধের কালে পরিণত করবার প্রকল্প নেবেন, তা নির্ভর করছে নতুন দেশ গঠনের অভিমুখ এবং প্রধান চালিকাশক্তিকে সরলভাবে নির্ণয় করবার উপরে। সকল স্থানে শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শকে ‘নেতা’ হিসাবে ‘চাপিয়ে’ দেবার বদভ্যাস শ্রমিক শ্রেণির ঐতিহাসিক মর্যাদাকে অপমান করবার নামান্তর। শ্রমিক শ্রেণি তার ঐতিহাসিক যোগ্যতাবশেই ধনতন্ত্রকে বাতিল করবার কাজে অগ্রগামী ভূমিকা নিতে দায়বদ্ধ, কারণ এই শ্রেণি হল ধনতন্ত্রের সেই অবিচ্ছেদ্য অংশ যা পুঁজির উৎসকে ধারণ করে, তার ফলে পুঁজির বিলুপ্তির সঙ্গে তারও আত্মবিলুপ্তির মাধ্যমে একটা ঐতিহাসিক প্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে চায়, যখন উৎপাদনের হাতিয়ারের উপরে উৎপাদক হিসাবে তারও সামষ্টিক (সামাজিক) মালিকানা প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়েছে। এই যাত্রাপথটিতে নতুন নির্মিত রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বাধীনে থাকা জরুরি এই কারণেই যে সেই রাষ্ট্রের অধীন বিদ্যমান কেন্দ্রীয় উৎপাদন সংগঠন ও পরিকাঠামোকে উৎপাদকের সরাসরি কর্তৃত্বে রাখা আবশ্যক, কিন্তু প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, সুরক্ষাব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বনির্ভর এককে প্রচালিত করবার ব্যবস্থা দ্বারা এই কেন্দ্রীয় অবকাঠামোটিকে বিলুপ্ত করে এক একটি দেশকে প্রকৃত মুক্ত করবার স্বপ্ন দেখাই এই মহাদেশে ইতিহাসসম্মত। কৃষি কারিগর হকার অর্থনীতিকে প্রাণ করে জনতার পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী কাজই এই দেশে সমাজতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান কাজ।
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
তীর্থরাজ ত্রিবেদী

লেখক, সমাজকর্মী, বসবাস পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরে।